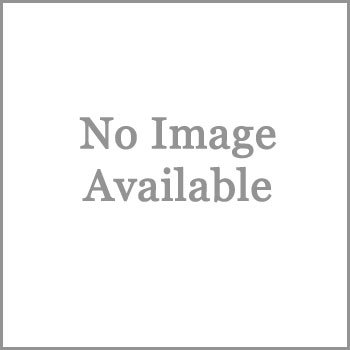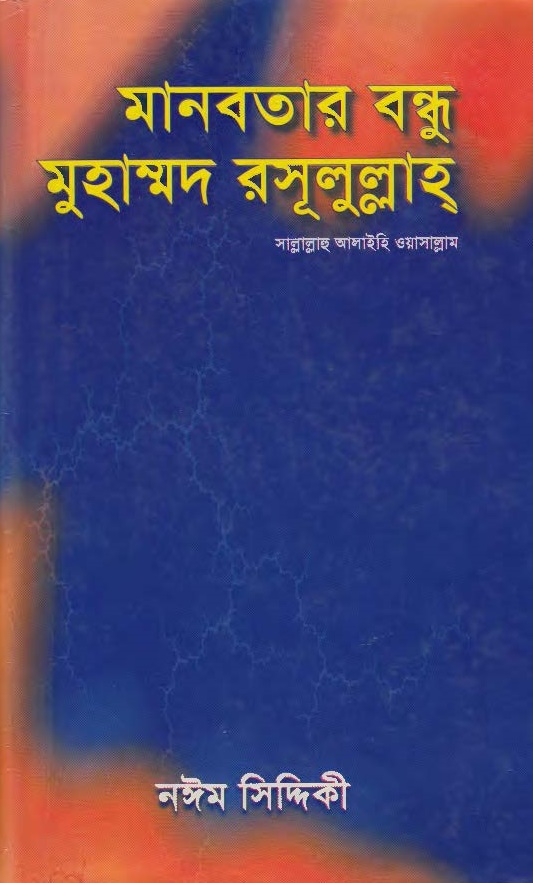অধ্যায়ঃ ৪
মাদানী অধ্যায়ে মানবতার বন্ধু সা. : ইতিহাসের পট পরিবর্তন
“অতি প্রত্যুষে উম্মে আহমদ আমাকে দেখলো, আমি যে ব্যক্তিকে না দেখেও ভয় পাই, তাঁর হেফাযতে বেরিয়ে যাচ্ছি, তখন সে বলতে লাগলো, তোমার যদি চলে যেতেই হয় তবে ইয়াসরিবে যেয়োনা, আমাদেরকে অন্য কোথাও নিয়ে চল।
আমি তাকে জবাব দিলাম, এখন ইয়াসরিবই আমাদের গন্তব্যস্থল। দয়াময় আল্লাহ যেদিকেই বান্দাকে নিতে চান, বান্দা সেদিকেই রওনা হয়।
কত যে প্রিয় সাথী ও শুভাকাংখীকে আমরা পেছনে ছেড়ে এসেছি এবং কত যে বেদনা ভারাক্রান্ত মহিলাকে অশ্রু বিসর্জন দিতে দেখে এসেছি, তার ইয়ত্তা নেই।
তুমি তো ভাবছ, আমাদেরকে যারা বহিষ্কার করেছে, তাঁদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছি। অথচ আমাদের অন্য উদ্দেশ্য রয়েছে।
এক পক্ষ আমরা, আর অপর পক্ষ হলো আমাদের সেই সব বন্ধু, যারা সত্য পথ থেকে দূরে সরে গেছে এবং আমাদের ওপর নির্যাতনের অস্ত্র প্রয়োগ করে হাঙ্গামা বাধিয়েছে।
এই দুটো বিবাদমান পক্ষের একটা সত্যের পতাকা ওড়াবার সৌভাগ্য লাভ করেছে এবং সঠিক পথে পরিচালিত হয়েছে। আর অপর পক্ষ আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।
রক্ত সম্পর্কের দিক থেকে যদিও তাঁরা আমাদের ঘনিষ্ট আত্মীয়, কিন্তু (আদর্শ ও লক্ষ্যের ঐক্য ভিত্তিক) আন্তরিক সম্পর্ক যেখানে থাকেনা, সেখানে কেবল রক্ত সম্পর্ক অচল।
এমন একদিন আসবে, যেদিন তোমাদের ঐক্য ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। তোমাদের সামষ্টিক অস্তিত্ব ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। তখন তুমি ভালো ভাবেই জানবে, আমাদের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে কারা সত্যের পথে রয়েছে।”
(আবু আহমাদ বিন জাহাশের হিজরত সংক্রান্ত কবিতার সার সংক্ষেপ)
মানবতার সবচে বড় বন্ধু এবং বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইতিহাসের স্রষ্টা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনেতিহাসের মক্কী যুগটা দাওয়াত ও আদর্শ প্রচারের যুগ। আর মাদানী যুগ শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের যুগ। মক্কায় লোক তৈরী করা হয়েছে। আর মদিনায় সামষ্টিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মক্কায় মালমসলা তৈরী করা হয়েছে। আর মদিনায় ভবন নির্মিত হয়েছে।
এই পার্থক্যের কারণে কোরআন, নবী জীবন ও ইসলামের ইতিহাসকে স্থূল দৃষ্টিতে অধ্যয়নকারী সাধারণ মানুষের ধারণা হলো, ইসলামী আন্দোলন ও তার আহ্বায়কের ওপর পরীক্ষার কথিত সময় কেবল মক্কায়ই কেটেছে। মদিনায় বিরোধিতার তেমন তীব্রতা ও উগ্রতা ছিলনা এবং সেখানে তেমন সাবর্ক্ষণিক নির্যাতনের দুবির্সহ পরিবেশ ছিলনা, যেমন ছিল মক্কায়। অন্তত পক্ষে এরূপ মনে করা হয় যে, বিরোধিতা ও শত্রুতা মাদানী যুগে নগ্ন তরবারীর রূপ ধারণ করে যুদ্ধের ময়দানে চলে এসেছিল। শত্রুদের পক্ষ থেকে হীন ও ইতরসুলভ আচরনের যুগটা অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। এ কথা সত্য যে, মাদানী যুগে প্রধান বিরোধী গোষ্ঠী কোরায়েশ উন্মুক্ত যুদ্ধের ময়দানে মুখোমুখি চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল। কিন্তু এ কথাও অস্বীকার করা যায়না যে, ইসলামী আন্দোলন আগের চেয়ে জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার নতুন নতুন শত্রু সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এ সব শত্রু অপকর্মে মক্কাবাসীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলনা। তাঁদের নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীদেরকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উত্যক্ত ও বিব্রত করেছে এবং পূনর্জাগরণের কাজে বাধা দিতে কোন অপচেষ্টাই বাদ রাখেনি।
ইতিহাসের একটা চিরচারিত নিয়ম হলো, সংস্কার সংশোধন ও পূনর্জাগরণের কাজ যতই অগ্রসর হয়, সংস্কার বিরোধী ও কর্মবিমুখ গোষ্ঠীগুলো তাকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করার জন্য শত্রুতার আবেগে ততই হন্যে হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত যখন নির্যাতনের ফাঁসি কাষ্ঠ থেকে উদ্ধার পেয়ে এক লাফে ক্ষমতার মসনদে আসীন হয় তখন বাতিলের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা সকল সীমা অতিক্রম করে যায়। মদীনায় নতুন ইসলামী সমাজ ও শান্তিপূর্ণ কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এ ধরনের পরিস্থিতিরই উদ্ভব হয়েছিল।
মদিনার ভিন্নতর পরিবেশ
ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা যে, মদিনার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ ছিল মক্কা থেকে একেবারেই ভিন্নতর। এ কারণে ইসলামের যে চারাগাছ মক্কায় চরম প্রতিকূল পরিবেশে বেড়ে উঠতেই পারছিল না, মদিনায় এনে লাগানো মাত্রই তা দ্রুত পত্র পল্লবে বিকশিত হয়ে উঠলো ও ফল দিতে শুরু করলো।
প্রথম পার্থক্যটা ছিল এইযে, মক্কা ও তার আশ পাশের গোটা জনবসতি পরস্পরে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল। তারা ছিল একই ধর্মাবলম্বী গোত্র ও পারস্পরিক চুক্তির বন্ধনে আবদ্ধ এবং তাদের ওপর কোরায়েশদের ছিল পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য। কিন্তু মদীনা ও তাঁর আশেপাশে দুটো ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির জনগোষ্ঠী বাস করতো এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও উত্তেজনা বিরাজ করছিল।
মদিনা ছিল ইহুদীদের প্রতিষ্ঠিত ‘ইয়াসরিব’ নামক প্রাচীন শহর। এখানে তাদের ক্রমান্বয়ে বংশ বিস্তার ঘটতে থাকায় মদিনার আশপাশে তাদের নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠেছিল। সেই সাথে তাদের ছোট ছোট সামরিক দূর্গও নির্মিত হয়েছিল। এভাবে সমগ্র এলাকা ইহুদীদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাবাধীন ছিল।
দ্বিতীয় জনগোষ্ঠীটা ছিল আনসারদের। তাদের আসল জন্মভূমি ছিল ইয়ামান। কাহতানের বংশধর ছিল তারা। ইয়ামানের ইতিহাস খ্যাত বন্যায় যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটিত হয়, তা থেকে বেঁচে যাওয়া লোকেরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। কাহতান গোত্রের দু’ভাই আওস ও খাজরাজ তৎকালে মদিনায় এসে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে অন্যান্য লোকও এসে থাকতে পারে। তবে এই নবাগতদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে নতুন অধিবাসীর সমাগম ঘটে। পড়ে বংশ বিস্তার ঘটতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে একটা নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটে। প্রথম প্রথম তারা ইহুদী সমাজ ও কৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জীবন যাপন করতে চেয়েছিল। কিন্তু আগে থেকে জেঁকে বসা ইহুদী জনগোষ্ঠীর প্রভাব ও শক্তির চাপে বাধ্য হয়ে তাদের সাথে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। এই চুক্তিভিত্তিক মৈত্রী দীর্ঘকাল সুষ্ঠুভাবে চলতে থাকে। কিন্তু ইহুদীরা যখনই অনুভব করলো যে, আনসারদের ক্রমবর্ধমান শক্তি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির জন্য একটা হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে, তখন তারা মিত্রতার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললো।
ইহুদীদের মধ্যে ফিতিউন নামক এক লম্পট সরদারের আবির্ভাব ঘটে। সে শক্তির দাপট দেখিয়ে আদেশ জারি করলো, তার এলাকায় যে মেয়েরই বিয়ে হবে, তাকে প্রথমে তার প্রমোদ রজনীর শয্যা সঙ্গিনী হয়েই তবে দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করতে হবে। ইহুদীদের নৈতিক অধোপতন ও বিকৃতি কোন পর্যায়ে গিয়েছিল, তা এ থেকেই বোঝা যায় যে, তারা এই আদেশ মাথা পেতে নিয়েছিল। কিন্তু এই শয়তানী আদেশের দরুন আনসারদের আত্ম সম্ভ্রমবোধ একদিন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মালেক বিন আজলানের বোনের বিয়ে হতে যাচ্ছিল। কিন্তু ঠিক যেদিন বর এলো, সেদিন ফিতিউন মালেকের সামনে দিয়ে একেবারে বিবস্ত্র অবস্থায় যাচ্ছিল। মালেক তাকে তিরস্কার করলে সে বললো, কাল তাকে আরও বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে। উত্তেজিত হয়ে মালেক ফিতিউনকে হত্যা করে ফেললো এবং সিরিয়া পালিয়ে গেল। সেখানে গাসসানী রাজা আবু জাবালার শাসন চলছিল। সে যখন এ অবস্থা জানলো তখন মদীনা আক্রমণ করে বড় বড় ইহুদী নেতাকে হত্যা করে ফেললো এবং আওস ও খাজরাজকে পুরস্কৃত করলো। এ ঘটনাবলী ইহুদীদের শক্তি খর্ব করে দেয় এবং আনসারদের শক্তি বাড়িয়ে দেয়।
মোটকথা ইহুদীদের সাথে আনসারদের সম্পর্ক সব সময়ই দ্বন্দ্ব সঙ্ঘাতে পূর্ণ ছিল, কিন্তু কোন আদর্শ বা লক্ষ্য না থাকায় আনসারদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য কোন মযবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব কলহে তাদের শক্তি ঘুনের মত খেয়ে নষ্ট করে দেয়। ফলে এক সময় আওস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে বুয়াস নামক যুদ্ধ পর্যন্ত সংঘটিত হয় এবং উভয় পক্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ নিহত হয়। এভাবে তারা ইহুদীদের সামনে আবার শক্তিহীন হয়ে যায়। এ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে তারা কিছুদিন আগে কোরায়েশদের সাথে মৈত্রী স্থাপনের আবেদন জানায়। কিন্তু নানা কারণে এ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়।
অপরদিকে ইহুদীদের আধিপত্য ও আভিজাত্যের একটা কারণ ছিল তাদের ধর্মীয় মোড়লিপনা। তাদের কাছে তাওরাত ছিল। এই সুবাদে তারা একটা স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিধানের পতাকাবাহী ছিল, তাদের কাছে আলাদা আকীদা ও আদর্শগত পুঁজি ছিল, কিছু চারিত্রিক নীতিমালা ছিল, কিছু ধর্মীয় আইন ও বিধি ছিল, কিছু ঐতিহ্য ছিল এবং এবাদত পালনের স্বতন্ত্র বিধান ছিল। এদিক দিয়ে আনসারদের বলতে গেলে কিছুই ছিলনা। এ সব বিষয়ে তারা ইহুদীদের মুখাপেক্ষী ছিল। তাদেরই ‘বাইতুল মাকদাস’ (তৎকালে ইহুদীদের ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র) থেকে তারা শিক্ষা লাভ করত। এমনকি যদি কোন আনসারীর সন্তান না বাঁচতো, তাহলে সে এই বলে মান্নত মানত যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাকে ইহুদী বানানো হবে। আনসারদের মধ্যে এদিক থেকে হীনমন্যতাবোধ বিরাজ করতো। তাদের আত্মসম্মানবোধ ও আভিজাত্যবোধ ক্ষুন্ন হওয়ায় তারা মনে মনে সব সময় বিব্রত থাকতো। এই সমস্ত তথ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, মদিনার পরিমন্ডলে ইহুদী ও আনসারদের মাঝে দ্বন্দ্ব কলহ বিরাজ করতো এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিল গভীর প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইহুদীরা প্রায়শ আনসারদের সামনে আস্ফালন করতো যে, শিগগীরই শেষ নবী আসবেন। তিনি এলে আমরা তার সাথে মিলিত হয়ে তোমাদেরকে দেখে নেব। ইহুদীদের এই হুমকী ও ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে আনসাররাও প্রতিক্ষীত নবীর অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে। তারা মনে মনে সংকল্প নেয়, ঐ নবীর আবির্ভাব ঘটলে তারা সবর্প্রথম তাঁর দলে ভিড়বে। হলোও তাই। যারা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল, তারা বঞ্ছিত থেকে গেল। ইহুদীরা যাদেরকে মার খাওয়াতে চেয়েছিল, তাদের হাতে নিজেরাই মার খেয়ে গেল। (সীরাতুন্নবীঃ শিবলী নুমানী)
মদিনার এই পরিবেশ ও পটভূমি বিবেচনা করলে বুঝে আসবে মক্কার তুলনায় এখনকার পরিবেশ কেন ইসলামী আন্দোলনের অধিকতর অনুকূল হলো।
ইসলামী আন্দোলন মদিনায়
মক্কা দীর্ঘ ১৩ বছর যাবত ইসলামের আহ্বান শুনেছে। এর সপক্ষে যুক্তি কী কী তাও জেনেছে। উপরন্তু ইসলামের আলোয় আলোকিত এক অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের চরিত্র এবং ভূমিকা তাঁর সামনে দেদীপ্যমান ছিল। ইসলামের পতাকাবাহীরা যুলুম নিষ্পেষণের চাকার তলে পিষ্ট হয়েও আহাদ আহাদ (আল্লাহ এক, আল্লাহ এক) ধ্বনি তুলেছে। তবুও মক্কার সামগ্রিক পরিবেশ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যানই করেছে।
কিন্তু দাওয়াত মদিনায় পৌঁছা মাত্রই সেখান থেকে ‘লাব্বাইক’ (গ্রহণ করলাম) ধ্বনি উঠলো। মদিনার প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী যুবক ছিলেন সুয়াইদ বিন ছামিত। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মেধাবী কবি, দক্ষ ঘোড় সওয়ার ও বীর যোদ্ধা। এ ধরণের যুবকরা সাধারণত বিপ্লবী আন্দোলনের সৈনিক হয়ে থাকেন, উন্নয়ন ও গঠনমূলক যে কোন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন ও যথা সবর্স্ব উতসর্গ করেন। এ যুবক মক্কায় এলে রাসুল সা. তার সাথে যথারীতি মিলিত হলেন এবং দাওয়াত দিলেন। সুয়াইদ বললো, এ ধরনেরই একটা জিনিস আমার কাছে আছে, যার নাম ‘সহিফায়ে লুকমান’। তিনি তা থেকে কিছুটা পড়েও শোনালেন। এরপর রসূল সা. তাকে কোরআন পড়ে শোনালেন। হঠকারীতামুক্ত ও বিদ্বেষমুক্ত বিবেক কাকে বলে দেখুন। সুয়াইদ সংগে সংগে বলে উঠলেনঃ “এটা আরো সুন্দর কথা!” এরপর রসূল সা. এর দাওয়াত তার অন্তরে গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় তিনি মক্কা থেকে ফিরে যাওয়ার পর পরই খাজরাজীদের হাতে নিহত হন। তাঁর সম্পর্কে অনেকে বলেছেন যে, নিহত হবার সময় তিনি মুসলমান ছিলেন এবং মুখে ‘আল্লাহু আকবর’ ধ্বনি উচ্চারণ করছিলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃঃ৬৭-৬৮)
মদিনায় দ্বিতীয় যে যুবক ইসলামের দাওয়াতে প্রভাবিত হন, তাঁর নাম আয়াস বিন মু’য়ায। এই ব্যক্তি মদীনার একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। এই দলটি মক্কায় এসেছিল খাজরাজের বিরুদ্ধে কোরায়েশের সাথে মৈত্রী চুক্তি করতে এবং সাহায্য লাভের আশায়। রসূল সা. এই দলের লোকদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছান এবং কোরআন পড়ে শোনালেন। আয়াস বিন মু’য়ায তখনো কিশোর মাত্র। সে বললো, “হে আমার সাথীরা, তোমরা যে জন্য এসেছ তার চেয়ে এটাই তো ভালো”। প্রতিনিধি দলের নেতা আবুল হুসাইর সংগে সংগে তার মুখে মাটি ছুড়ে মারলো। তার অর্থ এই ছিল যে, তুমি আবার মাঝখানে এ কোন ঝামেলা বাধাচ্ছ? সে আরো বললো, ‘আমরা এজন্য আসিনি’। আবুল হুসাইর কোরায়েশদের সাহায্য লাভের জন্য উদগ্রীব ছিল। সে জানতো যে, মুহাম্মাদ সা. এর দাওয়াত গ্রহণ করলে কোরায়েশদের সাহায্য পাওয়ার পথ একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। আয়াস চুপ করলো বটে। ইসলামের দাওয়াত তার অন্তরে প্রবেশ করলো। প্রতিনিধি দল মদিনায় ফিরে গেল। দুঃখের বিষয় যে, এই সচেতন যুবকটিও শীঘ্রই বুয়াস যুদ্ধের কবলে পড়ে মারা গেল।
নবুয়তের একাদশ বছরে মদিনা থেকে যে দলটি এসেছিল, তার সাথে এক বৈঠকে রসূল সা. এর বিস্তারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। রসূল সা. এর দাওয়াত শোনার পর তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলো, “তোমরা নিশ্চিত জেন, এই ব্যক্তিই সেই নবী, যার কথা ইহুদীরা তোমাদের কাছে বলে আসছে। এখন ইহুদীরা যেন আমাদের আগে এই নবীর সহযোগী হয়ে যেতে না পারে।” এরপর আল্লাহ তাদের অন্তর উন্মুক্ত করে দেন এবং তারা সবাই ইসলামকে হৃদয়ে বদ্ধমূল করে নেয়। তারপর তারা বলতে থাকেঃ
“আমরা আমাদের জনগনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। আমাদের মধ্যে যত শত্রুতা ও কলহ কোন্দল, তা বোধহয় আর কোন জাতিতে নেই। হতে পারে রসূল সা. এর মাধ্যমে আমাদের জাতিকে আল্লাহ আবার ঐক্যবদ্ধ করবেন। আমরা তাদের কাছে ফিরে যাওয়ার পর রসূল সা. এর দ্বীনের প্রতি তাদেরকে দাওয়াত দেব এবং আমরা তাঁর সামনে এই দ্বীনের ব্যাপারে যে মনোভাব ব্যক্ত করেছি, তাদের সামনেও সেই মনোভাব ব্যক্ত করবো। তারপর আল্লাহ যদি তাদেরকে এই দ্বীনের ব্যাপারে একমত করে দেন তাহলে এরপর ইনিই হবেন সবচে শক্তিশালী ব্যক্তি”। (সীরাত ইবনে হিশাম)
যে দাওয়াতকে মক্কার লোকেরা বিভেদের কারণ বলে মনে করেছিল, মদীনার লোকেরা প্রথম দৃষ্টিতেই তাকে তাদের ঐক্যের ভিত্তি দেখতে পেল। ইসলামী আন্দোলনের পতাকা উত্তোলনের জন্য মক্কায় বসে সংগঠিত মদীনার এই প্রথম দলটির সদস্য ছিলেন ছয় ব্যক্তিঃ
(১)আবুল হাইছান বিন বিন হাম (২)আসাদ বিন যারারা (৩)আওফ বিন হারিস (৪)রাফে বিন মালেক আজলান (৫)কুতবা বিন আমের (৬)জাবের বিন আব্দুল্লাহ।
এই ব্যক্তিবর্গ মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর তারা সেখানে নতুন চাঞ্চল্য ও নতুন জাগরণ সৃষ্টি করেন। সেখানে ইসলামের দাওয়াত জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং ব্যাপক বিস্তার লাভ করতে থাকে। আনসারদের পরিবারগুলোর মধ্যে কোন পরিবারই এমন ছিলনা, যেখানে মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিলনা।
প্রথম আকাবার বায়য়াত
পরবর্তী বছর অর্থাৎ নবুয়তের দ্বাদশ বছর বারো ব্যক্তি মদিনা থেকে এসে বায়য়াত সম্পাদন করেন। এটা ‘মাতৃশপথ’ নামে পরিচিত। এই নামকরণের কারণ হলো, এই বায়য়াতে শুধু মৌলিক বিষয়ে অঙ্গীকার গ্রহণ করা হয় এবং কোন যুদ্ধ বিগ্রহের বিষয় এতে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। এই ঈমানী অঙ্গীকারের বক্তব্য ছিল নিম্নরূপঃ
“আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করবোনা, চুরি করবোনা, ব্যভিচার করবোনা, সন্তান হত্যা করব না, জেনে শুনে কারো বিরুদ্ধে মনগড়া অপবাদ রটাব না এবং কোন সৎ কাজে মুহাম্মদ সা. এর অবাধ্য হবনা।”
এই দলটি যখন মদিনায় রওনা হলো, তখন রসূল সা. মুসয়াব বিন উমাইরকে মদিনায় ইসলামের দাওয়াতী কাজ সম্পাদনের জন্য নিযুক্ত করেন। সেখানে গিয়ে মুসলমানদেরকে কোরআন পড়ানো, ইসলামের শিক্ষা দান এবং ইসলামের বিস্তারিত ও সঠিক জ্ঞান দানের দায়িত্ব তাকে অর্পণ করেন। তিনি সেখানে নামাযের ইমামতিও করতেন এবং ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী চারিত্রিক নীতিমালাও শিক্ষা দিতেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)
দুই নেতার ইসলাম গ্রহণ
রসূল সা. এর নিযুক্ত ইসলাম প্রচারক মুসয়াব যে বাড়ীতে অবস্থান করতেন, সে বাড়ীর মালিক আস’য়াদ বিন যারারা একদিন মুসয়াবকে সাথে নিয়ে বনু আবদুল আশহাল ও বনু যফর গোত্রের বাসস্থানের দিকে দাওয়াতী অভিযানে রওনা হলেন। তারা মারাক নামক কুঁয়ার পার্শ্ববর্তী বনু যফরের বাড়ীর চৌহদ্দীর কাছে পৌঁছলেন। ইসলাম গ্রহণকারী কতিপয় ব্যক্তি এসময় তাদের পাশে এসে সমবেত হলো। বনু আবদুল আশহালের দুই নেতা সা’দ বিন মু’য়ায এবং উসাইদ বিন হুযাইর তখনো তাদের গোত্রের ধর্মানুসারী অর্থাৎ-পৌত্তলিক ছিলেন। আস’য়াদ বিন যারারা ও মুসয়াবের পরিচালিত দাওয়াতী তৎপরতায় সা’দ বিন মু’য়ায আগেই রেগে আগুন হন। এই দুই ব্যক্তির আগমনের খবর শুনে তিনি উসাইদকে কানে কানে বললেন, “এই দুই ব্যক্তি আমাদের ভেতরকার দুবর্ল লোকদেরকে ধোকা দিয়ে বিপথগামী করতে আসে, যেয়ে ওদেরকে নিষেধ করে দাও আমাদের বাড়ীতে যেন না আসে। আস’য়াদ বিন যারারা যদি আমার খালাতো ভাই না হতো, তাহলে তোমাকে বলতামনা, আমি নিজেই তাঁর মোকাবিলা করতাম।” এরপর যখন দাওয়াতী বৈঠক বসলো, সা’দ বিন মু’য়াযের নির্দেশ মোতাবেক উসাইদ একটা বর্শা উঁচিয়ে তাদের উভয়ের কাছে এল। কয়েক মূহুর্ত থমকে দাঁড়িয়ে কটূ ভাষা প্রয়োগ করে বললো, “তোমাদের এখানে আগমনের উদ্দেশ্য কী? তোমরা আমাদের দুবর্ল লোকদের বিভ্রান্ত কর। প্রাণে বাঁচতে চাওতো আমাদের এলাকা ছেড়ে এক্ষুনি চলে যাও।” মুসয়াব বিনম্র ভাষায় বললেন, “আপনি একটু বসে মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শুনুন না। শোনার পর ভালো লাগলে মেনে নেবেন, নচেত প্রত্যাখ্যান করবেন।” উসাইদ এ কথা শুনে একটু শান্ত হলো। সে বর্শাটা নীচে রেখে দিয়ে আস’য়াদ ও মুসয়াবের পাশে শান্তভাবে বসে পড়লো। মুসয়াব আলোচনা শুরু করলেন এবং কোরআন পড়ে শোনালেন। তারা উসাইদ মুখ দিয়ে কিছু বলার আগেই তার মুখ মণ্ডলের হাবভাব লক্ষ্য করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের মনোভাব উপলব্ধি করেছিলেন। অবশেষে উসাইদ মুখ ফুটে বললো, “কী সুন্দর ও কত মনোমুগ্ধকর কথা!” সে জিজ্ঞাসা করলো, “তোমরা ইসলাম গ্রহণের সময় কি পন্থা অবলম্বন কর?” উভয়ে বললেন, “যাও, গোসল কর, পাক পবিত্র হও, নিজের কাপড় ধুয়ে ফেল, তারপর সত্যের সাক্ষ্য দাও এবং নামায পড়।” যে উসাইদ একটু আগে বর্শা তাক করে দাঁড়িয়েছিল, তাঁর বুকে এখন ইসলামের উজ্জীবনী বর্শা বিদ্ধ হয়ে গেছে। সে উঠে যেয়ে গোসল করে পাকসাফ হয়ে এসে দু’রাকাত নামায পড়লো। নামায শেষে উসাইদ বললো, “আমার সাথে আর এক ব্যক্তি আছে। সেও যদি তোমাদের দলে যোগ দেয়, তাহলে গোত্রের আর কেউ বিরোধিতা করবেনা। আমি এখনই তাকে ডেকে আনি। সে হচ্ছে সা’দ বিন মু’য়ায।” সে তৎক্ষণাত বর্শা হাতে সা’দের কাছে গেল। সেখানে মজলিশ বসলো। মু’য়ায উসাইদকে দূর থেকে দেখেই তার সাথীদের বললো, “আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, উসাইদ যাওয়ার সময় যে রকম চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তার সে রকম চেহারা নেই।” তারপর উসাইদকে বললো, “বল, তুমি কী করে এসেছ?” উসাইদ সরল ভাবে জবাব দিল, “আমি উভয়ের সাথে কথা বলেছি। আল্লাহর কসম, তাদের দিক থেকে কোন আশংকা অনুভব করিনি। তাদেরকে আমি নিষেধ করে দিয়েছি। আর তুমি যা বল, তাই আমরা করবো।” সাথে সাথে সা’দকে উত্তেজিত করার জন্য বললো, “বনু হারেসা আস’য়াদ বিন যারারাকে হত্যা করতে চায়। আস’য়াদ তোমার আত্মীয়, তা জেনেও এটা করতে চাইছে যাতে তোমাকে হেয় করা যায়।” সা’দ বনু হারেসার পক্ষ থেকে আচরণের আশংকা বোধ করে রেগে উঠলো। উসাইদের হাত থেকে বর্শাটা ছোঁ মেরে নিয়ে মু’য়ায আস’য়াদ ও মুসয়াবের কাছে গেল। কিন্তু গিয়ে দেখে উভয়ে শান্তভাবে বসে আছে। মু’য়ায বলেন, “আমি তৎক্ষণাত বুঝে ফেললাম, উসাইদ চালাকি করে আমাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে যাতে আমি ওদের দু’জনের কথাবার্তা প্রত্যক্ষভাবে শুনি। তাকে মনে মনে অনেক তিরস্কার করে উভয়ের সামনে থমকে দাঁড়ালাম। আস’য়াদ বিন যারারাকে বললাম, তোমরা আমাদের কাছে এমন সব কথাবার্তা বলতে আস যা আমরা ঘৃণা করি।” মুসয়াব বিনম্রভাবে বললেন, “একটু ঠাণ্ডা হও, আমাদের কথা শোন। তারপর ভালো লাগলে গ্রহণ করো, নচেৎ তোমরা যা ঘৃণা করো, তা আমরা তোমার সামনে পেশ করবোনা।” সা’দ শান্ত হয়ে গেল এবং বললো, “ তুমি তো ন্যায়সঙ্গত কথাই বলেছ।” সা’দ বসে পড়লে মুসয়াব তাকে ইসলামের বার্তা ও কোরআন শোনালেন। এখানেও উসাইদের মত অবস্থার পুনরাবৃত্তি হলো। সা’দ কিছু বলার আগেই তার চেহারা থেকে ইসলাম গ্রহণের লক্ষণ ফুটে উঠলো। কয়েক মূহুর্তে দ্বিতীয় নেতা ইসলাম গ্রহণ করলো।
সা’দ বিন মু’য়ায ‘নতুন জীবন’ নিয়ে যখন ফিরে এলেন, তখন গোত্রীয় মজলিসের লোকজন দূর থেকে দেখেই বললো, সা’দের চেহারা বদলে গেছে। এসেই সা’দ বললেন, “হে বনু আবদুল আশহাল গোত্রের জনমণ্ডলী, আমার সম্বন্ধে তোমাদের মত কী ?” সবাই বললো, “তুমি আমাদের সরদার। তোমার মতামত আমাদের মতামতের চেয়ে পরিপক্ক। আমাদের সবার চেয়ে তুমি গুণবান ও কল্যাণময়।” সা’দ বললেন, “তা হলে শুনে রাখ, তোমরা যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান না আনবে, ততক্ষণ তোমাদের নারী ও পুরুষদের সাথে কথা বলা আমার হারাম।” এরপর আর যায় কোথায়। সমগ্র গোত্রের নারী ও পুরুষেরা এক যোগে ইসলাম গ্রহণ করলো।
এই দুই নেতার মাধ্যমে যখন ইসলামী আন্দোলনের শক্তি প্রভূত বৃদ্ধি পেল, তখন দাওয়াতী অভিযানও জোরদার হলো এবং ঘরে ঘরে ও গোত্রে গোত্রে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো।
আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াত
ইতিমধ্যে হজ্জের মওসুম এসে গেল। এবার বিপুল সংখ্যক মুসলমান মদিনা থেকে মক্কায় গেল। কারণ মদিনার ভূমিতে ইসলাম ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করছিল। মদিনার এই নওমুসলিমগণ নতুন ধর্মীয় উদ্দীপনায় উদ্দীপিত হয়ে হজ্জ উপলক্ষে এসে কোরায়েশদের দৃষ্টি এড়িয়ে রাতের অন্ধকারে নিজেদের প্রিয় নেতা রসূলের সা. সাথে মিলিত হলো। এবার পুনরায় আনুগত্যের অঙ্গীকার নেয়া হলো। তবে এবারের অঙ্গীকার ‘মাতৃ বায়য়াত’ এর চেয়ে অনেকটা অগ্রগামী ছিল। প্রথম বায়য়াতের কেবল একটি ধারায় রাজনৈতিক বক্তব্য পরিলক্ষিত হতো। সেটি ছিল এই প্রতিজ্ঞা যে, “আমরা মুহাম্মাদ সা. এর ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করবোনা।” কিন্তু এবার যাবতীয় ঝুঁকি মাথায় নিয়ে রাজনৈতিক বক্তব্য অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এ বায়য়াতের আলোকে মুহাম্মাদ সা. এর সহযোগিতা করার অর্থ ছিল কোরায়েশ ও সমগ্র আরব জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। দ্বিতীয় বায়য়াত প্রকৃত পক্ষে সম্পাদন করাও হয়েছিল এই অর্থকে সামনে রেখেই। আলাপ আলোচনার সময় ইসলামী আন্দোলনের এই সব ইয়াসরিবী সৈনিক ভবিষ্যতের সম্ভাবনাগুলো পুরোপুরিভাবে অনুধাবন করে বললেন, “ইয়াসরিবের লোকদের (অর্থাৎ ইহুদীদের) সাথে আমাদের যে সব চুক্তি আছে, তা আমাদের বাতিল করতে হবে। বাতিল করার পর এমন যেন না হয় যে, আল্লাহ আপনাকে বিজয় দান করলে আপনি স্বজাতির লোকদের কাছে ফিরে যাবেন এবং আমাদেরকে ত্যাগ করবেন।” এই আশংকার জবাবে রসূল সা. মুচকি হেসে বললেনঃ “তোমাদের রক্ত আমারই রক্ত, তোমাদের শত্রু আমারই শত্রু, আমি তোমাদের লোক এবং তোমরা আমার লোক। যাদের সাথে তোমাদের যুদ্ধ হবে তাদের সাথে আমারও যুদ্ধ হবে, আর যাদের সাথে তোমাদের সন্ধি হবে তাদের সাথে আমারও সন্ধি হবে।” আব্বাস বিন উবাদা বললেন, “হে খাজরাজের বংশধরগণ! তোমরা কি জান, মুহাম্মাদের সা. সাথে তোমরা কিসের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছ? এ হচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের সাথে লড়াই এর প্রতিশ্রুতি।” প্রতিনিধিদলের সদস্যরা পরিপুর্ণ দায়িত্বোপলব্ধি সহকারেই জবাব দিলেনঃ “আমরা আমাদের সমস্ত সহায় সম্পদ ধ্বংস এবং আমাদের গোত্রপতিদের হত্যার বিনিময়ে হলেও আপনার সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখবো বলে অঙ্গীকার করছি।” এই বায়য়াতের বিশেষ প্রকৃতির কারণেই এর নাম হয়ে গেল “বায়য়াতুল হারব” বা “সামরিক অঙ্গীকার”। এর একটা মৌলিক শর্ত ছিল এই যে, “আমরা অনটনে অথবা প্রাচুর্যে, সুখে কিংবা দুঃখে, যে অবস্থায়ই থাকিনা কেন, রসূল সা. এর প্রতিটি নির্দেশ শুনবো ও তাঁর আনুগত্য করবো, রসূলের আদেশকে আমরা নিজেদের ওপর অগ্রাধিকার দেব এবং নেতৃবৃন্দ ও দায়িত্বশীলদের সাথে দ্বন্দ্বকলহ করবোনা। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কেউ আমাদের নিন্দা ভৎর্সনা করলে আমরা তাঁর পরোয়া করবোনা।”
এ বায়য়াতকে আসলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিপ্রস্তর বলা যায়। সেই সাথে একে হিজরতের ভূমিকা বলেও আখ্যায়িত করা চলে। এ বায়য়াতের মাধ্যমে কার্যত ভবিষ্যতের ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য তার ভাবী নাগরিকগণ সেচ্ছায় ও সানন্দে মুহাম্মাদ সা. এর রাষ্ট্রনায়কত্বকে গ্রহণ করে নিল। উপরন্তু আনুগত্যের ব্যবস্থাও এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।
এর মাধ্যমে শুধু যে একটা অঙ্গীকার নেয়া হলো তা নয়, বরং সামষ্টিক নিয়ম-শৃঙ্খলার ভিত্তিও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। ইসলামী আন্দোলনের নেতা নাগরিক সংগঠনের মতানুসারে বারোজন আঞ্চলিক দায়িত্বশীল (নকীব) নিয়োগ করলেন। তন্মধ্যে ৯ জন খাজরাজ থেকে এবং তিনজন আওস থেকে নিযুক্ত হলো। এই নকীবদেরকে আদেশ দেওয়া হলো যে, তোমরা নিজ নিজ গোত্রের যাবতীয় বিষয়ের দায়িত্বশীল, যেমন হযরত ঈসার আ. হাওয়ারীগণ দায়িত্বশীল ছিলেন এবং যেমন আমি স্বয়ং আমার দলের দায়িত্বশীল। এরা স্বয়ং রসূল সা. এর প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। তাদের নিযুক্তির মাধ্যমে সংগঠিত সমাজ নির্মাণের কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে শুরু হলো।
খবরটা যখন কোরায়েশদের কানে গেল, তখন তারা বুক চাপড়াতে লাগলো। প্রতিনিধি দল ততক্ষণে মক্কা থেকে চলে গেছে। অনুসন্ধানে লোক পাঠানো হলো। সা’দ বিন উবাদা ও মুনযির বিন আমরকে ধরে আনা হলো। তাদের ওপর তারা গায়ের ঝাল ঝাড়লো। কিন্তু তাতে আর কী লাভ? (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
মদিনায় আন্দোলনের নতুন জোয়ার
এই প্রতিনিধি দল নতুন উদ্যম ও উদ্দীপনা নিয়ে মদিনায় ফিরে এলে দাওয়াতের কাজ প্রকাশ্যে ব্যাপকভাবে শুরু হলো। যুবকরা যখন কোন পরিবর্তনের উদ্যোক্তা হয়ে ময়দানে নামে, তখন তার মোকাবিলায় বুড়ো জনগোষ্ঠী বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনা। কোন আন্দোলনের ভবিষ্যত কেমন তা উপলব্ধি করতে হলে জানতে হবে, তা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ওপর নির্ভরশীল, না তাঁর শিরায় নবীনদের রক্ত প্রবাহিত। মক্কায় ও বিশেষত মদীনায় যারা ইসলামী আন্দোলনের ঝাণ্ডা নিয়ে আগে আগে চলেছিল, তারা প্রায় সবাই ছিল উঠতি বয়সের। এই তরুণ প্রজন্ম ইসলামী আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য কত কী যে করেছে তার ধারণা পাওয়ার জন্য একটা মজার ঘটনা উল্লেখ করা জরুরী মনে হচ্ছে।
বনু সালামা গোত্রে আমর ইবনুল জামুহ নামে এক প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নিজ গৃহে মানাত নামে কাঠের একটা মূর্তি সংগ্রহ করে এনে রেখেছিলেন। বুড়ো তার পূজো করতেন ও অষ্ট্র প্রহর ঝাড়ামোছায় নিয়োজিত থাকতেন। বনু সালামার দুই তরুণ মুয়ায বিন জাবাল ও মুয়ায বিন আমর ইসলাম গ্রহণ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হয়ে গিয়েছিলেন। শেষোক্তজন আলোচ্য বুড়ো মিয়ারই ছেলে। এরা দু’জন প্রতিদিন রাতের অন্ধকারে উঠে গিয়ে বুড়ো মিয়ার মূর্তিটাকে প্রথমে কাদামাটিতে লুটোপুটি খাওয়াতেন, অতঃপর বনু সালামার যে গর্তে লোকেরা যাবতীয় বর্জ্য নিক্ষেপ করতো, সেখানে মাথা নিছের দিকে করে ফেলে রেখে আসতেন। সকাল বেলা উঠে বুড়ো চিৎকার করতেনঃ “রাতের বেলা আমার খোদার উপর কে হস্তক্ষেপ করলো?” তারপর তিনি নিজের হারানো খোদাকে খুঁজতে বেরুতেন। খুঁজে পাওয়ার পর ধুয়ে মুছে আবার যথাস্থানে রেখে দিতেন। পরবর্তী রাতেও আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো। বুড়ো আবারও চিল্লাচিল্লি করতেন। একদিন বুড়ো আমর বিরক্ত হয়ে মূর্তির ঘাড়ে নিজের তলোয়ার ঝুলিয়ে দিলেন। মূর্তিকে বললেন, “আল্লাহর কসম, আমি জানিনা তোমার সাথে কে এমন আচরণ করে। তোমার যদি একটুও শক্তি থেকে থাকে, তবে এই যে তলোয়ার রেখে গেলাম, আত্মরক্ষার চেষ্টা ক’রো।” রাত হলো। আমর ঘুমিয়ে গেলেন। এই নাটকের উভয় অভিনেতা রাতের বেলায় এলেন। তারা মূর্তির ঘাড় থেকে তলোয়ার খুলে ফেললেন। তারপর একটা মরা কুকুর খুঁজে এনে মূর্তির গলায় রশি দিয়ে বাঁধলেন এবং তাকে এমন এক বদ্ধ কূয়ায় ফেলে আসলেন, যা মানুষের মলমূত্রে ভর্তি থাকতো। সকাল বেলা উঠে আমর দেখলেন, তার খোদা আবারো উধাও হয়েছে। খোঁজাখুঁজি করে যখন তার এরূপ করুণ দশা দেখলেন, তার মনে প্রচণ্ড ভাবান্তর উপস্থিত হলো এবং আমর ইসলাম গ্রহণ করলেন। এ থেকে বুঝা যায়, মদীনায় কী আমূল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল।
আন্দোলনের নতুন কেন্দ্র
ইসলামী আন্দোলনের নেতা সবর্দাই এই ভাবনায় থাকতেন যে, মক্কায় যদি আন্দোলন তিষ্টিতে না পারে এবং মক্কার নিষ্ঠুর নেতৃত্ব যদি “নতুন বিশ্ব” গড়ার সুযোগ দিতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পৃথিবীর আর কোন্ অঞ্চলে সবর্শক্তি নিয়োগ করে এই গঠনমূলক কাজটা শুরু করা যেতে পারে? তাঁর প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল আবিসিনিয়ার ওপর এবং এজন্যই তিনি সাথীদেরকে সেখানে পাঠিয়েছিলেন। বাদশাহ নাজ্জাশী যদিও মক্কার মযলুমদের সাহায্যের ব্যাপারে সাধ্যমত সব কিছুই করেছেন। কিন্তু একে তো সেখানে খৃষ্টান ধর্মযাজকদের ন্যাক্কারজনক ভূমিকা মুসলমানদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ওদের সবব্যার্পী প্রভাবের আওতায় সেখানে ইসলামের বিকাশ লাভ সহজ ছিলনা। তদুপরি সেকানে স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে একেবারে নতুন করে প্রচারকার্য শুরু করতে হতো। আর এ কাজ করতে গিয়ে বিদেশের মাটিতে নানা রকমের দূরতিক্রম্য বাধার সম্মুখীন হতে হতো। এ জন্য অন্য কোন ভূখণ্ডের সন্ধান করা হচ্ছিল। মদিনা যখন খোলা মনে দাওয়াতে সাড়া দিল, তখন রসূল সা. আশার আলো দেখতে পেলেন। আকাবার প্রথম বায়য়াত এই আশাকে আরো জোরদার করে। তারপর হযরত মুসয়াব ইবনে উমাইর সেখানে অবস্থান করে কিছু দিন কাজ করার পর আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের প্রাক্কালে হজ্জের সময় যে রিপোর্ট দেন, তাতে মদীনার মুসলমানদের বিস্তারিত বিবরণ দেন, তাদের শক্তি সামর্থের তথ্য জানান এবং সুসংবাদ দেন যে, এ বছর বিপুল সংখ্যক মুসলমান হজ্জ করতে আসছে। এই রিপোর্ট রসূল সা. কে গভীর চিন্তা ভাবনার প্রেরণা যোগাচ্ছিল। মদিনায় মুসলমানদের শক্তি ও সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া খুবই আশাব্যঞ্জক ব্যাপার ছিল। সেখানে ইহুদীদের দিক থেকে তাদের তেমন মারাত্মক বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিলনা, যেমন মক্কায় কোরায়েশদের দিক থেকে হতে হচ্ছিল। ইয়াসরিব বাসী মক্কার সাথীদের জন্য খুবই চিন্তিত থাকতেন। ইয়াসরিববাসীর অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল। তাদের ক্ষেতখামার ও বাগবাগিচা ছিল। রসূল সা. ভাবতেন, মক্কার মুসলমানরা মদীনায় চলে গেলে এবং কোরায়শদের যুলুম থেকে মুক্তি পেয়ে ইসলামের দাবী পূরণ করলেই কি ভালো হয়না? তাই আগত প্রতিনিধি দলের মধ্যে যারা হজ্জ করতে এসেছিলেন, তাদের কাছে তিনি নিজের এই ধারণা ব্যক্ত করলেন এবং পরে যে বায়য়াত সম্পন্ন হলো, তা এই পটভূমির ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। (হায়াতে মুহাম্মদ, মুহাম্মদ হোসেন হাইকেল)
আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই একজন দুজন করে মুসলমান রসূল সা. এর অনুমতিক্রমে মদিনা যাচ্ছিল। কিন্তু আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের পর এর গতি তীব্রতর হয় এবং দ্বিতীয় হিজরতের স্থান যে মদিনা হবে, তা প্রায় ঠিকঠাক হয়ে যায়।
মক্কার মোড়লরা দেখতে পাচ্ছিল যে, ইসলামী আন্দোলন নতুন একটা মজবুত ঘাঁটি সৃষ্টি করে ফেলেছে। তাদের দৃষ্টিতে ভবিষ্যত অত্যন্ত ভয়ানক বলে মনে হচ্ছিল। তারা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারছিল যে, এখন মদীনায় যদি ইসলামের ইসলামের শিকড় গাড়ে, তাহলে আমাদের নাগালের বাইরে তা এক অজেয় শক্তিতে পরিণত হবে। অতঃপর তা একদিন আমাদের ওপর চড়াও হবে এবং আমাদের অতীতের কীর্তিকলাপের পাই পাই করে প্রতিশোধ নেবে। তারা এ আশংকাও বোধ করছিল যে, সিরিয়ার বাণিজ্যিক সড়ক যেহেতু মদীনার ওপর দিয়ে অতিক্রম করে, তাই মদিনায় নতুন ইসলামী কেন্দ্র এই পথ আটকে দিতে পারে। এভাবে মক্কার কোরায়েশদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অপমৃত্যু ঘটবে। তারা ভেতরে ভেতরে গভীর আতংক ও উৎকণ্ঠায় দিশেহারা হয়ে যাচ্ছিল। কিছুই বুঝতে পারছিলনা যে কি করবে। তারা দিন রাত এই চিন্তায় মগ্ন থাকতো যে, মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সমগ্র দল হাতছাড়া হয়ে না যায়। এই দুশ্চিন্তার কারণেই তারা শেষ পর্যন্ত রসূল সা.কে হত্যার পরিকল্পনা করে। একটা ঐতিহাসিক শক্তি তাদের গৃহ থেকেই আবির্ভূত হয়েছিল এবং দুনিয়ার অন্য সবার চাইতে তাদেরই নিজস্ব ছিল। সেই শক্তিকে তারা নিজেদেরই অপকর্ম দ্বারা ‘পর’ বানিয়ে দেয় এবং নিজেরাই তার শত্রু হয়ে যায়। তাই এরপর তা যতই জোরদার হচ্ছিল তাদের জন্য ততই প্রাণঘাতী আপদে পরিণত হচ্ছিল।
এজন্য প্রথম মোহাজের যখন মদিনায় যাওয়ার জন্য রওনা হলো, তখন মক্কাবাসী তার ওপর অত্যাচার চালায়। এই ব্যক্তি ছিলেন আবু সালামা আব্দুল্লাহ ইবনুল আসাদ মাখযুমী। তিনি স্ত্রী ও ছেলেমেয়েকে উটের ওপর চড়িয়ে রওনা দিচ্ছিলেন, ঠিক এই সময় তাঁর স্ত্রীর পৈতৃক গোত্র বনু মুগীরার লোকজন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে তাঁর স্ত্রী উম্মে সালামার উটের রশী আবু সালামার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। তারা বললো, আমাদের মেয়ে উম্মে সালামাকে তোমার সাথে ভবঘুরে হতে ছেড়ে দিতে পারিনা। এরূপ আবেগজড়িত ঘটনায় আবু সালামার গোত্রের লোকেরা ক্ষেপে গেল। তারা বনু মুগীরাকে বললো, তোমরা যদি আমাদের লোকের স্ত্রী কেড়ে নাও, তাহলে আমরা আমাদের শিশু সন্তানকে তার কোলে থাকতে দেবনা। ফলে স্বামী, স্ত্রী ও শিশু তিনজনই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। আবু সালামা এ অবস্থায়ই মদিনায় চলে গেলেন। উম্মে সালামা প্রতিদিন সকালে শহরের উপকণ্ঠের সেই জায়গাটায় এসে বিলাপ করে কাঁদতো। এভাবে প্রায় এক বছর কেটে যাওয়ার পর কোন এক ব্যক্তির মনে দয়ার উদ্রেক করলো এবং সে বনু মুগীরাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে উম্মে সালামাকে শিশুসন্তানসহ উটে চড়িয়ে মদিনা পাঠিয়ে দিল। মহিলা একাই রওনা হয়েছিল। আল্লাহর অনুগ্রহে ঘটনাক্রমে পথিমধ্যে উসমান বিন তালহার সাথে দেখা হয় এবং তিনি মদিনার উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন।
অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় হিজরতের তিক্ত অভিজ্ঞতার পর এখন মক্কাবাসীর নীতি হয়ে দাঁড়ালো এই যে, মুসলমানদের হাতছাড়া হতে দেয়া যাবেনা। যদি কেউ হিজরত করতেই চায়, তবে গোত্র ও পরিবার পরিজন মক্কাবাসীর হাতে জিম্মী হয়ে থাকবে। এই নীতি প্রথমে একটু শিথিল ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তা কঠোর হয়। এমনকি বিলম্বে হিজরতকারী হযরত ওমর, আইয়াশ ইবনে আবি রবীয়া ও হিশাম ইবনে আ’স ইবনে ওয়ায়েলকে এত গোপনে যাত্রা করতে হয় যে, যে কোন মূহুর্তে গ্রেফতার হবার ভয়ে তটস্থ থাকতে হয়েছিল। হযরত ওমর ও আইয়াশ তো কোন রকমে দ্রুত গতিতে ছুটে চলে গেলেন। কিন্তু হিশাম ধরা পড়ে গেল এবং নির্যাতনের শিকার হলো। হযরত ওমর ও আইয়াশ নিরাপদে মদীনায় পৌঁছে গেলেন। কিন্তু মক্কা থেকে একটা কুচক্রী দল তাদের পিছু পিছু রওনা হয়ে গেল। এ দলটির সদস্য ছিল আবু জাহল বিন হিশাম ও হারেস বিন হিশাম। তারা দুজনে গিয়ে আইয়াশের সাথে সাক্ষাত করে বললো, তোমার মা মৃত্যু পথযাত্রী। তিনি কসম খেয়েছেন যে, তোমার মুখ না দেখা পর্যন্ত তিনি মাথার চুল আচড়াবেন না এবং প্রখর রৌদ্রে দাঁড়িয়ে থাকবেন। সাথীরা আইয়াশকে অনেক বঝালেন যে, এটা একটা চালাকি মাত্র। তুমি একবার যদি মক্কাবাসীর চাতুর্যের জালে ধরা পড়, তাহলে তারা তোমাকে ইসলাম ত্যাগে বাধ্য করবে। ধনাঢ্য আইয়াশ এ লোভেও পড়ে গিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের ধন সম্পদের একটা অংশ নিয়ে আসবেন। হযরত ওমর তার এ ইচ্ছার কথা জেনে বললেন, “আমি তোমার চেয়েও বেশী সম্পদশালী এবং আমার অর্ধেক সম্পদ তোমাকে দিয়ে দেব। ওদের সাথে যেয়না।” কিন্তু আইয়াশ কোন কথা শুনলেন না। হযরত ওমর বললেন, “যদি যেতেই চাও তবে আমার দ্রুতগামী উটনীটা নিয়ে যাও, যেখানেই কোন আশংকা অনুভব কর, অতে চড়ে পালিয়ে এস।” কিন্তু মক্কার কুচক্রীরা এমন চক্রান্ত করলো যে, ঐ উটনীকে ভিন্ন পথে চালিয়ে পালিয়ে আসাও আইয়াশের পক্ষে সম্ভব হলোনা। তাকে কষে বেধে নেয়া হলো। মক্কায় পৌঁছে তারা অন্যান্য লোককে বললো, “তোমাদের মধ্যে যারা যারা হিজরত করতে চায়, তাদেরকে আমাদের মত চিকিৎসা কর।”
পরে হযরত ওমর রা. স্বহস্তে হিশাম ইবনুল আসকে একটা চিঠি লেখেন। ঐ চিঠিতে তিনি “হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের ওপর যুলুম করেছ, আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়োনা”-এই প্রখ্যাত আয়াতটি উদ্ধৃত করেন। মক্কার নিকটবর্তী ‘মীতুয়া’ নামক স্থানে হিশাম চিঠিটি পড়েন এবং তা নিয়ে বারবার চিন্তাভাবনা করেন। যখন বুঝতে পারলেন যে এতে স্বয়ং তার দিকেই ইংগিত করা হয়েছে, তখন কাল বিলম্ব না করে উটে চড়ে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু এর চেয়েও বিশুদ্ধ বর্ণনা এইযে, রসূল সা. মদীনায় হিজরত করার পর একদিন তাঁর মজলিশে এই দুই বন্দীর বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত হলো। রসূল সা. বললেন, “আইয়াশ ইবনে আবি রবীয়া ও হিশাম ইবনে আ’সকে মুক্ত করে আনতে কে আমাকে সাহায্য করবে?” ওলীদ বিন মুগীরা নিজের প্রস্তুতির কথা জানালেন। ওলীদ রসূলের সা. আদেশে মক্কা রওনা হয়ে গেলেন। লুকিয়ে কুকিয়ে লোকালয়ের কাছে পৌঁছে দেখলেন, এক মহিলা খাবার নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কোথায় যাচ্ছ?” সে জবাব দিল, “এখানে দু’জন কয়েদী আছে। তাদেরকে খাবার দিতে যাচ্ছি।” ওলীদ পিছে পিছে যেতে লাগলেন। একটা ছাদবিহীন কক্ষে ঐ দু’জনই আতক ছিল। সন্ধ্যা হয়ে গেলে দেয়াল টপকে তাদের কাছে পৌঁছলেন। তারপর শেকলের নিছে পাথর রেখে তলোয়ার দিয়ে তা কেটে ফেললেন। তারপর দু’জনকে বাইরে এনে উটে বসালেন এবং সবাই একযোগে পালালেন।
যে সকল মোহাজের মদিনায় যেতে সক্ষম হয়েছে, তাদের অধিকাংশেরই যাবতীয় সহায় সম্পদ মক্কাবাসী রেখে দিয়েছে।
কিন্তু হিজরত এত মর্মান্তিক কাজ হওয়া সত্ত্বেও নারীপুরুষ নিবির্শেষে সবাই দ্বীনী দায়িত্ব পালনের পথে নির্দ্বিধায় মাতৃভূমি ত্যাগ করে যেতে লাগলো। ইসলামী আন্দোলনের এ অলৌকিক কৃতিত্বের কোন তুলনা নেই যে, আজ থেকে শত শত বছর আগের অসভ্য আরব সমাজের নিরক্ষর মহিলাদেরকে পর্যন্ত সে ইসলামী প্রেরণায় প্রবলভাবে উজ্জীবিত করেছে।
মোহাজেরদের যাত্রায় বাধা দিয়ে কোরায়েশরা চরম অসহিষ্ণুতার মনোভাব প্রকাশ করছিল। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির সাথে তাদের বোঝাপড়া চলছিল, তিনি দেখাচ্ছিলেন পবর্তের ন্যায় উচ্চ এবং সমুদ্রের ন্যায় ঔদার্য ও মহানুভবতা। তিনি ছিলেন ধৈর্য, সহনশীলতা, গাম্ভীর্য ও স্থিরচিত্ততার মূর্ত প্রতীক। তাই তিনি দাওয়াতের কেন্দ্রস্থলে স্থির থাকলেন। তিনি শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত সবর্প্রকারে নিজের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থেকেছেন এটা প্রমান করা তার কর্তব্য ছিল। মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে আল্লাহর ইচ্ছার পূর্নতা লাভ করা পর্যন্ত তিনি ধৈর্যের সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন ডুবন্ত জাহাজের দুঃসাহসিক নাবিকের মত, যাকে সকল কর্মচারী ও যাত্রীদের নিরাপদে অন্য জাহাজে তুলে দেয়ার পরই সবার শেষে জাহাজ ত্যাগ করতে হয়।
যাদেরকে কোরায়েশরা জোরপূবর্ক আটকে রেখেছে, কিংবা যারা কোন বিশেষ স্বার্থ বা সুবিধার কারণে যেতে পারেনি, তারা ছাড়া আর কেউ যখন বাকী রইলনা, কেবল তখনই তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে হিজরতের অনুমতি পেলেন। তিনি মক্কা ত্যাগ করলেন কেবল তখনই, যখন মক্কাবাসী তাকে জীবিত দেখতে প্রস্তুত ছিলনা। তাঁর সফরের মূহুর্ত যখন ঘনিয়ে এল, তখন তিনি রক্তপিপাসু তরবারীর বেষ্টনীর ভেতর দিয়ে নির্ভয়ে ও নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন।
মদিনাঃ প্রতীক্ষার মূহুর্ত
মোহাজেরদের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে মদিনার প্রাণচাঞ্চল্য বেড়ে যাচ্ছিল। ইসলামী দাওয়াতের ঔজ্জ্বল্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। ইসলামের বিস্তারের সাথে ইসলামের বার্তাবাহকের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। বিশেষত আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের পড় থেকে মদিনার জনগণ প্রতি মূহুর্তে মক্কার পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো। যেন ক্ষেতভরা ফসলের ক্ষেত অপেক্ষমান রয়েছে যে, কখন মেঘ আসবে এবং বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যেন সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী স্তুপ হয়ে রয়েছে। মানবতার ভবনের নির্মাতা এসে তা দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করে দেবেন।
বাতাসে কাঁধে ভর করে এ খবরও মদিনায় ছড়িয়ে পড়লো যে মুহাম্মাদ সা. মক্কা থেকে চলে গেছেন এবং হিজরতের পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন। এ খবর শুনে স্বভাবতই মদিনায় ঔৎসুক্য চরম আকার ধারণ করলো এবং অপেক্ষার মূহুর্তগুলো অসহনীয় হয়ে উঠলো।
ছোট ছোট শিশুদের মুখে পর্যন্ত এ কথাই লেগে ছিল যে, রসূল সা. আসছেন, রসূল সা. আসছেন। লোকেরা প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে শহরের বাইরে জমায়েত হয়ে অপেক্ষা করতো। গ্রীষ্মের সূর্য মাথার ওপর এলে এবং রৌদ্র অসহনীয় হয়ে উঠলে আক্ষেপ করতে করতে ঘরে ফিরে যেত। যেদিন রসূল সা. সত্যি সত্যি এসে পৌঁছলেন, সেদিনও যথারীতি লোকের জমায়েত হওয়ার পর ঘরে ফিরে যাচ্ছিল। সহসা এক ইহুদী এক দূর্গের ওপর থেকে দেখেই সুসংবাদ শোনালো, “অহে ইয়াসরিববাসী, ঐ দেখ, তোমরা যে মহা মানবের অপেক্ষা করছ, তিনি এসে গেছেন।” আর যায় কোথায়! সমগ্র শহর আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে ফেতে পড়লো। লোকেরা হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো। অধিকাংশ আনসার সশস্ত্র হয়ে বেরুলো।
মদিনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী শহরতলীর জনপদ কোবাতে তিনি সবর্প্রথম আবাসস্থল করলেন। আমর বিন আওফের পরিবার সানন্দে অভ্যর্থনা জানালো এবং এই পরিবারই তাঁর আতিথেয়তা করার সৌভাগ্য লাভ করলো। এই বাড়ী আসলে ইসলামী আন্দোলনের একটা কেন্দ্রীয় ঘাঁটি ছিল। আর মোহাজেরদের অধিকাংশের জন্যই এই বাড়ীটা প্রথম মনযিলে পরিণত হলো। কিছু কিছু মোহাজের সাহাবী তখনো ওখানে অবস্থান করছিলেন। হযরত আলীও আমানতগুলো পৌঁছিয়ে দিয়ে এখানেই নিজের প্রাণপ্রিয় নেতা ও কাফেলার সাথে এসে মিলিত হলেন। এখানে চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। লোকেরা দলে দলে সাক্ষাত করতে আসতে থাকে। যার বাণী তারা ইতিপূর্বেই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে, তাঁকে স্বচক্ষে দেখার জন্য তাদের আগ্রহের অন্ত ছিলনা। তাঁর চেহারা দর্শন, তাঁর মিষ্টি বাণী শ্রবণ এবং তাঁর দোয়া লাভের আশায় সবাই জমায়েত হচ্ছিল। সালাম, সাক্ষাত, আলাপ আলোচনা, দোয়া, বৈঠক কোন কিছুই বাদ যাচ্ছিলনা।
কোবায় রসূল সা. নিজ হাতে একটা মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। প্রত্যেক মুসলমান এর নির্মাণ কাজে শরীক ছিল। পৃথিবীর ইতিহাসের সেরা ব্যক্তিত্ব একজন সাধারণ শ্রমিকের ন্যায় বড় বড় পাথর তুলে আনতে লাগলেন। কাজের সাথে গানও গাওয়া হচ্ছিলঃ
********
“মসজিদ নির্মাণকারী, কোরআন পাঠকারী এবং এবাদতের জন্য রাত্র জাগরণকারী যথার্থ সফলকাম।”
এ মসজিদ শুধু ইটপাথর ইত্যাদির সমষ্টি ছিল না, বরং নবী সা. থেকে একজন সাধারণ মুসলমান পর্যন্ত সবাই সবোর্ত্তম উদ্দীপনার পরিচয় দিয়েছিল। এ জন্যই এ মসজিদ সম্পর্কে কোরআন বলেছেঃ
*********
“এটা এমন মসজিদ যার ভিত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকওয়ার ওপর।”
রসূল সা. কোবায় পৌঁছলেন নবুয়তের একাদশ বছরের ৮ই রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার। চৌদ্দ দিন পর তিনি সদলবলে মদিনায় রওনা হলেন। কোবা থেকে মদিনা পর্যন্ত আনসারগণ দু’ধারে লাইন করে দাঁড়িয়েছিলেন মোবারকবাদ জানানোর জন্য। রসূল সা. এর মাতুলালয়ের আত্মীয়রা বিশেষভাবে সশস্ত্রভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। মহিলারা ছাদের উপর জমায়েত হয়ে স্বাগত সংগীত গাইতে থাকেঃ
********
ছোট ছোট শিশুরা দলে দলে ঘুরছিল এবং ঢোল বাজিয়ে বাজিয়ে গাইছিলঃ
*******
এই শিশুদের ভালোবাসার জবাবে রসূল সা. তাদের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন করলেন। তাদের সাথে কথা বললেন। জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমরা কি আমাকে চাও?” তারা বললো, “জ্বী হাঁ!” রসূল সা. বললেন, “আমিও তোমাদের চাই।” (সীরাতুন্নবী)
মদিনার ভাগ্যে যখন এই ঐতিহাসিক মূহুর্তটা জুটলো, তখন সেখানে কেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, তা একবার কল্পনা করুন! সেখানকার অলিগলিতে কেমন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল এবং আকাশে বাতাসে কেমন অনুভূতি ও কেমন সাড়া জেগেছিল একটু ভাবুন তো!
সাময়িক আবাসস্থল হিসাবে আবু আইয়ূব আনসারীর বাড়ীর ভাগ্য চমকে উঠলো। এখানে রসূল সা. সাত মাস অবস্থান করেন।
উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ
একটু স্বস্তি লাভ করার এবং সফরের ক্লান্তি দূর হওয়ার পর রসূল সা. উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। প্রথমে যে কাজটা শুরু করা হলো, তা ছিল মসজিদ নির্মাণ। দু’জন এতীম শিশুর পতিত জমি খরিদ করা হলো এবং হযরত আবু আইয়ূবই তার মূল্য দিয়ে দেন। এই জমিতে মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপিত হলো। মসজিদ শুধু নামাযের স্থান হিসাবেই গুরুত্ব বহন করতো না, বরং ইসলামী রাষ্ট্র ও সভ্যতার কেন্দ্র ও উৎস হিসেবে গড়ে তলা হয়েছিল। একাধারে সরকারের দরবার, পরামর্শ কক্ষ, সরকারী অতিথি ভবন, গণপাঠাগার ও জাতীয় সম্মেলন ভবন হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছিল মসজিদে নববীকে। এই নির্মাণ কাজের বেলায়ও কোবার মত সাড়া জাগলো। এমন কোন মুসলমান থাকতে পারে কি, যে এই কাজে মনে প্রাণে অংশ গ্রহণ করেনি? স্বয়ং রসূল সা. পাথর ও কাঁদা তুলে আনছিলেন। এ দৃশ্য দেখে জনৈক সাহাবী আবেগাপ্লুত হয়ে বলে উঠলেনঃ “আল্লাহর নবী যদি এ কাজে এমনভাবে আত্মনিয়োগ করেন, আর আমরা বসে বসে দেখতে থাকি, তাহলে আমাদের সমস্ত সৎকাজ বাতিল হয়ে যাবে।”
কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে কোন বাজে কথার বালাই ছিলনা। বরং রসূল সা. সহ সবাই একযোগে আওয়াজ তুলছিলেনঃ
********
“আখেরাতের সুখই প্রকৃত সুখ। তা না হলে জীবন নিরর্থক। হে আল্লাহ, আপনি আনসার ও মোহাজেরদের প্রতি অনুগ্রহ করুন।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
এই প্রেরণা ও দোয়াই ছিল মসজিদে নববী নির্মাণের আসল উপকরণ। মসজিদের সাথে সংলগ্ন একটা হুজরাও রসূল সা. এর জন্য তৈরী হয়ে গেল লতাপাতা ও মাটি দ্বারা। তিনি এই হুজরাতেই থাকতে আরম্ভ করলেন।
মদিনায় রসূল সা. এর আগমনের সাথে সাথে আপনা আপনি দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগলো। এই সাত মাসে ইসলামী আন্দোলন প্রত্যেক গৃহ ও প্রত্যেক গোত্র থেকে নিবেদিত প্রাণ সাথী সংগ্রহ করে ফেলেছিল। কেবল মাত্র আওস গোত্রের খাতমা, ওয়াকিফ, ওয়ায়েল ও উমাইয়ার পরিবারে শেরকের অন্ধকার অবশিষ্ট ছিল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
দাওয়াতী কাজের বিস্তার ঘটানো ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক কাজ। রসূল সা. ব্যক্তিগত দাওয়াত তো দিতেনই। কিন্তু যে ভাষণ দিয়ে তিনি সামষ্টিক দাওয়াতের সূচনা করেন তা ছিল নিম্নরূপঃ
“হে জনমণ্ডলী, নিজেদের জন্য সময় মত কিছু উপার্জন করে নাও। জেনে রাখ, তোমাদের সকলেরই একদিন মরতে হবে। প্রত্যেকেই নিজের লোকজনকে এমনভাবে রেখে যাবে যে, তাদের কোন অভিযোগ থাকবেনা। তারপর তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাকে এমনভাবে সম্বোধন করা হবে যে, মাঝখানে কোন দোভাষী থাকবেনা। জিজ্ঞাসা করা হবেঃ তোমার কাছে কি আমার রসূল পৌঁছেনি! এবং রসূল কি তোমার কাছে আমার বাণী পৌঁছায়নি? আমি কি তোমাকে সম্পদ ও অনুগ্রহ দেইনি? তাহলে তুমি নিজের জন্য কি সঞ্চয় করেছ? এরপর সে ডানে বামে তাকাবে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাবেনা। এরপর সামনের দিকে দৃষ্টি দেবে। কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া কিছুই চোখে পড়বেনা। অতএব যার পক্ষে সম্ভব, সে যেন একটা খেজুরের বিনিময়ে হলেও নিজেকে দোজখের আগুন থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। যে ব্যক্তি এতটুকুও পারেনা, সে যেন একটু ভালো কথা বলে হলেও আত্মরক্ষা করে। কেননা সৎকাজের প্রতিদান দশগুণ থেকে সাতশো গুণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তোমাদের ওপর নিরাপত্তা এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত নাযিল হোক।”
(সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
আর একটা সামষ্টিক ভাষণ নিম্নরূপ
“সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি তাঁরই প্রশংসা করি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাই। আমরা সবাই আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে এবং আমাদের কর্মের কূপ্রভাব থেকে আল্লাহর পানাহ চাই। আল্লাহ যাকে হেদায়াত করেন তাঁকে কেউ বিপথগামী করতে পারেনা। আর তিনি যাকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত করেন, তার কোন পথ প্রদর্শক থাকেনা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক ও শরীক বিহীন আল্লাহ ছাড়া এবাদত ও আনুগত্য লাভের যোগ্য আর কেউ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাবই সবোর্ত্তম বাণী। আল্লাহ যার অন্তরে কোরআনকে প্রিয় বানিয়েছেন, যাকে কুফরির পর ইসলামে প্রবেশ করিয়েছেন এবং যে ব্যক্তি অন্য সকল মানবরচিত বাণীর চেয়ে কোরআনকে বেশী পছন্দ করে, সে সাফল্যমণ্ডিত হবে। এ হচ্ছে সবোর্ত্তম ও সবচেয়ে প্রভাবশালী বাণী। আল্লাহ যা ভালোবাসেন তোমরা শুধু তাই ভালোবাসবে এবং আল্লাহকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসবে। আল্লাহর কাজে শৈথিল্য দেখিওনা এবং এর জন্য তোমাদের মন যেন কঠোর না হয়। যেহেতু আল্লাহ নিজের সৃষ্টি থেকে উত্তম জিনিসই মনোনীত করেন, তাই তিনি উত্তম কাজ, উত্তম বান্দা ও পবিত্রতম বাণী চিহ্নিত করেছেন। তিনি মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন, তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম। কাজেই আল্লাহর দাসত্ব অবলম্বন কর। তার সাথে কাউকে শরীক করোনা। তার গযব থেকে এমনভাবে আত্মরক্ষা কর, যেমনভাবে করা উচিত। আল্লাহর সামনে সেই সব ভালো কথাবার্তাকে কার্যে পরিণত কর, যা তোমার মুখ দিয়ে বলে থাক। আল্লাহর রহমত দ্বারা পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোল। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভংগ করলে অসন্তুষ্ট হন। তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
বিভিন্ন রেওয়ায়াত থেকে তাঁর বক্তৃতার যে বিবরণ পাওয়া যায়, তা খুবই সংক্ষিপ্ত। রসূল সা. এর ভাষণ সাধারণত সংক্ষিপ্ত হতো। কিন্তু এর ভেতর কত সুদূর প্রসারী বক্তব্য সংযোজিত হয়েছে লক্ষ্য করুন। এতে বলতে গেলে যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে। এতে ইসলামের দাওয়াতও রয়েছে, কোরআনের শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, হালাল ও হারাম বাছবিচার করার তাগিদও দেয়া হয়েছে এবং আদর্শ ভিত্তিক ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেয়া হয়েছে।
এই দুটো ভাষণ দেখলে বুঝা যায় যে, সামষ্টিক দাওয়াত কিভাবে দেয়া হতো। একদিকে মৌলিক আদর্শ দিকে আহ্বান জানানো হতো। অপর দিকে আদর্শেরই আলোকে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমাজকে পথনির্দেশিকা দেয়া হতো।
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন
তৃতীয় পদক্ষেপ এবং সম্ভব রাজনৈতিক দিক দিয়ে সবচেয়ে বড় কাজ ছিল এই যে, রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য মদীনার ইহুদী, মোশরেক ও মুসলমানদের মধ্যে একটা ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজনৈতিক ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটা লিখিত চুক্তিনামা তৈরী করা হয়, যা একটা লিখিত সংবিধানের মত ছিল। একে যথার্থভাবেই পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান বলে অভিহিত করা হয়। আমি এখানে এ সংবিধানের ধারাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে চাইনা। তবে তার কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের সার সংক্ষেপ তুলে ধরবো। এই লিখিত সাংবিধানিক চুক্তি দ্বারা রসূল সা. যা কিছু অর্জন করেন তা নিম্নরূপঃ
- মদিনার নবগঠিত সমাজে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর আইন মূল ভিত্তির গুরুত্ব অর্জন করে।
- রাজনৈতিক, আইনগত ও বিচারবিভাগীয় চূড়ান্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব মুহাম্মাদ সা. এর হস্তগত হয়।
- এই সাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে বিধিসম্মতভাবে ও আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামী রাষ্ট্র গঠিত ও ইসলামী জীবন বিধান বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। [যে ব্যক্তি কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়, সে সব সময় সর্ব প্রথম নিজস্ব রাষ্ট্র গঠনের কথা চিন্তা করে। আরবের ইসলামী সংগঠন বাহ্যিক উপায় উপকরণ ও সহায় সম্পদের দিক দিয়ে কত রিক্ত হস্ত দেখুন। তা ছাড়া মদিনার অজানা অচেনা পরিবেশে এসে কতিপয় বাস্তু ভিটে হারা ব্যক্তির সমস্যা জর্জরিত অবস্থা দেখুন। তারপর লক্ষ্য করুন যে, কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হল কত ত্বরিত গতিতে। কিভাবে কয়েক মাসের মধ্যে তার সংবিধানও চালু হয়ে গেল। ধর্মীয় ও জাতিগতভাবে পরষ্পর বিরোধী জনতাকে এত শীঘ্র একটা সংগঠনের উপর ঐক্যবধ্য করা সত্যিই ইতিহাসের এক মহা বিস্ময়কর ঘটনা।]
সে যুগের পরিস্থিতির জটিলতার প্রতি লক্ষ্য করলে অনুমান করা যায় যে, এটা এক অসাধারণ কৃতিত্ব ছিল। এর পেছনে এক অতুলনীয় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও আলাপ-আলোচনার দক্ষতা সক্রিয় দেখতে পাওয়া যায়। এই সাংবিধানিক চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তি ও লেনদেন থেকে আমরা জানতে পারি যে, রসূল সা. নিছক একজন সুফী দরবেশই ছিলেন না, বরং সামষ্টিক বিষয়গুলোকে সামাল দেয়া ও সূচারুভাবে সম্পন্ন করার বিশেষজ্ঞীয় দক্ষতা ও বিচক্ষণতার তিনি অধিকারী ছিলেন এবং এ সব দায়িত্ব সম্পাদনের পূর্ণ যোগ্যতা তিনি রাখতেন।
ভ্রাতৃত্ব ব্যবস্থা
মদিনার সমাজের তখন একটা বড় রকমের সমস্যা ছিল মোহাজেরদের পূনর্বাসন। লোকেরা একের পর এক ঘরবাড়ী ছেড়ে চলে আসছিল। মাত্র কয়েক হাজার অধিবাসী সম্বলিত ও এই মাঝারি পর্যায়ের জনপদে তাদেরকে ঠাঁই দেয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। বস্তুত এটা এমন একটা সমস্যা, যা ইতিহাসে যখনই দেখা দিকনা কেন, বিব্রতকর হয়ে দেখা দিয়ে থাকে। মদীনার সমাজ ও তার রাষ্ট্রপ্রধান যে দক্ষতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এ সমস্যার সমাধান করেছিলেন, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। কোন অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়নি, কোন আইন চাপিয়ে দেয়া হয়নি, ভূমি ও অন্যান্য সম্পদ সরকারীভাবে বরাদ্দ করতে হয়নি, শরণার্থীদের সংখ্যা নির্ধারণ করে কোন কড়াকড়ি আরোপ করা হয়নি এবং কোন বলপ্রয়োগ করা হয়নি। কেবল একটি নৈতিক আবেদন দ্বারা এত বড় জটিল সমস্যার সমাধান মাত্র কয়েক দিনে করে ফেলা হয়। বিশ্বনবী সা. আকীদা, আদর্শ ও লক্ষ্যের ভিত্তিতে সত্যিকার অর্থে একটা নতুন ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে দেখিয়ে দেন এবং এক একজন আনসারীর সাথে এক একজন মোহাজেরের ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। প্রত্যেক আনসারী নিজের সহায় সম্পদ ঘরবাড়ী, বাগবাগিচা ও ক্ষেতখামার অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিজ নিজ আদর্শিক সাথীকে দিয়ে দিচ্ছিলেন। কেউ কেউতো নিজের একাধিক স্ত্রীর মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে তার দ্বীনী ভাই এর সাথে বিয়ে দিতে পর্যন্ত প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। অপরদিকে মোহাজেররা নিজেদেরকে এতদূর আত্মসম্ভ্রমী প্রমান করেন যে, তারা বলতেন, আমাদেরকে ক্ষেতখামার বা বাজার দেখিয়ে দাও, আমরা ব্যবসায় করে বা শ্রম খেটে জীবিকা উপার্জন করতে পারবো।
অবিবাহিত, বিশেষত উঠতি বয়সের যেসব মোহাজের সংসারী হওয়ার পরিবর্তে নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষা অর্জনে নিয়োজিত করতে চাইছিলেন, তাদের বাসস্থান ছিল ‘সুফফা’ অর্থাৎ মসজিদে নববীর একটা চত্বর। বিনির্মাণ কাজের জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের রূপ নেয়। সুফফাবাসী সাহাবীদের অভিভাবক ছিল ইসলামী সমাজ। রসূল সা. স্বয়ং তাদের প্রয়োজন পূরনে মনোযোগী ও সক্রিয় থাকতেন।
আবার সেই দ্বন্দ্ব সংঘাত
এখানে আমি ইসলামের ইতিহাস ও নবী জীবনের ইতিহাসের (সীরাত) সমস্ত ধারাবাহিক ঘটনার উল্লেখ করতে ইচ্ছুক নই। সংক্ষেপে শুধু দেখাতে চেয়েছি যে, ইসলামী আন্দোলনের প্রজন্ম মক্কা থেকে মদিনায় এসে কিভাবে নবতর প্রজন্মের জন্ম দিতে থাকে। পরিবেশ কেমন ছিল এবং একটা কার্যকর শক্তির আগমনে সেই পরিবেশে কী ধরণের নতুন তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। একটা ঘুমন্ত সমাজকে সত্যের সৈনিকরা কিভাবে এগিয়ে এসে জাগিয়ে দেয় এবং তার চরিত্র গঠনে এক কার্যকর ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ইতিবাচক ভূমিকা সামনে আসার সাথে সাথেই কোন না কোন নেতিবাচক ভূমিকারও আবির্ভাব ঘটা ঐতিহাসিক নিয়ম অনুসারে অনিবার্য ছিল। গঠনমূলক তৎপরতার পাশাপাশি একটা নাশকতামূলক শক্তির সক্রিয় হয়ে উঠাটা ছিল প্রাকৃতিক বিধির অবধারিত লিখন। সত্য যখন ময়দানে সক্রিয় হয় তখন বাতিলের ময়দানেও তৎপরতা শুরু হয়ে যাওয়া অনিবার্য। নায়কের সাথে সাথে খলনায়কের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। মদীনায় যে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল, তা দেখে শয়তান নিদারুণ অস্থিরতা ও অস্বস্তি বোধ করছিল। সে নিজের কিছু একনিষ্ঠ কর্মীকে মাঠে নামাতে চাইছিল। কিন্তু খলনায়ক সে পেয়েও গেল এবং তাদেরকে সে মঞ্চে এনে হাজির করলো। ইসলামী আন্দোলন মক্কায় পড়েছিল হযরত ইবরাহীমের তথাকথিত অনুসারীদের কবলে, আর মদিনায় সম্মুখীন হলো হযরত মূসার পবিত্র আলখেল্লা গায়ে দেয়া কুচক্রীদের। ইসলামী আন্দোলনের সাথে পবিত্র কা’বার মুতাওয়াল্লীরা যে আচরণ করেছিল, বাইতুল মাকদাসের অনুসারীরাও সেই একই আচরণ করতে আরম্ভ করলো।
ইহুদীদের ঐতিহাসিক অবস্থান ও ভূমিকা
ইসলাম ও জাহেলিয়াতের ইতিহাসের এটা একটা মর্মান্তিক ঘটনা যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রয়াস প্রতিরোধের কাজটা সবার্ধিক ঈমানী আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে চিরকাল ধর্মীয় মহলই করে এসেছে। ধর্মীয় মহলের যেখানে সত্য দ্বীনের দাওয়াতের প্রথম আওয়াযেই সাড়া দিয়ে প্রথম কাতারে গিয়ে দাঁড়ানোর কথা, সেখানে কতিপয় ব্যতিক্রম বাদে তারাই সবর্প্রথম তাকে প্রত্যাখ্যান করে এসেছে। ধর্মীয় মহল প্রথমে ধর্মের খাদেম ও পতাকাবাহী হয়। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন তাদের একটা পদমর্যাদার সৃষ্টি হয়ে যায় এবং ধর্মের সাথে তাদের কিছু স্বার্থ জড়িত হয়ে যায়, তখন তারা ধর্মকে নিজেদের তাবেদার বানিয়ে নেয় এবং ধীরে ধীরে ধর্মের নামে নিজেদের কিছু চিরস্থায়ী অধিকার সৃষ্টি করে ফেলে। ধর্মপ্রাণ জনসাধারণকে তারা নিজেদের কিছু শ্রেণী ভিত্তিক দাবীদাওয়া মানতে বাধ্য করে এবং পরিণামে তাদের জন্য কিছু বিশেষ সম্মানজনক পুরস্কার নির্দিষ্ট হয়ে যায়। ধর্ম তার অনুসারীদের নৈতিক অধোপতনের যুগে সবর্দাই এই সব স্তর অতিক্রম করে থাকে। এ পর্যায়ে এসে ধর্ম একটা চমৎকার লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয় এবং তা উত্তরাধিকার সূত্রে হস্তান্তরযোগ্য স্থাবর সম্পত্তির রূপ ধারণ করে। এ পর্যায়ে এসে ওয়ায নসীহত হয়ে যায় ব্যবসায়িক পণ্য, ধর্মীয় বিদ্যা হয়ে যায় জীবিকার উপায়, আর ফতোয়া বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পর্যবসিত হয়ে একটা নিজস্ব বাজার মূল্য সৃষ্টি করে। ধর্মীয় পদ আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ও ক্ষমতার সিড়িতে পরিণত হয়। ধর্মীয় নেতারা একবার এই স্তরে উপনীত হলে তাদের বাণিজ্যিক মানসিকতা প্রত্যেক ব্যাপারে এরূপ চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে, আমাদের স্বার্থ বহাল আছে কিনা এবং আমাদের পদমর্যাদা অন্য কেউ কেড়ে নিচ্ছে নাতো ? ব্যবসায়ী মনমানস যখন এসব গুণবৈশিষ্ট সহকারে ধর্মের গণ্ডীতে প্রবেশ করে তখন তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলো দেখা দিতে থাকেঃ
- কারো দিক থেকে ভিন্নমত পোষণ সহ্য করতে পারে না এবং কোন বৃহত্তর উদ্দেশ্যে অন্যদের সাথে সহযোগিতা করতে পারেনা।
- নিজেদের মধ্যে কোন ভুল ভ্রান্তি বা দুবর্লতার কথা স্বীকার করে না এবং তা সংশোধনেও প্রস্তুত হয় না।
- নেতৃত্বের পদ ও প্রভাব বিস্তারের গদি ছেড়ে অন্য কারো নেতৃত্বে, নির্দেশে বা আহ্বানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারেনা।
এই সব বৈশিষ্টের চরম অবস্থায় এসে পৌঁছে ছিল ইহুদী জাতি। তারা কখনো এটা মেনে নিতে পারেনি যে, তাদের শ্রেণীর চৌহদ্দির বাইরেও সত্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তাদের আনুগত্য না করে কেউ সুপথে পরিচালিত হতে পারে এবং নেতৃত্বের পদ তাদের ছাড়া আর কারো প্রাপ্য হতে পারে-এ কথা তারা স্বীকারই করতনা।
বিরোধিতা মক্কার কোরায়েশও করেছে, মদিনার ইহুদিরাও করেছে। উভয় গোষ্ঠীর কেউই বিরোধিতায় কোন কমতি রাখেনি। কিন্তু উভয়ের বিরোধী ভূমিকায় বিরাট পার্থক্য রয়েছে। উভয়ের ভূমিকার তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, কোরায়েশদের বিরোধিতার পিছনে আসল চালিকা শক্তি ছিল দাম্ভিকতা ও অহংকার। কিন্তু ইহুদীদের মন আচ্ছন্ন প্রতিহিংসা, বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতায়। কোরায়েশ আভিজাত্যবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ববোধের রোগে আক্রান্ত ছিল, আর ইহুদীরা আক্রান্ত ছিল হীনমন্যতার ব্যাধিতে। এ জন্য কোরায়েশদের মধ্যে ছিল খোলাখুলি প্রত্যাখ্যান ও সঙ্ঘাতের মনোভাব। আর ইহুদীদের বিরোধিতায় কুটিল ষড়যন্ত্র ও ধাপ্পাবাজী স্বভাবের প্রাধান্য ছিল। কোরায়েশদের মধ্যে ছিল বীরোচিত ঔদ্ধত্য, আর ইহুদীদের স্বভাবে ছিল কাপুরুষোচিত ইতরামি। কোরায়েশদের বিরোধিতা যেখানে সরাসরি আক্রমণাত্মক বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল, সেখানে ইহুদীরা এগিয়ে ছিল গোপন যোগসাজশ, চক্রান্ত, কপটতা ও ভণ্ডামির দিক থেকে। মক্কায় শুধু দুটো সম্প্রদায় ছিলঃ মুসলমান ও কাফের। কিন্তু মদিনায় মুসলমান ও কাফের এই দুই শক্তির মাঝে তৃতীয় শক্তি মোনাফেকদেরও অভ্যুদয় ঘটে। এই পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বক ধার্মিকতা ও বিকৃত দ্বীনদারী উগ্র প্রকাশ্য কুফরী, শেরক ও জাহেলিয়াতের চেয়েও কতটা নীচ হীন স্বভাবের হয়ে থাকে এবং সত্য ও ন্যায়ের বিরোধিতায় কতো বেশী জঘন্য ভূমিকা পালন করে থাকে?
আমরা এটাও দেখতে পাই যে, কুফরি ও দ্বীনদারীর এই সংঘাতে ইহুদীদের বিকৃত ও স্বার্থবাদী দ্বীনদারী ইসলামের মোকাবেলায় মক্কার কাফের ও মোশরেক শক্তির সবার্ত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করেছে। অথচ যতই মতভেদ থাকুক, এক আল্লাহর এবাদত ও নৈতিকতার পতাকাবাহীদের প্রতি তো তার অধিকতর সহানুভুতি থাকা উচিত ছিল। অন্তত এটুকু সহনীয় তো হতে পারতো যে, ইহুদীরা ইসলাম বিরোধিতায় নিজেদের অবস্থানকে কাফের ও মোশরেকদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা রাখতে পারতো। কিন্তু “এসো আমাদের ও তোমাদের মধ্যকার একটি সম্মত বক্তব্যে আমরা একমত হই” এই দায়পূর্ণ আহ্বান শোনার পরও তারা শ্রেষ্ঠতম মানব মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথীদের পবিত্র ধর্মীয় চিন্তা ও কর্মকে বাদ দিয়ে আবু জাহল ও আবু লাহাবের ন্যায় নিকৃষ্ট মানুষদের সহযোগী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। বক ধার্মিকতা ও বিকৃত দ্বীনদারীর আর একটা চিরন্তন ঐতিহাসিক ভূমিকা এই হয়ে থাকে যে, তা যুদ্ধের ময়দানেও কোন অবস্থায়ই ধর্মীয় পক্ষের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়না। বরং তা অবধারিতভাবে ধর্মের শত্রুদের পক্ষেই যায়। কুফরী, নাস্তিকতা ও পাপাচারীদেরই সহযোগী হয়ে যায়। গুটিকয় ব্যতিক্রমী ব্যক্তির কথা আমি আলোচনা করছিনা। এ ধরণের ব্যতিক্রম যে কোন গোষ্ঠীর মধ্যে নিকৃষ্টতম বিকৃতির সময়েও কিছু না কিছু পাওয়া যায়। আমরা কেবল সাধারণ নীতিগত বিষয়েই আলোচনা করছি।
এই ছিল ইহুদীদের ন্যাক্কারজনক অবস্থান। তারা নিজেদের গোপন ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মাচারের সকল অস্ত্র ধারণ করত নাশকতামূলক ও নেতিবাচক ফ্রন্টে গিয়ে তারা ইসলামের দিকে অস্ত্র তাক করে ওৎ পেতে বসে এবং কার্যত কাফের ও মোশরেকদেরকে সবার্ত্মক সহযোগিতা দেয়। তারা রসূল সা. এবং ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী সাহাবীগণের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য গালাগাল ও কটুবাক্য বর্ষণ করে, ব্যাংগ বিদ্রুপ করে, নিত্যনতুন প্রশ্নাদি তুলে হয়রানি করে। অপবাদ ও অপপ্রচারের তাণ্ডব তোলে এবং গোয়েন্দাগিরি করে। কখনো কখনো মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করে, তাদেরকে কাফের ও ফাসেক বলে ফতোয়া দেয়, রসূল সা. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং যুদ্ধ ও আপদকালীন অবস্থায় ভয়ংকর ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা করে। ইসলামের ক্ষতি সাধনে তারা সাধ্যমত কোন কিছুই করতে বাদ রাখেনি। কিন্তু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা একটা মারাত্মক ভুল ধারণায় পতিত থাকে। নাশকতামূলক কার্যকলাপে লিপ্ত নেতিবাচক স্বভাবের লোকেরা চিরকালই এ ধরনের ভুল ধারণায় পতিত হয়ে থাকে। (কিন্তু পরবর্তীকালের লোকেরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণও করেনা।) তাদের ভুল ধারণাটা ছিল এই যে, যারা কোন নীতি ও আদর্শের ধার ধারেনা, কোন গঠনমূলক কর্মসূচী রাখেনা এবং নৈতিক অধোপতনের সবর্নিম্ন স্তরে নেমে যায়, তারা যে কোন আদর্শবাদী ও গঠনমূলক আন্দোলনকে প্রতিহত করতে পারে। আসলে তাদের ভূমিকা এ রকম, যেমন উঠতি সূর্যের আলোক রশ্মির প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে চামচিকেরা শূণ্যে পাখনা মেলে কৃত্রিম অন্ধকার সৃষ্টির ব্যর্থ চেষ্টা চালায়, সশস্ত্র সেনাবাহিনীর গতিরোধ করার জন্য যেমন কিছু মশামাছি ভনভন করে, কিংবা পূর্ণিমার চাঁদ দেখে যেমন কোন গোঁয়ার তার দিকে থুথু নিক্ষেপ করে।
যাদের নিজস্ব কোন মূল্য নেই, যাদের কাছে কোন প্রাণবন্ত আদর্শ নেই, যাদের স্বভাব চরিত্রে সমকালীন মানব সমাজের জন্য কোন আদর্শ নেই এবং যাদের কাছ থেকে মানব জাতির কোন গঠনমূলক সেবা পাওয়ার কোন আশা নেই, তারা নিছক অন্যদের গতি রোধ করে নিজেদের জন্য কোন স্থায়ী সাফল্য আনতে পারেনা। যাদের কাছে স্থবিরতা, কর্মবিমুখতা, গোঁড়ামি, বিকৃতি ও নাশকতা ছাড়া অন্য কোন উপকরণ নেই, তারা সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত একটা কর্মচঞ্চল দলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর যাই হোক, নিজেদের মধ্যে কোন মূল্য ও মর্যাদা সৃষ্টি করতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত এ ধরনের লোকদের কপালে ব্যর্থতা ও অপমান ছাড়া আর কিছুই জোটেনা। কিন্তু যখন কোন বিকারগ্রস্ত জনগোষ্ঠী আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়ার গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে বিবেচনা শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন সে আর পরিণাম নিয়ে ভাবেনা। শুধুই সামনে এগিয়ে যেতে থাকে। বিকারগ্রস্ত ইহুদী সম্প্রদায়ও হীনমন্যতা ও হিংসার চোটে অন্ধ হয়ে ইসলামের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়।
মদিনার মুসলমানদের চরিত্রের সাথে ইহুদীদের চরিত্রের তুলনামূলক পর্যালোচনা করলে এও বুঝা যায় যে, সত্য ও ন্যায়ের পতাকাবাহীদের ডাকে যারা সাড়া দেয়, তাদের চরিত্র যতটা উন্নত মানের হয়ে থাকে, তাদের বিরোধিতাকারিদের চরিত্রেও ঠিক ততই অধোপতন ঘটে। ইতিবাচক আন্দোলন মানবতাকে যত সুষমামণ্ডিত করে, নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তাঁকে ততটাই বিকৃত ও বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়।
ইসলামী সমাজের পরিচালকের সামনে একদিকে অত্যন্ত ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী গঠনমূলক পরিকল্পনা ছিল। অপরদিকে অব্যাহতভাবে আগমনরত শরণার্থীদের পুনবার্সন ও তাদের অর্থনৈতিক সহায়তা দানের সমস্যা ছিল। উপরন্তু মক্কার কোরায়েশদের পক্ষ থেকে প্রতিমূহুর্তে আক্রমনের আশংকাও ছিল এবং তা প্রতিরোধের জন্য টেকসই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও অপরিহার্য ছিল। আর এই সমস্ত সমস্যাগুলোর ওপর বাড়তি আর একটা মারাত্মক সমস্যা এই ছিল যে, মদিনার নবগঠিত রাষ্ট্র ও বিকাশমান সমাজের অভ্যন্তরে কুচক্রী ও বিশ্বাসঘাতক গৃহশত্রু বিভীষণদের একটা বৃহৎ গোষ্ঠী নানা রকমের বিভ্রান্তিকর ও বিভেদাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছিল। ভেবে দেখা দরকার যে, এমন পরিস্থিতিতে বিশ্বনবীর দায়দায়িত্ব কত নাজুক ও জটিল হয়ে থাকতে পারে। ঐ একটি মাত্র মস্তিষ্ক দিনরাত কত রকমের সমস্যার ভাবনায় ছিল তা বোধ হয় আমাদের আমাদের পক্ষে চিন্তা করাও কষ্টকর। আমরা হয়তো ভেবেও কূল কিনারা পাবোনা যে, ক্ষুদ্র একটি ইসলামী সংগঠন এবং একেবারে প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রমরত আন্দোলন কত বড় প্রাণান্তকর পরিস্থিতিতে পড়েছিল। আর এই যাবতীয় জতিলতা সৃষ্টির দায়ভার ইতিহাসে একমাত্র ইহুদীদের ঘাড়েই চাপানো হয়েছে। এ দায়ভার যথার্থই আল্লাহকে মান্যকারী, হযরত ইবরাহীম আ. ও হযরত মূসা আ.-এর ভক্ত, তাওরাতের অনুগত এবং পবিত্রতা, আধ্যাত্মিকতা, আল্লাহর জ্ঞান ও খোদাভীরুতার স্বগত ঠিকাদার ইহুদী সম্প্রদায়ের ওপরই বর্তায়।
শুরুতে ইহুদীরা রসূল সা. ও ইসলামের প্রতি অত্যন্ত আশান্বিত ছিল। তারা দেখতে পাচ্ছিল যে, এই নব আবির্ভূত ধর্মের অনুসারীরা হযরত ইসমাঈলের বংশধরদের সাথে (অর্থাৎ কোরায়েশদের সাথে-অনুবাদক) দ্বন্দ্বে লিপ্ত, ইহুদীরা যেসব নবীর ভক্ত তারাও তাদেরকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, তাদের কিতাবকেও তারা ভক্তি করে এবং তাদের কেবলা অর্থাৎ বাইতুল মাকদাসকে নিজেদের কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ কারণে তাদের ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, ধীরে ধীরে মুহাম্মাদ সা. ও তাঁর সহচর বৃন্দকে ইহুদী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়া যাবে। ইহুদীরা ন্যায় ও সত্যের দৃষ্টিতে এ কথা ভাবছিল না, বরং এটা ছিল তাদের নির্ভেজাল ও বাণিজ্যিক ভাবনা। তারা ভেবেছিল, এই বাস্তুভিটে চ্যুত সবর্হারা লোকদেরকে তারা অচিরেই নিজেদের অনুগত বানাতে পারবে। এই আশায়ই তারা মুসলমানদের সাথে তেমন কোন বাদানুবাদ ছাড়াই চুক্তি সম্পাদন করে এবং মদিনায় যে রাজনৈতিক সংগঠনটা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল, তাকে মেনে নেয়। তাদের ধারণা ছিল যে, এই বিকাশমান রাজনৈতিক শক্তি তো আমাদের পকেটেই রয়েছে। আমাদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রতাপ তাদের চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। সত্য ও ন্যায়কে উপলব্ধি করা, চিন্তা ও চরিত্রের সংশোধন করা কিংবা পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করার কোন উদ্যোগ, চেষ্টা বা চিন্তা চেতনা ইহুদীদের ছিলনা। নিছক একটা গোষ্ঠী স্বার্থ এই হতভাগাদের মাথায় সওয়ার ছিল। তারা মনে করতো মদিনায় তাদের দোরগোড়ায় শিকার এসে জড় হচ্ছে। তাই তারা ফাঁদ ও জাল পেতে শিকার ধরার জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। তাদের দৃষ্টিতে মুসলমানরা ছিল সাগর থেকে কিনারের দিকে ভেসে আসা মাছের ঝাঁক। আর সেগুলোকে ধর্মীয় ভণ্ডামির জালে আটকানোর জন্য ইহুদী জেলেরা সমস্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হয়ে তীরে এসে বসে ছিল। কিন্তু অল্প কিছু দিনের অভিজ্ঞতাতেই তাদের আকাশ কুসুম কল্পনা ভেস্তে যেতে লাগলো। মুসলমানরা তাদের বুঝিয়ে দিল যে, তারা এত সহজ শিকার নয়। তারা এমন মজবুত শক্তি যে, শিকারী স্বয়ং তাদের হাতে শিকারে পরিণত হয়। তারা দেখতে পেল যে, ক্রমান্বয়ে একটা বিপ্লবী মেজাজের ইসলামী রাষ্ট্র বিকাশ লাভ করতে যাচ্ছে। এই রাষ্ট্র স্বয়ং একটা দূর্গের মত শক্তিশালী হতে লাগলো। ইহুদীরা মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই বুঝে ফেলল যে, সাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে যে রাষ্ট্রের পত্তনে তারাও অংশ নিয়েছে, সে রাষ্ট্রটা তাদের হাতের পুতুল হওয়া তো দূরের কথা, তার কোথাও তাদের আংগুল ঢুকানোরও অবকাশ নেই। ঐ রাষ্ট্রে তারা যে মোড়ল সুলভ আসন লাভ করার স্বপ্ন দেখেছিল, সে ব্যাপারে অচিরেই তারা চরমভাবে ব্যর্থ হলো। ঐ রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও তৎপরতায় প্রভাব বিস্তারের যে চেষ্টা তারা করেছিল তাতে তারা বারবার ব্যর্থ হলো। ঐ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি, অন্যান্য কর্মকর্তা ও তার মূলনীতিতে আস্থাশীল নাগরিকগণকে নিজেদের বাগে আনতে তারা যতগুলো ষড়যন্ত্র করেছিল, তার সবই নস্যাত হয়ে গেল। বরঞ্চ প্রাথমিক পর্যায়েই এমন বিপত্তি ঘটলো যে, তাদের লোকেরাই রসূল সা. এর পেশ করা মূলনীতির সামনে আত্মসমর্পণ করতে লাগলো। এই ‘বিপজ্জনক’ বৈপ্লবিক স্রোত কেবল নিরক্ষর সাধারণ ইহুদীদেরকে নয়, বরং বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে পর্যন্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এরপরই তারা সম্বিত ফিরে পেল। তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের আধ্যাত্মিকতার রমরমা ব্যবসা লাটে উঠতে চলেছে। তাদের সাধের শিকারগুলো একে একে হাতছাড়া হতে চলেছে। ইহুদীরা তাদের সম্পাদিত চুক্তির সবর্নাশা ফল দেখে আঁতকে উঠলো। এই চুক্তির আলোকে একদিকে তারা মুসলিম রাষ্ট্রের আইনের আনুগত্য করতে ছিল বাধ্য। অপরদিকে মুসলমানদের সাথে প্রতিরক্ষামূলক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে রেখেছিল। তৃতীয় দিকে তারা দেখতে পাচ্ছিল, যে আশায় তারা এসব করেছিল, তা সবই মরিচীকায় পরিণত হয়ে যাচ্ছে।
তাই এ কারণে ভেতরে ভেতরে তাদের মধ্যে চরম বিদ্বেষাত্মক লাভা পুঞ্জীভূত হতে লাগলো এবং থেকে থেকে সেই লাভা তাদের সমাজদেহ থেকে উদ্গীরণ করা হতে লাগলো। বিশেষত, কেবলা পরিবর্তনের ঘটনায় তো ইহুদী সমাজের প্রতিহিংসার মনোভাব নগ্নভাবে প্রকাশ পেল। প্রথমে তা অপপ্রচারে রূপ ধারণ করলো। তারপর তা পরিণত হলো নাশকতামূলক তৎপরতায়। সবর্শেষে তা বিশ্বাসঘাতকতার আকারে আত্মপ্রকাশ করলো। আসুন, মাদানী যুগে এই মনোভাবের প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট সেই ইসলাম বিরোধী তৎপরতার পর্যালোচনা করা যাক, যা মানবতার শ্রেষ্ঠতম শুভাকাংখী ও তার সাথীরা ভোগ করেছিলেন এবং যা থেকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে ইসলামী রাষ্ট্রকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিল।
অসহিষ্ণু আচরণ
মদিনার সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে যেসব গুরুদায়িত্ব বহন করতে হচ্ছিল, তার আলোকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিকদের ভূমিকাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত যারা প্রথম কাতারের কর্মী ছিল, তাদের কোন একজনের অভাবও রসূল সা. এবং তাঁর সাথীদের জন্য মর্মঘাতী ছিল। বনু নাজ্জার গোত্রের কাছে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আবু উমামা আসয়াদ বিন যারারা ঠিক এ ধরনেরই একজন কর্মী ছিলেন। কিন্তু একেবারে প্রাথমিক যুগেই তিনি ইন্তিকাল করেন। ফলে ইসলামের একজন সুযোগ্য সৈনিকের অভাব ঘটলো। এ ঘটনা রসূল সা. এর জন্য এমনিতেই মর্মঘাতী ঘটনা ছিল। তদুপরি মদিনার ইসলাম বিদ্বেষী গোষ্ঠী বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারের মাধ্যমে তাঁর এই মনোকষ্টকে দ্বিগুন করে তুললো। ইহুদী ও তাদের তল্পীবাহক মোনাফেকরা বলে বেড়াতে লাগলো যে, “দেখলে তো! মুহাম্মাদ সা. যদি সত্যি সত্যি নবী হতো, তাহলে তাঁর এমন সক্রিয় কর্মী এমন অসময়ে মারা যেত নাকি?” অর্থাৎ কিনা, তাঁর মৃত্যুতে তাদের উল্লাসের অবধি রইল না। চারদিক থেকে প্রতিনিয়ত দুঃখ দুবির্পাকের আঘাতে জর্জরিত স্বয়ং রসূল সা. এর সংবেদনশীল মনও পর্যন্ত এ অপপ্রচারে নীরব থাকতে পারেনি। তিনি বললেনঃ “আবু উমামার মৃত্যুটা ইহুদী ও আরবের মোনাফেকদের জন্য নিদারুণ মৃত্যু! ওরা বলে বেড়াচ্ছে যে, মুহাম্মাদ সা. যদি নবী হতো, তাহলে তার সাথী মরতোনা। অথচ আল্লাহর ইচ্ছা থেকে আমি নিজেও রক্ষা পেতে পারিনা, আমার কোন সাথীকেও রক্ষা করতে পারিনা।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
এই ক্ষুদ্র ঘটনা থেকেই বুঝা যায় যে, শত্রুদের মনে কত আক্রোশ পুঞ্জীভূত ছিল। বনু নাজ্জার গোত্রের লোকেরা এসে রসূল সা. কে বলল, “এখন আমাদের জন্য আর একজন দায়িত্বশীল নিয়োগ করে দিন।” বনু নাজ্জার যেহেতু রসূল সা. এর আত্মীয় ছিল, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য রসূল সা. বললেন, “তোমরা আমার মাতুল, আমি তোমাদের সব কিছুর সাথে আছি এবং আমিই তোমাদের দায়িত্বশীল।”
যে সব শর্তের ভিত্তিতে ইহুদীরা চুক্তিতে সই করেছিল, তাঁর কারণে তারা ইসলামী আন্দোলনের উন্নতি ও বিস্তার লাভে বাধা দিতে পারছিলনা। তাদের চোখের সামনে সাধারণ মানুষ ও তাদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছিল। অথচ তাদের আধ্যাত্মিক নেতারা, পীর দরবেশরা ও মুফতিরা নীরব দর্শক হয়ে তা দেখছিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাদের ঘরে ঘরেও ইসলাম প্রবেশ করা শুরু করেছিল। তাদের নিজেদের লোকেরা, বিশেষত গণ্যমান্য লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে থাকায় ধর্মব্যবসায়ী মানসিকতার অধিকারী এই সম্প্রদায়ের ধৈর্যের বাঁধ না টুটে গত্যন্তর ছিলনা। তাছাড়া প্রত্যেক বিপ্লবী আন্দোলনের প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা এত অপ্রতিরোধ্য হয়ে থাকে যে, নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে যারা তার প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে, তাদের মোকাবিলা করার জন্য তাদের পরিবারের নবীনরাই ঐ বিপ্লবী আদর্শে দীক্ষিত হয়ে থাকে। ফলে ছেলে বাপের সাথে, বউরা শাশুড়ীর সাথে, মেয়েরা মায়ের সাথে, পৌত্রেরা দাদা নানার সাথে এবং দাসেরা মনিবের সাথে বিরোধে লিপ্ত হয়ে থাকে।
প্রবীণদের ধর্মাচার যখন নবীন আন্দোলনের এই অভ্যন্তরীণ আক্রমণের শিকার হয়, তখন প্রবীণরা ক্রোধে বেসামাল হয়ে যায়। এ পর্যায়ে এসে তাদের ধৈর্যসহিষ্ণুতা একেবারেই ফুরিয়ে যায়। ইতিহাস মদিনায়ও তার এই চিরচারিত রীতির পুনরাবৃত্তি করলো। আমি আগেই বলেছি মদিনায় কত জোরেশোরে ইসলামের বিজয় পতাকা উত্তীর্ণ হচ্ছিল এবং কত দ্রুত গতিতে ঘরে ঘরে নতুন আদর্শের বিজয় ডংকা বাজছিল। এই অকল্পনীয় পরিবর্তন ঘটতে দেখে ইহুদীরা আক্রোশে অধীর হয়ে উঠছিল। বিশেষত যখন বিভিন্ন গোত্রের সরদাররা এবং খ্যাতনামা প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ ইসলামের সত্য দাওয়াতে সাড়া দিত, তখন হিংসা ও হীনমন্যতার প্রভাবে সমগ্র ইহুদী সমাজের দেহ শিউরে উঠতো। উদাহরণ স্বরূপ তাদের চোখের সামনেই যেদিন আবু কায়েস আবি আনাস ইসলাম গ্রহণ করলো, সেদিন ইহুদীদের মন যে উত্তেজনায় কি তোলপাড় হয়েছিল, তা বোধকরি ভাষায় ব্যক্ত করার সাধ্য কারোই ছিলনা। ইনি একজন নামকরা প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। জাহেলী যুগেই তিনি সমাজের প্রচলিত ধারার বিপরীত দিকে চলতে শুরু করেছিলেন। শুধুমাত্র স্বভাবসুলভ প্রজ্ঞা ও বিবেকের তাগিদে তিনি মূর্তিপূজা ছেড়ে দেন, স্ত্রী সহবাসে পর গোসল করা জরুরী সাব্যস্ত করেন এবং ঋতুবতী স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকেন। প্রথমে খৃষ্ট ধর্মের দিকে আকৃষ্ট হন, কিন্তু সহসাই থেমে যান। নিজ গৃহে মসজিদ বানিয়ে নেন এবং তাতে অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকেন। তিনি প্রকাশ্যে বলতেন, আমি ইবরাহীম আ. এর খোদার এবাদত করি। বার্ধক্য পীড়িত এই ব্যক্তি হক কথা বলায় খুবই সাহসী ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করতেন। তিনি কবিতার মাধ্যমে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাঁর কিছু কবিতা ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে সংকলিত আছে। এ ধরনের তীক্ষ্ণ মেধাবী ও সৎ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে সমাজে বিশিষ্ট গণ্যমান্য হিসাবে চিহ্নিত হবেন, সেটাই তো স্বাভাবিক।
বিচিত্র নয় যে, ইহুদীরা তার সাথে তর্কবিতর্ক করে থাকবে এবং নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করে থাকবে। কিন্তু তাঁর নির্মল ও বিকারমুক্ত স্বভাব প্রকৃতি তাঁর মধ্যে সত্য দ্বীনের যে চাহিদা ও রুচি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তা স্বয়ং রসূল সা. ছাড়া আর কারো পক্ষে পূরণ করা সম্ভব ছিলনা। রসূল সা. যখন মদিনায় পৌঁছলেন, তখন তাঁর সৌভাগ্যের মূহুর্তটি ঘনিয়ে এল। তিনি ইসলামী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন এবং ইসলামের বাস্তব অনুসারীতে পরিণত হলেন। এ ঘটনায় ইহুদীদের মধ্যে কেমন প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে, সেটা কল্পনা শক্তি প্রয়োগ করে কিছুটা আঁচ করা সম্ভব।
তবে এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে, তাদের নিজস্ব সামাজিক গণ্ডির বাইরেই হয়েছে। আসল তোলপাড় সৃষ্টিকারী ঘটনা তখনই ঘটলো যখন ইসলাম খোদ ইহুদী সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো। তন্মধ্যে যে ঘটনাটা ইহুদী সম্প্রদায়ের মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দেয়, তা ছিল অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মতাত্মিকের মানসিক বিপ্লব। ইতিহাস সাক্ষী যে, শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, তা সে দুনিয়াদারী কিংবা দ্বীনদারী যে দিককারই হোক না কেন, তাদের মধ্যে সত্য গ্রহণের আনুপাতিক হার খুবই কম হয়ে থাকে। তবে সৎ স্বভাব সম্পন্ন লোকেরা অবশ্যই সকল মহলে বর্তমান থাকে। সত্যের সূর্য দীপ্তি ছড়ানোর সময় তারা চোখ বুজে একগুঁয়েমি ও বিদ্বেষ পরায়ণতার বদ্ধ কুঠুরিতে গিয়ে আত্মগোপন করেনা। বরং উজ্জ্বল আলোক রশ্মি প্রবেশের জন্য মন মগজের বাতায়ন খুলে দেয়। গণ্যমান্য ও জ্ঞানী গুণীদের কাতার থেকে যদিও খুব কম লোকেরই সমাগম ঘটে থাকে ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনে, কিন্তু যারা আসে তারা খুবই মূল্যবান সম্পদ হয়ে থাকে। কেননা তাদেরকে স্বার্থ ও পদ মর্যাদার বড় বড় শেকল ভেংগে আসতে হয়। ইহুদী সমাজে এ ধরনেরই এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন সালাম। তাঁর প্রাগৈসলামিক নাম ছিল হাসীন। তিনি একজন উঁচুদরের আলেম ও খোদাভীরু ধর্মীয় নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন বনু কাইনুকা গোত্রের লোক। রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাতের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং নিজের পরিবার পরিজনকেও ইসলামে দাওয়াত দেন ও উদ্বুদ্ধ করেন। শেষ পর্যন্ত গোটা পরিবারই ইসলাম গ্রহণ করে। তাঁর এক আত্মীয় তাঁর কাছ থেকে শুনে তাঁর ইসলাম গ্রহণের যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তা শুনুনঃ “আমি যখন আল্লাহর বার্তাবাহকের আগমনের খবর প্রথম শুনলাম, তখন তাঁর নাম, গুণবৈশিষ্ট ও আগমনের দিনক্ষণ জেনে নিলাম। কেননা আমরা তাঁর প্রতীক্ষায় ছিলাম। তাই এই খবরটা শুনে মনে মনে আনন্দিত হচ্ছিলাম। কিন্তু মুখে কিছু বলছিলাম না। তিনি যখন মদিনায় চলে এলেন, তখন পর্যন্ত আমি চুপচাপ ছিলাম। যখন তিনি কোবায় বনু আমর ইবনে আওফের বসতিতে পৌঁছলেন, তখন একটা লোক এসে আমাকে তাঁর আগমন বার্তা শোনালো। এ সময় আমি আমার খেজুর গাছের মাথার ওপর চড়ে কাজ করছিলাম। আমার ফুফু খালেদা বিনতে হারেস নিচে বসা ছিলেন। আমি আগমন বার্তা শোনামাত্র উচ্চস্বরে আল্লাহু আকবর ধ্বনি তুললাম। ফুফু আমার ধ্বনি শুনে বললেন, “আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করে দিক! হযরত মূসা বিন ইমরানের আগমনের খবর শুনলেও তুই এমন উল্লাস প্রকাশ করতিনা।” আমি বললাম, “ফুফুজান! আল্লাহর কসম, ইনি মূসা বিন ইমরানের ভাই এবং তাঁরই ধর্ম পালনকারী। মূসা বিন ইমরান যে বিধান এনেছিলেন, ইনিও তাই নিয়ে এসেছেন।” ফুফু বললেন, “হে আমার ভাতিজা, যে নবীর কথা আমাদেরকে বলা হয় যে, কেয়ামতের আগে আসবেন, ইনি কি সেই নবী?” আমি বললাম, “হাঁ, ইনিই তো সেই নবী।” এরপর আমি আল্লাহর নবীর সান্নিধ্যে পৌঁছলাম এবং ইসলাম গ্রহণ করলাম। তারপর নিজের পরিবার পরিজনের কাছে এলাম এবং তাদেরকেও দাওয়াত দিলাম। ফলে তারা সবাইও ইসলাম গ্রহণ করলো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
এই নওমুসলিম আলেম যেহেতু ইহুদীদের দুবর্লতাগুলো জানতেন এবং তাদের বিদ্বেষপূর্ণ মানসিকতা ও নিকৃষ্ট চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন, তাই তাঁর ইসলাম গ্রহণে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হবে, তাও জানতেন। স্বার্থপরতার ভিত্তিতে যখন দল ও গোষ্ঠী গঠিত হয়, তখন চরিত্রের এত অধোপতন ঘটে থাকে যে, ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলার পরিবর্তে নিজেদের মন্দকে ভালো এবং প্রতিপক্ষের ভালোকে মন্দ বলা হয়। নিজের গোয়ালের গরু কালো হলেও তাকে সাদা এবং অন্যের গোয়ালের গরু সাদা হলেও তাকে কালো বলা হয়। এমনকি নিজের গোয়ালের সাদা গরু গোয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই কালো বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সকল যুগেই এ ধরনের ধর্মচারীদের চরিত্র একই রকম হয়ে থাকে। যতক্ষণ কোন ব্যক্তি তাদের সাথে থাকে অথবা অন্তত পক্ষে এই তার সম্পর্কে এই আশংকা জন্মেনা যে তার তৎপরতা তাদের বাণিজ্যিক স্বার্থকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে না, ততক্ষণ তার গুণাবলী খোলামনে স্বীকার করা হয়। বরং কখনো অতিরঞ্জিত করে ঢালাওভাবে তার বিদ্যা ও চরিত্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়। কিন্তু সময়ের কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ ধরনের কোন মহান ব্যক্তিত্বের ভূমিকা কারো ধর্মব্যবসায়ের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হলে তৎক্ষণাত মতামত পালতে যায়। আগে যিনি আলেম ছিলেন এখন তাকে মূর্খ বলা হয়। আগে যিনি মুমিন ছিলেন, এখন তাকে বলা হয় কাফের, ফাসেক এবং আরো অনেক কিছু। আগে যে ব্যক্তি জাতির সেবক বলে গণ্য হতো, এখন তাকে বলা হয় বিপথগামী। আগে যে ব্যক্তি ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র ছিল, এখন সে হয়ে যায় গালাগালের শিকার। বিকৃত স্বভাবের অধিকারী ইহুদী জাতির চরিত্রের এইসব হীনতা ও নীচতা আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের জানা ছিল। তিনি এই হীনতা ও নীচতার ওপর থেকে আবরণ তুলে ফেললেন। মনে মনে একটা নাটকের পরিকল্পনা করে নিজের ইসলামের গ্রহণের বিষয়টা গোপন রেখেছিলেন। উপযুক্ত সময় রসূল সা. এর কাছে হাজির হয়ে বললেন, ইহুদীরা একটা বাতিলপন্থী জাতি। তাদের বিকারগ্রস্ত স্বভাবের মুখোশ খুলে ফেলার জন্য আপনি আমাকে আপনার গৃহে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখুন। তারপর তাদের চোখের আড়ালে রেখে আমার সম্পর্কে তাদের মতামত জানতে চাইবেন। তারপর দেখবেন, আমার ইসলাম গ্রহণের কথা নাজানা অবস্থায় তারা আমার সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে। তারা যদি আমার ইসলাম গ্রহণের খবর জেনে ফেলে, তাহলে আমার ওপর অপবাদ আরোপ করবে ও দোষ বদনাম করবে। রসূল সা. অবিকল তাই করলেন। আব্দুল্লাহ বিন সালামকে তাঁর ঘরে পর্দার আড়ালে বসিয়ে রাখলেন। এদিকে ইহুদী নেতারা এলো এবং আলাপ আলোচনা চললো। তারা নানা প্রশ্ন করলো এবং তাঁর জবাব দেয়া হলো। সবর্শেষ রসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যকার হাসীন বিন সালাম কেমন লোক? তারা বলল, ‘উনি আমাদের সরদার এবং সরদারের ছেলে। উনি আমাদের একজন মহৎ ব্যক্তি এবং একজন বড় আলেম। এভাবে তারা গুণকীর্তন করার পর আব্দুল্লাহ বিন সালাম পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন এবং তাদেরকে সম্বধন করে বললেন, “ হে ইহুদী সম্প্রদায়, আল্লাহকে ভয় করো এবং যে ধর্ম মুহাম্মাদ সা. নিয়ে এসেছেন তা গ্রহণ কর। কেননা আল্লাহর কসম, তোমরা ভালোভাবেই জান যে, ইনি আল্লাহর প্রেরিত রসূল। তোমরা মুহাম্মাদ সা. এর পবিত্র নাম ও গুণাবলী তাওরাতে লিখিত দেখে থাক। তাই আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল। তাঁর ওপর ঈমান আনছি, তাঁকে সত্য বলে জানি এবং স্বীকার করছি।” ইহুদীরা এই নাটকে যারপর নাই বিব্রত হলো এবং তৎক্ষণাত বলল, “তুমি মিথ্যুক।” এরপর আব্দুল্লাহ বিন সালামের নিন্দাবাদ ও কুৎসা রটানো শুরু করে দিল। এক্ষুনি কয়েক সেকেন্ড আগে যাকে মহান ব্যক্তি ও আলেম বলে আখ্যায়িত করেছে, তাকেই মিথ্যুক বলতে শুরু করে দিল। আব্দুল্লাহ রসূল সা. কে বললেন, “আমি আপনাকে বলেছিলাম না যে, এরা একটি বাতিলপন্থী সম্প্রদায়। এরা অহংকার, মিথ্যাচার ও অসদাচারের দোষে দুষ্ট।” এভাবে একটা নাটকীয় পদ্ধতিতে আব্দুল্লাহ বিন সালাম নিজের গোটা পরিবারের ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এ ঘটনায় ইহুদীদের মনমগজে কি সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া হয়ে থাকতে পারে ভেবে দেখুন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, ১৩৮-১৩৯ পৃঃ)
এর অল্প কিছুদিন পর ওহুদ যুদ্ধের দিন প্রখ্যাত আলেম ও সম্মানিত ব্যক্তি মুখাইরিকের বেলায়ও এ ধরনের ঘটনা ঘটে। ইনি ইহুদীদের মধ্যে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর ছিল অনেকগুলো খেজুরের বাগান। তিনি নিজের জ্ঞানের আলোকে রসূল সা. এর গুণাবলী দেখে তাঁকে চিনে ফেলেছিলেন। ঘটনাক্রমে ওহুদের দিন এসে গেল এবং তা ছিল শনিবার। একটা মজলিশে তিনি বললেন, “হে ইহুদী জনমণ্ডলী, আল্লাহর কসম তোমরা জান যে, মুহাম্মাদ সা. এর সাহায্য করা তোমাদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য।” তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, মক্কার মোশরেকদের মোকাবিলায় মুসলমানদের দলকে সাহায্য করা তোমাদের ওপর নীতিগতভাবে ফরয। এর জবাবে ইহুদীরা যা বললো তা তাদের ধাপ্পাবাজি ও খল মানসিকতারই ঘৃণ্য ছবি তুলে ধরে। তারা বললো, “আজ তো শনিবার।” এ জবাব শুনে মুখাইরিক তেজোদীপ্ত কণ্ঠে বললেন, “তোমাদের জন্য কোন শনিবার নেই।” অতঃপর তিনি অস্ত্র হাতে নিয়ে ওহুদের ময়দানে গিয়ে রসূল সা. এর সাথে মিলিত হলেন। যাওয়ার সময় নিজের পরিবার পরিজনদের সাথে দেখা করে বলে গেলেন, আমি যদি আজ নিহত হই, তবে আমার সমস্ত ধন সম্পদ রসূল সা. এর হাতে সমর্পন করবো। তিনি আল্লাহর নির্দেশে যেভাবে ভালো মনে করেন, তা খরচ করবেন। সত্যিই এই ত্যাগী সৈনিকটি ঐদিন মারা গেলেন। রসূল সা. তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি গ্রহণ ব্যয় করেন। তবে মুখাইরিক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিনা, সে সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে।
ইসলামী আন্দোলনের এই বিজয়াভিযানে ইহুদীদের ভণ্ডামি যে গোপন প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে, তা একটা মজার ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উম্মুল মুমিনীন হযরত সফিয়া বিনতে হুয়াই বিন আখতার বর্ণনা করেন, আমি আমার বাবা (ইহুদী সরদার হুয়াই) ও চাচার কাছে অন্য সব সন্তানের চেয়ে বেশী প্রিয় ছিলাম। তারা উভয়ে সব সময় আমাকে সাথে সাথে রাখতেন। রসূল সা. যখন মদিনায় এসে কোবায় অবস্থান করতে লাগলেন, তখন আমার বাবা হুয়াই বিন আখতার ও চাচা ইয়াসার বিন আখতার খুব ভোরে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। সূর্যাস্তের সময় ফিরে এলেন। মনে হলো, তারা খুবই ক্লান্ত ও অবসন্ন। তারা খুব ধীর গতিতে চলছিলেন। আমি অভ্যাস মত মুচকি হেসে তাদের সামনে গেলাম। কিন্তু ক্লান্তির কারণে তারা আমার দিকে ভ্রুক্ষেপই করলো না। আমার চাচা আবু ইয়াসার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলো, “কি হে, ইনিই কি সেই (প্রতিশ্রুত নবী) ব্যক্তি?” বাবা বললেন, “হাঁ, আল্লাহর কসম।” চাচা আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তাঁকে চিনে ফেলেছ? তুমি কি নিশ্চিত?” বাবা বললেন, হাঁ। চাচা জিজ্ঞেস করলেন, “এখন তাঁর সম্পর্কে তোমার মনোভাব কি?” বাবা বললেন, “শুধুই শত্রুতা। যতদিন বেঁচে আছি, খোদার কসম, শত্রুতাই করে যাবো।”
এই ছিল ইহুদীদের আসল মানসিকতা। তারা খুব ভালো করেই জানতো যে, তাদের কাছে যিনি এসেছেন তিনি সত্যের আহ্বায়ক এবং নবী। তাঁর প্রতিটি কথা তার সত্যতার সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর সমগ্র চরিত্র তাঁর মর্যাদাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। তাঁর চেহারা তাঁর নবুয়তের লক্ষণ প্রতিফলিত করছে। তারা শুধু জানতো ও বুঝতো তা নয়, বরং গোপন বৈঠকে তা মুখ দিয়ে স্বীকারও করতো। কিন্তু ঈমান ও আনুগত্যের পথ অবলম্বন না করে তারা বিরোধিতা ও শত্রুতার জন্য কৃতসংকল্প হতো। এটাই ছিল ইহুদীদের চিরাচরিত স্বভাব। সূর্য উঠলে যে আলোর বান ডাকে তা কে না জানে। মানুষ ও জীবজন্তুর চোখ আছে, তাই তারা এ দৃশ্য দেখতে পায়। কিন্তু যে ঘাসপাতার চোখ নেই, তারাও টের পায় যে, প্রত্যেক অন্ধকার রাতের শেষে যে ঘটনা প্রতিদিন ঘটে থাকে, তা ঘটে গেছে। এমনকি তাপ, উষ্ণতা, মাটির নিষ্প্রাণ কণাগুলো, পানির ফোঁটাগুলো এবং বাতাসের ঝাপটাগুলোও জেনে ফেলে যে, আলোর বার্তাবাহক আবির্ভূত হয়েছে। সূর্যোদয় এমন এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা যে, চামচিকে ও বোবা পর্যন্ত তা জেনে ফেলে। কিন্তু তাদের স্বভাবের বক্রতা এই যে, রোদ ওঠার পর আর সব জীব জানোয়ারের চোখ খুলে যায়, কিন্তু পেঁচা ও চামচিকের চোখ বন্ধ হয়ে যায়। উপরন্তু তাদের জন্য সূর্যোদয়ের আলামতই হয়ে থাকে সূর্য রশ্মিতে তাদের চোখ ঝলসে যাওয়া ও বুজে যাওয়া। মানুষ এত অন্ধ হতে পারেনা যে, তাঁর সামনে আল্লাহর নবীগণ অলৌকিক পর্যায়ের জ্ঞান ও চরিত্র নিয়ে আবির্ভূত হবেন এবং সে অনুভবই করবেনা যে, কোন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেছে। এসব লোক দেখে, জানে, বোঝে এবং এ সব কিছুর পরও চোখ বন্ধ করে রাখে। তারপরও যদি আলো চোখের ভিতর প্রবেশ করে, তবে চোখের ওপর পত্তি বেঁধে নেয়; হাত দিয়ে ঢেকে নেয়, মুখ বালুতে লুকায়, কক্ষের দরজা জানালা বন্ধ করে তাঁর ওপর কালো পর্দা ফেলে দেয়। প্রবাদ আছে যে, ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যায়, কিন্তু জাগ্রত ব্যক্তিকে জাগানো যায়না। অনুরূপভাবে, অজ্ঞ লোককে জ্ঞান দান করা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি জেনেও না জানার ভান করে, তাকে অজ্ঞতার জগত থেকে বের করে আনা সম্ভব নয়। ইহুদী জাতির অধিকাংশ এবং তাদের বড় বড় আলেমদের এই অবস্থাই হয়েছিল। কোরআনও তাদের এই বিকৃতির উল্লেখ করে বলেছে যে, ********
“অর্থাৎ তারা নিজের সন্তানদেরকে যেমন নিশ্চিতভাবে জানে ও চেনে, রসূল সা. কেও ঠিক তেমনি জানে ও চেনে।”
ইহুদী নেতারা রসূল সা. এর উচ্চ মর্যাদা ও সাধারণ মানুষরা তাঁর নতুন দাওয়াতের প্রতি ধাবমান হতে দেখে হিংসায় জ্বলতে থাকতো এবং তাদের হৃদয়ের জগতে ঘোরতর অসহিষ্ণুতা সংকীর্ণতা কেবল বৃদ্ধিই পেত।
কুতর্ক ও বাজে প্রশ্নের বাণ
বিকারগ্রস্ত ভণ্ড ধার্মিকদের মনে যখন কোন সক্রিয় দাওয়াত, কোন বিকাশমান আন্দোলন ও কোন মহান দাওয়াতদাতার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জন্মে যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা জোরদার হয়, তখন তারা বুঝ সৃষ্টিকারী আলাপ-আলোচনার দ্বার রুদ্ধ করে বিতর্কের পথ খুলে দেয়। বিতর্কের মাধ্যমে যে সব প্রশ্ন ও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি করা হয়, তা কখনো কোন কথা বুঝার উদ্দেশ্যে নয় বরং না বুঝার উদ্দেশ্যেই করা হয়। অন্য কথায়, ‘আমি মানবোনা’ এটাই হয়ে থাকে তাদের বিতর্কের প্রেরণার উৎস। কিন্তু বিতর্কের উদ্দেশ্য কেবল এখানেই সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে সরলমতি জনসাধারণকে সত্যানুসন্ধানের স্বাভাবিক পথ হটিয়ে দিয়ে সন্দেহ সংশয়ের কবলে নিক্ষেপ করা, যাতে তারা সহজ সরল যুক্তি থেকে দূরে সরে গিয়ে জটিল তাত্বিক প্রশ্নের ফাঁদে আটকা পড়ে যায় এবং দাওয়াতের যৌক্তিক মূল্য ও নৈতিক প্রভাব যাচাই করার পরিবর্তে পেঁচালো সমস্যাবলীর কানাগলিতে ঘুরপাক খেতে থাকে। ভণ্ড আলেমরা নিজেদের সম্পর্কে তো পুরোপুরি আস্থাশীল থাকে যে, ইসলামী আন্দোলন তাদেরকে কখনো নিঃশেষ করতে পারবেনা। তাদের আশংকা থাকে সাধারণ মানুষদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া নিয়ে। তাই তাদেরকে তাদের সমর্থনের উপর বহাল রাখার জন্যে তারা বাঁকা বাঁকা প্রশ্নের বেড়ি তৈরী করে থাকে। ইহুদী ভণ্ড আলেমরাও এই কারসাজিতেই লিপ্ত ছিল।
আব্দুল্লাহ ইবনে সালামের ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে যাওয়ার পর ইহুদীরা সবার্ত্মকভাবে মনোযোগ দিল বিতর্ক সৃষ্টির দিকে। বাঁকা ও জটিল বাহাসের তীর নিক্ষেপ করতে লাগলো ইসলামী আন্দোলনের উপর। কিন্তু এই ন্যাক্কারজনক যুদ্ধের তৎপরতাও প্রকাশ্য ঘাঁটি থেকে নয়, বরং মোনাফেকদের গোপন ঘাঁটি থেকে চালু করা হলো। খোদাভীরুতার জমকালো পোশাকে আবৃত বহুরূপী লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের সম্মেলনগুলোতে যোগদান করতো এবং কথা প্রসংগে অত্যন্ত সরল ও নিরীহ গোবেচারার ভাব দেখিয়ে ঠোঁট উল্টিয়ে হরেক রকমের প্রশ্ন তুলতো।
এক বৈঠকে তারা রসূল সা. এর কাছে প্রশ্ন রাখলোঃ আল্লাহ যখন গোটা সৃষ্টিজগতকে সৃষ্টি করেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালাকে কে সৃষ্টি করেছে? দেখলেন তো মনের বক্রতা? ইহুদীরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে বলে দাবী করতো। তারা তাঁর নবীদের ওপর বিশ্বাসী এবং তাঁর কিতাবসমূহের নিশানবাহী ছিল। আল্লাহ ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে তারা আগে থেকেই ওয়াকিফহাল ছিল। অথচ ইসলাম যখন সেই আল্লাহর দিকেই আহ্বান জানালো, তখন আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মনে খুবই জটিল প্রশ্নের উদ্ভব হয়ে গেল। তাদের প্রশ্ন থেকে বাহ্যত মনে হতো যে, এই প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেলেই তাদের জন্য সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ খুলে যাবে। কিন্তু প্রশ্নের বক্রতা থেকে বুঝা যাচ্ছিল, হেদায়াত লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য নয়, বরং মানুষকে হেদায়াত থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য পালাবার পথ দেখানোই প্রকৃত উদ্দেশ্য। রসূল সা. এই বাঁকা প্রশ্নের জবাব খুবই সোজাভাবে দিলেন। অর্থাৎ খুবই সহজ সরল পন্থায় সূরা ইখলাস পড়ে শুনিয়ে দিলেনঃ “(হে মুহাম্মাদ) বল, আল্লাহ এক। তিনি অভাবশূন্য। তিনি কারো সন্তান নন এবং তাঁরও কোন সন্তান নেই। কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না।” (হায়াতে মুহাম্মদঃ মুহাম্মদ হোসেন মিশরী)
আসুন, আপনাকে আর একটা মজার মজলিশে নিয়ে যাই। ইহুদীদের কতিপয় নামকরা আলেম একবার রসূলের সা. বৈঠকে এলো এবং বললো, “আমাদের চারটে প্রশ্নের জবাব দিন। তাহলে আমরা আপনার দাওয়াতকে গ্রহণ করবো এবং আপনার আনুগত্য করবো।” রসূল সা. বললেন, “তোমাদের প্রতিশ্রুতির দায়দায়িত্ব তোমাদের ওপরই থাকলো, কী প্রশ্ন করতে চাও কর।” প্রশ্নগুলো সামনে আসার আগে পাঠক নিজেই একটু ভাবুন তো যে, ইসলামী আন্দোলনের যথার্থ রূপ অনুধাবন করার জন্য বুদ্ধিমান লোকদের পক্ষ থেকে কী ধরনের প্রশ্নের আশা করা উচিত। তাদের উচিত ছিল মৌলিক তত্ত্ব সমূহ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা, ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধ সমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাস্তবায়ন পদ্ধতি জানতে চাওয়া। মুসলমান হতে হলে কী কী করা উচিত জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু এসব জিনিসের প্রতি তাদের কোন আকর্ষণই ছিলনা। তারা নিজেদের জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার বাহাদুরি জাহির করার জন্য একে একে নিম্নের প্রশ্নগুলো তুলে ধরলোঃ
১-শিশুরা পিতার বীর্য দ্বারা তৈরী হওয়া সত্বেও দেখতে মায়ের মত হয় কেন?
২-রসুল সা. এর ঘুম কেমন হয়?
৩-ইসরাঈল (এয়াকুব আলাইহিস্ সালাম) কোন্ কোন্ জিনিসকে নিজের জন্যে হারাম করে নিয়েছিলেন এবং কেন?
ইসলামী আন্দোলন সঠিক কিনা তা যাচাই করার জন্যই নাকি এ প্রশ্নগুলো তোলা হয়েছিল। কেবল চতুর্থ প্রশ্নটার কিছুনা কিছু সম্পর্ক সরাসরি ইসলামী দাওয়াত ও আন্দোলনের সাথে ছিল। কিন্তু এরও প্রকৃতি একই ছিল। চতুর্থ প্রশ্নটা ছিলঃ রূহ কি?
রসূল সা. শান্তভাবে প্রতিটা প্রশ্নের জবাব দিলেন। শেষ প্রশ্নের জবাবে বললেন, তোমরা ভালো করেই জান যে, রূহ হচ্ছে জিবরীল এবং তিনিই আমার কাছে আসেন।
পাঠক হয়তো আশা করছিলেন যে, এই জবাবগুলো পাওয়ার পর তারা তাদের হৃদয়কে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। না, কখখনো নয়। রসূল সা. এর শেষ কথাটা শুনে তারা বললো, “কিন্তু হে মুহাম্মাদ সা., জিবরীল তো আমাদের শত্রু। সে যখনই আসে, আমাদের জন্য খুব খারাবীর বার্তা নিয়ে আসে।” এ কথার অর্থ এই যে, জিবরীল যখনই আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর দ্বীনের পতাকাবাহী হবার দাবী নিয়ে আসেন, তখনই একটা দ্বন্দ্ব-সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে, নানা রকমের ক্ষয়ক্ষতি হয়, এমনকি পরিস্থিতি জেহাদ পর্যন্ত গড়ায়। তাঁর সাথে আমাদের বনিবনা নেই। এই ফেরেশতার শত্রুতা যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে আমরা নির্ঘাত আপনার সহযোগী হয়ে যেতাম এবং আপনার অনুকরণ ও অনুসরণ করতাম। অর্থাৎ কিনা, দাওয়াত, আন্দোলন এবং বার্তা- সবই সঠিক। কিন্তু এর পটভূমিতে আল্লাহ যে ফেরেশতাকে জড়িত করেছেন, তাতেই আমাদের নিরাপত্তা বিনষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই ঐ জিবরীল যেখানে আছে, সেখানে আমরা আসতে পারিনা।
রসূল সা. কোরআনের ভাষায় এর এমন জবাব দিলেন, যারা তা শুনেছে, তারা কখনো তা ভুলতে পারবেনা। তিনি বললেন, “বল, (হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ব্যক্তি জিবরীলের শত্রু হবে, সে যেন জেনে রাখে, কোরআনকে আল্লাহ নিজের আদেশের আওতায় তোমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে নাযিল করেছেন। এই কোরআন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থসমূহের সমর্থন করে এবং মুমিনদের জন্য (শত্রুতা, বিপদমুসিবত বা খুনখারাবীর বার্তা নয় বরং) হেদায়াত ও সুসংবাদবাহী। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
আরো একটা বিতর্কের সূত্রপাত হলো, রসূল সা. কোন এক প্রসঙ্গে নবীদের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে হযরত সোলায়মান আ. এর বিষয়টা উত্থাপন করলেন। এ নিয়ে ইহুদী মহলে অনেক কথা হলো। বলা হতে লাগলো, মুহাম্মাদ সা. এর আশ্চার্য কথা শুনেছ? সে বলে যে, দাউদের ছেলে সোলায়মানও নাকি নবী ছিল। আরে, আল্লাহর কসম, সে তো নিছক একজন যাদুকর ছিল (নাউযুবিল্লাহ)। কোরআন তাদের এইসব প্রলাপোক্তি খণ্ডন করে বলেছে, যাদু তো কুফরি। হযরত সোলায়মান কুফরীতে লিপ্ত হননি। ব্যাবিলনের কূয়া সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে, সেতো কেবল শয়তানের কারসাজি। (সীরাতে ইবনে হিশাম)
কেবলা পরিবর্তন
ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক যুগে ইহুদীরা এমন অনেকগুলো লক্ষণ দেখতে পেয়েছিল, যার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে আশা জন্মে গিয়েছিল যে, ধীরে ধীরে এই ঐতিহাসিক শক্তি তাদের মুঠোর মধ্যে চলে যাবে। কোরআনে বনী ইসরাঈলের বিশ্বজোড়া মর্যাদার উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, “আমি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।” তাছাড়া কোরআনে তাদের নবীদের নবুয়ত ও তাদের পবিত্র গ্রন্থের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়েছে। তাদেরকে ‘এস, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সর্ব সম্মত একটা বক্তব্যের দিকে’ এই আহ্বান জানানোর মাধ্যমে দ্বীনের কেন্দ্রীয় তত্ত্বকে উচ্চকিত করা হয়েছিল।
এ ছাড়া, রসূলুল্লাহ সা. মোশরেকদের রীতিনীতির মোকাবিলায় ইহুদীদের কিছু কিছু রীতিনীতিকে পসন্দ করতেন, যেমন মোশরেকরা চুলের একটা গোছা বড় করে রাখতো, কিন্তু ইহুদীরা এটা রাখতোনা। এ ক্ষেত্রে তিনি মোশরেকদের বিরোধিতা ও ইহুদীদের পক্ষাবলম্বন করেন। যে সব ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ আসতোনা, সে সব ব্যাপারে রসূল সা. ইহুদী ও খৃষ্টানদের নীতি অনুসরণ করতেন। (বোখারী, পোশাক সংক্রান্ত অধ্যায়) মদিনার ইহুদীরা আশুরার দিন রোযা রাখতো। রসূলও সা. ঐ দিন রোযা রাখতেন এবং মুসলমানদের জন্যও রোযা রাখা পসন্দ করতেন। কোন ইহুদীর লাশ সৎকারের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। সবোর্পরি, মুসলমানদের নামাযের কেবলা ছিল বাইতুল মাকদাস। এ সব জিনিস সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতো যে, ইসলাম মোশরেকদের চেয়ে আহলে কিতাবের নিকটতম ছিল। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ইহুদী ধর্মের মূল কাঠামোকে তো ইহুদীদের স্বার্থপর ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক নেতারা সম্পূর্ণরুপে বিকৃত করে ফেলেছিল। আর সেই বিকৃত কাঠামোটাও হয়ে গিয়েছিল নিষ্প্রাণ। অথচ হযরত মূসা আ. যে ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন তা ছিল অবিকল ইসলাম। অন্য সকল নবীও ইসলামেরই বাহক, আহ্বায়ক ও প্রচারক ছিলেন। কেবল প্রত্যেক নবীর আমলে শরীয়তের বিধানে সামান্য কিছু কিছু পার্থক্য থাকতো। মুহাম্মাদ সা. সেই একই ইসলামকে সারা দুনিয়ার সামনে পেশ করেছিলেন। শুধু তত্ত্ব হিসাবেই পেশ করছিলেন না, বরং বাস্তব আইন ও বিধানের আকারে তা কার্যকরও করেছিলেন। এই তাত্ত্বিক সম্পর্কটার কারণেই রসূল সা. নিজেও আশাবাদী ছিলেন যে ইহুদীরা ইসলামী তৎপরতাকে পর্যায়ক্রমে বুঝতে পারবে, বুঝার সাথে সাথে স্বাগতও জানাবে এবং এ কাজকে নিজেদেরই করণীয় কাজ বলে গণ্য করবে। তারা একদিন এজন্য আনন্দিত হবে যে, আল্লাহর নামে পতাকা ওড়ানো হচ্ছে, নবীদের শেখানো চারিত্রিক নীতিমালার ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামষ্টিক জীবন গড়ে উঠছে এবং তাওরাতের শরীয়তের মৌলিক মূল্যবোধগুলোকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। এই আশাবাদের ভিত্তিতেই কোরআন স্বীয় দাওয়াতকে এভাবে পেশ করেছে যে, তার কাছে দলীয় ও গোষ্ঠীগত পরিচয়ের কোন গুরুত্ব নেই, বরং আসল গুরুত্ব হলো নীতি ও কর্মের তথা আদর্শ ও চরিত্রের এবং আকীদা ও আমলের। কোন ব্যক্তি চাই সে ইহুদী হোক, খৃষ্টান হোক, নক্ষত্র পূজারী হোক, কিংবা মুসলমান হোক, সে যদি আল্লাহ, আল্লাহর বিধান, তার নবীদের দাওয়াত ও কেয়ামতের দিনের হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহীর প্রতি যথাযথভাবে ঈমান আনে, এবং তারপর নিজের গোটা জীবনকে সৎকর্মশীল জীবনে পরিণত করে দেখিয়ে দেয়, তাহলে এটাই সত্যিকার কাংখিত ও বাঞ্ছিত জিনিস। নাম নয় বরং কাজই আসল বস্তু। সাইনবোর্ড নয়, নির্ভেজাল পথই আসল বাঞ্ছিত জিনিস। কে কার সাথে সম্পর্ক রাখে, কে কার দল বা গোষ্ঠীর লোক, তা আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়। আসল বিবেচ্য বিষয় হলো, কার চরিত্র কেমন, এবং মানবতার সম্মিলিত কল্যাণ কভাবে নিশ্চিত করা যায়। কিন্তু ইহুদীদের দিক থেকেও যেমন ইসলামী আন্দোলনের আশা পূরণ হয়নি, তেমনি ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকেও ইহুদীদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি।
এই টানাপোড়েনের মধ্যেই সহসা ইসলামী আন্দোলনে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গেল। এই পরিবর্তন ছিল কেবলা পরিবর্তনের ঘটনা। প্রত্যেক যুগে ইসলামী আন্দোলনের মূল স্বভাব এই ছিল যে, সে নিজের অস্তিত্বের স্বতন্ত্র বৈশিষ্টকে বহাল রাখতে চায় এবং প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে আদর্শিক ও আকীদাগত স্বকীয়তাকে জীবিত রাখতে বদ্ধপরিকর। মক্কায় থাকতে এই উদ্দেশ্যেই বাইতুল মাকদাসকে কেবলা বানানো হয়েছিল, যাতে ইসলামী আদর্শের পতাকাবাহী দল নিজের স্বতন্ত্র মর্যাদা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকে। এর ফলে হিযরত পর্যন্ত দীর্ঘকাল ব্যাপী মুসলমানরা মোশরেকদের মোকাবেলায় নিজেদের স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তাকে পুরোপুরিভাবে অনুভব করে। মোশরেকরাও বুঝতে পেরেছিল যে, তারা ও মুসলমানরা সম্পুর্ন আলাদা আলাদা দুটো আদর্শের ধারক ও বাহক। এই চেতনা ও অনুভূতিকেই “তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম” এই সংক্ষিপ্ত বাক্যটির মধ্য দিয়েই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, এতে স্পষ্টভাবেই বলে দেয়া হয়েছে, তোমাদের পথ আলাদা, আমাদের পথ আলাদা। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন মিলই নেই।
মদিনায় চলে আসার পর মুসলমানদের স্বকীয়তা যদি কোন দিক থেকে বিপন্ন হবার আশংকা থেকে থাকে, তবে তা ছিল সেখানকার ইহুদী ও খৃষ্টান গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। এখানে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল ইহুদী ও খৃষ্টানদের নিষ্প্রাণ ধর্মের মিশ্রণ থেকে ইসলামী আন্দোলনের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্যকে সুরক্ষিত করার এবং মুসলিম সমাজকে ইহুদী সমাজে মানসিকভাবে বিলীন হয়ে যাওয়ার কবল থেকে রক্ষা করার। মক্কী যুগে বাইতুল মাকদাসকে অস্থায়ীভাবে কেবলা বানানোর যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, এখানে সে প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের হৃদয়ের সম্পর্ক হযরত ইবরাহীম আ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেবলার প্রতিই ঘনিষ্ঠতর ছিল। রসূল সা. স্বয়ং হযরত ইবরাহীমেরই বংশধর ছিলেন এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রাথমিক সংগ্রামীরাও ছিলেন এই বংশেরই লোক। স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সেই অস্থায়ী ব্যবস্থা তখন নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই রসূলের সা. সত্যাভিষ্ট মন এই পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষমান ও উদগ্রীব ছিল।
আসলে কেবলা পরিবর্তনের আদেশ জারী করার মধ্য দিয়ে মহান আল্লাহ বনী ইসরাঈলকে বিশ্ব নেতৃত্ব থেকে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করলেন। তাদের শূণ্য পদে উম্মতে মুহাম্মদীকে নিয়োগ দান করলেন। গোটা বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত তৎপরতার যে কেন্দ্র এতদিন বাইতুল মাকদাসে ছিল, এখন তা কা’বা শরীফে স্থানান্তর হলো। মুসলমানদেরকে আখ্যায়িত করা হলো মধ্যপন্থী অর্থাৎ বিশ্ব ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় জাতি। তার ওপর অর্পণ করা হলো মানব জাতির সামনে সত্যের সাক্ষ্যদানের গুরু দায়িত্ব এবং সমগ্র মানবজাতির নেতৃত্ব।
মদিনায় হিজরতের পর ষোল মাস পর্যন্ত বাইতুল মাকদাসের দিকে মুখ করে নামায পড়া হতে থাকে। হিজরী দ্বিতীয় বর্ষের রজব কিংবা শা’বানের ঘটনা। ইবনে সা’দ বর্ণনা করেন যে, রসূল সা. বিশর বিন বারা ইবনে মারূরের রা. বাড়ীতে দাওয়াতে গিয়েছিলেন। সেখানে যোহরের নামাযের সময় হলে তিনি জামায়াতের ইমামতি করতে দাঁড়িয়ে গেলেন। দু’রাকাত পড়ানো হলো। তৃতীয় রাকাতে ওহী যগে নিম্নের আয়াত নাযিল হলোঃ
“আমি আকাশের দিকে তোমার মুখ তোলা দেখে থাকি। কাজেই তুমি যে কেবলা পসন্দ কর, সেদিকেই তোমাকে ফেরাচ্ছি। অতএব, তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফেরাও। এখন তুমি যেখানেই থাক, ঐ দিকেই মুখ করে নামায পড়।” (সূরা বাকারাঃ১৪৪)
এ আদেশ শোনা মাত্রই আল্লাহর সবচে অনুগত বান্দা নামাযের মধ্যেই কা’বার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর তাঁর সাথে সাথেই তাঁর অনুসারী নামাযীরা সবাই নতুন কেবলার দিকে মুখ ফেরালেন। বাইতুল মাকদাস মদিনা থেকে সোজা উত্তরে এবং মক্কা দক্ষিণে অবস্থিত। নামাযের মাঝখানে কেবলা পরিবর্তনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, ইমামকে মুক্তাদীদের সামনে থেকে সোজা পেছনের দিকে চলে আসতে হয়েছিল এবং নামাযীদের কাতারকে সোজা পেছনের দিকে ঘুরে যেতে হয়েছিল। এরপর মদিনা ও তার পার্শবর্তী পল্লীগুলোতেও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলো। বারা বিন আযের রা. বর্ণনা করেন যে, এক মসজিদে লোকেরা যখন রুকুতে ছিল, তখন এ খবর পৌঁছে। তারা খবর শোনামাত্রই ঐ অবস্থায়ই কা’বার দিকে মুখ ফেরালেন। আনাস বিন মালেকের বর্ণনা অনুসারে বনু সালামা গোত্রে পরদিন ফজরের নামাযের সময় খবর পৌঁছে, লোকেরা এক রাকাত পড়ে দ্বিতীয় রাকাতে ছিল। এই সময় ঘোষকের ঘোষণা শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাত সবাই নতুন কেবলার দিকে মুখ ঘুরায়। (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারাঃ টীকা ১৪৬)
এই পরিবর্তনে যে হৈ চৈ আসন্ন হয়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে কোরআন আগে ভাগেই মুসলমানদের সাবধান করে দেয়ঃ “অচিরেই অজ্ঞ লোকেরা অপপ্রচারের তাণ্ডব সৃষ্টি করবে যে, মুসলমানরা কোন কারণে কেবলা পরিবর্তন করলো?” নানা রকমের প্রশ্ন তোলা হবে, অদ্ভুত ধরনের মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে এবং পারস্পরিক জাতিগত সম্পর্কের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। মুসলমানরা যাতে আসন্ন অপপ্রচারের তাণ্ডবের সামনে জোরালো অবস্থান নিয়ে দাঁড়াতে পারে, সে জন্য কোরআন তাদেরকে কেবলা পরিবর্তনের তাৎপর্য পূবার্হ্নেই বুঝিয়ে দিল। সে জানিয়ে দিল যে, শুরুতে বাইতুল মাকদাসকে কেবলা বানানোর উদ্দেশ্য ছিল আরব জাতীয়তাবাদের মূর্তি ভেঙ্গে চুরমার করা। কেননা আরবরা নিজেদের জাতিগত বৃত্তের বাইরে কোন জিনিসের কোন গুরুত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। আর এখন বাইতুল মাকদাস থেকে কা’বার দিকে মুখ ঘুরানোর উদ্দেশ্য ইসরাইলী আভিজাত্যের মূর্তিও ভেংগে গুড়িয়ে দেয়া। একটা কাজ আগে করা হয়েছিল। দ্বিতীয় কাজটা এখন করা হলো। আরব জাতীয়তাবাদের উপাসকরা আগেই ছাটাই হয়ে গিয়েছিল। এবার ইসরাইলী জাতীয়তাবাদের পূজারীদের ছাটাই হওয়ার পালা। এভাবে মোনাফেক নামক ঘুনের কবল থেকে সমাজ পবিত্র হয়ে যাবে। এরপর ইসলামী সমাজে শুধু তারাই টিকে থাকবে, যাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর আদেশ ও রসূলের সুন্নাহর গুরুত্ব সবার্ধিক। এক্ষণে ইসলামী আন্দোলন যে পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে, তা রসূল সা. এর একনিষ্ঠ আনুগত্যকারীদেরকে সমস্ত আদর্শহীন লোকের মিশ্রণ থেকে মুক্ত করবে। আর আদর্শহীনদেরকে সেই সব একনিষ্ঠ ঈমানদারদের থেকে ছাটাই করে দেবে, যারা বিশ্বাস করে যে পূর্ব ও পশ্চিম সবই আল্লাহর এবং আল্লাহই আনুগত্যের আসল কেন্দ্র বিন্দু যারা এই নিগুঢ় তত্ত্ব জানে যে, শুধু পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করাই আসল নেক কাজ নয়, বরং আসল নেক কাজ হলো শরীয়তের এই সব বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতার অভ্যন্তরে সক্রিয় আসল প্রাণশক্তি। এই প্রাণশক্তি হলো আল্লাহর ওপর, আখেরাতের ওপর, ফেরেশতাদের ওপর, আল্লাহর কিতাবের ওপর, ও তার নবীদের ওপর ঈমান আনা এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করা। সুতরাং তোমাদের কেবলার বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতা প্রতিষ্ঠায় যে জিনিস সবোর্চ্চ গুরুত্ব দিতে হবে, তা হলোঃ
ভালোকাজ এবং কল্যাণমূলক কাজের দিকে অগ্রসর হও, আল্লাহর বড় বড় বৈপ্লবিক ও পরিবর্তনকামী নির্দেশ পালনে কোন বিরোধী শক্তির ভয় পেয়না, ভয় পেয়ো শুধু আল্লাহকে।
কোরআন বিশ্ব বিধাতার আদেশ ঘোষণা করার সময়েই বলে দিয়েছিল যে, এ ঘটনা দৃঢ় প্রত্যয়ী মুমিনরা ব্যতিত সবার কাছেই কঠিন ও কষ্টকর লাগবে। এ নিয়ে যখন গোলযোগ সৃষ্টি হবে, তখন অনেকে ঘাবড়ে যাবে। প্রত্যেক অলিগলিতে যখন বিতর্ক ছড়িয়ে পড়বে, তখন দূবর্ল লোকদের মাথায় চক্কর দেবে এবং তাদের আবেগে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হবে। এবার শুনুন কেবলা পরিবর্তন নিয়ে যে সব মন্তব্য করা হয়েছিল তার কিছু নমুনা।
মোশরেকরা বললো, ঐ দেখ, এবার মুহাম্মাদ সা. ও তার দলবলের কিছুটা চেতনা ফিরে এসেছে। আমাদের কা’বাকে এবার যখন কেবলা হিসেবে গ্রহণ করেছে তখন ওরা ধীরে ধীরে আমাদের ধর্মেও ফিরে আসবে।
ইহুদীরা বললো, ইসলামের নেতা আমাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আক্রোশে এতই বেসামাল হয়ে গেছে যে, নবীদের কেবলা পর্যন্ত পরিত্যাগ করেছে। সে যদি নবী হতো তাহলে এই কেবলাকে পরিত্যাগ করতোনা।
মোনাফেকরা বলতে লাগলো, ‘কিছুই বুঝে আসছেনা মুহাম্মাদের সঠিক কেবলা কোনটা। কেবলা নিয়ে যেন খেলা শুরু হয়েছে। যেদিকে মন চায়, সেদিকেই মুখ ফেরানো হয়। দেখে শুনে মনে হচ্ছে পুরো ইসলাম ধর্মটাই যেন ইচ্ছের খেলা।’
আর যারা পাক্কা ঈমানদার ছিল, তারা বললো, আমরা আদেশ শুনেছি, তার আনুগত্য করেছি এবং আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। এ সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এসেছে। (যাদুল মায়াদ, ২য় খণ্ড)
শেষোক্ত এই ঈমানদারদের দলটাই অপপ্রচারের ঝরের কবলে পড়ে গেল। চারদিক থেকে প্রশ্ন, কূটতর্ক এবং ব্যংগ বিদ্রুপের বান নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো। প্রত্যেক মজলিসে একই আলোচনা, প্রত্যেক অলিতে গলিতে জটলা পাকিয়ে একই কানাঘুষা এবং প্রতি মূহুর্তে উত্তেজনাকর বাগবিতণ্ডা চলছিল। যে কোন বিপ্লবী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটা স্বাভাবিক। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের এবং জনসাধারণের চিরাচরিত ধ্যান ধারণার বিপরীত প্রতিটি পদক্ষেপে এ ধরনের হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে তাদের কর্মীরা ঘাবড়ে গিয়ে ও দিশেহারা হয়ে অনেক সময় উত্তেজনার পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এই আশংকার পরিপ্রেক্ষিতেই উপদেশ দেয়া হলো, এ সব সংকটজনক পরিস্থিতি অতিক্রম করার জন্য ধৈর্য ও নামাযই সবোর্ত্তম পন্থা। অপপ্রচারকারীদের সম্পর্কে বলা হলো, সত্য অনুসন্ধান করা কখনো তাদের লক্ষ্য নয়। যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা তারা কখনো পরিতৃপ্ত ও শান্ত হবার নয়। তাদের প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কেবল বিব্রত করা। তোমরা যতক্ষণ তোমাদের আদর্শ ও মূলনীতি ত্যাগ করে তাদের অনুসারী না হবে, ততক্ষণ তারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।
অর্থহীন কূটতর্কের জবাবে চূড়ান্ত যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের দায়িত্ব ইসলামী আন্দোলনের কাঁধের ওপর অর্পিত ছিল। সে দায়িত্ব পালন করার জন্য অত্যন্ত ধারালো ও অকাট্য যুক্তি উপস্থাপন করা হলো এবং জনগণের সামনে পবিত্র কা’বার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সূরা আল ইমরানের এক জায়গায় ব্যাখ্যা করা হলো। এরশাদ করা হলোঃ
“মানব জাতির জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রথম এবাদতের স্থান হলো মক্কায় অবস্থি সেই ঘর, যাকে বরকত ও কল্যাণ দান করা হয়েছে এবং যাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতের কেন্দ্র বানানো হয়েছে। এতে প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। সেখানে ইবরাহীমের এবাদতের জায়গাও রয়েছে। সেখানে যে একবার প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি এই ঘরের কাছে পৌঁছার সামর্থ রাখে, তার সেখানে গিয়ে হজ্জ আদায় করা কর্তব্য। আর যে ব্যক্তি এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করে, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ সারা দুনিয়াবাসী থেকেই মুখাপেক্ষাহীন।” (আয়াত ৯৬-৯৭)
বাইতুল মাকদাস সম্পর্কে এ তথ্য বাইবেল থেকেই জানা গিয়েছিল যে, হযরত মূসার সাড়ে চারশো বছর পড় হযরত সোলায়মান তা নির্মাণ করিয়েছিলেন। হযরত সোলায়মানের শাসনামলেই তাকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়। পক্ষান্তরে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উভয় প্রকারের সবর্সম্মত বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, কা’বা শরীফকে হযরত ইবরাহীম আ. হযরত মূসারও আট/নয় শো বছর আগে নির্মাণ করেছিলেন। কা’বা শুধু সময়ের দিক থেকেই জ্যেষ্ঠ নয়, বরং তার পবিত্র পরিবেশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনাবলীও রয়েছে। এর সাথে ইসলামের অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহ্য জড়িত রয়েছে। তার প্রতিটি প্রান্তরে উৎকীর্ণ রয়েছে সত্য ও ন্যায়ের পতাকা সমুন্নত করার ইতিহাস। তা ছাড়া এতে হযরত ইবরাহীমের এবাদতের উপকরণও সংরক্ষিত রয়েছে। এ স্থান আজও তাওহীদী প্রেরণার উৎস। এবাদতের এই কেন্দ্রভূমি যে আল্লাহর কাছেও গৃহীত ও মনোনীত, তার অকাট্য প্রমাণ এইযে, উষর মরুর অভ্যন্তরে নির্মিত এই ঘরের আশপাশে বিশাল এক মনুষ্যবসতি গড়ে উঠেছে এবং লোকেরা এখানে অনেক দূর দূর থেকে এসে থাকে। এর উচ্চ মর্যাদার আরো একটা উজ্জ্বল প্রমাণ এই যে, এই তরুলতাহীন উষর মরুবাসীদের কাছে আপনা থেকেই সব ধরনের জীবিকা পৌঁছে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, আরবের জংগী বেদুঈন সমাজে এই পবিত্র ঘর চার হাজার বছর ধরে শান্তি ও নিরাপত্তার একটা দ্বীপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এর নিরাপত্তা বেষ্টনীতে যেই প্রবেশ করুক, তার জান মাল ও ইজ্জত নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে রক্ত পিপাসু লোকেরা পর্যন্ত এই ঘরের ছায়ায় এসে তরবারী কোষবদ্ধ করে ও আক্রোশের আগুন নিভিয়ে ফেলে। খুনী ও ডাকাত এর বেষ্টনীতে প্রবেশ করা মাত্রই শান্তি প্রিয় নাগরিক হয়ে যায়। তাই ইবরাহীম আ. এর দাওয়াত নিয়ে ময়দানে নামা যে কোন আন্দোলনের আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হওয়া এই ঘরেরই ন্যায্য অধিকার। এতে ধর্ম বা যুক্তির পরিপন্থী কোন জিনিসটা হয়েছে যে, তা নিয়ে অলিগলিতে এত কানাঘুষা চলছে?
এই যুক্তির ফলে কোন সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে থাকলে তা নেয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে। ইহুদীরা কেবলা পরিবর্তনকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটা চূড়ান্ত বৈরী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করেছিল। কেননা এর কারণে তাদের সকল আশা ভরসা খতম হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদেরকে বাগে আনা যাবে বলে তারা যে স্বপ্ন দেখেছিল, সে স্বপ্ন নস্যাত হয়ে গিয়েছিল। তারা বুঝতে পারলো, মুসলমানদেরকে বশে আনা সহজ নয়। অপরদিকে মুসলমানরাও ইহুদীদের মনের সমস্ত ক্লেদ স্পষ্ট দেখতে পেল। তাদের মানসিকতার সমস্ত অন্ধকার দিক তাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল। এত ঘৃণ্য মানসিকতা যাদের, তাদের সাথে সেই ভালো ধারণা পোষণ করা সম্ভব নয়, যার ভিত্তিতে তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মুসলমানরা পরিষ্কার বুঝে নিল যে, মদিনাতেও ইসলামী আন্দোলনকে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই টিকে থাকতে হবে। ধর্ম ও খোদাভীরুতার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন সাহায্য ও সহযোগিতা লাভের আশা করা বৃথা। বরঞ্চ দিন দিন এই আশংকা ঘনীভূত হতে লাগলো যে, ইহুদীরা মক্কার কাফের ও মোশরেকদের চেয়েও জঘন্য মানসিকতা নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের পথ আগলে ধরবে। কিন্তু এ আশংকা স্বত্ত্বেও রসূল সা. ও তাঁর সাহাবীদের আচরণে সব সমেয় ইসলামের আহ্বায়ক সুলভ নৈতিকতার মান বজায় রইল। যে যেমন, তাঁর সাথে তেমন আচরণ ইহুদী মোনাফেক ও অন্যান্য বৈরী শ্রেণীর লোকদের সাথে করা হয়নি। কূটতর্ক, ব্যংগ বিদ্রুপ ও ইতরসুলভ আচরণের মোকাবেলায় মুসলমানরা হার মানতো। কোন কথা বলতে হলে ভদ্রজনোচিত পন্থায় ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কেবল যুক্তিযুক্ত কথা বলেই তারা ক্ষান্ত থাকতেন। তাদের বাড়াবাড়িকে উদার মনোভাব নিয়ে ধৈর্য ও উদারতার সাথে গ্রহণ করতেন।
কিন্তু তা স্বত্ত্বেও মনের মধ্যে এ যাবত আটকে থাকা উত্তেজনা বাঁধভাঙ্গা বন্যার মত বেরিয়ে পড়তো।
অসভ্যপনা ও ইতরামি
যাদের কোন গঠনমূলক লক্ষ্য উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী থাকেনা, তারা সাধারণত অন্য কাউকেও কোন গঠনমূলক কাজ করতে দেয়না। এর কারণ শুধু এই যে, এতে দুনিয়াবাসীর সামনে তাদের অসারতা প্রমাণিত হয়। মদিনার ইহুদীদের অবস্থাও ছিল এরূপ। তারা দীর্ঘকাল মদিনায় অবস্থান করে আসছিল। কিন্তু নিম্নস্তরের মানুষদের নৈতিক মানোন্নয়নের জন্য তারা কোন কাজ করার যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। মানুষের মন মানসিকতার উন্নয়ন, চরিত্র সংশোধন, ভদ্রতা ও শৃংখলার প্রশিক্ষণ দান, এবং শান্তি ও নিরাপত্তামূলক জীবন যাপনের শিক্ষা দানে তারা কোন পদক্ষেপই নেয়নি। পতিত মানবতাকে সামাল দেয়া দূরে থাক, তারা নিজেদেরকেও অধোপতন থেকে রক্ষা করতে পারেনি। দুনিয়ার যাবতীয় সামাজিক ও নৈতিক ব্যাধি তাদের মেরুমজ্জায় ঢুকে গিয়েছিল এবং কোন রোগেরই চিকিৎসার ব্যবস্থা তারা করতে পারেনি। এমতাবস্থায় তাদের সামনে যখন একটা নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটলো এবং সেই শক্তি মানুষের মন মগজে প্রেরণাদায়ক নীতি, আদর্শ ও আকীদা বিশ্বাসের প্রদীপ জ্বালাতে শুরু করলো, সমস্ত সামাজিক ব্যাধির চিকিৎসা করে নব উদ্যমে নতুন জাতি গড়ার কাজ শুরু করলো এবং একটা পবিত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের উপযোগী করে ব্যক্তির চরিত্র গঠন ও সেই সব ব্যক্তির সাহায্যে একটা শান্তিপূর্ণ ন্যায়বিচারপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলার চেষ্টা শুরু করে দিল, তখন ইহুদীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। তারা এই গঠনমূলক আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য যে কোন হীন চেষ্টা তদবীর শুরু করে দিল। এ ধরনের নেতিবাচক ও নাশকতামূলক শক্তি যখন কারো বিরধিতায় বদ্ধপরিকর হয় তখন তা সভ্যতা, ভব্যতা ও ভদ্রতাকে শিকেয় তুলে রাখে। অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে অসভ্য ও অভদ্র আচরণ করা তার রপ্ত হয়ে যায়। ইহুদিরাও অনুরূপ চরম অসভ্য আচরণ শুরু করে দিল।
নবীদের উত্তরসূরি, আল্লাহর কিতাবের অনুসারী এবং আল্লাহর আইনের শিক্ষক ও ফতোয়াদাতা হিসাবে সুপরিচিত ইহুদী সম্প্রদায় শত্রুতা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে যে সব অপকর্ম ও অসদাচরণ করতে শুরু করলো, তার দুতিনটে অবিস্মরণীয় উদাহরণ এখানে উল্লেখ করা যাচ্ছে। নিজেদেরকে ছাড়া আর কাউকে ধার্মিক ও খোদাভীরু মনে করতোনা এই ইহুদী সম্প্রদায়। অথচ তাদের নৈতিকতার এমনই অবস্থা হয়েছিল যে, তারা যখন রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করতো, তখন ‘আসসালামু আলাইকুম’ এর পরিবর্তে ‘আসসামু আলাইকুম’ বলতো। এর অর্থ হলো, ‘তোমার মৃত্যু হোক।’ এই আচরণ করা হতো সেই মহান ব্যক্তির সাথে, যিনি হযরত ইবরাহীম, মূসা, ইয়াকুব, ইউসুফ, ইসহাক ও ইসমাঈল আ.-এরই আনীত দ্বীনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিলেন, যিনি তাওরাতের আসল প্রাণশক্তির পুনরুজ্জীবনে নিয়োজিত ছিলেন, যিনি আল্লাহর আইন ও বিধানকেই পুনপ্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামরত ছিলেন। বরং সত্য কথা এই যে, তিনি তো প্রকৃতপক্ষে ইহুদীদেরই ভুলে যাওয়া দায়িত্ব পালন করছিলেন, এবং তাদেরই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করছিলেন। একবার এদের কয়েকজন রসূল সা. এর বাড়ীতে এলে গুন্ডাপান্ডার ন্যায় আচরণ ও উপরোক্ত ভাষা ব্যবহার করে। এই অসদাচরণের বিরুদ্ধে হযরত আয়েশা পর্যন্ত পর্দার আড়াল থেকে কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি এতই রেগে যান যে, জবাব না দিয়ে থাকতে পারেননি। তিনি বলে অথেন, “হতভাগারা, তোদের মৃত্যু হোক।” রসূল সা. শুনতে পেয়ে বলেন, “আয়েশা, একটু নম্র হও।” হযরত আয়েশা বললেন, “আপনি শুনছেন ওরা কী বলেছে?” রসূল সা. বললেন, “আমি শুনেছি, তবে জবাবে শুধু বলেছি ‘ওয়ালাইকুম’ অর্থাৎ ‘তোমাদেরও’। এটুকুই যথেষ্ট”
অসভ্য আচরণের আরো দুটো লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত কোরআনে চিরদিনের জন্য সংরক্ষিত হয়েছে। লক্ষ্য করুনঃ
প্রথমত রসূল সা. এর দরবারে তারা হাজির হতো এবং আলাপ আলোচনার সময় যখনই এ কথা বলার প্রয়োজন বোধ করতো যে, ‘একটু থামুন, কথা বুঝার সুযোগ দিন’, তখন একটা দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ‘রায়িনা’ ব্যবহার করতো। আরবীতে এ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ হলো, ‘আমাদের একটু সুযোগ দিন, আমাদের বক্তব্য শুনুন, বা আমাদের দিকে একটু লক্ষ্য করুন’। কিন্তু ইহুদীদের মূল ধর্মীয় ভাষা ইবরানীতে এর কাছাকাছি ও প্রায় সম উচ্চারিত শব্দ এই অর্থ এই অর্থে ব্যবহৃত হত যে, ‘শোন, তুই বধির হয়ে যা’। তাছাড়া আরবীতেও এর প্রায় কাছাকাছি ধাতু থেকে তৈরী এবং প্রায় সম উচ্চারিত এমন শব্দ রয়েছে, যার খুবই খারাপ অর্থ বেরুতো। যেমন ‘রায়য়া’ থেকে নির্গত একটা শব্দ ছিল ‘আর রায়া’ যার অর্থ ‘নিকৃষ্ট মানুষ’। এ শব্দটাকে ‘রায়ায়েনা’ আকৃতিতে পরিবর্তন করা মোটেই কঠিন ছিলনা। (যার অর্থ দাঁড়াতো ‘আমাদের নিকৃষ্ট মানুষটি।’-অনুবাদক) অনুরূপভাবে ‘রায়ানা’ শব্দটি অজ্ঞ ও নিবোর্ধ হয়ে যাওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খোদ্ ‘রায়েনা’ শব্দটিকেও একটু জিহ্বা বাঁকিয়ে উচ্চারণ করলে ‘রায়িয়ানা’তে রূপান্তরিত করা যায়, যার অর্থ দাঁড়ায় ‘ওহে আমাদের রাখাল’। ইহুদীদের নেতৃস্থানীয় ধর্মীয় জুব্বা ও পাগড়িধারী লোকেরা এভাবে সুকৌশলে কটুবাক্যের তীর নিক্ষেপ করতো। সাধারণ মানুষ সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে এত দক্ষতা কোথায় পাবে। এটা তো বড় বড় দক্ষ আলেমদের কারসাজি। বাড়ী থেকে তারা ভালোমত চিন্তা গবেষণা করে প্রস্তুতি নিয়ে আসতো যে, আজ কি কি উপায়ে অসভ্য আচরণ করা যেতে পারে। এই সব ধড়িবাজ আলেমদের মধ্যে ‘যায়েদ বিন তাবুত’ নামক এক ব্যক্তি সম্পর্কে ইতিহাসে সুস্পষ্ট বিবরণ সংরক্ষিত রয়েছে। অনৈতিক ও অভদ্রজনোচিত বাক্যবান নিক্ষেপের ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে এই ইহুদী ভণ্ড মৌলবীও বিরাট অবদান রেখেছিল। বাহ্যত তারা খুবই ভদ্র ও মার্জিত আচরণের লেবেল আঁটা ছিল। কিন্তু তাদের অন্তরের গভীরে দৃষ্টি দিলে দেখা যেত, গুণ্ডাসুলভ মানসিকতা সক্রিয় রয়েছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে জানাজানি ছিল যে, আমরা এ যুগের সেরা মানুষটাকে ব্যংগ বিদ্রুপ করছি। কিন্তু কেউ যদি আপত্তি জানাতো তবে বলতো, আরে ভাই, আমাদের অভদ্র মনে করেছেন নাকি? আমরা তো যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আদবের সাথে কথা বলছি যে, আমাদেরকে একটু বুঝবার ও বুঝাবার অবকাশ দিন।
দ্বিতীয়ত, আলাপ আলোচনার মাঝখানে কখনো কখনো নবীদের উত্তরসূরি ইহুদী আলেমরা রসূল সা. এর সাথে এভাবে বাক্যালাপ করতোঃ ‘ইসমা’ গায়রা মুসমায়িন।’ এ কথাটার বাহ্যিক অর্থ হলো, “একটু শুনুন, আপনি এমন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি যে, আপনাকে আপনার ইচ্ছা বা অনুমতি ছাড়া কোন অথা বলা চলেনা।” কিন্তু তাদের কুচক্রী মানসিকতা এর অন্য একটা অর্থ বুঝাতো। সেটি হলো, “তুমি কোন কথা শোনানোর যোগ্যই নও। আল্লাহ যেন তোমাকে বধির করে দেয় এবং তোমার শ্রবণ শক্তিই যেন না থাকে।”
লক্ষ্য করুন, কত নোংরা ও ঘৃণ্য মানসিকতার অধিকারী লোকেরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিরোধে নেমেছিল।
তৃতীয়ত, মুমিনরা রসূল সা. এর বৈঠকে বসে যখন কোন কথা শুনতো এবং বুঝতো, তখন আল্লাহর নির্দেশে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে বলে উঠতো, “সামি’না ওয়া আতা’না’ অর্থাৎ আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য অবলম্বন করলাম।” কিন্তু তাওরাতের ধারক বাহকরা এরূপ ক্ষেত্রে অত্যন্ত নাটকীয় আচরণ করতো। প্রথমে জোরে শোরে বলতো ‘সামি’না অর্থাৎ জ্বী হা, শুনেছি।’ পরক্ষণে ‘আতা’না’ (আনুগত্য অবলম্বন করলাম)-এর পরিবর্তে একটু আসতে জিহ্বাটাকে একটু বাঁকিয়ে বলতো, ‘আসাইনা’ অর্থাৎ “তোমার আদেশ প্রত্যাখ্যান করলাম ও অমান্য করার সংকল্প নিলাম।” এখানেও সেই একই জটিলতা যে, কেউ আপত্তি তুললে বিরক্তি প্রকাশ করে বলতো, “আমাদেরকে তোমরা এতই বাজে লোক মনে করেছ? বিরোধিতার আতিশয্যে আমাদের ওপর এমন অপবাদ আরোপ করছ? তোমাদের নিজেদের মধ্যকার ছাড়া বাইরের আলেম ও বিজ্ঞজনদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কোন রেওয়াজ নেই? নিজেদের ছাড়া আর কাউকে তোমরা ভদ্র ও সদাচারী মনে করতে প্রস্তুত নও?”
ভেবে দেখার বিষয় হলো, এ ধরনের হীন আচরণ দ্বারা কি রসূল সা. এর আন্দোলনের কোন ক্ষতি সাধন করা গিয়েছিল? এ হীনতা ও নীচাশয়তার জোরে কি ইসলামী দলের অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করা গিয়েছিল? আসলে গালি ও কটূবাক্য বর্ষণ করে কোন গঠনমূলক শক্তির লোমও ছেড়া যায়না। প্রতিপক্ষ এতে শুধু এতটুকুই মজা পায় যে, তার নেতিবাচক, নাশকতামূলক ও গোঁড়ামিপূর্ণ মনের পুঞ্জীভূত বাষ্প বেরিয়ে যায়। এই সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যখন নবীজীর বৈঠকে এ ধরনের কীর্তিকলাপ সম্পাদন করে বিদায় হয়ে যেত, তখন নিজেদের বৈঠকে গিয়ে নিশ্চয়ই আস্ফালন করতো যে, আজ নবী সাহেবকে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে এসেছি। আপন মুরীদদের সমাবেশে বসে নিশ্চয়ই নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিত যে, আমরা একটা শব্দকে ওলট পালট করে কি সব অর্থ বের করেছি এবং আরোপ করেছি। আমাদের ভাষাজ্ঞান, ব্যাকরণ জ্ঞান এবং অলংকার শাস্ত্রীয় পারদর্শিতার বলে আমরা কত বড় বড় যুদ্ধ চালিয়ে এলাম।
ইহুদী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের এই সব অপকর্ম থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হলো, ধর্মীয় নেতারা যখন অধোপতনের শিকার হয়, তখন তাদের মধ্যে প্রধানত শাব্দিক বিকৃতির নোংরা ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত তাদের মধ্য থেকে মানবতা, ভদ্রতা, শালীনতা ও শিষ্ঠাচারের দাবী ও চাহিদা বিবেচনা করার ক্ষমতা লোপ পায়। তৃতীয়ত তাদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কর্মকাণ্ডের মাঝে লজ্জাজনক স্ববিরোধিতার জন্ম নেয়। চতুর্থত তাদের মধ্যে এক ধরনের কাপুরুষতা পাওয়া যায়, যার কারণে তারা খোলাখুলিভাবে তাদের মনের নোংরা ভাবাবেগ প্রকাশ করতেও পারেনা। বরং তারা নিজেদের নীচ ও কদর্য মানসিকতার ওপর শালীনতা ও ভদ্রতার লেবেল এঁটে চলে। এ আলামতগুলো যে কোন চিন্তাধারা ও মানসিকতার অকর্মণ্যতার অকাট্য প্রমাণ। বিশেষত কটু ও অশালীন বাক্যালাপ যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানে সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। সদ্য রান্না করা কোন খাবারের কোন হাড়ি থেকে বেরুনো সুগন্ধ যেমন খাবারটার ধরন ও মশলার মান সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, ঠিক তেমনি মানুষের প্রতিটা কথাবার্তা ও কথা বলার ভংগী তার স্বভাব চরিত্রের মাপকাঠি হয়ে থাকে। কারো মন মগজের ডেকচি থেকে যদি অশালীন বাক্যালাপ ও অভদ্র আচরণরূপী দুর্গন্ধ বেরোয়, তাহলে কিছুতেই আশা কড়া যায়না যে, তার মধ্যে পবিত্র ধ্যানধারণা ও ভদ্রজনোচিত মনোভাবের সমন্বয়ে কোন মহৎ চরিত্র তৈরী হচ্ছে। যখন কাউকে দেখবেন ভিন্ন মতাবলম্বীর সাথে অশালীন বাক্যালাপ ও অসদাচরণ করছে, তখন বুঝবেন সে তার প্রতিপক্ষের সাথে যুক্তির লড়াইতেও হেরে গেছে, নৈতিকতার লড়াইতেও পরাভূত হয়েছে। এখন এই হেরে যাওয়া মানুষটি গালাগাল দিয়ে কেবল মনের বিষ উদগীরণ করছে। আর মনের বিষ উদগীরণকারীরা ইতিহাসে কোন গুরুত্ব পায়না। তারা কেবল বিষেদাগারই করতে থাকে, আর গঠনমূলক দাওয়াতের কাজে নিয়োজিত কাফেলাতো কেবল সামনেই এগিয়ে যেতে থাকে।
এখানেই শেষ নয়। মদিনায় যখন আযানের প্রচলন হলো, তখন যেহেতু ইহুদীদের প্রচলিত ধর্মীয় বিধির বিরুদ্ধে এটাও একটা ধর্মীয় বেদয়াত ছিল, এ জন্য তারা আযান নিয়েও অনেক জটিলতায় ভুগতো। বিশেষত তারা যখন দেখতো যে, আযানের শব্দ ও বাক্যগুলো ইসলামের গোটা বিপ্লবী দাওয়াত ও তার মৌলিক মতাদর্শকে পরিপূর্ণভাবে তুলে ধরে এবং দিনে পাঁচবার এই আযান উচ্চ ও মধুর স্বর উচ্চারণ করা একটা অত্যন্ত কার্যকর ও প্রভাবশালী প্রচারমাধ্যম। এ আওয়ায তাদের নারী, শিশু ও গোলামদের কানে প্রতিদিন পাঁচবার প্রবেশ করতো। একবার কল্পনা করুন, এই নজীরবিহীন ধ্বনি যখন বিলালের সুলোলিত কণ্ঠে উচ্চারিত হতো, তখন মদিনার আকাশে বাতাসে কেমন নীরবতা বিরাজ করতো। মুসলমান অমুসলমান নিবির্শেষে সকলেরই মন হয়তো আকৃষ্ট হয়ে যেত। বিশেষত ঘণ্টা ও নাকাড়ার ধ্বনির সাথে আযানের ধ্বনির পার্থক্য নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতো। তাদের জনগণের মনেও এর প্রতি কিছু না কিছু অনুভূতি হয়তো জন্ম নিত। ঘণ্টা ও নাকাড়ার ধ্বনিতো কেবল ধ্বনিই ছিল। তাতে কোন কথাও ছিলনা অর্থও ছিল না। পক্ষান্তরে আযানের ধ্বনি ছিল সহজবোধ্য অর্থে ঝংকৃত কতিপয় বাক্যের সমষ্টি। নাকাড়া ও ঘণ্টার ধ্বনিতে কোন মানবীয় অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটতোনা, অথচ আযানের আহ্বানে প্রতিফলিত হতো মানুষের আবেগ ও অনুভূতি। এই পার্থক্যটা বুঝতে পারার পর ইহুদীদের এ কথা স্বীকার করা উচিত ছিল যে, আযানই যথার্থ এবাদতের দাওয়াত দেয়ার জন্য অপেক্ষাকৃত কার্যকর ও শ্রেষ্ঠতর মাধ্যম। কিন্তু তা স্বীকার না করে তারা ক্ষেপে গেল। তারা আযান দাতার আওয়াযকে আশ্চর্য ধরনের উপমা দিত, নকল করতো এবং শব্দ বিকৃত করে করে হাস্যোদ্দীপক অংগভংগী করতো। ঈর্ষা ও পরশ্রীকাতরতা এই ভণ্ড ধার্মিকদের ভাড়ের পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু আযান যে কাজ করছিল, তা ব্যংগবিদ্রুপ ও ভাড়ামী করে কিভাবে রোধ করা সম্ভব?
ইহুদীদের অসভ্যপনা এতদূর গড়িয়েছিল যে, তারা স্বয়ং আলাহ তায়ালাকেও এর শিকার তারা বানিয়ে ফেলেছিল। যেমনঃ কোরআনের আয়াত “আল্লাহকে কে ঋণ দিতে প্রস্তুত?” এর সরল অর্থ গ্রহণ করার পরিবর্তে এই বলে বিদ্রুপ করা শুরু করে দিল যে, ‘এখন তো আল্লাহ তায়ালাও গরীব হয়ে গেছেন। উনিও এখন বান্দাদের কাছে ঋণ চাওয়া শুরু করেছেন।’ আল্লাহর সাথে নির্লজ্জতা ও ধৃষ্টতার এমন জঘন্য উদাহরণ খুব কমই পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে কোরআনে যেখানে যেখানে মশা মাছি ও অনুরূপ ছোট ছোট জিনিসকে উদহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে এবং এগুলোর অস্তিত্বকে যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে, সেখানে ইহুদীরা ঠাট্টাবিদ্রুপের তাণ্ডব সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়ে যেত। তারা বলতো, মুসলমানদের আল্লাহও আশ্চর্য ধরনের। তিনি উদাহরণ দিতে গিয়েও মশামাছির মত নগণ্য প্রাণী ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাননা। আর যে কোরআনে এই সব নগণ্য জিনিসের উল্লেখ থাকে, তা আল্লাহর কিতাব হয় কি করে? তারা এর কেমন দাঁতভাঙ্গা জবাব পেল দেখুন আল্লাহর বক্তব্যঃ
“আল্লাহ মশা বা তার চেয়েও ক্ষুদ্র জিনিসের উদাহরণ দিতে কখনো লজ্জা পাননা। যারা হক কথা মানতে প্রস্তুত তারা এসব উদাহরণ দেখে বুঝতে পারে যে, এটা সত্য এবং এটা তাদের প্রতিপালকের কাছ থেকেই এসেছে। আর যারা মানতে প্রস্তুত নয়, তারা এগুলো শুনে বলতে থাকে, এ ধরনের উদাহরণের সাথে আল্লাহর কিসের সম্পর্ক?” (সূরা বাকারা-২৬)
হাস্যকর দাবী
ইহুদীদের বেয়াড়াপনা প্রমাণ দাবী করার রূপ ধারণ করে এক উদ্ভট হাস্যকর অবস্থায় পরিণত হয়। তারা রসূলকে সা. বলতে লাগলো, “আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন?” (বাকারা-১১৭) অর্থাৎ আল্লাহ তোমার কাছে গোপনে গোপনে ফেরেশতা পাঠান এবং গোপনেই তোমার কাছে নিজের বার্তা পাঠান কেন? আল্লাহ দুনিয়াতে নেমে আসুক, চোখের সামনে দেখা দিক, এবং আমাদের মুখোমুখি হয়ে বলুক যে, এ হচ্ছে আমার হুকুম, এগুলো মেনে চল, আর এইযে আমার নবী, এর আনুগত্য কর। তাও তিনি যদি করতে না চান, তাহলে অন্তত কোন একটা সুস্পষ্ট ও অকাট্য আলামত পাঠিয়ে দিক, যা দেখার পর কেউ আর এ কথা অস্বীকার করতে পারবেনা যে তুমি তার নবী এবং কোরআন তার বাণী।
এই অকাট্য আলামত কি হওয়া দরকার, তাও তারা নির্দিষ্ট করে বলে দিয়েছে যাতে করে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হতে পারে। ইতিহাস ও সীরাত বিষয়ক গ্রন্থাবলী থেকে জানা যায়, ইহুদী মহলে এই দাবী খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। দীর্ঘদিন যাবত তা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে এবং রসূল সা. এর সামনে তা বারবার উত্থাপিত হতে থাকে।
এই দাবী কিভাবে সৃষ্টি হলো প্রথমে তা শুনুন। ব্যাপারটা ছিল এই যে, মদিনার ইহুদীরা রসূল সা. এর আগমনের পূর্বে আওস ও খাজরাজকে ভয় দেখানোর জন্য পরিকল্পিতভাবে ভাবি নবীর তাৎক্ষণিক আবির্ভাবের জন্য দোয়া করতো। কিন্তু যখনই রসূল সা. নবী হিসেবে আবির্ভূত হলেন, অমনি তারা তাদের মনোভাব পাল্টে ফেললো এবং তাঁকে অস্বীকার ও অমান্য করতে বদ্ধপরিকর হলো। তাদের এই রাতারাতি ভোল পাল্টানোতে জনসাধারণের মধ্যে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়ে গেল। লোকেরা এসে এসে তাদের কাছে জিজ্ঞাস করতো, “ব্যাপার কী? আগে তো আপনারাই দোয়া করতেন এবং একজন নবী আসবেন বলে ভবিষ্যদ্বানী করতেন। আর এখন আপনারাই আবির্ভূত নবীর বিরুদ্ধে ক্ষেপে গেছেন!” বিশেষত এক মজলিসে মুয়ায বিন জাবাল ও বিশর বিন বারা বিন মারুরের ন্যায় শীষর্স্থানীয় নেতারা ইহুদী নেতৃবৃন্দকে খোলাখুলিভাবে বললেন, “হে ইহুদী সম্প্রদায়! আল্লাহকে ভয় কর এবং মাথা নোয়াও। কেননা তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে শক্তি লাভের নিমিত্তে নিজেরাই আল্লাহর কাছ থেকে মুহাম্মাদ সা. এর আবির্ভাব কামনা করতে। আমরা মোশরেক ছিলাম। তোমরাই আমাদেরকে জানাতে যে, সেই নবী আবির্ভূত হয়েছে এবং তাঁর গুণাবলীও তোমরা বর্ণনা করতে।” এ ধরনের কথাবার্তায় কিভাবে ইহুদীদের মুখোশ খুলে যেত, তা সহজেই অনুমেয়। তারা নিশ্চয়ই অনুধাবন করতো, তাদের সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত কি? নিজেদের দ্বীনদারী ও পরহেজগারীর মর্যাদা রক্ষার্থে তাদের কোন না কোন ঢালের আশ্রয় নেয়া অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এই ঢাল কি ছিল? এটা জানার জন্য উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব বনু নযীরের জনৈক ইহুদী নেতা সালাম ইবনে মুশকামের মুখ থেকে শুনুন। তিনি বলেনঃ “মুহাম্মাদ সা. নিজের সাথে এমন কোন প্রমাণ নিয়ে আসেননি, যা দ্বারা আমরা তাঁকে নবী হিসেবে চিনতে পারি। তাই মুহাম্মাদ সা. সেই ব্যক্তি নন, যার কথা আমরা তোমাদের কাছে উল্লেখ করতাম।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
ইবনে সিলভিয়া ফাতয়ূনীও রসূল সা. কে সরাসরি এ কথাই বলেছিল। অর্থাৎ একটু চূড়ান্ত আলামতের দরকার ছিল। সেই আলামত নির্ণয়ের কাজটাও ইহুদীদেরই করণীয়। তারা যেমন আলামত দাবী করতে চায় করবে। অনুরূপভাবে সাবেক নবীদের কাছ থেকে শেষ নবীকে মান্য করার যে অংগীকার নেয়া হয়েছিল, তাঁর ব্যাপারেও জনগণ তাদেরকে প্রশ্ন করছিল। কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব তারা এটা ওটা বলে এড়িয়ে যেত। ইহুদী মালেক ইবনুল কাতীদ একবার স্পষ্ট করেই বলেছিল যে, “আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সম্পর্কে আমাদের কাছ থেকে কোনোই অংগীকার নেয়া হয়নি।” (সীরাত ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
তাদের জন্য কোরআনের পবিত্র বাণী এবং অকাট্য যুক্তি প্রমাণে কোন নিদর্শন ছিলনা, রসূলের সা. চরিত্রে কোন নিদর্শন ছিল না। জীবনে আমূল পরিবর্তন আনয়নকারী আন্দোলনে কোন নিদর্শন ছিলনা, সত্যের সৈনিকদের বিকাশমান দলে কোন নিদর্শন ছিল না। নির্যাতন ও নিপীড়নকারী প্রতাপশালী শক্তিগুলোর মোকাবেলায় মুষ্টিমেয় সংখ্যক মুসলমান যে ত্যাগ কুরবানী ও প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছিল, তাতেও তাদের বিবেকে সাড়া জাগাতে পারে এমন কোন নিদর্শন ছিলনা। তারা চাইছিল কেবল বিস্ময়োদ্দীপক অথবা কৌতুকপ্রদ ঘটনা।
এবার শুনুন কি ধরনের আলামত বা নিদর্শনের দাবী তারা জানাচ্ছিল।
রাফে বিন হুরায়মালা ও ওহাব বিন যায়েদ রসূল সা. এর কাছে এসে আলাপ আলোচনা প্রসংগে বললো,
“হে মুহাম্মদ সা. আমাদের কাছে পুরো একখানা কিতাব লিখিতভাবে আকাশ থেকে নামিয়ে আনো, আমরা তা পড়ে দেখবো, আর আমাদের সামনে ঝর্ণা বানিয়ে দাও। তাহলেই আমরা তোমাকে অনুসরণ করবো এবং তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দেব।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
এই রাফে বিন হুরায়মালা এ দাবীও জানায় যে, “হে মুহাম্মদ সা. তুমি যদি আল্লাহর রসূল হয়ে থাক, যেমন তুমি বলে থাক, তাহলে আল্লাহকে আমাদের সাথে এমনভাবে কথা বলতে বল, যাতে আমরা শুনতে পাই।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
অন্য এক আলোচনা সভায় ফাখখাস, আব্দুল্লাহ বিন সবুর প্রমুখ ইহুদী নেতারা রসূল সা. এর সাথে কথা বলছিল, তারা বললো, “হে মুহাম্মদ, সত্যই কি এই কোরআন তোমাকে কোন জিন বা মানুষ শেখায়না?” রসূল সা. বললেন, “তোমরা ভালো করেই জান, এ কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত এবং আমি আল্লাহর রসূল। তোমরা এ সত্য তোমাদের তাওরাতেও লিখিত দেখতে পাও।” তারা বললো, “হে মুহাম্মাদ সা., তুমি যত কিছুই বলনা কেন, এ কথা তো সত্য যে, আল্লাহ যখন কোন রসূলকে পাঠান, তখন ঐ রসূল যা কিছুই চায় তা তিনি করে দেন, আর রসূল যা কিছুই ইচ্ছা করে, তা করে দেখানোর ক্ষমতা আল্লাহর পক্ষ থেকে পেয়ে থাকে। কাজেই তুমি আকাশ থেকে লিখিত গ্রন্থ অবতীর্ণ কর, যা আমরা পড়বো ও জানবো।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড)
ইহুদীরা একটা ঢাল পেয়ে গেল। এখন আর তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন গুরুত্ব রইলনা যে, রসূল সা. এর দাওয়াত কী? তিনি কী বলেন? তাঁর যুক্তি প্রমাণ কী? তাঁর দাওয়াতে জীবন কিরূপ গড়ে ওঠে? তাঁর শিক্ষায় কী ধরনের চরিত্র গড়ে ওঠে? এর গঠনমূলক চেষ্টা দ্বারা কি ধরনের সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা নির্মিত হয়? এই সমস্ত প্রশ্ন তাদের কাছে অবান্তর হয়ে গেল। তাদের কাছে তখন এই দাবীটাই প্রধান হয়ে উঠলো যে, “আকাশ থেকে কিতাব নামিয়ে দেখাও।” এখন সবার মুখ বন্ধ করার জন্য তারা একটা ছুঁতো পেয়ে গেল। কেউ এ নিয়ে কিছু বললেই তারা সাফ জবাব দিয়ে দিত যে, আমরা তো ঈমান আনতে প্রস্তুত। কিন্তু মুহাম্মাদ সা. কে যেয়ে বলে দাও যে, একটা কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দিক। আল্লাহর প্রিয় বান্দারা তো যা চায়, আল্লাহর কাছ থেকে আদায় করে নিয়ে থাকে। উনি কেমন রসূল যে, আল্লাহ তার আবদার রক্ষা করেনা? ওহে জনমণ্ডলী, এ সব বিভেদাত্মক কথাবার্তা বাদ দাও। যাও, আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার কাছে যাও। এতো নিছক ফাঁকিবাজি।
ইহুদীদের শাইলকী কর্মকান্ড
এটা সবর্জন বিদিত যে, মদিনার সীমিত উপায় উপকরণ ও সহায় সম্পদের ওপর যখন মোহাজেরদের চাপ বাড়তে লাগলো এবং সহায় সম্বলহীন ও আশ্রয়হীন মানুষেরা নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনের পুনর্গঠনে নিয়োজিত হলো, তখন ইসলামী আন্দোলনের অধিকাংশ কর্মীর মধ্যে দারিদ্র ও ক্ষুধা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। দারিদ্র ও ক্ষুধার এই পরীক্ষায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা স্বয়ং এবং তাঁর পরিবার পরিজন সাধারণ সাথীদের সমান অংশীদার ছিলেন। বরং পরীক্ষার প্রধান অংশ তাঁর ঘাড়েই পড়লো। বিপদ মুসিবত কখনো একাকী আসে না। দারিদ্র ও ক্ষুধার কষ্টের পাশাপাশি মোহাজেরদের মধ্যে রোগব্যাধিও ছড়িয়ে পড়ে। নতুন আবহাওয়া বহিরাগতদের শরীরে সইলনা। তারা একের পর এক রোগাক্রান্ত হতে লাগলো। অপ্রতুল খাদ্যের সাথে সাথে মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়া এক কষ্টদায়ক জ্বর মোহাজেরদের হাড্ডিসার ও অর্থনৈতিক চেষ্টা সাধনার অযোগ্য করে তুললো। ইসলামী আন্দোলন একদিকে সমস্যা ও বিরোধিতার নিত্য নতুন ফ্যাকড়ার সম্মুখীন হচ্ছিল। সদ্য গঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বদিক দিয়ে পুনর্গঠনের প্রয়োজন ছিল। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ শত্রুদের পক্ষ থেকে হরেক রকমের হুমকি আসছিল। কর্মক্ষম লোকেরা ক্রমেই শয্যাগত হচ্ছিল। খাদ্য ও পোশাকের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলনা। এমন একটা অবস্থাকে এই ক্ষুদ্র বিপ্লবী দল যে শক্তির বলে অতিক্রম করলো, তা ছিল আল্লাহর প্রতি ঈমান, উদ্দেশ্যের প্রতি ভালোবাসা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের শক্তি। আসলে বড় বড় ঐতিহাসিক কাজ সম্পাদনকারী ব্যক্তি ও সংগঠন সমূহের কেন্দ্রীয় শক্তিই হয়ে থাকে ঈমান ও ভ্রাতৃত্ব। এই শক্তি শারীরিকভাবে দুবর্ল লোকদেরকেও সবল রেখেছিল এবং সহায়-সম্পদের ঘাটতির প্রভাব অনেকটা কমিয়ে দিয়েছিল। এর মধ্য দিয়েও প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলছিল, তাকে সর্বব্যাপী মহামারী রোগ অনেকটা দুবর্ল করে দিল। এই সময় এ গুজবও ছড়িয়ে পড়ে যে, মদিনার ইহুদীরা যাদু করে দিয়েছে এবং মুসলমানরা এখন আর ওখানে টিকে থাকতে পারবে না। এ সময়ে পরিস্থিতি কত সংকটাপন্ন ছিল, সে সম্পর্কে ধারণা লাভের জন্য রসূল সা. এর কতিপয় সাহাবীর বক্তব্য শুনুন।
হযরত আবু বকর রোগ শয্যায় যন্ত্রণায় ছটফট করছেন এবং একটি কবিতা আবৃত্তি করে উদ্বেগ প্রকাশ করছেনঃ
******
“প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিবারে অবস্থান করে। অথচ মৃত্যু তার জুতোর ফিতের চেয়েও নিকটবর্তী।”
এদিকে হযরত বিলাল রোগ শয্যায় এপাশ ওপাশ করছেন, আর প্রচণ্ড রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়েও কবিতা আবৃত্তি করতে থাকেন, যার অর্থ হলোঃ
‘‘এখন মক্কার সমতল প্রান্তের, পাহাড় ও ঝর্ণার স্মৃতি চারণ করা হচ্ছে। যে সমতল ভূমিতে আযখর ও জুলাইল ঘাস জন্মে, সেখানে কি একটা রাত কাটাতে পারবো কখনো? মাজান্না ঝর্ণার পানিতে কি আর কখনো নামতে পারবো এবং শামা ও তোফায়েল পাহাড়ের দৃশ্য কি আর কখনো দেখতে পাবো?
আমের গাইছিলেনঃ ‘‘আমি মৃত্যুর স্বাদ উপভোগ করার আগেই মৃত্যুকে পেয়েছি। কাপুরুষের মৃত্যু আসে তার ওপর থেকে।’’ ইনি এত তীব্র শারীরিক যন্ত্রণায় ভুগছিলেন যে, মৃত্যু আসার আগে যেন মৃত্যুর পায়ের আওয়ায পেয়ে গিয়েছিলেন।’’
হযরত শাদ্দাদও রুগ্ন ছিলেন। রসূল সা. তাঁর এই সাথীকে দেখতে এলেন। রোগী রোগযন্ত্রণায় কাতর হয়ে বললেন, ‘‘বাতহানের পানি পান করলে হয়তো উপকার হতো।’’ রসূল সা. বললেন, চলে যাও। কে বাধা দিচ্ছে? রোগী বললেন, ‘‘হিজরতের কী হবে?’’ রসূল সা. প্রবোধ দিয়ে বললেন, ‘‘চলে যাও। তুমি যেখানেই যাবে মোহাজেরই থাকবে।’’
হোদায়বিয়ার সন্ধির পর যখন মুসলমানরা মক্কায় গেল, তখন তাদের শরীর বারবার রোগাক্রান্ত হওয়ার দরুন ভীষণ দুর্বল ছিল। আর এই অবস্থা দেখে মক্কাবাসী টিটকারী দেয় যে, ‘‘আবার মদীনায় যেওনা।’’ এই টিটকারীর কারণে রসূল সা. এর নির্দেশে মুসলমানরা বিরোচিত ভঙ্গিতে চলতো।
এসব কারণে রসূল সা. বলতেনঃ (********)
‘‘অর্থাৎ হিজরত কোন ছেলে খেলা নয়, বরং খুবই কঠিন কাজ। জনৈক বেদুঈন একবার রসূলের সা. কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু মদিনায় আসা মাত্রই তার জ্বর হলো। সে ইসলামকে অশুভ মনে করে ইসলাম পরিত্যাগ করে চলে গেল। এই ঘটনায় রসূল সা. বললেনঃ ‘‘মদিনা স্বর্ণকারের চুল্লীর মত। খাদকে বের করে দেয় এবং খাঁটি সোনাকে আলাদা করে।’’ (বুখারী) অর্থাৎ আন্দোলনের মহান কাজ সম্পাদনের জন্য যারা উদ্যোগী হয়, তাদেরকে পদে পদে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। সেই পরীক্ষায় খাঁটি ঈমানদার লোকেরাই পাশ করে। মেকি ও ভন্ড ঈমানের দাবীদাররা কোন না কোন পর্যায়ে আলাদা হয়ে যায়। তাই মদিনার এই অগ্নি পরীক্ষার পর্যায়টা স্বর্ণকারের চুল্লীর ভূমিকা পালন করছিল। (উসওয়ায়ে সাহাবা মাওলানা আবদুস সালাম নদভী)
এই সময়ই রসূল সা. আল্লাহর কাছে কাতর কণ্ঠে দোয়া করেনঃ ‘‘হে আল্লাহ! আমাদের কাছে মক্কাকে যেমন আকর্ষণীয় বানিয়েছিলে, মদিনাকেও তেমনি চিত্তাকর্ষক বানাও, অথবা তার চেয়েও বেশি। আমাদের জন্য এর খাদ্য শস্যে বরকত দাও। আর মদিনায় যে রোগ মহামারী এসেছে, তাকে মাহিয়ার দিকে সরিয়ে দাও।’’ (সীরাতে ইবনে হিশাম ২য় খন্ড)
অন্যদিকে দারিদ্র ও ক্ষুধা চরম উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। নতুন জায়গায় এসে অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি গড়ে তোলা এবং তাতে হালাল জীবিকা উপার্জনের ব্যবস্থা করা- তাও এমন পরিস্থিতিতে যে আন্দোলনের সামনে প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ব্যয়ের খাত এসে উপস্থিত হচ্ছিল- কত কঠিন, তা বলারই অপেক্ষা রাখেনা। সত্যের সৈনিকদের এই সময় যে বিপর্যয়কর অবস্থা অতিবাহিত করতে হয়েছে তার বেদনাদায়ক বিবরণে ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলী পরিপূর্ণ।
হযরত আবু তালহা এই দুর্যোগকালীন সময়ের বিবরণ দিয়েছেন এভাবেঃ
আমরা ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে সাহায্য লাভের জন্য রসূল সা. এর নিকট গেলাম। পুরো অবস্থা জানালাম এবং পেট খুলে দেখালাম যে, একাদিক্রমে কয়েকদিন উপোষ করার কারণে (পাকস্থলীতে সৃষ্ট বিশেষ ধরণের প্রদাহ রোধ করার উদ্দেশ্যে) পেটে একটা পাথর বেঁধে রেখেছিলাম। এটা দেখার পর মানবেতিহাসের ঐ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিটিও পেট খুলে দেখালেন, সেখানে একটা নয়, দুটো পাথর বাঁধা রয়েছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা যারা নিজেদের দুঃখের কাহিনী বণ্যনা করছিলাম, মনে সান্ত্বনা পেয়ে গেলাম। (শামায়েলে তিরমিযী, আইশুন্নাবী সংক্রান্ত অধ্যায়)
একবার এ ধরনেরই পরিস্থিতিতে হযরত আবু বকর রা. এলেন এবং সান্ত্বনা পাওয়ার জন্য নিজের দুর্দশা বর্ননা করতে চাইলেন। কিন্তু এতে অনর্থক রসূল সা. এর মনোকষ্ট বেড়ে যাবে এই ভেবে চুপ থাকলেন। কিছুক্ষণ পর হযরত ওমর রা. এলেন। তিনিও একই মুসিবতে আক্রান্ত ছিলেন। তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি খোলাখুলি বলে ফেললেন, ক্ষুধার তাড়নায় দিশেহারা হয়ে গেছি। একথা শুনে রসূল সা. বললেন, আমার অবস্থাও তদ্রুপ। সিদ্ধান্ত হলো, সবাই মিলে বাগবাগিচার মালিক অপেক্ষাকৃত সচ্ছল সাহাবী আবুল হাইসামের কাছে যাওয়া যাক। তিনজন তার কাছে যখন গেলেন, দেখলেন, ঐ বেচারা ভৃত্য না থাকায় নিজেই পানি আনতে গেছে। ফিরে এসে আগন্তুকদের দেখে আনন্দের আতিশয্যে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বাগিচায় নিয়ে গিয়ে খেজুর খেতে দিলেন। তারা খেজুর খেয়ে পানি পান করলেন এবং আবুল হাইসামের জন্য দোয়া করে ফিরে এলেন। (শামায়েলে তিরমিযী)
সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস একবার বর্ণনা করেন, আমিই ইসলামী আন্দোলনের সেই সদস্য যার হাতে সর্বপ্রথম ইসলামের একজন শত্রুর রক্ত ঝরেছে এবং আমিই জেহাদের ময়দানে সর্বপ্রথম তীর নিক্ষেপ করেছি। আমরা এমন অবস্থায় জেহাদ করেছি যে, গাছের পাতা ও কিকর ফল খেতে খেতে আমাদের মুখে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে যেত এবং উট ও ছাগলের মত পায়খানা হতো। [এ ঘটনাও শামায়েলে তিরমিযী থেকে গৃহীত। এটা কিছুটা পরবর্তীকালের ঘটনা হলেও এ দ্বারা মদিনার অর্থনৈতিক সংকটকালের ব্যাপারে সাধারণ ধারণা জন্মে।]
রসূল সা. এর ঘনিষ্ট সহচর হযরত আবু হুরায়রা জানান, ‘‘এক সময় আমি মসজিদে নববীর মিম্বর ও হযরত আয়েশার কক্ষের মাঝখানে ক্ষুধার জ্বালায় বেহুশ হয়ে পড়েছিলাম। লোকেরা আমাকে জ্বিনে ধরা ভেবে (চিকিৎসার ব্যবস্থা হিসেবে) পা দিয়ে ঘাড় টিপে দিত। অথচ আমাকে জ্বিনে ধরতোনা। শুধু ক্ষুধার জ্বালায় এমন অবস্থা হতো। (শামায়েলে তিরমিযী, আইশুন্নবী অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। হযরত আবু হুরায়রা আরো জানান যে, একবার আমি হযরত ওমরের সাথে কোথাও যাচ্ছিলাম। একটা আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করতে করতে চলছিলাম। সহসা বেহুশ হয়ে পড়ে গেলাম। ক্ষুধার কারণে এ অবস্থা হয়েছিল।
এরূপ পরিস্থিতিতে যদিও রাসূল সা. বাইতুল মালে আগত দ্রব্যাদি তাৎক্ষণিকভাবে সাহাবীদের ক্ষুধা দূর করার জন্য ব্যয় করতে থাকতেন। কিন্তু সংকট এত ব্যাপক ছিল যে, বাইতুল মালের উপার্জন এবং সচ্ছল মোহাজের ও আনসারদের মুক্ত হস্তে দান ও যথেষ্ট হতোনা। সাধারণ ক্ষুধার্ত মোহাজেরগণ ছাড়াও আসহাবে সুফফার (মসজিদে নববীতে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থানরত অসহায় সাহাবীগণ) স্থায়ী নিবাসও বিপুল সাহায্যের মুখাপেক্ষী ছিল। অনবরতই মেহমান আসতো। বেদুঈনরা যখন তখন ইসলাম গ্রহণ, সাক্ষাত ও শরীয়তের বিধি জিজ্ঞেস করতে আসতো, সাহায্য প্রার্থীরা এসে এসে সাহায্য চাইত। এবং একের পর এক মোহাজেরদের আগমণও অব্যাহত ছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে বাইতুল মাল কতদূর সামাল দিতে পারে? সাথীদের ও অভাবীদের চাহিদার চাপ যখন বেড়ে যেত তখন রসূল সা. সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতেন এবং যে যা পারতো, আন্তরিকতা সহকারে দিত। কখনোবা ঋণ গ্রহণ করা হতো। মুসলমানদের ভেতর থেকে বেশি ঋণ পাওয়া যেতনা। তাই ইহুদী বিত্তশালীদের কাছে যেতে হতো। ইহুদীরা ছিল ঝানু সুদখোর মহাজন। গোটা এলাকায় ছড়িয়ে ছিল তাদের সুদের জাল। কিন্তু মুহম্মদ সা. ও তাঁর সাথীদেরকে তারা যে উদ্দেশ্যে ঋণ দিত, তা ছিল সুদের চেয়েও ভয়ংকর। উদ্দেশ্য ছিল অর্থ কড়ি ও সাহায্যের জোরে তাদেরকে বশীভূত করা। এই মানসিকতা নিয়ে তারা ঋণ আদায় করতে গিয়ে একেবারেই শাইলকের রূপ ধারণ করতো এবং অপমানজনক আচরণ করতো। মোশরেকদের অবস্থাও ছিল একই রকম। এই তিক্ত অভিজ্ঞতা স্বয়ং রসূল সা. ও তাঁর সাথীদেরকেও অর্জন করতে হয়েছিল। এ ধরণের বহু ঘটনা ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবনকে উৎসর্গকারীগণ এত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন। এমন চরম বেগতিক অবস্থায়ও ইসলামের সৈনিকদের ঈমান ও লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে বিন্দুমাত্রও দুর্বলতা আসেনি।
রসূল সা. নিজের ঘনিষ্ট সহচর ও ব্যক্তিগত সহকারী হযরত বিলালকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন ইসলামী আন্দোলন ও তার সৈনিকদের প্রয়োজনে বাইতুলমালে প্রাপ্ত সম্পদ মুক্তহস্তে ব্যয় করেন। হযরত বিলাল করতেনও তাই। একবার নব্বই হাজার দিরহাম এল এবং তা একটা মাদুরের উপর স্তুপ করে রাখা হলো। ওখানে বসে বসেই রসূল সা. ঐ অর্থ অভাবীদের মধ্যে বিতরণ করলেন। একটা দিরহামও অবশিষ্ট রইলনা। বিলি বন্টন শেষ হয়ে যাওয়ার পর জনৈক সাহায্য প্রার্থী এলে তার জন্য ঋণ গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেন, একবার বিলালের সামনে খেজুর স্তুপীকৃত ছিল। রসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের মাল? হযরত বিলাল বললেন, ওটা ভবিষ্যতের অজ্ঞাত প্রয়োজনের জন্য রেখে দেয়া হয়েছে। রসূল সা. বললেন, ‘‘এই মাল এভাবে আটকে রাখার কারণে কেয়ামতের দিন যে তোমার কাছে জাহান্নামের ধূঁয়া পৌঁছে যেতে পারে, তা কি তুমি জান? ওটাও বন্টন করে দাও। হে বিলাল, সর্বময় ক্ষমতার মালিকের পক্ষ থেকে কোন কিছুর আশংকা করোনা।’’ হযরত বিলাল বর্ণনা করেন, একবার মদিনার জনৈক মোশরেক তাঁর কাছে এল সে বললো, ‘‘আমার কাছে অনেক সম্পদ আছে। যখন প্রয়োজন হয় নিও।’’ হযরত বিলাল তার কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে লাগলেন। একদিন যখন বিলাল ওযু করে আযান দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন সহসা ঐ মহাজন কতিপয় কারবারীকে সাথে করে এসে চিল্লাতে লাগলো, ‘‘ও হাবশী!’’ হযরত বিলাল তার কাছে এগিয়ে গেলেন। সে খুব উত্তেজিত হলো এবং বকাবকি করতে লাগলো। সে সতর্ক করলো যে, মাস প্রায় শেষ হয়ে আসছে। সময়মত ঋণ ফেরত না দিলে (আরবের জাহেলী প্রথা অনুসারে) তোমাকে গোলাম বানিয়ে নেব। তখন তোমার সাবেক অবস্থা ফিরে আসবে। হযরত বিলাল বলেন, এই অপমানজনক আচরণে আমি অন্য যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মতই বিব্রত বোধ করলাম। হযরত বিলাল এশার নামাযের পর এই দুঃখজনক ঘটনা জানাতে রসূল সা. এর কাছে হাজির হলেন। ঋণ পরিশোধ করার কোন উপায় না দেখে তিনি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন এবং বললেন, ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা হলে আমি ফিরে আসবো। কিন্তু হযরত বিলাল তার ইচ্ছা বাস্তবায়ন করার আগেই পরদিন সকালে রসূল সা. তাকে ডেকে পাঠালেন। গিয়ে দেখলেন, ফিদিকের শাসকের পক্ষ থেকে চারটে পণ্য বোঝাই উট এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঋণদাতাকে ডেকে ঋণ ফেরত দেয়া হলো এবং বাদবাকী মাল যথারীতি বিলি বন্টন করা হলো।
ইসরামী আন্দোলনের সৈনিক আবু হাদরু আসলামী জনৈক ইহুদীর কাছে ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁর কাছে পরণের কাপড় ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আবু হাদরু ইহুদির কাছে আরো সময় চাইলেন। কিন্তু ঐ শাইলকরূপী মহাজন একটুও সময় দিতে রাজি হলোনা। সে আবু হাদরুকে ধরে রসূলের সা. কাছে এনে বললো, আমার পাওনা পরিশোধের ব্যবস্থা করুন। রসূল সা. আবু হাদরুকে বললেন, ঋণ পরিশোধ করে দাও। আবু হাদরু ওযর পেশ করলেন। কিন্তু রসূল সা. মহাজনের অনড় মনোভাব দেখে বললেন, যেভাবে পার ঋণ ফেরত দাও। সাহাবী আবার বললেন, খয়বরের যুদ্ধ আসন্ন। ওখান থেকে ফিরে আশা করি পরিশোধ করা সম্ভব হবে। রসূল সা. পুনরায় কঠোরভাবে এই মুসিবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার আদেশ দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু হাদরুর পরনের পোশাক খুলে নিয়ই ইহুদী বিদায় হলো। আবু হাদরু নিজের পাগড়ি খুলে কোমরে জড়ালেন। কত সামান্য ঋণের জন্য ইহুদী মহাজনের যুলুমের ধরণ দেখুন যে, সে খাতকের পরনের কাপড় খুলে নিয়েই ক্ষান্ত হলো।
হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ ইসলামী আন্দোলনের আরেকজন নামকরা ব্যক্তি। তিনি মদিনার অধিবাসী ছিলেন এবং বেশ সচ্ছল ছিলেন। তথাপি মাঝে মাঝে প্রয়োজনের তাগিদে জনৈক ইহুদী মহাজনের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। একবার খেজুরের ফলন ভালো না হওয়ায় যথাসময়ে ঋণ ফেরত দিতে না পেরে পরবর্তী ফসল পর্যন্ত সময় বাড়িয়ে নিলেন। পরবর্তী ফসলও খারাপ হলো। মহাজন আর সময় দিতে রাজি হলোনা। অবশেষে তিনিও নিজের দুরাবস্থা বর্ণনা করার জন্য রসূল সা. এর দরবারে হাজির হলেন। রসূল সা. কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে ইহুদীর বাড়িতে গেলেন। তিনি জাবেরকে আরেকটু সময় দিতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইহুদী অস্বীকার করলো। রসূল সা. কিছুক্ষণ এদিক ওদিকে ঘোরাফিরা করে আবার এসে ইহুদীর সাথে আলোচনা করলেন। কিন্তু পাষাণ হৃদয় মহাজনের মন গললো না। অতঃপর কিছুক্ষণের জন্য রসূল সা. ঘুমালেন। জেগে আবার একই অনুরোধ করলেন। এবারও সে অনড়। অবশেষে রসূল সা. জাবেরের খেজুর বাগানে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং তাকে বললেন, খেজুর নামাও। খেজুর নামানো হলে আশাতীত খেজুর পাওয়া গেল। ঋণও পরিশোধ হলো এবং কিছু বেঁচেও গেল (সীরাতুন্নবী, শিবলী নু’মানী)
রসূল সা. এর ব্যক্তিগত বর্ম জনৈক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিল। তাঁর ইন্তিকাল পর্যন্তও ঐ বর্ম ছাড়ানোর মত অর্থ সঞ্চিত হয়নি। (সীরাতুন্নবী, শিবলী)
একবার রসূল সা. এর কাছে জনৈক বেদুঈন এসে ঋণ পরিশোধের জন্য তাড়া করতে লাগলো। স্বভাবসূলভ ভংগীতে সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে কথাবার্তা বললো। সাহাবীগণ তাকে বুঝালো যে, কত বড় ব্যক্তির সাথে কথা বলছ লক্ষ্য কর। সে বললো, আমি তো আমার পাওনা ফেরত চাইছি। রসূল সা. সাহাবাগণকে বললেন, তোমাদের উচিত ওকে সমর্থন করা। কেননা এটা তার প্রাপ্য। অতঃপর তার প্রাপ্য পরিশোধ করার আদেশ দিলেন এবং প্রাপ্যের চেয়ে কিছু বেশি দিলেন। (সীরাতুন্নবী, শিবলী)
যায়েদ বিন সাহনার ঘটনা থেকে এই সংকট সম্পর্কে আরো ধারণা পাওয়া যায়। ইনি একজন ইহুদী আলেম ছিলেন এবং বিভিন্ন আলামতের আলোকে রসূল সা.-এর নবুওয়াতের দাবীর সত্যতা যাচাই করছিলেন। তিনি জানান, জনৈক বেদুঈন এসে রসূল সা. এর সাথে সাক্ষাত করলো। সে বললো, আমার গোত্র মুসলমান হয়ে গেছে। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার সময় বলেছিলাম, তোমরা ইসলাম গ্রহন করলে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রচুর সম্পদ দেবেন। কিন্তু দুভাগ্যবশত এর বিপরীত দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এখন তাদেরকে সাহায্য না করলে তাদের ইসলাম পরিত্যাগ করার আশংকা আছে। রসূল সা. হযরত আলীর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। হযরত আলী রা. বললেন, এ মুহুর্তে কিছুই নেই। যায়েদ বিন সাহনা বললেন, আমার কাছ থেকে ৮০ মিসকাল স্বর্ণ নিয়ে নিন। এর বদলে মৌসুমে খেজুর দেবেন। কথাবার্তা পাকা হয়ে গেল। রসূল সা. স্বর্ণ নিয়ে বেদুঈনকে দিলেন। নির্দিষ্ট মেয়াদের দুতিন দিন বাকী থাকতে একদিন রসূল সা. যখন কতিপয় সাহাবীকে সাথে নিয়ে একজনের জানাযা পড়ে একটি প্রাচীরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন যায়েদ রসূল সা. এর গায়ের জামা ও চাদর ধরে অত্যন্ত রুক্ষভাবে বললেন, ‘‘হে মুহাম্মাদ! আমার ঋণ পরিশোধ করনা কেন? আল্লাহর কসম, তোমরা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর কেমন লোক তা আমি বিলক্ষণ জানি। তোমরা ঋণ পরিশোধ না করায় অভ্যস্ত।’’
হযরত ওমর রা. যায়েদের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। তারপর বললেন, ‘‘হে আল্লাহর শত্রু! আল্লাহর কসম, আমি যদি (রসূলের দিক থেকে তিরস্কারের) আশংকা না করতাম, তাহলে তোর গর্দান উড়িয়ে দিতাম।’’ রসূল সা. হযরত ওমরকে বললেন, ‘‘ওমর! এ ক্ষেত্রে তোমার উচিত ছিল, একদিকে আমাকে সুষ্ঠুভাবে ঋণ পরিশোধ করার পরামর্শ দেয়া এবং অপরদিকে এই ব্যক্তিকে ভদ্রজনোচিত পন্থায় ঋণ ফেরত চাওয়ার উপদেশ দেয়া।’’ তারপর বললেন, যাও, ওর পাওনা দিয়ে দাও। আর ধমক দেয়ার বদলে অতিরিক্ত বিশ সা খেজুর দিও।
আসলে এ ঘটনা ছিল যায়দ বিন সাহনার পক্ষ থেকে রসূল সাঃ এর নবুয়তের শেষ পরীক্ষা। তিনি হযরত ওমরকে নিজের পরিচয় জানালেন এবং তাকে সাক্ষী করে ইসলাম গ্রহণ করলেন।অতপর নিজের অর্ধেক সম্পত্তি মুসলিম জনগণকে দান করলেন। এই যায়দ বিন সাহনা ইহুদী মহাজনদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তার এ ঘটনা থেকেও জানা যায় ইসলামী আন্দোলন ও তার সদস্যরা কিরূপ আর্থিক সংকটে ছিলেন, সংকটের কারণে কত ঋন গ্রহণ করতে হতো এবং ঋণদাতাদের পক্ষ থেকে কত কঠিন আচরণ সইতে হতো।
ইহুদীরা ও ধনী মোশরেকরা একদিকে তো ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মহাজনীর অস্ত্র প্রয়োগ করতো। অপরদিকে তারা মুসলমানদেরকেও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতো, যাতে করে আন্দোলন আর্থিক অভাবের কারণে দুর্বল হয়ে যায়। এ উদ্দেশ্যে একদিকে তারা আল্লাহর পথে দানে উদ্বুদ্ধকারী আয়াতগুলো নিয়ে বিদ্রুপ করতো।তারা বলতো, এই দেখ, মুসলমানদের আল্লাহ তায়ালাও দেউলে হয়ে ঋণের জন্য ধর্না দিয়েছে। আবার কখনো বলতো, আল্লাহর হাত শেকলে বাধা। এ সব কথা ইহুদীদের মুখ থেকে পাচার হয়ে মোনাফেকদের মুখেও উচ্চারিত হতো এবং গোটা পরিবেশকে কলুষিত করতো। অন্যদিকে তারা দানে অভ্যস্ত মুসলমানদের সাথে সাক্ষাত করে বলতো, ‘আরে,নিজেদের সম্পদ নষ্ট করছ কেন? মক্কার ক’জন কাংগালকে খাইয়ে দাইয়ে তোমাদের কী লাভ? নিজেদের ছেলেমেয়েদের সেবাযত্ন কর। ব্যবসায় বাণিজ্যে সম্পদ খাটাও। সম্পদ বিনিয়োগের এমন নির্বোধসুলভ খাত কোথা থেকে পেলে?’ এই সব অপপ্রচারাভিযান পরিচালনাকারী ইহুদী ও মোনাফেকদের সম্পর্কেই কোরআনে বলা হয়েছে যে, ******** “অর্থাৎ তারা মানুষকে কার্পন্য করার শিক্ষা দেয়। এরা আনসারদের কাছে এসে বসতো এবং শুভাকাংখীর বেশ ধারণ করে বলতো, “নিজেদের টাকা পয়সা এভাবে উড়িওনা। এতে তোমরা অভাব অনটনে পড়বে। কাজেই তোমরা ইসলামী আন্দোলনের পেছনে এত অর্থ ব্যয় করোনা। পরিস্থিতি কী হয়ে দাড়াবে, তা বুঝতে চেষ্টা কর”।(সীরাতে ইবনে হিসাম)
ওদিকে ইহুদীদের ক্রীড়ানক পঞ্চম বাহিনীর লোকদের মধ্যে কানাঘুষা হতো যে, “রসূল সাঃ এর সাথীদের জন্য অর্থ ব্যয় করা বন্ধ কর। ওরা এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাক।”(সূরা মুনাফিকুন,আয়াত-৭)
কত দূরদর্শী কুট পরিকল্পনা ছিল! একদিকে আল্লাহর পথে দান করার মানসিকতা ও জযবার উৎস বন্ধ করে দেয়ার উদ্যোগ। অপরদিকে মহাজন হয়ে নিজেদের শাইলকী যুলুম দ্বারা ইসলামী আন্দোলনকে পিষ্ট করে ফেলার অপচেষ্টা। এ পরিকল্পনা সফল হলে ঈমান, যুক্তি এবং আমল ও চরিত্রের ময়দানে মোকাবেলা না করেই ইসলামী বিপ্লবকে পরাজিত করা যেত।কিন্তু যেহেতু ব্যাপারটা ছিল সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে জড়িত। তাই তার সুক্ষ তদবীরে ইসলামের শত্রুদের চক্রান্ত নস্যাত হয়ে গেল।
এই কাহিনীতে মূল বিষোয় হলো রসূল সাঃ ও সাহাবায়ে কেরামের সেই ধৈর্যশীল সুলভ চরিত্র ও ভূমিকা যা বিরোধীদের হীন নিপীড়নের জবাবে আত্নপ্রকাশ করেছিল। যারা চরম নৈরাজ্যজনক ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতিতেও তাদের উচ্চস্তরের নৈতিক মানকে এতটুকুও নিচে নামতে দেননি। তারা যে মানবতার কত বড় ও উজ্জ্বল নমুনা ছিলেন,ভেবেও তার কুল কিনারা পাওয়া যায়না।
ইহুদীদের গড়া পঞ্চম বাহিনী
মানবেতিহাসের হাজারো অবজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয়, যখনই সততা ও মানব কল্যাণের লক্ষ্যে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা সহকারে কোন আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে এবং তা বিজয়ের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন তার প্রতিরোধকারী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর একটি হয়ে থাকে যারা প্রকাশ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং সমকালীন অস্ত্র প্রয়োগ করে তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যায়। অপর শক্তিটি হয়ে থাকে সেই সব নৈরাজ্যবাদী ও নাশকতাবাদী লোক,যারা চারিত্রিক হীনতা ও নীচতার কারণে কাপুরুষতা ও শঠতার নিম্নস্তরে নেমে আসে এবং মোনাফেকীর গোপন ঘাটিতে বসে চক্রান্তের জাল বিস্তারের কাজে আত্ননিয়োগ করে। মক্কার মোশরেকদের প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ ছিল প্রথমোক্ত শক্তি আর মদিনার ইহুদী ও তাদের বংশবদরা ছিল শেষোক্ত শক্তি।
যেহেতু ইসলামী আন্দোলন একটা রাষ্ট্রের রূপ ধারণ করেছিল, এই রাষ্ট্র সকলের চোখের সামনেই বেড়ে উঠছিল এবং চারদিক থেকে বিবেকবান, সক্রিয় ও কর্মপ্রিয় লোকেরা এতে যোগদান করছিল। তাই বিরোধী শক্তি হীনমন্যতা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার ভয়ংকর প্রতিক্রিয়ার শিকার হচ্ছিল। কিন্তু তাদের মনের অভ্যন্তরে যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল তা প্রকাশ করা ও পরিস্থিতির ওপর প্রভাব বিস্তার করার কোন উপায় ছিলনা। ইসলামী আকীদা ও আদর্শের মোকাবেলায় ইহুদীদের কাছে কোন যুক্তিসংগত, সহজ সরল, জনগণকে আকর্ষণকারী এবং চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী কোন গঠনমূলক মতবাদ ইহুদী সম্প্রদায়ের কাছে ছিলনা। তাদের কাছে ছিল কতগুলো নিষ্প্রাণ ও অসার আকীদা-বিশ্বাস, যা ইতিহাসের প্রবাহকে রোধ করা ও মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে পংগুত্ব ও স্থবিরতা সৃষ্টি করার ক্ষমতাসম্পন্ন ছিল। ইসলামী আন্দোলন যে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী জনশক্তির সমাবেশ ঘটিয়েছিল, তাদের সামনে টিকে থাকার মত সমমানের নৈতিক চরিত্র সম্পন্ন জনশক্তি ইহুদীদের কাছে ছিলনা। তাদের কাছে যে জনশক্তি ছিল, তা নৈতিক দিক দিয়ে মনুষ্যত্বের কাংখিত সর্বমিম্নমানের চেয়েও নিম্ন মানের ছিল। এই পতিত দশা থেকে টেনে তোলার মত কোন প্রেরণা ও চালিকাশক্তি তাদের কাছে অবশিষ্ট ছিলনা। মানবতার পুনর্গঠনের কোরআনী দাওয়াত যে নতুন মানুষ গড়ে তুলেছিল, ইহুদীবাদের গড়া প্রাচীন ধাচের মানুষ তার সামনে দাড়ানোরই যোগ্য ছিল না। অপপ্রচার চালিয়ে ভুল বুঝাবুঝি ও শত্রুতা যতই সৃষ্টি করুক না কেন, যুক্তি ময়দানে ইহুদী শক্তি ক্রমেই পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল। তারা নিজেদেরকে যাই মনে করুকনা কেন,ইতিহাসের শক্তি ইসলামী আন্দোলনেরই পক্ষে ছিল। বাস্তবতার রণাঙ্গনে ইহুদীদের ওপর সর্বদাই দুরন্ত আঘাত আসছিল। সমকালীন মানব সমাজ তাদেরকে পেছনে ফেলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। রাজনৈতিক অংগনে ইহুদীদের সাধ ছিল ইসলামী বিপ্লবকে ধ্বংস করে দেবে। কিন্তু মৈত্রী চুক্তি তাদের হাত বেধে রেখেছিল।এ ই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে তারা একেবারেই অক্ষম ও অসহায় হয়ে পড়েছিল। আর এই অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের অনুভূতি তাদের চরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্টের সাথে মিলিত হয়ে কাপুরুষত্বের রূপ ধারণ করেছিল। অসহায়ত্ব ও কাপুরুষোত্বের পরিবেশে মানুষের মনে যে প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিকতা সক্রিয় থাকে, তা সর্বদাই হিংসা ও বিদ্বেষের পথ দিয়ে তাকে মোনাফেকীর গোপন ঘাটিতে পৌছে দিয়ে থাকে। ফলে সে প্রতিপক্ষের ওপর সম্মুখ থেকে আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে পেছন থেকে গোপন আঘাত হানে। প্রকাশ্য ডাকাতির পরিবর্তে সে সিঁদেল চুরির চক্রান্ত আটে। এই কাপুরুষোচিত ভূমিকাই অবলম্বন করলো ইহুদী সম্প্রদায়।
বাস্তব পরিস্থিতি ঘৃণ্য মোনাফেক চক্রের আবির্ভাবের জন্য দুট সহায়ক উপরকণ সৃষ্টি করে দেয়। প্রথমত ইহুদী চক্র ও তাদের বংশবদদের প্রতিহিংসামূলক মানসিকতা। এই মানসিকতার যেহেতু প্রত্যক্ষ আক্রমণের ক্ষমতা ছিলনা, তাই মোনাফেকীর গোপন ঘাটি সক্রিয় হয়ে উঠলো। দ্বিতীয়ত ইসলামের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে অনেকে নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে তোলার জন্য এই চোরা পথ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে লাগলো।
এই চোরা পথের উদ্বোধন ইহুদী মস্তিস্কই করেছিল। তাদের নামকরা সরদাররা নিজেদের বৈরী মানদিকতাকে লুকিয়ে রেখে ইসলামের আলখেল্লা পরে ইসলামী সংগঠনে প্রবেশ করতে লাগলো। বনু কাইনুকার নিম্নোক্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ “পঞ্চম বাহিনী” হিসেবে ইসলামে প্রবেশ করেঃ
(১) সা’দ বিন হানীফ (২) যায়েদ বিন লুসিত (৩) নুমান বিন আওফা বিন আমর (৪) রাফে বিন হুরাইমালা (৫) রিফা বিন যারেদ বিন তাবুত (৬) সালসালা বিন বারহাম (৭) কিনানা ইবনে সূরিয়া।
এদের মধ্যে যায়েদ বিন লুসিত হলো সেই ব্যক্তি,যে বনু কাইনুকার বাজারে হযরত ওমরের সাথে মারামারি বাধিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া এই ব্যক্তি রসূল সাঃ এর উটনী হারিয়ে গেলে টিটকারী দিয়েছিল যে,“এমনি তো উনি আকাশের খবরাদি দিয়ে থাকেন, অথচ ওর উটনীটা এখন কোথায় আছে তা জানেন না!” এর জবাবে রসূল সাঃ বলেছিলেন, “আল্লাহ যা আমাকে জানিয়ে দেন তাছাড়া আমি আর কিছু জানিনা। এখন আল্লাহ আমাকে উটনীর খবর জানিয়ে দিয়েছেন। উটনীটা অমুক মাঠে আছে এবং একটা গাছের সাথে তার বাগের রশী আটকে গেছে।” সাহাবীগণ তালাশে ছুটে গেলে অবিকিল সেই অবস্থাই স্বচোক্ষে দেখলেন।
রাফে বিন হুরাইমালা এমন উচুস্তরের মোনাফেক ছিল যে, সে যেদিন মারা গেল সেদিন রসূল সাঃ বললেন, আজ মোনাফেকদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা মারা গেছে। রিফা বিন যায়েদ বিন তাবুতও অনুরূপ একজন। বনুল মুসতালিক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার সময় একটা ঝড় উঠলে লোকেরা ভয় পেয়ে গেল। রসূল সাঃ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, “এই ঝড় জনৈক মোনাফেক নেতাকে শাস্তি দেয়ার জন্য এসেছে।” মদিনায় পৌছার পর সবাই জানতে পারলো যে, ঐঝড়েই রিফা পটল তুলেছে।(সীরাত ইবনে হিশাম,২য় খন্ড)
মজার ব্যাপার হলো, মোনাফেকদের কাতারে যত লোক শরীক হয়েছে, তারা সকলেই ছিল বয়সে প্রাচীন ও সচ্ছল। তারা ছিল স্বার্থপর এবং পাষাণ হৃদয়। যুবকরা সাধারণত ইসলামী আন্দোলনের সাথী ছিল। মাত্র একজন যুবক কিস বিন আমর বিন সাহলকে পঞ্চম বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত দেখতে পাওয়া যায়।
এই চক্রটি এত সীমিত ছিলনা। আসলে এই কয় ব্যক্তি তো ছিল পঞ্চম বাহিনীর নেতা ও সেনাপতি। তারা নিজেদের পরিচিত মহল থেকে নতুন নতুন মোনাফেককে ভর্তিও করতো। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্য থেকে দুর্বল লোকদেরকে খুজে খুজে তাদেরকেও প্রভাবিত করতো, তাদেরকে ব্যবহার করতো, তাদের মধ্যে সন্দেহ সংশয় ছড়িয়ে মুসলমানদের বৈঠকাদিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীতে বিদ্রুপ ও উপহাসের মাত্রা যোগ করে পরিবেশকে খারাপ করতো। মসজিদে গিয়ে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনে নিজেদের বৈঠকগুলোতে তার রিপোর্ট দিত। রাতের বেলা বসতো ষড়যন্ত্রের বৈঠক, তৈরী হতো নতুন নতুন ক্ষতিকর পরিকল্পনা এবং নতুন নতুন পন্থায় তা বাস্তবায়ন করা হতো। মোনাফেকদের তৈরী করা এই বেঢংগা চালচলন তার নিজস্ব অস্বাভাবিকতার কারণে রসূল সাঃ ও মুসলমানদের দৃষ্টিতে সুপরিচিত ছিল। সাথে সাথে প্রত্যেকটি স্তরে ওহীর মাধ্যমে তাদের চিন্তা, কর্মকান্ড ষড়যন্ত্র, এমনকি তাদের অপরাধ প্রবণ বিবেকের বিশেষ বিশেষ আলামতকেও চিহ্নিত করতে থাকতো। একবার তো মসজিদে নববীতে এই মোনাফেক সরদারদের আচরণ অসহনীয় হয়ে ওঠে। সাধারণ সমাবেশে এই চক্রটি একেবারেই আলাদাভাবে বসেছিল এবং পৃথকভাবে কানাঘুষায় লিপ্ত ছিল।এ দৃশ্য দেখে রসূল সাঃ তাদেরকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কেউ কেউ পরস্পরের সাথে এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে, হাত ধরাধরি ও জড়াজড়ি করা অবস্থায়ই বহিস্কৃত হলো।
এই মোনাফেক চক্রের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেন্দ্রীভূত ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর সত্তায়। হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনার নাটকের প্রধানতম খলনায়ক ছিল এই ব্যক্তি। ইসলামী বিপ্লবের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা তার মেরুমজ্জায় মিশে ছিল। এই দুরারোগ্য ঘৃণা ও বিদ্বেষের মূল কারণ হযরত উসাইদ বিন হুযাইরের মুখ থেকে শুনুন। তিনি রসূল সাঃ এর কাছে বনুল মুস্তালিক যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ বিন উবাই সম্পর্কে বলেনঃ
“হে রসূলুল্লাহ! এই ব্যক্তির (দুঃখভারাক্রান্ত আবেগের) প্রতি একটু সদয় হোন। মদিনায় যখন আপনার শুভাগমন ঘটেছিল, তখন আমারা তাদের রাজকীয় সিংহাসনে বসানোর সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলেছিলাম। তার জন্য মুকুট তৈরী হচ্ছিল। আপনার আগমনে তার বাড়াভারে ছাই পড়েছে। বেচারা সেই আক্রোশ ঝাড়ছে।” (তাফহীমুল কুরআন,সূরা নূরের ভূমিকা)
কোন দাওয়াত বা আন্দোলনের কারণে যাদের পরিকল্পনা নস্যাত হয়ে যায় এবং যাদের স্বার্থ সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেও বিফলে যায়, তারা বুকের ভেতরে বিষ ভরে নিয়ে সারা জীবন ছটফট করতে থাকে। এমন পরাজিত প্রতিদ্বন্দী কখনো প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করতে পারেনা।ইসলামের অবস্থাও ছিল তাই। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই তার ব্যর্থতার তিক্ত স্মৃতি প্রথম দিন থেকেই বহন করছিল এবং আজীবন বহন করেছে। শুরুতেই সে ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাতে এই নতুন শক্তির ভেতরে নিজের জন্য জায়গা তৈরী করে নিতে পারে এবং তার ভেতর থেকে ধাপে ধাপে উঠে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেদিকেই কেউ যেতে চায় তাকে ঈমান ও আমলের পথ ধরেই যেতে হয়। তাই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর পক্ষে মোনাফেক হিসেবে অবস্থান করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা।শুরু থেকে এই মোনাফেকী গোপন ছিল। কিন্তু একদিন তার মনের এই নোংরা ব্যাধি ঘটনাক্রমে জনসমক্ষে বেরিয়ে পড়ে।
একদিন রসূল সাঃ অসুস্থ সাহাবী সা’দ বিন উবাদাকে দেখতে গিয়েছিলেন। গিয়েছিলেন একটা গাধায় আরোহন করে। তার পেছনে বসেছিল উসামা বিন যায়েদ। এই উসামাই বর্ণনা করেন, পথিমধ্যে এক জায়গায় আব্দুল্লাহ বিন উবাই মজলিস জমিয়ে বসেছিল। তার চারপাশে স্বগোত্রের লোকেরাই উপবিষ্ট ছিল। রসূলকে সাঃ ওখান দিয়ে যেতে দেখে সে বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল। রসূল সাঃ তার কাছে গিয়ে সালাম দিলেন। তারপর একটু থেমে কোরআনের একটা অংশ পড়লেন, ইসলামের দাওয়াত দিলেন, আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তার ক্রোধ সম্পর্কে সতর্ক করলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাই নিরবে ও রুদ্ধশ্বাসে বসে রইল। কিন্তু রসূল সাঃ যখন কথা শেষ করে রওনা হলেন, তখন সে অত্যন্ত অভদ্র ও অশালীন ভাষায় চিৎকার করে বললো, “ওহে অমুক! তোমার কথা বলার এই পদ্ধতি ঠিক নয়।নিজের ঘরে বসে থাকো গে। যে ব্যক্তি তোমার কাছে যায়, তাকে যা বলতে চাও বলে দিও। যে ব্যক্তি তোমার কাছে না যায়, তাকে উত্যক্ত করোনা। কারো বাড়ীতে গিয়ে উপযাচক হয়ে এমন দাওয়াত দিওনা যা তার পছন্দ হয়না।” দেখুন প্রতিটা শব্দ কেমন বিষে ভরা! কেমন নোংরা ও মর্মঘাতী ভাষা এবং কেমন উস্কানীপূর্ণ ভাবাবেগ।
আসলে এ কথাগুলো ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর ছিলনা। এ ছিল আসন্ন সুখ সমৃদ্ধির যুগের বিরুদ্ধে পতনোন্মুখ জাহেলিয়াতের বিষোদগার।
রসূল সাঃ নিজের উচ্চ মর্যাদাপূর্ন অবস্থান থেকে এই ইতরসুলভ প্রলাপ শুনলেন। শুনে তার মহানুভব হৃদয়ে হয়তো ক্রোধের পরিবর্তে করুণারই উদ্রেক করে থাকবে।
মজলিসে মুসলিম দলের সদস্য আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহাও উপস্থিত ছিলেন। তার আত্নসম্মানবোধ তাকে আপন কর্তব্য পালনে উদ্বুদ্ধ করলো।তিনি মোনাফেক নেতাকে তীব্র কন্ঠে জবাব দিলেনঃ “রসূল সাঃ কেন আসবেন না? আমরা তাকে চাই। তিনি আমাদের বাড়ীতে ও মজলিসে আসবেন। আমরা তাকে ভালোবাসি এবং তারই ওছিলায় আল্লাহ আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন।”
পথিমধ্যে এই অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর বিশ্বমানবতার নেতা সা’দ বিন উবাদাকে দেখতে গেলেন। সা’দ রসূল সাঃ এর মুখমন্ডলে অস্বাভাবিক চিহ্ন দেখে কারন জিজ্ঞেস করলেন। রসূল সাঃ ঘটনা বর্ণনা করলেন।সা’দও একই পটভূমি বর্ণনা করলেন যেঁ, “আল্লাহ যখন আপনাকে মদিনায় নিয়ে এলেন তখন আমরা ওর জন্য মুকুট বানাচ্ছিলাম। আপনি এসে তো তার রাজত্বের স্বপ্ন গুড়িয়ে দিয়েছেন।” তিনি বুঝাতে চাইছিলেন যে, তার এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক। একে গুরুত্ব না দেয়াই ভাল।
এই ব্যক্তি মোনাফেকীর সমগ্র নাটকের প্রধান খলনায়ক হয়ে ইতিহাসের মঞ্চে অভিনয় করতে থাকে। সে ছিল এর প্রধান হোতা। তার পেছনে ছিল বড় বড় নেতার আশীর্বাদ। আর তাদের পেছনে ছিল সচেতন মোনাফেক এবং অপরিপক্ক মুসলমানদের গোষ্ঠী। সবার পেছনে ছিল অজ্ঞ ও অবুঝ বেদুঈনরা। ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি প্রতিক্রয়াশীল পদক্ষেপের পেছনে পর্যায়ক্রমে এই সব বিবিধ শ্রেণীর অবদান থাকতো। মদিনায় মুসলমানরা যে সব বিরোধিতা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে ছিল এবং রসূল সা. কে যে সব চক্রান্তের সম্মুখনি হতে হয়েছিল, তার সবগুলোর পেছনে ইহুদী প্রভাবিত মোনাফেকদের এই বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক শক্তির বিরাট ভূমিকা ছিল। সকল বৈরী তৎপরতার নেতৃত্ব যদিও ইহুদীদের হাতেই নিবদ্ধ থাকতো, কিন্তু রসূলের সা. পথ আগলে দাঁড়ানোর জন্য যতগুলো নেতিবাচক ঘটনা ঘটানো হয়েছে, তার পেছনে কার্যত সেই মোনাফেকদের ভূমিকাই ছিল প্রধান, যারা ইহুদীদের ক্রীড়ানক হিসাবে কাজ করতো।
অপপ্রচারমূলক তৎপরতা
কর্মবিমুখ নৈরাজ্যবাদী মহল যখন কোন সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক আন্দোলনের কবলে পড়ে, তখন তার নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আদাপানি খেয়ে লেগে পড়ে। নিজেরা তো কিছু করতে চায়না। আল্লাহ এবং জনগণের প্রতিও তারা কোন দায়দায়িত্ব অনুভব করেনা। এজন্য সকল শক্তি ও প্রতিভা অতি সহজেই নেতিবাচক তৎপরতায় নিয়োগ করে। এই সব লোক সংস্কারবাদী ও গঠনমূলক আন্দোলনের নেতা কর্মীদেরকে ভূতের মত চারদিক দিয়ে ঘিরে ধরে, দূরবিক্ষণ যন্ত্র দিয়ে তাদের দোষ অন্বেষণের চেষ্টা করে। তাদের প্রতিটা কথা, কাজ ও ঘটনার চুলচেরা বিশ্লেষণ করে। তারপর বিন্দুপরিমাণ কোন বক্রতা বা ত্রুটি খুঁজে পেলেই ঢেড়া পিটিয়ে প্রচার করতে আরম্ভ কওে যে, “ওহে জনমন্ডলী! দেখ, এরা গোমরাহী, বিকৃতি ও কুফরিতে লিপ্ত। অমুক কাজ প্রাচীন মনীষীদের বিরোধী, বড় বড় ইমামদের অবমাননা, বড় বড় বুযুর্গদের সমালোচনা। অন্ধ বিরোধীতার আবেগে যখন কোন ভালো লোকের ও তার জনহিতকর কাজের ক্ষতি সাধন করা কাংখিত হয়, তখন একদিকে প্রত্যেক ভালো কাজের দোষত্রুটি বের করে দেখানো হয়। অপর দিকে যারা কাজ করে, তাদের সামান্য ভুলত্রুটি হলেও তিলকে তাল বানিয়ে জনসমক্ষে প্রকাশ করে জনমতকে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়। নাশকতাবাদীদের সবচেয়ে বড় সুযোগ হয়ে থাকে তখন, যখন কোন ঘটনা সাধরণ মানুষের ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা, কুসংস্কার ও কুপ্রথা ইত্যাদিও বিরুদ্ধে ঘটে যায়, চাই তা সঠিক ও ন্যায় সংগতই হোক। এটা সর্বজন বিদিত যে, সংস্কারবাদী, গঠনমূলক ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলোকে অনেক জনপ্রিয় জিনিসের বিরোধিতা করতে হয়। তাই বৈরী অপপ্রচারের জন্য সব সময় একটা না একটা বিষয় অবশ্যই পাওয়া যায়। রসূল সা. ও সাহাবায়ে কিরাম ইহুদীদের পক্ষ থেকে এই পরিস্থিতিরই সম্মুখীন ছিলেন। প্রতিদিন সকাল বিকাল একটা না একটা হৈ হাঙ্গামা হতো এবং কোন না কোন অপপ্রচার চালানো হতো।
পদলোভের অভিযোগ
সত্যের নিশানবাহী মাত্রেরই আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার উপর একটা না একটা স্বার্থের কালিমা লেপনের জন্য বিরোধীরা প্রত্যেক যুগেই অপবাদ আরোপ করে থাকে যে, উনি একজন পদলোভী ব্যক্তি। উনি একটা বড় কিছু হতে চান। হযরত মূসা ও হারুনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগই তোলা হয়েছিল যে, ওঁরা রাষ্ট্রীয় গদি দখল করতে চান। হযরত ঈসার বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হয় যে, উনি ইহুদীদের বাদশাহ হতে চান। নাজরানের প্রতিনিধি দল যখন এলো, তখন ইহুদীরা রসূল সা. এর ওপর অপবাদ আরোপ করলো যে, ঈসা আ. এর যে মর্যাদা ছিল, সেটা দখল করার জন্যই উনি এত মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। উনি চান খৃষ্টানরা ও অন্যরা তাঁর পূজা করতে লেগে যাক। লক্ষ্য করুন, রসূল সা. কখনো এ ধরনের কোন দাবীই করেননি। এ ধরনের কোন গদি বা পদ লাভের ইচ্ছার আভাসও দেননি। অথচ বিরোধীদের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে এমন কাল্পনিক অভিযোগ গড়া হলো এবং আবিস্কার করা হলো যে, মুহাম্মদ সা. এর উদ্দেশ্য এটাই হবে যে, ঈসার আ. মত নিজের পূজা করাবেন। মুখে দাবী করেননি, তাতে কী? তাঁর অন্তরে নিশ্চয়ই এই দাবী রয়েছে, আজ না হোক, ভবিষ্যতে কোন না কোন দিন তিনি এ দাবী যে করবেন, তারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নাজরানী প্রতিনিধিদলের কানে এসব প্রলাপোক্তি ঢোকানো হয়েছিল বলেই ঐ দলের জনৈক সদস্য আবুনাফে কারজী রসূল সা. কে খোলাখুলি জিজ্ঞাসা করেছিল, আপনি কি চান খৃষ্টানরা ঈসা আ. এর যেমন পূজা কওে, তেমনি মুসলমানরাও আপনার পূজা করুক? অপর সদস্য জিজ্ঞাসা করে, আপনি কি আমাদের কাছ থেকে পূজা উপাসনা চান এবং তার জন্যই দাওয়াত দিচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, “আমি এ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই যে, আমি আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করি কিংবা আর কারো এবাদতের দাওয়াত দেই। আল্লাহ আমাকে এ উদ্দেশ্যে পাঠানওনি এবং আদেশও দেননি।” (সীরাতে ইবনে হিশাম. ২য় খন্ড) এ পর্যায়ে কোরআনও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলো যে, “এটা কোন মানুষের জন্য বৈধ নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, হিকমত ও নবূয়ত দেবেন, আর সে মানুষকে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও।”
সর্বসম্মত ধর্মীয়প্রতীক সমূহের অবমাননার অভিযোগ
বিশ্ব মানবের নেতা সা. হিজরত করে মদিনায় চলে আসার পর মক্কায় নতুন করে প্রতিশোধ স্পৃহা জাগতে শুরু করে এবং মদিনার উপর আক্রমণ পরিচালনার বিষয়ে ক্রমাগত চিন্তাভাবনা চলে। তাদের গোয়েন্দারা মদিনার আশপাশে ঘোরাফেরা করতো। মদিনার ইহুদীদের সাথে তাদের চিঠিপত্রের আদান প্রদান শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের সামরিক দল যখন তখন ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যেত। এর জবাবে ইসলামী রাষ্ট্রও টহলদানের ব্যবস্থা চালু করলো। সামরিক ও বেসামরিক দলগুলো টহল দিত এবং কোরায়েশদের গোয়েন্দা ও সামরিক দলগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করতো। মদিনা এ সব তৎপরতা দ্বারা কোরায়েশদেরকে বুঝিয়ে দিতে চাইত যে, আমরা ঘুমিয়ে নেই। সেই সাথে তাদেরকে এই মর্মে সাবধানও করা হতো যে, তোমরা যদি শান্তির পরিবেশ নষ্ট কর তাহলে তোমাদের বাণিজ্যিক কাফেলার চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়া হবে।
এই টহল ব্যবস্থার আওতায় রসূল সা. দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে আটজনের একটা সেনাদল কোরায়েশদেও গতিবিধি ও ভবিষ্যত পরিকল্পনার খোঁজ নেয়ার জন্য পাঠালেন। এই সেনাদলকে কোন সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়নি। কিন্তু কোরায়েশদের একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে তাদের মুখোমুখি সাক্ষাত হয়ে গেল। এই সাক্ষাতে উত্তেজনা এমন পর্যায়ে পৌঁছলো যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সেনাদল আক্রমণ চালিয়ে ওদের একজনকে হত্যা করে ফেললো। আর বাদবাকীদেরকে গ্রেফতার করে পণ্য সম্ভারসহ মদিনায় আনা হলো। এ ঘটনা যেহেতু রজব মাসের শেষে ও শাবানের শুরুতে রাতের বেলায় ঘটেছিল, এজন্য সন্দেহের সুযোগ নিয়ে একদিকে মক্কার কোরায়েশরা এবং অপরদিকে মদিনার ইহুদী ও মোনাফেকরা অপপ্রচারের তান্ডব সৃষ্টি করলো। তারা এ ঘটনাকে নিশ্চিতভাবে নিষিদ্ধ রজব মাসের সাথে সম্পৃক্ত করে জনগণকে উত্তেজিত করতে লাগলো যে, এরা আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে চায়, অথচ নিষিদ্ধ মাসেও রক্তপাত করতে দ্বিধা করেনা। (তাফীমুল কুরআন)
এই অপপ্রচারের ফল মুসলমানদের জন্য খুবই ক্ষতিকর ছিল। এই ক্ষুদ্র নবীন শক্তিটি এমনিতেই চারদিক থেকে শত্রু ও বিপদে পরিবেষ্টিত ছিল। তার জন্য যে কোন ব্যক্তি ও যে কোন মহলের সমর্থন খুবই মূল্যবান ছিল। এদের সম্পর্কে আরবে এমন ধারণা বিস্তার লাভ করা খুবই বিপজ্জনক ছিল যে, তারা নিষিদ্ধ মাসের সম্মান নষ্ট করে দিচ্ছে। কেননা নিষিদ্ধ মাসের এই সম্মান বহাল থাকার ওপরই আরবের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতি নির্ভরশীল ছিল। এতে মুসলমানদের সমর্থকরাও তাদের বিরোধী হয়ে যাওয়ার আশংকা ছিল। তাছাড়া এ বিষয়টা যেহেতু জনগণের স্পর্শকাতর ধর্মীয় অনুভূতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল, তাই এটা উস্কানির কারণও ছিল। বিশেষত এই অপপ্রচার মুসলমানদের খোদাভীতি, দ্বীনদারী ও নৈতিক দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে তাদের ওপর আস্থা নষ্ট করে দিতে সক্ষম ছিল। নাখলার এ ঘটনা আরো একটা কারণে খোদ ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টিতেই অপছন্দনীয় সাব্যস্ত হলো, রসূল সা. এই সেনাদলকে কোন সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি দেননি। যথারীতি নির্দেশ না পেয়েও এই সেনাদল এমন একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, যা ইসলামী রাষ্ট্রের টহল ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকেই পন্ড করে দিতে এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছিল, তার ক্ষতি সাধন করতে পারতো। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য অত্যধিক সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছিল। এখন যেহেতু নাখলার দুর্ঘটনা পুরোপুরি একটা বেআইনী ও নিয়ম বহির্ভূত পদক্ষেপ ছিল, তাই রসূল সা. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে কঠোর জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তাদেরকে শাস্তি দিলেন, এবং আটককৃত বন্দীদেরকে যুদ্ধবন্দী হিসেবে গ্রহণ ও তাদের পণ্য সম্ভারকে বাইতুল মালে জমা করতে অস্বীকার করলেন।
ইসলামী রাষ্ট্র নিজস্ব নিয়মশৃংখলা মোতাবেক এই নিয়মবহির্ভূত পদক্ষেপের ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সমীচীন ছিল তা গ্রহণ করেছে। কিন্তু বিরোধীরা এটা নিয়ে যে অপপ্রচার শুরু করলো, ইসলামী রাষ্ট্র অধিকতর যুক্তিনির্ভর, নৈতিক প্রভাব বিস্তারকারী ও পরিচ্ছন্ন অথচ দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে তার মোকাবেলা করলো। আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং ওহির মাধ্যমে রসূল সা. এর মুখ দিয়ে এর জবাব দেওয়ালেন যেঃ
“লোকেরা জিজ্ঞাসা করে, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা কেমন কথা! হে নবী, আপনি বলে দিন, এটা খুব অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে চলতে মানুষকে বাধা দেয়া, আল্লাহর অবাধ্যতা করা, আল্লাহর বান্দাদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে না দেয়া এবং সেখান থেকে তার অধিবাসীদেরকে বের করে করে দেয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চাইতে অনেক বড় অন্যায়। আর রক্তপাতের চেয়েও অরাজকতা মারাত্মক”। (বাকারা, ২১৭)
এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায়, ইসলাম বিরোধীদের জোরদার প্রচারাভিযানে প্রভাবিত ও বিব্রত হয়ে মুসলমানরা জিজ্ঞেস করেছিল, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ বিগ্রহ করা ইসলামের দৃষ্টিতে কেমন। যারা সততা ও শান্তিপ্রিয়তা সম্পর্কে একটা ভারসাম্যহীন ধারণা পোষন করতো এবং যারা সামান্য বিরোধিতা দেখলেই ঘাবড়ে যেত, তারা বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল যে, আমরা ইসলামের প্রকৃত চেতনা ও খোদাভীরুতা হারিয়ে ফেলছিনা তো? আমরা মাত্রাতিরিক্ত রাজনীতি প্রীতির অধীন আমাদের আসল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেরাই জনগণকে দূরে ঠেলে দিচ্ছিনা তো? এ ধরনের লোকদের বিব্রতবোধ অস্বাভাবিক ধরনের ছিল এবং তাদের মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। প্রশ্নের পেছনে এই মনমানস বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। এই প্রসঙ্গে ইসলাম বিরোধীদেরকেও দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হলো। আল্লাহ বললেন যে, মক্কার যে মোশরেকরা আল্লাহর পথে চলতে মানুষকে বাধা দেয়া, আল্লাহর অবাধ্যতা, হারাম শরীফে আগমনকারীদেরকে আসতে না দেয়া, এবং হারামবাসীকে উত্যক্ত করে হারাম শরীফ থেকে বের করে দেয়ার মত গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তারা এখন নিষিদ্ধ মাসের সম্মানের রক্ষক সেজে কোন মুখে ময়দানে আসছে। এর ভেতরে ইহুদী ও মোনাফেকদেরকেও প্রকারান্তরে বলা হয়েছে যে, তোমরা তো মক্কাবাসীর এত সব যুলুম নিপীড়ন এবং ধর্মীয় প্রতীক সমূহের পবিত্রতা বিনষ্টকারী কার্যকলাপের সময় মুখে কুলুপ এঁটে বসেছিলে এবং আজও তোমরা সে সম্পর্কে নীরব। আজ তোমরা নাখলার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার সূত্র ধরে ধর্মীয় পবিত্রতার এমন রক্ষক সেজে গেলে? অথচ এ কাজের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ কোন অনুমতি দেয়নি। বরং কতিপয় ব্যক্তির ভুলের কারণে ঘটনাটা ঘটে গেছে। এ ঘটনার সুফল গ্রহণ করতে রাষ্ট্রের শাসক অস্বীকার করেছেন এবং জড়িত ব্যক্তিদেরকে শাস্তি দিয়েছেন।
এ ঘটনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় বুঝা যায়, ইসলামের শত্রুরা কিভাবে ওৎ পেতে বসে থাকে যে, পান থেকে চুন খসলেই তারা হামলা করে দেবে। কারো দ্বারা সামান্যতম ভুলত্রুটি হয়ে গেলেই তারা তৎক্ষণাত তা সারা দুনিয়ায় নিজস্ব ব্যাখ্যার রং মেখে ছড়িয়ে দেবে।
যেখানে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি ব্যাপারে বিভ্রান্তি, খারাপ ধারণা ও উস্কানি ছড়ানোর অপচেষ্টা চলে, সেখানে শত্রু পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ইসলামী রাষ্ট্র, তার প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী আন্দোলন ও তার পরিচালক কত উদ্বেগ ও উৎকন্ঠার মধ্যে থাকেন, তা সহজেই অনুমেয়। গোটা পরিবেশ সেখানে সন্দেহ সংশয়, বিভ্রান্তির প্রশ্ন ও আপত্তিতে ভরপুর ছিল। কিন্তু এ ধরনের বাধাবিপত্তি কখনো কোন আদর্শবাদী ও চরিত্রবান সংগঠনের বিজয়কে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।
ধর্মের আড়ালে স্বার্থোদ্ধারের অপবাদ
আমি আগেই বলেছি, ইসলামের বাস্তবায়িত প্রতিটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপের ওপর ইহুদী আলেমরা একেবারেই অযৌক্তিকভাবে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল। একটা উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল ধর্মপুত্র বা মুখবলা পুত্রের মর্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত। এ নিয়েও বিরূপ প্রচারণা খুবই জোরে শোরে চালানো হয়।
পূর্বতন ধর্মীয় ও সামাজিক ধ্যান-ধারণা অনুসারে আরবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যবাহী প্রথা চলে আসছিল যে, পালিত (তথা মুখবোলা) পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা অবিকল আসল পুত্রবধুর ন্যায় অবৈধ। এই প্রথার বিলোপ সাধনের জন্য আল্লাহ তায়ালা নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে ঘটনা প্রবাহকে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে অবর্তিত করেন এবং একটা বৈপ্লবিক পরিণতিতে নিয়ে পৌঁছান। ঘটনাটা ছিল এই যে, মাত্র দশ বছর বয়সে যায়েদ বিন হারেসা ক্রীতদাসে পরিণত হন। রসূল সা. তাকে এত স্নেহ ও যত্নে লালন পালন করতে থাকে যে, তাঁর গৃহে তিনি পালিত পুত্রের মর্যাদা লাভ করেন। পরবর্তী সময় যায়েদের বাবা ও ভাই তাকে নিতে আসে এবং রসূলও সা. তাকে যাওয়ার অনুমতি দেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রসূল সা. কে যায়েদ এত গভীরভাবে ভালোবেসে ফেলেন যে, এই সম্পর্কটা ছিন্ন হওয়া তিনি মেনে নিতে পারেন নি এবং বাবার সাথে যেতে সম্মত হননি। যায়েদ ঘটনাক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হলেও আসলে সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারের সন্তান ছিলেন বিধায় মক্কার কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রসূলুল্লাহর সা. ফুফাতো বোন যয়নবকে তার সাথে বিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু যয়নবের ভাই এ বিয়েতে রাযী হননি। কেননা আরবে বিয়ের জন্য যে মাপকাঠ ও মানদন্ড চালু ছিল, এই বিয়ে সেই মানদন্ডে উত্তীর্ণ ছিলনা। জাহেলী মানসিকতার দৃষ্টিতে হযরত যায়েদের ললাটে তখনো দাসত্বের কলংক চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল। তাছাড়া তার সহায় সম্বলহীন ও চালচুলোহীন হওয়াটাও ছিল একটা আলাদা ত্রুটি। ইসলাম এসে এই মানসিকতাকেও পরিবর্তন করা জরুরী মনে করে। মানবতার বন্ধু রসূল সা. বিয়ে শাদীর পথ থেকে বংশগত বৈষম্যের বাধা অপসারণ করে সমগ্র ইসলামী সমাজকে একীভূত পরিবারে পরিণত করার চেষ্টা করেন। তাঁর এ চেষ্টার ফলে এই বৈষম্যের প্রাচীর সম্পূর্ণরূপে ধ্বসে যায় এবং ‘কুফু’ বা পরিবারিক সাম্যেও একটা নতুন অর্থের সৃষ্টি হয়। তিনি খুব গুরুত্ব দিয়ে মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টান। তিনি তাদেরকে শেখান যে, বিয়ে করার সময় সর্বপ্রথম কনের চরিত্র ও দ্বীনদারী দেখতে হবে। অন্যান্য জিনিসকে বিবেচনায় আনতে হবে এর পরবর্তী পর্যায়ে। একবার তিনি একথাও বলেন, দ্বীনদারী ও নৈতিকতার পরিবর্তে তোমরা যদি অন্য কোন মানদন্ড স্থির কর, তাহলে সমাজে বিরাট অরাজকতা ও বিশৃংখলার সৃষ্টি হয়ে যাবে। এভাবে ‘কুফু’ সম্পর্কে যে ধারণার প্রচলন ঘটে তা এই যে, জীবনের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে কে সর্বোত্তম জীবন সাথী বা জীবন সংগিনী হতে পারবে এবং কার সাথে রুচি ও মানসিকতার দিক দিয়ে সর্বাধিক বনিবনা ও একাত্মতা গড়ে ওঠবে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই জীবন সংগী নির্বাচন করতে হবে। অসংখ্য বিয়ে, বরং অধিকাংশ বিয়ে কার্যত এই নতুন দৃষ্টিভংগী অনুসারে হতে থাকে। এই মানসিক ও সামাজিক পরিবর্তন কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে, তার ধারণা হযরত আবু তালহার বিয়ের ঘটনা থেকেই পাওযা যায়। হযরত আবু তালহা নিজে কাফের থাকা অবস্থায় হযরত উম্মে সুলাইমকে রা. কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। অথচ উম্মে সুলাইম তখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি জবাব দিলেন, “তুমি এখনো কাফের রয়েছ, আর আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখন পরস্পর বিরোধী দুটো জীবন কিভাবে একত্রিত হতে পারে। তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে আমি তোমার কাছ থেকে ‘ইসলাম গ্রহণ’ ছাড়া আর কোন মোহর নেবনা।” এ জবাব থেকে বুঝা যায়, এই বিয়ের প্রস্তাব হযরত উম্মে সুলাইমের কাছেও কাংখিত ছিল। কিন্তু ইসলাম এমন বিপ্লবাত্মক মানসিকতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল যে, তিনি মনের ওপর বলপ্রয়োগ করে তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। তবে সেই সাথে ইসলামের প্রতি উৎসাহও দিলেন। শেষ পর্যন্ত আবু তালহা ইসলাম গ্রহণ করলেন। বিয়ে হয়ে গেল এবং সত্য সত্যই তাদের মোহর ধার্য হলো ইসলাম। (মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক ও উসওয়ায়ে সাহাবিয়াত, মাওলানা আব্দুস সালাম নদভী রা.)
সারকথা, বিয়েশাদীতে রুচি ও মানদন্ডে পরিবর্তন আসছিল। কিন্তু তবুও কিছু বাধা অবশিষ্ট ছিল। এ কারণেই হযরত যয়নবের ভাই প্রস্তাবিত বিয়েতে সম্মত হলেন না। রসূলও সা. চাইছিলেন যে বিয়েটা হোক। কিন্তু এর পথে যখন নিছক একটা জাহেলী মানসিকতা বাধ সাধলো, তখন এটা আল্লাহ ও রসূলের দৃষ্টিতে অবাঞ্ছিত বলে চিহ্নিত হলো। আভাসে ইংগিতে সূরা আহযাবে এর সমালোচনা করা হলো। ৩৫ নং আয়াতে বলা হলো, ‘‘মুসলিম নারী ও মুসলিম পুরুষ, মুমিন নারী ও মুমিন পুরুষ.................... এর জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন।’’ এ আয়াতের মূল বক্তব্য হলো, ইসলামী মতাদর্শ, ইসলামী মানসিকতা ও ইসলামের চরিত্রের অধিকারী মুসলমান নারী ও পুরুষ পরস্পর সম্পূর্ণ সমান ও সমমনা। তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও মমত্ব রয়েছে এবং তারা পরস্পরের কাছে কদর পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং তাদের মাঝে বংশীয় বৈষম্য ও ভেদাভেদ, কৌলিন্য ও অভিজাত্যের জাহেলী ধ্যানধারণা বাধা হয়ে দাঁড়ানো বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ইংগিত শুধু এতটুকুই ছিলনা। পরবর্তী আয়াত আরো কঠোর। তাতে বলা হলো, যখন আল্লাহ ও তার রসূল সা. কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিয়ে দেন, তখন কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর এ অধিকার নেই যে, ঐ সিদ্ধান্তের বিপক্ষে নিজের পছন্দ ও অপছন্দ এবং নিজস্ব মানদন্ডকে গুরুত্ব দেবে। এভাবে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তারা বিপথগামী হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।’’ (সূরা আহযাব-৩৬) অর্থাৎ যখন মুসলিম পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের পথ সুগম করা হয়, তখন পুরনো জাহেলী ধ্যান-ধারণাকে গুরুত্ব দিয়ে বাধার সৃষ্টি করা আল্লাহ ও রসূলের পথ নির্দেশনা ও তাদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এক ধরণের স্বেচ্ছাচার। এ ধরণের স্বেচ্ছাচারিতা পরিণামে গোমরাহীর রূপ ধারণ করে থাকে। এভাবে এ আয়াতে বেশ জোরদার আঘাত করা হয়েছে এবং তা সঠিক লক্ষ্যস্থলেই লেগেছে। যয়নবের ভাই এ আয়াতগুলো শুনে ইংগিতটা বুঝে ফেললেন এবং বিয়েতে রাযী হয়ে গেলেন। এর অর্থ দাঁড়ালো যে, জন্মগতভাবে সম্ভ্রান্ত ও অ-সম্ভ্রান্ত, এবং কুলীন ও অকুলীন হওয়ার জাহেলী মানদন্ডের শৃংখল ভেংগে গেল।
আল্লাহ তায়ালা এই ঘটনা দ্বারাই মুখবলা বা পালিত পুত্র সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাটাও বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরবর্তী সময়ে পরিস্থিতি দাঁড়ালো এ রকম যে, স্বামী স্ত্রীতে বনিবনা হলোনা। দু’জনের মধ্যে যে বাস্তব ব্যবধানটা বিদ্যমান ছিল, সেটা সম্পর্ককে প্রভাবিত করলো। রসূল সা. এর কাছে অভিযোগের পর অভিযোগ আসতে লাগলো। কিন্তু সম্পর্কের উন্নতির পরিবর্তে অবনতিই ঘটতে লাগলো। অবশেষে যায়েদ রসূল সা. এর কাছে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করতে লাগলেন। রসূল সা. খুবই বিচলিত হলেন। কারণ এমন একটা বিয়ে ভেংগে যাচ্ছে, যা সমাজে একটা বিপ্লবী দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা হয়েছিল। তাছাড়া এ বিয়েতে স্বয়ং রসূল সা. এর উৎসাহ ও পরামর্শেরও উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। তিনি যায়েদের অভিভাবক ছিলেন। তাই এ ক্ষেত্রে তার ওপর বিরাট দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তিনি বারবার এ বিয়েকে বহাল রাখার ও যায়েদকে তালাক থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এসব চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যায়েদ তাকে তালাক দিয়ে দেয়। অবশেষে প্রয়োজন দেখা দেয় যে, তিনি নিজেই যয়নবকে বিয়ে করবেন। শরীয়তের এ ক্ষেত্রে কোন বাধা ছিলনা। কিন্তু সাবেক জাহেলী ধ্যান-ধারণার কারণে আশংকা ছিল যে, জনসাধারণ হয়তো হতবাক হয়ে যাবে এবং সেই সাথে বিরোধীরা অপপ্রচারের আর একটা উপকরণ পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর পরিকল্পনা এটাই ছিল যে, জাহেলী যুগ থেকে চলে আসা পালিত পুত্র সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন খুবই স্পষ্টভাবে স্বচ্ছভাবে স্বয়ং রসূল সা. এর হাতেই সম্পন্ন করতে হবে, যাতে এই কু-প্রথার মূল সম্পূর্ণরূপে উৎপাটিত হয়ে যায়। কোরআনে আল্লাহ তায়ালা তার সুপ্ত দুশ্চিন্তাকে প্রকাশ করে দিলেন। বললেনঃ তুমি নিজের মনে যা লুকিয়ে রাখছ, তা আল্লাহ প্রকাশ করেই ছাড়বেন। তুমি মানুষকে ভয় কর, অথচ আল্লাহকেই বেশী ভয় করা উচিত।’’ (আহযাব-৩৭) মৃদু সমালোচনার ভংগিতেই বলা হয়েছে যে, তুমি এমন কথা মনে লুকিয়ে রাখছ, যা আল্লাহ প্রকাশ করে দিতে বদ্ধপরিকর। তুমি মানুষকে ভয় পাও, অর্থাৎ যে জিনিস আল্লাহর আইনে বৈধ, তাকে সমাজের জাহেলী ধ্যান-ধারণার আশংকায় মনে লুকিয়ে রাখা আল্লাহ পছন্দ করেন না। এটা প্রকাশ পাওয়া দরকার, ‘‘যাতে মুখবলা ছেলেরা তাদের স্ত্রীদেরকে পরিত্যাগ করলে তাদের ব্যাপারে মুমিনদের ওপর কোন বিধিনিষেধ না থাকে।’’ (আহযাব-৩৭) অর্থাৎ মুখবলা ছেলেদের ব্যাপারে সমাজে প্রচলিত প্রচীন কড়াকড়িকে মুসলমানদের ওপর থেকে চিরতরে তুলে দেয়াই এর উদ্দেশ্য। জাহেলিয়াতের এই শেকল ভাঙ্গার জন্য এভাবেই চূড়ান্ত আঘাত হানা হলো যে, আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে রসূল সা. এর সাথে হযরত যয়নবের বিয়ে দিয়ে দিলেন।
এ ঘটনাটা ঘটার সাথে সাথেই মদিনার ইসলাম বিরোধী মহলে হৈ চৈ পড়ে গেল। তারা এ বলে প্রচারণা চালাতে লাগলোঃ ‘‘দেখলে তো ধার্মিকতা ও পবিত্রতার ভড়ং? পালিত ছেলের বউকে উনি কিনা বিয়ে করে ফেললেন!” এই সাথে কাহিনীটাকে চটকদার ও মুখরোচক করার জন্য নানা রকমের গল্প বানানো হলো। দুর্মুখ ইহুদী ও মোনাফেকরা তখন গুজবও ছড়াতে লাগলো যে, (নাউযুবিল্লাহ) ‘‘আসলে উনি পুত্রবধুর প্রেমে মজে গিয়েছিলেন আর কি! এ জন্য তালাক দিতে বাধ্য করেছেন এবং তারপর নিজেই বিয়ে করে ফেলেছেন।’’ [উল্লেখ্য যে, আধুনিক কালের কিছু বিদ্বেষপরায়ণ ওরিয়েন্টালিস্ট ইসলামী আন্দোলনের তৎকালীন কট্টর দুশমনদের আরোপিত সমস্ত নোংরা অপবাদকে ইতিহাস থেকে হুবহু গ্রহণ করেছে। এই ঘটনাটাও ঐসব বিদ্বান ও গবেষকদের কাছে অত্যন্ত স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং একে অধিকতর মুখরোচক বানিয়ে তাদের বই পুস্তকে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ সা. নাকি হঠাৎ করেই যয়নবকে দেখে ফেলেন এবং প্রেমে মজে যান। একটু ভেবে দেখা দরকার, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিষ্কলংক যৌবন নিয়ে সার্বক্ষণিক চেষ্টাসাধনা ও অবিশ্রান্ত ব্যস্ততায় পুরো জীবনটা কাটিয়ে দিলেন এবং যিনি একটা মুহূর্ত স্বস্তিতে কাটাতে পারলেন না, তার চরিত্র পরিপক্কতার চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে এতই ঠুনকো হয়ে গেল যে, একটা মাত্র দৃষ্টিতে প্রেমে দিশেহারা হয়ে গেলেন? তার সামগ্রিক চরিত্রের সাথে কি এ অপমান আদৌ খাপ খায়? তাছাড়া হযরত যয়নব রসূল সা.-এর আপন ফুফাতো বোন ছিলেন এবং শৈশব থেকেই তার সামনে হেসে খেলে বড় হয়েছেন। তার অস্তিত্বতো রসূল সা. এর কাছে নতুন কিছু নয়। এটাও বাস্তব ঘটনা যে, তিনি নিজেই অনেক চেষ্টা করে যায়েদের সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই বিয়েতে তিনিই ছিলেন যায়েদের অভিভাবক। এসব অকাট্য তথ্যের সামনে কি এই মনগড়া কাহিনীর আদৌ কোন ভিত্তি খুজে পাওয়া যায়, যা মদিনার ইহুদী ও মোনাফেকরা তৈরী করেছিল এবং যাকে পুনরায় ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছে? যুক্তি (Rationalism) ও গবেষণার (Research) দাবীদারদের নিজস্ব মানদন্ডে কি এই কল্পকাহিনী উত্তীর্ণ হয়?]
বিয়েটাও যা তা বিয়ে নয়, একেবারে আকাশেই সম্পাদিত। এ বিয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নাকি ইচ্ছেমত ওহিও নাযিল করিয়ে নিয়েছেন। ইতিপূর্বে আকীদা ও ফেকাহ শাস্ত্রীয় ব্যাপারে অনেক বৈরী প্রচারণা চালানো হয়েছিল। কিন্তু এই ঘটনা নিয়ে তো সত্য সত্যই নোংরা প্রচারণা চালানো হয়েছে এবং রসূল সা. এর চারিত্রিক মহাত্ম্যের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছে। এ কথা সুবিদিত যে, কোন সংস্কারমূলক ও গঠনমূলক আন্দোলনের বিরুদ্ধে নৈতিক দিক দিয়েই সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ চালানো সম্ভব। কোন দাওয়াতে শীর্ষ নেতা সম্পর্কে যদি বিরোধীরা এরূপ প্রচারণায় লিপ্ত হয় যে, সে একজন লম্পট, সে নিজের প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার জন্য যেকোন পন্থা অবলম্বন করতে দ্বিধা করেনা, এবং সে কোন চারিত্রিক মানের প্রতি সম্মান দেখায়না, তা হলে এর চেয়ে ক্ষতিকর আঘাত আর কিছু হতে পারেনা। সহজেই অনুমেয় যে, শত্রুরা মদিনায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কত নোংরা প্রচারণা চালিয়েছে এবং মানবতার এই সর্বশেষ্ঠ শুভাকাংখীর কয়েকটা দিন কিরূপ মানসিক যন্ত্রণায় কেটেছে।
ইহুদীদের এই অপপ্রচার নিরীহ ও সরলমনা মুসলমানদের জন্যও অত্যধিক বিব্রতকর ছিল বলে মনে হয়। চলার পথে হয়তো তাদেরকে অনেক আজে বাজে কথা বলে উত্যক্ত করা হতো এবং তাদের মনে নানা রকম সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি চেষ্টা করা হতো। কোন কোন অপরিপক্ক মুসলমান হয়েতো এর ফলে ঘাবড়ে যেত। তাদের মধ্যে অনুপ্রবেশকারী মোনাফেকরা হয়তো আপন সেজে অনেক উল্টাপাল্টা কথা ছড়াতো। এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা মুসলমানদের সান্ত্বনা ও প্রশিক্ষণার্থে কয়েকটা বিষয় তাদের মনে বদ্ধমূল করে দিলেন। তাদের জানিয়ে দিলেন যে, নবী সা. এর জন্য আল্লাহ যা বৈধ করেছেন, তার ব্যাপারে তার ওপর আর কোন বিধিনিষেধ নেই। (সূরা আহযাব-৩৮) এই পদক্ষেপের উদ্দেশ্যই জানিয়ে দিলেন যে, মুসলমানদের ওপর তাদের পালিত পুত্রদের তালাক দেয়া স্ত্রীকে বিয়ে করায় কোন বাধা না থাকে। (সূরা আহযাব-৩৭) এ কথাও ঘোষণা করে দিলেন যে, মুহাম্মাদ সা তোমাদের পুরষদের কারো পিতা নন। (সূরা আহযাব-৪০) সবার শেষে স্বয়ং রসূলকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি কাফের ও মোনাফেকদের অনুসরণ করোনা। এবং তাদের অপপ্রচারে মর্মাহত হয়োনা। আল্লাহর ওপর ভরসা কর। আল্লাহই যথেষ্ট।’’ (সূরা আহযাব-৪০) এভাবে অত্যন্ত শান্ত ও শালীন পন্থায় এই ঘৃণ্য ও নোংরা অপপ্রচারের জবাব দেয়া হলো, যা ইহুদীরা অত্যন্ত হীন উদ্দেশে চালিয়েছিল।
আরো একটা নোংরা অপপ্রচার
উপরোক্ত ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ইসলামী আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে যখন কোন দিক দিয়েই হামলা করে ক্ষতিগ্রস্থ করার সুযোগ পাওয়া যায়না, তখন শয়তান তাকে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার প্ররোচনা দেয়। আর শয়তানের দৃষ্টিতে পিঠের দিক দিয়ে আঘাত করার সর্বোত্তম পন্থা হলো, এর নেতার ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের ওপর কলংক লেপন করা। এ জন্যই এক পর্যায়ে ক্ষমতার মোহ এবং আর এক পর্যায়ে স্বর্থপরতার জঘন্য অপবাদ আরোপ করা হয় রসূল সা. এর বিরুদ্ধে। এরপর অপপ্রচারণার এই ধারা আরো সামনে অগ্রসর হয় এবং ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতার পরিবারকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। অথচ এই পরিবারকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সমগ্র মুসলিম উ্ম্মাহর জন্য সামাজিক ও নৈতিক দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় নমুনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এই পরিবারকে কেন্দ্র করেই ইসলামী সমাজের অবকাঠামো তৈরী হচ্ছিল। আর এই পরিবারের কেন্দ্রের ওপর আঘাত হানাই ছিল ঐ অবকাঠামোকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। শেষ পর্যন্ত নাশকতাবাদী শক্তি এই শেষ আঘাতটা হানতেও দ্বিধা করলোন। এই বৈরী আঘাতের মর্মন্তুত কাহিনী কোরআন, হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতে গ্রন্থাবলীতে ‘‘ইফকের ঘটনা’’ তথা ‘‘হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদের কাহিনী’’ নামে শিক্ষা গ্রহণের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে।
মূল ঘটনার তথ্যাবলী তুলে ধরার আগে আমি একথা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন মনে করি যে, এমন জঘন্য অপবাদের ভয়াবহ তান্ডব ইসলামী আন্দোলনের গড়া সৎ ও পূণ্যময় সমাজে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুসংগঠিত দলের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হতে পারলো কিভাবে? কোন্ ছিদ্রপথ দিয়ে এই ভয়াবহ ঝড় ইসলামী সংগঠনের সুরক্ষিত দুর্গে ঢুকলো এবং কিছু সময়ের জন্য তা চরম বিভীষিকার সৃষ্টি করার সুযোগ পেল?
বিভ্রান্তি সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ
ইসলাম সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে নাশকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্য শয়তানের একটা বিশেষ ধরণের অনুকূল পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন। এই পরিবেশ সমাজের শৃংখলা ও নৈতিকতার কোন ত্রুটির কারণেই সৃষ্টি হোক, অথবা পরিস্থিতি ও পরিবেশগত বাধ্যবাধকতার কারণেই জন্ম নিক, বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ তৈরী হলেই শয়তানের চক্রান্ত কিছুটা ফলপ্রসু হতে পারে। আল্লাহর প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনার ধারায় শয়তানের জন্য কাজ করার কিছু ফাঁকফোকর অবশ্যই থেকে যায়, চাই তা যত বড় আদর্শ সমাজই হোক না কেন। আসলে মানুষের স্বভাব প্রকৃতিতে কিছু কিছু দুর্বলতা এমন থাকে, যার মধ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ও ফেলনা প্রবেশের সুযোগ পায়। রসূল সা. এর প্রতিষ্ঠিত সমাজের ব্যাপারেও এমন গ্যারান্টি দেয়া সম্ভব নয় যে, তার অভ্যন্তরে নৈরাজ্যবাদী শক্তি কাজ করার কোন সুযোগই পাবেনা। একজন মানুষ যত স্বাস্থ্যবানই হোক, তার কখনো কখনো জ্বর, কাশী ও সর্দিতে আক্রান্ত হওয়া যেমন সম্ভব, তেমনি একটা পবিত্রতম সমাজেরও রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া সম্ভব। একটা সুস্থ্য ও সজীব সমাজের কাছ থেকে যেটা প্রত্যাশা করা যায় তা হলো, সে সব সময় রোগের প্রতিরোধ ও রোগ জীবানু ধ্বংস করার কাজে ব্যাপৃত থাকবে। কিন্তু সে সমাজে কখনো কোন রোগের প্রাদুর্ভাবই ঘটবেনা, এমন প্রত্যাশা করা যায়না। শয়তানের জন্য কোন সমাজে সবচেয়ে অনুকূল পরিবেশ হয়ে থাকে গোপন সলাপরামর্শ ও ফিসফিসানির পরিবেশ। কোন সামষ্টিক ব্যবস্থায় যখন সমগ্র জনতার সামনে খোলাখুলি মতামত, পরামর্শ, সমালোচনা ও প্রশ্ন করার পরিবর্তে বিভিন্ন ব্যক্তি আলাদা আলাদাভাবে বসে গোপন সলাপরামর্শ করে, তখনই এই পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কোরআনে এ জিনিসটাকে ‘নাজওয়া’ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বস্তুত নাজওয়া আসলে সামষ্টিক জীবনে একটা বিপজ্জনক পথে যাত্রা শুরু করার নাম। প্রকাশ্যে কাজ করতে মানুষ যখন সংকোচ বোধ করে তখন বুঝতে হবে এর পেছনে কিছু ব্যাপার অবশ্যই আছে। স্বচ্ছতা এগিয়ে গোপন সলাপরামর্শ ও ফিসফিসানির এই প্রবণতাই শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ও যোগসাজসে রূপান্তরিত হয়।
দুর্ভাগ্যবশত রসূল সা. এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত আন্দোলনের ভেতরে ইহুদীদের নেতৃত্বে মোনোফেকরা এই ফিসফিসানির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের অনবরতই বিব্রত করতে থাকে। যারা এই পরিবেশ সৃষ্টি করছিল, কোরআন তাদেরকেও সংশোধন করতে থাকে। আর ইসলামী সংগঠনের পরিচালকদেরও সতর্ক করতে থাকে। কোরআন বলেঃ
‘‘তোমরা দেখতে পাওনা, যাদেরকে গোপন সলাপরামর্শ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল, তারা আবারো সেই নিষিদ্ধ কাজের পুনরাবৃত্তি করছে? তারা পরস্পরে অপকর্ম, অহংকার ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণের ব্যাপারে গোপন পরামর্শে লিপ্ত থাকে। (সূরা মুজাদালা-৮)
‘‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখনই পৃথকভাবে পরস্পরে পরামর্শ কর তখন অসৎ কাজ, অহংকার ও রসূলের অবাধ্যতার পরিকল্পনার করোনা। বরং সততা ও খোদাভীতির জন্য পরামর্শ কর।’’ (সূরা মুজাদালা-১)
‘‘ফিসফিসানি মুমিনদেরকে উত্যক্ত করার জন্য পরিচালিত শয়তানী কাজ। অবশ্য আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন জিনিসই তাদের ক্ষতি করতে পারেনা।’’ (সূরা মুজাদালা-১০)
‘‘এই সব গোপন পরামর্শকারীরা মানুষের চোখের আড়ালে যেতে পারে, কিন্তু আল্লাহর চোখ থেকে লুকাতে পারেনা। তারা যখন রাতের অন্ধকারে ও নিভৃতে আল্লাহর অপছন্দনীয় কথাবার্তা বলে, তখন আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন।’’ (সূরা নিসা-১০৮)
‘‘গোপন সলাপরামর্শের জন্য যখনই তিনজন মানুষ একত্রিত হবে, তখন সেখানে আল্লাহ হয়ে থাকেন চতুর্থজন, পাঁচজন জমায়েত হলে আল্লাহ অবশ্যই তাদের সাথে থাকেন, চাই তারা যেখানেই যাক না কেন।’’ (সূরা মুজাদালা-৭)
‘‘তারা মুখে বলে, আমরা (সামষ্টিক ফায়সালা ও নেতার আদেশের) আনুগত্য করবো। কিন্তু যখন তারা তোমার কাছ থেকে বের হয়, তখন তাদের একটা দল রাতের বেলা তোমার কথাগুলোর বিরুদ্ধে সলাপরামর্শে লিপ্ত হয়। আর আল্লাহ তাদের পরিকল্পনাগুলো লিখে রাখেন।’’ (সূরা নিসা-৮)
এ আয়াতগুলোতে দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলে দেয়া হয়েছে, ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র ও সংগঠন সামষ্টিকভাবে যে স্থিরকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে চলে এবং যে সব সামাজিক ফায়সালা ও দলীয় ঐতিহ্য চালু থাকে, তার সমর্থন, আনুগত্য, বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য লোকেরা আলাদাভাবে পরস্পরে গোপন বা প্রকাশ্যে স্বাধীনভাবে আলাপ আলোচনা করতে পারে। কিন্তু এগুলোকে অমান্য করা, দ্বিমত পোষণ করা, ব্যর্থ করা, এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করা, আপত্তি তোলা ও ব্যর্থ করে দেয়ার জন্য পরস্পরে আলাদা হয়ে গোপন পরামর্শ করা ও কানাঘুষা করা এমন জঘণ্য গুনাহ যা এসব ব্যক্তির চরিত্র ও পরিণামকে ধ্বংস করে দেয় এবং গোটা সামাজিক ব্যবস্থাকে বিব্রত ও সমস্যায় জর্জরিত করে। গোপন বিদ্রোহী ও ফিসফিসানির আসল প্ররোচনাদাতা শয়তান। এই প্ররোচনা থেকে কোরআন ইসলামী সংগঠনকে সাবধান করে দিয়েছে।
গোপন সলাপরামর্শ ও কানাঘুষার একটা বিষয় ছিলো “রাসুলের আদেশ অমান্য করা”। আসলে এটাই ছিলো কেন্দ্রীয় বিষয়। মদীনার ইসলামী আন্দোলনের আওতাধীন পরিবেশে এর আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিলো না যে, খোদ আন্দোলন এবং তার আদর্শ ও লক্ষ্যকে অপপ্রচারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে এবং আল্লাহর নাফরমানী ও তার কিতাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কোন পদক্ষেপ নেয়া হবে। মোনাফেকদের জন্য বড়জোর এতোটুক বিভ্রান্তি সৃষ্টির সুযোগ ছিলো যে, ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্বের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতে পারতো এবং সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারতো। একটি নৈতিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার সবচেয়ে কার্যকর ও সহজ পন্থা এটাই হতে পারে যে, তাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির বিরুদ্ধে দুর্নাম রটানো হোক।
এ প্রসংগে আমি আগেই বলেছি, স্বার্থপরতা ও গদির লোভ সংক্রান্ত অপবাদ আগেই আরোপ করা হয়েছিলো। কিন্তু আসলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আরোপের মধ্যেই এটা সীমিত ছিলো না বরং গুজব রটানোর একটা অভিযান (Whispering campaign) এবং ‘ঠান্ডা লড়াই’ স্থায়ী রূপ ধারণ করেছিলো।
উদাহরণ স্বরূপ, পরবর্তীকালে যখন যাকাত ও বন্টনের ব্যবস্থা আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হলো, তখন রসুল সা. এর প্রতি একটা হীন অপবাদ এই মর্মে আরোপ করা হলো যে, তিনি বায়তুল মালে জমাকৃত অর্থ নিজের খেয়াল খুশী মোতাবেক আত্মসাত করে ফেলেন। ব্যাপারটা ছিলো এই যে, সকল সঞ্চিত সম্পত্তি, বাণিজ্যিক পুজি, গবাদিপশু ও কৃষিজাত সম্পদ থেকে যখন নিয়মিতভাবে যাকাত ও উশর আদায় করা হতে লাগলো, তখন বিপুল সম্পদ একই কেন্দ্রে জমা হতে লাগলো এবং রসুল সা. এর হাতে তা বন্টিত হতে লাগলো। ধন সম্পদের এই বিপুলাকৃতির স্তুপ দেখে ধনলোভীরা লালায়িত হয়ে উঠতো। তারা চাইতো জাহেলী যুগের ন্যায় আজো এই সম্পদ তাদের ন্যায় ধন্যাঢ্যদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হোক। কিন্তু ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পদকে দরিদ্রমুখী করে দেয়। বিত্তশালীরা এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনে দারুণভাবে অসন্তুষ্ট ছিলো। তারা ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরতো আক্রমণ চালাতে পারতো না, যা তাদের পকেট ভর্তি করার পরিবর্তে তাদের কাছ থেকে আইনের জোরে ‘যাকাত’ নামক ‘জরিমানা’ আদায় করছিল। তারা মনের আক্রোশ মেটাতে রসুল সা. কে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিনত করতো। তারা বলতো, রসুল সা. নিজের সমর্থক ও আত্মীয় স্বজনের পেছনে সম্পদ ব্যয় করছেন এবং বিশেষভাবে মুহাজিরদের অকাতরে দান করছেন। অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কোষাগারের অর্থে পরিবার পরিজন ও স্বজন তোষণ করছেন। আল্লাহর নামে সাধারণ মানুষের কষ্টার্জিত সম্পদ কেড়ে নিচ্ছেন এবং সেই অর্থ নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও আধিপত্য বিস্তারে ব্যয়িত হচ্ছে। সরকারী কোষাগারের অর্থ সম্পর্কে যে কোন শাসন ব্যবস্থায় শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপিত হলে তা গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু বিশেষভাবে একটা ধর্মীয় ও নৈতিক সমাজ ব্যবস্থায়, যেখানে কোষাগারকে আল্লাহর সম্পদ বলা হয়ে থাকে এবং যার প্রতিটি আয় ব্যয় আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে পরিচালিত হয়ে থাকে, সেখানে এ ধরনের অভিযোগ থেকে নিদারুণ উত্তেজনা সৃষ্টি করা সম্ভব।
ভাববার বিষয় হলো এই অপবাদ সেই আদর্শ মানুষের বিরুদ্ধে আরোপ করা হচ্ছে যিনি যাকাত সাদাকার অর্থকে শুধু নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য নয় বরং গোটা বনু হাশেম গোত্রের জন্য আইনত হারাম করে দিয়েছেন। এমন নিঃস্বার্থ ব্যক্তির তুলনা সমগ্র মানবেতিহাসেও হয়তো কোথাও পাওয়া যাবে না। অথচ সে উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের ললাটেও নিতান্ত হীন চরিত্রের চুনোপুটিরা কালিমা লেপনের ধৃষ্টতা দেখালো।
এই লোকদের পরিচয় কোরআন এভাবে দিয়েছে যে, তারা নিজেদের জঘন্য কথাবার্তা দ্বারা রসুলের সা. মনে কষ্ট দেয় (সুরা তাওবাহ)। অর্থাৎ আন্দোলনের সামষ্টিক সমস্যাবলী নিয়ে খোলা মনে মুক্ত পরিবেশে কথা বলার পরিবর্তে তারা শ্রেষ্ঠতম নেতার ব্যক্তিত্বকে ঘায়েল করতে থাকে। এই ঘায়েল করার একটা দৃষ্টান্ত কোরআন নিজে তুলে ধরেছে। ঘটনা ছিলো এই যে, ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে মুনাফিকদের কার্যকলাপ ও চালচলন এমনই একটা বেখাপ্পা জিনিস ছিলো যে, তা মুমিনদের কাছে খুবই বিরক্তিকর লাগতো। মুমিনরা এসব চালচলন দেখে খুবই বিব্রতবোধ করতেন। তদুপরি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করাও ছিলো মুশকিল, আবার তা নীরবে বরদাশত করাও ছিলো দুরহ। বেচারা মুসলমানরা আর কী করবে? তারা জামায়াতী দাবী অনুযায়ী বাধ্য হয়ে মুনাফিকদের অশোভন তৎপরতা সম্পর্কে রসুল সা. কে অবহিত করতেন। এভাবে প্রত্যেক মুনাফিক ক্রমান্বয়ে সমাজে চিহ্নিত হয়ে যেতো এবং তার সম্পর্কে রসুল এক বিশেষ ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। এই প্রতিক্রিয়া প্রথমে অত্যাধিক কোমল এবং পরে ক্রমান্বয়ে কঠোর হতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মোনাফেকীর ব্যধিতে আক্রান্তরা নিজেদের অবহেলিত ও কোনঠাসা অনুভব করে বলাবলি করতে লাগলো যে, (নাউযুবিল্লাহ) রসুলুল্লাহর কোন বিচারবুদ্ধি নেই, যার কাছে যা শোনেন তাই বিশ্বাস করে ফেলেন। মামুলী ধরনের লোকেরা, যারা আমাদের তুলনায় কোন ব্যক্তিত্বের অধিকারীই নয়,তারা রসুল সা. এর কাছে চলে যায়, যার সম্পর্কে যা ইচ্ছা বলে আসে এবং তিনি সব কথাই তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বাস করে ফেলেন। সর্বোচ্চ নেতার এই দুর্বলতার কারণে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি। আজ আমাদের বলা হয় মোনাফিক ও কুচক্রী। আর সেদিনকার উপোষ করা গোলাম ছোকড়াগুলো হয়ে গেছে ওঁর ঘনিষ্ঠতম সাথী।
এ ধরনের পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবেই সম্ভবত মোনাফেকদের একটা দল একবার রসুল সা. এর সাথে পৃথকভাবে এক আলোচনা বৈঠকে মিলিত হয়। বৈঠক চলাকালে এক একজন মুনাফিক হঠাৎ বলে উঠতো আমার একটু নিভৃতে আপনার সাথে কিছু কথা আছে। রসুল সা. সৌজন্যের খাতিরে সবার জন্য এই সুযোগ উন্মুক্ত রাখতেন। কিন্তু নিভৃতে বিশেষ কথা বলার এই নাটকীয় ধারার ভিন্নতর উদ্দেশ্য ছিলো। এ দ্বারা মুনাফিকরা সাধারণ মুসলামানদের উপর নিজেদের প্রতিপত্তি জমাতে চাইতো এবং এই ধারণা দিতে চাইতো যে, আমরা অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা ভি আই পি গোছের লোক। আমরা শুধু সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বোচ্চ নেতার সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথাবার্তা বলে থাকি। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকতো রসুল সা. এর দৃষ্টিতে কৃত্রিম উপায়ে নৈকট্য লাভ করা এবং যতদূর সম্ভব নিষ্ঠাবান মুমিনদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে তাদের এবং সেই অবহেলিত ও কোনঠাসা অবস্থা কিছুটা হালকা করা যা তাদেরই অপকর্মের ফলেই উদ্ভুত হয়েছিলো। কিন্তু রসুল সা. এর সৌজন্য মুনাফিকদের কাল ক্ষেপণের যে অবাধ সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিলো, তাকে আল্লাহ তায়ালা নিন্মোক্ত আদেশ দ্বারা রহিত করে দিলেনঃ
“হে মুমিনগণ, তোমরা যখন রসুল সা. এর সাথে (বিশেষ সময় নিয়ে) নিভৃত আলোচনায় মিলিত হতে চাও, তখন আলোচনার পূর্বে সাদাকা দিও।” – (মুজাদালাহ-১২)
এই আদেশে ঘোরতর কৃপণ স্বভাবের মুনাফিকদের কোমর ভেঙ্গে গেলো এবং বারবার বিশেষ সময় নিয়ে আলোচনার ধারা থেমে গেলো। তবে এই কাজটা এই ধারণার ভিত্তিতেই শুরু হয়েছিলো যে, আন্দোলনের নেতা খুবই সরল বিশ্বাসী। কাজেই নিষ্ঠাবানদের মোকাবেলায় আমরাও তার তার কানে নানা কথা ঢুকিয়ে তাকে নিজের পক্ষে নেয়ার চেষ্টা করবো। কিন্তু তারা ধারণাও করতে পারেনি যে, একনিষ্ঠ মুমিনদের জন্য তিনি যেমন সরল বিশ্বাসী ছিলেন, তেমনি কুচক্রীদের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। যা হোক একথা সহজেই বোঝা যায়, যারা ইসলামী সংগঠনের মধ্যে বসে তার সর্বোচ্চ নেতার বিরুদ্ধে এ ধরণের তাচ্ছিল্যপূর্ণ কথা বলে বেড়াতো তাদের মধ্যে নিয়ম শৃংখলার প্রতি যথাযথ ভালোবাসা ও আনুগত্য থাকা সম্ভব নয়। অথচ এই আনুগত্য ও ভালোবাসাই দলের কর্মীদের সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল বানিয়ে থাকে। একটা ধর্মীয় ও নৈতিক সংগঠনে যারা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে ও কানাঘুষায় লিপ্ত থাকে তারা প্রকৃতপক্ষে ঐ সংগঠনকে ধ্বংস করার অপচেষ্টায়ই নিয়োজিত থাকে।
ইসলামী আন্দোলন যখন দাওয়াত ও প্রচারের স্তর থেকে জিহাদের স্তরের দিকে বৈপ্লবিক মোড় নিচ্ছিলো, তখন বিপুল সংখ্যক মোনাফেক আত্মপ্রকাশ করে। এ ধরনের মোড় নেয়ার সময় সব আন্দোলনেই কিছু লোক হতবুদ্ধি ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে কেবল সেইসব কর্মীই ভারসাম্য রাখতে পারে, যারা আগে থেকেই শুনে আসে যে, তারা কোন দিকে চলেছে এবং পথে কোন কোন মঞ্জিল তাদের অতিক্রম করতে হবে। নচেৎ দুনিয়ার সব আন্দোলনেরই অবস্থা এ রকম হয়ে থাকে যে, কোন বড় মোড় যখন সামনে আসে এবং লাফ দিয়ে এক স্তর থেকে অন্য স্তরে প্রবেশ করতে হয়, তখন এই পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকে যাদের বুঝ নেই, তারা অকর্মন্য ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। এ ধরনের ঐতিহাসিক ঘটনায় অনেক সময় ভালো ভালো কর্মী জটিলতার শিকার হয়ে ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ে। ইসলামী আন্দোলনে এই ব্যপারটাই ঘটেছিলো। আন্দোলন প্রচারের স্তর থেকে সংগ্রামের স্তরে প্রবেশ করলে কিছু লোক মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। বিশেষত যারা জিহাদের দুঃসহ বোঝা বহনে প্রস্তুত ছিলো না, তারা চিরদিনের জন্য মুনাফিক হয়ে গেলো। এই পরিস্থিতির জন্য আগে থেকে মন মানসকে প্রস্তুত না রাখায় তাদের এই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছিলো।
কোরআনে বলা হয়েছে, এক শ্রেণীর লোককে প্রাথমিক যুগে আদেশ দেয়া হয়েছিলো যে, “তোমাদের হাত সংযত রাখো”। অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে গিয়ে যুলুম ও বাড়াবাড়িকে বরদাশত করে যাও এবং সংঘাতে যেওনা। কেবল নামাজ কায়েম কর ও যাকাত দেয়ার মতো কার্যকলাপে লিপ্ত থাকো (নিসা- ৭৭)। কিন্তু সেই পর্যায়ে এই আদেশ তাদের মনঃপূত ছিলো না। পরবর্তী পর্যায়ে ঐ লোকদেরই যখন জিহাদের আদেশ দেয়া হলো, অমনি তারা মানুষকে এতো ভয় পেয়ে গেলো যে, তাদের কর্মতৎপরতাই থেমে গেলো। তাদের মানসিক প্রতিক্রিয়া এরূপ ছিলো যে, আল্লাহকে তারা বললো, হে আল্লাহ আমাদের উপর যুদ্ধ কেনো ফরজ করলে? আমরা আরো কিছু দিন দাওয়াত দিতাম, নামাজ ও যাকাত দ্বারা চরিত্র শুদ্ধির কাজ করে নিতাম, চাদা তোলা ও গঠন মূলক কাজ চালিয়ে যেতাম। এক স্তরেই চাহিদা পূরণ হলো না, সময় হওয়ার আগে আরেক স্তরের কাজ চাপিয়ে দিলে!
কিন্তু তারা ছিলো অসহায়। আল্লাহর সাথে তর্ক বিতর্ক ও করতে পারছিলো না। তার আদেশ জারী করাও ঠেকাতে পারছিলো না। তাদের সামনে ছিলো শুধু রসুল সা. এর ব্যক্তিত্ব। তাই তারা তাকে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেনি। প্রতিটি লড়াই থেকে তারা পালিয়েছে এবং প্রত্যেক নাজুক ঘটনায় তারা নানারকম ছলছুতোঁর আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহর আরোপিত দায় দায়িত্বের প্রতিশোধ তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতার কাছ থেকে পুরোদমে নিয়ে নিয়েছে।
যেকোন আন্দোলন যখন সঙ্ঘাতে লিপ্ত হয়, তখন তার পতাকাবাহীরা শত্রুর উপর যেমনি আঘাত আনে তেমনি নিজেরাও আঘাত খায়। কোন আঘাত সফল হয় আবার কোনটা হয় ব্যর্থ। ফলাফল কখনো আশানুরুপ হয় কখনো হয় হতাশাব্যঞ্জক। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন লড়াইয়ের ময়দান পাওয়া যায়নি, যেখানে সব সময় কেবল এক পক্ষই জয় লাভ করে। যে পক্ষ জয়লাভ করে সেও বহু প্রাণ বিসর্জন দিয়ে বিজয়েরর মূল্য পরিশোধ করে, অনেকে আহত হয় এবং অনেক সম্পদ বিনষ্ট হয়। মদীনার ইসলামী আন্দোলনের কর্মরত মোনাফেকদের (...............।) “প্রত্যেক দুঃখের সাথেই অবশ্যই সুখ রয়েছে” এই দর্শনে আস্থা ছিলো না। তারা প্রত্যেক ক্ষয়ক্ষতি ও প্রত্যেক আঘাতে চিৎকার করে উঠতো যে, এটা আন্দোলনের নেতার প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার অভাবের কারণেই হয়েছে। (নাউজুবিল্লাহ ) কোরআনে তাদের এই কর্মবিমুখ দার্শনিক প্রচারণার উন্মেষ এভাবে করা হয়েছে,
“তারা যদি সাফল্য লাভ করে তবে বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, আর কোন ক্ষতির সম্মুখীন হলে বলে, এটা তোমার (রসুল সা.) কারণে হয়েছে”। (সুরা নিসা-৭৮)
অর্থাৎ বিভিন্ন সঙ্ঘাতে সঙ্ঘর্ষে যে আঘাতই আসতো, যে ক্ষয় ক্ষতিই হতো, যে ত্যাগ কুরবানীরই প্রয়োজন পড়তো এবং যেসব চেষ্টা তদবীরে আশানুরূপ ফল ফলতো না সে সব কিছুর জন্য তারা রসুল সা. কে দায়ী করতো। ভাবটা এমন ছিলো যে, ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী সংগঠনের নিয়ম শৃংখলা সবই চমৎকার কিন্তু যিনি এর নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি অদক্ষ। কিছুটা খোদাভীতির পরিচয় ও দেয়া হয়েছে একথা বলে যে, সাফল্য যেটুকু আসছে তা আল্লাহরই দান। যেন প্রচারণাটা শুধু দার্শনিকই নয় বরং খোদাভীতিমূলকও। কিন্তু এই ভন্ডামীপূর্ণ খোদাভীতি রসুল সা. এর ন্যায় নেতার প্রতি এতটুকু আনুগত্য ও শুভাকাংখিতাও দেখাতে পারলো না, যা ইসলাম একজন নিগ্রো কৃতদাসের নেতৃত্বের প্রতি দেখানোর আদেশ দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল ও ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠতম নেতার প্রতি আনুগত্যহীনতা দেখিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই ব্যর্থ চেষ্টার মতো আত্মপ্রবঞ্চণা আর কী হতে পারে এবং মানুষ নিজের ধ্বংসের জন্য এর চেয়ে ভয়াবহ আর কী উপকরণ সংগ্রহ করতে পারে?
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যে সাফল্যকে তারা আল্লাহর দান বলে স্বীকার করতো সেটা কৃতজ্ঞতা ও নিয়ামাতের স্বীকৃতির কারণে নয় বরং এর দ্বারা তারা এ কথা বুঝাতো যে পরিস্থিতির কারণে সময়ে সময়ে যে ভালো দিক ফুটে উঠে এবং যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে সময়ে সময়ে যে সুফল পাওয়া যায় তাতে রসুল সা. এর অন্তদৃষ্টি ও বিচক্ষণতার কোন হাত নেই বরং ওগুলো আল্লাহর সৃষ্টি করা কাকতালীয় ঘটনামাত্র। [সুরা নিসার সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীর মুযিহুল কুরআনেও একই কথা বলা হয়েছে। যুদ্ধের কৌশল নির্ভুল প্রমানিত হলে এবং বিজয় অর্জিত হলে মুনাফিকেরা বলতো, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটনা ক্রমে ঘটে গেছে। রসুল সা. এর রণ নৈপূণ্যের স্বীকৃতি দিতো না। আর যদি পরাজয় ঘটতো তাহলে রসুল সা. এর অদক্ষতাকেই দায়ী করতো।]
প্রত্যেক কষ্টের সময় আন্দোলনের ভেতরেই সমালোচনা, উপহাস তাচ্ছিল্য প্রকাশকারী তথাকথিত সহচর উপস্থিত থাকায় ইসলামী আন্দোলনের সর্বোচ্চ নেতাকে কী ধরনের মর্মপীড়া ভোগ করতে হতো তা সহজেই বোধগম্য। কথায় কথায় তারা বলতো, এই নেতার কারনেই এখন অমুক মুসিবতটা দেখা দিলো, অমুক আঘাতটা খেতে হলো এবং ওদিক থেকে বিপর্যয় টা নেমে এলো ইত্যাদি। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ফল জানার পর তারা বিজ্ঞজনের মতো বসে পড়তো আর মন্তব্য করতো, অমুক কাজটা না করা উচিত ছিলো, অমুক কাজটা করলে ভালো হতো ইত্যাদি ইত্যাদি।
এই হীন মানসিকতা ছাড়াও তারা প্রত্যেক যুদ্ধ বিগ্রহের প্রাক্কালে নানারকম প্রলাপোক্তি করতো, যেমন, আমাদের আশঙ্কা, কখন না জানি আমরাও কোন বিপর্যয়ের কবলে পড়ে যাই” (মায়িদাহ ৫২)। অর্থাৎ কিনা আন্দোলনটাকে এমন অদক্ষভাবে চালানো হচ্ছে যে, যেকোন সময় তা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে যেতে পারে। আমরা কেনো অনর্থক জীবনের ঝুকি নিতে যাবো?
ওহুদ যুদ্ধের সময় এই মানসিকতার কারনেই মুনাফিকরা আক্ষেপ করেছিলো যে, নেতৃত্বে যদি আমাদের কোন হাত থাকতো তাহলে আমরা এখানে মরতাম না” (আল ইমরান, আয়াত ১৫৪, তাহফীমুল কুরআনে দেখুন) এ মানসিকতার ধারকরা রসূল সা. এর নেতৃত্ব ও বিচক্ষণতার সুস্পষ্ট অনাস্থা পোষণ করতো। তারা নিজেদেরকে সবচেয়ে বড় বুদ্ধিমান মনে করতো। আর যে ব্যক্তি এত বছর ধরে ওহির দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আন্দোলন করে আসছেন, তিনি নবী হলেও তাদের দৃষ্টিতে কিছুই ছিলেন না। নবীর প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব নিয়েও যখন এত অস্বস্তি, তবে কোন সাহাবীর নেতৃত্ব হলে একচেটিয়া দক্ষতা ও বিচক্ষণতার দাবীদার এই গোষ্ঠীটি তার কী দশা করতো, তা আল্লাহই ভালো জানেন।
এই সব উদাহরণ থেকে বুঝা যায় যে, সরাসরি ইসলামী আন্দোলনের বিরোধীতা করার পরিবর্তে রসূল সা. এর ব্যক্তিত্বকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে পরোক্ষ হামলা করাকেই সবচেয়ে সাফল্যজনক পন্থা মনে করা হয়েছিল এবং সেটাই অবলম্বন করা হয়েছিল। গোপন সলাপরামর্শের বৈঠকগুলোতে আন্দোলনের এই সবোচ্চ নেতার বিরুদ্ধেই যত আপত্তি ও অপপ্রচার খসড়া তৈরী করা হতো এবং তার অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ করার জন্যই নিত্য নতুন পদক্ষেপের কথা বিবেচনা করা হতো।
ইসলামী সংগঠনের অভ্যন্তরে নৈতিক ব্যবস্থাজনিত জটিলতা
ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক ব্যবস্থা ছিল আগাগোড়া একটা নৈতিক ব্যবস্থা। এ পরিবেশটা শয়তানের কাজ করার জন্য সবচেয়ে প্রশস্ত ও উত্তম ক্ষেত্র। বিশেষত এর দুটো দিক বিভ্রান্তিসৃষ্টিকারীদের অনুকূল। নৈতিক ব্যবস্থার একটা বিশেষ জটিলতা হলো, এতে সুস্পষ্ট আপত্তিকর ঘটনাবলী যতক্ষণ প্রামাণ্য তথ্যের আকারে আবির্ভূত না হয়, ততক্ষণ তার তার বিরুদ্ধে সংগঠন ও কোন ব্যবস্থা নিতে পারেনা, আর যারা বিব্রত বোধ করে, তারাও শেষ ফল বের হওয়ার আগে পরিস্থিতির ধাঁধালো পটভূমিকে জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেনা। ইসলামের নৈতিক বিধান ইসলামী সমাজের সদস্যদেরকে একে অপরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করে। একজন ন্যায়নিষ্ট মানুষ তাঁর সাথীদের প্রতিটি সন্দেহজনক কার্যকলাপের যতদূর সম্ভব ভালো ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য হয়ে থাকে। অতঃপর সে যদি একটা অবাঞ্চিত ঘটনার সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে আপন অন্তরের গভীরে একটা খারাপ ধারণ পোষণ করেও বসে, তাহলেও তাকে এ জন্যে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় যে, তার খারাপ ধারনাকে খন্ডন করার মত পাল্টা কোন তথ্য পাওয়া যায় কিনা?
নিছক ধারনা, চাই তা যতই দৃঢ় হোক না কেন, তার ভিত্তিতে কারো বিরুদ্ধে কোন আনুষ্ঠানিক মামলা পরিচালনা করা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায়না। এ সব কারণে মদিনার নিষ্ঠাবান মুসলমানরা গোপন সলাপরামর্শে লিপ্ত ফেতনাবাজ ও নৈরাজ্যবাদী লোকদের প্রাথমিক তৎপরতাকে কিছু অবাঞ্চিত আলামত বলে প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও নীরবদর্শক হয়ে দেখতে বাধ্য ছিলেন। তবে ফেতনা যখন যথারীতি ফসল ফলাতে শুরু করতো, কেবল তখনই সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা তাদেরকে তার বিরুদ্ধে কথা বলার অনুমতি দিত এবং সামষ্টিক ব্যবস্থাকে সক্রিয় করার সুযোগ দিত।
নৈতিক ব্যবস্থার দ্বিতীয় জটিলতা ছিল এই যে, সংগঠনের সবোচ্চ নেতা ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের উপর যদি কেউ অভিযোগ আরোপ করে, তাহলে তাদের অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। একদিকে তাদের হাতেই দলের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব থাকে, এবং তারাই সমস্ত ফেতনা তথা অরাজকতা ও বিভ্রান্তি খতম করার ক্ষমতা রাখেন। অপর দিকে তারাই ফেতনার শিকার হয়ে এমন অবস্থায় পতিত হন যে, মুসলিম জনগণের সামনে ফেতনাবাজ তথা হাঙ্গামা সৃষ্টিকারীদের মুখোস খুলে যাওয়ার আগে তাদের বিরুদ্ধে যদি নেতারা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহলে উল্টো নেতারাই সমালোচনা ও ভিন্নমত দমনের দায়ে অভিযুক্ত হন। তারা সত্যের আওয়ায বুলন্দকারীদেরকে স্বৈরাচারী পন্থায় পরাভূত করার দোষে দোষী সাব্যস্ত হন। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন বলা যায় যে, ভদ্রতা সবচেয়ে বড় শক্তি হলেও ভদ্রতা সবচেয়ে বড় দূর্বলতাও বটে, ঠিক তেমনি দলের ক্ষেত্রেও বলা যায় যে, নৈতিক ব্যবস্থা তার সবচেয়ে বড় জটিলতাও বটে। এই জটিলতার একমাত্র সমাধান হলো, দলের সামষ্টিক মনমানসকে এত সজাগ ও সচেতন হতে হবে এবং তার সামষ্টিক চরিত্রকে এত বলিষ্ট ও মজবুত হতে হবে যে, সে নিযের মেজাজ বা স্বভাবের বিরুদ্ধে কোন কিছুকেই দলের অভ্যন্তরে চালু থাকতে দেবেনা। দলীয় পরিমন্ডলে কেউ দলীয় শৃংখলা বিরোধী কানাঘুষা, ফিসফিসানি, গুজব বা গোপন সলাপরামর্শে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত হবেনা, কর্ণগোচর হওয়া এ ধরনের কোন বিষয়কে কেউ এদিক সেদিকে ছড়ানোর ধৃষ্টতা দেখাবেনা। কিন্তু এই চুড়ান্ত ও উৎকৃষ্টতম মানদন্ডে কোন দলের সামগ্রিকভাবে ও পরিপূর্ণভাবে উত্তীর্ণ হওয়া এবং উত্তীর্ণ হয়ে সর্বক্ষণ টিকে থাকা কঠিন। মনমগজ দ্বারা কুচিন্তা করা, মুখ দিয়ে কু-প্ররোচনা দান ও খারাপ বিষয়ে ফুসলানো এবং কান দিয়ে এই সব অবাঞ্চিত জিনিস শোনা – ইত্যাকার কর্মকান্ডে লিপ্ত মানুষ থেকে কোন মানবসমাজ পুরোপুরি মুক্ত ও পবিত্র হতে পারেনা। মানুষ যা ভাবে, যা বলে ও যা শোনে, তাতে শয়তান কিছু না কিছু অংশ গ্রহণ না করেই ছাড়েনা।
নৈতিক ব্যবস্থার এই নমনীয়তা ও উদারতা থেকে মোনাফেকরা পুরোপুরিভাবে উপকৃত হয়েছে এবং এর সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছে। কিন্তু পরিণামে তারা এর প্রবল শক্তির পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারেনি। কোরআনের ভাষায় তাদের সমগ্র কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত সার ছিল এইঃ “তারা যা চেয়েছিল, তা পায়নি”। কিন্তু ইসলামী সংগঠনকে বিব্রত অবশ্যই করেছে এবং তাকে বিশৃংখলায় অবশ্যই ফেলেছে।
গোপন সলাপরামশ, গুজব রটনা, কানাঘুষা ও ফিসফিসানির এই পরিবেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার ব্যক্তিত্ব শুরু থেকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল এবং একের পর এক আক্রমণ চালানোও হচ্ছিল। এহেন পরিবেশে নাশকতাবাদী কুচক্রী ফেতনাবাজদের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয়, তাহলে কুটিল থেকে কুটিলতর এবং জঘন্য থেকে জঘন্যতর অপবাদ রটনা করে কোন প্রলয়ংকারী বিপযয় ঘটিয়ে দেয়াও তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিলনা। এই নমনীয় পরিবেশের সুযোগ গ্রহণ ও মোনাফেকদের দক্ষতার সাথে কাজে লাগানোর জন্য শয়তানের দ্বিতীয় যে জিনিসটির প্রয়োজন ছিল, তা হলো এমন একজন ঝানু খলনায়ক, যার মস্তিষ্ক কুটিল চক্রান্ত উদ্ভাবনে অত্যন্ত সৃজনশীল ও দক্ষ হবে, এবং যার বুকে গোপন সলাপরামর্শকারীদের সৃষ্টি করা বারুদের স্তুপে জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপের সাহস থাকবে। এ ধরনের একজন ঝানু খলনায়ক আব্দুল্লাহ বিন উবাই – এর আকারে আগে থেকেই তৈরী ছিল। এই লোকটার মন নিজের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদার অনুভূতিতে কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। কেনইবা থাকবেনা? হিজরতের প্রাক্কালে মদিনার বাদশাহীর মুকুট তো তারই মাথায় পরানোর প্রস্তুতি চলছিল। কেবল মুহাম্মদ সা. এর উপস্থিতি তার আশার গুড়ে বালি দিল। বাদশাহী দূরে থাক, নিজের চরিত্রের কারণে ইসলামী সংগঠনের প্রথম সারির তো নয়ই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির মর্যাদাও তার কপালে জোটেনি। এই দুর্ঘটনা তার মনমস্তিস্কে অত্যন্ত তিক্ত ও বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং সেই প্রতিক্রিয়া থেকে প্রতি মুহূর্তে জন্ম নিতে থাকে নতুন নতুন ফেতনা, নতুন নতুন ষড়যন্ত্র। শয়তান মানষের ভেতরে প্রত্যক্ষভাবে খুব বেশী কাজ করেনা। তার প্রয়োজন হয়ে থাকে তার বশংবদ মানুষ-শয়তানদের। আর এই মানুষ শয়তানদেরকে আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধে তৎপর রাখার জন্য তার প্রয়োজন হয় একজন যুতসই নেতার, একজন ষড়যন্ত্র বিশারদ নেতার। শয়তান এ ধরনের একজন যুতসই ষড়যন্ত্র বিশারদ নেতা রেডিমেড পেয়ে গেল। সে ছিল আবার ইসলামী আন্দোলনের বৃত্তের ভেতরেরই লোক। এই লোকটা একদিকে নবীর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনকে মেনে নেওয়ার ঘোষণাও দিয়েছিল, অপরদিকে প্রতিনিয়ত ঐ আন্দোলনের বিরুদ্ধে সংঘাতেও লিপ্ত ছিল।
ঝোপ বুঝে কোপ মারায় অভিজ্ঞ এই দাম্ভিক কুচক্রী খলনায়কটি এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে নিজের বুকের ভেতরে জ্বলন্ত হিংসার অগ্নিকুন্ড থেকে একটা দগদগে অঙ্গার বের করে রসূল সা. এর পবিত্র পারিবারিক অংগনে নিক্ষেপ করলো। নিক্ষেপ করার সাথে সাথেই গোটা সমাজ মানসিকভাবে দগ্ধ হতে লাগল।
হযরত আয়েশার নিজস্ব প্রতিবেদন
এই ভয়াবহ দূর্যোগের সময়ে হযরত আয়েশার অন্তরাত্মার ওপর দিয়ে কী ঝড় বয়ে গেছে, সে সম্পকে প্রামাণ্য বিশদ বিবরণ হাদীস, ইতিহাস ও সীরাতের গুরুত্বপূণ গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এ সব বিবরণ স্বয়ং হযরত আয়েশা ও অন্যান্য বর্ণনাকারীদের মুখনিসৃত। আমার কাছে এ মুহূর্তে যাদুল মা’য়াদ (২য় খন্ড, পৃঃ ১১৩-১১৫) এবং সীরাতে ইবনে হিশাম (২য় খন্ড, পৃঃ ৩৪২-৩৪৭) এর ন্যায় প্রামাণ্য গ্রন্থ রয়েছে। তবে তাফহীমুল কোরআনের লেখক হযরত আয়েশার এই বেদনাবিধুর কাহিনীটাকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন বিধায়, ওটাই এখানে উদ্ধৃত করছিঃ
“মদীনায় পৌঁছে আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম এবং প্রায় একমাস শয্যাশায়ী থাকলাম। শহরে এই অপবাদ সম্বলিত গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল। স্বয়ং রসূলের সা. কানেও তা পৌঁছে গিয়েছিল। অথচ আমি কিছুই জানতাম না। তবে যে জিনিসটা দেখে আমার খটকা লাগছিল তা এই যে, রসূল সা. অসুস্থতার সময় আমার দিকে যে রকম বিশেষ মনোযোগ দিতেন, এবার সে রকম মনোযোগ দিচ্ছিলেন না, ঘরে এসে কেবল ”তুমি কেমন আছ” এই কথাটাই জিজ্ঞেস করতেন। এর চেয়ে বেশী একটা কথাও বলতেন না। এটা দেখে আমার সন্দেহ হতো, কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে। অবশেষে আমি তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মায়ের কাছে চলে গেলাম, যেন তিনি ভালভাবে আমার সেবা সশ্রুষা করতে পারেন। একদিন রাতের বেলা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বাইরে গেলাম। তখন পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে পায়খানা তৈরী হয়নি। তাই আমরা জংগলেই যেতাম। আমার সাথে মিসতার মাও ছিলেন। তিনি আমার মায়ের খালাতো বোন ছিলেন (অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত আবুবকর সিদ্দীক রা. এই পরিবারের সকলের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এত বড় অনুগ্রহ সত্ত্বেও মিসতাহ হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনাকারীদের অন্তভূক্ত গিয়েছিল।) জংগলের দিকে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে মিসতার মা একটা ঠোকর খেলেন। সাথে সাথে তার মুখ দিয়ে বে-এখতিয়ার বেরিয়ে গেলঃ “মিসতার মরণ হোক! আমি বললাম, আপনি কেমন মা যে, ছেলেকে অভিশাপ দিচ্ছেন? আর ছেলেও এমন যে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে”। তিনি বললেন, ওর কথা শোননি? এরপর তিনি পুরো ঘটনা শোনালেন। অপবাদ রটনাকারীরা আমার সম্পর্কে কি সব কথা ছড়াচ্ছে, তা খুলে বললেন। মোনাফেকরা ছাড়া মুসলমানদের মধ্যে থেকে যারা এই ফেতনায় জড়িয়ে পড়েছিল,তাদের মধ্যে মিসতাহ, বিখ্যাত কবি হাসসান বিন সাবিত, এবং হাসনা বিনতে জাহশ (উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশের বোন) উল্লেখযোগ্য। এই বিবরণ শুনে আমার রক্ত শুকিয়ে গেল এবং আমি সেই প্রাকৃতিক প্রয়োজনের কথা পর্যন্ত ভুলে গেলাম, যার জন্য এসেছিলাম। সোজা ঘরে ফিরে গেলাম এবং সারা রাত কেঁদে কাটালাম”। (ইবনে হিশামের বর্ণনায় এ কথাটাও যোগ করা হয়েছে যে, “কাঁদতে কাঁদতে আমার কলিজা ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিল!”)
একদিকে হযরত আয়েশা তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করছিলেন। অপরদিকে সমগ্র শহরে যথারীতি কানাঘুষা চলছিল। হযরত আয়েশার পক্ষে সবচেয়ে জোরদার সাফাই তার পিতা ও স্বামীই দিতে পারতেন। কিন্তু দুরাচার লোকেরা যখন এ ধরনের অপবাদ রটিয়ে দেয়, তখন যে যত ঘনিষ্ট হয়, সে ততই জটিলতায় পড়ে যায়। তাই পিতা ও স্বামী নির্বাক হয়ে গেলেন এবং চারদিক থেকে নিক্ষিপ্ত কুৎসার তীরে বিদ্ধ হতে লাগলেন।
মানবতার শ্রেষ্ঠতম উপকারী বন্ধু মুহাম্মদ সা. এর কাছে এই মুহূর্তগুলো ব্যক্তিগতভাবেও এবং সংগঠনের স্বার্থের দিক দিয়েও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। যে কোন সম্ভ্রান্ত, সচেতন ও দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে রসূল সা. এর এই অবস্থা উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি অনেক ধৈর্য ধারণ করলেন এবং দীঘ সময় নীরবে কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু এমন একটা স্পশকাতর বিষয়কে বতমান অবস্থায় ঝুলন্ত রাখাও সম্ভব ছিলনা। একটা কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। তাই রসূল সা. নিরপেক্ষভাবে তদন্ত শুরু করে দিলেন। নিজের দু’জন ঘনিষ্ট সাথী হযরত আলী রা. ও হযরত উসামা বিন যায়েদকে ডেকে তাদের মতামত চাইলেন। হযরত উসামা রা. বললেনঃ হে রসূল! তিনি আপনার মহিয়সী স্ত্রী। আমরা তার ভেতরে ভালো ছাড়া আর কিছু পাইনা। যা কিছু ছড়ানো হচ্ছে, সব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রচারণা। (সীরাতে ইবনে হিশাম) হযরত আলী রা. অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে অভিমত দিলেন। তিনি বললেন, “হে রসূল! স্ত্রী লোকের অভাব নেই। আপনি আয়েশার পরিবতে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করতে পারেন। তবে দাসীকে ডেকে তদন্ত করে নিন”। আসলে হযরত আলীর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, রসূল সা. এর পেরেশানী ভোগ করার চেয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করাই উত্তম এবং যে স্ত্রী সম্পর্কে এমন তুলকালাম কান্ড ঘটে গেছে, তাকে তালাক দেয়াই শ্রেয়। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী নিজের বিশেষ আত্মীয়তার বন্ধনের কারণে ঐ বিষয়টার আন্দোলনগত দিকের চেয়ে রসূল সা. এর ব্যক্তিগত পেরেশানীকে বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এজন্য তিনি রসূল সা. কে মানসিক অস্থিরতা থেকে মুক্তি লাভের পরামশ দিলেন।
তবুও রসূল সা. হযরত আলীর পরামর্শের দ্বিতীয় অংশকে গ্রহণ করলেন। তিনি দাসীকে ডাকলেন। হযরত আলী তাকে এক চড় বসিয়ে দিয়ে তাকে কঠোরভাবে শাসিয়ে বললেন, “রসূল সা. এর সামনে সত্য বলবে”। সে বললো, ”আল্লাহর কসম, আমি তার সম্পকে ভালো ছাড়া আর কিছু জানিনা। আয়েশার মধ্যে আমি কেবল একটাই ত্রুটি দেখেছি যে, আমি আটা বানানোর সময় যখন বাইরে যেতাম, তাকে বলে যেতাম যে, একটু দেখো। কিন্তু সে ঘুমিয়ে যেত এবং ছাগল এসে আটা খেয়ে ফেলতো” (সীরাতে ইবনে হিশাম)। এই স্বতস্ফূর্ত বিবৃতিতে দাসী হযরত আয়েশাকে যেমন নিখূঁত সাফাই দিয়েছিল, অন্য কোন বিবৃতি এর ওপর তেমন কিছু যোগ করতে পারতোনা। সে এমন একটা সরলমতি বালিকার প্রকৃত ছবি তুলে ধরেছিল, যার মধ্যে কোন খারাপ জিনিস কল্পনা করা মানবীয় বিবেক বুদ্ধির পক্ষে অসম্ভব। এই সাথে রসূল সা. দ্বিতীয় যে পদক্ষেপ নিলেন তা হলো, একটা সাধারণ সভা ডাকলেন এবং ভাষণ দিলেন। আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করার পর অত্যন্ত ব্যথাতুর কন্ঠে বললেনঃ
“যারা আমাকে আমার পরিবার পরিজন সম্পর্কে কষ্ট দেয় এবং তাদের সম্পর্কে অবাস্তব কথা বলে বেড়ায়, তাদের উদ্দেশ্যটা কী? আল্লাহর কসম, আমার পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া আর কিছু জানিনা। তারা যে ব্যক্তিকে জড়িয়ে এই অপবাদ রটিয়েছে, তাকেও আমি ভালো বলেই জানি। সে আমার অনুপস্থিতে কখনো আমার বাড়িতে আসেনি”। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)
অপর এক বর্ণনা মোতাবেক রসূল সা. শুরুতে বলেছিলেন, “যে ব্যক্তি আমাকে আমার পরিবারের ব্যাপারে কষ্ট দিচ্ছে, তার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারে, এমন কেউ আছে কি?” (যাদুল মায়াদ, ২য় খন্ড)
এ কথা শোনার পর আওস গোত্রের সরদার উসাইদ বিন হুযাইর দাঁড়িয়ে বললেন, “হে রসূলুল্লাহ! এ ধরণের লোকেরা যদি আমাদের গোত্রের হয়ে থাকে, তা হলে আমরা তাদেরকে উচিত শিক্ষা দেব। আর যদি তারা খাজরাজী হয়ে থাকে, তা হলে আপনি হুকুম দিন। আল্লাহর কসম, এ ধরনের লোকদের সমুচিত শাস্তি মস্তক ছেদন”।
সংগে সংগে অপর দিক থেকে খাজরাজের সরদার সা’দ বিন উবাদা প্রতিবাদ করে উঠলেন যে, “তুমি মিথ্যা বলছ, আল্লাহর কসম, আমরা তাদের মস্তক ছেদন করবোনা। ওহ, বুঝেছি, তুমি এ কথা এজন্যই বলেছ যে, তুমি তাদেরকে খাজরাজের লোক মনে কর”। হযরত সা’দের এই জবাবে উসাইদ বিন হুযাইর খুবই রুষ্ট হলেন। তিনি হয়তো বুঝেছেন, যে দলে অপরাধী, নৈরাজ্যবাদী ও কুচক্রীরা কোন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতা পায়, সে দলের পক্ষে সমাজকে অপরাধমুক্ত করা সম্ভব নয়। আবদুল্লাহ বিন উবাই এর মত লোকেরা সব আন্দোলনেই সব সময় জন্ম নিয়ে থাকে। কিন্তু একটা শক্তিশালী ও আত্মসচেতন দল এ ধরনের লোকদের দলে টিকতে দেয়না, বরং বের করে দেয়। তবে যদি কূচক্রী লোক কোন সংগঠনে প্রভাবশালী লোকদের আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়ে যায়, তাহলে গৃহশত্রু বিভীষণরা লালিত পালিত হতে থাকে এবং সমাজ তাদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই তিক্ত সত্য উপলব্ধি করেই হযরত উসাইদ রা. বলে উঠলেন, ‘‘মিথ্যা আমি নয়, তুমি বলছ। আল্লাহর কসম, তুমি একজন মোনাফেক বলেই মোনাফেকদের পক্ষ নিচ্ছ।’’ (সীরাতে ইবনে হিশাম)
এই তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার কারণ ছিল এই যে, আওস ও খাজরাজের মধ্যে উত্তেজনা বাধানোর জন্যও ক্রমাগত চক্রান্ত আঁটা হচ্ছিল। এজন্যই সামান্য একটা কথার জের ধরে উত্তেজনার সৃষ্টি হলো এবং একটা মারামারি বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। যিনি উভয় গোত্রের মধ্যে সুসম্পর্ক গঠন করে দিয়েছিলেন, সেই মহান নেতার এটা ভালো লাগলো না যে, বহু বছরের চেষ্টায় গড়া দু’গোত্রের ঐক্য তাঁরই কারণে আবার নষ্ট হয়ে যাক। তিনি মিম্বর থেকে নেমে এসে উভয় দলকে শান্ত করলেন এবং সভার সমাপ্তি ঘটলো। (সীরাতে ইবনে হিশাম)
দলের এই দুর্বল দিকটার অভিজ্ঞতা রসূল সা. এর মনোকষ্টকে আরো বাড়িয়ে দিল। আসলে বনুল মুসতালিক যুদ্ধের সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যে পুরানো বিভেদ ও বিদ্বেষের আগুন জ্বেলেছিল, এটা ছিল তারই ফলশ্রুতি।
কাহিনীর শেষাংশ, যা ট্রাজেডিকে কমেডিতে রূপান্তরিত করেছিল, খোদ হযরত আয়েশার মুখেই শুনুন!
‘‘এই অপবাদের গুজব কমবেশি এক মাস ব্যাপী শহরময় গুঞ্জরিত হতে থাকে। রসূল সা. প্রচন্ড মর্মযাতনা ভোগ করতে থাকেন। আমি সারাক্ষণ কাঁদতে থাকি। আমার পিতামাতা চরম উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় আক্রান্ত থাকেন। অবশেষে একদিন রসূল সা. এলেন এবং আমার কাছে বসলেন। এই পুরো সময়টায় তিনি একবারও আমার কাছে কাছে বসেননি। হযরত আবু বকর ও উম্মে রুমান (হযরত আয়েশার মাতা) ধারণা করলেন, আজ একটা চূড়ান্ত ফায়সালা হতে যাচ্ছে। তাই তারা দুজনেও কাছে এসে বসে গেলেন। রসূল সা. বললেন, ‘‘আয়েশা তোমার সম্পর্কে আমার কাছে এই সব খবর পৌঁছেছে। তুমি যদি নিরপরাধ হয়ে থাক, তাহলে আশা করি আল্লাহ তায়ালা তোমার নিরপরাধ হওয়ার বিষয় জানিয়ে দেবেন। আর যদি তুমি কোন গুণাহ করে থাক, তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা কর ও ক্ষমা চাও। বান্দা যখন নিজের গুনাহ স্বীকার করে তওবা করে, তখন আল্লাহ মাফ করে দেন। এ কথা শুনে আমার অশ্রু শুকিয়ে গেল। (নিরপরাধ মানুষের কাছ থেকে এ ধরণের প্রতিক্রিয়াই আশা করা যায়।– নঃ সিঃ)
আমি নিজের পিতাকে বললাম, ‘‘আপনি রসূলুল্লাহর সা. কথার জবাব দিন।’’ তিনি বললেন, ‘‘মা, আমার বুঝেই আসছেনা কী বলবো।’’ আমি নিজের মাতাকে বললাম, ‘‘আপনি কিছু বলুন।’’ তিনিও বললেন, ‘‘আমিও বুঝতে পারছিনে কী বলবো।’’ আমি বললাম, ‘‘আপনাদের কানে একটা কথা ঢুকেছে- সংগে সংগে তা আপনাদের মনেও বদ্ধমূল হয়ে গেছে, এখন যদি বলি যে আমি নিষ্পাপ, বস্তুত আল্লাহ সাক্ষী যে, আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ- তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি যা করিনি তা অনর্থক স্বীকার করি- বস্তুত আল্লাহ সাক্ষী যে আমি তা করিনি- তাহলে আপনারা বিশ্বাস করবেন। আমি এ সময় হযরত এয়াকুবের নাম মনে করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে করতে পারলামনা। (একজন নিরপরাধ মানুষ যখন কোন মারাত্মক অপবাদের শিকার হয়ে দিশেহারা হয়ে যায় তখন তার মনস্তাত্মিক জগতে এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটাই স্বাভাবিক।– নঃ সিঃ) অবশেষে আমি বললাম এ পরিস্থিতিতে আমার আর কী বলার আছে? আমি শুধু হযরত ইউসুফের পিতা যে কথা বলেছিলেন যে ******* ‘‘পরম ধৈর্য’’ সেই কথাটাই বলবো। (হযরত এয়াকুবের সামনে তার ছেলেরা যখন ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে বলে মিথ্যে বিবরণ দিয়েছিল, তখন তিনি এ কথাটা বলেছিলেন।- অনুবাদক) এই বলে আমি বিপরীত দিকে মুখ ঘুরিয়ে শুয়ে পড়লাম। (একজন নিরপরাধ মানুষের ওপর অপবাদ আরোপ করা হলে তার মধ্যে অসহায়াবস্থার পাশাপাশি যে বেপরোয়া মনোভাবের সৃষ্টি হয়, সেটাই এখানে ফুটে উঠেছে।– নঃ সিঃ) এই সময় আমি মনে মনে বলছিলাম, আল্লাহ আমার নিষ্পাপত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি নিশ্চয়ই প্রকৃত তথ্য ফাঁস করে দেবেন। যদিও তখন পর্যন্ত আমি ভাবতেও পারিনি যে, আমার পক্ষে ওহি নাযিল হবে যা কেয়ামত পর্যন্ত পঠিত হবে। আমি নিজেকে এতটা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন কখনো ভাবতামনা যে, আল্লাহ স্বয়ং আমার পক্ষে কথা বলবেন। তবে আমি মনে করেছিলাম, রসূল সা. কোন স্বপ্ন দেখবেন এবং তার মাধ্যমেই আল্লাহ জানিয়ে দেবেন যে, আমি নিরপরাধ। সহসা রসূল সা. এর মধ্যে এমন ভাবান্তর সৃষ্টি হলো, যা সচরাচর ওহি নাযিল হওয়ার সময় হতো এবং প্রচন্ড শীতের মৌসুমেও রসূল সা. এর মুখমন্ডল থেকে মুক্তার মত ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরতো। আমরা সবাই নীরব হয়ে গেলাম। আমি তো সম্পূর্ণ নির্ভীক ছিলাম। কিন্তু আমার পিতামাতা ভয়ে এমন জড়সড় হয়ে যাচ্ছিলেন যে, শরীরের কোথাও তখন কেটে দিলে বোধ হয় রক্তই বের হতোনা। তারা শংকিত ছিলেন এই ভেবে যে, আল্লাহ না জানি কী খবর জানান। রসূল সা. এর অবস্থা স্বাভাবিক হলে দেখা গেল, তিনি ভীষণ খুশী। তিনি হাসিমুখে সর্বপ্রথম যে কথাটা বললেন, তা ছিল, ‘‘আয়েশা তোমাকে মুবারকবাদ। আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ বলে ঘোষণা করেছেন।’’ এরপর রসূল সা. দশটা আয়াত শোনালেন। আমার মা বললেন, ওঠো, রসূলুল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমি বললাম, আমি ওঁর প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবোনা, আপনাদের প্রতিও নয়। আমি শুধু আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞ, যিনি আমাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আপনারাতো এ অপবাদকে অস্বীকার পর্যন্ত করেননি।’’ (তাফহীমুল কোরআন, সূরা নূর) হযরত আয়েশার কথায় কেবল তীব্র আত্মসম্ভ্রমবোধ যুক্ত অনুযোগ ফুটে উঠেছে, লক্ষ্য করুন। এটা কি কোন অপরাধী বিবেকের বক্তব্য হতে পারে? এই বিবরণের প্রতিটা শব্দ বলে দিচ্ছে যে, এটা একজন নিরপরাধ মানুষের দুঃখ বেদনার অকৃত্রিম স্বতস্ফূর্ত ও নিখুঁত প্রতিবেদন।
ওহির সাফাই
অপপ্রচারের এই ঝড় এবং তা থেকে সৃষ্ট সংকট দূর করার জন্য সহসাই ওহি নাযিল হলো। এই সংকট দূর করার জন্য যে সূরা নাযিল হলো, তার নাম ‘নূর’ (আলো)। বাস্তব পরিস্থিতির সাথে চমৎকার মানিয়েছে এ নাম। কেননা একটা গুরুতর সামাজিক সংকটের সৃষ্ট অন্ধকারকে দূর করে পরিবেশকে আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্যই এই সূরা নাযিল হয়েছে। এ সূরায় মুসলমানদের সংগঠন ও সমাজ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা, তার দূর্বলতা চিহ্নিত করা এবং এই সব দূর্বলতা থেকে তাদেরকে স্থায়ীভাবে মুক্ত করার জন্য নৈতিক ও আইনগত দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
এই সাড়া জাগানো সূরার বক্তব্যের সূচনাই চমকে দেয়া মত। বলা হয়েছেঃ
‘‘এ একটা সূরা, যাকে আমি নাযিল করেছি, যাকে আমি দায়িত্ব হিসাবে (ইসলামী সমাজের জন্য) অপরিহার্য করেছি এবং যার মধ্যে আমি সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী উপস্থাপন করেছি। হয়তো তোমরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।’’ (আয়াত ১)
এবার সমাজকে উদ্দেশ্য করে সূরা নূরের সোচ্চার ঘোষণাঃ
‘‘যারা এই অপবাদ তৈরী করেছে, তারা তোমাদেরই মধ্যকার একটা গোষ্ঠী। .... এ অপবাদে যে যতটুকু অংশ নিয়েছে, সে ততটুকুই পাপ কুড়িয়েছে। আর যে এর দায়দায়িত্বের প্রধান অংশ বহন করেছে, তার জন্য রয়েছে ভীষণ শাস্তি।’’ (আয়াত-১১)
কী সাংঘাতিক শ্লেষাত্মক ধমক! এমন একটা সাক্ষ্যপ্রমাণহীন অভিযোগ, যার আদৌ কোন সুষ্ঠু আলামত ছিলনা, ঝড়ের বেগে উঠলো এবং বাইরের কোন শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর পক্ষ থেকে নয়- বরং বহু বছরের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুসলিম দলের ভেতর থেকেই উঠলো। এটা এক আধজন মানুষের আকস্মিক পদস্খলনও ছিলনা। পুরো এক মাস ধরে একটা গোষ্ঠী চরম মানসিক বিপর্যয় সৃষ্টি করতে থাকলো। সূরা নূরে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের দলীয় পরিমন্ডলে এমন দুর্বলতার অস্তিত্ব রয়েছে যে, তার নির্মাতারাই তাকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়ে বসতে পারে। এ পরিবেশে এমন ফাঁকফোকর রয়েছে যার মধ্য দিয়ে সত্যের সৈনিকদের সমাজ ও সংগঠনে মিথ্যা ও বাতিল ঢুকে যেতে পারে। বলা হচ্ছে যে, এটা কেবল একটা বিচ্ছিন্ন অপবাদের ঘটনা ছিলনা, বরং পাপের একটা বহমান স্রোত ছিল। এই স্রোতধারা থেকে কেউ ড্রাম ভরে নিয়েছে, কেউ কলসী ভরে নিয়েছে, আবার কেউ শুধু হাতের তালুতে যতটুকু নেয়া যায় ততটুকু নিয়েছে। এভাবে যে যতটটুকু অংশ গ্রহণ করেছে, সে নিজের জন্য ততটুকু পাপ সঞ্চয় করেছে। এরপর এই অপকর্মের মূল হোতা অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যে প্রথম আগুন জ্বালিয়েছে, এবং তারপর অব্যাহতভাবে বাতাস দিয়ে তাকে দাবানলে পরিণত করেছে।
সূরা নূরে প্রশ্ন রাখা হয়েছেঃ
‘‘যখন তোমরা এটা প্রথম শুনলে, তখন মুমিন নারী ও পুরুষরা কেন নিজেদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলোনা, কেনইবা তৎক্ষণাত বললোনা যে, এটা একটা ভয়ংকর অপবাদ।’’ (আয়াত ১২)
এ বক্তব্যে কত জোরদার নৈতিক আবেদন রয়েছে এবং ভদ্রজনোচিত আবেদ ও মুমিন সুলভ অনুভূতির জন্য কত তীব্র কশাঘাত রয়েছে, তা লক্ষ্য করার মত। অর্থাৎ ইসলামী সমাজের এক মহীয়সী নারী ঘটনাক্রমে কাফেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন এবং সেই সমাজেরই একজন সম্মানিত সদস্য তাকে পথিমধ্যে পেয়ে সাথে করে নিয়ে এলেন, শুধু এতটুকু ঘটনা তোমাদের জন্য সর্বনিম্ন স্তরের একটা খারাপ ধারণা পোষনের ভিত্তি হয়ে গেল কেমন করে? তোমাদের মধ্যকার অন্য কোন নারী ও পুরুষ যদি একটা দুর্ঘটনা হিসেবে এরূপ পরিস্থিতির শিকার হতো, তাহলে তারা কি অবশ্যই এরূপ নিকৃষ্ট কাজে লিপ্ত হতো? নিজেদের চরিত্র সম্পর্কে কি তোমাদের ধারণা এ রকম? তোমাদের সমাজ কি এতই নীচ যে, তার দুই ব্যক্তি ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেই ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার সামান্যতম সুযোগও হাতছাড়া করেনা? তোমরা নিজেদের সম্পর্কে যদি এমন হীনতার ধারণা করতে না পার, তাহলে তোমাদের দলের একজন শ্রেষ্ঠ নারী ও একজন বিশিষ্ট সদস্য সম্পর্কে এমন জঘন্য ধারণা পোষণের কী অধিকার তোমাদের ছিল?
বস্তুত এ সমাজের বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ এই সংকটকালেও নিজেদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখেছিলেন। নচেত গোটা সমাজদেহে যদি এই বিষ সংক্রমিত হবার সুযোগ পেত এবং সমাজ সামগ্রিকভাবে এর মানসিক প্রতিরোধে অক্ষম হতো, তা হলে এ আঘাত তার গোটা অস্তিত্বকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিত। এক্ষেত্রে হযরত আবু আইয়ুব আনছারী সবচেয়ে নির্ভুল প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী যখন তাকে এই নোংরা গুজবের কথা জানালেন, তখন তিনি বললেন, ‘‘ওহে আইয়ুবের মা, আয়েশার পরিবর্তে তুমি যদি ঐ স্থানে থাকতে, তাহলে কি এমন কাজ করতে? তিনি বললেন, ‘‘আল্লাহর কসম, কখখনো না।’’ হযরত আবু আইয়ূব বললেন, ‘‘তাহলে আয়েশা তোমার চেয়ে অনেক ভালো। আমিও বলি যে, সফওয়ানের স্থলে যদি আমি থাকতাম, তাহলে এ ধরণের চিন্তাও মাথায় আসতোনা। আর সফওয়ান তো আমার চেয়ে ভালো মুসলমান।’’ (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)
এই নোংরা অপবাদ রটনাকারীদেরকে সূরা নূরে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তোমরা আবু আইয়ূব আনসারীর মত প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারলেনা কেন?
এরপর সূরা নূর আইনগত দৃষ্টিভংগি থেকে প্রশ্ন তুলেছে যেঃ
‘‘তারা তাদের অভিযোগের প্রমাণ স্বরূপ চারজন সাক্ষী কেন নিয়ে আসেনি? আল্লাহর দৃষ্টিতে তো ওরাই মিথ্যুক।’’ (আয়াত-১৩)
অর্থাৎ কোন পুরুষ ও নারীর চরিত্রের ওপর কলংক লেপন করা নিছক একটা তামাসা নয় বরং এটা একটা গুরুতর অপরাধ এবং এর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ একটা জীবন্ত সমাজে অত্যন্ত জরুরী। একজন সৎ ও নিরীহ নাগরিক সম্পর্কে ইচ্ছা হলেই এ কথা বলা যে, সে হত্যা করেছে, চুরি করেছে, অথবা ব্যভিচার করেছে, কোন মামুলী ব্যাপার নয় যে, যা হবার হয়ে গেছে বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে। এটা সর্বোচ্চ পরিমাণ দায়িত্ব সচেতনতার দাবী জানায়। এ ধরণের অভিযোগ তোলার পর তার প্রমাণ দেয়া, আইনানুগ সাক্ষী উপস্থাপন করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। যারা ইসলামী সমাজের দু’জন সম্মানিত ও ভদ্র লোকের বিরুদ্ধে স্বচোক্ষে না দেখে একটা অপবাদ আরোপ করে, আরোপিত অপবাদের সাক্ষ্য প্রমাণ আনা তাদেরই কর্তব্য। নচেত আইন অনুযায়ী তারাই মিথ্যাবাদী ও অপরাধী।
এরপর সূরা নূর ইসলামী সমাজের দুর্বল সদস্যদের ত্রুটিকে কিভাবে চিহ্নিত করেছে দেখুনঃ
‘‘ভেবে দেখ, তোমরা কত বড় মারাত্মক ভুল কাজ করছিলে যখন একজনের মুখ থেকে আর একজনের মুখে এই মিথ্যার বিস্তার ঘটাচ্ছিলে এবং তোমরা মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যার সম্পর্কে তোমাদের কোনই জ্ঞান ছিলনা। তোমরা একে একটা মামুলী ব্যাপার মনে করেছ। অথচ আল্লাহর কাছে তা গুরুতর। কথাটা শোনা মাত্রই তোমরা বলে দিলেনা কেন যে, এমন কথা উচ্চারণ করা আমাদের জন্য অন্যায়। সুবহানাল্লাহ, এতো একটা জঘন্য অপবাদ!’’ (আয়াত ১৫-১৬)
এটা যে কোন সমাজ ও সংগঠনের একটা মস্ত বড় দুর্বলতা যে, তার অভ্যন্তরে ভিত্তিহীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন গুজব সহজেই ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত যে সংগঠন সারা বিশ্বের নৈতিক সংস্কারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যার নেতৃত্বে একটা সামজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত হয়, তার পক্ষে এটা আরো বড় দুর্বলতা। একজন মানুষ কান দিয়ে যা কিছু শুনবে মন দিয়ে তৎক্ষণাত তা বিশ্বাস করবে, এবং মুখ দিয়ে তা প্রচার করবে, অতঃপর এক মুখ থেকে আর এক মুখে স্থানান্তরিত হতে থাকবে, কেউ তার সত্যাসত্য যাচাই করবেনা, কোন বাছবিচার করবেনা এবং কোথাও গিয়ে এই ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটবেনা, যে যার বিরুদ্ধে যা কিছু বলতে চায় অবাধে বলে যাবে, যার বিরুদ্ধে কলংক রটাতে চায় রটাতে কোন বাধা পাবেনা – এ ধরণের সমাজে কারো মানসম্ভ্রমের নিরাপত্তা থাকতে পারেনা। যে সমাজে স্বয়ং রসূল সা., হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা., হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. ও সফওয়ানের ন্যায় ব্যক্তিবর্গ একজন মোনাফেকের ছড়ানো অপবাদ থেকে রক্ষা পায়না, সে সমাজে আর কার মান সম্ভ্রম নিরাপদ থাকতে পারে?
সূরা নূরে এ জন্যই প্রচন্ড ধমকের সুরে বলা হয়েছেঃ
‘‘যারা সরলমতি নারীদের নিরুদ্ধে অপবাদ রটায়, তাদের ওপর দুনিয়া ও আখেরাতে অভিসম্পাত এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব।’’ (আয়াত-২৩)
এ আয়াতে হযরত আয়েশার চরিত্রের ছবি এঁকে দেয়া হয়েছে। একজন ঈমানদার সচ্চরিত্রা মহিলা, যার ধারণাই নেই যে ব্যভিচার কী জিনিস এবং কিভাবে করা হয়, আর এ ব্যাপারে কেউ তাকে অপবাদ দিতে পারে এ কথা যার কল্পনায়ই আসেনা। তেমনি এক সরলমতি মযলুম মহিলার এ চিত্র নৈতিকভাবে প্রতিটি মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করেছে।
এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, যেসব একনিষ্ঠ ঈমানদার আল্লাহ রসূলের অনুগত এবং ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বস্ত ব্যক্তি এই দুরন্ত ও সতেজ গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিত্বও ছিলেন, যিনি ইসলামী আন্দোলনের মূল্যবান সেবা করেছিলেন এবং তার সাহিত্যিক ও আত্মীক সম্পদ বৃদ্ধি করেছিলেন। ইনি ছিলেন হযরত হাসসান বিন সাবেত রা.। যারা সূরা নূরের ধমক ও তিরস্কারের আওতায় এসেছিলেন, হাসসানও তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন। অথচ ইসলামী সংগঠনে ও রসূল সা. এর দরবারে তিনি যথেষ্ট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। বিভিন্ন সময় রসূল সা. তাঁকে বিশেষ ভাবে উপদেশ দিতেন যেন জাহেলী কবি ও সাহিত্যিক মহলের হামলার জবাব তিনি যেন কবিতা ও সাহিত্য দিয়েই দেন এবং ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দায়িত্ব পালন করেন। এক পর্যায়ে হাসসান রা, এই দুর্লভ সৌভাগ্যও লাভ করেন যে, রসূল সা. স্বয়ং তাঁকে নিজের মিম্বরে বসান এবং ইসলামী আন্দোলনের জাতীয় সংগীত গাইতে বলেন। তার এই মর্যাদা স্বয়ং হযরত আয়েশা রা. এতটা উপলব্ধি করতেন যে, এই উত্তেজনাপূর্ণ সময়টা অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তিনি সর্বদাই তাকে সম্মান করতেন। কখনো কখনো তাকে মনে করিয়ে দেয়া হতো যে, এই ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে কুতসা রটনায় অংশ গ্রহণ করেছিল। তখন হযরত আয়েশা উদারতা ও মহানুভবতার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে বলতেন, “বাদ দাও। উনি ইসলাম বিরোধী কবিদেরকে সব সময় রসুল সা. ও ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন এবং কবিতার অংগনে মূল্যবান অবদান রেখেছেন।”
সে যাই হোক, বস্তুত ঘটনা এটাই যে, ইসলামী আন্দোলনের এই অসাধারন ব্যক্তি মোনাফেকদের পাতানো ভ্রান্তির বেড়াজালে আটকে পড়ে গিয়েছিলেন। এই হাঙ্গামায় তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা তিনি নিজে আন্তরিকতা সহকারে এবং ন্যায়সংগত মনে করে করলেও আন্দোলনের জন্য তা অত্যাধিক ক্ষতিকর ছিল। তার এ ভূমিকা দেখে যে কেউ এ শিক্ষা লাভ করতে পারে যে, কোন মানুষ যত দৃঢ় চরিত্রের অধিকারীই হোক না কেন, নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারে না যে, কোন অবস্থায়ই কোন বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হবে না। অনুরূপ অন্য কোন ব্যক্তি যতই শীর্ষ পর্যায়ের হোক না কেন, তার সম্পর্কেও কেউ গ্যারান্টি দিতে পারে না যে, সে কোন ব্যাপারেই কোন মতিভ্রমের শিকার হবে না। ছোট বা বড় প্রতিটি মানুষ প্রতি মুহূর্তে শয়তানের চক্রান্তের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকে। বরং প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির চারপাশে ষড়যন্ত্রের জাল পাতার ব্যাপারে সে অধিকতর উদগ্রীব হয়ে থাকে। এ কারণেই ইসলামী আন্দোলন সর্বকালে যে মৌল তত্ত্বের অনুসরণ করে থাকে তা হলো, ব্যক্তি নয় নীতি ও আদর্শের প্রতিই দলের আসল আনুগত্য থাকা বাঞ্ছনীয়।
ইসলামী আন্দোলনের একজন শীর্ষ ব্যক্তিত্বকে ফাঁদে আটকে ফেলা ছিল আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সাংগ পাংগদের অতি বড় সাফল্য। তারা মোনাফেকসুলভ কোটিল্য দ্বারা তাড়িত হয়ে অপততপরতা চালাচ্ছিল, আর হাসসান বিন সাবেত আন্তরিকতার সাথে তাদের ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। এ কথা বলা বেমানান হবেনা যে, আন্দোলনের জন্য আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর মোনাফেকী যত ক্ষতিকর ছিল, তার চেয়েও বেশী ধ্বংসাত্মক ছিল হাসসানের আন্তরিকতা ও সরলতা। কেননা আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়ে যে পদক্ষেপ নেয়া হয়, তা ক্ষতি সাধনে স্বেচ্ছায়ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত পদক্ষেপের চেয়ে অনেক বেশী সফল হয়ে থাকে।
হাসসান বিন সাবেত কাদের পক্ষে কাজ করেছেন এবং কাদের দৃষ্টিভংগী ছড়াচ্ছেন, সেটা তিনি বুঝতেই পারেননি। তিনি অনুভবই করেননি যে, তিনি কাদের ধ্যানধারণা ও সংকল্প বাস্তবায়িত করছেন, তার কার্যকলাপ সমাজের কোন শ্রেনীর লোকদের পক্ষে যাচ্ছে, এবং সংঠনের কোন গোষ্ঠীর হাত সবল করছে। তিনি যে এ ক্ষেত্রে মুমিনসুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে পারলেন না, সেটা বোধ হয় আল্লাহর ইচ্ছারই ফল।
আব্দুল্লাহ বিন উবাই এর সাথে ইসলামী সমাজের সম্পর্ক ছিল ক্ষীণ ও দূরত্বের। তার বৈরী তৎপরতা বরদাশত করা যেত। কিন্তু হাসসান বিন সাবেত ছিলেন ইসলামী সংগঠনের আপনজন। এ জন্যই তার বৈরী আচরণ অসহ্য মনে হচ্ছিল। কেননা এতে সবার মনে হচ্ছিল যে, আমাদেরই একখানা তরবারী আমাদেরকে ঘায়েল করছে। এ ধরনের পরিস্থিতি কোন আন্দোলনে ও সংগঠনে দেখা দিলেই ধৈর্যের বাঁধ টুটে যাওয়ার উপক্রম হয়। সম্ভবত হয়েছিলও তাই। কিন্তু ইসলামী সংগঠনের কঠোর নৈতিক শৃঙ্খলা ভাবাবেগকে থামিয়ে রেখেছিল। কেবল এক ব্যক্তি নিজেকে সংযত রাখতে পারেননি। তিনি ছিলেন সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল। দুটো কারণে তিনি বেসামাল হয়ে যান। প্রথমত যে হযরত আরেশাকে তিনি নিজের মায়ের মত জানতেন, তার বিরুদ্ধে অপবাদ আরোপ করা হচ্ছিল। দ্বিতীয়ত, সেই অপবাদ স্বয়ং তাকে জড়িয়েই আরোপ করা হচ্ছিল। সাফওয়ান একেতো ছিলেন বদরযোদ্ধা, ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ সেবক, স্পষ্টবাদী হিসেবে খ্যাত। উপরন্তু তার চরিত্রে আজ পর্যন্ত কোন পাপের চিহ্ন দেখা যায়নি এবং একজন লাজুক ছেলের মত হযরত আয়েশার দিকে একটা দৃষ্টিও না দিয়ে, সারা পথে একটা কথাও না বলে, পূর্ণ সতর্কতার সাথে পেছনের অবস্থানস্থল থেকে ইসলামী বাহিনীর পরবর্তী অবস্থানস্থলে এনে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। এ জন্য তার মাথায় খুন চড়ে গিয়েছিল।
মোনাফেকদের আরোপিত অপবাদের বিবরণ দিয়ে হাসসান যে কবিতা লিখেছিলের, তার কয়েকটা ছত্র শুনেছিলের সাফওয়ান। এতে ভাষা ছিল হাসসানের, কিন্তু বক্তব্য ও মানসিকতা ছিল মোনাফেকদের।
সাফওয়ানের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল হাসসানের সাথে। এক পর্যায়ে তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে বসলেন। সাবেত বিন কায়েস মাঝখানে এসে থামানোর চেষ্টা করলেন, সাফওয়ানকে বেধে ফেললেন ও বনুহারেসের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা রসূল সা. পর্যন্ত গড়ায়। হাসসান ও সাফওয়ান দুজনকেই তিনি ডাকলেন। সাফওয়ান বললো, “হে রসূল, এই ব্যক্তি আমাকে কষ্ট দিয়েছে এবং আমার বিরুদ্ধে চরম অশালীন উক্তি করেছে। এ জন্য আমি রাগ সামলাতে না পেরে ওকে মেরেছি।” রসূল সা. নম্র ভাষায় হাসসানকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করলেন এবং সাফওয়ানের কাছ থেকে তলোয়ারের যখমের বাবদ দিয়াত (জরিমানা) আদায় করে দিলেন। (সীরাত ইবনে হিশাম,৩য় খন্ড)
সাফওয়ানের উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। তাই হাসসান নরম হলেন। কোন প্রতিশোধ স্পৃহা লালন পূর্বক পরবর্তীতে আন্দোলনের জন্য আরো ক্ষতিকর কিছু করার চিন্তা থেকে আল্লাহ তাকে রক্ষা করলেন।
পরে হযরত হাসসান গভীর অনুশোচনায় পড়েন এবং তা তার একটা কবিতায় ফুটে ওঠে। এ কবিতা দ্বারা তিনি হযরত আয়েশার ওপর লেপন করা কলংক ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। তিনি বলেনঃ
“তিনি সকল সন্দেহের উর্ধ্বে অবস্থানকারী এক পর্দানশীল সতী নারী। সরলমতি নারীদের মানসম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত। তিনি এক সুশীলা ও সচ্চরিত্রা নারী। আল্লাহ তার স্বভাবকে পবিত্র করেছেন এবং তাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করেছেন। এ যাবত যা কিছু বলা হয়েছে, তা তার ওপর আরোপিত হয়না। কেবল একজন চোগলখোরের সাজানো মিথ্যাচার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েই আমি ওসব বলেছিলাম।” (সীরাত ইবনে হিশাম ৩য় খন্ড)
এই সাথে সূরা নূর একটা সামাজিক তত্ত্বকে নীতিগত যুক্তির আকারে মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেঃ
“অসচ্চরিত্র নারীরা অসচ্চরিত্র পুরুষদের জন্য এবং অসচ্চরিত্র পুরুষেরা অসচ্চরিত্র নারীদের জন্য আর পবিত্র নারীরা পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষরা পবিত্র নারীদের জন্য। তারা তাদের মনগড়া কথাবার্তা থেকে মুক্ত।” (আয়াত-২৬)
অর্থাৎ বিয়ের জন্য সচরাচর নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে সমান সাথী খোজা হয়। মানুষ যার মধ্যে নিজের মত চরিত্র দেখতে পায়, তাকেই বাছাই করে। বিশেষোত যারা কোন সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পেছনে সমগ্র জীবনটাকে নিয়োজিত করে, তারা দাম্পত্যজীবনের জন্যও এমন সাথীই খোঁজে যে জীবনের ঐ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সহারক ও সহযোগী হতে পারে। বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত এ সত্য কিভাবে উপেক্ষা করা যায় যে, চরিত্র ও মানসিকতার ঐক্য এবং চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগীর সাহায্যই যে কোন দম্পতির মিল ও বনিবনা নিশ্চিত করতে পারে? এটা না হলে তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব কলহ ও অবনিবনা লেগেই থাকবে। এ আয়াত অপবাদ রটনাকারীদেরকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়ে বলে যে, তোমরা কি দেখতে পাওনি, দাম্পত্য জীবনের জন্য ইসলামী আন্দোলনের মহান নেতা যে মহীয়সী নারীকে মনোনীত করেছিলেন, যার সাথে তার হৃদয়ের গভীর সম্পর্ক ছিল এবং যার সাথে দৃষ্টিভংগী ও চিন্তাভাবনার একান্ততা ও সমন্বয় একটা আদর্শ নমুনা ছিল, তিনি কি পুরোপুরিই কেবল একটা সাজানো পুতুল ছিলেন যে, এক মুহুর্তের মধ্যেই সাজগোজ খসে পড়লো এবং শুধু অচল পুতুলটা অবশিষ্ট রইল?
তিনি ছিলেন এমন একটা পবিত্র ও নিষ্কলংক পরিবারের আদরের দুলালী, যে পরিবারের পিতামাতা ইসলামী আন্দোলনের প্রথম পতাকাবাহীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই আন্দোলনেরই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে তার শৈশব কেটেছে, রসূল সাঃ এর জীবন সংগিনী হয়ে তার জ্যোতির্ময় চরিত্র থেকে উপকৃত হওয়ার সবচেয়ে বেশী সুযোগ তিনিই পেয়েছেন, রসূল সাঃ এর প্রশিক্ষণের বিশেষ সুযোগ তিনিই পেয়েছেন এবং তাঁর কক্ষ বহুবার ওহির আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে। এমন পবিত্র পরিবেশে গড়ে ওঠা ও বেড়ে ওঠা একজন মহিলার চরিত্র কি এরূপ হওয়া সম্ভব যে, একটা জঘন্যতম অপবাদ তার প্রতি প্রযোজ্য হতে পারে? অথচ তার পিতামাতা, রসূল সাঃ এবং সাধারণ মুসলিম জনতার মনে এই অপবাদ রটনার পূর্বে তার সম্পর্কে এ ধরনের কোন ধারণা কল্পনাই জন্ম নিতে পারেনি! আগাগোড়া পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সততার ঔজ্বল্যে উদ্ভাসিত এক পারিবারিক পরিবেশে বহু বছর ধরে লালিত ও বিকশিত একটা নির্মল চরিত্র দ্বারা সহসাই এমন একটা জঘন্য কাজ সংঘটিত হওয়া কিভাবে সম্ভব, যার প্রাথমিক লক্ষণও কারো সামনে কখনো প্রকাশ পেলনা? এ কথা কিভাবে কল্পনা করা যেতে পারে যে, একটা চমৎকার ফলদায়ক গাছ দীর্ঘকাল ব্যাপী সুমিষ্ট ফল দিতে দিতে সহসা একদিন টক ফল দেয়া শুরু করবে?
আইন সক্রিয় হয়ে উঠলো
সূরা নুরের আলোর বন্যায় মুসলমানদের হৃদয়নগরী ঝকমকিয়ে উঠলো, জনমত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে একাগ্র চিত্তে ধাবমান হলো, এবং ইসলামী সমাজ দীর্ঘ অশান্ত পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠায় হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সূরা নূর ‘হদ্দুল কাযাফ’ (অপবাদের শাস্তি) সংক্রান্ত আইন সাথে নিয়ে এসেছিল। অপবাদ রটনাকারীরা আন্তরিকতার সাথে অনুতপ্ত হওয়া ও অপরাধের স্বীকারোক্তি দেয়া ছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণও ছিল। তারা ইসলামী আইনের সামনে নিজেদের পিঠ পেতে দিল এবং আশীটা করে বেত্রাঘাত খেয়ে নিজেদের বিবেকের পবিত্রতা বহাল করে নিল। মিসতাহ, হাসসান বিন সাবেত ও হামনা বিনতে জাহশ- এই তিনজন এ শাস্তি ভোগ করলেন। কিন্তু আসল অপরাধী আইনের ধরপাকড় থেকে রেহাই পেয়ে গেল। তবে জনমতের কাছে তার হীন স্বভাব ও জঘন্য কারসাজি পুরোপুরিভাবে ধরা পড়ে গেল এবং ইসলামী সমাজ তাকে সম্পুর্ণ গুরুত্বহীন করে একদিকে ফেলে রাখলো।
ভুলত্রুটি সবারই হয়ে থাকে। নবীগণ ছাড়া কোন মানুষই নিষ্পাপ নয়। কিন্তু হযরত আদম আঃ এর ঘটনার দুই পরস্পর বিরোধী চরিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, পাপ কাজ সংগঠিত হওয়ার পর পাপীর সামনে দুটো পথ খুলে যায়, একটা শয়তানের মনোনীত পথ। এটা হলো পাপকে আরো শক্তভাবে আকড়ে ধরার হঠকারী পথ। দ্বিতীয়টা সুস্থ ও সৎ স্বভাবের অনুকুল হযরত আদমের মনোনীত পথ। অর্থাৎ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পর অনুতপ্ত হয়ে নিজেকে শুধরে নেয়া। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ও তার সংগীরা শয়তানী পথ অবলম্বন করলো। আর হাসসান, মিসতাহ ও হামনা অবলম্বন করলেন আত্নশুদ্ধির পথ।
শাপে বর
সময়ের আবর্তনকে কল্পনার চোখে একটু পুনরুজ্জীবিত করুন এবং ক্ষণিকের জন্য নিজেকে মদিনার মাসব্যাপী অপবাদের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে নিয়ে যান। আপনার সামনে একটা ভয়াবহ ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতি ভেসে ওঠবে। যে আন্দোলন এক একজন করে কর্মী সংগ্রহ করে একটা ক্ষুদ্র বিপ্লবী কাফেলায় রূপান্তরিত হয়েছিল, যে আন্দোলন এক দীর্ঘ দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে মদিনায় ইসলামী রাষ্ট্র নামে একটা ক্ষুদ্র শান্তির নীড় তৈরী করেছিল, যে আন্দোলন বহু বছরের অশান্তি ও অরাজকতার আগুনে পোড়া বিপন্ন মানবতাকে ঐ শান্তির নীড়ে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, সেই আন্দোলনের একেবারে ভেতর থেকে যদি কোন ধ্বংসাত্মক তান্ডব জন্ম নেয়, তা হলে এর চেয়ে উদ্বেগজনক ব্যাপার আর কিছু হতে পারেনা। বিশেষত এমন এক পরিস্থিতিতে, যখন ঐ ইসলামী রাষ্ট্র চারদিক থেকে শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি ছিল, যে কোন মুহূর্তে তার কোন না কোন দিক থেকে সামরিক আগ্রাসনে পতিত হওয়ার আশংকা ছিল, এবং স্বয়ং নিজেরই অমুসলিম অধিবাসীদের একটা বড় অংশের ক্ষতিকর তৎপরতা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।
কিন্তু কোরআন তাকে শান্তনা দিল যে, ঘাবড়ানো ও উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। “এই ঘটনাকে নিজের জন্য ক্ষতিকর মনে কর না, আসলে ওটা তোমাদের কল্যাণের উপকরণ।” (নূর - ১১)
বস্তুত আদর্শবাদী ও বিপ্লবী আন্দোলনগুলো যখন মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী দুর্যোগ ও হাঙ্গামার কবলে পড়ে, তখন পরিণামের দিক দিয়ে তা অধিকতর কল্যাণ ও অগ্রগতি, সংস্কার ও নির্মাণ এবং শক্তি ও প্রতিঘাত সৃষ্টির কারণ হয়ে দেখা দেয়, চাই ঐ সব দুর্যোগ তার ভেতর থেকেই স্পষ্ট হোক কিংবা বাহির থেকে। উচ্চাভিলাষী সুযোগ্য ব্যক্তিগণের জন্য যেমন নানা রকমের উত্থান পতন, দুর্ঘটনা ও দুর্বিপাক উন্নতির সহায়ক হয়ে থাকে, তদ্রুপ চিন্তা ও কর্মের ক্ষমতাসম্পন্ন আন্দোলনগুলোর জন্য বিরোধিতা ও অরাজকতা পূর্ণ পরিস্থিতি উন্নতি ও স্থিতির পথ সুগম করে থাকে। যে সংগঠন আপন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন থাকে, যার একটা সামষ্টিক মানসিকতা গড়ে ওঠে, যার নৈতিক ও চিন্তাগত মেযাজ পরিপক্কতা লাভ করে, যার নেতৃত্বের চাবিকাঠি থাকে সদা চঞ্চল, সজাগ, বিচক্ষণ ও প্রাজ্ঞ লোকদের হাতে, যার কর্মীরা যাবতীয় বৈরী ও নৈরাজ্যবাদী শক্তির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে, সম্ভাব্য যে কোন বিবাদ ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকে এবং যার জনমত কোন ইসলাম বিরোধী মতবাদও সংগঠনের অভ্যন্তরে চালু হতে দেয়না, সে সংগঠন প্রত্যেক বৈরী আক্রমন ও বিরোধিতা থেকে কিছুনা কিছু লাভবান হয়ে থাকে।
অপবাদ ও অপপ্রচারের এই নোংরা অভিযান দ্বারাও মদিনার মহান ইসলামী রাষ্ট্র ও সংগঠন একাধিক দিক দিয়ে উপকৃত হয়েছে এবং এর পরিণতিতে তা আগের চেয়েও শক্তিশালী ও সচেতন হয়েছে।
সততা ও ন্যায়পরায়নতার এই আলোকোজ্জ্বল আন্দোলনের নেতা ও কর্মীগন মানবতার এই সব বিপজ্জনক ও সুদুরপ্রসারী দুর্বলতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে, প্রত্যক্ষ তিক্ত অভিজ্ঞতা দ্বারা। পীরমুরীদীর খানকায় বসে এগুলোর জ্ঞান অর্জন দূরে থাক, সামান্যতম ধারণাও লাভ করা যায়না এবং এর মোকাবিলার জন্যও মানুষকে তৈরী করা যায়না। এই ঘটনার মাধ্যমে সামষ্টিক জীবনের এমন বহু ফাঁকফোকর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, যার ভেতর দিয়ে সমস্ত বিধ্বংসী দোষত্রুটিগুলো ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। রসূল সাঃ ও তার সাহাবীগণ এর মাধ্যমে চিনে নিয়েছিলেন সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের জনশক্তির মধ্যে কারা মোনাফেকীর ব্যাধিতে আক্রান্ত, কারা দুর্বল ঈমানের অধিকারী, কারা স্থূল জ্ঞান ও আবেগপূর্ণ মেজাযের অধিকারী, কারা সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েও বিপথগামী হয়ে থাকে এবং কারা সরলতার কারণে শত্রুদের ধোকার শিকার হয়ে থাকে। বিশেষত কুচক্রী মোনাফেক নেতা ইসলামী সংগঠনের ভেতরে যে ক্ষুদ্র একটা উপদল সৃষ্টি করে ফেলেছিল, তা কতদূর যেতে পারে, সে কথা সুস্পষ্টভাবে জানা গিয়েছিল।
বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের এই দুর্বল দিকগুলো জেনে নেয়ার পর এমন একটা মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেল যাকে কাজে লাগিয়ে একদিকে নতুন নৈতিক নির্দেশনাবলী দিয়ে প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা করা হলো, অপরদিকে এমন সামাজিক বিধি চালু করা হলো, যা বিভিন্ন চারিত্রিক দোষ থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম। তৃতীয়ত,নতুন নতুন আইন ও দন্ডবিধি সম্বলিত একটা কঠোর ফরমান জারী করা হলো, যা মানবতার চিরস্থায়ী সামষ্টিক কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করলো।
এ ঘটনা মদিনার ইসলামী সমাজের সমষ্টিক বিবেককে ঝাঁকি দিয়ে জাগিয়ে তুললো। তার নৈতিকতাকে জাগ্রত ও তার সামষ্টিক সম্ভ্রমবোধকে সক্রিয় করে তুললো অনুভুতির কশাঘাত হেনে। মোনাফেক শক্তির এই বিব্রতকর আগ্রাসন থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর ঐ সমাজের প্রত্যেক সদস্য আগের চেয়ে সতর্ক ও মজবুত হয়ে গেল।
এই ঘটনার সময় হযরত আয়েশার সাথে সাথে যিনি সবচেয়ে বেশী যুলুমের শিকার হন, তিনি ছিলেন স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যপূর্ণ, শান্ত ও আবেগহীন আচরণ দ্বারা যে উদারতা, মহানুভবতা এবং ধৈর্য ও সহিঞ্চুতার পরিচয় দেন, তা মানুষকে বিষ্ময়ে অভিভূত করে। এ ঘটনায় রসূল সা.-এর পর ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠনের নেতৃত্ব দানকারীদের জন্য একটা শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বিশ্বমানবতাকে একটা হৃদ্যতাপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা উপহার দেয়ার জন্য তিনি চরম মানসিক নির্যাতন সহ্য করেন। যিনি সকল মানুষের মানসম্ভ্রম রক্ষার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন, সমকালীন সমাজ তাকে এই প্রতিদান দিল যে, তাঁর মান সম্ভ্রমের ওপর মিথ্যা অপবাদের কালিমা লেপন করলো। আর কেউ যদি এমন অবস্থার শিকার হতো, তাহলে হয় বিরোধীদেরকে পিষে ফেলতো, নচেত চরম হাতাশা চরম হতাশা নিয়ে ঘরের কোণে গিয়ে বসতো। কিন্তু তিনি ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক হয়ে আপন কর্তব্য পালন অব্যাহত রাখলেন।
উস্কানীমূলক তৎপরতা
মদিনার ইহুদীরা একদিকে নিজেদের সুসংহত শক্তির দম্ভে এবং অপর দিকে রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে রসূল সা. এর সাথে একটা সাংবিধানিক চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনের আওতায় এসে গিয়েছিল। সম্ভবত তারা এই নতুন রাজনৈতিক শক্তিকে যথাসময়ে ভালোমত বুঝতে পারেনি। তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তারা আঁচ করতে পারেনি। এই শক্তি যে এত দ্রুত বিকাশ লাভ করবে এবং কতিপয় চালচুলোহীন শরণার্থী ও মদিনার আনসারদের সহযোগিতায় নিছক ঈমান ও চরিত্রের বলে ইতিহাসের গতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিতে পরিণত হবে, তা তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তারা ভেবেছিল, গাছের ঝরে যাওয়া শুকনো পাতার মত মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত এই মুসলমানরা সম্ভাব্য দুর্যোগ দুর্বিপাকের প্রথম আঘাতেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর যদি কোনমতে টিকেও থাকে, তাহলেও তারা কোন শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে পারবেনা। কিন্তু কলেমায়ে তাইয়েবার বিপ্লবী প্রাণশক্তির অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে চরম বৈরী পরিবেশেও এই ক'জন মানুষ একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক অবকাঠামো গড়ে তুললো। শুধু তাই নয়, কয়েক মাসের মধ্যেই ইহুদীরা বুঝতে পারলো, ইসলামী রাষ্ট্র এমন এক উদীয়মান সূর্য যার সামনে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির প্রদীপ টিমটিমে হয়ে যাবে। বিশেষত, বদরযুদ্ধ থেকে মুসলামানদের শুধু নিরাপদে নয়, বরং বিজয় প্রতাকা ওড়াতে ওড়াতে মদিনায় ফিরে আসতে দেখে ইহুদীরা এতই হতবাক হয়ে গিয়েছিল যে, তারা নিশ্চয়ই পুরো বিষয়টা নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে বাধ্য হয়েছিল।
রসূল সা. এর সাথে সম্পাদিত শান্তি চুক্তি ইহুদীদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের মিত্র ও আইনানুগ নাগরিকে পরিণত করেছিল। কিন্তু তাদের অন্তরে বিদ্রোহ ও হিংসার আগুণ দাউদাউ করে জ্বলছিল।
এই পরস্পর বিরোধী অবস্থান তাদেরকে শেষ পর্যন্ত ষড়যন্ত্র ও নৈরাজ্যের পথে পরিচালিত করলো। সুযোগ পেলেই, আর সুযোগ না পেলে সুযোগ সৃষ্টি করে হলেও তারা চেষ্টা করতো যেভাবেই হোক মুসলমানদের সামাজিক ঐক্য বিনষ্ট করে দিতে তাদেরকে উষ্কানী দিতে, কোন না কোন উপায়ে প্রশাসন ও আইনশৃংখলাকে অচল করে দিতে, সংকটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে এবং রসূল সা: এর নেতৃত্বকে দুর্বল করে দিতে। ইহুদীদের তল্পীবাহী লোকেরা মোনাফেকের বেশে ইসলামী সমাজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকতো। তারা আনসারদের মধ্য থেকে দুর্বল ঈমানের লোকদের সাথে নিয়ে ইহুদীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতো। দুষ্কৃতি প্রবণ এই সব কূচক্রী শক্র শেষ পর্যন্ত একটা কুটিল পস্থা উদ্ভাবন করলো। তারা মুসলিম নারীদের নামে অশ্লীল কবিতা রচনা করতো, শুনিয়ে শুনিয়ে আবৃত্তি করতো ও প্রচার করতো। তাদের সুনাম ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করতো। এই নোংরা কবিতা চর্চার কারণে তাদের মনমগজ এমনভাবে গড়ে উঠে যে, সতীত্বের ন্যায় একটা মৌলিক সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তাদের মনে কোন শ্রদ্ধাবোধই ছিলনা। ইহুদীদের এই নির্লজ্জ মানসিকতা একদিন এভাবে আত্নপ্রকাশ করলো যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী যুবক পুরোপুরি গুণ্ডাদের মত আচরণ করে বসলো। বনু কাইনুকা নামক একটা ইহুদী গোত্র মদিনায় বাস করতো। তাদের বাজারে জনৈকা আরব মুসলিম মহিলা কেনাকাটা করতে গেল। দোকানদার তার সাথে প্রথমে ফস্টিনষ্টি করলো, তারপর তাকে প্রকাশ্য বাজারে উলংগ করে দিল। এই অপকর্মটা করার পর সে ও তার সাথীরা লজ্জিত হওয়ার পরিবর্তে তাকে আরো ব্যংগ বিদ্রুপ করতে লাগলো। মহিলা আরবীয় পদ্ধতিতে চিৎকার করলো ও সাহায্য প্রার্থনা করলো। তার চিৎকার শুনে জনৈক আরব যুবকের সম্ভ্রমবোধ সক্রিয় হয়ে উঠেলো এবং সে তীব্র উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে বদমায়েশ ইহুদীটাকে তৎক্ষণাত হত্যা করে ফেললো। কূচক্রীরা যা চেয়েছিল সেটাই হাতে পেয়ে গেল। আরব মুসলমান ও ইহুদীদের মধ্যে দাংগা বেধে যাওয়ার উপক্রম হলো। রসূল সা. খবর পেয়ে কালবিলম্ব না করে ঘটনাস্থলে পৌছে গেলেন। তিনি বনু কাইনুকা গোত্রকে তাদের ঘৃণ্য অপকর্মের জন্য তিরষ্কার করলেন এবং এই বলে হুঁশিয়ারও করলেন যে, “হে ইহুদী জনতা, (বদর যুদ্ধে) কোরায়েশদের যে পরিণতি হয়েছে, তোমাদেরও সেই পরিণতি হবার আগে ভালো হয়ে যাও।”
ইবনে সা’দের বর্ণনা মতে, বনু কাইনুকা গোত্র যেহেতু তীব্র বিদ্বেষ ও হঠকারিতার মনোভাব পোষণ করতো, তাই তারা উত্তেজিত স্বরে জবাব দিল: “হে মুহাম্মদ! কোরায়েশদের ক’টা লোককে মেরে ফেলেছ বলে ধরাকে সরা মনে করোনা। ওরা শক্তিহীন ও যুদ্ধবিদ্যায় অদক্ষ। আল্লাহর কসম, তুমি যদি আমাদের ওপর তলোয়ার ওঠাও, তাহলে বুঝতে পারবে, আমরাই যথার্থ লড়াকু। আমাদের মত লোকের সাথে তোমার ইতিপূর্বে কখনো পরিচয় হয়নি।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)
মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা এ যাবত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মেধাগত দিক দিয়ে ইহুদীদের চেয়ে অনেক পশ্চাৎপদ ছিল। অথচ ইসলামী আন্দোলন তাদের মধ্যে নতুন জীবনের স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল এবং একটা পবিত্র লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার লাগাতার চেষ্টা ও উদ্যম তাদেরকে পরস্পর ও মোহাজেরদের সাথে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। তাদের ভাগ্যের শুভ পরিবর্তন দেখে ইহুদীরা মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। ইহুদীদের এক কুখ্যাত ধড়িবাজ বুড়ো শাস বিন কায়েস পরিস্থিতির এই পরিবর্তনকে খুবই উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করতো। ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে তার বুক হিংসা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ থাকতো। একবার সে রসূল সা. এর সাহাবীদের একটা বৈঠকের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখতে পায়। ঐ বৈঠকে আওস ও খাজরাজের কিছু লোক পরস্পর কথাবার্তা বলছিল। তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি সম্প্রীতি ও ইসলামের সৃষ্টি করা একাত্নতা দেখে তার কলিজা যেন জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। কোথায় জাহেলী যুগের সেই মারামারী হট্টগোল, আর কোথায় একাত্নতার এই মধুর দৃশ্য। ইহুদী বুড়ো মনে মনে বলতে লাগলো, “ওহ্, বুঝেছি। এ শহর এখন তাহলে কায়লার বংশধর (আওস ও খাজরাজ গোত্রের দাদীর নাম কায়লা) মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল! ওরা যদি এভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে তো আমাদের পক্ষে স্বস্তিতে জীবন যাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।” অবশেষে তার গোত্রের লোকেরা একটা ষড়যন্ত্র পাকালো এবং জনৈক ইহুদী যুবককে তদনুসারে কাজ করার জন্য ক্রীড়নক বানালো। তারা তাকে শিখিয়ে দিল, তুমি যেয়ে মুসলমানদের বৈঠকাদিতে বসবে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বুয়াস যুদ্ধ ও তার পূর্ববর্তী সেই সব যুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে, যা আওস ও খাজরাজের মধ্যে সংগঠিত হয়েছিল। ইহুদী এজেন্ট তার উপর অর্পিত দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করলো। একবার এক মজলিসে আওস ও খাজরাজের লোকেরা মিলে মিশে বসেছিল। কথা প্রসংগে জাহেলী যুগের অন্ধকার অধ্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। ক্রমে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহ ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের সৃষ্টি হলো, পরস্পরকে হেয় করার প্রতিযোগীতা চললো এবং তা উত্তেজনায় রুপান্তরিত হলো। শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের উত্তেজিত লড়াকুরা মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালো যেন নতুন করে যুদ্ধ করে প্রমাণ করবে কার কেমন শক্তি। আওয়াজ উঠলো, “অস্ত্র আনো, অস্ত্র!” আওস ও খাজরাজ উভয় গোত্রে সাজ সাজ রব পড়ে গেল। লড়াইর স্থান ও কাল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়ে গেল। উত্তেজিত লোকেরা সব অস্ত্র সজ্জিত হয়ে বেরুচ্ছিল। এই সময় রসূল সা: মোহাজেরদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন। অত:পর নিম্নরুপ ভাষণ দিলেন:
“হে মুসলিম জনতা, আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ইসলামের পথ দেখিয়েছেন, এর মাধ্যমে তোমাদের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন, তোমাদের ঘাড়ের ওপর থেকে জাহেলিয়াতের শেকল ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, তোমাদেরকে কুফরি থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং তোমাদের পারস্পরিক প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধনে করেছেন। এর পরও তোমরা আমার উপস্থিতিতেই জাহেলিয়াতের শ্লোগান দিতে শুরু করেছ-এ কেমন কথা?”
এই সংক্ষিপ্ত ভাষণ শুনেই লোকেরা অনুভব করলো যে, এই সব কিছুই আসলে শয়তানের সৃষ্টি করা ফেতনা ও কুটিল ষড়যন্ত্র। ইসলামের শক্ররাই এ সব বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। তারা অনুতপ্ত হয়ে মাথা নোয়ালো এবং আনুগত্য প্রকাশ করে রসূল. এর সাথে ফিরে এল।
এ ধরনেরই একটা ঘটনা ঘটেছিল বনুল মুসতালিক যুদ্ধে যাওয়ার পথে। ইহুদীদের বশংবদ মোনাফেকরা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর নেতৃত্বে আনসার ও মোহাজেরদের মধ্যে বিপজ্জনক পর্যায়ের উত্তেজনা সৃষ্টি করে ফেলেছিল। এ ঘটনা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। রাসূল সা. ঐ সময়েও অত্যন্ত ক্ষিপ্রতা ও বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনেন।
এ ধরণের চক্রান্ত সমূহের মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত কুটিল চক্রান্ত ছিল মসজিদে যেরারের ঘটনা, এই চক্রান্তের আসল হোতা ছিল খাজরাজ গোত্রের আবু আমের নামক এক ভন্ড পীর। রসূল (সা:) মদীনায় আসার আগে সে পূর্বতন আসমানী কিতাব সম্পর্কে নিজের পান্ডিত্য ও দরবেশসুলভ জীবন যাপনের সুবাদে বেশ প্রভাবশালী ছিল। রসূল সা. যখন মদিনায় এসে সর্বশ্রেণীর মানুষের আশ্রয়স্থলে পরিণত হলেন, তখন আবু আমেরের প্রভাব প্রতিপত্তি শূণ্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়ালো। এ কারণে সে মনে মনে ভীষণ খাপ্পা থাকতো। উপরন্তু বদর যুদ্ধের ফলাফল তার সামনে ভবিষ্যতের যে ছবি তুলে ধরলো, তাতে সে উত্তেজনায় অধীর হয়ে পড়লো। সে একদিন মক্কার কোরায়েশ নেতাদেরকে ওহুদ যুদ্ধের জন্য উস্কে দিতে লাগলো, অপরদিকে আরবের অন্যান্য মোশরেক নেতাদের সাথে যোগসাজস করলো, স্বয়ং আনসারদেরকে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্ররোচনা দিল এবং রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে পর্যন্ত মদিনা আক্রমণ করার আমন্ত্রণ জানালো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৪র্থ খন্ড)
মোনাফেকদেরকে সে এই মর্মে প্ররোচনা দিল যেন রসূল সা. এর মোকাবিলা করার জন্য তারা একটা বিকল্প কেন্দ্র স্থাপন করে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতেই মসজিদে যেরার নির্মাণ করা হলো। এই ইসলাম বিরোধী তৎপরতার আখড়ার স্থপতিরা রসূল সা. কে নাটকীয় ভংগীতে আবেদন জানালো যে, যে সমস্ত দুর্বল ও অক্ষম লোকেরা নামাজ পড়ার জন্য বেশীদূর যেতে পারেনা, তাদের জন্যই আমরা এ মসজিদ নির্মাণ করেছি। তাছাড়া অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে এবং ঝড় বৃষ্টির সময় আশ পাশের লোকজন সহজেই এখানে সমবেত হতে পারবে। আপনি গিয়ে এর উদ্বোধন করে আসুন এবং বরকত মন্ডিত করুন। রসূল সা. তখন তাবুক রওনা হচ্ছিলেন। তিনি তবুক থেকে ফেরার সময় পর্যন্ত ব্যাপারটাকে মুলতবী করলেন। ফেরার সময় ওহির মাধ্যমে তাঁকে সাবধান করা হলোঃ
“যারা (মুসলমানদের) ক্ষতি সাধন, কুফরি করা, মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ ছড়ানো, এবং আগে থেকে আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্তদেরকে ওঁৎ পেতে থাকার ঘাঁটি বানিয়ে দেয়ার জন্য মসজিদ নির্মাণ করেছে, এবং কসম খেয়ে বলে যে, আমরা কেবল সদুদ্দেশ্যে কাজ করেছি, আল্লাহ সাক্ষী যে তারা মিথ্যুক। আপনি কখখনো তাদের নির্মিত মসজিদে নামাজ পরবেননা। তবে যে মসজিদের (অর্থাত মসজিদে কোবা) ভিত্তি প্রথম দিন থেকেই পরহেজগারীর ওপর স্থাপিত হয়েছে, এই মসজিদই আপনার নামাজ পড়ার বেশী উপযুক্ত। পবিত্রতা অর্জন করতে চায় এমন বহু লোক সেখানে রয়েছে। আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনে ইচ্ছুকদেরকে ভালোবাসেন।” (তওবা, ১০৭, ১০৮)
এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় যে, প্রতিহিংসার একটা ক্ষুদ্র বীজ কিভাবে একটা বিশাল বিষবৃক্ষের জন্ম দেয় এবং ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করার জন্য কুফরি শক্তিও কিভাবে একটা মসজিদকে ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে। লক্ষ্য করুন, ইসলামের ক্ষতি সাধনের জন্য যে সব ফেতনার সৃষ্টি করা হয়, তা কিভাবে ধর্ম ও খোদাভীতির লেবেল এঁটে আত্নপ্রকাশ করে। কত দল উপদল, কত খানকাহ, কত মসজিদ, কত মাদ্রাসা, কত প্রকাশনী এবং কত পত্রপত্রিকা আজও আমাদের সামনে এ মসজিদে যেরার মতই অসদুদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত ও লালিত হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই। এ সবের স্থপতিদেরও দাবী এটাই যে, “আমরা কেবল সদুদ্দেশ্যে কাজ করছি।”
এই মসজিদ যদি আল্লাহর এবাদতের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হতো এবং অক্ষম ও দুর্বল মুসলমানদের জন্য জামায়াতে নামায পড়ার সহজ ব্যবস্থা করাই যদি তার লক্ষ্য হতো, তা হলে এ প্রয়োজনটা রসূল সা. এর বিবেচনার জন্যই পেশ করা হতো। তখন ইসলামী সমাজের নেতাই এ মসজিদ নির্মাণের ফায়সালা করতেন। অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এটাও মুসলমানদের সামষ্টিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে নির্মিত হতো, কিন্তু তা না করে কিছু লোক গোপনে গোপনে সলাপরামর্শ করে ইসলামী সংগঠন ও তার নেতার অজান্তে একটা গোপন পরিকল্পনা করে এবং সবার অলক্ষ্যে তাদের জন্য একটা আলাদা মসজিদ বানিয়ে ফেলে। অথচ নিকটেই কোবার মসজিদটি আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, খোদাভীতির পোশাকে আবৃত হয়ে সম্পাদিত এই কাজটার পেছনে কিছুনা কিছু কারচুপি অবশ্যই রয়েছে। ওহি নাযিল হয়ে এই কারচুপি উদঘাটিত করে সমাজের সামনে রেখে দিল। কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে কর্মরত একটা সংগঠনের উপস্থিতিতে কিছু লোক যদি তার ভেতরে নিজেদের আলাদা উপদল গড়ার কথা ভাবে এবং সামষ্টিক কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচীর বাইরে নিজেদের আলাদা পরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়িত করে, তাহলে তারা তাদের খোদাভীতিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য যতই বাগাড়ম্বর করুকনা কেন এবং যতই নয়নাভিরাম বেশভূষা ধারণ করুক না কেন, তার ফলাফল ইসলামী সমাজের ক্ষতি সাধন, কুফরির প্ররোচনা ও বিভেদ সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছু হতে পারেনা।
অবশেষে মসজিদের পবিত্র নামে নির্মিত এই অপবিত্র আখড়াকে রসূল সা. এর নির্দেশে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া হলো, যাতে তার সাথে সাথে তার ঘৃণ্য ইতিহাসও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খন্ড)
মোটকথা, আল্লাহর হেদায়াতের একচেটিয়া দাবীদার ও নবীরসূলদের উত্তরাধিকারী ইহুদী গোষ্টি উস্কানী সৃষ্টির কোন সুযোগই হাত ছাড়া করেনি। কিন্তু এই সব বিব্রতকর অপতৎপরতার চেয়েও অনেক বেশী ধ্বংসাত্নক ছিল তাদের সেই সব যড়যন্ত্রমূলক তৎপরতা, যা তারা প্রতিটি যুদ্ধের সময় ইসলামী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষতি সাধনের জন্য চালাতো। আমরা পরবর্তিতে এ সব অপতৎপরতার বিবরণ দেব।
বিচার ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
যে কোন শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা তার দুটো কাজ সূচারুভাবে সম্পন্ন হওয়ার ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত থাকা চাই। দ্বিতীয়ত তার বিচার ব্যবস্থা সুচারুভাবে কাজ করতে থাকা ও তার আইন কানুন বাস্তবায়িত হতে থাকা চাই। প্রথম কাজটা বহিরাক্রমণ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য এবং দ্বিতীয়টা আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলী থেকে নিরাপদ রাখার জন্য। কিন্তু রসূল সা. এর সরকারকে এই উভয় কাজ সম্পাদনে ইহুদী ও মোনাফেকদের পক্ষ থেকে একটা প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই প্রতিরোধক শক্তিদ্বয় কিভাবে ইসলামী রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থায় বাধা দিয়েছে এবং বেসামরিক প্রশাসনকে দুর্বল করে দেয়ার জন্য কী কী কারসাজি করেছে, সেটা এখানে উল্লেখ করতে চাই। একটা নবীন রাষ্ট্রের বেসামরিক প্রশাসনকে যদি প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগই না দেয়া হয়, তাহলে সে তার আভ্যন্তরীণ সমস্যাবলীকেও নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনা, বাইরের শক্তিগুলোরও মোকাবিলা করতে সমর্থ হয় না। এমতাবস্থায় তার অস্তিত্ব অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। ইতিহাসে এমন অসংখ্য নজীর বিদ্যমান যে, বিজেতা বা বিপ্লবীরা যেখানেই কোন নতুন সরকার কায়েম করেছে, সেখানে প্রথম প্রথম বেসামরিক প্রশাসনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অস্বাভাবিক কঠোরতা ও বল প্রয়োগের সাহায্য নিতে হয়েছে। কিন্তু রসূল সা. এর সরকার যে নৈতিক মতাদর্শ ও যে বিচার ব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাতে অস্বাভাবিক বা বিধি বহির্ভূত কঠোরতার অবকাশ ছিলনা। এ জন্য মদিনার পঞ্চম বাহিনী কিছুটা খলতা ও কপটতার আশ্রয় নেয়ার সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল।
মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের যে সাংবিধানিক চুক্তির আওতায় মুসলমান মোহাজের আনসার ও ইহুদী গোত্রগুলো একটা একক রাজনৈতিক সংস্থায় একীভূত হয়েছিল, সেই চুক্তিতে স্বীকার করা হয়েছিল যে, রাজনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় দিক দিয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতা (Final Authority) মুহাম্মদ সা. এর হাতে নিবদ্ধ থাকবে। সেই দলীল আজও সুরক্ষিত আছে এবং তাতে নিম্নলিখিত দুটো স্পষ্ট ধারা বিদ্যমানঃ
(আরবী *******)
এই সাংবিধানিক চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর চুক্তিবদ্ধ ইহুদী গোত্রগুলোর ওপর আইনগত, নৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় ইসলামী রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থাকে সফল করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করা এবং রসূল সা. এর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রশাসনের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করা। একটা অসংগঠিত ও বিশৃংখল সমাজকে আইনের শাসনের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক নাগরিক শৃংখলার আওতায় নিয়ে আসা রসূল সা. এর একটা অসাধারণ ও অমূল্য কীর্তি ছিল এবং অপরাধ ও দুস্কৃতির মূলোৎপাটনের জন্য ইনসাফের স্বাভাবিক ও চিরন্তন মূলনীতিগুলোর বৈষম্যমুক্ত প্রয়োগ একটা অতীব কল্যাণময় পদক্ষেপ ছিল। এ পদক্ষেপের ফলে সুষ্ঠু নির্মল শান্তি ও নিরাপত্তামূলক পরিবেশ অন্যদের ন্যায় ইহুদীদের জন্যও উপকারী ছিল। তাছাড়া আল্লাহর আইন চালু করা ইহুদীদেরও জাতীয় লক্ষ্যবস্তু ছিল। দৃশ্যত ইহুদীরা এই সাংবিধানিক চুক্তির দায়দায়িত্ব স্বেচ্ছায় ও সানন্দে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেখানেই তারা অনুভব করতো, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন দ্বারা তাদের কোন স্বার্থ ব্যাহত কিংবা তাদের কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছে, সেখানেই তারা রাজনৈতিক, আইনগত ও নীতিগতভাবে এবং চুক্তির আলোকে অর্পিত দায়দায়িত্বকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করতো, আর সমাজ ও মানবতার সার্বিক স্বার্থকে একেবারেই উপেক্ষা করতো। একবার জনৈক ইহুদী বিবাহিত পুরুষ অপর এক বিবাহিত ইহুদী মহিলার সাথে ব্যভিচার করলো। ঘটনাটা ইহুদী সরদারদের কানে এল। তারা পরামর্শের জন্য বসলো এবং এক ব্যক্তিকে রসূল সা. এর নিকট এ কথা জানতে পাঠালো যে, এ ধরণের কুকর্মের জন্য কী শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তারা ইতিপূর্বে পরামর্শ করে স্থির করেছিল যে, মুহাম্মদ সা. যদি আমাদের সমাজে প্রচলিত ‘তাহমিয়া’র (মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে করে এলাকায় ঘোরানো) নির্দেশ দেন, তাহলে মুহাম্মদ সা. কে একজন রাজা হিসেবে মেনে নেয়া হবে এবং তার আদেশ শিরোধার্য করা হবে। কিন্তু যদি আল্লাহর কিতাবের বিধান মোতাবেক ‘রজম’ এর নির্দেশ দেন, তাহলে বুঝতে হবে (সঠিক জ্ঞান, সৎ সাহস এবং আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যের দিক দিয়ে) তিনি একজন নবী এবং সে অবস্থায় মুহাম্মদ সা. এর আদেশ মানা যাবেনা। কেননা তাহলে তোমাদের যেটুকু নেতাসূলভ প্রভাব প্রতিপত্তি এখনো অবশিষ্ট আছে তাও শেষ হয়ে যাবে। যাহোক, বার্তাবাহক এসে ইহুদী নেতাদের বার্তা হস্তান্তর করলো। এতে ইহুদী শীর্ষ নেতাদের পক্ষ থেকে এই মর্মে প্রস্তাবও দেয়া হয়েছিল যে, আমরা আপনাকে বিচারক মেনে নিচ্ছি। তাদের এ প্রস্তাব সাংবিধানিক চুক্তির পরিপন্থী ছিল। কারণ ঐ চুক্তি অনুসারে রসূল সা. স্থায়ীভাবেই মদিনার প্রধান বিচারপতি ছিলেন। সম্ভবত এ কারণেই রসূল সা. উঠলেন এবং সরাসরি ইহুদীদের ধর্মীয় কেন্দ্রে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে বললেন, ‘তোমাদের আলেমদের ডাকো।’ তৎক্ষণাত আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে নিয়ে আসা হলো। কোন কোন বর্ণনা মোতাবেক আব্দুল্লাহর সাথে আবু ইয়াসার বিন আখতা এবং ওহব বিন ইয়াহুদাও এই দলের অন্তভুক্ত ছিল। আলাপ আলোচনার সময় সবাই এক বাক্যে আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে তাওরাত সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ লোক বলে আখ্যায়িত করলো। রসূল সা. আব্দুল্লাহ বিন সুরিয়াকে নিভৃতে ডেকে নিয়ে প্রথমে আল্লাহর ভয় দেখালেন এবং বনী ইসরাইলের ইতিহাসের স্বর্ণ যুগকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তুমি কি জান যে, বিবাহিত ব্যক্তি ব্যভিচার করলে তাওরাতে তাকে ‘রজম’ (পাথর মেরে হত্যা) করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে? সে জওয়াব দিল, ‘‘আল্লাহর কসম হাঁ।’’ ওহির মাধ্যমে যে তথ্য রসূল সা. এর জানা ছিল বিরোধীদের কাছ থেকেও তার পক্ষে সমর্থন গেল। কিন্তু সাধারণ সভায় ইহুদী সরদাররা ও আলেমরা উল্টাপাল্টা তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলো। তারা জোর দিয়ে বলতে লাগলো যে, আমাদের শরীয়তের বিধান তাহামিয়াই ব্যভিচারের শাস্তি। এই পরিভাষাটির অর্থ অনুযায়ী ইহুদী ব্যভিচারীদের মুখে কালি মেখে গাধার পিঠে চড়িয়ে জনপদে ঘোরানো হতো। তাওরাতে রজমের (পাথর মেরে হত্যা করার) বিধানকে তারা শিকেয় তুলে রেখেছিল। তাদের ভেতরে যখন ব্যভিচারের ব্যাধি ছড়িয়ে পড়লো এবং তাদের উচ্চস্তরের লোকেরা পর্যন্ত এতে জড়িত হয়ে পড়লো, তখন সমাজ শরিয়তের পক্ষ অবলম্বন করার পরিবর্তে অপরাধীকে সহায়তা করতে লাগলো এবং শাস্তি লঘুতর করলো। মদিনার ইহুদী নেতারা আশংকা বোধ করলো যে তাওরাতের রজমের বিধান যদি পুনরায় চালু হয়ে যায় তাহলে কারো আর ভালাই থাকবেনা। আজ একজনের শাস্তি হবে, কাল হবে আর একজনের। এ জন্যই তারা রজমের শাস্তির বিধান রহিত করাতে চেয়েছিল। তাই বাধ্য হয়ে রসূল সা. প্রকাশ্য জনসমাবেশে তাদের কাছ থেকে তাওরাত চেয়ে পাঠালেন। তাওরাত আনা হলো এবং জনৈক ইহুদী আলেম সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে পড়ে শোনালো। তাওরাতের ঐ কপিটায় রজম সংক্রান্ত আয়াত অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এ জন্য ঐ দুরাচারী আলেম সংশ্লিষ্ট আয়াতকে হাত দিয়ে ঢেকে রেখে আগের আযাত ও পরের আয়াত পড়ে ফেললো। আব্দুল্লাহ ইবনে ছালাম (খ্যাতনামা ইহুদী আলেম, যিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন) লাফ দিয়ে এগিয়ে তার হাত সরিয়ে দিলেন এবং রসূল সা. কে দেখিয়ে বললেন, ‘‘হে রসূল, এই দেখুন রজমের বিধান সংক্রান্ত আয়াত!’’ [ইউহান্না (জন) লিখিত ইনজীলে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে, বিবাহিতা ব্যভিচারিণীর জন্য মূল তাওরাতে রজমের বিধানই লিপিবদ্ধ ছিল। জন এর ৮: ৫ আয়াতের এই উক্তিটি দেখুনঃ
‘‘তাওরাতে মূছা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন এ ধরণের মহিলাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করি।’’ তাওরাতের প্রচলিত সংস্করণগুলোতে ইহুদী মুফাসসির, ফকীহ ও বিকৃতকারীদের মিশ্রণ সত্ত্বেও ব্যভিচারের জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা ও প্রস্তরাধাতে হত্যার শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ ‘‘কোন পুরুষ যদি এমন কোন মহিলার সাথে ব্যভিচাররত অবস্থায় ধরা পড়ে, যার স্বামী আছে, তাহলে ঐ দু’জনকেই হত্যা করতে হবে।।’’ (ব্যতিক্রম অধ্যায়, আয়াত ২১-২২)
‘‘কোন কুমারী মেয়ে যদি কারো সাথে যুক্ত হয়ে যায় এবং অন্য কোন ব্যক্তি তাকে শহরে পেয়ে তার সাথে সংগম করে, তাহলে তোমরা ঐ দুজনকেই শহরের উপকণ্ঠে এনে পাথর মেরে হত্যা করবে।’’ (ব্যতিক্রম, অধ্যায় ২২, আয়াত ২৩) ২৬ নং আয়াতেও জোরপূর্বক ধর্ষণকারীর জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করা হয়েছে।] রসূল সা. এই জালিয়াতির জন্য ঐ ইহুদী আলেমকে কঠোরভাবে তিরস্কার করেন এবং এই বলে সংশ্লিষ্ট অপরাধীকে তাওরাতে ঘোষিত ‘রজম’ এর শাস্তি প্রদান করেনঃ ‘আমিই সর্ব প্রথম আল্লাহর আইন ও তার কিতাবের বিধান বাস্তবায়নের পুনঃপ্রচলন করছি।’’ (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, মুসলিম, ইহুদী জিম্মীদের ওপর রজম কার্যকর করা সংক্রান্ত অধ্যায়, যাদুল মায়াদ, ৩য় খন্ড)
এই ছিল সেকালের ইহুদী আলেমদের কারসাজি। বগলে আল্লাহর আইন চেপে রেখে তারা মনগড়া বাতিল আইন চালু করছিল। আর এহেন চরিত্র নিয়ে তারা আল্লাহর আইনকে আসল ও অবিকৃত অবস্থায় বাস্তবায়ন করতে সংকল্পবদ্ধ রসূল সা. এর পথরোধ করতে চাইছিল। তাদেরকে উদ্দেশ্য করেই কোরআন বলেছেঃ ‘‘যতক্ষণ তোমরা তাওরাত ও ইঞ্জীলকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়া বিধানকে চালু করে না দেখাবে, ততক্ষণ তোমাদের কোন ভিত্তিই নেই।’’ অর্থাৎ যতক্ষণ তোমাদের বিশ্বাসে ও কাজে এমন মারাত্মক বৈপরিত্য বিদ্যমান, ততক্ষণ তোমরা একটা অর্থহীন ও গুরুত্বহীন জনগোষ্ঠী। ইহুদীদের সর্বব্যাপী বিকৃতির একটা প্রধান লক্ষণ ছিল এই যে, তাদের সমাজ উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীতে স্থায়ীভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং আইনের চোখে সমতা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রভাবশালী লোকদের জন্য ও দুর্বলদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন ছিল। উদাহরণ স্বরূপ বনু নযীর ও বনু কুরায়যার মধ্যে দুর্বলতা ও সবলতার ভেদাভেদের কারণে বৈষম্যপূর্ণ দিয়াত (হত্যার বদলা হিসাব প্রদেয় অর্থ দণ্ড) ব্যবস্থা চালু ছিল। বনু নযীরের কোন লোক বনু কারায়যার কাউকে হত্যা করলে একশো ওয়াসাক পরিমাণ দিয়াত গ্রহণ করা হতো। পক্ষান্তরে বনু কুরায়যার কেউ বনু নযীরের কাউকে হত্যা করলে পঞ্চাশ ওয়াসাক গ্রহণ করা হতো। রসূলের সা. মদিনায় আসা এবং ইসলামী ন্যায়বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বনু নযীরের এক ব্যক্তি বনু কুরায়যার এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে হত্যাকারীর পক্ষ দ্বিগুণ দিয়াত দিতে অস্বীকার করতো এবং সমতা মেনে নেয়ার জন্য চাপ দিল। ইসলামী বিধানের সহায়তা পেয়ে এবার তাদের শক্তি বেড়ে গিয়েছিল। বাদানুবাদে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে এতদূর গড়ালো যে, উভয গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ার উপক্রম হয়। অবশেষে উভয় গোত্র তাদের বিরোধকে রসূল সা. এর কাছে নিয়ে যেতে এবং তাঁর মীমাংসা মেনে নিতে সম্মত হয়।
রসূল সা. কোরআনের নির্দেশ অনুসারে দিয়াতের এই বৈষম্যকে চিরতরে রহিত করে সমান করে দিলেন। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড, সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড) সেই সাথে কোরআন আল্লাহর সু-বিচার ব্যবস্থা পরিবর্তনকারীদেরকে এই বলে সতর্ক করে দেয়ঃ
‘‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধি মোতাবেক বিচার ফায়সালা করেনা, তারা কাফের।’’ (মায়েদা)
ইসলামের সুবিচার ব্যবস্থা ও দণ্ডবিধি (হুদুদ) বাস্তবায়নে যদি শুধু মদিনার ইহুদীরাই অন্তরায় হতো তা হলেও চলতো। আসলে সমস্যা ছিল এই যে, সামগ্রিককভাবে গোটা আরব সমাজেই বৈষম্য বিরাজ করতো। প্রভাবশালী শ্রেণীর জন্য আইন ছিল এক রকম, আর দুর্বল ও সাধারণ লোকদের জন্য অন্য রকম।
মক্কা বিজয়ের সময় বনু মাখযূম গোত্রের ফাতেমা নাম্নী এক মহিলা চুরির দায়ে ধরা পড়লো। সে একটা প্রভাবশালী গোত্রের সদস্য ছিল বলে কোরায়েশের লোকেরা তার ধরা পড়ায় বিচলিত হয়ে পড়লো। তারা এ কথা ভাবতেও পারছিল না যে, এমন এক অভিজাত মহিলার ওপরও আইনের সেই শাস্তিই চালু হবে যা সর্ব সাধারণের জন্য বিধিবদ্ধ। তারা পরামর্শক্রমে স্থির করলো, রসূল সা. কে অনুনয় বিনয় করে তাকে মুক্ত করতে হবে। কিন্তু সমস্য দেখা দিল এই যে, এই অনুনয় বিনয়টা করবে কে? অনেক ভেবে চিন্তে তারা উসামা বিন যায়েদকে সুপারিশ করতে পাঠালো। উসামা বক্তব্য পেশ করতেই রসূল সা. এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, ‘‘তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত একটা শাস্তি সম্পর্কে (রহিত করার) সুপারিশ করতে এসেছ?’’ শুধু এই কথাটুকু শুনেই উসামা বুঝে ফেললেন। তিনি ক্ষমা চাইলেন। অবশেষে রসূল সা. সমবেত জনতাকে সম্বোধন করে বললেনঃ
‘‘তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধ্বংস হয়ে যাওয়ার একটা কারণ ছিল এই যে, তাদের মধ্যে কোন সবল লোক অপরাধ করলে তা দেখেও না দেখার ভান করা হতো। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, আমার মেয়ে ফাতেমাও যদি চুরি করে, তবে আমি তার হাতও কেটে ফেলবো। (সহীহ মুসলিমঃ দণ্ডবিধি প্রয়োগের বিরুদ্ধে সুপারিশ করতে নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত অধ্যায়)
উম্মে হারেসা নাম্নী অপর এক মহিলার ক্ষেত্রে অনুরূপ মানসিকতা দেখা দেয়। এই মহিলা একজনের দাঁত ভেংগে দিয়েছিল। মামলা রসূল সা. এর আদালতে নেয়া হলে তিনি কিসাসের (দাঁতের বদলে দাঁত) আদেশ দিলেন। উম্মে রবী (সম্ভবত অপরাধিনীর বোন। কিন্তু এ ব্যাপারে রেওয়ায়াতে অস্পষ্টতা রয়েছে) এ আদেশ শুনে অবাক হয়ে রসূল সা. কে জিজ্ঞাসা করলো, ‘‘ওর কাছ থেকেও কিসাস নেয়া হবে? আল্লাহর কসম, এটা সম্ভব নয়।’’ রসূল সা. বললেন, ‘‘ওহে উম্মে রবী! কিসাস তো আল্লাহর বিধান।’’ কিন্তু ঐ মহিলা তবুও বলতে লাগলো, ‘‘আল্লাহর কসম, তার কাছ থেকে কিসাস নেয়া সম্ভব নয়।’’ তার বুঝেই আসছিলনা যে, এই পর্যায়ের অপরাধিনীর দাঁত কিভাবে ভাঙ্গা যাবে?
ওদিকে কার্যত উভয় পক্ষ দিয়াতের ব্যাপারে সম্মত হয়ে গেল। এভাবে কিসাসের বিধিও (যার ব্যাপারে দিয়াতে অবকাশও ছিল) পালিত হলো, আবার উম্মে রবীর কথাও ঠিক থাকলো। এ জন্য রসূল সা. রসিকতা করে বললেন, ‘‘আল্লাহর এমন বান্দাও আছে, যারা কসম খেলে আল্লাহ নিজেই কসম পূরণ করে দেন।’’ (সহীহ মুসলিমঃ কিসাস সংক্রান্ত অধ্যায়)
ইহুদীরা শুধু ইসলামী বিচার বিভাগের কাজেই বাধা দিতনা। বরং সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনের যেখানেই তারা সুযোগ পেত, সেখানেই বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পেত। এর একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ এই যে, খয়বর বিজয়ের পর যখন খযবরের ইহুদীদের আবেদনক্রমে তাদেরকে তাদের যমীতে অর্ধেক ফসলের বিনিময়ে ভাগচাষী করে রাখা হলো এবং ইসলামী সরকারের তহশীলদার তাদের কাছ থেকে প্রথমবার সরকারের প্রাপ্য অংশ আদায় করতে গেল, তখন তারা ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করে। দুর্নীতির যে ভয়ংকর রোগে তারা আক্রান্ত ছিল, নতুন প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরও তাতে জড়িত করতে তারা সচেষ্ট হলো। এই তহশীলদার ছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহা। রসূল সা. এর পাঠানো বিশ্বস্ত তহশীলদার খয়বরের ইহুদীদের ধারণার চেয়ে অনেক উর্ধে ছিলেন। তিনি তাদেরকে পরিষ্কার ভাষায় বললেন, ‘‘হে আল্লাহর দুশমনেরা তোমরা কি আমাকে হারাম খাদ্য খাওয়াতে চাও?’’ (সীরাতুন্নবী, শিবলী নুমানী)
তিনি বলেন, ‘‘রসূল সা. আমাকে তোমাদের কাছে এজন্য পাঠাননি যেন আমি তোমাদের সম্পদ আত্মসাৎ করি। বরঞ্চ আমাকে পাঠানো হয়েছে তোমাদের ও মুসলমানদের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করার জন্য। তোমরা রাজি থাকলে আমি অনুমান করে অর্ধেক তোমাদেরকে দিয়ে দেই, আর যদি তোমরা চাও, তবে তোমরাই অনুমান করে অর্ধেকটা আমাদেরকে দিয়ে দাও।’’
অতপর ইবনে রওয়াহা মোট ৪০ হাজার ওয়াসাক অনুমান করলেন এবং তা থেকে ২০ হাজার ওায়াসাক মুসলমানদের প্রাপ্য নিয়ে নিলেন। এই ন্যায্য বণ্টনে কিছু সংখ্যক নিচাশয় ইহুদী ক্ষেপে গিয়ে বললো, এটা যুলুম। তবে ইনসাফ প্রিয় জনসাধারণ স্বীকার করলো যে, এটাই ন্যায়সংগত। আব্দুল্লাহ ইবনে রওয়াহাই আজীবন এই দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। (বুখারী, মুযারায়া ও শিরকাত অধ্যায়)
মোটকথা একটা আধা সংগঠিত সমাজকে একটা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করায় ও আল্লাহ প্রদত্ত ইনসাফের নীতিমালার বাস্তবায়নে ধর্ম ও সভ্যতার আদি একচেটিয়া দাবীদার ইহুদী জাতি রসূল সা. কে সহযোগিতা করার পরিবর্তে পদে পদে বাধা দিতে থাকে এবং ইসলামী ব্যবস্থার শেকড়কে প্রাথমিক যুগেই উৎখাত করার অমার্জনীয় অপচেষ্টা চালায়।
রসূলের সা. পরিবারে কলহ বাধানোর অপচেষ্টা
মদিনায় বসবাসকারী ইসলামের শত্রুরা রসূলের সা. পরিবারেও বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে। তাদের দৃষ্টিতে রসূল সা. এর পরিবার ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সাথীদের মাধ্যে কলহ-কোন্দল বাধানোর জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে মোক্ষম পন্থা। ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে ঘরোয়া বিবাদে জড়িয়ে ফেলার চক্রান্ত সফল হলে তার ফলাফল অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক হতে পারতো। মদিনার সাধারণ মহিলারা তো এমনিতেই রসূল সা. এর বাড়ীতে আসা-যাওয়া করতেন। তারপর তারা যা কিছুই দেখতো, নারী জাতির স্বভাবসুলভ মনস্তত্ব অনুযায়ী তা সবার কাছে বলে বেড়াতো। এতে করে মোনাফেক ও দুশ্চরিত্র শ্রেণীর লোকেরা ভালোভাবেই জানতে পারতো যে, রসূল সা. এর পরিবারে কি ধরণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিরাজ করে। রসূল সা. এর স্ত্রীগণ অভিজাত পরিবারের মহিলা ছিলেন এবং তাদের রুচি কারো চেয়ে নিম্নমানের ছিলনা। কিন্তু অপর দিকে এই পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা যে পর্যায়ের ছিল, তাতে রসূল সা. আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকলেও তা তাদের মনোপুত সাবেক মানের চেয়ে অনেক নিম্নে ছিল। রসূল সা. এর সাথে তাঁর স্ত্রীগণও এরূপ পরিস্থিতির ওপর ধৈর্য ধারণ করতেন। তারা এটা বিলক্ষণ বুঝতেন যে, নতুন বিশ্বের স্থপতি যে প্রাণান্তকর অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন, তাতে সর্বাংগীন সুখ-শান্তি আশা করা যায় না। কিন্তু তবু মানুষ মানুষই। মানুষ সব সময়ই তার স্বাভাবিক আবেগ অনুভূতি ও আশা-আকাংখা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। রসূল সা. এর স্ত্রীগণ ঈমান ও চরিত্রের দিক দিয়ে উচ্চস্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও একাত্মতার চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত বিশ্বের সামনে পেশ করেছিলেন, তা সত্য। তথাপি একই পরিবারের সদস্যা হওয়ার কারণে তাদের কখনো কখনো পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীসূলভ মানসিকতা দ্বারা সামান্য পরিমাণে হলেও প্রভাবিত হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক ছিলনা। এ ছাড়া কোরায়েশ বংশীয়া মহিলাদের মধ্যে স্বামীর ভক্ত ও অনুগত থাকার ঐতিহ্য যতটা কঠোরভাবে পালিত হয়ে আসছিল, সেটা মদিনার মহিলাদের মধ্যে ততটা ছিলনা। মদিনার মহিলারা বরং স্বামীর ওপর বেশ খানিকটা তেজস্বিতা দেখাতো। উদাহরণস্বরূপ, হযরত ওমরের ন্যায় দোর্দন্ড প্রতাপশালী পুরুষ একবার মদিনায় থাকাকালে যখন আপন স্ত্রীকে ধমক দিলেন, তখন তিনিও সতেজে পাল্টা জবাব দিলেন। এতে অবাক হয়ে গিয়ে হযরত ওমর বললেন, ‘‘তুমি আমার মুখের ওপর জবাব দিলে?’’
এই সময়ে তিনি অনুভব করতে পারলেন যে, মুসলমানদের দাম্পত্য জীবনে মক্কার ঐতিহ্য ও ভাবধারার ওপর মদিনার পরিবেশ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে।
মোনাফেক ও দুশ্চরিত্র লোকদের কাছে এ পরিস্থিতি স্পষ্ট ছিল এবং এর মধ্য দিয়েই তারা চক্রান্ত করার সুযোগ পেয়ে যায়। তারা রসূল সা. এর পরিবারের অভ্যন্তরে বিভেদ ও বিভ্রান্তির আগুন জ্বালানোর জন্য কিছু সংখ্যক মহিলাকে গুপ্তচর হিসেবে ব্যবহার করে। এ ধরণের জনৈকা মহিলার নাম উম্মে জালদাহ। তাঁর কাজ ছিল রসূলের সা. স্ত্রীদেরকে উস্কে দেয়া। এ ধরনের মহিলা গুপ্তচরদের ষড়যন্ত্রেই হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করা সম্ভব হয়েছিল।
দুশ্চরিত্র লোকদের এ জাতীয় চক্রান্তের ফলে একাদিক্রমে এমন কতগুলো ঘটনা ঘটে, যা খুবই ক্ষতিকর হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য, রসূল সা. এর চরিত্র, বিশিষ্ট সাহাবীদের সহায়তা ও স্ত্রীগণের সৌজন্যের প্রভাবে যথাসময়ে সমস্যার নিরসন হয়ে যায়।
এ সবের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক ঘটনা ছিল ভরণ পোষণ বাবদ বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য স্ত্রীগণের দাবী। এই দাবীর ফলেই ‘ঈলা’ (রসূল কর্তৃক স্ত্রীদের সংশ্রব সাময়িকভাবে পরিত্যাগ) সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে রসূল সা. এর পক্ষ নিয়েছিলেন এবং তাদের কন্যাদ্বয়কে উৎসাহ দেয়ার পরিবর্তে কঠোরভাবে ধমকে দিয়েছিলেন। এদিকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে চ্যালেঞ্জ এলো যেঃ
‘‘হে নবী তোমার স্ত্রীদের বলে দাও, তোমরা যদি দুনিয়ার জীবন ও তার বিলাসব্যসন চাও, তবে (তা এই বাড়ীতে পাওয়া যাবে না) এস, আমি তোমাদের বিদায়ের পোশাক দিয়ে সুন্দরভাবে বিদায় করে দেই। আর যদি তোমরা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আখেরাতের জীবনকে চাও, তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ সৎ কর্মশীলা মহিলাদের জন্য বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।’’ (সূরা আহযাব)
বস্তুত রসূল সা. এর স্ত্রীদের সামনে দুটো পথ খোলা রাখা হয়েছিল। দুটো পথের যে কোন একটা তারা গ্রহণ করতে পারতো। স্ত্রীরা আপন মহত্বের গুণে তৎক্ষণাত সাবধান হয়ে গেলেন। যিনি নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি এবং অসাধারণ মেধা প্রতিভার কারণে এই দাবীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, সেই হযরত আয়েশাকেই রসূল সা. সর্বপ্রথম আল্লাহর এই সিদ্ধান্ত জানালেন। আর হযরত আয়েশাই সর্ব প্রথম ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহ ও রসূল ছাড়া আর কিছু চাইনা। তারপর একে একে অন্য সব স্ত্রীও সর্বান্তকরণে দাবীদাওয়া পরিহার করলেন।
শত্রু পরিবেষ্টিত একটি পরিবারে দুষ্ট লোকদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রের ফলে এবং নিকৃষ্ট ধরণের গুপ্তচর মহিলাদের অপতৎপরতার কারণে যদি কোন এক পর্যায়ে দ্বন্দ্ব-কলহ সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে সেটা বিচিত্র কিছু নয়। বরং এত ষড়যন্ত্রের পরও এই পরিবারটির নিরাপদে টিকে থাকাটাই তার সদস্যদের দৃঢ়তা, একাত্মতা ও মহত্বের লক্ষণ।
এবার বুঝে নিন, রসূল সা. এর চারদিকে কত রকমের ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হচ্ছিল।
হত্যার ষড়যন্ত্র
সত্যের আহ্বান যখন আন্দোলনের পরিণত হয়, তখন তার বৈরী শক্তিগুলো অন্যায় বিরোধীতা করতে গিয়ে ক্রমাগত হীনতা ও নীচতার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত তারা যখন মূল দাওয়াতে বিরুদ্ধে যুক্তিতেও হেরে যায়, এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও সহিংসতার অভিযান চালিয়েও ব্যর্থ হয়, তখন তাদের আজন্ম লালিত ঘৃণা বিদ্বেষ, গোয়ার্তুমি ও ইতরামি তাদের মধ্যে অপরাধ প্রবণ খুনী ও ডাকাতসুলভ মানসিকতা সৃষ্টি করে দেয়। এই পর্যায়ে এসে তারা ইসলামী আন্দোলনের নেতাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। এ ধরণের কুচক্রী শত্রুরা যদি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের গদিতে আসীন হয়, তাহলে তারা প্রতিপক্ষের ওপর রাজনৈতিক নির্যাতন চালায় এবং আইনের তরবারী চালিয়ে বিচারের নাটক মঞ্চস্থ করে মানবতার সেবকদের হত্যা করে। আর ক্ষমতা থেকে যারা বঞ্চিত থাকে, তারা সরাসরি হত্যার ষড়যন্ত্রমূলক পথই বেছে নেয়। মক্কার জাহেলী নেতৃত্ব এই শেষোক্ত পথই বেছে নিয়েছিল। আর এবার মদিনার ভণ্ড ধর্মগুরুরাও এই নোংরা পথই বেছে নিল।
হিজরী চতুর্থ সালের কথা। আমর বিন উমাইয়া যামরী আমের গোত্রের দুই ব্যক্তিকে হত্যা করলো। রসূল সা. এই হত্যাকান্ডের দিয়ত আদায় করা ও শান্তি চুক্তির দায়দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য বনু নাযীর গোত্রের লোকদের কাছে গেলেন। সেখানকার লোকেরা রসূল সা. কে একটা দেয়ালের ছায়ার নীচে বসালো। তারপর গোপনে সলাপরামর্শ করতে লাগলো যে, একজন উপরে গিয়ে তাঁর মাথার ওপর বিরাটকায় পাথর ফেলে দিয়ে হত্যা করবে। আমর বিন জাহ্হাশ বিন ক’ব এই দায়িত্বটা নিজের কাঁধে নিয়ে নিল। রসূল সা. তাদের দুরভিসন্ধি টের পেয়ে আগে ভাগেই উঠে চলে এলেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড; রাহমাতুল্লিল আলামীনঃ কাযী সুলায়মান মানসুরপুরী; রসূলে আকরাম কী সিয়াসী জিন্দেগীঃ ডক্টর মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ)
কুখ্যাত ইহুদী নেতা ক’ব বিন আশরাফের পিতা ছিল তাই গোত্রের লোক, আর তার মা ছিল বিত্তশালী ইহুদী নেতা আবু রাফে ইবনে আবি হাকীকের কন্যা। এই দ্বিমুখী সম্পর্কের কারণে কা’ব ইবনে আশরাফ আরব ও ইহুদীদের ওপর সমান প্রভাবশালী ছিল। একদিকে সে ছিল ধনাঢ্য, এবং অপরদিকে নামকরা কবি। ইসলামের বিরুদ্ধে তার বুক ছিল বিষে ভর্তি। (ফাতহুল বারীর) অপর এক রেওয়ায়অতে বলা হয়েছে, কা’ব একদিকে রসূল সা. কে দাওয়াত দিয়েছিল। অপর দিকে কিছু লোককে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিল যেন রসূল সা. আসা মাত্রই তাকে হত্যা করে। এই রেওয়ায়াত সূত্রের দিক দিয়ে কিছুটা দুর্বল হলেও কা’বের আক্রোশ ও তার সঠিক তৎপরতার আলোকে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।
যে সময় রসূল সা. বনু কুরায়যার সাথে চুক্তি নবায়ন করেন, সে সময় বনু নাযীর রসূল সা. কে খবর পাঠায়, আপনি তিনজন লোক নিয়ে আসবেন। আমরাও তিনজন আলেম উপস্থিত করবো। আপনি এই বৈঠকের সামনে নিজের বক্তব্য পেশ করবেন। আমাদের আলেমরা যদি আপনার বক্তব্য সমর্থন করে, তাহলে আমরা সবাই আপনার প্রতি ঈমান আনবো। রসূল সা. রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যে জানতে পারলেন, ইহুদীরা তাঁকে হত্যার প্রস্তুতি চালাচ্ছে। তাই তিনি ফিরে এলেন।
খয়বর বিজয়
খয়বর যুদ্ধের সময় জনৈকা ইহুদী মহিলা যয়নব বিনতুল হারস (ছালাম বিন মুশকিমের স্ত্রী) একটি বকরীর গোস্ত ভুনে রান্না করে এবং তাতে বিষ মিশিয়ে দেয়। এর পরে সে জিজ্ঞাসা করে, বকরীর কোন অংশ রসূল সা. বেশী ভালোবাসেন। যখন জানতে পারলো যে, সামনের পায়ের গোশত বেশী প্রিয়, তখন তাতে আরো বেশী করে তীব্র ধরণের বিষ মেশালো। তারপর সে সেই গোশত রসূল সা. ও তার সাথীদের জন্য উপঢৌকন হিসাবে পাঠালো। রসূল সা. এক লোকমা গোশত মুখে নিলেন (কিছুটা হয়তো গিলেও ফেলেছিলেন) এবং তৎক্ষণাত থুথু করে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন, এই গোশত আমাকে বলছে যে, তার সাথে বিষ মিশ্রিত। তারপর নিজেও খেলেন না, সাহাবীদেরকেও খেতে দিলেন না। পরে ঐ ইহুদী মহিলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে সে স্বীকারোক্তি করলো। আসলে এই ঘটনার পেছনে ছিল বহু ইহুদীর সম্মিলিত কারসাজি। রসূল সা. যখন সাধারণ জনসমাবেশে তাদের সবাইকে ডেকে কথা বললেন, তখন সবাই স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তারা সুকৌশলে বললো, আমরা আপনাকে যাচাই করতে চাইছিলাম যে, আপনি সত্য নবী হলে প্রকৃত সত্য জেনে ফেলবেন। নচেত আমরা আপনার কবল থেকে রেহাই পেয়ে যাবো। (সীরাতুন্নবীঃ শিবলী নোমানী, ১ম খন্ড, সূত্রঃ ফাতহুল বারী)
এই ভোজ সভায় সাহাবাদের মধ্যে হযরত বারা ইবনে মা’রুরও ছিলেন। তিনি গ্রাস মুখে নিয়ে বিষের তীব্রতা অনুভব করলেও বেআদবীর আশংকায় গ্রাস ফেললেন না। ঐ এক গ্রাসেই তাঁর ইন্তেকাল হয়ে গেল। (যাদুল মায়াদঃ ২য় খন্ড; শামায়েলে তিরমিযী; আসাহহুস সিয়ার)
তাবুক থেকে ফেরার পর মুসলমানদের বিজয়ে মোনাফেকদের মন ক্রোধের আগুনে ভাজা ভাজা হয়ে গেল। এই সব গোপন দুশমনের আশা ছিল মুসলমানরা পরাজয় বরণ করুক। কিন্তু সে আশা সফল না হওয়ায় তারা রসূল সা. কে হত্যার ষড়যন্ত্র করলো। এই ষড়যন্ত্রের বারো জন শরীক হয়। তাদের নাম হলোঃ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই, সা’দ বিন আবি সারাহ, আবু ফাতের আরাবী, আমের, আবু আমের রাহেব, জাল্লাস বিন সুয়াইদ, মাজমা বিন জারিয়া, মালীহ তায়মী, হাসান বিন নুমায়ের, তুয়াইমা বিন উবাইরিক, আব্দুল্লাহ ইবনে উয়াইনা ও মুররা বিন রবী।
ষড়যন্ত্র সভায় জাল্লাস বললোঃ ‘‘আজ রাতে আমরা মুহাম্মদকে সা. পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে না দিয়ে ছাড়বোনা, চাই মুহাম্মদ সা. ও তার সাথীরা আমাদের চেয়ে ভালোই হোক না কেন। কিন্তু আমরা যেন ছাগল আর ওরা আমাদের রাখাল হয়ে গেছে। আমরা যেন বোকা আর ওরা বুদ্ধিমান হয়ে গেছে।’’
সে আরো বললোঃ ‘‘মুহাম্মাদ সা. যদি সত্যবাদী হয, তাহলে আমরাতো গাধার চেয়েও অধম।’’ (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)
আব্দুল্লাহ বললোঃ ‘‘আজ রাত যদি জাগো, তবে আজীবন শান্তিতে থাকবে। এই লোকটাকে হত্যা করাই আজ তোমাদের একমাত্র কাজ।’’
মুররা বললোঃ ‘‘আমরা যদি শুধু একটা লোককে হত্যা করি তবে সবাই নিরাপদ হয়ে যাবে।’’
এই বারোজনের মধ্যে হাসান বিন নুমায়েরের বড় একটা ‘কৃতিত্ব’ ছিল এই যে, সে দানের সম্পদ ডাকাতি করেছিল।
অপরজন আবু আমের রাহেব দেখতে সুফী, দরবেশ ও সংসার বিরাগী ছিল। কিন্তু সে মসজিদে যেরারের উদ্যোক্তা ছিল। রোম ও গাসসানের শাসকদের সাথে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাতো। তার মুত্তাকী সুলভ পোশাকে ভন্ডামি ও দৃষ্কৃতি প্রতিফলিত হতো।
স্থির হয় যে, রসূল সা. পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে নিচে ফেলে দেয়া হবে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এই বারো জন কুচক্রী রসূল সা. এর সাথে সাথে চলতে লাগলো। রসূল সা. যখন পাহাড়ের কাছে পৌঁছলেন, সবাইকে বললেন, যারা সমতল ভূমির প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে যেতে চায় তারা সেখান দিয়ে যেতে পারে। তিনি নিজের পাহাড়ী পথ ধরে চললেন। সাহাবাদের অনেকেই সমতলের পথ ধরে গেলেন। কিন্তু কুচক্রীরা রসূল সা. এর সাথে থাকলো। রসূল সা. এর দৃষ্টি এমনিতে এত সূক্ষ্ণ ছিল যে, অন্তরের অন্তস্থলে পৌঁছে যেত এবং গোপন আবেগ অনুভুতিও বুঝে ফেলতেন। মোনাফেকরা তো রসূল সা. এর সামনেই বেড়ে উঠেছে। তাই মোনাফেকদের তাঁর চেয়ে বেশি আর কে চিনবে? তদুপরি গায়েবী ইশারা দিয়েও আল্লাহ তাকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সাবধান করে দিলেন। তিনি হুযাইফা বিন ইয়ামান এবং আম্মার বিন ইয়াসার এই দু’জনকে সাথে নিয়ে পাহাড়ী পথে চললেন। আম্মারকে সামনে রসূল সা. এর উটের লাগাম ধরে চলতে বললেন। আর হুযাইফাকে পেছনে পেছনে চলতে বললেন। বিশেষ জায়গাটা এসে গেলে কূচক্রী দলটি লাফাতে লাফাতে এসে গেল। একে অন্ধকার রাত। তদুপরি দৃষ্কৃতিকারীরা ছিল মুখোশপরা। রসূল সা. পায়ের আওয়াজ পাওয়া মাত্রই সাথীদ্বয়কে নির্দেশ দিলেন, পেছনে যারা আসছে তাদেরকে হটিয়ে দিতে। হযরহ হুযাইফা লাফিয়ে চলে গেলেন। তাদের উট দেখে তার থুতনীতে তীর নিক্ষেপ করলেন। তারা হযরত হুযাইফাকে দেখে ভাবলো, ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে। অগত্যা পেছনে পালিয়ে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদের সাথে মিশে গেল।
হযরত হুযাইফা যখন ফিরে এলেন, তখন রসূল সা. নির্দেশ দিলেন, ‘এখান থেকে উট জোরে হাঁকিয়ে নিয়ে যাও।’ আর হুযাইফাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ওদের চিনেছ? হুযাইফা বললেন, অমুক অমুকের বাহন চিনেছি। কিন্তু মানুষ চিনিনি। রসূল সা. বললেন, তুমি তাদের মনোভাব বুঝেছ? তিনি নেতিবাচক জবাব দিলেন। এরপর রসূল সা. নিজে তাকে জানালেন, ওরা আমাকে পাহাড়ের ওপর থেকে ফেলে দিতে চেয়েছিল।
পরদিন সকালে রসূল সা. ঐ বারোজন কূচক্রীকে নাম ধরে ধরে তলব করলেন। প্রত্যেকের মনোভাব ও ষড়যন্ত্র পাকানোর সমাবেশে যে যা বলেছিল, তা তাদের সামনে তুলে ধরে প্রত্যেকের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন।
তাদের সবার জবাব ছিল কৌতুকপ্রদ। যেমন হাসান বিন নুমায়ের বললো, ‘‘আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলনা যে, আপনি এসব জানবেন। কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম, আপনি যথার্থই আল্লাহর রসূল। এ যাবত আমি সাচ্চা মুসলমান ছিলাম না। আজ আমি একনিষ্ঠভাবে ইসলাম গ্রহণ করলাম।’’
প্রত্যেকের এ ধরণের ছলছুতো ও ওযর বাহানা পেশ করলো। কেউ কেউ মাফ চাইল। রসূল সা. সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন। (আসাহহুশ্ সিয়ার-মাওলানা আব্দুর রউফ দানাপুরী)
অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একাধিক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রসূল সা. শুধু হযরত হুযাইফাকে গোপনে এই ঘটনায় জড়িত অপরাধীদের নাম জানিয়েছিলেন। সাধারণ মুসলমানদের সামনে ফাঁস করেননি। তাছাড়া এই বারো জনের মধ্যে কয়েকজন সম্পর্কে কিছু কিছু মতভেদও রয়েছে। দু’তিন জন সম্পর্কে অনেকে এ কথাও বলে থাকেন যে, তাদের মধ্যে পরবর্তীকালে আর কোন মোনাফেকীর লক্ষণ দেখা যায়নি।
তবে আসল ঘটনা যথাস্থানে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। কোরআনে সেই বিষয়ই বলা হয়েছে যে, “তারা যা করতে চেয়েছিল, তা করতে পারেনি।”
রাসূল সা. এর এই মহানুভবতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। তিনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মানবতার সেবার জন্য বিপ্লব সংগঠিত করলেন। অথচ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আসল নাযুক মুহুর্তে কয়েকজন দুস্কৃতিকারী তাঁর সমগ্র কীর্তির মূলোৎপাটনের জন্য তাঁকে হত্যা করার পরিকল্পনা করে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের সমস্ত অপকর্মের রহস্য ফাঁসও হয়ে যায় এবং তারা স্বীকারোক্তিও করে। অথচ এই মহামানব এত বড় অপরাধকেও নির্দ্বিধায় ক্ষমা করে দেন। রাসূল সা. কে বলাও হয়েছিল যে, “আপনি এই অপরাধীদের প্রত্যেকের গোত্রকে নির্দেশ দিন তারা যেন ওদের মাথা কেটে আপনার কাছে এনে জমা দেয়।” কিন্তু রসূল সা. জবাব দেন, “আমি পছন্দ করিনা যে আরবরা বলাবলি করুক, মুহাম্মদ সা. কতক লোককে সাথে নিয়ে শত্রুর সাথে যুদ্ধ করেছে এবং বিজয় লাভ করার পর নিজেই সাথীদেরকেই হত্যা করতে আরম্ভ করেছে।”(তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড) এ কথা দ্বারা রসূল সা. বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, এ রকম প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ইসলামী আন্দোলনের আসল শক্তি স্বীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারবেননা। এ জন্য নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি আসুক, এবং নিত্য নতুন ষড়যন্ত্র ও নাশকতার মোকাবিলা করতে হোক-তাও তিনি সহ্য করতেন। কিন্তু এটা পছন্দ করতেন না যে, পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য বল প্রয়োগ করা হোক এবং বিশৃংখলা দেখলেই তা ক্ষমতা ও আইনের জোরে নির্মুল করা হোক। মানব সমাজের শাসন ও ব্যবস্থাপনার কাজ পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক প্রজ্ঞা, বিচক্ষনতা ও সুক্ষদর্শিতার পরিচয় দিতে হয়, অনেক স্বার্থ ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় এবং প্রতিকূলতা ও বক্রতা শোধরানোর অনেক কৌশল বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। ইসলামী বিপ্লব যে অন্যান্য বস্তুগত বিপ্লবের চেয়ে কঠিন, তার একটি কারণ হলো, এর অত্যন্ত নাযুক ও স্পর্শকাতর নৈতিক প্রাণসত্তাকে প্রতিমুহূর্তে সংরক্ষণ করতে হয়, যাতে এর স্বচ্ছতা কোন সাধারণ ভুলবুঝাবুঝি ও কোন বিরূপ প্রচারণা দ্বারা কলংকিত হতে না পারে।
রসূল সা. এর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের ঘটনাবলীর মধ্যে ইহুদীদের পক্ষ থেকে জাদুর আক্রমণও একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রকাশ্যে আক্রমণকারীরা শত্রু হলেও তারা বীর হয়ে থাকে। কাউকে হত্যা করার ইচ্ছা থাকলেও তাকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করার পর আক্রমণ করাই ন্যায় সংগত রীতি। কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সেই বীরত্ব ও সৎসাহস ছিলনা। এ জন্য তারা গোপন ও কুটিল ষড়যন্ত্রের কাপুরুষোচিত ও নারকীয় পথ অবলম্বন করে। কিন্তু এর চেয়েও নিম্নস্তরে নেমে জাদুটোনা, মন্ত্র ও ঝাড়ফুঁকের শক্তি প্রয়োগ করে কারো ওপর আক্রমণ চালানো সেই সব লোকের কাজ যারা কাপুরুষতা ও পাশবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে যায়। ইহুদী নরপশুরা হিংসা ও ক্রোধের আতিশয্যে রসূল সা. এর বিরুদ্ধে এই জঘন্যতম কাজও করতে দ্বিধা করেনি।
বনী রুযাইক গোত্রের লাবীদ বিন আসেম নামক এক ব্যক্তি ইহুদীদের মিত্র এবং বর্ণচোরা মুসলমান ছিল। তার হাত দিয়েই জাদুর আক্রমণটা চালানো হয়। একজন ইহুদী কিশোর স্বীয় জন্মগত সৎস্বভাবের কারণে রসূল সা. এর প্রতি আকৃষ্ট ছিল এবং তাঁর খিদমত করতো। কতিপয় ইহুদী তাকে বাধ্য করে রসূল সা. এর মাথার চুল ও চিরুনীর দাঁত আনিয়ে নিল। ঐ চুলের ওপর জাদুমন্ত্র পড়ে ১২টা গিরে দিয়ে যারওয়ান নামক এক কূঁয়ার মধ্যে রাখা হলো।
বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, এই জাদুক্রিয়ার ফলে, রসূল সা. এর মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবান্তর ঘটে। একটা কাজ না করেও ভাবতেন যে করেছেন। স্ত্রীদের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ওহির মাধ্যমে তিনি এই জাদুক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হন। সেই চুল বের করা হয় এবং তিনি স্বাভাবিক হয়ে যান। (তাফহীমুল কুরআন, ২য় খন্ড, টীকা-১১৪)
এ ঘটনা প্রসংগে একটা বিতর্ক চলে আসছে যে, নবীর ওপর জাদু কার্যকর হতে পারে কিনা? একটা অভিমত হলো, মোটেই হতে পারেনা। এই মত প্রয়োগ করে হাদীস অস্বীকারকারী গোষ্ঠী হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য আখ্যায়িত করেছে। অথচ একজন নবীর মানবীয় দেহ যেমন রোগ ব্যাধি, আঘাত, বিষ ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়, তেমনি তার মানসিক ক্ষমতাও যাবতীয় গোপনও প্রকাশ্য কার্যকলাপ দ্বারা উপকৃত বা ক্ষতিগ্র্রস্ত হয়ে থাকে। যেমন ফেরাউনের জাদুকরদের জাদু দেখে হযরত মুসার ওপর মানসিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। তাদের রশীগুলোকে সাপের আকৃতিপ্রাপ্ত হতে দেখে তিনি ভয় পেয়ে গিয়েছিলেনঃ (আরবী********)
“মূসা নিজের মধ্যে ভীতি অনুভব করলো। (সূরা তোয়াহাঃ ৬৭) তবে নবীদের ওপর জাদুর যে প্রভাবটা হয়না বলা হয়েছে, সেটা হলো, জাদু তাঁর নবীসুলভ তৎপরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনা। তাঁর মনমস্তিষ্কের ওপর অন্য কারো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা এবং তাঁর ইচ্ছাশক্তির ওপর থেকে তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারে না।
এই বিতর্কের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করেও এটা স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, ইহুদীরা রসূল সা. এর ওপর জাদুর আক্রমণ সত্যই চালিয়েছিল। তাদের এ অপরাধ অকাট্যভাবে প্রমাণিত একটা বাস্তবতা।
এসব ঘটনা যখন আমাদের সামনে আসে, তখন আমরা বুঝতে পারি কী কারণে মুসলমানরা মাদানী যুগে রসূল সা. এর জীবনাশংকায় উদ্বিগ্ন ও তটস্থ থাকতো? রাতের বেলা তাঁর কখনো বাড়ীর বাইরে যেতে হলে তাঁর সাথীরা প্রচন্ড দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হতেন। এই পরিস্থিতির কারণেই হযরত তালহা বিন বারা তার মৃত্যুপূর্ব অসুস্থায় ওসিয়ত করেন, আমি রাতের বেলায় মারা গেলে কেউ রসূল সা. কে খবর দিওনা। কেননা ইহুদীদের দিক থেকে তাঁর প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে। আল্লাহ না করুন, তিনি যেন আমার জানাযায় আসতে গিয়ে শত্রুদের হাতে কোন আঘাত না পান। কখনো ঘটনা চক্রে রসূল সা. সাহাবীদের চোখের আড়াল হলেই তারা ঘাবড়ে যেতেন এবং তার খোঁজে বের হতেন।
হযরত আবু হুরায়রার একটা প্রসিদ্ধ হাদীস, যাতে আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দিলেই বেহেশত প্রপ্তি সুনিশ্চিত বলা হয়েছে, তাতে এই পরিস্থিতির কিছুটা প্রতিফলন ঘটেছে। হযরত আবু হুরায়রা বলেনঃ
“আমরা রসূল সা. এর চারপাশে বসেছিলাম। আমাদের সেই বৈঠকে হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমরও ছিলেন। রসূল সা. আমাদের ভেতর থেকে উঠে কোথাও চলে গেলেন এবং অনেক দেরী করলেন। আমরা গভীর উদ্বেগে পড়ে গেলাম যে, রসূল সা. এর সাথে আমরা কেউ না থাকায় তার কোন ক্ষতি না হয়ে যায়। আমরা সবাই অস্থির হয়ে তাঁর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। সবার আগে আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তাই আমি তার সন্ধানে বেরিয়েই পড়ি।” (মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, ৩য় অধ্যায়)
খুঁজতে খুঁজতে হযরত আবু হুরায়রা বনু নাজ্জারের জনৈক আনসারীর বাগানে গিয়ে পৌঁছেন। প্রাচীরের চার পাশে ঘুরে দেখলেন কোথাও কোন দরজা আছে কিনা। কিন্তু প্রাচীরটা হয়তো লম্বা ছিল এবং ভীতি ও তাড়াহুড়োর কারণে কোন নিকটতর পথ খুঁজে পেলেন না। অবশেষে দেখলেন প্রাচীরের নীচ দিয়ে একটা ছোট পানির নালা বেরিয়ে এসেছে। তিনি খুব শুটি গুটি হয়ে (তাঁর নিজের বিবরণ মোতাবেক শৃগালের মত গুটি শুটি হয়ে) নালীর ভেতর দিয়ে প্রাচীরের ভেতরে ঢুকলেন। রসূল সা. কে সেখানে দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হলেন। এরপর তাঁর সাথে আবু হুরায়রার কথা হলো। এই সময়েই রসূল সা. সেই বিখ্যাত সুসংবাদ দেন।
একজন বিশিষ্ট সাহাবীর এই বিবরণ পড়ে বুঝা যায় যে, ইহুদী ও মোনাফেকদের প্রতিনিয়ত হত্যার ষড়যন্ত্রের কারণে মদিনার পরিবেশ কী ধরনের ছিল এবং রসূল সা. এর জীবন কি রকম ঝুঁকির মধ্যে ছিল। কিন্তু সেখানে আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এত বেশী ছিল যে, একবার এই সব আশংকা ও উৎকন্ঠার কারণে সাহাবায়ে কেরাম রসূল সা. এর চার পাশে প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু রসূল সা. কে যেহেতু আল্লাহ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, (আরবী********)
“আল্লাহ আপনাকে মানুষের কবল থেকে রক্ষা করবেন।” (সূরা মায়িদাঃ ৬৭) তাই তিনি নিজেই তাঁবুর ভেতর থেকে মাথা বের করে প্রহরীদের বললেনঃ
“তোমরা চলে যাও। আল্লাহ নিজেই আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়েছেন।” (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ২য় খন্ড)
এই ঈমানই রসূল সা. কে হত্যা করার উদ্দেশ্য এসে গ্রেফতার হওয়া অন্য এক অপরাধীকেও মুক্তি দেয়ার প্রেরণা যোগায়। তিনি বলেছিলেন, “ওকে ছেড়ে দাও। কেননা সে আমাকে হত্যা করতে চাইলেও করতে পারতোনা।” (তাফসীরে ইবনে কাছীর)
একটু ভেবে দেখুন, মানবতার প্রাসাদের এই মহান স্থপতি কত উদার মনের অধিকারী ছিলেন যে, তার বিরদ্ধে চারদিকে ক্রমাগত হত্যার ষড়যন্ত্র চলতে থাকা সত্বেও তিনি ছিলেন পর্বতের মত স্থির ও অবিচল। মদিনায় কতকগুলো মাকড়সা যেন ক্রমাগত জাল বুনে চলছিল এই দুঃসাহসী শার্দুলকে ধরার জন্য।
ওদিকে মক্কার, আগ্নেয়গিরিও ক্রমেই বিস্ফোরণ্মুখ হয়ে উঠছিল। মক্কার বুকের ভেতরে পাশবিকতা ও হিংস্রতার লাভা ক্রমেই জোরদার হচ্ছিল। হিজরতের প্রাক্কালে রসূল সা. কে হত্যার বিরাট সম্মিলিত ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, সেটা হিজরতের পর বড় বড় আগ্রাসী যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল। কিন্তু তাদের সেই সব প্রকাশ্য আগ্রাসনের ব্যর্থতা হত্যার গোপন ষড়যন্ত্র পাকাতে প্ররোচনা দিচ্ছিল।
বদরের যুদ্ধে রসূল সা. এর ক্ষুদ্র মুসলিম দলটি জাহেলিয়াতের সন্তানদের এমন উচিত শিক্ষা দিয়েছিল যে, তার ব্যাথা তারা দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভুলতে পারেনি। মক্কার কোন পরিবারই এমন ছিলনা, যার বাছাই বাছাই জোয়ান কিংবা সরদার এই যুদ্ধে মারা যায়নি। কিন্তু হাতে গনা কয়েকজন সহায় সম্বলহীন বিপ্লবী মুসলমানের হাতে মার খেয়ে তখন উহ্ আহ্ করাটাও অধিকতর লজ্জার কারণ ছিল। তাই কোরায়েশ নেতারা এই মর্মে আদেশ জারী করিয়ে দিয়েছিল যে, বদরের নিহতদের জন্য কোন শোক মা’তম করা যাবেনা। এই লড়াইতে আসওয়াদের তিন ছেলে নিহত হয়েছিল। শোকে তার কলিজা চৌচির হবার উপক্রম হলেও সে মুখে টুশব্দটিও করতে পারছিলনা। একদিন পাশের এক বাড়ী থেকে কান্নার শব্দ শুনে ভৃত্যকে পাঠালো, যাও, কাঁদার অনুমতি দেয়া হয়েছে কিনা জেনে এসো। ভৃত্য খোঁজ খবর নিয়ে এসে জানালো যে, এক মহিলার উট হারিয়ে যাওয়ায় সে কাঁদছে। এই খবর শুনে আসওয়াদ তার আবেগকে আর ধরে রাখতে পারলোনা। সে স্বতস্ফুর্তভাবে একটা কবিতা আবৃত্তি করে ফেললো। এই কবিতাটা আরবী সাহিত্যে বিশেষ কদর লাভ করেছে। এর তিনটে লাইনের অনুবাদ নিম্নরুপঃ
“একটা উট হারিয়ে যাওয়ায় ঐ মহিলা কাঁদছে এবং তার ঘুম হারাম হয়ে গেছে? উটের জন্য কেঁদনা। কাঁদতে হলে বদরের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার জন্য কাঁদো। কাঁদতে হলে আকীলের জন্য কাঁদো। কাঁদতে হলে বীরকেশরী হারেসের জন্য কাঁদো।”
মক্কার এহেন শোকতুর পরিবেশে উমাইর বিন ওহাব ও সাফওয়ান বিন উমাইয়া এক জায়গায় বসে বদরের নিহতদের জন্য কাঁদছিল। সাফওয়ান বললোঃ এখন আর বেঁচে থাকার কোন মজা নেই। উমাইর বললোঃ আমি যদি ঋণগ্রস্ত না থাকতাম এবং আমার ছেলে মেয়ে নিয়ে ভাবনা না থাকতো, তাহলে এক্ষুনি গিয়ে মুহাম্মদকে সা. কে হত্যা করে আসতাম। আমার ছেলেটাও এখনো মদিনায় বন্দী। সাফওয়ান তার ছেলে মেয়ে ও ঋণের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করলো। উমাইর তৎক্ষনাত বাড়ীতে এসে তলোয়ারে বিষ মেখে নিল এবং মদিনা অভিমুখে রওনা হয়ে গেল। মদিনায় পৌঁছার পর তার মুখমন্ডলের হাবভাব দেখে হযরত ওমর তার মনোভাব বুঝে ফেললেন এবং ঘাড় ধরে রসূল সা. এর কাছে নিয়ে এলেন। রসূল সা. ওমরকে বললেন ওকে ছেড়ে দাও। তারপর কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কী উদ্দেশ্যে এসেছ? সে বললো, ছেলেকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছি। জিজ্ঞেস করলেন, তলোয়ার ঝোলানো কেন? উমাইর বললেন, তাতে কী হয়েছে। তলোয়ার বদরে কোন কাজে লেগেছে?
এবার রসূল সা. তার মনের গোপন কথাটা বের করে তার সামনে রেখে দিলেন। তিনি বললেন, “তুমি ও সাফওয়ান একটা কক্ষে বসে আমাকে হ্ত্যার ষড়যন্ত্র করেছ। কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের্ এ ষড়যন্ত্র সফল হতে দেননি।”
কথাটা শুনে উমাইর হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে বললো, “আল্লাহর কসম, আপনি সত্যই নবী। আমি ও সাফওয়ান ছাড়া আর কেউ এ বিষয়টা জানতোনা।”
উমাইর মুসলমান হয়ে মক্কায় ফিরলো। সে সাহসিকতার সাথে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে বহু লোককে মুসলমান বানিয়ে ফেললো। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)
মক্কা বিজয়ের সময় ফুযালা বিন উমাইরও প্রতিশোধ স্পৃহার বশবর্তী হয়ে মনে মনে রসূল সা. কে হত্যা করার সংকল্প নিল। রসূল সা. কা’বা শরীফের তওয়াফ করছিলেন। সহসা ফুযালা আবির্ভুত হলো। কাছে এলে রসূল সা. ডাকলেন, “কে, ফুযালা নাকি?” সে জবাব দিল, “জ্বী, ফুযালা।” রসূল সা. বললেন।“তুমি মনে মনে কী মতলব এঁটেছ? ফুযালা ঘাবড়ে গিয়ে বললো, “কিছুই না, আমি তো আল্লাহকে স্মরণ করছি।”
রসূল সা. তার জবাব শুনে হেসে দিয়ে বললেন, “আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।” এই কথাটা বলার সাথে সাথে তিনি ফুযালার বুকের ওপর হাত রাখলেন। সংগে সংগে তার মন স্বাভাবিক হয়ে গেল। ফুযালা বলেন, রসূল সা. আমার বুকের ওপর থেকে হাত তুলে নেয়ার পর আল্লাহর সৃষ্টি জগতে রসূল সা. এর চেয়ে আর কেউ আমার কাছে প্রিয় ছিল না।” এই মনস্তাত্মিক বিপ্লবের পর ফুযালা বাড়ী ফিরে গেল। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড)
শুধু মক্কা নয়, সমগ্র আরবের বিজেতাকে হত্যা করার সংকল্প নিয়ে যে এলো, সে নতুন জীবন নিয়ে ফিরে গেল। যেই এসেছিল আঘাত হানতে, সে বরং নিজের ক্ষত স্থান সারানোর মলম নিয়ে চলে গেল।
কোরায়েশ, ইহুদী, মোনাফেক-সবাই নিজ নিজ সাধ্যমত চক্রান্ত চালিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ নিজের ওয়াদা পূর্ণ করলেন এবং তাঁর বান্দা ও রসূলকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করলেন।
এই সব ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য কেবল এক ব্যক্তিকে হত্যা করা ছিলনা, বরং এরা সবাই হত্যা করতে চেয়েছিল গোটা ইসলামী আন্দোলনকে। সত্য ও ন্যায়ের সেই উজ্জ্বল প্রভাতকে তারা বদ্ধভূমিতে পাঠাতে চেয়েছিল, যার আবির্ভাব ছিল অন্ধকারের জন্য মৃত্যুঘন্টা। যে নতুন সমাজ ব্যবস্থা শত শত বছরের শোষিত নির্যাতিত মানুষকে প্রথম বারের মত জীবনের স্পন্দন, সাম্য, স্বাধীনতা ও মান মর্যাদায় অভিষিক্ত করতে চেয়েছিল, সেই নজীরবিহীন চমৎকার সমাজ ব্যবস্থাকে তারা গলা টিপে মারতে চেয়েছিল।
সর্বনাশা বিশ্বাসঘাতকতা
ওপরে আমি মদিনার ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিগুলোর যে সব অপতৎপরতার উল্লেখ করেছি, তা নৈতিক ও আইনগত দিক দিয়ে জঘন্যতম অপরাধের পর্যায়ে পড়ে। এগুলোর দায়ে যদি কঠোরতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতো, তাহলে ধর্ম ও রাজনীতির আলোকে তা হতো সর্বোত্তম ন্যায়বিচার। কিন্তু রসূল সা. অত্যন্ত শান্ত ও ধৈর্যশীল আচরণ করলেন। যে আন্দোলনের আসল লক্ষ্য হয় মানবতার নৈতিক সংশোধন ও পুনর্গঠন, তা ক্ষমতা ও আইনের অস্ত্রের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হতে পারেনা। মানুষ যতই হীনতা ও পাশবিকতা প্রদর্শন করুক, ইসলামী আন্দোলন কখনো মানুষের স্বভাব সম্পর্কে হতাশ হয় না, বরং দীর্ঘমেয়াদী আশাবাদের ভিত্তিতে অগ্রসর হয়। এর আসল শক্তি হয়ে থাকে শেখানো, বোঝানো ও পড়ানো, শাস্তি দেয়া ও হুমকি দেয়া নয়। শাসন ক্ষমতা ও আইনের শক্তি কিছু না কিছু প্রয়োগ না করে তো কোন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজের অস্তিত্বই রক্ষা করতে পারেনা। কিন্তু মানুষের চরিত্র ও মানসিকতার পরিবর্তনের কাজ তরবারী ও লাঠি দিয়ে হয়না, নৈতিক আবেদন ও যুক্তি দ্বারা হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধের পরিবর্তে সংযম এবং প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার পরিবর্তে ধৈর্য ও সহনশীলতা অধিকতর কার্যকর হয়ে থাকে। মানবতার সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু রসূল সা. ইতিহাসের পরিমণ্ডলকে নৈতিক সদাচারের আলো দিয়ে উদভাসিত করতে চেয়েছিলেন এবং শত্রুদের বাড়াবাড়ি ও কুটিল চক্রান্তকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ধৈর্য দ্বারা জয় করতে চেয়েছিলেন। ইতিহাসে এত বড় ক্ষমার কোন নজীর খুঁজে পাওয়া যায়না যা তিনি এ ক্ষেত্রে দেখিয়েছিলেন। রসূল সা. বহু বছরের চেষ্টা সাধনা দ্বারা যেটুকু সাফল্য অর্জন করেছিলেন, গুটিকয় লোক তাকে হাঙ্গামা ও গোলযোগ বাধিয়ে ধ্বংস করে দিতে চাইল। আইন শৃংখলা ও প্রশাসনকে অচল করে দিতে চাইল। হত্যার ষড়যন্ত্র পাকালো এবং নিকৃষ্টতম পন্থায় উত্যক্ত করল। অথচ সারা পৃথিবী মধ্যে নিজস্ব মডেলের প্রথম নবীন ইসলামী রাষ্ট্রের এই রাষ্ট্রপ্রধান বিপর্যয় ও ষড়যন্ত্রের তান্ডবের মধ্য থেকে অত্যন্ত শান্তভাবে, তরংগমালাকে একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে নিজের নৌকাকে নিরাপদ স্থানে বের করে নিয়ে গেলেন।
এতদসত্ত্বেও বৈরী শক্তিগুলো অপরাধ প্রবণতা ও পাপাচারের শেষ সীমা পর্যন্ত না গিয়ে ছাড়লোনা। তারা একবার নয়, বারবার বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতার আচরণ করলো এবং তাও চরম ধৃষ্টতা সহকারে খোলাখুলিভাবেই করলো। একটা সাংবিধানিক চুক্তির মাধ্যমে যে রাষ্ট্রের তারা নাগরিক হয়েছে, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক-উভয় দিক দিয়েই যে তার আনুগত্য করা তাদের অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়েছে, তার কোন তোয়াক্কাই তারা করলোনা। বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ এমন এক কাজ, যার শাস্তি কোন কালেই নাগরিকত্ব হরণ ও মৃত্যুদন্ডের চেয়ে কম ছিল না এবং আজও নেই। কিন্তু যিনি সভ্যতার ভাগ্য পরিবর্তন করতে এসেছিলেন, তিনি এত বড় ও গুরুতর অপরাধেও চরম ধৈর্যের পরিচয় দিলেন। তিনি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেলেন, যাতে বৈরী শক্তির মধ্যে ভদ্রতা চেতনার উন্মেষ ঘটে, তাদের চিন্তাশক্তি জেগে ওঠে, তারা যুক্তির দিকে ফিরে যায়, এবং একবারে নাহোক, দু’বারে না হোক, তৃতীয়বারে যেন শুধরে যায়। কিন্তু যারা বাঁকা পথে চালিত হয়ে গিয়েছিল, অল্প সংখ্যক ব্যতিক্রম বাদে তাদের চোখ ব্যর্থতার গহবরে পতিত না হওয়া পর্যন্ত খোলেনি।
ধ্বংসাত্মক বিশ্বাসঘাতকতার কয়েকটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমি এখানে পেশ করছি, যা দ্বারা বুঝা যাবে, সত্য ও ন্যায়ের বিধান প্রতিষ্ঠাকারীদের কত কঠিন ও কণ্ঠকাকীর্ণ পথ ধরে চলতে হয়।
এ কথা সুবিদিত যে, আকাবার দ্বিতীয় বায়য়াতের বৈঠকে যে সব একনিষ্ঠ মু’মিন বান্দা রসূল সা.এর হাতে হাত দিয়ে অংগীকার করেছিল, তারা একথা বুঝে শুনেই করেছিল যে, রসূল সা.এর মদিনায় যাওয়া এবং সেখানে ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অর্থ যুদ্ধ ছাড়া কিছু নয়। এ ঘটনা নানা কারণে কোরায়েশদের জন্য বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে এবং তারা প্রচন্ড আবেগে ও উত্তেজনায় বেসামাল হয়ে অস্ত্র ধারণ করবে। এ কারণে এ বিষয়টা স্পষ্ট ছিল যে, রসূল সা.এর জীবন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলে অস্তিত্ব এবং ইসলামী আন্দোলনের অন্যান্য কেন্দ্রের সংরক্ষণ আল্লাহর সাহায্যের অধীনে পুরোপুরি মদিনাবাসীর সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যেই রসুল সা. আনসারদের প্রতিনিধি ও কর্মঠ যুবকদের কাছ থেকে অংগীকার নেন এবং এই উদ্দেশ্যেই হিজরতের প্রথম বছরেই সব কয়টা ইহুদী গোত্রের সাথেও চুক্তি সম্পাদন করেন। আনসারগণ তো সামগ্রিকভাবে নিজেদের অংগীকার জীবনের শেষ মুহূর্ত পযন্ত রক্ষা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কিতাবের আমানতদার ও নবীদের উত্তরাধিকারীরা এবং তাদের ভক্তরা নিজেদের কৃত এইসব চুক্তিকে বারংবার লংঘন করেছে।
সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা এই যে, মক্কার কোরায়েশরা মোনাফেক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে যোগ্যতম ব্যক্তি বুঝতে পেরে তাকে একটা গোপন চিঠি পাঠাল। এই চিঠির মাধ্যমে তারা মদিনার সমস্ত দুষ্কর্মপ্রবণ, উচ্ছৃংখল ও দুর্বল ঈমানের লোকদেরকে নিজেদের প্রভাবাধীন করার জন্য একটা সর্বাত্মক বার্তা পাঠায়। চিঠিতে তারা লেখে:
“তোমরা আমাদের লোককে (অর্থাৎ মুহাম্মাদ সা. কে) আশ্রয় দিয়েছ। আমরা আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, হয় তোমরা তাকে হত্যা করে ফেল, নচেত মদিনা থেকে বের করে দাও। অন্যথায় আমরা সবাই মিলে তোমাদের ওপর আক্রমণ চালাবো, তোমাদের হত্যা করবো এবং তোমাদের স্ত্রীদের প্রমোদ সংগিনী বানাবো। (সুনানে আবু দাউদ)
আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই যদি সৎ ও ঈমানদার লোক হতো, তাহলে এই চিঠি তৎক্ষণাত রসূল সা. এর কাছে পৌঁছাতো এবং সে আন্তরিকভাবে কামনা করতো যে, কোরায়েশের হুমকির মোকাবিলায় সমগ্র মদিনাবাসীর আত্মমর্যাদাবোধকে সংগঠিত করা হোক। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা ছিল তার মজ্জাগত। সে তার ক্ষমতা হারানোর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য কোরায়েশের অভিলাষ পূর্ণ করতে বদ্ধপরিকর হলো। সে জানতো, ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মদিনাবাসীর মধ্যে বিপুল সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী রয়েছে। কিন্তু এই চিঠির রহস্য শীঘ্রই ফাঁস হয়ে গেল এবং স্বয়ং রসূল সা. ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তিনি নিজেই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর কাছে চলে গেলেন এবং তাকে বুঝালেন, স্বয়ং তোমাদেরই ছেলে, ভাতিজা ও ভাগ্নেরা যৌবনের পূর্ণ শক্তি নিয়ে ইসলামের পতাকা বহন করে চলেছে। কোন অনাকাংখিত পরিস্থিতির উদ্ভব হলে দেখে নিও, তোমাদেরই সন্তানরা তোমাদের মোকাবিলায় দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদেরকে তোমাদের নিজেদের সন্তানদের সাথেই যুদ্ধ করতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই কথাটা বুঝলো এবং তার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলো। উল্লেখ্য যে, বদরের যুদ্ধের পর কোরায়েশরা পুনরায় এ ধরনের একটা চিঠি আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর কাছে পাঠিয়েছিল।
এই কুচক্রী নেতা এক চরম নাযুক মুহূর্তে মারাত্মক বিশ্বাসঘাতক সুলভ একটা কাজ করে বসলো। ইহুদী গোত্র বনু নযীরের বারংবার ওয়াদাখেলাপী ও নাশকতামূলক কার্যকলাপের কারণে যখন তাদেরকে দশ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে চলে যাওয়ার চরমপত্র দেয়া হলো, এবং বনু নযীর এ জন্য প্রস্তুতিও নিতে লাগলো, তখন আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদেরকে বার্তা পাঠালো, খবরদার! তোমরা এই আদেশ মানবেনা এবং নিজ বাড়ীঘর ত্যাগ করবেনা।
আমি তোমাদেরকে দু’হাজার লোক দিয়ে সাহায্য করবো। একদিকে ইহুদী গোত্র বনু কুরায়যা তোমাদের সাহায্য করবে, অপর দিকে আরব মোশরেক গোত্র গিতফান তো তোমাদের মিত্র আছেই। এই আশ্বাসের ফল দাঁড়ালো এই যে, বনু নযীর রসূল সা. কে জানালো, “আমরা এখান থেকে যেতে পারছিনে। আপনি যা ইচ্ছা করুন।” অবশেষে ইসলামী সরকারকে বাধ্য হয়ে নিজের হুকুম বাস্তবায়িত করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছিল।
এরপর এই লোকটি ওহুদ যুদ্ধের অতীব নাযুক ও সিদ্ধান্তকরী মুহূর্তে নগ্নভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। মুসলিম বাহিনী মদিনা থেকে বেরিয়ে ‘শুতা’ নামক স্থানে পৌঁছা মাত্রই সে তিনশো মোনাফেককে সাথে নিয়ে মদিনায় ফিরে গেল। এ কাজটা মুসলিম বাহিনীর পিঠে ছুরিকাঘাত সমতুল্য ছিল। সে বললো, আমাদের মতামত অনুসারে যখন কাজ করা হয়না এবং ক্ষমতা যখন অন্যদের হাতে কেন্দ্রীভূত, তখন আমরা খামাখা জীবন দেব কেন? আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইর মত ছিল মদিনার বাইরে না গিয়ে মদিনার ভেতরে বসেই লড়াই করার পক্ষে। (আসাহহুস্ সিয়ার আব্দুর রউফ দানপুরী)
বিশ্বাসঘাতকতামূলক যোগসাজশের দিক দিয়ে দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল আবু আমের। মসজিদে যেরার প্রসংগে তার পরিচিতি ইতিপূর্বেই দিয়েছি। বদরের যুদ্ধে রসূল সা. এর বিজয়ের সংবাদে ক্ষিপ্ত হয়ে এই কুচক্রী মক্কা সফর করে এবং আবু সুফিয়ানের সাথে সাক্ষাত করে প্রতিশোধ গ্রহণের উসকানি দেয়। এভাবে ওহুদ যুদ্ধের আগুন জ্বালাতে সেও অবদান রাখে। সে নিজেও কোরায়েশী বাহিনীর সহযোগিতার যুদ্ধে নামে। তার ধারণা ছিল, তার কথা আওস গোত্র ইসলামের সহযোগিতা পরিত্যাগ করে কোরায়েশদের পক্ষ নেবে। সে যুদ্ধের ময়দানে আওসীদেরকে ডাকলো। কিন্তু যে জবাব পেল, তাতে তার ভ্রান্তি দূর হয়ে গেল। অন্যরা দূরে থাক, স্বয়ং তার ছেলে হযরত হানযালা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে রসূল সা.এর নির্দেশে প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ওহুদের পর যে রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে গেল তাকে মদিনা আক্রমণ চালাতে প্ররোচনা দেয়ার জন্য। এদিকে মোনাফেকদেরকেও সে গোপনে আশ্বাস দিল যে, তোমরা প্রস্তুত থেক, আমি সহায়ক বাহিনী নিয়ে আসছি। এই লোকটি হুনায়েনের নিকটে রসূল সা.কে কষ্ট দেয়ার জন্য গর্ত খনন করিয়েছিল। রসূল সা. একটা গর্তে পড়ে গিয়ে বেশ ব্যথা পান (আসাহহুস সিয়ার ও সীরাতুন্নবী:শিবলী)
তৃতীয় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ছিল কা’ব বিন আশরাফ। এর সম্পর্কেও ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই ব্যক্তি একদিকে বেতন দিয়ে দিয়ে মদিনায় ভাড়াটে দালাল বাহিনী সৃষ্টি করেছিল, অপরদিকে মক্কাবাসীকে মদিনার ওপর হামলা চালাতে উস্কানি দিত। এ উদ্দেশ্যে সে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি, অর্থ সম্পদ ও কবি প্রতিভাবে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাতো। তার প্ররোচনায় আবু সুফিয়ান ও অন্যান্যরা কাবার গেলাফ ধরে প্রতিশোধ গ্রহণের অংগীকার করে।
এই ষড়যন্ত্রপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানগণ বিশেষ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হলো। রসূল সা.নিজেও রাত জাগতেন এবং তাঁর সাহাবীগণকে পালাক্রমে রাত জেগে পাহারা দিতে আদেশ দিতেন। এই সময়কার একটি ঘটনা এই যে, তিনি একবার সমাবেশে বললেন, “আজ কোন সুযোগ্য লোক পাহাড়া দিক।”এ কথা শুনে হযরত সা’দ বিন আবি ওয়াক্কাস অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে সারা রাত পাহাড়া দিলেন। এই সময় সাহাবীগণ সন্ধ্যা থেকে সকাল পযন্ত অস্ত্র নিয়ে ঘুমাতেন। সম্ভবত এই সময়ই তিনি বলেছিলেন:
“আল্লাহর পথে একদিন পাহারা দেয়া গোটা পৃথিবী ও তার ভেতরকার যাবতীয় সহায় সম্পদের চেয়েও উত্তম।” (মিশকাত)
তিনি আরো বলেন:“একদিন ও একরাত আল্লাহর পথে পাহারা দেয়া একমাস রোযা ও একমাস রাত জেগে নামায পড়ার চেয়েও উত্তম।” (ঐ)
এই পাহারা দানের কাজ সম্পর্কে তিনি আরও বলেন, এর সওয়াব কেয়ামত পর্যন্ত বাড়তেই থাকে এবং কবরের আযাব থেকেও তা রেহাই দেয়। (রিয়াদুস সালেহীন)
মদিনার এই সব বর্ণচোরা পঞ্চম বাহিনীর লোকেরা ইসলামী আন্দোলনের পিঠে ছুরিকাঘাতের সবচেয়ে মোক্ষম সুযোগ পেত জেহাদের সময়। রসূল সা.মদিনায় যে দশ বছর কাটান, তার বেশীর ভাগ সময় যুদ্ধবিগ্রহে কাটান। কিন্তু হক ও বাতিলের সংঘর্ষ যখনই পুরোদস্তুর যুদ্ধের রূপ ধারণ করতো (স্বল্প বিরতি দিয়ে বারবার এরূপ হয়েছে), তখন ইহুদী ও মোনাফেকরা ষড়যন্ত্র শুরু করে দিত। অর্থনৈতিক সংকটের পাশাপাশি এই সব যুদ্ধবিগ্রহ ও গৃহশত্রু বিভীষণদের অপতৎপরতা মিলিত হয়ে এক কঠিন অগ্নি-পরীক্ষার সৃষ্টি করতো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রহরীদের জন্য।
ওহুদের ঘটনা আমরা একটু আগেই বলেছি যে, ইসলামী বাহিনী রণাঙ্গনে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ষড়যন্ত্রের হোতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তিনশো যোদ্ধাকে নিয়ে মদিনায় চলে যায়। রসূল সা.ও সাহাবায়ে কেরামের স্থলে অন্য কোন বস্তুবাদী শক্তি যদি এরূপ পরিস্থিতির শিকার হতো, তাহলে হিম্মত হারিয়ে তৎক্ষণাৎ রণে ভঙ্গ দিত। কেননা শত্রু বাহিনীর সংখ্যা যেখানে তিন হাজার, সেখানে তাদের মোকাবিলায় গমনরত মুসলিম বাহিনীর সংখ্যা ছিল সর্বমোট এক হাজার। এর মধ্য থেকে আবার তিন শো ফেরত গেল। বাদবাকী সাত শোর মধ্যেও ছিল বর্ণচোরা মোনাফেক ছিল। এ পরিস্থিতিতে বনু সালমা ও বনু হারিসার মোজাহেদরা ফেরত যাওয়ার চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু সাহাবীদের উপদেশে তারা সাহস ফিরে পায় এবং ময়দানে টিকে থাকে। আল্লাহর উপর ঈমান, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাস, নৈতিক শক্তির সাফল্যের ধারণা এবং গায়েবী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা–এ সবই ছিল ইসলামী বাহিনীর আসল পুঁজি। ফলে তাদের মনে আর কোন দুর্বলতা থাকলোনা। পূর্ণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তারা ওহুদের ময়দান অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। তারপর ওহুদের ময়দানে যখন মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হলো এবং রসূল সা.এর শাহাদাতের গুজব রটে গেল, তখন মোনাফেকরা প্রস্তাব দিল, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হাতে পায়ে ধরে ফিরিয়ে এনে আবু সুফিয়ানের কাছ থেকে নিরাপত্তা এনে দিতে অনুরোধ করা হোক। এই ময়দানে মুসলমানদের কিছু ত্রুটি সংশোধনের জন্য আল্লাহ এক ধরনের পরাজয় দিলেন, তা নিয়ে মোনাফেকরা বলতে লাগলো, উনি যদি নবী হতেন, তা হলে পরাজিত হতেন না। এতো দুনিয়ার অন্যান্য রাজা বাদশার মত অবস্থাই হলো যে, কখনো জয় কখনো পরাজয়। এই অপপ্রচারের ফলে মুসলমানদের কারো কারো মধ্যে কিছু কিছু সন্দেহ সংশয় সৃষ্টিও হলো। কেউ কেউ এভাবে চিন্তা করতে লাগলো যে, আল্লাহর নবীর নেতৃত্বে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে গিয়েও পরাজয় বরণ করতে হলো, এ কেমন কথা? এর জবাবে কোরআনে বলা হয়েছে, “এ বিপর্যয় তোমাদেরই সৃষ্টি।” অর্থাৎ তোমাদেরই ত্রুটির ফল।
এরপর প্রতিটি যুদ্ধের শুরুতে, মাঝখানে বা শেষে গোপন শত্রুরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে থাকে। যেখানে বাস্তবে কিছু করা সম্ভব হয়নি, সেখানে অপপ্রচারের মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার চেষ্টা চলেছে।
পঞ্চম বাহিনী নিজেদের কারসাজি সবচেয়ে বেশী দেখিয়েছে খন্দক যুদ্ধের সময়। বদরের যুদ্ধে কোরায়েশদের শক্তি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে হামলা চালায় এবং ওহুদের যুদ্ধ হয়। কিন্তু তারা তাদের বিজয়কে পূর্ণতা না দিয়েই ফিরে যেতে বাধ্য হয়। ৫ম হিজরীতে তারা নিজেদের, মদিনার ষড়যন্ত্রকারীদের এবং বিভিন্ন গোত্র থেকে উস্কিয়ে আনা বিপুল এক বাহিনী নিয়ে মদিনাকে ঘিরে ফেলে। এটা ছিল চূড়ান্ত যুদ্ধ। এরপর কোরায়েশ ও অন্যান্য শত্রুদের শক্তি একেবারেই বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এরপর মুসলমানরা আত্মরক্ষার নীতি পরিত্যাগ করে ইসলামের শত্রুদেরকে নিস্তেজ করার জন্য আক্রমণাত্মক নীতি অবলম্বন করে। বস্তুত খন্দক যুদ্ধের সমাপ্তির দিনেই মক্কা বিজয়ের পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।
এই চূড়ান্ত লড়াই বাধাতে যে সব কুচক্রী মহল সর্বাধিক অবদান রেখেছিল তাদের মধ্যে বনু নযীরের ইহুদিরা অন্যতম। এদের মধ্যে যারা খয়বরে গিয়ে অবস্থান করছিল, তারা পরিস্থিতির ওপর নজর রেখেছিল এবং সুযোগের অপেক্ষায় ওঁৎ পেতে ছিল। তারা যখন জানতে পারলো, ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানরা মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। এবং কোরায়েশরা পুরো বিজয়ী না হলেও যথেষ্ট দাপট দেখিয়ে এসেছে তখনই তারা সক্রিয় হয়ে ইতিহাসের গতিধারাকে তীব্রতর করার সিদ্ধান্ত নিল। বনু নযীরের ছালাম ইবনে আবিল হাকীক, ছালাম বিন মুশকিম, হুয়াই বিন আখতাব, কিনানা বিন রবী প্রমুখ নামকরা সরদাররা বেরিয়ে পড়লো এবং বনু ওয়ায়েলের হাওযা বিন কায়েস, আবু ইমারা এবং অন্যান্যদেরকে সাথে নিল। মক্কায় গিয়ে তারা কোরায়েশদেরকে মদিনা আক্রমণ চালাতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং সর্বাত্মক সমর্থনের আশ্বাস দিল। এরপর তারা বনু গিতফানের কাছে গিয়ে তাদেরকেও উদ্বুদ্ধ করলো। এরপর অন্যান্য গোত্রের কাছেও ঘোরাফিরা করলো। কোরায়েশরা অন্যান্য গোত্রকে সংঘবদ্ধ করলো। এভাবে দশ হাজার সৈন্য মদিনাকে অবরোধ করলো।(আসাহহুস সিয়ার, সীরাতে ইবনে হিশাম)
যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হুয়াই বিন আখতাব কা’ব বিন আসয়াদের সাথে যোগসাজ করে রসূল সা.এর সাথে কৃত বনু কুরায়যার চুক্তি ভাঙ্গালো। (সীরাতে ইবনে হিশাম) এ খবর শুনে মুসলমানরা ভীষণ উদ্বিগ্ন হলো। তারা যে কোন মুহূর্তে বনু কুরায়যার হামলার আশংকা করতে লাগলো। শিশু ও মহিলাদের রক্ষার জন্য রসূল সা.তিনশো সৈনিক নিয়োগ করলেন। ওদিকে মোনাফেকরা অনিশ্চয়তা ও ভয়ভীতি সৃষ্টিকারী গুজব ছড়াতে লাগলো এবং তাদের অনেকে পরিবার পরিজনকে রক্ষার নামে ঘাঁটি থেকে ভেগে যেতে লাগলো। তারা এভাবে অপপ্রচার শুরু করে দিল যে, “একদিকে তো মুহাম্মাদ সা. আমাদেরকে রোম ও পারস্যের সাম্রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখান, অপরদিকে আমাদের অবস্থা হলো, আমরা নিরাপদে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতেও যেতে পারিনা।” (সীরাতে ইবনে হিশাম)
একবার এমনও হলো যে, লড়াই এর সময় যখন মহিলাদের থাকার জায়গার হেফাজতের সন্তোষজনক ব্যবস্থা হয়নি, তখন তার আশেপাশে একজন ইহুদীকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল। হযরত সফিয়া বিনতে আব্দুল মোত্তালেব একখানা কাঠ নিয়ে গিয়ে তাকে হত্যা করে ফেললেন। (সীরাতে ইবনে হিশাম)
ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদের জন্য এটাই ছিল সবচেয়ে উদ্বেগজনক অবস্থা। কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য তারা পেয়েছিলেন। প্রথমত খন্দকের নতুন প্রতিরক্ষা কৌশল, দ্বিতীয়ত কোরায়েশ ও বনু কুরায়যার যোগসাজশ ছিন্ন করার ব্যাপারে নঈম বিন মাসউদের বিস্ময়কর দক্ষতা, তৃতীয়ত রসূল, তাঁর সুপ্রশিক্ষিত নেতৃবৃন্দ ও গোটা মুসলিম জামায়াতের বলিষ্ঠ মোজাহেদ সুলভ ভূমিকা এবং চতুর্থত আল্লাহর প্রেরিত আকস্মিক ঘুর্ণিঝড় শত্রু বাহিনীকে ময়দান থেকে পিটিয়ে বিদায় করলো।
এ ধরনের আর একটা ঘটনা ছিল তবুক অভিযান। মদিনার কুচক্রী পঞ্চম বাহিনী এ সময় তাদের সুনিপুন কলাকৌশলের কিছু উচ্চতর নমুনা প্রদর্শন করে। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস রসূল সা.এর পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত সম্বলিত পত্র পাওয়ার পর থেকেই ক্ষিপ্ত ছিল। মাঝে ষড়যন্ত্রের হোতারাও সম্রাটের দরবারে পৌঁছে তাকে উসকে দেয়ার চেষ্টা করে। এই হিরাক্লিয়াস সম্পর্কে হঠাৎ খবর পাওয়া গেল, মদিনা আক্রমণ করার জন্য সে চল্লিশ হাজার সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী পাঠিয়ে দিয়েছে।
মদিনায় তখন একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। সময়টা ছিল দুর্ভিক্ষের। তবে গাছে গাছে ফল পেকেছে। প্রচন্ড গরম আবহাওয়া। বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে অনেক দূরে পাঠাতে হবে। অথচ সরকারের আর্থিক অবস্থা দুর্বল। প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, উট-ঘোড়া ও রসদপত্রের নিদারুণ অভাব। এ কারণে তবুক অভিযাত্রী বাহিনীকে “জাইশুল উছরাহ” ‘সংকটকালীন বাহিনী’ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এই অবস্থা দেখে এবং এ লড়াইতে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম অনুমান করে মোনাফেকরা অসহযোগিতার নীতি অবলম্বন করলো। নানা রকমের মিথ্যা ওযর দেখিয়ে তারা ঘরে বসে রইল। এদিক থেকে একে “গুয্ওয়ায়ে ফাদেহা” অর্থাৎ মোনাফেকদের “মুখোস উন্মোচনকারী অভিযান” নামেও আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। মোনাফেকরা কী কী ধরনের হাস্যকর ওযর আপত্তি পেশ করতো তার একটা চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া যায় জাদ্দ ইবনে কায়েসের কাছ থেকে। সে এসে রসূল সা.কে বললো, “লোকেরা জানে আমি নারীদের প্রতি একটু বেশী আবেগ প্রবণ। আমার আশংকা যে, সুন্দরী রোমক নারীদের দেখে আমি প্রলুব্ধ হয়ে যাবো। তাই আমাকে বাড়ীতে থাকার অনুমতি দিন।” এই সব মোনাফেক শুধু নিজেরাই জেহাদে যাত্রা থেকে পিছিয়ে থাকতোনা, বরং অন্যদেরকেও বলতো, “আরে, ঘরে বসে আল্লাহ আল্লাহ করো। পাগল হয়ে গেছ নাকি যে, এমন টাকফাটা গরমে জেহাদ করতে যেতে চাও? সুয়াইলিম নামক ইহুদীর বাড়ীতে তাদের সলাপরামর্শের আড্ডা বসতো। সেখানে যারা আসতো, তাদের জেহাদে যেতে নিষেদ করা হতো। শেষ পযন্ত এই আড্ডাখানাটা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করা হয়।
ওদিকে সদাতৎপর আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই সানিয়াতুল বেদা নামক স্থানে ইহুদী ও মোনাফেকদের সমন্বয়ে গঠিত আলাদা একটা বাহিনী অসদুদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে গড়ে তুললো। এ বাহিনীর সংখ্যাও ছিল প্রচুর। তবে এ বাহিনী রসূল সা. এর সাথে যাত্রা করতে পারেনি।
বাহিনী যাত্রা শুরু করার পর তারা আরো একটা বিভ্রাট সৃষ্টি করলো। রসূল সা.স্বীয় পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের জন্য ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে হযরত আলীকে মদিনায় রেখে এসেছিলেন। মোনাফেকরা তা দেখে অপপ্রচার শুরু করে দিল, আজকাল মুহাম্মাদ সা.এর মন আলীর প্রতি প্রসন্ন নয়। সে জন্যই তাকে সাথে নেননি। হযরত আলীর আত্মমর্যাদাবোধ এতে প্রচন্ড ধাক্কা খেল, তিনি তৎক্ষণাত অস্ত্র সজ্জিত হয়ে রসূল সা.এর সাথে মিলিত হলেন এবং মোনাফেকদের উস্কানিমূলক তৎপরতার বিবরণ দিলেন রসূল সা.তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে মদিনায় ফেরত পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, মদিনায় ঐ লোকদের দ্বারা অঘটন ঘটার আশংকা আছে।
তবুক পৌঁছার পর মোনাফেক সহযাত্রীরা (কিছু না কিছু মোনাফেক অঘটন ঘটানোর জন্য সব সময়ই সামরিক অভিযানে শরীক হতো) মুসলিম মোজাহেদদেরকে এই বলে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো, রোমক বাহিনীর দুর্ধর্ষ যোদ্ধাদেরকে তোমরা আরবদের মত ভেবেছ। কাল যখন তোমরা সবাই গোলাম হিসেবে বন্দী হয়ে যাবে, তখন বুঝবে ধারণাটা কত ভুল ছিল।’ এই বিভ্রান্তিকর প্রচারণার জন্য যখন তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হলো, তখন তারা বললো, “আমরা তো কেবল রসিকতা করছিলাম, ওটা কোন গুরুত্ববহ ব্যাপার ছিলনা।” (আসাহাহুস সিয়ার, পৃঃ ৩৬১-৩৮৫ দেখুন)
রোমক বাহিনী তো রণাঙ্গণেই আসেনি। তবে এই অভিযান দ্বারা একদিকে রোমকরাও বুঝতে পারলো, মদিনা পুরোপুরি সচেতন এবং আমাদের মোকাবিলায় আসতে সক্ষম, অপরদিকে এ অভিযানের ফলে আয়লা, জাবরিয়া ও দুমাতুল জানদাল নামক এলাকাগুলো মুসলিম শক্তির প্রভাবাধীন আসায় বহিরাক্রমণের আশংকা কমে গেল।
এই অভিযানকালে দুই জায়গায় রসূল সা.মুসলিম বাহিনীকে পথিপার্শের জলাশয় থেকে পানি খেতে নিষেধ করেন। কিন্তু কিছু কিছু মোনাফেক নিষেধাজ্ঞা লংঘন করে নিজেদের মনের ব্যাধিকে প্রকাশ করে দেয়।
এই অভিযানকালেই গিরিপথে রসূল সা. কে হত্যার ব্যর্থ ষড়যন্ত্র করা হয়। এই ঘটনার বিবরণ আমি ইতিপূর্বে দিয়ে এসেছি।
মোনাফেকদের এত বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও রসূল সা.এই অভিযানে সফলকাম হয়ে ফিরে আসেন এবং মোনাফেকদের নির্দ্বিধায় ক্ষমা করতে থাকেন। রসূল সা.এর তিনজন নিষ্ঠাবান সাহাবী কা’ব বিন মালেক, হিলাল বিন উমাইয়া ও মুরারা বিন রবী অলসতার কারণে মদিনায় থেকে যান। তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেন। তবুও তাদেরকে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হয়। এই পরীক্ষায় তারা সর্বোতভাবে সফল হন এবং তাদের তওবা কবুল হয়। কিন্তু মোনাফেকরা বলছিল, “এরা কী বেকুফ! আমাদের মত যে কোন একটা বাহানা পেশ করলেই ল্যাঠা চুকে যেত। খামাখা নিজেদেরকে বিপদে ফেলে রেখেছে। এখন বুঝুক মজা।
এ থেকে বুঝা যায় ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আন্দোলনকে কত কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মানব জাতিকে যিনি কল্যাণের পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁকে হযরত মূসার কপট অনুসারীরা ও তাদের তৈরী করা মোনাফেকদের কাছ থেকে কী কী ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্ত ভোগ করতে হয়েছে।
কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি তাতে থেকে থাকেনি, বরং বেড়েই চলে। একনিষ্ঠ ঈমান ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়েছে, আরা গাদ্দারী ও ভন্ডামী সমূলে উৎপাটিত হয়েছে।
কোরায়েশদের ঘৃণ্য প্রতিশোধমূলক তৎপরতা
মদিনায় প্রাথমিক যুগে, যুদ্ধ বিগ্রহ শুরু হওয়ার আগে, আওস গোত্রের বিশিষ্ট নেতা সা’দ বিন মুয়ায ওমরা করার জন্য মক্কায় গিয়েছিলেন। যেহেতু উমাইয়া বিন খালফের সাথে সা’দের অনেক দিনের পুরানো সম্পর্ক ছিল, তাই তিনি তার বাড়ীতেই অবস্থান করলেন। তিনি উমাইয়াকে সাথে নিয়ে কা’বা শরীফের তাওয়াফ করতে লাগলেন। ঘটনাক্রমে আবু জাহল সেখানে উপস্থিত হলো। সে উমাইয়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, “তোমার সাথে ঐ ব্যক্তি কে?” উমাইয়া বললো, “সা’দ”। আবু জাহল ক্রুদ্ধ স্বরে হযরত সাদকে বললো, “তোমরা ঐ ধর্মচ্যুতদের আশ্রয় দিয়েছ তাই না? তোমার মত লোকেরা কা’বা শরীফের চত্তরে পা রাখবে, এটা আমার অসহ্য। তুমি যদি উমাইয়ার আশ্রয়ে না থাকতে, তাহলে আজ জ্যান্ত ফিরে যেতে পারতেনা।” (সীরাতুন্নবী; শিবলী নুমানী, প্রথম খন্ড, সহীহ মুসলিম, বুখারীর বরাতসহ)
লক্ষ্য করুন যে, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কোরায়েশ নেতার স্পর্ধা এতদুর বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তার ঘরে প্রবেশকে নিষিদ্ধ করে দিতে উদ্যত। তাদেরকে হজ্জের ন্যায় এবাদাত থেকে বঞ্চিত করতে চায়! যেন কা’বা শরীফও তাদের সম্পত্তি। আসলে মসজিদুল হারামের মুতাওয়াল্লীগিরিকে তারা নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতিয়ারে পরিণত করে রেখেছিল। রসূল সা.ও তাঁর যে সব সাথীকে হিজরত করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তাদের জন্য তো হারাম শরীফের দ্বার রুদ্ধ ছিলই। কিন্তু সা’দ ইবনে মায়াযকে এরূপ খোলাখুলিভাবে হারাম শরীফে প্রবেশের অযোগ্য আখ্যা দিয়ে আবু জাহল তার অন্যায় অবস্থানকে অত্যন্ত কুৎসিতভাবে নগ্ন করে দিয়েছিল। ও দিকে সা’দ বিন মায়া’যও তো কোন আত্মমর্যাদাহীন দরবেশ ছিলেন না। তাঁর ভেতরে ইসলামী সম্ভ্রমবোধ পুরোমাত্রায় সক্রিয় ছিল এবং তিনি মদিনার রাজনৈতিক শৌযবীযের অর্থ জানতেন। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষায় এমন জবাব দিলেন যে, আবু জাহল ও কোরায়েশ সম্প্রদায়ের চোখের সামনে এক ভয়াবহ বিপদ ভেসে উঠলো। সা’দ বললেন, “তোমরা যদি আমাদের হজ্জ বন্ধ করে দাও, তবে আমরা তোমাদের মদিনার (বাণিজ্যিক) পথ বন্ধ করে দেব।” অন্য কথায় এটা ছিল কোরায়েশদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি। এ হুমকি সমগ্র মক্কাবাসীকে সচকিত করে তুললো। পরবর্তীকালে হযরত সা’দের এই উক্তি অনুসারেই মদিনার নীতি নির্ধারিত হয়। ফলে কোরায়েশ একেবারেই অনন্যোপায় হয়ে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে প্রস্তুত হয়ে যায়।
আবু জাহল উত্তেজনার বশে এমন কথা বলে ফেলেছিল বটে তবে এই অনাকাংখিত হুমকি তাদের প্রভাব প্রতিপত্তিকে প্রচন্ড ধাক্কা দেয়। পবিত্র কোরআন হারাম শরীফের ওপর তাদের এই একচেটিয়া কর্তৃত্বের কঠোর সমালোচনা করে। কেননা এটাকে পুঁজি করেই তারা আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর ঘরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করছিল। আল্লাহ বলেনঃ
“সেই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালিম আর কে, যে আল্লাহর মসজিদগুলোতে আল্লাহর স্মরণ বন্ধ করে এবং ওগুলোকে জনশূন্য করার চেষ্টা করে?” (আল-বাকারা, ১১৪)
“লোকেরা জিজ্ঞেস করে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা কেমন? তুমি বল, নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়। কিন্তু আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ঠেকানো, আল্লাহর সাথে কুফরি করা, আল্লাহর বান্দাদেরকে মসজিদুল হারামে যেতে না দেয়া এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করা তার চাইতে বড় অন্যায়।” (বাকারা, ২১৭)
“এখন কোন কারণে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেননা যখন তারা মসজিদুল হারামের পথ রোধ করছে? অথচ তারা এই মসজিদের বৈধ মুতাওয়াল্লী নয়।”
কোরআনের এ সব উক্তি ক্রমশ সারা আরবে ছড়িয়ে পড়লো এবং কোরায়েশদের ধর্মীয় ভাবমূর্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে লাগলো।
হোদাইবিয়ার সন্ধির (৬ষ্ঠ হিজরীর জিলকদ মাসে) সময় কোরায়েশরা মসজিদুল হারামে যেতে মানুষকে বাধা দেয়ার’ কাজটা আরো বড় আকারে করলো। আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে একটা ইংগিত পেয়ে রসূল সা. কেবল ওমরাহ আদায় করার উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে যাত্রা করেন। কোন যুদ্ধের ঘোষণা দেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে সাহাবীগণ ওমরার জন্য বের হন। কুরবানীর পশুও সাথে নেয়া হয়। সামরিক প্রয়োজনে অস্ত্রসজ্জিত না হয়ে নিছক মামুলী আত্মরক্ষামূলক হাতিয়ার নিয়ে কাফেলা রওনা হয়। যুল হুলায়ফা নামক স্থানে সুপরিচিত বিধি অনুযায়ী কুরবানীর উটগুলোকে চিহ্নিত করা হয় এবং ওগুলোর গলায় মালা পরানো হয়। এসব দেখে প্রথম দৃষ্টিতেই যে কেউ অনুমান করতে পারে যে, এই উট হারাম শরীফে কুরবানী করার জন্য নেয়া হচ্ছে এবং এগুলো সামরিক বাহক নয়। পথিমধ্যেই বার্তাবাহক বিশর বিন সুফিয়ান আল কা’বীর মাধ্যমে জানা গেল, কোরায়েশরা সর্বাত্মক যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং কোনক্রমেই হারাম শরীফে যেতে দেবেনা। হুদাইবিয়া পৌঁছে রসূল সা.বার্তা পাঠালেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, বরং ওমরা করতে এসেছি। বনু খুযায়া গোত্রের বুদাইল বিন ওয়ারাকা মধ্যস্থতার চেষ্টা করলো। তারপর উরওয়া বিন মাসউদ আলাপ আলোচনা কিছুটা এগিয়ে নিলেন। এরপর বনু কিনানার এক ব্যক্তি হুলাইস মধ্যস্থতা করার জন্য ছুটে এল। সে যখন স্বচোক্ষে মালা পরা উটের এক বিরাট বহর মাঠে চরতে দেখলো তখন অভিভূত হয়ে গেল। সে গিয়ে কোরায়েশদেরকে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলে তারা “তুমি মিয়া গ্রাম্য মানুষ এ সবের কী বুঝবে?” বলে তাকে নিদারুণভাবে নিরুৎসাহিত করলো। হুলাইস খুবই মর্মাহত হলো। সে বললোঃ
“হে কোরায়েশ, এটা আমাদের ও তোমাদের চুক্তি নয়। এর ভিত্তিতে আমরা মৈত্রী সম্পর্কও স্থাপন করিনি। আল্লাহর ঘরের মর্যাদা বাড়াতে এসেছে, এমন লোকদেরকে কোন্ যুক্তিতে আল্লাহর ঘরে আসতে বাধা দেয়া হবে? আল্লাহর কসম, মুহাম্মাদ সা.যা করতে চায়, তা তাকে করার সুযোগ দাও। নচেত আমরা আমাদের সকল লোকজনকে ফেরত নিয়ে যাবো।”
রসূল সা.এর সরল ও স্বচ্ছ নীতি এই লোকটার ভালো লেগেছিল। তার ভালোমন্দ বাদবিচারের ক্ষমতা কাজ করতে আরম্ভ করেছিল এবং তার বিবেক কোরায়েশদের অন্যায় কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। অবশেষে তার মন রক্ষার খাতিরে তাকে এই বলে শান্ত করা হলো যে, আমাদের উদ্দেশ্য কিছু সংগত শর্ত মানানো। তুমি একটু চুপ থাক।” এরপর এমন শর্তাবলী আরোপ করা হলো যে, আর কিছু না হোক রসূল সা.ও তার সাথীগণের ৬ষ্ঠ হিজরীর ঐ ওমরা কার্যত এক বছরের জন্য পিছিয়ে দেয়া হলো। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, ৪র্থ খন্ড, সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, আসাহহুস সিয়ার)
এ পর্যায়ে আল কোরআন কা’বার রক্ষকদের হীন মানসিকতার মুখোস কিভাবে খুলে দিয়েছে দেখুনঃ
“এরাই সেই সব লোক, যারা (সত্য দ্বীনকে) অস্বীকার করার নীতি অবলম্বন করেছে, তোমাদের মসজিদুল হারামে যাওয়া বন্ধ করেছে এবং কুরবানীর পশুকে বদ্ধভূমি পর্যন্ত যেতে দেয়নি।” (আলফাতাহ, ২৫)
হযরত ইবরাহীম আ. এর আমল থেকে যে সব ধর্মীয় রীতিপ্রথা সর্বসম্মতভাবে চলে আসছিল, তাতে কোরায়েশদের হস্তক্ষেপ ও রদবদল তাদের ভাবমূর্তিকে নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন করে। তারা নিছক বোকামি ও হঠকারিতার মাধ্যমে সমগ্র আরবে নিজেদের সম্পর্কে একটা বিরূপ জনমত গড়ে তোলে। জনসাধারণ বুঝতে পারে যে, কোরায়েশদের মধ্যে সততা, ধর্মপরায়ণতা ও ভদ্রতার নামগন্ধও নেই এবং তারা যা-ই করছে নিছক জিদের বশে করে চলেছে।
কোরায়েশদের প্রতিশোধ স্পৃহা যে পাশবিকতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গিয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো, তারা নিজেদের মনের আক্রোশ মেটানোর জন্য রসূল সা.এর দুই মেয়েকে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে তালাকে আনিয়ে ছাড়ে। এটি ছিল মানবতার মুক্তিদূতের ঠিক কলিজার ওপর এক নিদারুণ বিষাক্ত ছোবল।
হযরত রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয়েছিল আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সাথে। প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী নিকটতম আত্মীয়ের পরিবারের সাথে তাদের এ সম্পর্ক নবুয়তের আগে থেকেই চলে আসছিল। চরম বদরাগী আবু লাহাবের মধ্যে এতটুকু সৌজন্যবোধের অস্তিত্বই ছিলনা যে, সে আদর্শিক বিরোধকে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উর্দ্ধে রাখবে এবং আত্মীয়তার অধিকারকে বিরোধের সাথে জড়িয়ে ফেলবে। তার হিংসা বিদ্বেষ সব সময়ই অতিমাত্রায় তীব্র ছিল এবং তার কার্যকলাপ ছিল অত্যন্ত হীন ও ইতরসূলভ। তার ঘৃণ্য কার্যকলাপের কারণে যখন সূরা লাহাব নাযিল হলো এবং তাতে “আবু লাহাবের দুই হাত ধ্বংস হোক” বলে অভিশাপ দেয়া হলো, তখন সে ক্ষেপে গেল। দুই হাত ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, সে সব রকমের বিরোধী ও ক্ষতিকর কাজ করেও ইসলামী আন্দোলনের কিছু মাত্রও ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা এবং সততার শক্তি তার দুই দুই হাত ধ্বংস হওয়ার অর্থ হলো, সে সব রকমের বিরোধী ও ক্ষতিকর কাজ করেও ইসলামী আন্দোলনের কিছু মাত্রও ক্ষতি সাধন করতে পারবেনা এবং সততার শক্তি তার দুই হাতকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবে। কথাটার এই মর্ম উপলব্ধি করেই সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গিয়েছিল। সে নিজের দুই ছেলেকে এই বলে চাপ দিতে লাগলো যে, এখন আর মুহাম্মাদের সা. মেয়েদেরকে ঘরে রাখা তোমাদের জন্য কিছুতেই বৈধ হতে পারেনা। ওদেরকে তালাক দিতেই হবে। হযরত রুকাইয়া নিজ ঘরে চরম অস্থিরতার মধ্যে সময় কাটাচ্ছিলেন। উতবা বাপের ইংগিতে তাকে তালাক দিল। পরে হযরত উসমানের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। আবু লাহাবকে উত্তেজিত করতে ও তার ছেলে দুটিকে দিয়ে এই ঘৃণ্য কাজ করাতে কোরায়েশদের অন্যান্য সরদারও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। তারা পরস্পরে আলোচনা করতো যে, আজকাল মুহাম্মাদকে সা. উত্যক্ত করার তৎপরতা অনেকটা কমে গেছে। তাই নতুন একটা কিছু উদ্ভাবন করা দরকার। তারা স্থির করলো তার মেয়েদেরকে তাদের স্বামীদের কাছ থেকে তালাক দেয়াতে হবে। এতে অন্তত মুহাম্মাদের সা. জন্য কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করা যাবে। তারা আবু লাহাবের ছেলে উতবাকে বললো, কোরায়েশের যে মেয়েকেই চাও, যোগার করে দেয়া হবে। শর্ত শুধু এই যে, মুহাম্মাদের সা. মেয়েকে বিদায় করে দেবে। উতবা কাল বিলম্ব না করে তালাক দিয়ে দিল। উতায়বা আরো খানিকটা তেজ দেখালো। যে হযরত উম্মে কুলসুমকে তালাক দিয়ে গুন্ডা পান্ডার মত রসূল সা. এর কাছে উপস্থিত হলো। তারপর চরম ধৃষ্টতার সাথে বললো, “আমি তোর ধর্মকেও অস্বীকার করেছি, তোর মেয়েকেও তালাক দিয়েছি, তুইও আমাকে ভালোবাসিসনে, তোকেও আমি পসন্দ করিনে।” অতঃপর চরম বেআদবীর সাথে হাত বাড়িয়ে রসূল সা. এর জামার একাংশ টেনে ছিড়ে ফেললো। যুবক জামাতা হিংসুটে বাপের কথা মত একদিকে নিরীহ ও ভদ্র মেয়েকে তালাক তো দিলই, তদুপরি এমন গুন্ডার মত আচরণ করলো যে, দুঃখের চোটে স্বতস্ফূর্তভাবে রসূল সা. এর মুখ দিয়ে এই বদদোয়া বেরিয়ে গেল যে, “হে আল্লাহ, তোমার হিংস্র জন্তুগুলোর মধ্য থেকে কোন একটা জন্তুকে তার ওপর লেলিয়ে দাও।” আবু তালেব যখন ঘটনা শুনলেন, বললেন, “এখন আর আমার ভাতিজার এই বদদোয়া থেকে তোমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।” এরপর উতাইবা এক বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে যখন সিরিয়ায় রাত্র যাপন করছিল, তখন রাতের অন্ধকারে কোথা থেকে এক বাঘ এসে সমগ্র কাফেলার মধ্য থেকে বাছাই করে ওর মাথাটাই চিবিয়ে খেয়ে গেল। (আল মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ১৯৭)
হযরত রুকাইয়ার মৃত্যুর পর রসূল সা. তাঁর এই দ্বিতীয় মেয়ে উম্মে কুলসুমকেও হযরত উসমানের সাথে বিয়ে দেন। এ জন্য তাকে “যুন্নুরাইন” নামে আখ্যায়িত করা হয়।
কোরায়েশ কুচক্রীরা আবু লাহাবের ছেলে উতবার ওপর যেভাবে চাপ প্রয়োগ করেছিল, রসূল সা. এর তৃতীয় কন্যা যয়নবের স্বামী আবুল আসের ওপরও চাপ প্রয়োগ করেছিল এবং তাকেও এই বলে প্রলুব্ধ করেছিল যে, তুমি যদি মুহাম্মাদের সা. মেয়েকে তালাক দাও, তবে যত সুন্দরী মেয়ে চাও, তোমাকে দেয়া হবে। আবুল আসের মধ্যে মহত্বের উজ্জ্বল নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। সে বললো, “ছি ছি! এটা কখনো হতে পারেনা যে, আমি নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করব। যয়নবের পরিবর্তে আর কোন নারী আমার ঘরে আসুক - এটা আমার পছন্দ নয়। পরবর্তী সময় রসূল সা. আবুল আসের চরিত্রের এই দৃঢ়তার প্রশংসা করতেন। তার এই ভদ্র আচরণের প্রতিদান স্বরূপ তিনি দুটো ঘটনায় তার ওপর বিরাট অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। প্রথমত যখন আবুল আস বদরের যুদ্ধবন্দীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এল এ সময় মুক্তিপণ হিসাবে হযরত যয়নব কর্তৃক প্রেরিত হারটি রসূল সা. ফেরত দেন এবং তাকে বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দেন। দ্বিতীয়বার যখন তার বাণিজ্যিক পণ্য যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসাবে মুসলমানদের মধ্যে বন্টিত হয়ে গিয়েছিল, তখন রসূল সা. এর ইংগিতে যাবতীয় জিনিস অক্ষতভাবে তাকে ফেরত দেয়া হয়। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ২৯৬)
বদর যুদ্ধের পর যখন রসূল সা. আবুল আ’সতে বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ বিনা মুক্তিপণে মুক্তি দেন, তখন কথা প্রসংগে তার কাছ থেকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেন যে, সে হযরত যয়নবকে মদিনা আসবার সুযোগ দেবে। এই প্রতিশ্রুতি সাধারণ মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। হযরত যয়নবের মদিনায় রওনা হবার নির্ধারিত সময় দু’জন সাহাবী হযরত যায়েদ বিন হারিসাকে এবং অপর একজন আনসারীকে পাঠানো হয়। এই দু’জনকে রসূল সা. নির্দেশ দিয়ে দেন যে, তোমরা ইয়াজিজ (মক্কা থেকে ৮ মাইল দূরবর্তী একটি জায়গার নাম) নামক স্থানে দাঁড়াবে। যয়নব ওখানে এলে তাকে নিয়ে চলে আসবে। ওদিকে আবুল আস যয়নবকে প্রস্তুত করলো এবং আসবাবপত্র গুছিয়ে দিল। তার দেবর কিনানা বিন রবী খুব ভোরে উটের পিঠে চড়িয়ে দিয়ে যখন যাত্রা করলো, তখন কোরায়েশরা ব্যাপারটা জেনে ফেললো। ঐ নরপশুরা ভাবলো, মুহাম্মাদের সা. মেয়ে এভাবে নিরাপদে আমাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যাবে, এটাতো কলংকজনক ব্যাপার হবে। কিছু লোক পেছনে গেল এবং যী তুয়াতে গিয়ে ধরলো। জনৈক হাব্বার বিন আসওয়াদ যয়নবের হাওদা লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। হযরত যয়নব তখন গর্ভবতী ছিলেন। তীর বিদ্ধ হয়ে তিনি মারাত্মক অবস্থার শিকার হলেন এবং গর্ভপাত ঘটে গেল। পরক্ষণে তার দেবর যখন তীর ধনুক নিয়ে হাঁক ছাড়লো, অমনি মক্কার সেই কাপুরুষ গুন্ডাটা দ্রুত পালিয়ে গেল।
কিছুক্ষণের মধ্যেই আবু সুফিয়ানও এসে হাজির। সে দূর থেকে আক্রমণকারীদেরকে ডেকে বললো, “আমার কথা শোন।” সে কিনানা বিন রবীকে বললো, “তুমি এমন কাজ করতে গেলে কেন যে, প্রকাশ্যে এই মহিলাকে নিয়ে সফরে বেরুলে? অথচ কেমন শত্রুতার পরিবেশ বিরাজ করছে, তাতো জানই। মুহাম্মাদ সা. এর কারণে আমাদের মাথার ওপর এই অবাঞ্ছিত পরিবেশ বিরাজ করছে। এভাবে দুপুরে এ ধরনের পদক্ষেপে মক্কার মানুষ অপমান বোধ করে। আমার জীবনের কসম, মুহাম্মাদের মেয়ের যাত্রা থামানোর কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। এখন ওকে ফেরত নিয়ে চল। কোন এক সময় গোপনে নিয়ে যেও।”
এ থেকে বুঝা যায়, মক্কাবাসী রসূল সা. কে কষ্ট দেয়া ও উত্যক্ত করার জন্য কী জঘন্যতম ইতরামির আশ্রয় নিচ্ছিল। তাদের অন্তরে আত্মীয়তার কোন গুরুত্ব ছিলনা। একজন নারীর ওপর অত্যাচার চালাতে তাদের একটুও লজ্জা বোধ হতোনা। যুলুমকে যুলুম মনে করার মত বোধশক্তিও তাদের ছিলনা। তাদের দৃষ্টিতে মানবতার কোন মূল্য ও অধিকার অবশিষ্ট ছিলনা। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খন্ড, আসাহহুস্ সিয়ার)
এবার অন্য একটা ঘটনা শুনুন। এ ঘটনা ইসলামের শত্রুদের চরম রক্ত পিপাসু মানসিকতা ব্যক্ত করে। রসূল সা. মদিনার সন্নিহিত এলাকাগুলোতে ইসলামে শিক্ষা বিস্তার কল্পে শিক্ষক দল পাঠানোর যে প্রক্রিয়া চালু করেন, তার আওতায় ওহুদ যুদ্ধের অব্যবহিত পর (সফর মাসে) আজল ও কারাহ (বনু হুযায়েল) গোত্রের অনুরোধে ছয়জনের একটি দল পাঠান। এই অনুরোধের পেছনে ছিল ভয়ংকর ষড়যন্ত্র। রসূল সা. যে ছ’জনকে পাঠালেন তাদের চারজনকে রজী নামক স্থানে পৌঁছুলে শহীদ করে দেয়া হলো। বাকী দু’জন হযরত খুবাইব ও যায়েদ বিন দাসনাকে বন্দী করে মক্কায় পাঠানো হলো। (রজী’র ঘটনার অপরাপর বিবরণ এবং অন্যান্য শিক্ষক দলের বিবরণও পরে আসছে) কোরায়েশদের কাছে বনু হুযায়েলের দু’জন কয়েদী ছিল। এই দু’জনকে দিয়ে বিনিময়ে সেই দু’জনকে মুক্ত করা হলো। হুযায়ের বিন ইহাব তামিমী হযরত খুবাইবকে উতবা বিন হারেস বিন আমেরের জন্য নিল, যাতে সে হারেসের প্রতিশোধ নিতে পারে। এই হারেসকে বদর যুদ্ধে হযরত খুবাইব হত্যা করেছিলেন। আর যায়েদ বিন দাসনাকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া খরিদ করলো তার পিতা উমাইয়া বিন খালফের প্রতিশোধ নেয়ার জন্য।
বীরত্ব ও পৌরুষের সদম্ভ আস্ফালনকারীরা যুদ্ধের ময়দানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক সহায় সম্বলহীন মুসলমানদের হাতে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার পর এখন এই দুই অসহায় বন্দীকে হত্যা করে নিজেদের জিঘাংসা চরিতার্থ করতে চাইছিল। ইসলামী সমাজের এই দুই মূল্যবান ব্যক্তিত্বকে যদিও শহীদ করে দেয়া হলো, কিন্তু এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের চরিত্রের যে তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন হলো, তার প্রভাব ইতিহাসের শীরায় শীরায় ছড়িয়ে পড়লো।
সাফওয়ান যায়েদ বিন দাসনাকে স্বীয় গোলাম ফুসতাসের হাতে সোপর্দ করে আদেশ দিল যে, তাকে হারাম শরীফের বাইরে তানয়ীমে নিয়ে গিয়ে হত্যা কর। এই মজাদার নাটক দেখে আনন্দ উপভোগ করার জন্য ঘটনাস্থলে কোরায়েশদের এক জনসমাবেশ করা হয়েছিল। এদের মধ্যে স্বয়ং আবু সুফিয়ানও ছিল। আবু সুফিয়ান কাছে গিয়ে যায়েদকে জিজ্ঞেস করলো, ‘তোমাকে যদি এখন ছেড়ে দেয়া হয় এবং তুমি গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের সাথে হাসিখুশী মনে বসবাস করতে থাক, আর তোমার বদলায় যদি আমরা মুহাম্মাদকে সা. খতম করে দেই, তাহলে এটা তোমার কাছে কেমন লাগবে? যায়েদের সামনে তখন মৃত্যু মুচকি হাসছে তবু ঈমানের অভাবনীয় উচ্চস্তর থেকে তিনি জবাব দিলেনঃ
“আল্লাহর কসম, আমরা এতটুকুও পছন্দ করিনা যে, মুহাম্মাদ সা. যেখানে আছেন, ওখানেও তার গায়ে একটা কাঁটা বিধুঁক, আর তার বিনিময়ে আমরা মুক্ত হয়ে পরিবার পরিজনের কাছে গিয়ে থাকার সুযোগ লাভ করি।”
এ জবাব শুনেতো আবু সুফিয়ান হতবাক। সে বললো, মুহাম্মাদ সা. কে তার সহচররা যেভাবে ভালোবাসে, অমন ভালোবাসা আমি আর কোথাও দেখিনি। তারপর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার এই মূর্ত প্রতীককে তরবারীর গ্রাসে পরিণত করা হলো। যায়েদ শহীদ হলেও তার এই চরিত্র কতজনের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং কতজনের অন্তরাত্মা কোরায়েশদের এই অত্যাচার ও পাশবিক হিংস্রতার বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করেছে কে তার ইয়ত্তা রাখে। (সীরাতে ইবনে হিশাম, আসাহহুস্ সিয়ার)
হযরত খুবাইব এর পরও কিছুদিন বন্দী থাকেন। বন্দী অবস্থায় তিনি নিজের ঈমান ও আখলাকের যে উদাহরণ পেশ করেন, তার একটা ফল দাঁড়ালো এই যে, হুজাইর বিন ইহাবের দাসী মাবিয়া পরবর্তীকালে ইসলামী সমাজের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কাছে থেকেই খুবাইবের বন্দী দশার বিবরণ জানা গেছে। মাবিয়া বর্ণনা করেছে যে, খুবাইবের হত্যার সময় যখন ঘনিয়ে আসলো তখন একদিন তিনি খেউরি হওয়ার জন্য ক্ষুর চাইলেন। ক্ষুর দেয়া হলো। কিন্তু এরপর একটা দৃশ্য দেখে আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগলো। দেখলাম, খুবাইবের হাতে ক্ষূর আর তার কোলে আমার শিশু সন্তান বসে আছে। যে বন্দীকে এমন অন্যায়ভাবে হত্যা করার প্রস্তুতি চলছে তার নাগালে যদি তার শত্রু পক্ষের কোন শিশু এসে যায় এবং তার হাতে উপযুক্ত অস্ত্রও থাকে, তাহলে কি আশংকা দেখা দিতে পারে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। খুবাইব আমার আশংকা বুঝতে পেরে আশ্বাস দিলেন যে, আমি কোন অবস্থাতেই এই নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করবোনা। তারপর ঐ শিশুটাকে কোল থেকে সরিয়ে দিলেন। এমন মহৎ চরিত্র কি মক্কার তমসাচ্ছন্ন পরিবেশে মশাল হয়ে জ্বলে ওঠেনি?
এরপর তাকে শূলে চড়াতে নিয়ে যাওয়া হলো তানয়ীমে। সেখানে গিয়ে তিনি অনুমতি নিয়ে জীবনের শেষ নফল নামায পরম একাগ্রতার সাথে পড়লেন। এভাবে তিনি শাহাদাতের বধ্যভূমিতে গমনকারীদের জন্য একটা চমৎকার ও মহিমান্বিত দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, যা আজও পর্যন্ত অনুসৃত হয়ে আসছে।
এরপর দ্রুত নামায শেষ করে বললেন, তোমরা ভেবনা যে, আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি। তারপর এভাবে দোয়া করলেনঃ
“হে আল্লাহ! আমরা তোমার রসূলের বার্তা পৌঁছে দিয়েছি। তুমিও রসূল সা. কে জানিয়ে দিও যে আমাদের ওপর কি রকম যুলুম করা হচ্ছে। হে আল্লাহ! এই শত্রুদের সংখ্যা কমিয়ে দাও, তাদেরকে কলহ কোন্দলের কবলে ফেলে ধ্বংস কর এবং এমন হিংস্র নরপশুদের কাউকে জীবিত ছেড়ে দিওনা।”
খুবাইবকে শূলে চড়ানো হলো। সবার শেষে আবু মুগীরা বর্শা মেরে তাঁর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁর মুখ দিয়ে কয়েকটা কবিতা উচ্চারিত হয়। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ চরণটি এইঃ
(আরবী********)
“আমাকে যখন মুসলিম হবার কারণে হত্যা করা হচ্ছে তখন মৃত্যুকালে আমি যে যাতনাই ভোগ করি, তাতে আমার কিছুই যায় আসে যায়না।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড)
এই দু’জনকে হত্যা করে কোরায়েশরা হয়তো ভেবেছিল, তারা ইসলামের শক্তিকে অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তারা কল্পনাও করতে পারেনি এই মজলুমদের শাহাদাতের রক্তের প্রতিটি ফোঁটা ঈমানের ফসলকে কত বেশী পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সব জঘন্য প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি কোরায়েশদের সেই রাজনৈতিক বিশ্বাস ঘাতকতাও আমরা তুলে ধরছি, যা তারা হুদাইবিয়ার সন্ধি ভংগের মাধ্যমে করেছিল। এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্থির করা হয়েছিল যে, আরব গোত্রগুলোর মধ্যে যেটি কোরায়েশদের মিত্র হতে চাইবে, হতে পারবে এবং যেটি মুসলমানদের মিত্র হতে চাইবে হতে পারবে। গোত্রগুলো এ ব্যাপারে পুরোপুরি স্বাধীন থাকবে। কারো ওপর কেউ কোন বল প্রয়োগ করতে পারবেনা। এই বিধান অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে বনুবকর কোরায়েশদের সাথে এবং বনু খুযায়া মুসলমানদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করলো।
প্রাগৈসলামিক যুগ থেকে ঐ দুটো গোত্রের মধ্যে একটা হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে প্রতিশোধের পর প্রতিশোধের এক অশুভ চক্র চলে আসছিল। ইতিমধ্যে উভয় গোত্রের মধ্যে একাধিক হত্যার ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। সর্বশেষ প্রতিশোধ গ্রহণের পালা ছিল বনু বকরের এবং তারা এর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এই সময় ইসলামী আন্দোলন ইতিহাসের প্রচন্ডতম ঘাত-প্রতিঘাতের সৃষ্টি করে সকল গোত্রের মনোযোগ নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। ফলে ঐ সব গোত্র নিজেদের পারস্পরিক দ্বন্দ কলহ আপাতত স্থগিত রেখে এই নয়া দাওয়াতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ায়। ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা ও বিদ্বেষ তাদের মধ্যে যে বাহ্যিক ঐক্যের জন্ম দিয়েছিল, হুদাইবিয়া সন্ধির পর সেই ঐক্যের তেজ স্তিমিত হতে থাকে। পুরানো বিরোধগুলো তাদের মনে পড়তে থাকে। বনু বকরের একটা শাখা ছিল বনু ওয়েল। এই বনু ওয়েলের এক ব্যক্তি আসওয়াদ বিন রজনের কয়েকটি ছেলে বনু খুযায়া গোত্রের হাতে নিহত হয়েছিল। সেই হত্যাকান্ডের বদলা নেয়ার জন্য বনুওয়েলের সরদার নওফেল বিন মুয়াবিয়া সমগ্র গোত্রকে সংঘবদ্ধ করে। হুদাইবিয়ার সন্ধির ফলে যে যুদ্ধ বিরতি চলছিল, সেই সুযোগে তারা বনু খুযায়ার ওপর হামলা চালিয়ে বসলো। এই হামলায় সর্বপ্রথম নিহত হলো আল-ওয়াতীর নামক জলাশয়ের কাছে অবস্থানরত এক নিরপরাধ খুযায়ী। খুযায়া গোত্রের অন্যান্যরা এই অপ্রত্যাশিত চুক্তি লংঘন দেখে দিশেহারা হয়ে ছুটে পালাতে লাগলো। আক্রমণকারীরা তাদেরকেও ধাওয়া করে হত্যা করল।
কোরায়েশরা হুদাইবিয়ার সন্ধির দায়দায়িত্বকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বনু বকরকে অস্ত্র সরবরাহ করলো, আবার রাতের আঁধারে লুকিয়ে লুকিয়ে খুযায়ীদের সাথে সন্ধিও চালাতে লাগলো। বনু খুযায়া হারাম শরীফে (কা’বার চত্তরে) আশ্রয় নিয়ে বনু বকরের সরদারকে ডেকে বললো, “ওহে নওফেল! দেখ, এখন আমরা হারাম শরীফে প্রবেশ করেছি। আল্লাহর দোহাই এখন আক্রমণ থামাও।” কিন্তু তারা জয়ের নেশায় অন্ধ হয়ে পড়েছিল। নওফেল বললো, “আজ কোন আল্লাহ নেই। ওহে বনু বকর! পুরোপুরি প্রতিশোধ নিয়ে নাও। হারাম শরীফের সম্মানের খাতিরে তোমরা কি নিজেদের অবমাননার প্রতিশোধ নিতে ভুলে যাবে?” অবশেষে বনু বকর হারাম শরীফে ঢুকেও রক্তপাত করলো। কিছু সংখ্যক খুযায়ী অতি কষ্টে প্রাণ নিয়ে বুদাইল বিন ওয়াবরা ও তার গোলাম রাফের বাড়ীতে গিয়ে লুকালো।
কোরায়েশরা গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে উদ্ভুত প্রচন্ড উত্তেজনার বশে এ কাজটা করেছিল। কিন্তু এটা তাদের এত বড় নির্বুদ্ধিতা ছিল যে, এর কুফল তারা হাতে হাতেই পেয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনাটা মক্কা বিজয়ের কারণ ঘটায়। কোরায়েশরা এ কথা মোটেই ভেবে দেখেনি যে, ইসলামী আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবিলায় তাদের শক্তি নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক দিয়েই চরম অধোপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। তাই তাদের অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পা বাড়ানো উচিত ছিল। এ ঘটনার কারণে আরবের গোত্র শাসিত সমাজে কোরায়েশদের প্রতিশ্রুতি লংঘনের বিষয়টা ব্যাপক নিন্দা না কুড়িয়ে পারেনি। তাদের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। তাছাড়া কোরায়েশদের আস্কারা পেয়ে বনু বকর যে চরম নির্যাতনমূলক কর্মকান্ড চালায় এবং বনু খুযায়া যে লোমহর্ষক অত্যাচার ভোগ করে, তা আরবের সব ক’টা গোত্রকে সচকিত করে দেয় যে, কোরায়েশ নেতৃত্ব শান্তি ও সুবিচারের নিশ্চয়তা দিতে অক্ষম। তাছাড়া এ ঘটনায় শত শত বছরের ঐতিহ্যের মুখে কালিমা লেপন করে আল্লাহর নামের মাহাত্ম্য ও হারাম শরীফের পবিত্রতাকে যেরূপ ন্যাক্কারজনকভাবে পদদলিত করা হয়, তাতে জনমনে ব্যাপক অস্থিরতা ও অস্বস্তি জন্মে। এই দাংগা হাঙ্গামায় কোরায়েশ জুলুমবাজ পক্ষকে আস্কারা দিয়ে নিজের মান মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করে। কোরায়েশ হয়তো ভেবেছিল, ইসলামী রাষ্ট্রের মিত্র বনু খুয়াযাকে ধ্বংস করতে পারলে মুহাম্মাদ সা. এর বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিশোধ স্পৃহা কিছুটা হলেও চরিতার্থ করা যাবে। কিন্তু তারা এ কথা ভেবে দেখেনি যে, এত করে তারা জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক গোত্রগুলোর ঐক্য নিজ হাতেই বিনষ্ট করতে চলেছে। এমনকি কোন কোন প্রতিবেশী গোত্রকে মদিনার আশ্রয়ে পাঠাতে চলেছে।
আসলে প্রত্যেক মান্ধাতা আমলের সমাজ ব্যবস্থা এবং প্রত্যেক পুরোনো নেতৃত্ব, যাদের না আছে কোন উচ্চতর আদর্শ ও লক্ষ্য, না আছে নৈতিক মূল্যবোধ ও গঠনমূলক সংস্কৃতি, এবং যাদের একমাত্র সম্বল হলো প্রত্যেক গঠনমূলক ও সংস্কারকামী শক্তিকে দমন করা ও ধ্বংস করার নেতিবাচক লক্ষ্য, তাদের ভাগ্যলিপি সাধারণত এটাই হয়ে থাকে যে, তাদের বুদ্ধিই তাদেরকে নির্বুদ্ধিতার পথে নিয়ে যায়, তাদের শক্তিই তাদেরকে দুর্বলতার গভীর খাদে নিক্ষেপ করে, তাদের আভিজাত্যবোধই তাদেরকে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকারে পরিণত করে এবং তাদের অগ্রগতিই তাদের পশ্চাদপদতাকে ও তাদের উন্নতিই অধোপতনকে অনিবার্য করে তোলে।
বনু খুযায়া গোত্রের আমর বিন সালেম মদিনায় রওনা হয়ে গেল এবং রসূল সা. এর কাছে পৌঁছে বনু বকর ও কোরায়েশদের যুলুম নির্যাতনের মর্মান্তিক কাহিনী শোনালো। রসূল সা. মসজিদে বৈঠকে বসেছিলেন। সেখানে আমর বিন সালেম চিরাচরিত আরবীয় রীতি অনুযায়ী নিজের করুণ কাহিনীকে একটা মর্মবিদারী কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করলোঃ
(আরবী********)
“হে আল্লাহ! আমি মুহাম্মাদকে সেই চুক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেব, যা আমাদের ও তাঁর প্রাচীন পরিবারগুলোর মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। হে নবী, আমাদেরকে সাহায্য করুন এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্যের জন্য সমবেত হবার আহবান জানান। ফেনা রাশি তোলা সমুদ্রের ঢেউ এর ন্যায় বিশাল বাহিনী নিয়ে ময়দানে নামুন। কেননা কোরায়েশ আপনার চুক্তি ভংগ করেছে। তারা রাতের অন্ধকারে ওয়াতীরের কাছে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা যখন ঘুমন্ত ছিলাম, তখন তারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। আমরা যখন রুকু সেজদার অবস্থায় ছিলাম, তখন আমাদের ওপর আঘাত হেনেছে।”
জবাব দেয়া হলোঃ “হে আমর বিন সালেম, তোমাকে সাহায্য করা হবে।”
এবার কোরায়েশরা বুঝতে পারলো, তারা কী ধ্বংসাত্মক কাজ করে ফেলেছে। আবু সুফিয়ান চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে মদিনায় ছুটে গেল। কিন্তু সেখানকার পরিবেশ ছিল এ রকম যে, আবু সুফিয়ান নিজের মেয়ের ঘরে গিয়ে যখন বিছানার ওপর বসতে উদ্যত হলো, তখন মেয়ে বিছানা গুটিয়ে ফেললো এবং বললো, এটা আল্লাহর রসূলের বিছানা। আপনি একজন অপবিত্র মোশরেক হয়ে ওটার ওপর বসতে পারবেন না।” আবু সুফিয়ান ব্যর্থ হয়ে ফিরলো এবং কয়েকদিন পরই দেখলো, এক বিশাল বাহিনী মক্কায় উপস্থিত। (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খন্ড, আসাহহুস সিয়ার, সীরাতুন্নবী শিবলী নোমানী, প্রথম খন্ড)
এই ঘটনাবলী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জাহেলী নেতৃত্বের নেতিবাচক শক্তিকে তার নিজের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ষড়যন্ত্র, প্রতিটি প্রতিশোধমূলক তৎপরতা এবং প্রতিটি প্রতিশোধমূলক কর্মকান্ড ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর করেছে। অপর দিকে ইতিবাচক ও গঠনমূলক শক্তি ইসলামী আন্দোলন ক্রমেই শক্তি অর্জন ও সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে।
পক্ষান্তরে রসূল সা. এর আচরণ দেখুন, উভয়পক্ষে যুদ্ধ চলছে। এ সময় ইয়ামামার শাসনকর্তা ইসলাম গ্রহণ করে স্থায়ীভাবে মক্কা অভিমুখে খাদ্যশস্য সরবরাহ বন্ধ করে দেন। ঠিক এই সময় মক্কায় চলছিল দুর্ভিক্ষ। মানবতার ত্রাণকর্তা মুহাম্মাদ সা. দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের কথা ভেবে নিজেই অনুরোধ করে ইয়ামামা থেকে খাদ্য শস্য সরবরাহ পুনঃ চালু করালেন এবং নিজের কাছ থেকে মক্কার দরিদ্র লোকদের জন্য পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। এই মহানুভবতা মক্কার জনগণকে বিপুলভাবে অভিভূত করে। এক বর্ণনায় জানা যায়, মক্কাবাসী স্বয়ং রসূল সা. কে লিখেছে যে, “আপনি তো আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করার নির্দেশ দেন, কিন্তু আপনি আমাদের সাথে এই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছেন।” কেউ কেউ এও লিখেছে যে, “তুমি পিতাদেরকে তরবারী দিয়ে এবং সন্তানদেরকে ক্ষুধা দিয়ে হত্যা করছ।” (সীরাতে ইবনে হিশাম, ৪র্থ খন্ড, আসাহহুস সিয়ার, রসূলে আকরাম কি সিয়াসী জিন্দেগী, ডঃ হামীদুল্লাহ)
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি