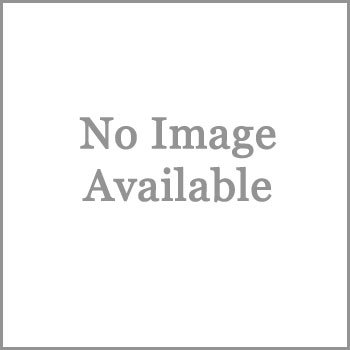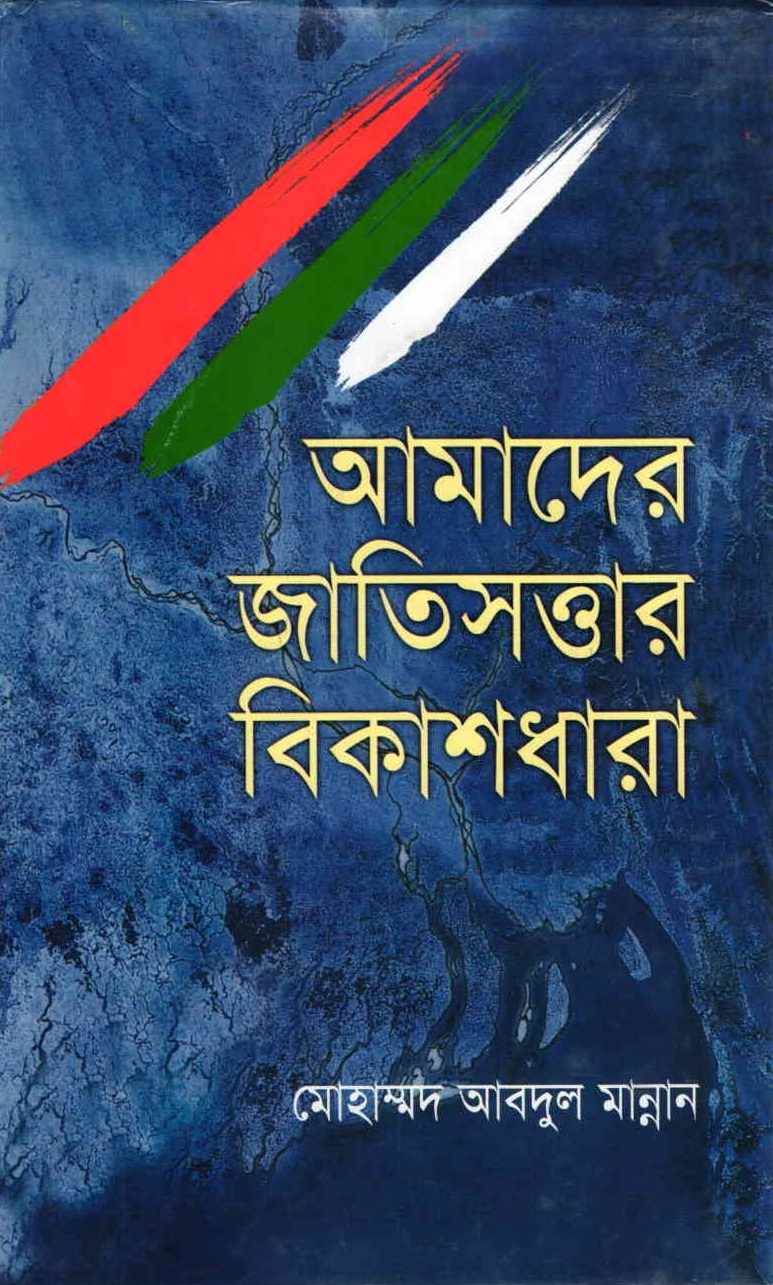৮.
বাংলায় মুসলিম নবজাগরণ
‘ভেতর থেকে সংস্কার’
সিপাহী বিপ্লবোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইঙ্গ-হিন্দু দ্বিমুখী সাঁড়াশী হামলার শিকার মুসলমানদের আপহীন মুক্তিসংগ্রামের জিহাদী কাফেলা বহু আত্মদান সত্ত্বেও ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। এই নতুন প্রেক্ষাপটে ধ্বংসোন্মুখ মুসলমানদের রক্ষার জন্য নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হয়। ১৮৬৩ সালের ২ এপ্রিল ফরিদপুরের নওয়াব আবদুল লতিফ কলকাতায় ‘মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি’ গঠন করেন। ১৮৬৪ সালে সৈয়দ আহমদ খানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘গাজীপুর ট্রান্সলেশন সোসাইটি’। এটি পরে ‘আলীগড় সায়েন্টিফিক সোসাইটি’ নাম ধারণ করে। ১৮৭৭ সালে সৈয়দ আমীর আলী কায়েম করেন ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন’।
জিহাদ আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা কারামত আলী জৌনপুরীও এ সময় ধ্বংসোন্মুখ মুসলমানদের আপসহীন সশস্ত্র লড়াই থেকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে তাদের মধ্যে ‘ভেতর থেকে সংস্কার’ তথা অন্তর্বিপ্লবের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ১৮৬৭ সালে তিনি জিহাদ আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। ১৮৭০ সালে নওয়াব আবদুল লতিফের ‘মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি’র এক সভামঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইংরেজ কবলিত ভারত ‘দারুল হরব’ নয়।
তাঁর এই ফতওয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মাঝে বাহাস-বিতর্ক জিইয়ে রাখলেও জনযুদ্ধের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ মোড় পরিবর্তনের সূচনা হয়। এ সময় বাংলার সনাতনপন্হি এবং জিহাদী ও ফরায়েজীদের মধ্যে বৃহত্তর সমঝোতার ক্ষেত্র রচনায় জামালউদ্দীন আফগানীর (১৮৩৮-৯৭) ‘প্যান ইসলামাবাদ’ বিশেষ অবদান রাখে।
নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আহমদ খান ও সৈয়দ আমীর আলী ইংরেজদের সাথে নমনীয় নীতি অবলম্বনের মাধ্যমে অধঃপতিত মুসলমানদের অধিকার ও ন্যায্যা হিস্যা আদায়ের নীতিগ্রহণ করেন। হিন্দু জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রবল জোয়ারের বিপরীত ধারায় দাঁড়িয়ে এই তিন কান্ডারীর নেতৃত্বেই এ সময় বিপর্যস্ত মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায় এবং সাংস্কৃতিক অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য সুরক্ষার আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। মুসলমানদের স্বকীয় সত্তা, তাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের স্বতন্ত্র প্রেরণাকে উপজীব্য করে মুসলিম জাগরণের লক্ষ্যে শিক্ষিত ও তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন মুসলিম পরিবারগুলো আলেম সমাজের আন্দোলনমুখী কার্যক্রমের সাথে যোগদান করেন। তাঁরা নতুনভাবে সংগঠিত এই আন্দোলনের মধ্যে মুসলিম জনগণকে রাজনৈতিকভাবে উদ্বদ্ধ, জাগ্রত ও সংগঠিত করার এবং হিন্দু এলিটদের বিরুদ্দে সংগ্রাম পরিচালনার এক সম্ভাবনাময় শক্তির সন্ধান পান। ঢাকা, কলকাতা, হুগলীও চট্টগ্রামের সদ্র প্রতিষ্ঠিত উচ্চতর মাদরাসা থেকে বেরিয়ে আসা গ্র্যাজুয়েটগণ এবং দেওবন্দী আলেমগণ বাংলার মুসলিম গণজাগরণে এ সময় মুখ্য ভূমিকায় এগিয়ে আসতে থাকেন।
এ সময় মুসলমানদের বহু নতুন মাদরাসা গড়ে ওঠে এবং আলেমগণ ধর্মীয় পুস্তক রচনা ও মাহফিলে বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্বদ্দ করতে থাকেন। নসিহতনামা জাতীয় বই-পুস্তক ছাড়াও প্রকাশিত হতে থাকে জাতীয় জাগরণমূলক বইপত্র। খ্রিস্টান মিশনারীদের ব্যাপকক তৎপরতা মোকাবিলার জন্য ‘ইসলাম মিশন ফান্ড’ গঠন করা হয়। এ সময় বিশেষত ফুরফুরার পীর সাহেবের অনুপ্রেরণায় মুসলমানদের কয়েকটি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা উল্লেখোগ্য ভূমিকা পালনকারী যশোরের মুনশী মেহেরউল্লাহ (১৮৬১-১৯০৭) বইপত্র রচনা, সংগঠন কায়েম, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং বিশেষভাবে এদেশে শান্তিপুর্ণ ধর্মীয় সমাবেশরূপে ওয়াজ মাহফিলকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তোলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে এসে প্রচারক ও রাজনীতিকদের কাছে এই মাহফিল সম্মেলনের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ চমৎকার জনসংযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পশ্চাতপদ জনগণের কাছে আন্দোলনের বাণী দ্রুত পৌঁছিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়। জনগণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া সৃষ্টি হওয়ার ফলে বিভিন্ন আঞ্জুমান ও মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং মসজিদগুলোতে মুসল্লিদের সংখ্যা বেড়তে থাকে। এভাবে মুসলিম সমাজ সমস্বার্ত ও অভিন্ন আদর্শের পথ ধরে আত্ম পরিচয়ে উদ্বদ্ধু হতে থাকে এবং তাদের মধ্যে ক্রমশ জাতিগত ঐক্য-চেতনা দানা বেঁধে ওঠে। ড. রফিউদ্দীন আহমদের ভাষায়ঃ
“By 1905 the building blocks which eventually went into the making of Pakistan were already there.” (The Bengal Muslims, 1871-1906)
মুসলিম সাংবাদিকতা ও স্বাতন্ত্র্য চেতনা
আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেনঃ
“বাঙালি মুসলমান কর্তৃক সংবাদপত্র প্রকাশের সত্যিকার চেষ্টা হয় সম্ভবত ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে। তখন কয়েকজন উদ্যমশীল মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় যাঁদের সমাজ হিতৈষণা মুসলিম বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই সমাজপ্রাণ ও সাহিত্যিকগোষ্ঠী হচ্ছেন মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রিয়াজউদ্দীন মাশহাদী, মৌলভী মেরাজউদ্দীন, মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ আবদুর রহীম এবং শান্তিপুরের কবি মোজাম্মেল হক। বাংলার মুসলমানের দুঃখ-দৈন্য অভাব-অভিযোগ এঁদের প্রাণে একটা তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করছিল। এঁরা বুঝতে পারেন, বাংলার মুসলমানের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-বেদনা ব্যক্ত করার জন্য চাই তার একটা বাংলা সাপ্তাহিক মুখপত্র। এঁদেরই চেষ্টায় ‘সুধাকর’ প্রকাশিত হয়। মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ এই সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক পদে বরিত হন”। (দৃষ্টিকোন, পৃষ্ঠা ১৬৯)
এই উদ্ধৃতি থেকেই তখনকার দিনের মুসলমানদের একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা এবং সাধ্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও আন্দায করা যায়। এর আগে বাংলার মুসলানদের বাংলা-ফারসি দ্বি-ভাষিক প্রথম সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৩১ সালের মার্চ মাসে, স্বল্পকালের জন্য। সময়ের বিস্তর ব্যবধানে ১৮৭৭ সালে প্রকাশিত হয় উর্দু-বাংলা দ্বি-ভাষিক সাময়িকপত্র ‘মোহাম্মদী আখবার’। ১৮৭৪ সালে বাংলা সাময়িকপত্র ‘আজিজন নেহার’, ১৮৮১ সালে ‘নব সুধাকর’, ১৮৮৪ সালে ‘মুসলমান’, ১৮৮৫ সালে ‘মুসলমান বন্ধু’ ও ‘ইসলাম’, ১৮৮৬ সালে ‘আহমদী’, প্রকাশিত হয়। এসবই ছিল অত্যন্ত স্বল্পায়ু পত্রিকা।
১৮৮৯ সালে সাপ্তাহিক ‘সুধাকর’ প্রকাশের পর ১৮৯০ সালে মীর মশারফ হোসেন প্রকাশ করেন পাক্ষিক ‘হিতকারী’। ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয় ‘ইসলাম প্রচারক’, ১৮৯২ সালে ‘মিহির’ ও ‘হাফেজ’। ১৮৯৪ সালে শেখ আবদুর রহীমের ‘মিহির’ এবং শেখ মোহাম্মদ রিয়াজউদ্দীন আহমদ-এর ‘সুধাকর’ যুক্ত হয়ে যৌথ সম্পাদনায় ‘মিহির’ ও সুধাকর’ নামে ১৯১০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। ১৮৯৮ সালে ‘কোহিনূর’, ১৮৯৯ সালে ‘ইসলাম’, ১৯০০ সালে ‘নূর অল ইমান’, ১৯০১ সালে ‘মুসলমান’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এভাবে বাংলা চৌদ্দ শতকের একেবারে সূচনালগ্ন থেকেই বলা চলে বাংলার মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশের সূচনা হয়। এরপর বহু সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকার জন্ম হয়। এ সময় থেকে কুড়ি শতকের ত্রিশের দশকের ভিতর প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার মধ্যে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত ‘সওগত’ এবং ১৯২৭ সালে প্রকাশিত ‘মোহাম্মদী’ স্থায়িত্ব ও ভূমিকার বলিষ্ঠতার বিবেচনায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অধঃপতিত মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়ন তথা বাংলার মুসলমানদের নবজাগরণ ছিল এ সময়কার সকল পত্র-পত্রিকার মূল কথা।
হিন্দু পুনরুজ্জীনবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে প্যান-ইসলামী আদর্শের প্রবক্তা ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকা। সাধারণভাবে মুসলমানদের মাঝে ইতিহাস-ঐতিহ্যের ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি, মুসলিম স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার,ইসলামী আন্তর্জাতিকতা বা উম্মাহ-ধারণার প্রচার, তুর্কী খিলাফতের প্রতি আনুগত্য, ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলিম অবদানের মহিমা প্রচার, ইংরেজ ও বর্ণ-হিন্দুদের প্রচার মাধ্যমে সমাজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করে তার প্রতিকারের উপায় অনুসন্ধান, শিরক-বিদআত-কুসংস্কার দূর করে শরীআতের অনুশাসনের ভিত্তিতে সকল প্রকার আলস্য ও জড়তা কাটিয়ে নতুন হিম্মতে জেগে ওঠার আহবান প্রচার প্রভৃতি বিষয় ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকার প্রধান উপজীব্য। বিজাতীয় সাংস্কৃতির আগ্রাসন প্রতিরোধ এবং নিজস্ব তাহযীব-তমদ্দুনের বিকাশ সাধন ছিল এ সকল পত্র-পত্রিকার একটি সুচিহ্নিত বিশেষ লক্ষ্য। এমনকি পরবর্তীকালের ‘শিখা’‘সাম্যবাদী’, ‘জয়তী’ প্রভৃতি পত্রিকার অন্তরের বাণীও ছিল মুসলিম সংস্কৃতিভিত্তিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা। তাদের বক্তব্যও ছিল ইসলামের সাথে সঙ্গতি-সন্ধানে প্রয়াসী।
তৎকালীন মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র সম্পর্কে ডক্টর আনিসুজ্জামান লিখেছেনঃ
“যে চেতনা ইতিহাস চর্চার মূলে ক্রিয়াশীল ছিল, সমাজ সংস্কার চেষ্টার মূলে প্রেরণাস্বরূপ ছিল, তুরস্কের প্রতি অসামান্য প্রীতির উদ্বোধন করেছিল, সে চেতনা স্বাভাবতই এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবোধের সৃষ্টি করেছিল”। (মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃষ্ঠা ৪০)
মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম দশকগুলোতে সাংবাদিকতার সাথে যারা যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরা মূলত সাহিত্যিক, সমাজ সংস্কারক ও সংস্কৃতিসেবী। অধঃপতিত অনগ্রসর মুসলমানদের অবস্থা লক্ষ্য করে সমাজ সংস্কার এবং মুসলিম জাগরণ ও স্বাধীনতার প্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে তাঁরা এ কঠিন সাধনায় অংশ নিয়েছেন। তাঁদের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। জাতির প্রতি অকৃত্রিম দায়িত্ববোধ তাঁদেরকে আর্থিক অনটনের মধ্যে পত্রিকার একেকটি সংখ্যা প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁরা সকলেই যে যুগান্তকারী সৃজনধর্মী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এমনও নয়। স্ব-সমাজের প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও সহমর্মিতা এবং অধঃপতিত জাতিকে জাগিয়ে তোলার প্রেরণাই সংবাদপত্রের সেবায় নিয়োজিত হতে তাদেরকে উদ্বদ্ধ করেছে। পেশাদারী সাংবাদিকতা কিংবা সংবাদপত্রকে শিল্পরূপে বিকশিত করার ধারণাও তখন সৃষ্টি হয়নি। সকল কিছুর ঊর্ধ্বে তাদের জীবন-মিশন ছিল কর্দমে প্রোথিত মুসলিম জাতির জাগরণ। সেকালের অন্য সকল মুসলিম সাহিত্যিকের প্রবন্ধ রচনার মূলেও কাজ করেছে এই অভিন্ন প্রেরণা।
সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের এই বাধা-সংকুল পথ ধরেই দুই দশক পর ১৯০৯ সালে আবদুল গফুর সিদ্দিকীর সম্পাদনায় মুসলিম বাঙালার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র ‘হাবলুল মতীন’ প্রকাশিত হয়। মুফাফঅর আহমদ, কাজী নজরুল ইসলাম ও ফজলুল হক সেলবার্ষী ১৯১৯ সালে প্রকাশ করেন ‘নবযুগ’। এর পর দৈনিক সেবক, দৈনিক মোহাম্মদী, দৈনিক সুলতান’ দৈনিক তরক্কী’ দৈনিক কৃষক মুসলিম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকার মধ্যে ১৯৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘আজাদ’ ছাড়া সবকটি দৈনিক সংবাদপত্রই ছিল স্বল্পস্থায়ী। আজাদ থেকেই বাংলায় মুসলিম দৈনিকের স্থায়ী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।
আবুল কালাম শামসুদ্দিন লিখেছেনঃ
“মুন্সী মোহাম্মদ রিয়াউদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম নিঃসন্দেহে বাংলার মুসলিম সাংবাদিকতার পাইওনীয়র, কিন্তু সংবাদপত্রকে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত করেছেন এবং তার মারফতে মুসলিম বাংলাকে চিন্তার খোরাক যোগাতে শুরু করেন প্রধানত মাওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মাওলানা আকরাম খাঁ এবং মওলবী মুজীবুর রহমান মুসলিম সাংবাদিকতাকে শুধু যে চিন্তা, আদর্শ-নিষ্ঠা ও নির্ভিকতায় মণ্ডিত করেন, তা নয়, তাঁরা একে বাংলায় শ্রদ্ধেয় করে তোলেন। বাংলার সংবাদপত্র-ক্ষেত্রে কারুর পক্ষেই মুসলমানদেরকে যে আর উপেক্ষা করার উপায় নাই, এদেরই সাধনায় তা বাস্তবে সম্ভব হয়ে উঠল”। (দৃষ্টিকোণ, পৃষ্ঠা ১৭৪)
জাতিগত ঐক্য-চেতনার জন্ম
উনিশ শতকের শেষ ও কুড়ি শতকের প্রথম বছরগুলোতে আলেম সমাজ ও নব্য শিক্ষিত শ্রেণীর মিলিত চেষ্টার মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম জাগরণের আভাস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আলেম সমাজের সাথে নব্য শিক্ষিত মুসলমানগণ ধর্মীয় সংস্কার ও মুসলমানদের সামাজিক জাগরণ প্রচেষ্টায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। এই সময়ের মুসলমানদের জাগরণ প্রয়াসের বৈশিষ্ট্যগুলো হলোঃ
ক. মুসলিম সমাজে পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিরোধ ও বাহাস-বিতণ্ডা প্রশমিত হয় এবং পারস্পরিক নির্ভরতা ও সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়।
খ. গ্রামীণ মুসলমানগণ বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংযোগধারায় মিলিত হতে শুরু করেন।
গ. মুসলমানদের রাজনৈতিক ও দীনী সচেতনতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বহু নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সমাজকল্যাণ সংগঠন ও আঞ্জুমান কায়েম হয়।
ঘ. বিপুলসংখ্যক নসিহতমূলক, ধর্মীয় সংস্কারমূলক, ইতিহাস ও ঐতিহ্যধর্মী, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগৌরবমূলক এবং জাতিসত্তা-উদ্দীপক বই-পত্র রচিত ও প্রকাশিত হয়।
ঙ. মুসলমানদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথা তুলে ধরার জন্য বাংলা ভাষায় এ সময় মুসলিম সম্পাদিত অনেক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
চ. এ সময়ই শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় সম্মেলনরূপে ওয়াজ মাহফিল ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং জনগণকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করতে এসব মাহফিল অবদান রাখে।
তখনকার মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক জীবনে সংঘাত ও বিরোধের বহু উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও উনিশ শতকের শেষ বছরগুলোতে তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের দু’টি ধারা জাতিগত ঐক্যচেতনার ভিত্তিতে অভিন্ন রাজনৈতিক লক্ষ্যে পরিচালিত হতে শুরু করে। ১৯০৫ সালের মধ্যে তা একটি পরিণত পর্যায়ে উপনীত হয়।
৯.
বঙ্গভঙ্গঃ দুই স্বতন্ত্র জাতিসত্তার সংঘাত
১৬৯৮ সালে সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর- এই তিনটি মাত্র গ্রামের জমিদারীর ইজারা নিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাত্র ৭৫ বছরের মধ্যে সেই ইংরেজদের শাসনাধীন বাংলার ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সী এক বিশাল আয়তন লাভ করে। এ সময়ের মধ্যে মধ্য-ভারতের একাংশ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত এবং পুবে চট্টগ্রামের সমুদ্র-সৈকত পর্যন্ত এক বিশাল এলাকা ইংরেজদের অধিকারে আসে। ১৭৭৩ সালে ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের সনদ ২০ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়। এই সময়ই প্রথমবারের মতো চার জন কাউন্সিলরসহ একটি গভর্নর জেনারেলের পদ সৃষ্টি করা হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস ভারত-সাম্রাজ্য বিষয়ক প্রথম গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৭৯৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক সনদ শেষবারের মতো ১৮১৩ সাল পর্যন্ত মেয়া দের জন্য নবায়ন করা হয়। প্রশাসনিক চার্টার নবায়নের এই মুহূর্তে একটি ডেপুটি গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়।
১৮০৩ সাল নাগাদ আধুনিক উত্তর প্রদেশের প্রায় সম্পূর্ণ এলাকা ইংরেজদের দখলে চলে যায়। তখন এ প্রদেশের নাম করা হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ। ১৮১০ সালের মধ্যে দিল্লী ও শিখ-সীমান্ত পর্যন্ত ইংরেজ-দখলের ব্যাপ্তি ঘটে। ১৮১৬ সালে নেপাল ও ছোট নাগপুর এবং ১৮১৭ সালে মধ্য-ভারতের মারাঠা অধিকৃত এলাকা ইংরেজরা গ্রাস করে। বেঙ্গলের অধীনে এই নবগঠিত এলাকা সাগর ও নর্দমা অঞ্চলরূপে চিহ্নিত হয়। ১৮২৪ সালে আসাম, কাছাড়, জয়ন্তিয়া ও মনিপুর এবং বিশাল বর্মী এলাকা ইংরেজরা দখল করে। প্রশাসনিকভাবে এই বিশাল ভূখণ্ডের পুরোটা ছিল বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর অধীন। ১৮৩৩ সালের সনদ অনুযায়ী আগ্রাকে রাজধানী করে একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অধীনে চতুর্থ প্রেসিডেন্সী স্থাপন করা হয়। বাংলা এ সময় মোগল বাদশাহী আমলের সাবেক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা সুবাহসমূহের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৮৩৯-৪০ সাল নাগাদ পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।
ইংরেজ রাজত্ব ফুলে-ফেঁপে ওঠার সাথে সাথে নানা ধরনের প্রশাসনিক জটিলতা ও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার মোকাবিলার জন্য ১৮৫৩ সালে স্থায়ীভাবে একটি লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮৫৪ সালে গভর্নর জেনারেল ডালহৌসির আমলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর-এর অধীন করা হয়। এই দুই প্রশাসনিক প্রধানেরই দফতর ছিল কলকাতায়। ১৮৬২ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কেন্দ্রীয় রাজধানী কলকাতায় একটি মনোনীত ব্যবস্থাপক পরিষদ গঠন করা হয়। এ বছরই কলকাতায় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় ‘বেঙ্গল ফোর্ট উ্ইলিয়াম প্রেসিডেন্সী’র আয়তন ছিল ২ লাখ ৪৬ হাজার ৭৮৬ বর্গমাইল। পুব থেকে পশ্চিমে চিহ্নিত সীমানার দুরত্ব ৮০০ মাইল। (এম কে ইউ মোল্লা: দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম, পৃষ্ঠা ১৫)
ইংরেজ প্রশাসনে তখন এক বেসামাল অবস্থা বিরাজ করছিল। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যার ৬টি জেলায়, বিহারের কিছু এলাকায় ও উত্তরবঙ্গে দুর্ভিক্ষে কয়েক লাখ মানুষ মারা যায়। দুর্ভিক্ষের জন্য দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামোকে দায়ী করা হচ্ছিল। এ সময় থেকেই মাদ্রাজ ও বোম্বের মতো বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী এলাকার জন্য একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্ণর-এর প্রয়োজন অনুভূত হতে থাকে। এ প্রস্তাবের সমর্থকরা ইংল্যান্ডে বক্তব্য উপস্থাপন করেন, ব্রিটিশ্র ভারতে গভর্নর জেনারেল-এর অফিস কলকাতায় থাকা সত্ত্বেও কূটনীতি বিষয়ক কাজের অস্বাভাবিক চাটের দরুন গভর্নর জেনারেলের পক্ষে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসনিক বিষয়ে পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অবিলম্বে ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ গভর্নর নিয়োগ অপরিহার্য।
১৮৬৭-৬৮ সাল থেকে ১৮৭০-৭১ সালের মধ্যে আসামের কিছু ঘটনা ইংরেজ শাসকদের বিব্রত করে তোলে। ১৮৬৭-৬৮ সালে নাগা উপজাতির লোকেরা আসামের শিবসাগর জেলায় কয়েক দফা হামলা চালায়। ১৮৭০-৭১ সালে তারা সিলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম, কাছাড়ড় ও ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় হামলা ও লুটপাট করে। আসামের চা বাগানগুলোতে উপর্যুপরি তাদের হামলা চলতে থাকে। এসব ঘটনার কারণে ১৮৭৪ সালে সিলেট জেলা ও আসামকে যুক্ত করে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে আলাদা প্রদেশ করা হয়। এর প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন চীফ কমিশনারের হাতে ন্যস্ত হয়। এই নতুন প্রদেশের আয়তন ছিল ৪১ হাজার ৭৯৮ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৪১ লাখ। এর ফলে বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সির আওতায় থাকল। আসাম-বিযুক্ত অবিভক্ত বাংলা ছাড়াও বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যা প্রদেশ। এর আয়তন ছিল ২ লাখ ৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭ কোটি ৮০ লাখ। ১৮৯৮ সাল নাগাদ লুসাই হিলস এলাকা বেঙ্গল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের অধীনে দেওয়া হয়। তারপরও ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় বিরাট বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছিল ১,৮৯,০০০ বর্গমাইল।
১৮৯৬ সালের ২৫ নভেম্বর আসামের চীফ কমিশনার উইলিয়াম ওয়ার্ড ভারত সচিবের কাছে একটি চিঠি লেখেন। তাতে তিনি আসামের সাথে ঢাকা, মোমেনশাহী ও চট্টগ্রাম এলাকা সংযুক্ত করার প্রস্তাব করেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হলে আসামের জন্য একটি পৃথক সিভিল সার্ভিস গঠন ছাড়াও প্রস্তাবিত সম্প্রসারিত প্রদেশটি দ্রুত সমৃদ্ধি লাভ করবে। সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশের আয়তন হবে ৮০ হাজার ৯৫০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা থাকবে ১ কোটি ৫৫ লাখ ৮০ হাজার। (এম কে ইউ মোল্লাঃ দি নিউ প্রভিন্স অব ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম)
আসাম প্রদেশের এলাকা সম্প্রসারণের বিষয়ে আরো আগে থেকেই আলোচনা চলছিল বলে মনে হয়। চট্টগ্রামকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা প্রশ্নে কলকাতার ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকায় ১৮৯২ সালের ৯ এপ্রিল এবং ঢাকা গেজেট-এ ১৮ এপ্রিল মন্তব্য করা হয় যে, বেঙ্গল প্রেসিডিন্সীর আর কোন এলাকা পৃথক করার প্রস্তাব সমর্থনযোগ্য নয়। তখনও অন্য কোন এলাকার বিষয় আলোচিত হয়নি। ‘ভারত সভা’র সভাপতি সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৮৯৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারের কাছে একটি প্রতিবাদ-লিপি দেন। সবশেষে আসামের চীফ কমিশনারের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব কলকাতার বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। আসামের ভূমি-ব্যবস্থার কারণেই কলকাতায় বসবাসকারী জমিদারদের কাছে আসাম প্রদেশের সম্প্রসারণ গ্রহণযোগ্য ছিল না।
১৮৯৬ সালের দিকে আসামের চীফ কমিশনারের দায়িত্ব পেলেন স্যার হেনরী জন স্টেড কটন। তিনি ছিলেন কলকাতার বর্ণহিন্দু স্বার্থের কট্টর সমর্থক। বর্ণহিন্দু বিত্তশালী ও মধ্যশ্রেণীর প্রিয় মানুষ কটন ১৯০২ সাল পর্যন্ত এক নাগাড়ে প্রায় ছয় বছর দায়িত্বে থাকাকালে আসাম প্রদেশের সম্প্রসারণের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। এখানে বলে রাখা যেতে পারে, স্যার কটন অবসর নিয়ে কলকাতায় বসবাস করার সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। তখন তিনি জোর গলায় বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করেছেন, হিন্দুদের প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমর্থন করেছেন এবং বঙ্গ বিভাগ রদ হওয়ার পর উচ্ছসিত আনন্দও প্রকাশ করেছেন। ত্রিশ বছরের বেশি সময় এদেশে থাকার পর স্বদেশে ফিরে লন্ডনের উদারনৈতিক দলের টিকিটে এমপি হয়ে কটন বিলাতের পার্লামেন্টে কংগ্রেসের প্রতিটি কাজ নির্বিচারে সমর্থন করেছেন। তাঁর বিবেচনায় কংগ্রেস ছিল একমাত্র সঙ্গত ‘জাতীয়’ প্রতিষ্ঠান আর মুসলিম লীগ একটি ‘সাম্প্রদায়িক’ দল।
ভারতীয় রাজনীতিতে এ সময় ছিল এক ঐতিহাসিক ক্রান্তিকাল। এ যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতের গভর্নর জেনারেলের দায়িত্বে ছিলেন জর্জ ন্যাথানিয়াল কার্জন (১৮৫৯-১৯২৫)। তাঁর সম্পর্কে পারসিভাল স্পিয়ার ‘এ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া’ বইয়ে লিখেছেনঃ
“ভিক্টোরিয়ান সাম্রাজ্যবাদের শেষ পর্যায়েল চিন্তাধারার স্পর্শে উজ্জীবিত রোমান্টিকধর্মী আভিজাত্যমণ্ডিত হয়ে তিনি একজন জুনিয়র সরকারি কর্মচারি থেকে উন্নতির সোপান অতিক্রম করে চল্লিখ বছর বয়সে এই দায়িত্ব লাভ করেন।….. তিনি ভবিষ্যতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় ভারতে তাঁর কার্যক্রমে সাফল্যের ব্যাপারে উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু ওয়েলেসি ও ডালহৌসির মতো ভারত তাঁকেও প্রতারিত করল এবং এখানেই তাঁর কর্মজীবনের প্রায় পরিসমাপ্তি হতে চলেছিল”।
লর্ড কার্জন দুই দফায় মোট পাঁচ বছরকাল ভাইসরয় ছিলেন। প্রথমে ১৮৯৯ থেকে ১৯০৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত। দ্বিতীয়বার ১৯০৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের নভেম্বর পর্যন্ত। কার্জন ভারতীয় ইতিহাসের সবচে বিতর্কিত ভাইসরয় হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছেন। অন্যদিকে কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি (বর্তমান ন্যাশনাল লাইব্রেরি), প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং ইংরেজ স্বার্থে আফগান সমস্যা সমাধানের জন্য ‘ডুরান্ড লইনৱ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান অব্যবস্থা তদন্তের লক্ষ্যে কার্জনের নিদের্শে গঠিত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯০৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন জারি হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে কলকাতার বর্ণীহন্দু বুদ্ধিজীবী মহল বিক্ষুব্ধ হয়। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতেই প্রশাসনিক কাজের সুবিধা ও অনুন্নত এলাকার সমৃদ্ধি সাধনের যুক্তিতে বিশাল আয়তন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে পূর্ববঙ্গ ভাগ করে আসামের সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।
লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ চিন্তার উদগাতা ছিলেন না। ‘টাইমস অব ইন্ডিয়ার সম্পাদক ল্যেভট ফ্রেসার ‘ইন্ডিয়া আন্ডার কার্জন এন্ড আফটার’ গ্রন্হে তথ্য প্রকাশ করেছেন, ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মধ্য প্রদেশের চীফ কমিশনার হিসেবে স্যার এন্ডু ফ্রেসার সম্বলপুর জেলার আদালতের ভাষা উড়িষার পরিবর্তে হিন্দী করার অনুমতি চেয়ে গভর্নর জেনারেল কার্জনের কাছে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে প্রসঙ্গত তিনি প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে অবিলম্বে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সাথে যুক্ত করার পরামর্শ দেন। কিন্তু ভারত সরকারের তৎকালীন কৃষি সচিব ব্যামফিল্ড ফুলার ও স্বরাস্ট্র সচিব জে পি হেওয়েট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী থেকে উড়িষ্যাকে বিচ্ছিন্ন করার সরাসরি বিরোধিতা করেন। ইতোমধ্যে বেরার অঞ্চল ইংরেজ-ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে ইংরেজ শাসিত সব প্রদেশের সীমানা নতুন করে নির্ধারণের প্রয়োজনে এক উচ্চ পর্যায়েল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে এন্ডু ফ্রেসার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বিভক্ত করার পক্ষে যুক্তি দেখান।
১৯০৫ সালে ইংরেজ শাসিত মাদ্রাজ প্রদেশে ছিল ৬১টি পৌরসভা, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে পৌরসভা ছিল ১৫৮টি। এ সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী কলকাতার লোকসংখ্যা ১১ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। কলকাতাসহ ১৫৮টি পৌরসভার সমস্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি লে. গভর্নরের একক হাতে। ১৯০৩ সালে ইংরেজ শাসিত তিনটি বড় প্রদেশের মধ্যে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা ছিল সবচে’ বেশি। মাদ্রাজে সাড়ে ৪২ মিলিয়ন, ইউ পিতে সাড়ে ৪৮ মিলিয়ন এবং বেঙ্গলে ৭৮ মিলিয়ন। এই অবস্থায় ১৯০২ সালের ২৪ মে লর্ড কার্জন লন্ডতে ভারত সচিব লর্ড হ্যামিল্টনের কাছে প্রশাসনিক কাজের বৃহত্তর স্বার্থে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ভাগ করার যুক্তি দেখিয়ে একটি চিঠি পাঠান। তাতে তিনি বলেন, এক ব্যক্তির প্রশাসনিক কর্তৃত্বের জন্য এটি অসম্ভবরূপে একটি বৃহৎ প্রদেশ। এই চিঠির জের ধরে ভারতের স্বারাষ্ট্র-সচিব হার্বার্ট রিসলে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর তারিখে বেঙ্গল, মাদ্রাজ ও বোম্বের প্রাদেশিক সরকারগুলোর কাছে চিঠি পাঠান। তাতে তিনি ইংরেজ শাসিত প্রদেশগুলোর সীমানা পুনঃনির্ধারনের প্রসঙ্গ ছাড়াও আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ করেন। এই চিঠিতে বঙ্গভঙ্গের রূপরেখাও উপস্থাপন করা হয়। তিনি লিখেছেনঃ
“অব্স্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, বেঙ্গলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর প্রায় সারা বছর সফর করলেও নিজের এলাকার একাংশের বেশি পরিদর্শনে সক্ষম হবেন না। পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যেও তাঁর পক্ষে চট্টগ্রাম, ঢাকা, কটক, রাঁচি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান একবারের বেশি সফর করা অসম্ভব”।
চিঠিতে বলা হয়ঃ (ক) মাদ্রাজের উড়িয়াভাষী এলাকা বাংলার সাথে যুক্ত করা হবে, (খ) ছোট নাগপুরের বিরাট অংশ বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং (গ) চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য ত্রিপুরাকে আসাম প্রদেমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফলে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির লোকসংখ্যা ৭৮ মিলিয়ন থেকে ৬০ মিলিয়নে হ্রাস পাবে এবং বেঙ্গলের ২৪,৮৮৪ বর্গমাইল এলাকা আসাম প্রদেশের আওতাভুক্ত হবে। উপরন্তু প্রায় ৩১ মিলিয়ন জনসংখ্যা সম্বলিত সম্প্রসারিত আসাম প্রদেশ চট্টগ্রামের মতো একটি বন্দরের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারবে। আসামের প্রশাসনের জন্য একটা পৃথক সিভিল চালু করাও সম্ভব হবে।
১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগের খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেন। তিনি ১৯০৪ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ঢাকা এবং ২০ফেব্রুয়ারি মোমেনশাহী সফর করেন। উন্নততর প্রশাসনিক সুবিধার লক্ষ্যে বঙ্গ বিভাগের পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে জনসভায় বক্তৃতা করেন। এই সফরের আগে তিনি তার স্ত্রীকে এক চিঠিতে বলেন : ‘পূর্ব বঙ্গ আলাদা করার বিরুদ্ধে পুরোদমে হৈচৈ চলচে, কিন্তু এ পর্যন্ত কোন যুক্তি দেখানো হয়নি’।
লর্ড কার্জনকে ঢাকায় বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ তাঁর সম্মানে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে রাজপথ সজ্জিত করেন। নওয়াব বাড়িতেই কার্জনের মেহমানদারী করা হয় এবং ২০ ফেব্রুয়ারি আহসান মঞ্জিলে সংবর্ধনা দানকালে জেলা পরিষদ ও পৌরসভার পক্ষ থেকে একটি, ঢাকাবাসীদের পক্ষ থেকে একটি, প্রাদেশিক মুসলমান সমিতির পক্ষ থেকে একটি এবং জমিদারদের পক্ষ থেকে একটি- মোট চারটি মানপত্র দেওয়া হয়। প্রতিটি মানপত্রেই বঙ্গভঙ্গের প্রসঙ্গটি গুরুত্বের সাথে উল্লেখিত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ লর্ড কার্জনের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর প্রকাশ্যে বঙ্গ বিভাগের প্রতি সমর্থন জানান। চট্টগ্রাম, মোমেনশাহী ও ঢাকা সফর করে কার্জন আরো দৃঢ়ভাবে অনুভব করেন যে, পরিবর্তন অত্যাবশ্যক।
বঙ্গ বিভাগের পরিকল্পনা বিলাতে বিশেষভাবে পরীক্ষিত হওয়ার পর ১৯০৫ সালের জুর মাসে বারত সচিব সেটি অনুমোদন করেন। বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব প্রচার করা হয় ১৯০৫ সালের ৫ জুলাই। ১ সেপ্টেম্বর নতুন প্রদেশ গঠনের সরকারি ঘোষণা প্রকাশ করা হয়। লর্ড কার্জন নতুন প্রদেশের নাম দিয়েছিলেন ‘উত্তর-পূর্ব প্রদেশ’। সেভাবেই তা অনুমোদিত হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ১ অক্টোবর ভারত সচিব নতুন প্রদেশের নাম ‘পূর্ববাংলা ও আসাম’ রাখার পরামর্শ দিয়ে তারবার্তা পাঠান। অবশেষে প্রবল উত্তাপ আর উত্তেজনার মধ্যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ’ জন্ম লাভ করে। নতুন প্রদশের প্রথম গভর্নর হলেন আসামের চীফ কমিশনার ব্যামফিল্ড ফুলার (১৮৫৪-১৯৩৫)।
প্রায় পৌনে দু’শ বছরের ব্যবধানে ঢাকা আবার প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদা লাভ করল। চট্টগ্রাম হলো প্রধান বন্দর-নগরী। নতুন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভা ও রাজস্ব-বোর্ড থাকবে। কিন্তু হাইকোর্টের এলাকা থাকল অপরিবর্তিত। অবিভক্ত বাংলার ১৮টি জেলা ও ২টি দেশীয় রাজ্য নতুন প্রদেমের অন্তর্ভুক্ত হয় সেগুলো হলো : ১. চট্টগ্রাম, ২. নোয়াখালি. ৩. বাকেরগঞ্জ, ৪. ফরিদপুর, ৫. ত্রিপুরা, ঢাকা, ৭. মোমেনশাহী, ৮. পাবনা, ৯, বগুড়া, ১০, রাজশাহী, ১১, মালদহ, ১২. দিনাজপুর, ১৩, রংপুর, ১৪. জলপাইগুড়ি, ১৫. কুচবিহার ও ১৬. পার্বত্য ত্রিপুরা।
মালদহ থেকে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেমের সীমানা এমনভাবে চিহ্নিত করা হয়, যার ফলে কোন হিন্দীভাষী এলাকা নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। চা ও পাট ছাড়াও বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্দ এই নতুন প্রদেশের আয়তন হলো ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৩ কোটি ২০ লাখ। বাকিরা, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে থাকল তার পুব দিকের বিভাগসমূহ, ছোট নাগপুরের পাঁচটি হিন্দী রাজ্য ছাড়া বাকি অংশ এবং সম্বলপুর ও ৫টি উড়িয়া রাজ্য। বঙ্গ বিভাগের পরও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির আয়তন ছিল ১ লাখ ৪১ হাজার ৫৮০ বর্গমাইল। আর লোকসংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লাখ। তার মধ্যে ৪ কোটি বিশ লাখ হিন্দু, ৬০ লাখ মুসলমান।
ঢাকা ও কলকাতাঃ বিপরীত স্রোতের যাত্রী
উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকালীন অধ্যায়রূপে বঙ্গভঙ্গ ভারতীয় রাজনীতিতে সৃষ্টি করে এক বড় ধরনের অভিঘাত। বঙ্গভঙ্গ ইংরেজ আমলের সবচে’ চাঞ্চল্যকর ও সর্বাধিক বিতর্কিত ঘটনা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই কলকাতার বর্ণহিন্দুরা দেড়শ’ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো তাদের ভাগ্য-বিধাতাদের ‘বয়কট’ করার কর্মসূচি গ্রহণ করে। তার সবখানে সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে দেয়। সে আগুলে পুড়ে ছাই হয় গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের রাজনৈতিক ভবিষ্যত। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ঘটনাপ্রবাহের অভিঘাতে নিদারুল মর্ম-যতনা নিয়ে অপরিণত বয়সে ইনতেকাল করেন ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলিম লীগ নামে উপমহাদেশের মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক মঞ্চের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুসলমানদের এই স্বতন্ত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানটি তাদেরকে স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে স্বাধীন রাষ্ট্রসত্তা অর্জনের সংগ্রামে পরিচালিত করে। বঙ্গভঙ্গের তিক্ত ঘটনাপ্রবাহের পটভূমিতে কলকাতার বাঙালি বর্ণহিন্দুদের একাধিপত্য খর্ব করার জন্য ১৫৪ বছর পর কলকাতা থেকে ব্রিটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়। কলাকাতা তার পুরনো মর্যাদা আর কখনো ফিরে পায়নি।
ইংরেজ শাসকরা তাদের প্রশাসনিক প্রয়োজনে বিশাল ‘বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি’ ভাগ করেছিল। এটিকে তারা দেখেছিল একটি বলিষ্ঠ প্রশাসনিক সিদ্ধান্তরূপে। পূর্ববাংলার ভাগ্য-বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বঙ্গ বিভাগকে দেখেছিল তাদের ‘ভাগ্যোদয়ের প্রথম প্রভাত’-রূপে। অন্যদিকে ইংরেজদের সম্পূরক শক্তিরূপে পূর্ণতাপ্রাপ্ত কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা এ ঘটনাকে মূল্যায়ন করেছে তাদের দেড়শ’ বছরে গড়ে তোলা আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর একটি কঠিন আঘাতরূপে। তাদের ভাষায় এ ঘটনা ছিল ‘এক গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়’। বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় ঢাকাকেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যশ্রেণী ছিল আনন্দিত এবং এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য সংগ্রামরত। আর কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু মধ্যশ্রেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ছিল, ‘গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি আর কখনো এত বড় দুর্দিনের শিকার হয়নি”।
বঙ্গভঙ্গকে বর্ণহিন্দুরা চিহ্নিত করেছে ‘বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদ” রূপে। তারা বলেছে, একটি প্রাচীন প্রদেশ যেসব আচার-ব্যবহারও রীতি-নীতির পুরনো বন্ধনে যুক্ত ছিল, বঙ্গ প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত করে সেগুলো ছিন্ন ভিন্ন করা হয়েছে। এটাই ছিল তাদের প্রধান অভিযোগ। অথচ দূর অতীতে কিংবা নিকট অতীতে পরিবর্তনশীল সীমানার অধীনে বাংলা নামে কোন দেশ ছিল না। দূর অতীতে এই অঞ্জল অঙ্গ, বঙ্গ, পুণ্ডু, কলিঙ্গ, রাঢ়, সূম্ম প্রভৃতি নামে বহু খণ্ডে বিভক্ত ছিল। বাংলার মুসলিম সুলতানী আমলেই প্রথমবার শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে ‘বাংগালাহ’ নামে একটি বিস্তীর্ণ এলাকাকে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক সত্তার অধীনে সংস্থাপিত করা হয়েছিল। সেই সীমানা বঙ্গভঙ্গকালীন বাংলার অনুরূপ ছিল না। এরপরেও বারবার রাজ্যের বহিঃসীমানা এবং অভ্যন্তরীন প্রশাসনিক বিভাগসমূহে নিরন্তর পরিবর্তন এসেছে। সুলতানী আমলের তিনটি ইকলিম বা প্রদেশ ছিল সোনারগাঁও, সাতগাঁও ও লাখনৌতি। শেরশাহ তাঁর প্রশাসনিক বিবেচনায় এই তিনি প্রদেশকে ১৯টি ‘সরকার’ ও ৬৮২টি পরগণায় ভাগ করেন। এরপর মুর্শিদ কুলী খাঁ ১৭২২ সালে শেরশাহের আমলের বিভাগসমূহ পরিবর্তন করে তাঁর শাসনাধীন এলকাকে ১৩টি চাকলা ও ১৬৬০টি পরগণায় পুনর্বিন্যাস করেন। সুবাহদারী আমলে প্রায়শ বাংলা ও বিহারের জন্য সরাসরি দিল্লী থেকে পৃথক সুবাহদার নিযুক্ত হতেন। বাংলা প্রদেশ একাধিক নায়েব-নাযিমের অধীনে ন্যস্ত ছিল। তাদের ওপর ছিলেন সুবাহদার। নবাবী আমলে শতবর্ষব্যাপী ঢাকা ছিল সুবাহ বাংলার রাজধানী। সুবাহদারগণ প্রায় স্বাধীন শাসকের মতো শাসন পরিচালনা করেছেন। তাঁদের আমলে একটি স্বাধীন রাজধানীর মেজাজ নিয়েই ঢাকা নগরী বেড়ে উঠেছিল। এরপর মুর্শিদ কুলী খাঁ ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন। সে সময় এবং তার দীর্ঘদিন পরও কলকাতা ছিল ধানক্ষেত, কলকাবাগান আর জঙ্গল অধুষিত ‘গোবিন্দপুর-কলকাতা-সুতানুটি’ গ্রাম-সমষ্টি মাত্র। একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের অধীনে বাংলার যে আকার বা গঠন বিন্যাস, তা ছিল একেবারে সাম্প্রতিক বিষয়। বৃটিশ শাসন দৃঢ়ভাবে কায়েম হওয়ার অনেক পরে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছিল। অর্থাৎ যে বঙ্গ মাতার অঙ্গচ্ছেদের যন্ত্রণায় কলকাতার বর্ণহিন্দুরা বিশ শতকের গোড়ার দিকে ছটফট করছিলেন, সেই বাংলার বয়স তখন ছিল একশ’ বছরেরও কম।
কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুদের বিরোধীতার ছয় কারণ
‘বঙ্গ মাতা’র অখণ্ডতার প্রশ্ন তুলে কলকাতার বর্ণহিন্দরা গরিস্ঠ হিন্দু জনতাকে ধর্মীয়ভাবে উম্মক্ত করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আসল কারণ ছিল ভিন্নরূপ। সরাসরি নথিপত্র, পত্র-পত্রিকার সমসাময়িক বিবরণ এবং বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্হের আলোকে বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতার ছয়টি প্রধান কারণ খুঁজে পাওয়া যায়ঃ
এক.
ইংরেজদের নতুন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে সৃষ্ট বর্ণহিন্দু ভূমি-বিচ্ছিন্ন, অনুপস্থিত নব্য জমিদারগোষ্ঠী প্রজা-শোষণের নানারূপ কৌশলের মাধ্যমে অর্জিত উদ্বৃত্ত অর্থে কালকাতায় যে বিলাসী জীবন কাটাচ্ছিলেন, বঙ্গভঙ্গের মধ্যে তারা নানাবিধ স্বার্থহানির বিপদ দেখতে পেলেন। নিয়মিত খাজনা আদায়ের জন্য ঢাকায় এখন আলাদা অফিস বসাতে হবে। ফলে খরচ বাড়বে। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক-প্রজারা মুসলমান আর জমিদাররা হিন্দু হওয়ায় নতুন প্রাদেশিক ব্যবস্থায় শক্তি সঞ্চয় করে সেই মুসলিম প্রজারা জমিদারদের জুলুমের প্রতিবাদ ও খাজনা কমানোর আন্দোলন শুরু করতে পারে। তৃতীয়ত, আসামের ভূমি-ব্যবস্থা বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে আলাদা এবং প্রতি ত্রিশ বছর পর বাজস্বের নতুনভাবে নির্ধারণ করা হতো। এই নতুন ব্যবস্থা বাংলার জমিদারদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না।
দুই.
পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক সস্তা হবে বলে অনেক ব্যবস্যা চট্টগ্রামে স্থনান্তিরত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কলকাতার ব্যবসায়ীরা এটিকে তাদের ব্যবসায়িক কায়েমী স্বার্থের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বিবেচনা করে।
তিন.
কলকাতার বর্ণহিন্দু আইনজীবীদের ভয় ছিল, ঢাকায় নতুন হাইকোর্ট স্থাপিত হলে তাদের জীবিকার ক্ষেত্র সংকুচিত হবে এবং তাদের বহু মক্কেল হাতছাড়া হয়ে যাবে।
চার.
কলকাতার সংবাদপত্রের মালিকরা ভয় পাচ্ছিলেন যে, নতুন প্রদেশ স্থাপিত হওয়ার কারণে বিকাশমান ঢাকাকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তদের নতুন নতুন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হবে। ফলে মুসলিম জন অধ্যুষিত পূর্ববাংলায় কলকাতার পত্রপত্রিকার বিরাট বাজার নষ্ট হবে। এবং বড় কথা, প্রতিবাদী চিন্তা-চেতনাকে বিকশিত ও শাণিত করবে সংবাদ মাধ্যমে।
পাঁচ.
কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু রাজনীতিকরা শংকিত ছিলেন যে, নুতন পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশের ভাগ্য স্থানান্তরিত হলে বর্ণহিন্দুদের কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে।
ছয়.
হিন্দু পুনর্জাগরণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কলকাতাকেন্দ্রিক তৎকালীন রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গি গড়ে উঠেছিল। সে কারণে তারা মনে করেছিল যে, নতুন প্রদেশ সৃষ্টির ফলে দেড়শ’ বছরের বঞ্চনার শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির কাছে এটা ছিল একেবারেই অসহ্য। ‘ভারত সভা’র প্রতিষ্ঠাতা, কলকাতার শীর্ষস্থানীয় বর্ণ-হিন্দু নেতা, কংগ্রেসপন্হি রাজনীতিবিদ ও বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিত্ব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বিষয়টি রাখ-ঢাক ছাড়াই প্রকাশ করেছেন।
তাঁর ভাষায়ঃ
“For it was openly and officially given-out that Eastren Bengal & Assam was to be a Mohameban Province; and that credal distinctions were to be recognised as tha basis of the new policy to be adopted in the Province.” (A Nation in Making, London. P. 187-88)
কলকাতার প্রতিক্রিয়াঃ ‘দেড়শ বছরের বৃহত্তর জাতীয় বিপর্যয়’
কলকাতা নগরীকে ঘিরে ইংরেজ প্রসাদ-পুষ্ট বর্ণহিন্দুদের ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী স্বার্থতাড়িত যে মনস্তাত্ত্বিক সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল, তাদের বঙ্গভঙ্গবিরোধী মারমুখি মনোভঙ্গি ছিল তারই প্রত্যক্ষ ফল। রেভারেন্ড জেমস লঙ তাঁর ‘পিপস ইনটু সোশ্যাল লাইফ অব ক্যালকাটা’ বইয়ে লিখেছেনঃ
“কলকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসের সাথে বাংলার তথা ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রগতির ইতিহাস ঘনিষ্টভাবে জড়িত; জলাভূমি, জঙ্গল ও গ্রাম থেকে কিভাবে কলকাতা ধীরে ধীরে আধুনিক শহর ও মহানগরে পরিণত হয়েছে, সে কাহিনী লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে সযত্নে রিক্ষত প্রায় এক লক্ষ সরকারি নথিপত্রের মধ্যে সবিস্তারে লেখা রয়েছে।
বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণীহিন্দুদের প্রতিক্রিয়াকে তাদের বিশেষ মানসিক অবস্থানের প্রেক্ষিতেই বিবেচনা করতে হবে। আর এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য কলকাতা নগরীর ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি নযর ফেরাতে হবে। ১৭৭৪ সাল থেকে দেড়শ বছর ধরে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দুরা শোষণ-সাফল্যের একেকটি স্তর উতরিয়ে উঠে গেছে একেবারে শীর্ষ-চূড়ায়। তাদের সেই উত্থান-আরোহনের কার্যকারণরূপে পূর্ববাংলার গরিষ্ঠ মুসলমান কৃষক-প্রজাসাধারণ পতনের একটির পর একটি ধাপ বেয়ে নেমে গেছে অধঃপাতের অতল অন্ধকারে। একদিকে বর্ণহিন্দুদের উত্থান, অন্যদিকে মুসলমানদের পতন-এসব কিছুরই মধ্যবিন্দুতে কলকাতা। বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কার্যকরণ কলকাতা কেন্দ্র করে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের দ্রুত বিকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমিতেই তাই তালাশ করতে হবে।
ইংরেজ সরকার বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব কার্যকর করার আগেই কলকাতার জমিদার, বুদ্ধিজীবী ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া আঁচ করতে পেরেছিলেন। এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গবেষক সুমিত সরকার ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত গ্রন্হ ‘দি স্বদেশী মুভমেন্ট ইন বেঙ্গল’ (১৯০৩-১৯০৮)- এ ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিসলের ১৯০৪ সালের ৭ ফেব্রুয়ারির একটি প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন।
তাতে বলা হয়ঃ
“বিক্রমপুরের ‘বাবুগন’ এই ভেবে সন্ত্রস্ত হবেন যে, অধন্তন সরকারি চাকুরিতে তাদের এতদিনকার আধিপত্য বুঝি বিলুপ্ত হলো, প্রস্তাবিত ভাগরেখার দু’পাড়েই যেসব জমিদারের ভূসম্পত্তি আছে তাদের দুই সেট করে প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগ করতে হবে; ভাগ্যকুলের রায়েরা- কলিকাতার হাটখোলাকে কেন্দ্র করে যাদের কাঁচা পাট ও চালের বিরাট ব্যবসা-ভীত হয়েছে এই জন্য যে, চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি বিকল্প বাণিজ্যপথ খোলা হবে; কলিকাতার আইন ব্যবসায়ীদের ভয়, শেষ পর্যন্ত কলিকাতা হাইকোর্টের এখতিয়ার অনেকটা হ্রাস পাবে; চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশে (পূর্ববঙ্গ ও আসাম) অবস্থান করতে হলে পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদগণ ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন; আর কংগ্রেস-রাজনীতিতে কলিকাতা এবং বাংলার (বর্ণহিন্দুদের) ক্ষমতা ও আধিপত্য নিশ্চয়ই এক চরম সুপরিকল্পিত আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে”।
১৯০৫ সালের প্রস্তাবিত বঙ্গভঙ্গের জন্য সবচে’ বেশি আতংকগ্রস্ত হয়েছিল কলকাতায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় বর্ণহিন্দু জমিদারগোষ্ঠী। এরা অন্য সকল ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর অনুগত ছিল। কিন্তু নিজেদের বড় রকমের স্বার্থহানির আশঙ্কায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রশ্নে সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার ঝুঁকি নিয়েছে। ড. অরবিন্দ পোদ্দার লিখেছেনঃ
“বিচিত্র উপাদান এবং বৈষয়িক স্বার্থ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গতি সঞ্চার করে। ….. জমিদারশ্রেণী- যাদের পুরাতন এবং নতুন উভয় প্রদেশেই জমিদারী ছিল- এই ভাবনায় চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে, রাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ব্যবস্থায় তাঁরা এ পর্যন্ত যেভাবে লাভবান হয়ে আসছিলেন বাঙালা বিভাগের ফলে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা! কারণ, আসামে সাময়িক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারিত হতো এবং ত্রিশ বছর মেয়াদে এর পুনির্বন্যাস করার ব্যাবস্থা প্রচলিত ছিল। সুতরাং আসামের সঙ্গে পূর্ববাংলা সংযুক্ত হলে পূর্ববাংলার জমিদারদের রাজস্ব খাতে আয় হ্রাস নিশ্চিত। তার উপর বাংলা বিভক্ত হলে ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের চাকুরির সম্ভাবনা ও পরিধি সংকুচিত হবে, এইরূপ বাস্তব আশঙ্কায়ও অনেকেই বিচলিত ছিলেন। এ আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারণ আইন ব্যবসায়, সরকারি চাকুর, শিক্ষাক্ষেত্র ইত্যাদি ইতোমধ্যেই জনাকীর্ণ হয়ে উঠেছিল।….. সুতরাং বেকারীর ভয় বাস্তব”। (রবীন্দ্রনাথ- রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পৃষ্ঠা ১২১-১২৩, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮২)
বঙ্গভঙ্গের ফলে বর্ণহিন্দু শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ঐতিহাসিক বি.বি মিশ্র তাঁর গ্রন্হ ‘দি ইন্ডিয়ান মিডল ক্লাসেস’-এ লিখেছেনঃ
…… এই বিভাগের ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দারুণ ক্ষতি হলো এবং তারা প্রায় সবাই বর্ণহিন্দু। তাদের স্বার্থভোগের ক্ষেত্রভূমি বিভাগের ফলে আরও সংকুচিত হয়ে গেল, বিশেষত তখন বিধান সভাগুলির সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছিল তারা স্বাভাবিকভাবেই ভীত চক্ষে দেখলো, উভয় বাংলার বিধান সভায় তারা একেবারেই সংখ্যালঘু হয়ে যাচ্ছে- পূর্ববাংলায় অসমীয়া ও মুসলমানদের দ্বারা এবং পশ্চিমবাংলায় বিহারী ও উড়িয়াদের দ্বারা- এজন্য তারা ক্রোধে পাগল হয়ে উঠল”।
বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত পাকাপাকি হওয়ার পর বর্ণহিন্দু রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক ও অন্যান্য শিক্ষিত শ্রেণী ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তাদের কার্যক্রমে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায়। কংগ্রেস নেতা সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বললেন, “গোপনে এই বঙ্গভঙ্গ চিন্তার সূত্রপাত, গোপনে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে আর গোপনেই এর চূড়ান্তকরণ করা হয়েছে”। কংগ্রেসের এককালের সভাপতি মোমেনশাহী আনন্দমোহন বসু বঙ্গভঙ্গ বানচালের প্রকাশ্য শপথ ঘোষণা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর নেতৃত্বে বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ৬ জুলাই বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গবঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত ‘বেংগলী’ পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে ‘একটি গুরুতর জাতীয় বিপর্যয়’ রূপে চিহ্নিত করা হয়। হিতবাদী পত্রিকা লিখলঃ
“গত ১৫০ বছরের মধ্যে বাঙালি জাতি এই রকম দুর্দিনের সম্মুখিন হয়নি”।
প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়। এসব সভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত হয়। এ ক্ষেত্রে ছাত্রদের ভূমিকা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (আধুনিক ভারত, প্রথম খণ্ড)
স্বদেশী আন্দোলন
বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ‘স্বদেশী’ নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করা হয়। সে আন্দোলনকে আরো তীব্র করতে বিলাতী পণ্য বর্জনের ডাক দেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের ১৭ জুলাই বাগেরহাটে এক জনসভায় বিলাতি পণ্য বর্জন সংক্রান্ত প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, যতদিন বঙ্গভঙ্গ বাতিল না হবে, ততদিন ব্রিটিশ পণ্য বর্জন করা হোক। পরবর্তী ছয় মাস সব ধরনের আনন্দ অনুষ্ঠান ও উৎসবে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। কলকাতার রিপন কলেজে দু’দিনব্যাপী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিলাতি পণ্য পোড়ানের আহ্বান জানানো হয় এবং সেখানে একটি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়।
স্বদেশী আন্দোলন শুরু হওয়ার সাথে সাথে বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) এই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ‘স্বদেশ বান্ধব সমিতি’ ১৫৯টি শাখার মাধ্যমে বরিশাল জেলায় স্বদেমী ও বয়কট আন্দোলন সংঘটিত করে (প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ আধুনিক ভারত)।
মহারাজা গিরিজা নাথের সভাপতিত্বে দিনাজপুরে এক সভায় বছরব্যাপী জাতীয় শোক পালন এবং জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড ও পৌরসভা থেকে সকল সদস্যের পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বরিশালে লর্ড কার্জনের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাতে যুদ্ধ-মন্ত্রের মতো ‘বন্দে মাতরম’ গাওয়া হয় এবং বিভক্ত ‘বাংলা-মা’- এর পুনঃসংযোজন না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার সংকল্প প্রকাশ করা হয়।
১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর উদ্যোগে মনীন্দ্রনাথ নন্দীর সভাপতিত্বে বাংলার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ থেকে ৪৬ জন প্রতিনিধি এই সভায় যোগ দেন। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, “বঙ্গ বিচ্ছেদ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ পণ্য ব্যবহার হবে না”। বিলাতি পণ্য বয়কটের পাশাপাশি স্বদেশী মাল ব্যবহার, জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, কর্মচারীদের অফিস বর্জন, সরকারের কাছে প্রতিনিধি দল প্রেরণ প্রভৃতি কর্মসূটি নেওয়া হয়। ১৯০৫ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে ঢাকার জগন্নাথ কলেজে বাবু অন্নদা চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী অংশগ্রহণ করেন। এর কয়েক দিন পর বড়লাটের কাছে বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়।
স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতাদের সর্বাধিনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (১৮৪৮-১৯২৫), তাঁর সহযোগী ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২), আনন্দচন্দ্র রায় (১৮৪৪-১৯০৫), মোমেনশাহীর অনাথবন্দু গুহ, বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, বরিশালের অশ্বিনা কুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), সিলেটের বিপিন চন্দ্র পাল, কলকাতার অরবিন্দু বোস (১৮৭২-১৯৫৯), আনন্দমোহন বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ।
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবল বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হওয়ার প্রথম দিনে ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম নেতৃবৃন্দ নর্থব্রুক হলের সভাস্থলে মিলিত হয়ে যখন নতুন প্রদেশের উন্নয়নে তাঁদের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করছেন, কলকাতার চেহারা সেদিন সম্পূর্ণ অন্য রকম। এ সম্পর্কে এম আর আখতার মুকুল লিখেছেনঃ
“১৬ আক্টোবর এদের কর্মসূটির মধ্যে ছিল ধর্মঘট, গঙ্গাস্নান এবং রাখী বন্ধন। বাস্তব তথ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করতে হয় যে, এদিন কলকাতায় যে শোভাযাত্রা হয়েছিল অন্যদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও তার পুরোভাগে ছিলেন এবং তিনি অসংখ্য পথচারীর হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছিলেন। অপরাহ্নে রোগ-জর্জর আনন্দমোহন বসু ‘মিলন মন্দিরের’ ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানের জন্য ইংরেজিতে যে ভাষণ লিখে এনেছিলেন তা পড়ে শুনালেন আাশুতোষ চৌধুরী এবং বাংলায় অনুবাদ করে পাঠ করেছিলেন বঙ্গদর্শন পত্রিকার সেই আমলের সম্পাদক কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিকেলের জনসভায় ঘোষিত শপথ বাক্যের বাংলায় তর্জমা করেও পাঠ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ”। (কলিকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, পৃষ্ঠা ২১৩)
সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন
বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন অত্যন্ত দ্রুত বর্ণহিন্দু চরমপন্হি নেতৃবৃন্দের কব্জায় চলে যায়। ১৯০৬ সালে এসে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গোপন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিস্তার ঘটে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের শুভেচ্ছাপুষ্ট অনুশীলত সমিতি এ সময় পুরাপুরি সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে পরিণত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস আর স্বামী বিবেকান্দের ‘নব্য হিন্দুবাদের’ দীক্ষাপ্রাপ্ত বর্ণহিন্দুরা দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, শরীর চর্চার আখড়া স্থাপন এবং কালী মন্দিরকে ঘিরে শক্তি সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। হিন্দুদের সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে উগ্রমূর্তি নিয়ে হামলা চালাতে থাকে। চরমপন্হিরা ১৯০৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে নরমপন্হিদের সাথে উত্তপ্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। হিন্দু ধর্ম-রাজ্যে বিশ্বাসী মারাঠা ব্রাহ্মণ বালগঙ্গাধর তিলককে কংগ্রেসের সভাপতি পদে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং এ নিয়ে ১৯০৭ সলে সুরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে মারামারি হয়।
১৯০৭ সাল ছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের চরম পর্যায়। ১৯০৯ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। ১৯১০ সালে এসে এই আন্দোলনের উম্মত্ততা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন ঘোষ, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখের প্রচেষ্টায় বর্ণহিন্দু লেখক, কবি ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের হিন্দু জাতীয়তাবাদমূলক রচনা ও প্রচারণায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সরকার বিরোধীতার সাথে সাথে মুসলিমবিরোধী আন্দোলনের রূপ লাভ করে। রাখী বন্ধন, কালী মন্দীরে শপথগ্রহণ, বন্দে মাতরম স্লোগান, এমনি অসংখ্য হিন্দু আচার এই আন্দোলনের সাতে জুড়ে দেওয়া হয়। সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়িয়ে দেওয়া হয় সর্বত্র। ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের দারুণ অবনতি ঘটে। রাস্তাঘা্টে সর্বত্র বিদ্বেষেরে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। স্কুলে হিন্দু ছাত্ররা তাদের সহপাঠি মুসলমান ছাত্রদের মুখ থেকে ‘পিয়াজের গন্ধ আসে’ বলে অভিযোগ তুলে তাদের সাথে একত্রে বসতে অস্বীকার করে। ক্লাসে মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক শাখার ব্যবস্থা করতে হয়। (নিরোদচন্দ্র চৌধুরীঃ অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান, পৃষ্ঠা ২৩৭)
কংগ্রেসেপন্হি ভারতীয় গবেষক প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, বঙ্গভঙ্গবিরাধী আন্দোলনের সময় বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস অশ্বিনী কুমারের সাথে সাথে থাকতেন এবং ‘স্বদেশী যাত্রার’ প্রবর্তক হিসেবে এ সময় তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। সম্প্রতি কলকাতার বসুমতি সাহিত্য মন্দির পত্রিকায় প্রকাশিত ‘মুকুন্দ দাসের গ্রন্হাবলী’তে উল্লেখ করা হয়েছেঃ
“বরিশালের উপকণ্ঠে কালী মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়াই তাহার সকল স্বপ্ন, সকল সাধনা মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় সংগঠন সফল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ‘আনন্দময়ী আশ্রম’। ……. ‘মাতৃপূজা’ তাহার প্রথম যাত্রাভিনয়”।
বঙ্গভঙবিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক অন্যান্য যাত্রাগানেও সকলেই ‘বন্দে মতরম’ এর জয়গান গেয়েছেন এবং সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রশান্তির লক্ষ্যে বীর পূজা চালূ করেছেন।– এর মধ্যে মথুর সাহার ‘পদ্মিণী’ ও ‘ভরতপুরের দুর্গজয়’, ভূষণ দাসের ‘মাতৃপূজা’, শশী অধিকারীর ‘প্রতাপাদিত্য’, ভূপেন্দ্র নারায়ণ রায়ের ‘রামলীলাবাসন’, ‘মনিপুরেরর গৌরব’, ‘মনোজয়ের মহামুক্তি’ হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘রণজিত রাজার জীবযজ্ঞ’ উল্লেখযোগ্য।
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে আগাগোড়াই লক্ষণীয় বিষয় হলো বর্ণহিন্দু নতাদের সাংস্কৃতিক প্রেরণা। এ আন্দোলনে রাজনৈতিক বক্তব্যের চাইতেও সাংস্কৃতিক বিবেচনা বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে। এ আন্দোলনের যা কিছু অর্জন, তা এসেছে এ পথেই। আর তাদের এই সংস্কৃতির বাতাবরণ ও অন্তরাত্মা পুরেপুরি হিন্দু। এ সম্পর্কে ১৯০৮ সালে মুসলিম লীগের অমৃতসর অধিবেশনে সৈয়দ আলী ইমাম সভাপতির ভাষণে বলেনঃ
“I can not say what you think, but when I find the most advanced province of India put forward the sectarian cry o f ‘Bande Mataram’ as the national cry, and the sectarian Rakhi Bandhan as a national observance, my heart is filled with despair and disappointment: and the suspicion that under the cloak of nationalism “Hindu nationalism” is benig preached in India becomes a conviction.” (Sharifuddin Pirzada: Foundation of Pakistab. vol.- 1, p-151)
ঢাকার প্রতিক্রিয়াঃ ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত
বহু ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন তাদের বঞ্চনার অবসানের সূচনা-ভাগ্যোদয়ের নতুন প্রভাত-কৈশোর উত্তীর্ণ বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশধারা ত্বরান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ‘কর্দমে প্রোথিত’ কৃষক-প্রজাদের দীর্ঘকালীন জুলুম-শোষণের অবসান। বঙ্গ বিভাগের আগে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমা ‘টাওয়ার বঙ্গের’ লুণ্টনক্ষেত্র- ‘খামার-বাড়ি’। পূর্ববাংলার কৃষকদের উৎপাদিত কাঁচামালের সিংহভাগ কলকাতা ও তার আশপাশর জেলাগুলোর উন্নতির কাজে ব্যবহার হতো। পুবের কাঁচামালে পশ্চিমে গড়ে উঠেছিল শিল্প-কারখানা। পুবের কৃষকদের রক্ত পানি করা শ্রমের ফসলে পশ্চিমের উচুঁকোঠার লোকেরা পশ্চিমে গড়েছেন সম্পদের পাহাড়, গড়ে তুলেছেন কলকাতার বাবু কালচার। পুবের শ্রস আর ঘামের, ফসল আত্মসাৎ করে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহিন্দু বাবুশ্রেণীর জীবনে এসেছে রেনেসাঁ বা নবজাগৃতি। পূর্ববঙ্গের বর্ণহিন্দু ধনিকশ্রেণী এখান থেকে অর্জিত উদ্বত্ত মূলধন ব্যয় করত কলকাতায়, সেখানেই তারা গগেড় তুলেছে স্কুল কলেজ-হাসপাতাল। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলাকে লুণ্টন করেই ‘গোবিন্দুপুর-কলকাতা-সুতানুটির’ জঙ্গল, ধানক্ষেত আর কলাবাগান-এর ভেতর থেকে মাথা তুলেছে মহানগরী কলকাতা। ঢাকাকেন্দ্রিক নুতন প্রদেশ গঠিত হওয়ায় কলকাতর অবাধ লুণ্টনক্ষেত্র-রিক্ত নিঃস্ব পূর্ববাংলা আবার নতুন করে মাথা জাগানোর সুযোগ পেল। বঙ্গভঙ্গে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতিক্রিয়া এই পটভূমিতেই বিচার্য। এই পটভূমিতেই ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের নতুন ভোরে ঢাকার নর্থব্রুক হলের এক সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে নতুন প্রদেশ গড়ে তোলার প্রেরণায় জন্ম লাভ করে ‘প্রভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন’। নতুন প্রদেশের জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ এই সংস্থার অন্যতম লক্ষ্য ছিল। পূর্ববাংলার মুসলমান ছাড়াও এ সময় উপমহাদেশের অন্যান্য এলকার মুসলমানরা এই নতুন প্রদেশ গঠনের প্রতি সমর্থন জানান। বর্ণহিন্দুরা হিন্দু জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বদ্ধ হয়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতা করেন। কিন্তু তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুরা ছিলেন নতুন পরিবর্তের পক্ষে। কারণ বর্ণহিন্দুদের আর্থি ও সামাজিক নিপীড়নের কারণে মুসলমানদের মতো তারাও ছিলেন ক্ষুব্ধ। এ প্রসঙ্গে তফসিলী সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর বি. আর আম্বোদকর বলেনঃ
“সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এমনকি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার বর্ণহিন্দুদের চারণভূমি। প্রদেশের সবগুলো সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিল। বঙ্গ বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমির সীমানা সংকোচন। বঙ্গ বিভাগের প্রতি হিন্দুদের এই বিরোধীতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ববাংলার মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশগ্রহণে বাধা দেওয়া”। (বি. আর আম্বোদকরঃ পাকিস্তান অর পার্টিশন অব ইন্ডিয়া, পৃষ্ঠা ১১)।
পূর্ববাংলার বর্ণহিন্দুদের মধ্যে যারা বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করেছেন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি বলেনঃ
“আমি বঙ্গ বিভাগ নীতির বিপক্ষে নই; বরং স্বপক্ষে। আমার বিশ্বাস এর ফলে পশ্চাৎপদ, অনুন্নত ও নানাভাবে অভাবগ্রস্ত পূর্ববঙ্গের বিশেষ কল্যাণ ও উন্নতি হবে। ঢকার রাজধানী ও পূর্ববঙ্গের সীমান্তবর্তী বঙ্গোপসাগরের অদূরস্থ চট্টগ্রাম নগর বিশেষ বাণিজ্য স্থান হতে চলল; পূর্ববঙ্গবাসীদের অর্থাগমের পথ মুক্ত হলো; এদেশে রাজকীয় প্রধান প্রধান কার্যালয় স্থাপিত ও বাণিজ্যের প্রসার হবে; দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে; আসাম প্রদেশ ও পূর্বঙ্গের সাথে ঘনিষ্ঠসূত্রে আবদ্ধ হয়ে বিশেষ উন্নত লাভ করবে এটা ভেবে আমার আহলাদ হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের কথা ছেড়ে দেই। বাঙালিদের উন্নতির দর্শন অনেকের চক্ষুশূল হতে পারে। কলকাতা অঞ্চলে পূর্ববঙ্গ নিবাসী কৃতবিদ্য লোকেরা যে কোন অফিসে তাদের (কলকাতাবাসীদের) দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সহজে প্রবেশ করতে পারে না। এখানকার (কলকাতার) কেরানীগিরি প্রভৃতি কাজ এক প্রকার এখানকার লোকেরই একচটিয়া হয়ে রয়েছে”। (আত্মজীবনী, পৃষ্টা ১১৯-২০)
মুসলমান পরিচালিত পত্রিকাগুলো শুরু থেকেই বঙ্গ বিভাগের সমর্থনে ভূমিকা পালন কর। নবগঠিত প্রদেশের প্রতি কলকাতার মুসলমানদের সমর্থন ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এটা ছিল পূর্ববাংলার মুসলমানদের প্রতি তাদের আন্তরিক দরদ ও স্বজাত্যবোধের বহিঃপ্রকাশ। বিহার ও উড়িষ্যার মুসলিম নেতৃবৃন্দও বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানান। কারণ এতে তাঁরাও কলকাতার বর্ণহিন্দু বাবুশ্রেণীর আধিপত্য থেকে নিস্তার লাভের উপায় খুঁজে পেয়েছিলেন।
বঙ্গ বিভাগের বিষয়টি আঞ্চলিক হলেও তা উপমহাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। নতুন প্রদেশের প্রতি উপমহাদেশীলয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের সমর্থন লাভের জন্য নওয়াব সলীমুল্লাহ ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেন। বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনকে ত্বরান্বিত করে। মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় আটশ’ মুসলিম প্রতিনিধির এক বিশেষ সভায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ গঠন করা হয়। এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থে বঙ্গ বিভাগকে স্বাগত জানানো হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।
১৯০৮ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর অমৃতসরে মুসলিম লীগের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনেও বঙ্গ বিভাগের সমর্থনে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সলীমুল্লাহর সহকর্মী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অসরাতা প্রমাণ করেন। তিনি বলেনঃ
“What was the state of affairs in the eastern part of the province, specially in the tracts of watered by the Brahmaputra, the Padma and the Meghna? They were so detached and segregated fron the centre of administrative influence that it was inpossible under the old system to have hoped for any improvement, social, political, educational or commercial, before many long years to come”. (Qouted by Sharifuddin Pirzada: Foundation of Pakistan. vol-1, P-85)
১৯০১ সালের জানুয়ারিতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের তৃতীয় অধিবেশনেও হিন্দুদের সন্ত্রাসমূলক কার্যাবলীর নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহীত হয়।
বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বর্ণহিন্দুদের আন্দোলন তীব্র হওয়ার সাথে সাথে এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়িছিল। বৃদ্দি পেয়েছিল বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের সমর্থন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ব্যাপকভাবে বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেনঃ
“…… স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু ধর্ম ও আদর্শের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমান জনগণের মনেও এর বিরুদ্দে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেমন ‘ইসলমা প্রচারক’, ‘মিহির ও সুধাকর’, ‘হাফিজ’-এ মুসলমান লেখকেরা প্রচার করতে লাগলেন যে, তিলক, অরবিন্দ্র, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রাহ্মবান্ধব প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ হিন্দুধর্মকে কেন্দ্র করে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যা করেছেন তা উগ্রভাবে ইসলামবিরেধী। …. কিন্তু সাধারণ মুসলমান কৃষিজীবী সম্প্রদায় কেন স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি বিমুখ হলেন তা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ জমিদার ও ভূস্বামীগণ ছিলেন হিন্দু এবং তারাই স্বদেশী আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্গভঙ্গের ফলে মুসলমান প্রজা অধ্যষিত তাদের ভূসম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় হিন্দু জমিদারগণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেন। …. অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে পূর্ব বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দেয়”। (আধুনিক ভারত, প্রথম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩)
কংগ্রেসী বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বর্ণহিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগের প্রথম বর্ষপূর্তি জাঁকালোভাবে উদযাপন করা হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকা, মোমেনশাহী, ফরিদপুর ও সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন স্থঅনে জনসভা করেন। এসব জনসবা নস্যাত করার জন্য বর্ণহিন্দুরা নানাভাবে চেষ্টা করে, প্রতিবাদ জানায়, এমনকি হামলা চালায়। কুমিল্লায় এ উপলক্ষে একটি জনসভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর ওপর হামলা পরিচালনা করা হয়। সলীমুল্লাহসহ মুসলিম নেতৃবৃন্দ বর্ণহিন্দুদের নানামুখী উস্কানী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করেন।
হিন্দু জমিদাররা বঙ্গ বিভাগ রদ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি মুসলিম প্রজাদের সমর্থন আদায়ের জন্য নানাভাবে তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ঋণের টাকা আদায়ের জন্য মহাজনরা বল প্রয়োগ করে। এসব সত্ত্বেও মুসলমান ও তফসিলী সম্প্রদায়ের লোকেরা বঙ্গভঙ্গের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখেন। বঙ্গভঙ্গবিরোধী জমিদার মহাজনদের মুসলিম নির্যাতনের অনেক কাহিনী তখনকার মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠা দখল করে।
বঙ্গভঙ্গের বিরোধীতাকারীদের মধ্যে এ সময়কার কয়েকজন মুসলমানদেরও নাম পাওয়া যায়। ড. এম কে ইউ মোল্লা প্রদত্ত এই তালিকায় নবাব সলীমুল্লাহর সৎভাই খাজা আতিকুল্লাহ, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী, সিরাজগঞ্জের ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, কুমিল্লার ব্যারিস্টার আবদুর রসূল এবং নোয়াখালীর লিয়াকত হোসেন অন্যতম। এছাড়া আরো যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন সাংবাদিক মুজিবর রহমান, দেলদুয়ারের জমিদার আবদুল হালিম গজনবী, আবুল হোসেন বর্ধমানের আবুল কাসেম, দীন মোহাম্মদ, দিদার বখশ ও আদুল গফুর। ড. মফিজুল্লাহ কবির-এর বরাত দিয়ে ড. মোল্লা জানাচ্ছেন, সলীমুল্লাহর সৎ ভাই খাজা আতিকুল্লাহ নওয়াবের সাথে বৈষয়িক বিবাদের জের হিসেবে বঙ্গবিভাগের বিরোধী ভূমিকা নিলেও বিবাদ মিটে যাওয়ার পরপরই বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে কাজ করেছেন। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ফরিপুরের আলিমুজ্জামান চৌধোরীর প্রতিবাদ লিপি পাঠানোর ব্যাপারটি একটি বিতর্কিত বিষয়। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তার লিপিটি কলকাতায় প্রণীত হয় এবং স্বাক্ষরকারী প্রথম চারজন মুসলমানদের মধ্যে দু’জন ছিল হিন্দু আইনজীবীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত ফরিদপুরের লোন অফিস পাড়ায় ঋণভরে জর্জরিত। তৃতীয় দস্তখতকারী লিয়াকত হোসেন সম্পর্কিত তথ্য আরো চাঞ্চল্যকর। ১৯০৭ সালের ২৪ জানুয়ারি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের চীফ সেক্রেটারি পি, সি, লিওন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে যে নোট পাঠান, তার বরাত দিয়ে ড. মোল্লা জানাচ্ছেন, বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোর জন্য বর্ণহিন্দুরা লিয়াকত হোসেনকে মাসে চল্লিশ টাকা হারে ভাতা প্রদান করত। ব্যারিস্টার আবদুর রসূল শুরুতে বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করলেও পরে সলীমুল্লাহর সাথে কাজ করেন। কংগ্রেসপন্হি মুসলিম জমিদার দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবীর বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার আসল কারণ ছিল জমিদারী স্বার্থ। আবুল কাসেমও কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। কংগ্রেসের যুক্ত জাতীয়তাবাদ ও অখণ্ড ভারতের নীতির পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচনা করে তিনি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। আর দীন মোহাম্মদ ও আবদুল গফুর-এর বিরোধিতা ছিল লিয়াকত হোসেনের মতোই আর্থিক স্বার্থতাড়িত।
বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের হাতে গণা ঐসব মুসলিম সমর্থন সম্পর্কে পূর্ববঙ্গও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর লেন্সলট হেয়ার মন্তব্য করেছেনঃ
“The Mohamedans who took part in the agitation are in many cases the paid agents of the Hindu leaders. While others are under the thumds of the same men, owing to financial embarrassments and to the fact that they are under Hindu landlords. There are practically none, who carry any real weight or who can be called representative.” (Quoted in M K U Molla: The New. Province of Eastern Bengal & Assam)
পূর্ববাংলার উন্নয়নের সুবাতাস
‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ নতুন প্রদেশ গঠনের সাথে সাথে রাজধানী ঢাকাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ অবহেলিত এই এলাকায় উন্নয়নের একটি নতুন যুগ শুরু হয়। নব গঠিত প্রদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং প্রশাসনিক অবকাঠামো গঠনের লক্ষ্যে অফিস-আদালত নির্মাণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হয়। পূর্ববাংলার হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের বিরোধীনা করা সত্ত্বেও এই নতুন উন্নয়ন কর্মকণ্ডের সাথে যুক্ত হন। ১৯০৯ সালে অনুমোদিত নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে গঠিত হয় ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক পরিষদ’। এ সময়ের মধ্যেই নতুন প্রদেশে উন্নয়নের কিছুটা ছাপ পড়েছিল। পূর্ববঙ্গ ও আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হিসেবে ১৯১০ সালের ৫ এপ্রিল পরিষদের সভায় রায় সীতারাম রায় রাজধানী ঢাকার উন্নয়নের চিত্র তুলে ধরে বলেনঃ
But so far as the new town on the northern part of Dhaka is concerned, it is in its external aspect altogether a different thing from what it was only five years before. The dense jungles of the the vast maindan on the north has been converted, as if by the wand of a magician, into a fairy land, dotted with large and stately buildings, such as the new Government House and numerous charming bungalows and intersected by a number of very wide roads, and the whole maidan now looks picturesque and compares favourably, if I may say so, with Chowringhee of Calcutta.” (The Eastern Bengal & Assam Gazette, Part VI, April 27, 1910, P. 50-58)
ঢাকার ইতিহাসের সমসাময়িক লেখক মুনশী রহমান আলী তায়েশ তাঁর বিখ্যাত ‘তাওয়ারিখে ঢাকা’ গ্রন্হে ১৯১০ সালের অবস্থা তুলে ধরে লিখেছেনঃ
“ঢাকা এক সময় ছিল ইসলামী রাজধানী। ব্রিটিশ শাসনামলে অনেককাল পর তা আবার রাজধানীতে পরিণত হলো। এখন নবযুগের সূচনা হয়েছে, ঢাকাবাসীর সুপ্ত ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। এখন উন্নতির ধারা বয়ে চলেছে। ঢাকাতে একটি সিভিল সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে যেসব স্থানে জাঁকালো সৌধ এবং শাহী প্রাসাদ দন্ডায়মান ছিল, আল্লাহর শুকুর, সে সব জায়গায় আবার নতুন নির্মাণ কাজ চলছে। এই সব উচ্ছন্ন স্থানে নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত এলাকাকে বলা হয় ‘নিউ টাউন”।
বঙ্গভঙ্গের ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ‘পুর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশের যে অসামান্য উন্নতি হয়, তার মধ্যে সবচে’ উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র হলো শিক্ষা। মধ্যবিত্ত বিকাশের ধারা এ সময় দ্রুত এগিয়ে চলছিল। নতুন প্রেরণায় মধ্যশ্রেণী এমন কি কৃষক-প্রজদের ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। বঙ্গভঙ্গের পর মাত্র পাঁচ বছরে মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা শতকরা ৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময় মুন্সিগঞ্জে এক জনসবায় নওয়াব সলীমুল্লাহ বলেনঃ
“বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিস্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে”।
বঙ্গভঙ্গ রদঃ মুসলিম ভারতে ক্ষব্ধ প্রতিক্রিয়া
১৯১০ সাল থেকেই বর্ণহিন্দুদের বঙ্গঙ্গ বিরোধিতার উত্তাপ কমে এসেছিল। অরাজকতা ও সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হওয়ার কারণে ১৯১১ সালের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী সন্তোষ প্রকাশ করেন। সভার আলোচনার সমাপ্তি টেনে লে. গভর্নর হেয়ার নতুন প্রদেশের বিভিন্নমুখী অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে মন্তব্য করেনঃ
“জনগণের মধ্যে নতুন প্রদেশের নাগরিক হিসেবে গৌরববোধ সৃষ্টি হয়েছে, বিরোধীদের বিরোধিতার প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে এবং বঙ্গভঙ্গের কতিপয় অনমনীয় দুষমণও এখন জনহিতকর বিভিন্ন দুরূহ কাজে সরকারের সহযোগিতা কামনা করছে”। (দি ইস্টার্ন বেঙ্গল এন্ড আসাম গেজেট, ষষ্ঠ খণ্ড, ১৯১১, পৃষ্ঠা ৮১-৮৪)
পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে উন্নতির গতিধারা যখন সবেমাত্র শুরু হয়ে পুরোদমে এগিয়ে চলছিল, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল শান্ত এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে, এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। একখণ্ড ঝড় এসে যেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের বিকাশামান সাজানো সংসারকে সম্পূর্ণ লণ্ডভণ্ড করে দিল। পূর্ববঙ্গের নেতাদের সাথে কোনরূপ আলাপ-আলোচনা না করে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় রাজ্যভিষেক অনুষ্ঠান উপলক্ষে দিল্লীর দরবার থেকে সম্রাট পঞ্চম জর্জ স্বয়ং বঙ্গ বিভাগ ইংরেজদের বঙ্গঙ্গ রদ ঘোষণা সম্পর্কে ‘কোয়ার্টারলি রিভিউ’ পত্রিকা মন্তব্য করেছিলঃ
“বন্ধুকে পদাঘাত করে শক্রকে খুশি করার এরূপ মেকিয়াভেলী-নীতি এমন নির্লজ্জভাবে অতীতে আর কখনো অনুসৃত হয়নি”।
গোখলের দ্বারা প্রভাবিত ভারত সচিব লর্ড মর্লির অনুপ্রেরণায়, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের গোপন পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্লজ্জ এই বড় ঘটনাটি অত্যন্ত নিখুতভাবে সম্পাদিত হয়।হিন্দুদের বিরাগের চাইতে মুসলমানদের সাথে ওয়াদা ভঙ্গ করা ছিল অনেক সহজ কাজ। দিল্লীতে দরবার অনুষ্ঠান করে খোদ রাজা পঞ্চম জর্জের মুখ দিয়ে এই ঘোষণা জারি করার মধ্যেও ছিল আরেকটি কৌশলের খেলা। শাসনতান্ত্রিক বিধানের কারণেই সম্রাটের উক্তির বিরুদ্ধে কারো পক্ষে আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভব নয়। এভাবেই মুসলমানদের প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করা হয়েছিল।
রাজা পঞ্চম জর্জের ঘোষণার পূর্ব ও পশ্চিমবাংলাকে সংযুক্ত করে যুক্তবঙ্গীয় প্রদেশ সৃষ্টি করা হলো। এ প্রদেশ থেকে আসামকে সরিয়ে নেওয়া হলো। বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলো বিহার ও উড়িষ্যাকে। এই দুই এলাকা নিয়ে গঠন করা হলো একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ। আর ব্রিটিশ-ভারতের দেড়শ’ বছরের পুরনো রাজধানী স্থানান্তর করা হলো কলকাতা থেকে দিল্লীতে। কলকাতার বর্ণহিন্দুরা নিজেদের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করলেন এবং ‘জনগণ-মন-অধিনায়ক হে ভারত-ভাগ্য বিধাতা’ বলে পুরনো সুরে ব্রিটিশ-প্রভুর জয়গান গাইলেন। ইংরেজ শাসকরাও অল্পকালের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, কলকাতার বাইরে ভারতের আর কোথাও তাদের জন্য ‘অভয়াশ্রম’ ছিল না। ১৯১২ সালের ৩০ ডিসেম্বর দিল্লীতে ব্রিটিম ভারতের রাজধানী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন উপলক্ষে চকবাজার থেকে মিছিল বেরোলো বড়লাটের নেতৃত্বে। এই মিছিলে বড়লাট হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা নিক্ষিপ্ত হলো। মুসলিম শাসনের প্রাচীন কেন্দ্র দিল্লী এভাবেই ইংরেজদেরকে পুষ্পরেণুর বদলে বারুদ ছিটিয়ে স্বাগত জানালো।
বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে শুধু বাংলাদেশ নয়, গোটা ভারতের মুসলমানগণ স্তম্ভিত হলেন। এক কঠিন আঘাত মুসলিম-ভারতকে হত-বিহবল করে ফেলল। দারুণভাবে আহত হলেন নওয়াব সলীমুল্লাহ। বাংলার বাইরের মুসলিম নেতাদের সবচে’ ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন নওয়াব ওয়াকার উল মুলক (১৮৪১-১৯১৭)। দিল্লীর দরবার থেকে ফিরে এসে বঙ্গ বিভাগ রদের মাত্র এক সপ্তাহ পর ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বর তিনি আলীগড় ইন্সটিটিউট গেজেটে ‘ভারতীয় মুসলমানদের কর্মপন্হা’ নামে এক আবেগময় প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে তিনি বলেনঃ
“বঙ্গ বিভাগ রদ করে সরকার মুসলমানদের প্রতি অন্যায় উদাসীনতা দেখিয়েছেন। …. তাই আমাদেরকে অবশ্যই বিকল্প কর্মপন্হার কথা ভাবতে হবে। মধ্যদিনের আলোকিত সূর্যের মতোই এটা এখন পরিস্কর হয়ে গেছে যে, মুসলমানদেরকে সরকারের ওপর নির্ভরশীল থাকার পরামর্শ দেওয়া অর্থহীন। কারোর ওপর ভরসা করার সময় এখন উত্তীর্ণ। নিজেদের শক্তির ওপরই আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে। আমাদের গৌরবান্বিত পূর্ব-পুরুষগণ আমাদের জাতির জন্য সে নযীর রেখে গেছেন”।
দিল্লীর দরবারে উপস্থিত উপমহাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে নওয়াব সলীমুল্লাহ ওয়াকার উল মূলক-এর প্রবন্ধ প্রকাশের একই তারিখে অর্থাৎ ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বর লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে বাংলার মুসলমানদের পক্ষ থেকে আট দফা দাবি সম্বলিত একটি পত্র পেশ করেন। সেই আট দফা দাবি হলোঃ
১. বঙ্গ প্রেসিডেন্সির গভর্নর কলকাতা ও ঢাকা এই উভয় রাজধানীতে সবভাবে অবস্থান করবেন;
২. বঙ্গ প্রেসিডেন্সির মুসলমানদেরকে স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যানুপাতিক হারে ব্যবস্থাপক পরিষদ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে সুযোগ দিতে হবে;
৩. পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্রভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে অথবা পূর্ববঙ্গের রাজম্ব এখানকার জেলাসমূহের শাসন-ব্যবস্থা ও উন্নয়ন খাতে ব্যয় করতে হবে;
৪. সরকারি চাকরিতে আরো অধিকহারে মুসলমানদের নিয়োগ করতে হবে। এবং পালাক্রমে একজন হিন্দুর পর একজন মুসলমান সদস্য বঙ্গ প্রেসিডেন্সির এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নিয়োগ করতে হবে;
৫. এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে এমন একজন অফিসার থাকতে হবে, যিনি পূর্ববাংলা ও আসামের প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনার ব্যাপারে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;
৬. ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে এমন দু’জন কমিশনার নিয়োগ করতে হবে, যাদের অনুরূপ অভিজ্ঞতা রয়েছে। পূর্ববাংলা ও আসামের মুলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় তত্ত্বাবধানের জন্য একজন যুগ্ম পরিচালক বা সহ-পরিচালক নিয়োগ করতে হবে;
৭. মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা খাতে বিশেষ অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে;
৮. মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
১০.
মুসলিম রাজনীতিতে নবচেতনা
বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলার মুসলমানদের নব অংকুরিত আশা-আকাঙ্ক্ষা স্লান করে দেওয়ার প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তরুল মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে। তারা ব্রিটিশ-রাজের বিরুদ্ধে ‘সক্রিয় কর্মপন্হা’ অবলম্বনের পক্ষে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। বঙ্গভঙ্গের ঘটনা ‘আলোকপ্রাপ্ত’ মুসলিম নেতৃবৃন্দের রাজানুগত্যে ফাটল সৃষ্টি করে। মুসলিম ভারতের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সরকারের ওয়াদাভঙ্গের কারণে সৃষ্ট মনোবেদনা নিয়েও ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করার আহ্বান জানান। সদ্য বিকাশমান দীর্ঘ অবহেলিত মুসলমানদের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতার কথা বিবেচনা করে তাঁরা একদিকে পূর্ণ বিকশিত বর্ণহিন্দু, অন্যদিকে ব্রিটিশ রাজশক্তি- এ দুই প্রবল শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে লিপ্ত হওয়া অসময়েঅচিত বিবেচনা করেন। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের মুখ থেকে আসায় তার বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জে যাওয়া শাসনতান্ত্রিক বিধিবদ্ধতার কারণে তাঁরা ঠিক মনে করেননি। তাই অনন্যোপায় কর্মপন্হা হিসেবে ব্রিটিশ আনুগত্য বজায় রেখেই জাতির দাবি-দাওয়া আদায়ের বলিষ্ঠ পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে অপেক্ষাকৃত তরুণ একদল মুসলিম রাজনীতিক এ সময় ব্রিটিশানুগত্যের উর্ধ্বে উঠে বঙ্গভঙ্গ রদের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্হা গ্রহণের লক্ষ্যে মুসলিম বাংলার জন্য স্বতন্ত্র একটি রাজণৈতিক দল গঠনের মনোভাব ব্যক্ত করতে শুরু করেন।
প্যান-ইসলামবাদী নেতা আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী বঙ্গভঙ্গ রদ সম্পর্কে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেনঃ
“I f we are silent and less vocal, our silence is silence of anger and sorrow and not that of acquiecense, In proportion to our devotion to the person on Throne of His Majesty is the intensity of our resntment at the cowardly device of putting the announcement in the mouth of the King Emperor and muzzling us effectively.” (Matiur Rahman: Fron Consultation to Confrontation. P. 219)
বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্রবীণ ও তরুণ মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে যে দু’টি ধারা সৃষ্টি হয়, নওয়াব সলীমুল্লাহ এই দুই শিবিরের মনোভাবের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। (ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ: নওয়াব সলীমুল্লাহ) ১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ কলকাতায় মুসলিম লীগের অধিবেশনে নওয়াব সলীমুল্লাহর ভাষণ বঙ্গভঙ্গজনিত কারণে সৃষ্ট তাঁর গভীর মর্মবেদনার স্মৃতিচিহ্ন। এরপরই তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর পরিস্থিতির নিরিখে বলা হয়েছিল ‘আত্মনির্ভরতা’ বা Self Reliance- এর কথা। আর এখন বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়া হিসেবে প্যান-ইসলামী ভাবধারায় উদ্বদ্ধ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ‘স্বাধিকার আদায়ে’র বাসনা জোরদার হয়ে ওঠে। ১৯১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর বাঁকিপুরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ কাউন্সিল তার সদ্য প্রণীত গঠনতন্ত্রে স্বায়ত্তশাসনের (Self Government) দাবি অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯১৩ সালের ২২ মার্চ মুসলিম লীগের লাখনৌ অধিবেশনে তা অনুমোদিত হয়। এভাবে বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিক্রিয়ার পথ ধরেই মুসলিম বঙ্গ ও মুসলিম ভারতের রাজনীতি স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী ও নওয়াব সলীমুল্লাহর রাজনীতির ধারা অতিক্রম করে সক্রিয় রাজনীতিতে পদার্পন করে।
রাজনীতি থেকে নওয়াব সলীমুল্লাহর অবসর গ্রহণের পটভূমিতে অপেক্ষাকৃত তরুণ ও সক্রিয়পন্হিগণ মুসলিম বঙ্গে নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্বের হাল ধরলেন। এই তরুল দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সলীমুল্লাহর মানস-পুত্র আবুল কাসেম ফজলুল হক। সলীমুল্লাহর জীবদ্দশাতেই আবুল কাসেম ফজলুলু হক তাঁর যুগপ্রবর্তনের ধারা চিহ্নিত করে ১৯১৩ সালের ৪ এপ্রিল কলকাতার ব্যবস্থাপক সভায় বাজেট বক্তৃতায় প্রবীণ নেতাদের ‘আবেদন-নিবেদনের করজোড়-নীতি’ ভঙ্গ করে বলিষ্ঠ ভাষায় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। মুসলমানদের দাবি-দাওয়া পূরণে বারবার ব্যর্থ হলে ইংরেজ রাজশক্তিকে এজন্য খেসারত দিতে হবে বলে তিনি সাবধান করে দেন। তাঁর এই উক্তি বাংলার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে নতুন যুগের এই নেতার হাতেই বাংলার মুসলিম রাজনীতি এক নতুন রূপ লাভ কর। (J. H. Broomfield : Elite conflict. P-64)
মুসলিম লীগের জন্মঃ নতুন রাজনৈতিক যুগের সূচনা
বঙ্গভঙ্গের ব্যাপক ঘটনা-প্রবাহে কলকাতাকেন্দ্রিক বর্ণহ্দিু সাম্প্রদায়িক শক্তির সাথে ঢাকাকেন্দ্রিক বাঙালি মুসলমানদের যে দ্বন্দ্ব, তার পটভূমি যেমন বিস্তীর্ণ, তাৎপর্যও তেমনি গভীর। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বর্ণহিন্দুদের সাথে যে মানসিক বিচ্ছেদ তা কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না।
ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভাষায়ঃ
“যদিও তারা একই দেশের মানুষ ছিল, তবুও এক ভাষা ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে তারা বিভিন্ন ছিল। ধর্মে, শিক্ষায়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে আটশ’ বছর ধরে তারা বাস করেছে যেন দু’টি ভিন্ন পৃথিবীতে”। (নিরোদচন্দ্র চৌধুরীঃ অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান, পৃষ্ঠা ৫০৪)
মুসলিম শাসনের শুরু থেকে কয়েক শতাব্দী বাংলাদেশের মুসলমান ও হিন্দুগণ, অভিন্ন ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক আবহাওয়ায় নিজেদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস ও জীবনাচরণ পদ্ধতি নিয়ে ধর্মীয় জীবনের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য অর্জনে আপাতদৃষ্টিতে বড় রকমের কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি করেনি। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকালে হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মীয় পার্থক্য তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিস্তার লাভ করে। ব্রিটিশ শাসনকে হিন্দুরা নিছক শাসক-বদলের ঘটনারূপে গ্রহণ করে। ইংরেজদের আস্থা ও অনুগ্রহ লাভের জন্য তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। রাতারাতি তাদের একটি শ্রেণী বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। তারা এই শাসনের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে ‘রানীর বিদ্রোহী প্রজা’ রূপে অভিহিত হয়। সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে পড়ে। হিন্দুরা ইংরেজদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে তাদের বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন পরিচালনা করে। মুসলমানদের সংগ্রামে হিন্দুদের কোন সহানুভূতি ছিল না।
উনিশ শতকের হিন্দু ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মাঝে সাম্প্রয়াদিক স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্র হয়। মুসলমানদের শক্ররূপে চিহ্নিত করে তাদের ওপর তারা নানামুখী হামলা পরিচালনা করে। কুড়ি শতকের শুরুতে প্রশাসনিক কারণে বঙ্গভঙ্গ হওয়ার ফলে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়। তার বিরুদ্ধে হিন্দুদের মারমুখী সংগ্রাম হিন্দু-মুসলিত জাতি-স্বাতন্ত্র্যের দিকটিকে আরো প্রকটভাবে উপস্থিত করে।
বস্তুত ব্রিটিশ শাসনামলের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহ মুসলিম চিন্তা-চেতনায় যে সকল ঘাত-সংঘাত সৃষ্টি করে সে পটভূমিতেই উনিশ শতকের শেষের দিকে মুসলিম রাজনীতি নিজস্ব স্বতন্ত্রধারা রচনায় অগ্রসর হয়। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে সংখ্যালঘু মুসলমানদের জন্য একটি রক্ষাকবচের ব্যবস্থা অর্জন করা ছিল মুসলিম নেতৃবৃন্দের একটি আশু বিবেচ্য বিষয়। সৈয়দ আমীর আলী সর্বপ্রথম তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় মুসলমানদেরকে একটি ‘স্বতন্ত্র জাতি’ (Nationality, Nation) নামে অভিহিত করে তাদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের দাবি করেন। এর আগে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদেরকে ‘কওম’ নামে অভিহিত করলেও আমীর আলীর দাবি ছিল অধিকতর রাজনৈতিক তাৎপর্যমণ্ডিত। ১৮৮৩ সালে আমীল আলী ‘মিউনিসিপ্যালিটি বিলে’ সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। এ সময় থেকেই মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন কায়েমের প্রয়োজনও অনুভূত হচ্ছিল। ১৯০১ সালের অক্টোবরে নওয়াব ওয়াকার উল মূলক লাখনৌতে মুসলমানদের এক ঘরোয়া বৈঠকে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯০৩ সালে সাহারানপুরে একটি মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হয়। ১৯০৬ সালের ফ্রেরুয়ারি মাসে পাঞ্জাবে ফযল-ই-হুসাইন ‘মুসলীম লীগ’ নামে একটি সংগঠন কায়েম করেন।
এ সময় ভারত সচিব লর্ড মর্লি পার্লামেন্টে আভাস দেন যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয় বিবেচনা করছেন। এই নতুন শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার দাবি নিয়ে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক প্রতিনিধি দল আগা খানের নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর সিমলায় বড় লাট মিন্টোর সাথে সাক্ষাত করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে সিমলা ডেপুটেশনে যোগ দেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও আবুল কাসেম ফজুলল হক। তাঁরা নওয়াব সলীমুল্লাহর সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেসী গঠনের খসড়া পরিকল্পনা সাথে নিয়ে যান। একই বছর আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা থেকে বেরিয়ে এসে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের উদাত্ত আহবান জানান।
মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের সলীমুল্লাহর পরিকল্পনা নিয়ে প্রতিনিধিদলের সদস্যগণ সিমলায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন। তাঁরা ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিতব্য শিক্ষা সম্মেলনে কনফেডারেসী বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এরপর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু জমিদার, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রবল আন্দোলনের পটভূমিতে ঢাকায় ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন শেষে সর্বভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিদের এক বিশেষ সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর প্রস্তাবক্রমে ‘অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ’ গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর রবিবার ঢাকার শাহবাগে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের আটশ’ প্রতিনিধির এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করা হয় এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। এভাবেই ভারতীয় মুসলমানগণ একটি নতুন রাজনৈতিক যুগে প্রবেশ করেন। এ রাজনৈতির ভিত্তি হলো জাতিস্বাতন্ত্রভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ।
মুসলমানদের অবিচল ও অব্যাহত দাবির মুখে ১৯০৯ সালের ভারতীয় শাসন-সংস্কার পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থার বিধান রাখা হয়। স্বতন্ত্র নির্বাচন ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতীয়তা স্বীকৃতি লাভ করে। এর ফলে তাদের রাজনৈতিক উন্নতির পথও সুগম হয়।
ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের দাবির কাছে নতি স্বীকার করে ১৯১১ সালের ১১ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর কংগ্রেসপ্রেমিক মুসলমানদের অনেকেই স্বপ্নভঙ্গ হয়। সৈয়দ আমীর আলীর আহ্বানে এ সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দেন। জিন্নাহর চেষ্ঠায় ১৯১৩ সালে ‘ওয়াকফ বিল’ পাস হয় এবং ওয়াকফ সম্পত্তি মুসলমানদের শিক্ষার কাজে নিয়োগের বিধান করা হয়।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাঃ বিজাতীয় প্রতিক্রিয়া
বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে পূর্ববাংলার মুসলিম জন-মানস দারুণভাবে আহত ও ক্ষুব্ধ হয়। প্রতিবাদমুখর মুসলিম নেতৃবৃন্দকে শান্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারি তিন দিনের জন্য ঢাকায় আসেন। ৩১ জানুয়ারি নওয়াব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের এক মুসলিম প্রতিনিধিদল বড়লাটের সাথে দেখা করে একটি মানপত্র প্রদান করেন। মানপত্রে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যায়ল প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করা হয়। এটি ছিল নওয়াব সলীমুল্লাহর একটি পুরনো দাবি। বড় লাট ঢাকার মুসলমান নেতৃবৃন্দের এই দাবি মেনে নিয়ে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করেন এবং এটিকে পূর্ববাংলার জনগণের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে ঘোষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কায়েমের প্রস্তাব প্রকাশ করার সাথে সাথে কলকাতা ও ঢাকার হিন্দু নেতৃবৃন্দ এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধীতা শুরু করেন। তারা বলেনঃ
“এর ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে এবং তাদের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা বেড়ে যাবে। পূর্ববাংলার মুসলমানরা অধিকাংশই কৃষক, তাই তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র থেকে আদৌ কোন উপকার লাভ কতে পারবে না”।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকায়, ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও ফরিদপুরে এবং ১১ ফেব্রুয়ারি মোমেনশাহীতে সভা করেন। ১৬ ফেব্রুয়ারি বর্ধমানের রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সাথে দেখা করে বলেনঃ
“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হবে অভ্যন্তরীণভাবে বঙ্গবিভাগের সমতুল্য; তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক, তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তারা কোন মতেই উপকৃত হবে না”।
৫ ও ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা উকিল লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত দু’টি প্রতিবাদ সভায় সভাপতি ছিলেন বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু। সভা দু’টিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ
“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্সার অবনতী হবে। তাই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন দরকার নেই”।
২৬ মার্চ কলকাতা টাউন হলে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়ঃ
“কোন স্কুল-কলেজের ওপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন অধিকার থাকতে পারবে না এবং পূর্ববঙ্গের কোন বিশেষ শিক্ষা কর্মসূচিও থাকতে পারবে না”।
সিলেটের বিপিনচন্দ্র পাল বলেনঃ
“ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশিক্ষিত ও কৃষকবহুল পূর্ববঙ্গের শিক্ষাদানের কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষানীতি ও মেধার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই থাকবে না”।
পূর্ববাংলার মুসলমানদের যে-কোনও ধরনের কল্যাণ ও উন্নয়নের ব্যাপারে বর্ণহিন্দুদের এরূপ অসহিষ্ণু বিজাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিপত্য ও গুরুত্ব হ্রাস পাবে এবং সেই সাথে এর দ্বারা দীর্ঘ দিনের অবহেলিত মুসলমানদের কল্যাণ হবে, এটাই ছিল বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের আশঙ্কার কারণ। অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে পূর্ববাংলার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই কল্যাণ নিহিত ছিল। কিন্তু হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী আন্দোলনের পটভূমিতে এই নেতৃবৃন্দ এক সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ধারক ছিলেন। তাঁরা ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে হৃদয়ের এতটুকু প্রসারতা দেখাতে পারলেন না। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার সম্পদ লুণ্টন করেই গড়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠেছে কলকাতার সব কিছু। অথচ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে কোন ‘অসাম্প্রদায়িক মানবহিতৈষী’ ব্যক্তিকেই সেদিন এই হিন্দু মানসিকতার বিরুদ্ধে কোন আওয়াজ তুলতে দেখা যায়নি।
১৯১২ সালে ঘোষণা দেওার পর দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন বাস্তব উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বিষয়টি ইম্পোরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে উত্থাপন করন। এরপর ২০ মার্চ তিনি সরকারের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল পাস করার প্রস্তাব পেশ করেন। কাউন্সিল জানায় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার খসড়া বিল তৈরি হয়েছে এবং যুদ্ধের পর যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১৯১৭ সালে এ ব্যাপারে ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন’ গঠন করা হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত ন্যাথনে কমিটির রিপোর্ট উক্ত কমিশনে অনুমোদন লাভের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। ভাইসরয় কাউন্সিলের হিন্দু সদস্যগণ এই কমিশনেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করেন। এত কিছুর মধ্য দিয়ে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো তার কোন এফিলিয়েটিং ক্ষমতা বা কর্তৃত্বই থাকলো না। কলকাতার বর্ণহিন্দু নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটিয়ে নিছক একটি ‘আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে’র মর্যাদা দেওয়া হলো। নওয়াব সলীমুল্লাহর দান করা কয়েকশ’ বিঘা জমির ওপর ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। জুলাই মাসে এখানে ক্লাস চালূ হয়। ১৯৪৭ সালে মুসলমানদের নিজস্ব আবাসভূমিরূপে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসহ পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শেরে বাংলা আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেনঃ
“I was very closely and actively associated with all the plans and schemes and I know the difficulties which we Muslins has to face and the obstinate opposition we had to overcome at the time in pushing the scheme fov the establishment of Dhaka University.”
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বৈঠকেই আবুল কাসেম ফজলুল হক নওয়াব সলীমুল্লাহর প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষ থেকে গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞপন করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে পূর্ববাংলায় উচ্ছশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে পূর্ববাংলায় উচ্চশিক্ষার দ্রুত বিস্তার ঘটে। একটি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উত্থান এই বিশ্ববিদ্যালয়ই ত্বরান্বিত করে। হিন্দু নেতৃবৃন্দ এটিকে ‘মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়’ ও ‘ফাক্কা বিশ্ববিদ্যালয়’ বলে কটাক্ষ করেন। তাদের সকল পরিহাস উপক্ষো করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ই বাংলাদেশের প্রতিভাবান রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, আইনবিদ তৈরির কারখানারূপে বাংলাদেশের রাজনৈতিক আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার মুসলমানদের জাতিসত্তার বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ, গভীর ব্যাপক অবদান রাখে।
১১.
হিন্দু-মুসলিম রাজনীতিঃ মিলমিশেলের চেষ্টা
কংগ্রেসে দাদাভাই নওরেজী ও গোখলের স্থলে বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় ও বিপিন পালের মতো উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটল। ফলে এই দলটি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। বেদ-উপনিষদ থেকে উৎসারিত হিন্দু সংস্কৃতিই ছিল তাদের মতে ভারতীয় জাতীয় চেতনার প্রতীক। গণপতি পূজা তাদের জাতীয় অনুষ্ঠান। বন্দে-মাতরম জাতীয় সংগীত। ফলে মুসলমান নেতাগণ শঙ্কিত ছিলেন যে, ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনই কায়েম হবে। বাংলাদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত্র প্রদেশ ও বালুচিস্তান ছাড়া অন্য সব প্রদেশে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যালঘু। এ অবস্থায় চল্লিশ কোটি মানুষের অখণ্ড ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নয় কোটি মুসলমানের অধিকার ও স্বার্থের জন্য একটা রক্ষাকবচ অর্জন করা ছিল মুসলমান নেতদের বিবেচনায় অপরিহার্য। এ জন্যে তাঁরা প্রদেশগুলোর পূর্ণ স্বায়ত্তশান, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নূন্যতম ক্ষমতা এবং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম সংখ্যালঘু প্রদেশগুলো মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষঅর নিশ্চয়তা দাবি করেন।
লাখনৌ চুক্তি
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ (১৮৭৬-১৯৪৮) ও এ, কে, ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) সহ ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় ১৯১৬ সালে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে একটি শাসনতান্ত্রিক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ‘লাখনৌ চুক্তি’ নামে পরিচিত এই চুক্তিতে মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথা ও আইনসভাগুলোর আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিধান স্বীকৃত হয়। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এই চুক্তির পরিকল্পনার মূল ভিত্তি ছিল। তখন বাংলার লোকসংখ্যার শতকরা ৫৪ জন ছিলেন মুসলমান। সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশের মুসলমানদের অতিরিক্ত আসন দেওয়ার স্বার্থে ফজলুল হকসহ মুসলিম নেতাগণ বাংলাদেশের আইন সভায় মুসলমানদের জন্য মাত্র শতকরা ৪০টি আসন নিতে সম্মত হন। বাকি আসনগুলো বিহার, যুক্ত প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থের জন্য ছেড়ে দেন। পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল শতকরা ৫৫ ভাগ। পাঞ্জাবের মুসলমান নেতাগণ শতকরা ৫০টি আসন রেখে বাকি পাঁচ ভাগ আসন অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ট প্রদেশের মুসলমানদের সুবিধার জন্য ছেড়ে দেন। ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থে বাংলার মুসলমানদের ত্যাগ ছিল এক নযীরবিহীন ঘটনা।
অসহযোগ আন্দোলন
প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হিন্দু-মুসলিম সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র রচিত হয়। রাউলটি বিলের প্রতিবাদে ১৯১৯ সালের এপ্রিলে অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে কয়েকশ লোককে গুলী করে হত্যা করা হয়। এর প্রতিবাদে সারা দেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ফজলুল হক, সিআর দাস, মতিলাল নেহেরু ও তাইয়েবজীকে নিয়ে এ উপলক্ষে এক বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। সে বছরই মাওলানা আবদুল বারীর নেতৃত্বে লাখনৌয়ে তুরস্কের অখন্ডত্ব ও খলীফার মর্যাদা রক্ষার দাবিতে সর্বভারতীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ১৪ নভেম্বর দিল্লীতে ফজলুল হকের সভাপতিত্বে খিলাফত কমিটির প্রথম অধিবেশনে খিলাফত সংক্রান্ত দাবির ভিত্তিতে মুসলমানরা ইংরেজ সরকারের সাথে অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে।
১৯২০ সালের জুন মাসে হিন্দু ও মুসলমান নেতাদের এক সভায় অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। ৩১ আগস্ট মুসলমানরা খিলাফত দিবস পালন করে। সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস, মসুলিম লীগ, খিলাফত কমিটি ও জমিয়াতে উলামায়ে হিন্দ কলকাতায় এক অধিবেশনে মিলিত হয়ে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু অসহযোগ উপলক্ষে গান্ধীর নেতৃত্বে স্কুল-কলেজ বয়কটের যে কর্মসূচির গৃহিত হয়, জিন্নাহ, ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ তার বিরোধিতা করেন। তাঁরা উপলব্ধি করেন যে, শিক্ষায় পশ্চাৎপদ মুসলমানরা এর ফলে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফজলুল হক স্পষ্টতহই ঘোষণা করেন যে, আসহযোগের নামে স্কুল-কলেজ বয়কট করলে শিক্ষায় শত বছর দরে এগিয়ে যাওয়া হিন্দুদের কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মুসলমানরা, যারা নতুন করে মাত্র শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করতে শুরু করেছে, তারা আবার অজ্ঞানতার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। ১৯২০ সালের ১২ ডিসেম্বর সি আর দাস ঢাকার আরমানীটোলা ময়দানে ছাত্রদেরকে স্কুল কলেজ বর্জনের আহ্বান জানান। পরদিনই ফজলুল হক একই ময়দানে সভা করে ছাত্রদেরকে স্কুল-কলেজ বর্জন না করার পরামর্শ দেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোদে আগ্রণী মুসলিম নেতৃবৃন্দও সে সময় উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই ঐক্যবব্ধ আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে মুসলিম জনগণকে দমিয়ে দেওয়ার একটি কারসাজি কাজ করছে।
স্কুল-কলেজ বয়কটের ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে মতান্তরের কারণে ফজলুল হক শেষ পর্যন্ত অসহযোগ কর্মসূচি থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। উগ্রবাদী হিন্দুদের কারণে অসহযোগ আন্দোলে কার্যত মুসলিমবিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয়। নানা স্থানে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ দেখা দেয়। এই সময় হিন্দুদের ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী উত্থান ঘটে। হিন্দুরা ‘শুদ্ধি আন্দোলন’ শুরু করে। তা ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অব্যহত থাকে। অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গান্ধীর হাত থেকে কার্যত সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায়। যুক্ত প্রদেশের চৌরিচৌরায় একটি থানা আক্রমণ ও অগ্নিসংযোগের ফলে ২২ জন পুলিশ মারা যাওয়ার পর গান্ধী হঠাৎ করে অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা করেন।
জিন্নাহ ও ফজলুল হক অসহযোগ আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে শুরু থেকে ভিন্ন ধারণা পোষণ করেছেন এবং তাদের মত ছিল যে, এরূপ কর্মসূচি দেশের মুক্তি ত্বরান্বিত না করে বরং বিলম্বিত করবে। তাদের ধারণা সত্য প্রমাণিত হয়।
বেঙ্গল প্যাক্ট
কংগ্রেসের সাতে মতানৈক্যের কারণে সি আর দাস ১৯২২ সালে সভাপতির পদে ইস্তফা দেন। সি আর দাস ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘স্বরাজ পার্টি’ গঠিত হয়। এই দুই নেতা উপলব্ধি করেন যে, ব্যবস্থাপক পরিষদের হিন্দু-মুসলিম মিলিত সংগ্রাম ছাড়া বাংলার স্বাধিকার অর্জন সম্ভব নয়। এ জন্য তাঁরা দীর্ঘ অবহেলিত মুসলমানদের সঙ্গত অধিকারসমূহের প্রতি কিছু সহানুভূতি দেখানো অপরিহার্য বিবেচনা করেন। এ পটভূমিতেই সি আর দাস তৎকালীন বাংলার অবিসংবাদিত মুসলিম নেতা ফজলুল হক ও সোহরাওয়ার্দীর সাথে ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ নামক রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯২৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর এক সভায় ‘বেঙ্গল প্যাক্ট’ আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। এই চুক্তির সবচে’ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত ছিলঃ
ক. লোকসংখ্যার অনুপাতে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকবে।
খ. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোত প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ষাট ভাগ আসন পাবে।
গ. সরকারি দফতরে মুসলমানদের জন্য শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা চাকরিক্ষেত্রে এই পর্যায়ে উন্নীত না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্য থেকে শতকরা আশি জনকে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ করা হবে। উপরিউক্ত লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত তাদেকে নূন্যতম যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়েঅগ করা হবে। এরপর মুসলমানরা শতকরা ৫৫টি এবং অমুসলমানরা চাকরির শতকরা ৪৫টি পদ পাবে। মধ্যবর্তীকালে হিন্দুদের জন্য শতকরা ২০টি চাকরি বরাদ্দ থাকবে।
ঘ. কোন সম্প্রদায় ধর্মীয় বিষয়ে কোন আইন পাস করতে হলে সেই সম্প্রদায়ের নির্বাচিত তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।
ঙ. মসজিদের সামনে গান-বাজনা সহকারে মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবেহ করার ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা যাবে না।
হিন্দ-মুসলিম মিলনের চেষ্টা ব্যর্থ
১৯২৮ সালের নেহেরু-কমিটির রিপোর্টের মাধ্যমে কংগ্রেস লাখনৌ চুক্তিতে স্বীকৃত মুসলমানদের সকল দাবি অস্বীকার করে। কংগ্রেসের এই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কেল ভিত্তি ধসে পড়ে। জিন্নাহ এরপর ১৯২৯ সালে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য চৌদ্দ দফা দাবি উত্থাপন করেন। কংগ্রেস নেতৃত্ব সে সব দাবি অগ্রাহ্য করেন। ১৯৩০ সাল থেকে শুরু করে লন্ডনে তিন দফা গোলটেবিল বৈঠকেও ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব হয়নি। এরপরও ‘হিন্দু-মুসলিম মিলনের অগ্রদূত’ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেস নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের সাথে তাঁর আলোচনা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৭-৩৮ সালে তিনি গান্ধীর সাথে পত্র বিনিময় করেন। গান্ধী মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিতেই অস্বীকার করেন। জিন্নাহর সাথে পত্রালাপে জওহরলাল নেহেরু হিন্দু-মুসলমান সমস্যা আলোচনায় মুসলিম লীগকে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেন। ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সাথে পত্র বিনিময় করেও সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হন।
এভাবেই হিন্দু-মুসলিম একের পর এক চেষ্টা ব্যর্থ হয়।
১২.
লাহোর প্রস্তাবঃ জাতীয় ইতিহাসের নতুন মাইলফলক
কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে মুসলিম স্বার্থ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা অমূলক বলে উড়িয়ে দেন। কিন্তু কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোতে মুসলমানদের প্রতি অবিচার মুসলিম নেতৃত্বকে বিচলিত করে তোলে। এসব প্রদেশের কংগ্রেস সরকার ওয়ার্ধা শিক্ষা-পরিকল্পনা, বিদ্যামন্দির শিক্ষাব্যবস্থা, বন্দে মাতরম সংগীত, শ্রীপদ্ম প্রতীক এবং হিন্দুয়ানী পাঠ্যপুস্তক চালু করেন। ফলে হিন্দুপ্রতিভাবিত রাজ্যে নিজেদের আদর্শ সম্পর্কে মুসলমানদের স্বপ্রভঙ্গ হয়। মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আওয়াজ ক্রমেই জোরদার হয়ে ওঠে। এ পটভূমিতেই ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ ঐতিহাসিক ‘লাহোর প্রস্তাব’ গ্রহীত হয়। ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ নামে অভিহিত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই ঐতিহাসিক প্রস্তাব উত্থাপনকালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্র আবুল কাসেম ফজলুল হক বলেনঃ
“১৯০৬ সালে বাংলাদেশেই প্রথম মুসলিম লীগের নিশান উত্তোলিত হয়েছিল। এখন বাংলাদেশের নেতা হিসেবে মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকেই মুসলমানদের জন্য আমি আবাসভূমি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করার অধিকার পেয়েছি”।
লাহোর প্রস্তাব গ্রহণের পর পাক-ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মুসলমানদের চিন্তাধারায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়। তাঁরা অখণ্ড ভারতের চিন্তা থেকে দ্রুত সরে আসেন। কংগ্রেস ও হিন্দু নেতাগণ এবং ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগের বিরোধিতা করেন। ফলে মুসলিম লীগ নেতৃত্বকে এ দাবি আদায়ে প্রবল বাধার মোকাবিলা করতে হয়।
মুসলিম লীগের শক্তির উৎস বাংলাদেশ
ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রতিনিধিত্বের দাবি যাচাইয়ের জন্য ১৯৪৫ সালে নভেম্বরে কেন্দ্রীয় আইন সভা এবং ১৯৪৬ সালের মার্চে প্রদেশিক আইন সভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে নিজেদের দাবি প্রমাণ করার লক্ষ্যে মুসলিম লীগ পাকিস্তান দাবির ভিত্তিতে এই নির্বাচনে অংশ নেয়। মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা, শক্তি ও সংহতি এবং স্বতন্ত্র জাতিসত্তার ভিত্তিতে পৃথক আবাসভূমির দাবির প্রতি মুসলমানদের সমর্থন এই নির্বাচনে সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয়। সর্বভারতীয় মানচিত্রে সর্বাধিক মুসলিম জন-অধ্যুষিত বাংলাদেশের মুসলমানগণ এই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করেন যে, এ প্রদেশই ‘মুসলিম লীগের শক্তির প্রধান উৎস’ এবং ‘ভারতীয় মুসলমানদের শক্তির দুর্ভেদ্য দুর্গ’। কেন্দ্রীয় আইন সভার সবক’টি আসনে মুসলিম লীগের প্রার্থীগণ বিজয়ী হন। প্রাদেশিক আইন সভায়ও ১১৯টি আসনের মধ্যে ১১৩ টিতে মুসলিম লীগ প্রার্থগণ জয়ী হন।
নির্বাচনের গণরায়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যেই পাকিস্তান অর্জনের জন্য সর্বাধিক সংহতি ও সংকল্পের এবং অবিচল দৃঢ়তার প্রকাশ ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসবা গঠিত হয়। তখনকার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে এটিই ছিল মুসলিম লীগের একমাত্র মন্ত্রিসভা। বাংলাদেশে মুসলিম লীগের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও তাদের অতুলনীয় সাফল্যের মূলে কাজ করেছে এদেশের জনগণের সামাজিক, সাংস্কৃতিকও ধর্মীয় পটভূমি এবং ইংরেজ ও তাদের প্রসাদভোগী হিন্দু মধ্যশ্রেণীর শোষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত এদেশের কৃষক-প্রজাদের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা। এদেশেই ইংরেজ শাসন সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে এবং শোষকশ্রেণীর সাক্ষাত প্রতিভূ হিসেবে ইংরেজদের চাইতেও তাদের দালাল হিন্দু জমিদারদের সাথেই পুরুষানুক্রমে মুসলমানদের মোকাবিলা হয়েছে। জমিদার ও সুদখোর মহাজনরা প্রায় সবাই ছিল হ্দিু। আর মজলুম কৃষক-প্রজার অধিকাংশই মুসলমান। এই কৃষক-প্রজারা তাদের গর্দানকে জমিদার-মহাজনদের জুলমের জিঞ্জীর থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিল। সেই সাথে জিহাদ ও ফরায়েজী আন্দোলনের ঐতিহ্যে লালিত এই কৃষক-প্রজরা স্বপ্ন দেখেছিল দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত ইসলামী হুকমত।
১৯৩৭ সালে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের সমন্বয়ে প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এর মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানগণ দু’শ বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো শাসন ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার গৌরবময় উপলব্ধি অর্জন করেন। এই শাসনামলে ১৯৩৮ সালে ‘বঙ্গীয় কৃষি খাতক আইন’ পাস হয়। ফলে বাংলাদেশে ষাট হাজার ‘ঋণ সালিশি বোর্ড’ গঠিত হয়। এই বোর্ড মহাজনদের ঋণের দাবি ৯০০ কোটি টাকা থেকে ৬০ কোটিতে নামিয়ে আনে। মহাজনের কবল থেকে কৃষকদের রক্ষার ভবিষ্যত গ্যারান্টিরূপে কুসীদজীবী আইন পাস করে সুদী কারবারের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ১৯৩৮ সালে ‘বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইন’ পাস করে প্রজাদের ওপর জমিদারী স্বেচ্ছাচার বন্ধের ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে কৃষকদের বুকের ওপর থেকে প্রায় দু’শ বছর চেপে থাকা জগদ্দল পাথরগুলো একের পর এক অপসারিত হতে থাকে। মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি এবং সরকারি চাকরিতে তাদের নিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই আমলে অনেকগুলো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। স্ব-শাসনের এই সুফলগুলো বাংলাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংকল্পের পক্ষে ইতিবাচকরূপে কাজ করে।
প্রজা-লীগ মন্ত্রিসভা গঠনের পরপরই এ কে ফজলুল হক মুসলিম লীগে যোগ দেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও সোহরাওয়ার্দী কর্ম-সচিব নিযুক্ত হন। ফজলুল হকের জনপ্রিয়তা ও সোহরাওয়াদীর্র সাংগঠনিক দক্ষতা এবং আলেম সমাজের ব্যাপক সামাজিক যোগাযোগ ও প্রচার অভিযান মুসলিম লীগের প্রতি জনসমর্থনের ব্যাপক গণজোয়ার সৃষ্টি করে। গণজোয়ারের এই উত্তাল তরঙ্গের মুখে হিন্দু ও ইংরেজদের মিলিত প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমিরূপে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি বিশ্ব-মানচিত্রে অস্তিত্ব লাভ করে। গৌরবময় অতীতের আলোকে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত রচনার লক্ষ্যে নিজস্ব জাতিসত্তার বুনিয়াদের ওপর স্বতন্ত্র স্বাধীন আবাসভূমি অর্জনের সুতীব্র প্রেরণাই জনগণকে ব্যাপকভাবে পাকিস্তান ইস্যুতে মুসলিম লীগের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।
লাহোর প্রস্তাব থেকে দিল্লী প্রস্তাব
১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ‘পাকিস্তান’ নামে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল না। লাহোর প্রস্তাবের দু’টি দিক ছিল। এক, উপমহাদেশকে হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগুরু অঞ্চলের ভিত্তিতে বিভক্ত করা, দুই. উপমহাদেশের দক্ষিণ ও পর্বাঞ্চলের মুসলিম এলাকাসমূহের সমন্বয়ে একাধিক পৃথক ও স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন। এই প্রস্তাবের খবর পরিবেশন করতে গিয়ে হিন্দু সংবাদপত্রগুলোই এটাকে ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ নামে উল্লেখ করে। পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ এই নামকরণ মেনে নেয়।
১৯৪৬ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লেজিসলেটর্স কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাব আংশিক সংশোধন করে উপমহাদেশের দুই প্রান্তের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলো নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্তে একটিমাত্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সে সময় উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার বিরুদ্ধে হিন্দু-ব্রিটিশ অশুভ আঁতাতের মোকাবিলায় বৃহত্তর মুসলিম সংহতির প্রয়োজনে এই সংশোধনীর প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এই প্রস্তাবের উত্থাপক।
বঙ্গভঙ্গের দাবি তুলল হিন্দু মহাসভা ও কংগ্রেস
মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিতে অবিচ দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন পারিচালনা করে। এ পটভূমিতে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার নেতাগণ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করার প্রস্তাব করেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও হিন্দু মহাসভার অন্যান্য নেতা ছিলেন বাংলাকে ভাগ করার দাবির প্রথম উত্থাপক। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে এ ব্যাপারে কংগ্রেস মহলও সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে যুক্তিতে তারা অখণ্ড ভারতের দাবিতে সোচ্চার ছিল, বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্ত করার দাবি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাম্প্রদায়িকতা বা দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতার নামেই তারা ভারত-বিভক্ত রোধ করতে চেয়েছিল। আর সেই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধিই তাদেরকে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মত সংকীর্ণ দাবির পথে টেনে নিয়ে গেল।
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কংগ্রেসের বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভক্তির দাবিকে চক্রান্তমূলক বলে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মুসলমানগণ পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, বালুচিস্তান, বাংলাদেশ ও আসাম নিয়ে তাদের আবাসভূমি ও জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের দাবি করেছে। পাঞ্জাব ও বাংলাদেশকে বিভক্ত করা হলে এ নীতিতে অন্যান্য প্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। এ ধরনের বিভাজন প্রদেশগুলোর প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের মূলে আঘাতের শামিল হবে।
বাংলাদেশ বিভাগের জন্য হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসে এই ব্যাপারে মতানৈক্য দেখা দেয়। পশ্চিম বাংলার কংগ্রেস নেতারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশ থেকে আলাদা হয়ে পৃথক প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব করেন। অন্যদিকে পূর্ববাংলার কংগ্রেস নেতারা এ দাবি অযৌক্তিক বিবেচনা করেন। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার হিন্দুদের প্রতিক্রিয়াও এভাবে বিভক্ত ছিল। তফসিলী সম্প্রদায়ের হিন্দুরা অখণ্ড বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে বক্তব্য রাখেন।
বাংলাদেশের ইতিহাসের এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। ১৯০৫ সালে যে হিন্দু নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সারা বাংলার বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালে এসে তাঁরাই হলেন বাংলা বিভাগের অনমনীয় প্রবক্তা। অন্যদিকে ১৯০৫ সালে যে মুসলমান নেতাগণ বঙ্গভঙ্গের কারণে খুশি হয়েছিলেন, তাঁরা ১৯৪৭ সালে ছিলেন বাংলাদেশ বিভাগের বিরুদ্ধে। এর পেছনে যে মনস্তত্ব কাজ করেছিল, সেটিই এদেশের ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।
মুসলিম লীগঃ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা
উপমহাদেশের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্কের পটভূমিতে তখনকার বাংলাদেশের মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অখণ্ডতা বজায় রেখে পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশের মর্যাদা নিয়ে টিকে থাকাকেই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। কিন্তু হিন্দু নেতারা বাংলাদেশকে বিভক্ত করার আন্দোলন শুরু করলে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই অখণ্ড বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রস্তাব করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে দিল্লী প্রস্তাবের উপস্থাপক বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কর্ম-সচিব আবুল হাশিম প্রস্তাব করেন যে, পাকিস্তান কিংবা হিন্দুস্তান কোন রাষ্ট্রেই বাংলাদেশ যোগ দেবে না। এটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে।
বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম নেতাই সে সময়ে এই প্রস্তাবের পক্ষে ছিলেন। রাষ্ট্রীয় আইন সভার স্পীকার নূরুল আমীন ১৯৫৭ সালের ১৬ মার্চ দিনাজপুরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে বলেনঃ
“আমরা স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি। ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে। এই স্বাধীন রাষ্ট্রের নাম পূর্ব-পাকিস্তান হোক অথবা বঙ্গ-আসাম তাতে কিছু আসে যায় না। মুসলমানরা এই স্বাধীন রাষ্ট্র শাসন করবে। আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অথবা কেন্দ্রীয় সরকাররূপী কোন প্রকার সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপস করব না; আমরা আমাদের জন্মগত অধিকারের ওপর কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না”। (ডন, ২৭ মার্চ, ১৯৪৭ ইন্ডিয়ান রেজিস্টারঃ ১ম খণ্ড, ১৯৪৭)
বাংলাদেশের মর্যাদা সম্পর্কে খাজা নাযিমউদ্দীন ১৯৪৭ সালের ২২ এপ্রিল বলেনঃ
“আমর সুচিন্তিত অভিমত এই যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ তার হিন্দু-মুসলমান সকল অধিবাসীর সমস্বার্থের অনুকূল হবে এবং আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যে, বাংলাদেশ বিভক্ত হলে বাঙালিদের মারাত্মক ক্ষতি হবে”। (পূর্বোক্ত)
এর আগে ১৯৪৭ সালের ১৭ মার্চ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ত্রিপুরা জেলার কিষাণপুরে এক জনসভায় বলেন, “মুসলমানরা অবশ্যই বাংলাদেশ পাবে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভক্ত হবে”। তিনি বাংলাদেশ বাগ করার দাবির নিন্দা করে বলেন, “বাংলাদেশ বাঙালিদের এবং এটি অবিভাজ্য”। কিন্তু হিন্দু নেতাদের আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ বিভাগ অনিবার্য হয়ে হড়ার পর তিনি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলার পরিকল্পনা করেন। ৮ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, “আমি সব সময় অখণ্ড বাংলা ও বৃহৎ বাংলার পক্ষপাতি”। তিনি আশা করেন যে, বঙ্গভঙ্গের নতুন উদ্যোক্তরা নিজেদের নাক কাটার আগেই বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারবেন এবং আন্তরিকভাবে মীমাংসায় আসার চেষ্টা করবেন। ২৭ এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন বাংলার পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে সোহরাওয়ার্দী বলেনঃ
“হিন্দুগণ সার্বভৌম অবিভক্ত বাংলা নীতিগতভাবে মেনে নিলে আমি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য বহু দূর পর্যন্ত যেতে রাজি আছি”।
ড. শ্যামাপ্রসাদসহ কয়েকজন হিন্দু নেতা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেন। তার জবাবে সোহরাওয়ার্দী ৭ মে এক বিবৃতিতে মুসলমান ও হিন্দু নেতাদের যুক্ত বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাব করেন।
তিনি এই চমৎকার সুযোগ নষ্ট না করার আবেদন জানিয়ে বলেনঃ
“বাংলাদেশ (অখণ্ডরূপে) স্বাধীন না হলে বাংলার হিন্দুদের বিশেষ মর্যাদা থাকবে না। (ভারতে) তাদের ভাষা ও কৃষ্টি ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং অন্যান্য প্রদেশ বাংলাদেশকে শোষণ করবে”। (ডন, ৯ মে, ১৯৪৭)
সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম ও বগুড়ার মুহাম্মদ আলী ১২ মে সোদপুর আশ্রমে গান্ধীর সাথে দেখা করে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলাদেশ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৪ ও ১৫ মে সোহরাওয়ার্দী জিন্নাহের সাথে দিল্লীতে আলোচনা করেন। তিনি ১৬ মে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ইঙ্গিত দেন যে, অবিভক্ত স্বাধীন বাংলাদেশের পরিকল্পনার প্রতি মুসলিম লীগ হাই কমান্ডের সমর্থন রয়েছে।
এ সময় মওলানা আকরাম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি ও আবুল হাশিম কর্ম সচিব ছিলেন। বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের সাথে আপস মীমাংসার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ কার্যনির্বাহী কমিটিএকটি সাব কমিটি গঠন করে। এই কমিটি কংগ্রেস নেতাদের সাথে কয়েকটি যুক্ত বৈঠকে মিলিত হয়। এরপর সোহরাওয়র্দীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক যুক্ত সভায় দুই দলের এক যুক্ত কমিটি গঠন করা হয়। সোহরাওয়ার্দী, নাযিমউদ্দিন, আবুল হাশিম, ডাঃ এ এম আবদুল মালিক, ফজলুর রহমান ও অপর একজন মুসলিম লীগ নেতা এবং শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শঙ্কর রায় ও অপর চার জন কংগ্রেসের প্রতিনিধি এই যুক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। এই কমিটিকে বাংলাদেশের হিন্দু ও মুসলমানদের গ্রহণযোগ্য একটি শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা রচনার ভার দেওয়া হয়। ২০ মে শরৎ বসুর বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক সভায় যুক্ত কমিটির সদস্যরা একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ২৩ মে শরৎ বসু গান্ধীকে একটি চিঠি লিখে এ চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত করেন।
‘কীটদষ্ট ও সঙ্কুচিত’ পাকিস্তান
কংগ্রেস অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলাদেশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করে। শরৎ বসুকে ৮ জুন লিখিত এক চিঠিতে গান্ধী জানিয়ে দেন যে, তিনি বাংলাদেশ পরিকল্পনার বিষয় নিয়ে নেহেরু ও প্যাটেলের সাথে আলোচনা করেছেন এবং এর প্রতি তাঁদের সম্মতি নেই। গান্ধী শরৎ বসুকে তাঁর পরিকল্পনা ত্যাগ করে বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা হতে বিরত থাকার উপদেশ দেন। এভাবেই স্বাধীন অখণ্ড বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার চেষ্ঠা ব্যর্থ হয়। ভারত বিভাগের সাথে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের ব্যবস্থা করা হয়। ভারতের মুসলিম নেতৃবৃন্দ এক অনন্যোপায় ব্যবস্থা হিসেবে তা মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৪৭ সালের ৯ জুন দিল্লীতে ইম্পেরিয়েল হোটেলে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ পরিষদের সভায় বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের বিভক্তি স্বীকার করে নিয়ে পাকিস্তান-এর পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা আকরাম খাঁ, সোহরাওয়ার্দী, নাজিমউদ্দিন ও আবুল হাশিমসহ বাংলাদেশর ষাট জন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করেন।
মুসলিম লীগ পরিষদের সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ২০ জুন যে বিবৃতি দেন তার এক স্থানে তিনি বলেনঃ
“পশ্চিম বাংলার জনসাধারণকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে, তাদের অধিকার ও স্বার্থ কোর রকমেই বিপন্ন হবে না। মুসলিম জগেত তাদের নিকট থেকে এত বেশী দূরে নয় যে, সেখানে তাদের আওয়াজ পৌঁছবে না এবং সেখান থেকে তাদের কাছে সাহায্য আসবে না”। (ডন, ১১ জুন, ১৯৪৭)
খণ্ডিত বাংলাদেশ ও খণ্ডিত পাঞ্জাব নিয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ভাষায় ‘কীটদষ্ট ও সংকীর্ণ’ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার এই হলো পটভূমি।
ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলায় জাগরণের ধারা
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার জাতীয় জীবন নতুন আশা ও প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। নব-নির্মাণের আনন্দ-উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠেন দেশের কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র-শিক্ষক-কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-গায়ক-শিল্প-ক্রীড়াবিদ তথা সমাজের সকল স্তরের মানুষ। বলা চলে একবারে শূণ্য থেকে শুরু হয় এ নবনির্মানের আয়োজন। দু’শ বছর কলকাতাকেন্দ্রিক ‘টাওয়ার বাংলা’র শোষণ ও লুণ্ঠনক্ষেত্ররূপে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলা একেবারেই নির্জীব হয়ে পড়েছিল। অফিস আদালত, পার্লামেন্ট বসানোর জন্য ভবন নেই। টেবিল-চেয়ার পর্যন্ত নেই। কিন্তু কোন কিছুই দমিয়ে দিতে পারল না সেই প্রেরণা। পিন-আলপিনের বদলে বাবলা কাটাঁয় কাগজ জুড়ে দিয়ে কাজ এগিয়ে চলল।
সাতচল্লিশের আগে ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলায় একটি মাত্রত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতার প্রবল বিরোধিতা মোকাবিলা করে ১৯২১ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হলেও এর কোন এফিলিয়েটিং মর্যাদা ছিল না। এফিলিয়েটিং মর্যাদা না দিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যত পঙ্গু করে রাখা হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই ১৯৪৭ সালের এক সরকারি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ববাংলার সকল কলেজ অধিভুক্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। ফলে পূর্ববাংলার কৃষক-মুসলমান পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার ভরকেন্দ্র রাতারাতি কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।
১৯৫৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬১ সালে মোমেনশাহী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকার প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৭০ সালে জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর সংশ্লিষ্ট দুটি বিভাগের কলেজগুলো যথাক্রমে এই দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল ও মোমেনশাহীতে মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কায়েম হয় ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহীতে। ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার প্রত্যন্ত এলাকায় বহু সংখ্যক স্কুল, কলেজ, মক্তব, মাদরাসা, পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ফলেই পূর্ববাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সময় নবযুগের প্রবর্তন হলো এবং নবচেতনায় জাগরণ ঘটলো।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলকাতা থেকে মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-সঙ্গীতশিল্পীগণ ঢাকায় চলে আসেন। পূর্ববাংলার জীবনপ্রবাহে এ সময় নতুন জাগরণ সৃষ্টি হয়। ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলায় ‘এগ্রিকালচার’- এর সাথে ‘কালচার’ তখন থেকেই সমান তালে পা মিলিয়ে চলতে শুরু করে। ১৯৪৭ সালের আগে বাংলাভাষী অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতি বিকশিত হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সৃষ্ট নগর-কলকাতা ও তার আশপাশের এলাকাকে ঘিরে। দুই শতাব্দীর মধ্যবিত্তের উত্তরাধিকার নিয়ে কলকাতা ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতির এক নতুন বদ্বীপ। নাটকে-উপন্যাসে-সঙ্গীতে-কবিতায় সে ভুবন দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।
আগে শিল্প-অর্থনীতির যা কিছু বিকাশ ঘটেছিল, সবই কলকাতাকে কেন্দ্র করে। এখন ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ববাংলার ‘খামার বাড়ী’তেও গড়ে উঠতে লাগল পাটকল, বস্ত্রকল, চিনিকল, কাগজকলসহ নানা কলকারখানা। স্বর্ণসূত্র নামে অভিহিত পাটের প্রধান উৎপাদক এলাকা হিসেবে গর্বিত পূর্ববাংলায় সাতচল্লিশের আগে একটিও পাটকল ছিল না। পূর্ববাংলার কৃষকরা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক ‘টাওয়ার বাংলা’র পাটকলগুলোর কাঁচামালের যোগানদার। স্বতন্ত্র আবাসভূমি অর্জনের মাধ্যমেই তারা পাটকল প্রতিষ্ঠারও অধিকার অর্জন করল।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরই এখানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্পেরও বিকাশ ঘটল। এ সম্পর্কে শামসুল হক লিখেছেনঃ
“মুদ্রণ ও প্রকাশনাক্ষেত্রে কলকাতা ১৭৮৮ থেকে যে ঐতিহ্য গড়ে তুলেছিল, সে ঐতিহ্য ঢাকার ছিল না। এক্ষেত্রে ঢাকা ছিল প্রায় অবহেলিত। মফস্বল শহরের দীনতার মধ্যে সে যতটুকু নিজেকে সাজাতে পেরেছিল, তার বেশি কিছু ছিল না। ,,,,,,,, যাও বা ছিল, তাদের অনেকেই দেশ বিভাগের পর কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিল। প্রকাশকের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। প্রেসের মতো এরাও পাততাড়ি গুড়িয়ে চলে গেলেন ইন্ডিয়া”। (বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষঃ প্রকাশনা, পৃষ্ঠা ৩৮৭)
এই শূন্যতা পূরণের জন্য মেতে উঠল ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রজন্ম। মুদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হলো নতুন জাগরণ। ফলে কাব্য, উপন্যাস, ছোট গল্প, নাটক, প্রবন্ধ-সাহিত্য, শিশু সাহিত্য, সাময়িকপত্র ও সংবাদপত্র প্রকাশনার ক্ষেত্রে এখানে উন্মোচিত হলো নবযুগের নুতন দিগন্ত। ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ববাংলার মৃত্তিকা-সংলগ্ন কবি-সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জাগরণ ঘটলো এবং তাদের প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটলো সহস্রধারায়। ভাষা আন্দোলনের স্বর্ণ-ফসল বাংলা একাডেমি ও বাংলা উন্নয়ন বোর্ডসহ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার রেনেসাঁ একটি সংহত রূপ লাভ করল।
অন্নদাশংকর রায় ঢাকাকেন্দ্রিক বাংলার এই জাগরণকেই ‘দ্বিতীয় রেনেসা’ বলে উল্লেখ করে লিখেছেনঃ
“এতকাল আমরা যেটাকে বাংলার রেনেসাঁ বলে ঠিক করেছি বা ভুল করেছি, সেটা ছিল অবিভক্ত বাংলার ব্যাপার। পার্টিশনের পর পূর্ববাংলা- এখন তো বাংলাদেশ- নতুন করে জেগে ওঠে। সেখানে দেখা দেয় দ্বিতীয় এক রেনেসাঁস। প্রথম রেনেসাঁসে নায়কদের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন, খ্রিস্টান ছিলেন, কিন্তু মুসলমান ছিলেন না। দ্বিতীয় রেনেসাঁয় নায়করা প্রায় সকলেই মুসলমান। এবার তারা পা মিলিয়ে নিচ্ছেন। প্রথম রেনেসাঁসের ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। দ্বিতীয় রেনেসাঁস হচ্ছে ঢাকাকেন্দ্রিক। এর পূর্বাভাস পূর্বেই সূচিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে”। (বাংলার রেনেসাঁস, ভূমিকা, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৮৪)
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি