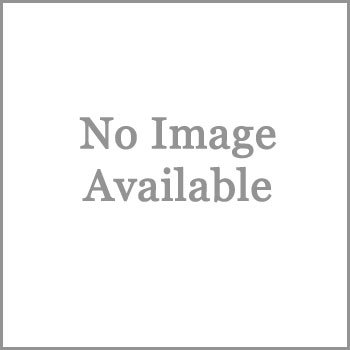ইসলামী হুকুমাতের বিভিন্ন বিভাগ
[তিনটি বিভাগ –আইন প্রণয়ন বিভাগ –মসলিসে শু’রা –শু’রা সদস্যদের যোগ্যতার মান –নির্বাহী বিভাগ –নির্বাহী বিভাগ –নির্বাহঅ সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব –আমর বিল মা’রুফ ও নিহী আনিল মুনকার নির্বাহী সংস্থারই দায়িত্ব –সরকার সংস্থারদায়িত্ব –রাসূলে করীম (স)-এর যুগের প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ –প্রশাসনিক দায়িত্ব নিযুক্ত লোকদের জরুরী গুণাবলী –বিচার বিভাগ –জনগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির কাণ –বিচার বিভাগের লক্ষ্য অর্জনের পন্থা –বিচারকের যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও বিচার কার্যের উপযুক্ততা –অর্থনৈতিকও রাজনৈতিকভাবে বিচারকের স্বাতস্ত্র্য ও স্বাধীনতা –বিচার-নীতির পূর্ণ সংরক্ষণ –সাক্ষ্যদান।
———————————————————————————————————–
তিনটি বিভাগ
দুনিয়ার সাধারণ সরকার সমূহের ন্যায় ইসলামী হুকুমতেও তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে। এই তিনটি বিভাগের ভারসাম্যপূর্ণ সক্রিয়তা ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গড়ে উঠ একটি পূর্ণাঙ্গ সরকার ব্যবস্থা।
এ তিনটি বিভাগেরই প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব দায়দায়িত্ব, ক্ষমতা ও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।
সাধারণত দাবি করা হয়, একটি সরকার ব্যবস্থা এরূপ তিনটি ভাগে বিভক্ত করার কাজটি আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উদ্ভাবন ও অবদান। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বাস্তবতার বিচারে এ দাবি সম্পূর্ণ মূল্যহীন। কেননা আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞান বড়জোর বিগত শতাব্দীর ব্যাপার। কিন্তু দেড় হাজার বছর পূর্বে ইসলাম ইসলামী হুজুমতের সেই প্রথম প্রতিষ্ঠালগ্নেই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীকে এই তিনটি বিভাগে বিভক্ত করেছে। কুরআন মজীদ ও রাসূলের সুন্নাতেই এ বিভক্তি স্পষ্টভাবে বিধৃত।
আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ যে সব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে, দেড় হাজার বছর পূর্বে প্রথম প্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রও প্রায় সেই সব দায়িত্বই পালন করেছে। অবশ্য বলা যেতে পারে, তার প্রেক্ষিত ভিন্নতর ছিল এবঙ তার আয়তনও ছিল সীতিম। রাষ্ট্রসমূহকে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য দায়িত্ব ও জবাবদিহির ভিক্তি যেমন অপরিহার্য, তেমনি তার কার্যকারতার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাথিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য।
প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে এই বিভক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখেই কাজ করতে হয়েছে তার সমগ্র রাষ্ট্রীয় জীবনে।যদিও তার স্বতন্ত্র নামকরণ করা হয়নি এবং সেজন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদে ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরও খোলা হয়নি।
ইসলামী রাষ্ট্রকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের জন্য কার্যাবলীকে অবশ্যই নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করে নিতে হবেঃ
১. আইন বিভাগ
২. নির্বাহী বিভাগ এবং
৩. বিচার বিভাগ
অতঃপর এর প্রত্যেকটি বিভাগ পর্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা যাচ্ছে।
আইন-প্রণয়ন বিভাগ
পূর্বেই চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে যে, ইসলামে আইনদাতা (Law-giver) হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা’আলা। সে আইন তাঁরই মনোনীত প্রতিনিধি রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল হয়েছে। তিনি যে আইন নিজে পালন করেছেন, জনগণকে শুনিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন ও প্রচার করেছেন, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, আল্লাহর নির্দেশ, অনুমতি ও শিক্ষানুযায়ী উপবিধি (By-laws) তৈয়ার করেছেন এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে তা কার্যকর করেছেন, জনগণের উপর জারি করেছেন। কাজেই ইসলামে আইন প্রণয়নের (Legislation) কোন ধারণা নেই। রাসূলে করীম (স) এর যুগে বা কোন অবকাশ নেই। যার প্রয়োজন আছে, তা হচ্ছে, আল্লাহর দেয়া আইন-আদেশকে রাসূলে করীম (স) প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সূক্ষ্ম অধ্যয়ন, অনুবাধন, অনুসরণ ও কার্যকরণ –সমসাময়িক সমাজ পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে।
পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আল্লাহ বা রাসূলের কোন অস্তিত্ব বা কার্যকরতা স্বীকৃত নয়। তাতে মানুষই মানুষের জন্য আইন রচনা করে। তথায় আইন রচনার জন্য যে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়, তা পার্লামেন্ট (Parliament) নামে পরিচিত। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আল্লাহর দেয়া আইন পর্যায়ে মানুষের যতটুকু এবং যা কিছু করণীয়, তা করবার জন্য একটি সংস্থা অবশ্যই গঠিত হবে। ইসলামী পরিভাষা হিসেবে কাজের প্রকৃতির দৃষ্টিতে তার নাম ‘মজলিসে শু’রা’ হওয়াই বাঞ্চনীয়।
কেননা ইসলামী রাষ্ট্রে মৌলিকভাবে কোন আইন প্রণয়নের কাজ নেই। আছে রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাতের আলোকে আল্লাহর আইনসমূহকে সন্ধান করা, ধারাবদ্ধ (Codify বা Codification) করা এবং আইন কার্যককরণের পদ্ধতি ও প্রেক্ষিত রচনা করা। বলা যায়, ইসলামী আইনের কার্যকর হওয়ার চারটি পর্যায়ঃ
১. আইন রচনা –আল্লাহর কাজ;
২. আইন সন্ধান, ধারাবদ্ধকরণ ও প্রেক্ষিত নির্ধারণ –মসলিসে শু’রার কাজ;
৩. আইন কার্যকরকরণ (নির্বাহী পর্যায়ের আইন) –নির্বাহী কর্মকর্তার; এবং
৪. আইনের ভিত্তিতে পারস্পরিক নিষ্পত্তি ও অপরাধীকে দন্ডদান –বিচার বিভাগের কাজ।
কুরআন মজীদের আয়াত ও রাসূলে করীম (স) –এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এ পর্যায়ে আমাদের আলোচ্য মজলিসে শু’রা।
মজলিসে শু’রা
কুরআনের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ দেয়ার, রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মসলিশে শু’রাকেই বহন করতে হবে। অতএব রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচন ও নিয়োগের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে ‘মজলিশে শু’রা’ গঠন। আর এই মজলিস যে মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দানের মাধ্যমেই গঠন করতে হবে –মজলিসে শু’রা গঠনের অপেক্ষা উত্তম পন্থা আর কিচু হতে পারে না –তা অনস্বীকার্য। যদিও শু’রার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পরামর্শদানের দায়িত্ব ও অধিকার দেশের প্রত্যেকটি বয়স্ক নাগরিকেরই। কিন্তু সকলে একত্রিত হয়েই তো আর শু’রার দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই সকলের স্বাধীন-স্বতঃস্ফূর্ত ভোট দানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সঙখ্যক সদস্য সারা দেশ থেকে নির্বাচিত করতে হবে। আর তা করা হলেই আইন নির্ধারণ ও ধারাবদ্ধকরণে জনমতের প্রতিফলন সঙঘটিত হওয়া সম্ভবপর হবে। জনগণ যেহেতু স্বাধীন ও স্বেচ্ছামূলক অধিকারের ভিত্তিতে ইসলামী আদর্শে উত্তীর্ণ ব্যক্তিকেই সর্বাধিক সংখ্যক ভোট দিয়ে মসলিসে শু’রার সদস্য নির্বাচন করবে তাই আশা করা যায় যে, একদিকে নির্বাচিত সদস্যরা মসলিসে জনমতেরই প্রকাশ ঘটাবে এবং অপরদিকে নির্বাচকমন্ডলী তাদের নির্বাচিত শু’রা সদস্যের মতামতের সাথে একাত্ম থাকবে। উপরন্তু তারা নিজেরা যদি কোন বিশেষ বিষয় শু’রার আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজনীয় মনে করে, তাহলে তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে তা খুব সহজেই করতে পারবে।
শু’রা সদস্যদের যোগ্যতার মান
অবশ্য ইসলাম মু’রা সদস্য হওয়ার যোগ্যতার একটা মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং শু’রা সদস্যদের নির্বাচকমন্ডলীকে নির্বাচনকালে সেই মানকে রক্ষা করেই তাদের ভোট প্রয়োগ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, আঞ্চলিকতা বা অন্য কোন বস্তুগত বা বৈষয়িক দিককে কোন রূপ গুরুত্ব দেয়া মজলিসে শু’রা গঠনের মহান উদ্দেশ্য ক্ষুন্ণ ও বিনষ্ট করারই শামিল।শু’রা সদস্য নির্বাচনে ইসলামের ঈমানী ও নৈতিক মান ছাড়াও জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের দিকটিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন জাতীয় লক্ষ্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।
কুরআনের আলোকে মজলিসে শু’রার সদস্যদের অবশ্যই ইসলামী জীবন বিধান ও আইন-কানুন সম্পর্কে পূর্ণ অবিহিত হতে হবে। জনগণের প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠাবান কল্যাণকামী হতে হবে। বিশ্বস্ত, আল্লাহর নিকট জবাবদিহির তীব্র অনুভূতি সম্পন্ন, আমানতদার ও দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা জাতীয় আদর্শ যেমন ব্যাহত হবে, তেমনি ক্ষুণ্ন হবে সার্বিক কল্যাণ এবং সারা দেশে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার এবং জাতি ও রাষ্ট্রের কঠিন বিপদে পড়ে যাওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।
কুরআনের দৃষ্টিতে বেতন বা মজুরীর বিনিময়ে শ্রমিক বা কর্মচারীকে কাজে লাগাতে গেলে সেই মজুরী কর্মচারীকেও শক্তি ও কর্মক্ষমতা সম্পন্ন এবং সর্বোপরি বিশ্বস্ত হওয়া কুরআনের দৃষ্টিতে কাম্য। তাই কুরআনে বলা হয়েছেঃ
(আরবী………………)
তুমি যাকে কোন কাজে মজুরীর বিনিময়ে নিযুক্ত করবে, তার শক্তিশালী ও যোগ্যতা সম্পন্ন এবং অতীব বিশ্বস্ত আমানতদার হওয়াই সর্বোত্তম।
কাজেই রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় মজলিসে শু’রার সদস্যেরও অধিক যোগ্যতা সম্পন্ন ও বিশ্বস্ত হওয়াই ইসলামের দৃষ্টিতে কাম্য।
সবচেয়ে বড় কথা, মজলিসে শু’রার উপর অর্পিত দায়িত্ব হচ্ছে, কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে ইসলামী আইন বের করা ও ধারা হিসেবে সজ্জিত করা। এজন্য শু’রা সদস্যদের –অন্তর তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সঙখ্যক সদস্যদের যে কুরআন-সুন্নাহ পারদর্শী হতে হবে তাতে কোনই সন্দেহের অবকাশ নেই। এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ হচ্ছেঃ
(আরবী………….)
তোমরা নিজেরা যদি না-ই জানো, তাহলে যারা জানে, তাদের নিকট জিজ্ঞাসা কর।
অর্থাৎ যারা জ্ঞানে না তারা যারা জানে তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করে নেবে। এই ‘যারা জানে’ বলতে পূর্ববর্তী আহলি কিতাবের আলিমদের বোঝানো হয়েছে মনে করা যেতে পারে। তবে তা আয়াতটির নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতের দৃষ্টিতেই মাত্র। কিন্তু কুরআনের কোন আয়াতেই যেমন তার নাযিল হওয়ার প্রেক্ষিতের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে না, তেমনি এ আয়াতটিও। তাই এ নির্দেশ সাধারণভাবে একটি স্থায়ী বিধান হিসেবেই গ্রহণীয়।
মজিলেস শু’রা মর্যাদাই হচ্ছে এই যে, তার নিকট যাবতীয় বিষয়ে ইসলামী আইন চাওয়া হচ্ছে। তাকে নিযুক্তই করা হয়েছে জাতীয়, সামষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারাদিতে ইসলামী আইন দেয়ার জন্য। আর ইসলামী আইনের একমাত্র উৰস যেহেতু কুরআন ও সুন্নাহ, তাই শু’রার সদস্যদেরকে কুরআন ও সুন্নাহতে মৌলিকভাবে ইজতিহাদী যোগ্যতা সম্পন্ন জ্ঞানী হতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা দায়িত্ব পালন কোনক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। আয়াতের ‘আহলিয্-যিকর’ অর্থ ‘আহলিল ইলম’–কুরআন সুন্নাহর ইলম এর অধিকারী।
এই পর্যায়ে নিম্নোব্ধৃত আয়াতটিও গভীরভাবে বিবেচনার দাবি রাখে। ইরশাদ হয়েছেঃ
(আরবী………….)
লোকদের নিকট শান্তি বা ভীতির কোন খবর এলেই তারা তা চতুর্দিকে প্রচার করে দেয়। অথচ বিষয়টি যদি রাসূল ও দায়িত্বশীলদের নিকট পৌছিয়েঁ দিত, তাহলে যারা তার নিগূঢ় তত্ত্ব বের করার কাজে নিয়োজিত তারা তার মর্ম জেনে নিত। আর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া যদি তোমাদের উপর না হতো, তাহলে তোমরা অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর সবাই শয়তাদের অনুসরণ করতে।
আয়াতটি যদিও মদীনার সমাজে মুনাফিকদের শত্রুতামূলক কর্মতৎপরতার প্রেক্ষিতে এবং তাদের কাজের দোষ বলা হয়েছে। কিন্তু আয়াতটির মোটামুটি বক্তব্যের মধ্যেই আমাদের আলোচ্য বিষয় পর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব নিহিত রয়েছে।
তা হচ্ছে, মুসলিম সমাজের সম্মুখে শাস্তি বা সুখের কোন খবর এলেই তা নিজ থেকে প্রচার করতে শুরু করে না দিয়ে বরং বিষয়টি রাসূলে করীম (স) ও তাঁর নিয়োজিত বিভিন্ন ব্যক্তির কারোর নিকট পৌছিয়েঁ দেয়াই কর্তব্য। তাহলে সেই খবরের মধ্যে নিহিত সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাঁরা বের করতে সক্ষম হতেন।
আয়াতে ব্যবহৃত (আরবী………..) থেকেই (আরবী………) শব্দটি এসেছে এবং তার অর্থ গবেষণা করে নিগূঢ় তত্ত্ব বের করা। ইসলামী আইন জানার জন্য এই ‘ইস্তিনবাত’–নিগূঢ় তত্ত্ব বের করার পদ্ধতি গ্রহণ অপরিহার্য। আর তা সম্ভব কেবলমাত্র সেই লোকদের পক্ষে, যারা ইসলামী জ্ঞান-গবেষণায় বিশেষ পারদর্শী, যার কুরআন-হাদীস-রাসূলে করীম (স)-এর জীবনের ঘটনাবলীর উত্থান-পতন, চড়াই-উতরাই ও আবর্তন-রিবর্তন সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী এবং যারা আইনের প্রকৃতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষ ওয়াকিফহাল। রাসূলে করীম (স) কুরআন ও সুন্নাতের শিক্ষাদানের মাধ্যমে এ কাজের যোগ্যতা সম্পন্ন বিপুল সংখ্যক লোক তৈরী করেছিলেন। রাসূলে করীম (স)-এর সময়ে ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন দিকে এবং কাফিরদের সাথে যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এ ধরনের যোগ্যতা সম্পন্ন যথেষ্ট সঙখ্যক লোক থাকতে হবে, যারা কুরআন-সুন্নাহ্ সামনে নিয়ে গভীর সূক্ষ্ম গবেষণা চালিয়ে প্রয়োজনীয আইন বের (আরবী…………) করতে সক্ষম।
সাইয়েদ কুতুব শহীদ এই আয়াতাংশের তাফসীর লিখেছেনঃ
(আরবী…………..)
অন্যথায় নিত্য পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় নিত্যনব সংঘটিত ঘটনা ও ব্যাপারাদিতে ইসলামসম্মত আইন ধারাবদ্ধ করা মজলিসে শু’রার পক্ষে সম্ভব হবে না।
এ কারণে আল্লাহ তা’আলা প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে অন্তত কিছু সংখ্যক লোককে উচ্চতর দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের জন্য বের হয়ে আসবার –প্রয়োজন হলে বিদেশে গমন করার জন্য উৎসাহিত করেছেন। বলেছেনঃ
(আরবী……………………)
জনগণের মধ্যের প্রত্যেকটি গোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক কেন বের হয়ে যায় না দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে এবং এই উদ্দেশ্যে যে, তারা ফিরে এসে তাদরকে সতর্ক করবে? তাহলে আশা করা যায় যে, তারা সতর্ক হবে।
জনগণকে দ্বীনি বিষয়াদি দিয়ে সাবধান করার জন্য দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান প্রথমেই অর্জন করতে হবে। তাহলেই তারা এই সাবধান করা কাজটি যোগ্যতা সহকারে করতে পারবে এবং তাদের এ সাবধান বাণী শুনে জনগণ হেদায়েত লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যায়।
মজলিসে শু’রাকে যেহেতু কুরআন-সুন্নাহর আইন বের করতে হবে ও তার ভিত্তিতে গোটা দেশ, রাষ্ট্র ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে, তাই কুরআন-সুন্নাহতে বিশেষ পারদর্শিতা সম্পন্ন লোক তাতে অবশ্যই থাকতে হবে। সুনানে আবু দাউদ-এ এই হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে। রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ
(আরবী…………..)
তোমরা কুরআন সুন্নাহতে পারবর্দী মু’মিন লোকদের একত্রিত কর। অতঃপর তাদের সমন্বয়ে শু’রা গঠন কর। তবে তাদের কোন একজনের মতের ভিত্তিতে কোন সিদ্ধান্ত করে ফেলবে না।
একজনের মতে সিদ্ধান্ত করে ফেলতে নিষেধ করার অর্থ, প্রত্যেকটি বিষয়ে শু’রার অধিবেশনে বিস্তারিতভাবে আলোচন-পর্যালোচনা করে –প্রত্যেক সদস্যকে তাতে অংশ গ্রহণ ও মত প্রকাশের –ভিন্নমতের –সমালোচনা করার ও তার ক্রটি দেখাবার অবাধ সুযোগ দেয়ার পর এমনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে যা, সর্ববাদীসম্মত –অন্ততঃ বেশী সংখ্যক লোকের মতের ভিত্তিক হবে।
নির্বাহী বিভাগ (Executive)
মজলিসে শু’রা বা পার্লামেন্ট ধারাবদ্ধ আইন পাস হয়ে যাওয়ার পর আধুনিক নিয়মে তাতে রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর হতে হয়। তা না হওয়া পর্যন্ত কোন আইন ‘আইন’ নাম অভিহিত ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনা মাধ্যমে কার্যকর হতে পারে না। রাষ্ট্রপ্রধানের স্বাক্ষর হওয়ার পরই নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বারা সারাদেশে তা কার্যকর হবে। তাই নির্বাহী বিভাগ বা আইন-প্রয়োগকারী “অথোরিটি”(Authority) আধুনিক কালের প্রত্যেকটি সরকার প্রতিষ্ঠানের একটি অপরিহার্য এবং সম্ভবত সবচাইতে বেশী গুরুত্বসম্পন্ন বিভাগ।
আধুনিক কালের প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার হলে প্রেসিডেন্ট ও তার মন্ত্রীসভা (Cabinet), আর পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার হলে প্রধান মন্ত্রী ও তার মন্ত্রীদের সমন্বয়েই এ নির্বাহী যন্ত্র গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে প্রাদেশিক কর্মকর্তা আর ‘ইউনিটারী সরকার’ হলে বিভাগীয ও জিলা –প্রভৃতি প্রশাসনিক বিভাগসমূহের কর্মকর্তারা নির্বাহী সরকার যন্ত্রের বিভিন্ন অংশ। আর বাস্তবতার দৃষ্টিতে এ সরকারই হয়ে থাকে একটি দেশের শাসক ও প্রশাসক।
নির্বাহী সরকারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
বস্তুত আল্লাহর কুরআন ও রাসূলে করীম (স)-এর সুন্নাত মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ও ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবভাবে প্রয়োগ ও অনুসরণের জন্য। মজিলসে শু’রা যে চিন্তা-গবেষণা –‘ইস্তিনবাত’ করে, পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনা করে যে আইনসমূহ ধারাবদ্ধ করে দিয়েছে, তারও চরম লক্ষ্য তাই। এই কারণে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের প্রয়োগ ক্ষমতার অধিকারী একটা যন্ত্র এই আইনসমূহ যথাযথভাবে কার্যকরকরণের জন্য অবশ্যই দায়িত্ব থাকতে হবে। অন্যথায় সব কিচুই নিস্ফল ও অর্থহীন।
আইনকে অন্ধ নির্বিচার রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে শুধু জারি করাই তো একমাত্র কাজ নয়, ইসলামের দিক দিয়ে আসল লক্ষ্য হচ্ছে, সে আইনের ভিত্তিতে ব্যক্তি সমাজ ও পরিবার গঠন এবং লালন। সে জন্য পূর্ণ সতর্কতা, সহনশীলতা, দৈর্য ও ক্ষমাশীলতার সাথে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। তাহলেই সেই আদর্শ ব্যক্তি, আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে, যা গড়ার জন্য দুনিয়ায় ইসলামের আগমন। এরূপ গঠনমূলক কাজের গুরুত্ব অনুধাবন করাবার জন্যই আল্লাহ্ তা’আলা কুরআন মজীদে ইরশাদ করেছেনঃ
(আরবী………..)
সমস্ত মানুষ নিঃসন্দেহে চরম ধ্বংস ও বিরাট ক্ষতির মধ্যে নিপতিত। তা থেকে রক্ষা পেতে পারে কেবল তরাই, যারা ঈমান এনেছে, নেক আমল করেছে, পরম সত্য ও কল্যাণের উপদেশ ও পরামর্শ একজন অপরজনকে দিয়েছে এবং দ্বীন পালনে দৈর্য ধারণের জন্য পরস্পরকে উৎসাহিত করেছে।
বস্তুত ইসলাম যেমন ব্যক্তির অন্তর দিয়ে ঈমান আনার ব্যাপার, তেমনি ব্যক্তির নিজের জীবনে ও কমের্ তা পালন করার ব্যাপার। কিন্তু ইসলাম শুধু এতটুকু-ও নয় –তা প্রশাসনিক আইন-ও। অতএব তা সরকারের প্রশাসনিক যন্ত্রের বলে অবশ্যই কার্যকর হতে হবে। আর এ কাজের জন্য প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ প্রত্যক্ষভাবে দায়ী। আল্লাহর আইন জারি ও যথাযথভাবে কার্যকরকরণে কোনরূপ অনীহা উপেক্ষা বা দুর্বলতা দেখাবার অধিকার কারোরই থাকতে পারে না। বরং এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক যন্ত্রকে অত্যন্ত শক্ত ও অনমনীয় হতে হবে। কুরআন মজীদে এই শক্তিকেই ‘লৌহ’ (Iron) বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছেঃ
(আরবী…………)
নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের রাসূলগণকে পাঠিয়েছি অকাট্য দলীল প্রমাণ সহকারে এবং তাদের সঙ্গে কিতাব ও মানদন্ড নাযিল করেছি, যেন জনগণ ইনসাফের উপর প্রতিষ্টিত হতে পারে। আর নাযিল করেছি লৌহ। তাতে বিপুল শক্তি যেমন নিহিত, তেমনি জনগণের জন্য অশেষ কল্যাণও।
আয়াতে ‘আল-হাদীদ’‘লৌহ’ বলে প্রশাসনিক শক্তিকেই বুঝিয়েছে, যার কাজ হচ্ছে আল্লাহর কিতাব –আইনকে মানদন্ডের ভারসাম্য সহকারে জারি করা। এ আইন জারি করার শক্তি যেমন ‘লৌহ’-এর ন্যায় অনমনীয়, তেমনি তা জারির ক্ষেত্রে বাস্তবভাবে সেই অনমনীযতা অবশ্যই অবলম্বনীয়। এ ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র দুর্বলতা দেকানো কুরআনের ভাষায় প্রশাসনিক শক্তিকে ‘লৌহ’ বলার পক্ষে চরম অবমাননাকর। ‘লৌহ’ স্বভাবতই অমোঘ। তাই তাকেই এ ব্যাপারে সেই অমোঘতাই রক্ষা করতে হবে।
প্রশাসনিক দুর্বলতা গোটা রাষ্ট্রকেই দুর্বল করে। জনগনের মনে রাষ্ট্র শক্তির প্রতি আনুগত্যমূরক ভাবদারা নিঃশেষ করে দেয়। এ কারণে আল্লাহর আইন জারি ও কার্যকরকরণের একবিন্দু নম্রতা, দুর্বলতা কিংবা দয়া-সহানুভূতি প্রদর্শন তো দূরের কথা –তার উদ্রেক হওয়াও কুরআনের স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। ব্যভিচারীদ্বয়ের দন্ড কার্যকর প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছেঃ
(আরবী…………)
সেই দুইজনকে আল্লাহর আইনের দন্ড দানের ব্যাপারে তোমাদেরকে যেন কোনরূপ দয়া-অনুগ্রহ পেয়ে না বসে –যদিও তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হও।
এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রশাসনিক শক্তিকে আল্লাহর আইন জারি করতে হবে এবং আল্লাহর আইন জারি ও কার্যকরকরণে কোন রূপ দয়া প্রদর্শন করা যাবে না, দয়ার উদ্রেক হওয়া ঈমানের পরিপন্থী। দয়া দেখানো হলে প্রমাণিত হবে যে, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান নেই। কেননা তা থাকলে এক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শন বা এ ব্যাপারে তাদের ম নে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক হওয়াও সম্ভব হতো না।
প্রশাসনিক কর্মদক্ষতার প্রতীক ছিলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। তিনি যেমন আল্লাহর আইন কার্যকরকরণের কোনরূপ দুর্বলতা দেখান নি, তেমনি সে ক্ষেত্রে তিনি কোনরূপ সুপারিশ গ্রহণ করতেও স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করেছেন। শুধু অস্বীকার নয়, আল্লাহর আইন জারি করার ব্যাপারে সুপারিশের কথা শুনে তীব্র ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন।
মাখজুমী বংশের একটি মেয়েলোক চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হয়। রাসূলে করীম (স)-এর অত্যন্ত প্রিয় ব্যক্তি উসামা ইবনে জায়দ (রা) –তাঁর নিকট দন্ডদানের ব্যাপারে সুপারিশ করার ইচ্ছা করেছিলেন। নবী করীম (স) তাঁর কথা শুনে অত্যন্ত ধমকের সুরে বললেনঃ
(আরবী…………..)
আল্লাহ ঘোষিত একটি দন্ড কার্যকরকরণের ক্ষেত্রে তুমি সুপারিশ করছ?
অতঃপর তিনি মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বললেনঃ
(আরবী…………..)
হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু এই কারণে যে, তাদের মধ্য থেকে কোন অভিজাত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে তারা অব্যাহতি দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর দন্ড কার্যকর করত।
আল্লাহর নির্দেশঃ
(আরবী…………)
তোমাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক অবশ্য অবশ্যই এই কাজে নিযুক্ত ও রত থাকতে হবে, যারা সব সময় কল্যাণের দিকে আহবান জানাবেন, শরীয়াতসম্মত কাজ করার আদেশ করতে ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে লোকদেরকে বিরত রাখতে থাকবে।
বস্তুত এ আয়াতে যে কাজের কথা বলা হয়েছে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক সংস্থার দাযিত্বই হচ্ছে সেই কাজ করা। শরীয়াতসম্মত কাজের আদেশ ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ থেকে বিরত রাখার দায়িত্ব সরকারের এ বিভাগ-ই পালন করবে।
আল্লাহর আইন-বিধান প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সমাজের উপর কার্যকর করতে হবে। ‘হদ্দ’ সমূহ জারি করতে হবে। এ কাজ যেমন একান্ত জরুরী, তেমনি তা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই –নির্বাহী শক্তির সাহায্যেই আঞ্জাম দিতে হবে। এ কাজের দায়িত্ব তো আর সাধারণ মানুষের উপর ছেড়ে দেয়া যায় না, সাধারণ মানুষকে কোন প্রকারেই সুযোগ দেয়া যায় না আইন হাতে লওয়ার। অন্যথায় চরম অরাজকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয়া অবধারিত। মানুষের উপর নির্বিচার জুলুম হওয়া, মানুষের মর্যাদা বিনষ্ট হওয়া এবং মানুষের মানবিক অধিকারও হরণ হওয়া নিশ্চিত। রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও নির্বাহী সংস্থা এ জন্যই একটি অপরিহাযর্ বিভাগ। এই বিভাগটিই হবে এ কাজের একমাত্র দায়িত্ব ও কর্তৃত্বশীল।
বড়ই আশ্চর্যের ব্যাপার, ইসলামের রাষ্ট্রীয় বিধানে এই ব্যবস্থা একেবারে শুরু থেকে উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও পশ্চাত্যের কোন স্বঘোষিত কোন প্রাচ্যবিদ (Orientals) হওয়ার দাবিদার ইসলামের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ তুলবার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে যে, ইসলাম শুধু ওয়ায-নসীহতের বিধান দেয়, তাতে প্রশাসনিক নির্বাহী সংস্থা (Executive) বলতে কিছু নেই। আর সেই কারণে ইসলাম রাষ্ট্রীয় বিধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।
আমরা বলব, এহেন স্বঘোষিত প্রাচ্যবিদ ইসলামী জীবন বিধান ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার পূর্ণাঙ্গ রূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ ও মূর্খ। তারা যদি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাত অধ্যয়ন করত, তাহলে তাদের মনে একটা মারাত্মক ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারত না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ তোলা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হতো না। আমাদের স্পষ্ট দাবিই হচ্ছে, ইসলাম পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র ব্যবস্থা –তার প্রয়োজনীয সব সংস্থা অবকাটামো পুরাপুরিভাবে উপস্থাপিত করেছে, তার কোথাও একবিন্দু ফাঁক নেই।
ইসলামে স্পষ্টভাবেই প্রশাসনিক সংস্থা –নির্বাহী ব্যবস্থা, বিচার বিভাগ ও আইন নির্ধারক মজলিসে শু’রা –আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান উপস্থাপিত এ তিনটি বিভাগই পুরাপুরি বর্তমান। কেননা ইসলামী আদর্শ তো সর্বতোভাবে বাস্তবায়িত হওয়ার বিধান। আর তা এ বিভাগসমূহের সক্রিয়তার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য যে কল্যাণ নিয়ে এসেছে, তা এসব বিভাগ ও সংস্থার পূর্ণাঙ্গ কার্যকরতার মাধ্যমেই তো জনগণের নিকট পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারে।
উপরন্তু কুরআন মজীদের উপরোদ্ধৃত আয়াতে যে ‘আল্-তাকুম-মিনকুম উম্মাতুন’‘তোমাদের মধ্যে এমন লোক সমষ্টি অবশ্যই থাকতে হবে’ বলে যে ‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’–ন্যায় ও আইনসম্মত কার্যাবলীর কার্যকর করা ও আইন বিরোধী কার্যবলী করতে ও হতে না দেয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, তা তো এই প্রশাসনিক সংস্থার মাধ্যমেই বাস্তবায়িত হতে পারে।
‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’ নির্বাহী সংস্থারই দায়িত্ব
সূক্ষ্ম দৃষ্টিমান ব্যক্তিবর্গ অবশ্যই দেখবেন এবং স্বীকার করবেন যে, ‘আমর বিল’মা’রূফ’ ও ‘নিহী’ আনিল মুনকার’-এর নিয়মাবলী, তার সমস্যা ও শর্তসমূহ পূরণের জন্য একটি সংস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। এই সংস্থাই হচ্ছে কার্যত ইসলামী রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ (Executive Department)। ইসলামের আইনসমূহ বলবৎ করা, প্রয়োগ করা (Enforced)- এর জন্য দাযিত্বশীল। আইন বিভাগ কর্তৃক সাব্যস্ত করা আইন ও বিচার বিভাগের রায়সমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করা এই সংস্থাটি ব্যতীত কখনই সম্ভব হতে পারে না। আর তা হতে না পারলে দ্বীন-ইসলামের গোটা ব্যবস্থাই অর্থহীন, নিষ্ফল, অকার্যকর এবং অবাস্তব। তাই ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজে আল্লাহর আইনসমূহ কার্যকর করার পূর্ণ দায়িত্ব এ বিভাগটির উপর অর্পিত।
বস্তুত এ দায়িত্বটি মূলত ইসলাম কর্তৃক উদ্ভাবিত ও প্রবর্তিত। এ এক অভিনব ও মৌলিক ব্যবস্থা। ইসলাম পূর্বকালীন মানব রচিত বিধান-ব্যবস্থায় এর কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। জনগণের মধ্যে কল্যাণের ও ভালো ভালো কাজের ব্যাপক প্রচলন করার দাযিত্ব ইসলাম জনগণের উপর অর্পণ করেছে। মানুষকে সমস্ত প্রকারের আইন-বিরোধী অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে বিরত রাখার কাজ-ও সেই-জনগণকেই আঞ্জাম দিতে হবে। সমাজে কি হচ্ছে –ভালো কি মন্দা, ক্ষতিকর কি কল্যাণকর, আইন পালন কিংবা আইন লংঘন –সে দিকে জনগণকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। জনগণ এ ব্যাপারে নির্বাক-নিষ্ক্রিয় ও আত্মকেন্দ্রিক হয়ে কিছুতেই থাকতে পারে না।
দ্বীন-ইসলাম এই বিষয়টিকে সমাজ-দর্শন পর্যায়ে পণ্য করে তারই ভিত্তিতে এ দায়িত্বের কথা বলেছে। ইসলামের সমাজ-দর্শন হচ্ছে –মানুষ সমাজেরই একটি অংশ ও অঙ্গ। সমাজ বিচ্ছিন্ন মানব জীবন অকল্পনীয়। একই পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের পরিণতি অভিন্ন হতে বাধ্য। সমাজের কোথাও যদি কল্যাণ কিছু থাকে, তবে সে কল্যাণ গোটা সমাজেই পরিব্যাপ্ত হবে। কল্যাণকারী সেই এক ব্যক্তির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকবে না। পক্ষান্তরে সমাজে যদি মন্দ থাকে, তা হলে সমাজের একটি ব্যক্তিও সে মন্দ ও অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেতে পারে না, তার প্রবাব সেই মন্দকারী পর্যন্ত সীমিত হয়ে থাকতে পারে না। এ কারণে সমাজের ব্যক্তিগণের মন-মানসিকতা ও আচরণ চরিত্র অভিন্ন হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে একান্তই বাঞ্চনীয়। গোটা জনসমষ্টির সামগ্রিক কল্যাণের জন্যই ব্যক্তিদের থাকতে হবে মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা।
নবী করীম (স) এই ব্যাপারটির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং তিনি এ বিষয়ের সূক্ষ জটিলতাকে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটি সমাজের লোক স মুদ্রগামী এক জাহাজের আরোহীদের মত। এই জাহাজ যদি কোন বিপদে পড়ে তা হলে সে বিপদ কোন একজন আরোহীর জন্যই হবে না, জাহাজের সমস্ত আরোহীর জন্যই হবে সে বিপদ। এই অবস্থায় আরোহীদের কোন একজনকে যদি সেই জাহাজের তলদেশ ছিদ্র করার সুযোগ দেয়া হয়, তাহলে গোটা জাহাজই ডুবে যাবে। নিমজ্জিত হবে সমস্ত আরোহী। একই সমাজের লোকদের অভিন্ন পরিণতির এ এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।
সমাজের কোন ব্যক্তি যদি সঙক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে তাহলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোর কোন অধিকারই তার থাকা উচিত নয়। কেননা তাহলে সমাজের অন্যান্য মানুষেরও সেই রোগে আক্রান্ত হওয়ার অনেক বেশী আশঙ্কা। কাজেই সমাজ-সমষ্টির সার্বিক কল্যাণের দৃষ্টিতেও তার গতিবিধকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, তাকে অন্য লোকদের সংস্পর্শ হতে অবশ্যই দূরে রাখতে হবে।
এ সব দৃষ্টান্তের আলোকে ‘আমর বিল’মা’রূপ ও নিহী আনিল মুনকার’ কথাটির গভীর তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় এবং তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। অতএব সমাজে বেশী বেশী কল্যাণের ব্যাপক প্রসারতা বিধান এবঙ বেশী বেশী অন্যায় প্রতিরোধের শক্তিশালী ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। দ্বীন-ইসলামের কার্যকরতা ও আল্লাহ্ অর্পিত দায়িত্ব পালনের অব্যাহত ধারাবাহিকতার জন্য ‘আমর বিল মা’রূফ ও নিহী আনিল মুনকার’-এর দায়িত্বশীল সংস্থার অপরিহার্যতা একান্তই অনস্বীকার্য।
এই কারণে কুরআন মজীদ ও সুন্নাতে রাসূলে এ বিষয়ের উপর খুব বেশী গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। অবশ্য একটি আয়াত এর বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হওয়ার কারণ হতে পারত –যদি সঙ্গে সঙ্গেই তার ভুল ব্যাখ্যার পথ বন্ধ করে দেয়া না হতো। আয়াতটি এইঃ
(আরবী………………..)
হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা নিজেদেরই কথা চিন্তু কর, অপর কেউ যদি পথভ্রষ্ট হয়ও তা হলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না যদি তোমরা নিজেরা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ে তাকতে পার। তোমাদের সকলকেই আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন তোমরা দুনিয়ায় কি কি কাজ করছিলে।
আয়াতটির বাহ্যিক অর্থ এই হয় যে, ব্যক্তি নিজে যদি ইসলামের উপর অবিচল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে ‘আমর বিল মা’রূফ ও নিহী আনিল মুনকার’ করার কোন দায়িত্বই তার উপর থাকবে না, সে সেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবে। তা না করলে তাকে পাকড়াও করা হবে না, তাকে সেজন্য জবাবদিহিও করতে হবে না।
কিন্তু এ অর্থ ঠিক নয়। আল্লাহর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং তা যে আল্লাহর মূল বক্তব্যের বিপরীত তা হাদীস থেকেই নিঃসন্দেহে জানা যায়। তাই প্রসঙ্গত বলা যায়, কুরআনের নির্ভুল ব্যাখ্যা হাদীসের আলোকেই পেতে হবে। হাদীসকে বাদ দিয়ে কুরআনের সঠিক-নির্ভুল তাফসীর করা বা জানা সম্ভব নয়।
আবূ দাউদ ও তিরমিযী প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা) ভাষণ প্রসঙ্গে বললেনঃ ‘তোমরা কুরআনের এ আয়াতটি পাট কর’; কিন্তু তার অর্থ মূল ব্কতব্যের বিপরীত গ্রহন কর। আমি রাসূলে করীম (স)-কে বলতে শুনেছিঃ
(আরবী…………)
লোকেরা যখন জালিমকে জুলুম করতে দেখে, তখন যদি তারা সেই জারিমকে না ধরে ও জুলুম থেকে বিরত না রাখে, তাহলে খুবই আশঙ্কা রয়েছে, আল্লাহ্ তাঁর নিকট থেকে পাঠানো আযাবে তাদের সকলকেই গ্রাস করবেন।
আবূ ঈসা তিরমিযী এ হাদীসটি উদ্ধৃত করে লিখেছেনঃ
(আরবী………..)
এ হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে উত্তম ও সহীহ।১
(আরবী……………..)
উক্ত আয়াতের তাফসীরে সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। সে আলোচনার সারনির্যাস আমরা এখানে তুলে দিচ্ছিঃ
এ আয়াতটি মুসলিম উম্মত ও অমুসলিম কাফির সমাজের মধ্যে দায়িত্বশীলতার দিক দিয়ে পার্থক্য রচনাকারী। সেই সাথে মুসলিম জনগণের পরস্পরের প্রতি কল্যাণ কামনা ও অসীয়ত-নসীহতের দায়-দায়িত্বের কথা ঘোষণাকারী। কেননা তারা সকলে মিলে এক অভিন্ন উম্মত।
আয়াতের প্রথম অংশের বক্তব্য হচ্ছে, মুসলমানরা অন্যদের থেকে ভিন্নতর এক জনসমষ্টি। তারা নিজেরা পরস্পরের প্রতি কঠিন দায়িত্বশীল। অতএব তোমরা নিজেরা নিজেদের সকলের সম্পর্কে অবশ্য চিন্তু-ভাবনা করতে বাধ্য তোমাদের সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে হবে, পরস্পরের প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে তা পালন করতে হবে। অবশ্য অন্যরা –মুসলিম সমাজ বহির্ভূত লোকেরা –যদি পথভ্রষ্ট হয়ে যায়, আর তোমরা হেদায়েতের পথে অবিচল থাক, তাহলে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। অন্য লোকদের গুমরাহীর কোন শাস্তি তোমাদের ভোগ করতে হবে না –যদি তোমরা নিজেরা ঠিক থাক। এদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, হতে পারে না কোনরূপ বন্ধুত্ব।
এ অর্থে মুসলিম উম্মত ও অন্যান্য মুসলিম জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের রূপ নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে। মুসলিম উম্মত হিজবুল্লাহ –আল্লাহর দল, আর অন্যরা শয়তানের দল। এ দুয়ের মাঝে আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে কোনই একাত্মতা ও অভিন্নতা হতে পারে না।
এর অর্থ হল মুসলিম উম্মতের সদস্যদের পরস্পরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হতে হবে, পরস্পরের প্রতি কঠিন দায়িত্বও পালন করতে হবে। কিন্তু তাই বলে বিশ্বমানবকে আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান জানানোর কঠিন দায়িত্ব তেকে মুসলিম উম্মত কখনই নিষ্কৃতি পেতে পারে না। তাকে প্রথমত কোথাও দ্বীন-ইসলাম প্রতিষ্টিত করতে হবে এবং অতঃপর নির্বিশেষে সমস্ত মানবতাকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান জানাতে হবে। সর্বাত্মকভাবে চেস্টা চালাতে হবে তাদেরকে আল্লাহর প্রতি ঈমানদার বানানোর জন্য। এ জন্য তারা আল্লাহর পক্ষ থেকেই দায়িত্বশীর এবং তা না করলে তাদেরকে আল্লাহর নিকট কঠিনভাবে জবাবদিহি করতে হবে। অন্য কথায়, মুসলিম উম্মতকে প্রথমে নিজেদের মধ্যে ‘আমল বিল মা’রূফ ও নিহী আনিল মুনকার’-এর দায়িত্ব পালন করতে হবে। পরে এ দায়িত্ব পালন করতে হবে সমগ্র বিশ্বমানবতার প্রতি। প্রথম পালনীয় কাজ হচ্ছে ‘আমর বিল-মা’রূফ’–আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আল্লাহর শরীয়াতকে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাহায্যে কার্যকর করা। আর ‘নিহী আনিল মুনকার’ হচ্ছে জাহিলিয়াতকে নির্মূল করা, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও আইন-বিধান অমান্য করাকে প্রতিরুদ্ধ করা। কেননা জাহিলিয়াতের শাসন তাগুতের শাসন, আল্লাহর শাসনের পক্ষে অতি বড় চ্যালেঞ্জ, আল্লাহর আইন-বিধান লংঘনের ক্ষমার অযোগ্য দৃষ্টতা। মুসলিম উম্মত প্রথমত নিজেদের জন্য দায়িত্বশীল, তার পরে দায়িত্বশীর গোটা বিশ্বমানবতার জন্য।
কাজেই উক্ত আয়াত থেকে একথা মনে করার কোন কারণ নেই যে, মুসলিম উম্মত বুঝি ‘আমল বিল মা’রূপ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর জন্য দায়িত্বশীল নয়। এ কথা কেউ মনে করলে তা হবে আয়াতের আসল ব্কতব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ গ্রহণ। আর শুধু হেদায়েত প্রাপ্ত হলেই বুঝি মুসলিম উম্মত রেহাই পেয়ে যাবে, তাকে ইসলামী শরীয়াতকে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করতে হবে না –এমন ধারণা গ্রহণ-ও এ আয়াতের সম্পূর্ণ বিপরীত তাৎপর্য গ্রহণ।
মোটকথা, এ আয়াত ব্যক্তিকে অন্যায়-অস্ত্য, জুলুমের প্রতিরোধ করার দাযিত্ব থেকে বিন্দুমাত্র মুক্তি দেয়নি, তাগূতী শাসন-প্রশাসন উৎখাত করে আল্লাহর শাসন ও খিলাফতের প্রশাসন কায়েম করার কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি দেয়নি। কেননা তাগূতী মাসন আল্লাহর ‘ইলাহ’ হওয়াকেই অস্বীকার করে, আল্লাহর সার্বভৌমত্বকেই চ্যালেঞ্জ করে মানুষকে আল্লাহর শরীয়াতের পরিবর্তে নিজের আইন-আদেশের দাসানুদাস বানায়। এ এমন একটা ‘মুনকার’, যা কোন ঈমানদার ব্যক্তিই বরদাশত করতে পারে না, বরদাশত করা উচিত নয়। এরূপ অবস্থায় গোটা উম্মত যদি হেদায়েত প্রাপ্ত হয়ও তবু তাদের এ হেদায়েত প্রাপ্তি কোন কাজেই আসবে না।
আল্লাহ্ তা’আলার শোকর, উপরোক্ত আয়াতের ভুল অর্থ গ্রহণের কারণে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছিল, তা প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) রাসূলে করীম (স)-এর স্পষ্ট হাদীসের ভিত্তিতেই নস্যাৎ করে দিয়েছেন এবং আয়াতের যথার্থ অর্থ জনগণকে জানিয়ে দিয়েছেন। আমাদের একালের কোন কোন দুর্বলমনা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তি এ আয়াতকে ভুল মতের দলিল হিসেবে পেশ করে জনগণকে ‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’ এর দাযিত্ববিমুখ বানিয়ে দিতে চেয়েছে, তাদের এ অপচেষ্টাও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে।
না, কখনই তা হতে পারে না। আল্লাহর এই দ্বীন ‘জিহাদ’ ব্যতীত কখনই কায়েম হতে পারে না। মুসলিম সমাজ কখনই সংশোধনপ্রাপ্ত হতে পারে না অন্যায়ের প্রতিরোধ ও ন্যায়ের বাস্তব প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে। এই দ্বীনের জন্য একদল লোককে অবশ্যই এ কাজে নিয়োজিত থাকতে হবে। তারা মানুষকে অন্যায় পথ থেকে বিরত রাখবে। প্রথমে ওয়ায-নসীহতের সাহায্যে। আর তা ব্যর্থ হলে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্তৃত্বের সাহায্যে। তাহলেই মানুষ মানুষের নিকৃষ্ট গোলামী থেকে মুক্তি পেতে পারবে। পারবে একান্তভাবে মহান আল্লাহর বান্দা হয়ে জীবন যাপন করতে। আল্লাহর যমীনে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করতে। এজন্য আল্লাহর সার্বভৌমত্ব যারা কেড়ে নিয়ে নিজেদের সার্বভৌমত্ব জনগণের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, সে সার্বভৌমত্বকে কেড়ে আনতে হবে, সর্বত্র জারি করতে হবে কেবল মাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব, কার্যকর করে তুলতে হবে একমাত্র আল্লাহর আইন।
‘আমর বিল মা’রুফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ প্রথমে প্রচার ও সমঝ-বুঝ পর্যায়েই করতে হবে একথা ঠিক। কিন্তু তা ব্যর্থ হলে সে জন্য শক্তির প্রয়োগ করতে হবে নির্দ্বিধায়।১
(আরবী……………..)
অবশ্য এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, অন্যরা কি করে না করে-সে চিন্তার পূর্বে নিজে হেদায়েতের পথে আছে কিনা সেই চিন্তা প্রত্যেক ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে করতে হবে। কেননা ব্যক্তি নিজেই যদি হেদায়েতপ্রাপ্ত না হলো, তাহলে অন্যদের হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া না হওয়ার চিন্তা করার কোন অধিকারই তার থাকতে পারে না। আর সংশোধনের কাজ সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়েই শুরু করতে হবে, তার পরই অন্যদের হেদায়েতের প্রশ্ন উঠে।
হযরত আলী (রঃ)-এর এ কথাটি এই প্রেক্ষিতে খুবই যথার্থঃ
(আরবী………..)
যে লোক নিজেকে লোকদের নেতার স্থানে প্রতিষ্টিত করবে, তার কর্তব্য, অপরকে শিক্ষাদানের পূর্বে সে যেন নিজেকে শিক্ষাদানের কাজ শুরু করে এবং তার মুখের কথা-বক্তৃতা দ্বারা লোকদেরকে সদাচার শিক্ষাদানের পূর্বে সে যেন নিজের আচরণ ও চরিত্র দ্বারা লোকদের শিক্ষাদান করে। বস্তুত যে লোক নিজের শিক্ষক, নিজেকে সদাচারের শিক্ষাদাতা, অন্য লোকদেরকে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ দেয়ার দিক দিয়ে সে-ই বেশী অগ্রাধিকার পাওয়ার অধিকারী।
এক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রয়োজনীয় হচ্ছে কুরআনের সেই আয়াত, যা তিনি মদীনার ইয়াহুদীদের প্রতি নাযিল করেছিলেন। তা হচ্ছেৱ
(আরবী……………..)
তোমরা লোকদেরকে ‘বির’ সর্বপ্রকারের শুভ কাজের আদেশ কর, অথচ তোমরা এদিক দিয়ে নিজেদেরকে ভুলে যাও?
আল্লামা আ-লূসী লিখেছেনঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর বর্ণনানুযায়ী আয়াতটি মদীনার ইয়াহুদী আরিমদের আচরণ সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তারা গোপনে গোপনে লোকদেরকে বলত মুহাম্মদ (স)-কে মেনে নিতে, তাঁকে অনুসরণ করতে। কিন্তু তারা নিজেরা তাঁকে মানতও না, অনুসরণও করত না অথবা তারা সাধারণ মানুষকে দান-সাদকা করতে উপদেশ দিত, কিন্তু তারা নিজেরা তা করত না। আল্লামা সুদ্দী বলেছেনঃ তারা লোকদেরকে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য নসীহত করত, আল্লাহর নাফরমানী করতে নিষেধ করত, কিন্তু তারা আল্লাহর আনুগত্য না করে তাঁর নাফরমানী-ই করত বেশী বেশী করে।
তাদের এই বৈপরীত্যপূর্ণ চরিত্র ও আচার-আচরণের উপরই এইকঠোর শাসনমূরক ও আপত্তি জ্ঞাপক প্রশ্ন। তার অর্থ অন্যদেরকে ভালো ভালো ও পূণ্যময় কাজ করতে বলা ও উপদেশ দেয়া –নিজেদের তার কিছুই না করা একটা ঘৃণ্য নির্লজ্জতা, একটা অতিবড় জঘন্য অপরাধ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ‘বির’ সর্বপ্রকারের শুভ কাজ করার উপদেশ দেয়া ও লোকদেরকে সে কাজে অনুপ্রাণিত করা নিঃসন্দেহে অতীব উত্তম কাজ বরং কর্তব্য। কিন্তু আপত্তির বিষয় হলো এই দিক দিয়ে নিজেকে ভুলে যাওয়া –নিজে সেই কাজসমূহ না করাটাই আপত্তির বিষয়।
(আরবী……………..)
বস্তুত যে সমাজ নৈতিকতার দিক দিয়ে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গেছে, বিকৃতি ও বিপথগামিতা মানুষকে পেয়ে বসেছে, সেই সমাজে যদি সংশোধনমূলক কার্যক্রম করার সংকল্প গ্রহন করা হয়, তাহলে নিজেকে দিয়েই সে কাজের সূচনা করতে হবে। সেই মুহূর্তে অন্যরা কে কি করতে তা দেখা চলবে না। কেননা তা দেখতে গেলে কারোর পক্ষেই সম্ভব হবে না নিজেকে পর্যন্ত সংশোধন কা। তখন অন্ততঃ কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষে এই কথা বলার কোন অধিকার থাকতে পারে না –গোটা সমাজই যখন বেঈমানীতে ডুবে গেছে, তখন একা আমার পক্ষে ঈমানদারী রক্ষা করা কি করে সম্ভব হতে পারে? এরূপ মানসিকতাই আল্লাহর নিকট আপত্তির কারণ। কথাটি আরও খোলাসা করার জন্য রাসূলে করীম (স)-এর সেই প্রখ্যাত হাদীসটিও এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, যার ভাষা হচ্ছে এইঃ
(আরবী………..)
ইসলাম নেহায়েতই অপরিচিত অসহায় অবস্থায সূচিত হয়েছিল। খুব শীগগীরই ইসলাম সেই অবস্থায় ফিরে যাবে। তবে তখনকার সেই ‘গুরাবা’ অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ, ধন্যবাদ।
এই কথা মুনে সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞাসা করলেনঃ
(আরবী………….)
‘গুরাবা’ বলে আপনি কোন্ লোকদেরকে বুঝিয়েছেন হে আল্লাহর রাসূল?
জবাবে বললেনঃ
(আরবী……….)
তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা জনগণ যখন আমার সুন্নাত থেকে বিচ্যুত হয় তখন সংশোধনমূলক কাজ করে।
আল্লাহর পথে জিহাদের তুলনায়ও এই ‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ অনেক সময় অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বরং এটাই হচ্ছে জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ। আর রাসূলে করীম (স)- এর কথাঃ
(আরবী………..)
অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে স্পষ্ট সত্য কথা বলা উত্তম জিহাদ।
ও তো সেই প্রাথমিক পর্যায়ের ‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজই।
হযরত আলী (রা)-র কথাঃ
(আরবী……………)
সমস্ত রকমের নেক ও শুভ কাজও আল্লাহর পথে জিহাদ ‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’- কাজের তুলনায় মহাসমুদ্র থেকে এক ফোটা পানি গ্রহণের সমান।
কেনা ‘আমর বিল মা’রূফ’ ও ‘নিহী আনিল মুনকার’- কাজটি মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। তা ব্যক্তিগতভাবে করা হোক, কি সামষ্টিকভাবে। আর ‘জিহাদ’ (প্রচলিত অর্থে) হচ্ছে বৈদেশিক আগ্রাসনের প্রতিরোধ। প্রথমটি দ্বিতীয়টির আগেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। কেননা যে সমাজ অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে ভাঙ্গন ও বিপর্যয়ের মধ্যে, তার পক্ষে বহিঃশত্রুর মুকাবিলা করা সম্ভব হয় না।
কাজেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করা জুলুমের প্রতিরোধ করার কাজ সর্বপ্রথম মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেই ব্যাপকভাবে কার্যকর হতে হবে। কুরআন মজীদের একটি আয়াত এ কথাটি আরও স্পষ্ট করে বলেছে। আয়াতটি এইঃ
(আরবী………..)
আল্লাহ এই কিতাবে তোমাদেরকে পূর্বেই এই হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরির কথা বলতে এবং তার প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে শুনবে, সেখানে (তাদের সাথে) তোমরা অদৌ বসবে না –যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায লিপ্ত হয়। তোমরাও যদি তাই কর, তাহলে তোমরাও তাদের মতই হবে। নিশ্চয়ই জানবে, আল্লাহ্ মুনাফিক ও কাফিরদেরকে জাহান্নামে একত্রিত করবেন।
এ আয়াত স্পষ্ট করে বলছে, আল্লাহর কালাম, কালামের কোন আয়াত –আল্লাহর কোন হুজুম-বিধানের বিরুদ্ধতা করা বা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা আল্লাহদ্রোহী কাফিরদেরই কাজ, একবিন্দু ঈমান যার মধ্যে আছে, তার পক্ষে এ কাজ করা তো দূরের কথা, তা করতে দেখলে বা শুনতে পেলে যারা তা করে তাদের সাথে একত্রে বসা বা সম্পর্ক রক্ষা করাও সম্ভব হতে পারে না। করা –ঈমানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেউ যদি তা করে তাহলে বুঝতে হবে, তার ঈমান নেই, সে-ও সেই কাফিরদের মতই হয়ে গেছে।
সাধারণত লক্ষ করা যায়, কোন একজন লোকই হয়ত ইসলাম বা কুরআনের কোন স্পষ্ট নির্দেশের বিরুদ্ধতা, কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করল, আর তার চারপাশের অন্যান্য লোক তা শুনে চুপ চাপ থাকল কোন প্রতিবাদ করল না। এইরূপ জঘন্য কথা শুনে হজম করে ফেলল, তা হলে তার মধ্যে ঈমানের একবিন্দুও আছে, তার কোন প্রমাণই পাওয়া যেতে পারে না।
হযরত আলী (রা) বলেছেন, কুরআন মজীদে হযরত সালেহর মু’জিজা হিসেবে যে উষ্ট্রীকে দেয়া হয়েছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা এই উষ্ট্রীর উপর কোনরূপ অত্যাচার করবে না। অত্যাচার করা হয়েছিল, কিন্তু সকলে করেনি, করেছিল মাত্র এক ব্যক্তি, আর অন্যরা তাতে একমত ছিল। তাই আল্লাহ্ যে আযাব দিয়েছিলেন, তা কেবল সেই এক ব্যক্তির উপরই নয়, সমস্ত মানুষই সে আযাবে ধ্বঙস হয়ে গিয়েছিল।
বস্তুত সমাজে দুস্কৃতি ও অনাচার সকলেই হয়ত করে না, করে মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু তার পরিণামে যে আযাব আসে, তা থেকে কেউ-ই রেহাই পায় না। কেননা সেই অন্যান্য সকল লোক –যারা নিজেরা অনাচার করেনি বটে, কিন্তু কতিপয় লোকের অনাচারকে তারা নীরবে সহ্য করেছে বলেই এই পরিণতি তাদেরও ভাগ্যলিপি হয়েছে।
তাই সমাজের লোকদের সামষ্টিক কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত পরহেযগারী কিছু মাত্র রক্ষাকবচ হতে পারে না। সমাজকেও সকল প্রকার অন্যায় অনাচার থেকে রক্ষা করতে চেস্টা চালিয়ে যেতে হবে।
তবে আমাদের এ পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে বলতে হচ্ছে, ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’- এর দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাহী দায়িত্বশীল একটি বিভাগ অবশ্যই থাকতে হবে। এ বিভাগের প্রধান দায়িত্বই হবে এই কাজ করা। তা যেমন ব্যক্তিগণের মধ্যে করতে হবে, তেমনি করতে হবে সামাজিক-সামষ্টিকভাবেই এ কাজ করতে হবে। প্রথমোক্ত কাজের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ও আয়াত কয়টি থেকেঃ
(আরবী………………)
মু’মিন পুরুষ মেয়েলোক পরস্পরের কল্যাণকামী –অভিভাবক। তারা ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করে, তারা সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এরা সেই লোক, যাদের প্রতি আল্লাহ অবশ্যই রহমত করবেন। আর আল্লাহ তো সর্বজয়ী-মহাবিজ্ঞানী।
(আরবী……………..)
তারা তওবাকারী-ইবাদতকারী-হামদকারী, যমীনে পরিভ্রমণকারী, রুকু’কারী-সিজদাকারী, ভালো কাজের আদেশকারী, মন্দা কাজ থেকে নিষেধকারী, আল্লাহর নির্ধারিত সীমা রক্ষাকারী –হে নবী! তুমি এই মু’মিন বান্দাগণকে সুসংবাদ দাও।
(আরবী……………)
তোমরাই হচ্ছ সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। তোমাদেরকে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরাই ভালো কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখ আর তোমরা সব সময়ই আল্লঅহর প্রতি ঈমান রক্ষা করে চল।
এ তিনটিই এবং এ ধরনের আরও অন্যান্য আয়াতে মুসলিম সমষ্টিকে সাধারণভাবেই সম্বোধন করে অন্যান্য কাজের সাথে সাথে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’- এর কাজ করার কথা বলা হয়েছে। স্পষ্ট মনে হচ্ছে, এ কাজ ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি –প্রত্যেক নারী ও পুরুষকেই করতে হবে।
এ ছাড়া অপর কিছু আয়াতে মুসলিম সমাজ সমষ্টিকে সন্বোধন করেছে। তা থেকে নিঃসন্দেহে মনে হয়, এ দায়িত্ব মুসলমানদের মধ্য থেকেই একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপর অর্পণ করা হয়েছে, যাদের উম্মত বলে অভিহিত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ
(আরবী…………..)
হে মুসলিমগণ তোমাদের মধ্য থেকে একটা জনগোষ্ঠী –কতিপয় ঐক্যবদ্ধ মানুষ –এমন অবশ্যই বের হয়ে আসতে ও নিয়োজিত থাকতেই হবে, যারা সার্বিক কল্যাণের দিকে আহবান জানাতে থাকবে এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার জন্য সর্বক্ষণ নিযুক্ত থাকবে। বস্তুত এরাই হচ্ছে সফলকাম।
আয়াতে একটি উন্মতকে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা বলা হয়েছে। আর ‘উম্মত’ বলতে তো এমন কিছু লোক সমষ্টি বোঝায়, যারা আকীদা-বিম্বাসে এবং চিন্ত ও কর্মে অভিন্ন। কোন কোন আয়াতে মাত্র এক ব্যক্তিকেও ‘উম্মত’–জনসমষ্টি –ছিল। ছিল আল্লাহর আদেশানুগত, একমুখী, আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ। সে কখনই মুশরিকদের মধ্যের কেউ ছিল না।
এ আয়াতে হযরত ইবরাহীম (আ) এক ব্যক্তিকেই ‘উম্মত’ বলা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে, যিদি বিপুল কল্যাণের মিল-কেন্দ্র। ইবনে ওহাব ও ইবনুল কাসেম ইমাম মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) একদা বলেছেনঃ
উপস্থিত একজন বলেনঃ আল্লাহ্ তা’আলা তো হযরত ইবরাহীম (আ)-কে এই শব্দে অভিহিত করেছেন (যে শব্দে আপনি হযরত মায়াযকে অভিহিত করলেন)? জবাবে তিনি বলেনঃ
(আরবী……………..)
উম্মত তো সে-ই যে লোকদেরকে মহাকল্যাণের জ্ঞান শিক্ষা দেয়। আর ‘কানেত’ অর্থ হচ্ছে অনুগত।
(আরবী টীকা……………)
ইমাম জা’ফর সাদেক (র) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করা সমস্ত উম্মতের প্রতি ওয়াজিব? বললেনঃ না।…কেননা তা এমন ব্যক্তির কাজ, যে শক্তিশালী, সকলেই মানে এবং ‘মা’রূফ’ও ‘মুনকার’ সম্পর্কে যথার্থ আলিম। কোন দুর্বল ব্যক্তির জন্য একাজ নয়।
(আরবী টীকা…………..)
বস্তুত ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজটি কোন ছেলেখেলা নয়। নেহাত দাওয়াতখুর, ওয়ায নসিহত ও পীর-মুরীদীর ব্যাপারও নয়, তা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। এ কাজের জন্য রাষ্ট্রশক্টির সমর্থন ও সহযোগিতা একান্ত অপরিহার্য। আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ
(আরবী***********)
তারা সেই লোক, যাদেরকে আমরা যদি পৃথিবীতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করি তাহলে তারা ‘সালাত’ কায়েম করবে, যাকাত আদায় ও বন্টন করবে এবং ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করবে। অবশ্য সর্ব বিষয়ের শেস পরিণতি তো আল্লাহরই জন্য।
এ আয়াত স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ যথার্থভাবে করার জন্য শক্তি-সামর্থ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তির প্রয়োজন, যা কেবল রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠাপোষকতা ও সমর্থনের মাধ্যমেই পাওয়া যেতে পারে। আয়াতের শুরুর শব্দটিতে রাষ্ট্রের প্রধান নায়ক বুঝিয়েছে। আর পরবর্তী শব্দসমূহ রাষ্ট্রপ্রধানের অধীন সরকারী শাসন-প্রশাসক ও কর্মচারীদের বুঝিয়েছে, যাদের হাতে নির্বাহী শক্তি (Executive power) থাকে। অন্যথায় শুধু মৌখিক ওয়ায-নসীহতই হতে পারে, কোন ‘আমর’–আদেশ এবং কোন ‘নিহী’–নিষেধ বাস্তবভাবে কার্যকর ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আর তা কার্যকর ও বাস্তবায়িত না হলে পারলে তা নিতান্তই ব্যর্থ ও অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।
কিন্তু তাই বলে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান অপেক্ষায় ফেলে রাখতে হবে এবং যদ্দিন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হচ্ছে তদ্দিন তা করা হবে না, এমন ধারণা পোষণও ঠিক নয়। সত্য কথা হচ্ছে, এ কাজ করতেই হবে। ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর এ কাজ করতে হবে রাষ্ট্রীয়ভাবে। আর ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা-পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া না গেলেও –এমন কি তার প্রবল বিরুদ্ধতা থাকলেও তা উপেক্ষা করেই এই কাজ করতে হবে। করতে হবে সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে, যা প্রতিষ্টিত হওয়ার পর এই কাজ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবেই করবে। আর তা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তা কায়েম করার লক্ষ্যেই তা করতে হবে, করে যেতে হবে এবং সকল বাঁধা প্রতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য ও উপেক্ষা করেই তা করতে থাকতে হবে। করতে হবে সকল সময়, সকল অবস্থায়। তখন এই কাজ মৌখিক দাওয়াত হিসেবেই করতে হবে। এই মৌলিক দাওয়াতকে দু পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ
প্রথম পর্যায়ে এ কাজ করবে এমন প্রত্যেক মুসলামনই, যার ইসলামের বুনিয়াদী ও জরুরী বিষয়াদি –তার হালাল ও হারাম সম্পর্কে মৌলিক ও মোটামুটি ইলম রয়েছে। এ কাজ হবে ব্যক্তিগতভাবেই।
আর দ্বিতীয পর্যায়ে তা হবে দলবদ্ধভাবে। এই দল হতে হবে এমন সব লোকের সমন্বয়ে যারা দ্বীন-ইসলাম সম্পর্কে গভীর ও ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করেছে, এজন্য সময় শ্রম নিয়োগ করেছে। তারা দ্বীন সম্পর্কে কেবল মোটামুটিভাবেই জানবে না, বরং তার বিস্তারিত ও খুটিনাটি বিষয়েও ভালভাবে ও গভীর সূক্ষ্মভাবে জানবে। এ কথাই আল্লাহর এ আয়াতটি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেঃ
(আরবী****************)
ঈমানদার লোকদের সকলেরই বের হয়ে পড়া জরুরী ছিল না। কিন্তু এরূপ কেন হলো না যে, তাদের প্রত্যেক জনগোষ্ঠী থেকে কিছু সংখ্যক লোক বের হয়ে আসত ও দ্বীন সম্পর্কে গভীর সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ করত এবং তাদের নিকট ফিরে এসে নিজ নিজ এলাকার লোকজনকে পরকালের ব্যাপারে সতর্ক করে তুলবে, তাতে আশা করা যায়, তারা হয়ত সতর্ক হয়ে যাবে।
‘ইলম’ অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া যে ওয়াজিব, এ আয়াতটি তারই দলীল। মদীনা থেকে দূরে দূরে অবস্থানকারী লোকেরা এক সাথে নিজেদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করে সকলেই রাসূলের নিকট দ্বীন শিক্ষা লাভের জন্য চলে যাবে, তা আল্লাহর পছন্দ নয়। শুধু তাই-ই নয়, বাস্তবে তা অনেক সময় সম্ভবও হয় না। তাই আল্লাহ বললেন, সকলেই নয়, প্রত্যেক এলাকার লোকজনের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যাক লোক রাসূলে করীম (স)-এর নিকট গিয়ে অবস্থান করতে পাররে এবং তাঁর নিকট থেকে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করতে পারে। জ্ঞান অর্জন শেষ হলে তারা নিজেদের লোকজনের নিকট ফিরে এসে তাদেরকে দ্বীনের শিক্ষা দান করবে।
কি শিক্ষা লাভের জন্য তারা বেরিয়ে পড়বে? কুরআন বলেছেঃ (আরবী************) দ্বীন সম্পর্কে ‘তাফাক্কহ্ –(আরবী*************) লাভ করার জন্য। এই ‘তাফাক্কহ্ বলতে কি বোঝায়? শব্দটি ‘ফিক হুন’–(আরবী**************) থেকে নির্গত। এর অর্থঃ সমঝ বুঝ, গভীর সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং তৎলব্ধ দৃঢ় প্রত্যয়, যা জনগণকে সতর্ক করার জন্য –অন্য কথায় দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে লোকদের মধ্যে চিন্তা বিবেচনা বিচার-বুদ্ধি ও সমঝ-বুঝ সৃষ্টি করে তাদেরকে পরকালীন দুঃখময় পরিণতি থেকে বাঁচার জন্য এখন-ই –এই দুনিয়ায় সতর্ক জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করা। আর সেজন্য এ কাজ যারা করবে তাদের নিজেদেরকেই সর্বাগ্রে এই গুণ ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। অন্যথায় তারা তাদের জন্য প্রস্তাবিত দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হবে না।
এই ইলম অর্জন করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য রাসূলে করীম (স) বলেছেনঃ
(আরবী*************)
ইলম সন্ধান –ইলম লাভ করতে চাওয়া –সেজন্য চেষ্টা ও সাধনা করা প্রতিটি মুসলিমের জন্যই ফরয।
এই কাজের ফযীলত পর্যায়ে রাসূলে করীম (স) থেকে বর্ণিত বহু সঙখ্যক সহীহ্ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেনঃ
বনি-ইসরাঈল বংশে ব্যক্তি ছিল। একজন ছিল দ্বীনের আলিম, সে ফরয নামায পড়ে বসে যেত ও লোকদেরকে দ্বীনের কল্যাণের শিক্ষা দান করত। আর অপর জন ফরয নামায পড়া ছাড়া দিনের বেলা নফল রোযা রাখত, রাতে না ঘুমিয়ে নফল ইবাদত করত।–হে রাসূল, আপনি বলুন, এই দুই জনার মধ্যে কোন্ জন অতি ভালো?
জবাবে রাসূলে করীম (স) বললেনঃ
(আরবী*************)
যে আলিম ফরয নামায রীতিমত আদায় করে লোকদিগকে দ্বীনের কল্যাণ শিক্ষা দানের জন্য বসে যায়, সে সেই ইবাদাতকারী ব্যক্তির তুলনায় অনেক ভালো, যে দিনে নফল রোযা রাখে ও রাতে ইবাদাত করে –এই ভালো ঠিক তেমনি, যেমন তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির তুলনায় আমি ভাল।
অপর এক হাদীসের প্রথম অংশ হচ্ছেঃ
(আরবী*********)
আল্লাহ্ যাকে কল্যাণ দিতে চান, তাকে দ্বীনের সমঝ-বুঝ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী বানান।
এই দীর্ঘ আলোচনা (আরবী টীকা***************) থেকে গৃহীত।
‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজটিকে এ ভাবে দু’ভাগে ভাগ করা যায় যে, এ কাজ মোটামুটি সহজ, সেজন্য খুব বেশী প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়ে না। খুব শক্তি-সামর্থ বা যোগ্যতারও তেমন আবশ্যকতা থাকে না। কেননা এ পর্যায়ের কাজ এতটুকু যে, মুখে বলতে হবে, লোকদের হৃদয়কে উদ্বুদ্ধ করতে ও তা পালন করার জন্য প্রত্তুত করতে চাইতে হবে।
আর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ যথেষ্ট প্রস্তুতি শক্তি-সামর্থ্য ও কর্তৃত্ব প্রতিপত্তির উপর নির্ভরশীল।
প্রথম পর্যায়ের কাজ সম্পর্কে হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ
(আরবী******************)
দিল্ ও মুখ দিয়ে অন্যায় ও পাপের প্রতিবাদ করার কাজকে যে লোক ত্যাগ করল, সে জীবিত লোকদের সমাজে এক মৃত মানুষ।
এ পর্যায়ের কাজ করা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির পক্ষেই অতিব সহজ। কেননা মুখ দিল ও চেহারাকে অতিক্রম করে না। এ কাজ শাসক-শাসিত, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সব মানুষের পক্ষে করাই সম্ভব এবং সহজ।
আর দ্বিতীয় পর্যায়ের ‘আমল বিল মারূফ’‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ করা ফরয রূপে পণ্য। তা দ্বীন কায়েমের সহায়ক এবং পথ-ঘাটে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা এবং জালিমের হাত থেকে মজলুমকে রক্ষা করার পথ উন্মুক্ত করে। সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতির জন্য তা অপরিহার্য এবং শত্রুর প্রতিরোধ –তার উপর দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের একমাত্র পথ। আর তা শক্তি, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ভিন্ন হতে পারে না।
আল্লাহ্ তা’আলা হযরত লুকমান (আ)-এর তাঁর পূত্রের প্রতি নসীহত প্রসংঙ্গে অন্যান্য কথার সঙ্গে এ কথাটিরও উল্লেখ করেছেনঃ
(আরবী*******************)
ভালো কাজের আদেশ কর এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ কর। আর তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধারণ কর। মনে রেখো, এ নিশ্চয়ই অত্যন্ত উচুঁদরের সাহসিকতা ও বীরত্বের কাজ।
‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর নির্দেশের পরই ধৈর্য অবলম্বন করতে বলা হয়েছে সেই বিপদে, যা তোমার উপর ঘনিয়ে আসবে। এ থেকে বোঝ যায়, এ কাজটাই এমন যে, এর ফলে এই কাজ যারাই করবে তাদের উপর বিপদ ঘনিয়ে আসা যেমন কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়, তেমনি নয় কিচু মাত্র অসম্ভাবও। অন্যথায় এখানে ধৈর্য ধারনের নির্দেশ দেয়ার কোন সঙ্গতি থাকে না।
‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ যে অত্যন্ত বড়, অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং সে জন্য বিরাট সাহসিকতা ও দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন তা ও থেকেই বোঝা যায়।
আবুল আব্বাস আল-মুবরাদ বলেছেনঃবনী-ইসরাইলীদের নিকট নবী এলেন তাদেরকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়ার জন্য। কিন্তু লোকেরা নবীগণকে হত্যা করলে পরে তাদের মধ্য থেকেই কিছু সংখ্যক মু’মিন লোক দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁরা লোকদেরকে ইসলাম পালনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদেরকেও লোকেরা হত্যা করল। তাদের সম্পর্কে কুরআনে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছেঃ
(আরবী****************)
যারা আল্লাহর আয়াত অমান্য করে, নবীগণকে অন্যায়-অকারণ হত্যা করে, এমনি তাদের পর জনগণের মধ্য থেকে যারা উঠে ইনসাফ ও সুবিচার করতে বলে তাদেরকেও হত্যা করে, এই লোকদেরকে কঠিন পীড়াদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। এই লোকেরা হচ্ছে এমন, যাদের (নেক) আমল ইহকাল পরকাল সর্বত্রই সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিঃশেষ হয়ে যাবে। আর তাদের সাহায্যকারী কেউ-ই কোথাও নেই।
এ আয়াতদ্বয় স্পষ্ট করে বলছে যে, বনি ইসরাইলের লোকেরা অকারণ ও নিতান্ত অন্যায়ভাবে কেবল নবী-রাসূলগণকেই হত্যা করেনি; নবী বা রাসূলের পর তাঁদের উম্মতের মধ্য থেকে যারাই ইনসাফ সুবিচারের আহবান জানানো ও প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্ঠা চালানোর জন্য উঠেছেন, তাঁদেরকেও তারা হত্যা করেছে।
নবী-রাসূলগণের কাজ আল্লাহর বন্দেগী কবুল করার আহবান জানানো। যারা এই আহবানকে অগ্রাহ্য করবে তারা কাফির। বনু-ইসরাইলীদের মধ্যকার এই কাফিররা দ্বীন, ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার আহবানকারী কাউকেই ক্ষমা করেনি, সহ্য করেনি। তাদেরকে দুনিয়া থেকেই চিরদিনের তরে বিদায় করে দিয়েছে তাদেরকে হত্যা করে। এই নবী-রাসূল ও তাঁদের পরে যারা উঠেছেন, তারা যে কাজ করতেন, তা ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ ছাড়া তো আর কিছু নয়। কিন্তু এই কাজের জন্যও তাদেরকে শক্ত প্রতিরোধ, আক্রমণ-প্রতি-আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই অপরাধে (?) জীবনটাকে পর্যন্ত অকাতরে বিলিয়ে দিতে হয়েছে।
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজটির প্রথম পর্যায় খুবই সহজ, নির্বিঘ্ন ও বিপদহীন। কিন্তু এ কাজ যখন তার যথাযথ দায়িত্ব পালন করে, সমালোচনা তীব্র ও তীক্ন হয়ে উঠে, যখন শক্তি প্রয়োগে ইসলামের দুশমনদের নির্মূল করার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়, ঠিক তখনই হয় ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজটির চূড়ান্ত স্তর।
হযরত আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) একটি ভয়াবহ ও করুণ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন –নবী করীম (স) বলেছেনঃ
বনি ইসরাইলীরা দিনের প্রথম ভাগে মাত্র এক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তেতাল্লিশ জন নবীকে হত্যা করেছিল। তারপর বনি ইসরাইলের দাসদের মধ্য থেকে একশ’বারোজন ব্যক্তি মাথা তুলে দাঁড়াল এবং তারা ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করতে লাগল। কিন্তু বনি ইসরাইলীরা সেই দিনের শেষ প্রহরেই সেই সমস্ত লোককে হত্যা করেছিল। উপরোদ্ধৃত আয়াতে তাদের কথাই বলা হয়েছে।
এই সব কথাই (আরবী টীকা*********************) থেকে উদ্ধৃত।
কাজে ই ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজটি কিছুমাত্র সহজ-সরল ও জটিলতা, বাধা-প্রতিবন্ধকতাহীন নয়। এ কাজ শুরু করলে যারা তা পছন্দ করে না –তা হোক তা চায় না তারা বাধা দেবেই। যদি বাধা না দেয় আর সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নতার সাথে এ কাজ চলছে বলে দেখা যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে, সমস্ত মানুষই তা গ্রহণ করেছে। এ কাজের সাথে তাদের কোন বিরোধই নেই। ফলে বিঘ্ন সৃষ্টির কোন কারণ ছিল না। আর জনগণ সকলেই যদি তা গ্রহণ না করে ও তার বিরুদ্ধতা না করে তাহলে দৃঢ় প্রত্যয় সহকারে জনাবে যে, যা হচ্ছে তা আর যা-ই হোক, কুরআন উপস্থাপিত ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ নয়। তা অন্য কিছু।
বস্তুত ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই করণীয়। কিন্তু যদ্দিন রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা করা যাচ্ছে না –অন্য কথায় ইসলামী হুকুম কায়েম হয়ে সে দায়িত্ব পালন শুরু করে না দিচ্ছে, তদ্দিনও এ কাজ করতে হবে। এমনভাবে করতে হবে যেন শেষ পর্যন্ত সে কাজ রাষ্ট্রীয়বাবেই সম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থায় এই কাজ কঠিন বাধার সম্মুখীন হতে পারে। সেজন্য জীবন ও প্রাণ দেয়ার প্রয়োজনও হতে পারে। শুধু প্রয়োজন হতে পারে তাই নয়, ইসলামী হুকুমত এমনই এক বিষ্ময়কর প্রকৃতি সমৃদ্ধ ব্যবস্থা যা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য চেষ্টাকারীদের রক্ত প্রবাহিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। অর্থাৎ শাহাদাত বরণ করতে প্রস্তুত লোকদের দ্বারাই ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হতে পারে। আর তা হয়ে গেলে তখন এ কাজটির দায়িত্ব প্রধানত প্রশাসনিক ও নির্বাহী শক্তি বা বিভাগের হাতে থাকবে বটে কিন্তু প্রতি মুহূর্তের, দিন-রাতের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ও ব্যাপারে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ ব্যক্তিগণের দ্বারা একান্তই ব্যক্তিগতভাবে ও সমাজের দ্বারা দলবদ্ধভাবেই আঞ্জাম পেতে হবে। কেননা এটা সর্বজনীন দ্বীনী ফরয। এ ফরয প্রত্যেক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে তো অবশ্যই পালন করতে হবে। সমষ্টিগত বা রাষ্ট্রীয়ভাবে তা পালিত হওয়ার প্রশ্ন তো অনেক পরে। তার স্তর ও পর্যায়ও এবং চূড়ান্ত। তখন রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে প্রধানত পালিত হবে।
এই ক্রমিক পর্যায়ে দায়িত্ব পালনের কথা ও তার মাত্রা একটি প্রখ্যাত ও প্রায় মানসম্মত হাদীসে স্পষ্ট করে উদ্ধৃত হয়েছে। নবী করীম (স) এরশাদ করেছেনঃ
(আরবী******************)
তোমাদের মধ্যের কেউ যখন কোন অন্যায় ও শরীয়াত পরিপন্থী কাজ হতে দেখবে, তখন হস্ত দ্বারা –শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে (ও ক্রমিক নিয়মে) তা পরিবর্তন করতে চেষ্টা করা তার কর্তব্য। তা করতে সমর্থ না হলে মুখ দিয়ে তার বিরুদ্ধে বলতে (বা ভাষা-সাহিত্য প্রয়োগে লিখতে) হবে। আর তা করতেও অসমর্থ হলে দিল দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে (কিংবা তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করতে হবে ও তার বিনাশ কামনা করতে থাকতে হবে)।
স্মরণ রাখতে হবে, সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন, ইসসাফ কায়েম, শত্রুর উপর থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ –সর্বোপরি জালিমকে তার জুলুম থেকে বিরত রাখা, কাউকে দ্বীনে সীমালংঘন করতে না দেয়া, মুসলিম জনগণের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে বায়তুলমালের সম্পদ বণ্টন, যাকাত-সাদাকাত আদায় ও ব্যায় –এক কথায় অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা বিধান ব্যক্তিগত বা নিছক মৌখিকভাবে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করার দ্বারা সম্পন্ন হতেই পারে না, তা সম্পন্ন করতে হবে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। রাষ্ট্রশক্তির অমোঘতা ও অপ্রতিরোধ্যতার দ্বারা। কেননা সেজন্য প্রশাসনিক শক্তি ও কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেই হবে। আর তা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রের ব্যবস্থাধীনেই কার্যকর হওয়া সম্ভব।
হযরত আমীর মু’আবিয়া (রা)-র পর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব যখন ইয়াযীদের হাতে এলো, তখন এই দীর্ঘ আলোচিত ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর কাজ বিপর্যস্ত হয়ে যাবে মনে করেই হযরত ইমাম হুসাইন (রা) তার বিরুদ্ধে প্রায় এককভাবে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাঁর প্রতিরোধ শক্তি যখন নিঃশেষ হয়ে আসছিল, তখন আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন এই ভাষায়ঃ
(আরবী***************)
হে আমাদের মহান আল্লাহ! এই যা কিছু হয়েছে তা ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা করার জন্য ছিল না। চূর্ণ-বিভক্ত জিনিসের কোন একটি অংশ অর্জনেরও ছিল না কোন আকাঙ্কা। আসলে লক্ষ্য ছিল তোমার দ্বীনের নিদর্শনসমূহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা, তোমার জমীনের শাসন-শৃঙ্খলার অবস্থা সংশোধন ও উন্নয়ন প্রকাশমান করা, যেন তোমার মজলুম বান্দাগণ শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করতে পারে এবং তোমার শরীযাতের ‘হদ্দ’সমূহ –যা বর্তমানে সম্পূর্ণ বন্ধ ও অকেজো করে রাখা হয়েছে –পুনঃ কার্যকর করা।
বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাহী বিভাগ (Executive) সদা কার্যকর না থাকলে মজলুম মানুষেরা নিরাপত্তা পেতে পারে না, বেকার করে রাখা আল্লাহর ‘হদ্দ’ ও দন্ডসমূহ কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে না। সমাজে সাধারণ সংস্কারমূলক কার্যাদি সুসম্পন্ন হতে পারে না। আল্লাহর আইন বিধান –আদেশ নিষেধসমূহ কার্যকর হতে পারে না। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী এই বিভাগটিই হচ্ছে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ বিভাগ। এই বিভাগটি অবশ্যই সরকারী পর্যায়ে সরকারী শক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। এ কাজ কোন ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে সম্পাদন করতে পারে না।
এই নির্বাহী বিভাগও নিছক মুখের কথা দ্বারা বা শুধু ওয়ায-নসীহতের মাধ্যমে এ কাজ করতে পারে না। এজন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কার্যকর প্রয়োগ একান্তই অপরিহার্য। এ বিভাগটিই হবে সেজন্য দায়িত্বশীল। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি থেকেও আমরা এ তত্ত্ব জানতে পারিঃ
(আরবী************)
তোমরা দেখতে পাও, এদের (ইয়াহুদী সমাজের) অনেক লোক-ই গুনাহ্, জুলুম, রাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘনমূলক কাজে-কর্মে প্রবল প্রতিযোগিতা ও চেষ্টা-সাধনা করে যাচ্ছে। এরা নির্ভয়ে হারাম খাচ্ছে। বস্তুত এরা যা কিছু করে, তা অত্যন্ত খারাপ।
এদের মধ্যকার আলিম ও পীর-পূরোহিতগণ তাদেরকে এসব পাপের কথা ও কাজ হারাম মাল ভক্ষণ থেকে কেন বিরত রাখছে না। …………… এরা যা কিছু কাজকর্ম করছে, তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত খারাপ।
কুরআন মজীদের এই ঘোষণাটি ঐতিহাসিকভাবে এতই সত্য যে, ইতিহাসের সাক্ষ্য ও কুরআনে উল্লিখিত ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য দেখে বিপুলভাবে বিষ্মিত হতে হয়। কুরআন মজীদে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে নিঃসন্দেহে লক্ষ্য করা যায় না, সমাজের লোকেরা যখনই আল্লাহর নাফরমানী কাজে লিপ্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যকার সাধারণ সুস্থ বুদ্ধির লোকেরা, আলিম ও পন্ডিত লোকেরা এবং সর্বোপরি শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণকে সেই নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেনি, লোকদেরকে বোঝায় নি কিংবা বাধা দেয়নি –জনগণ সেই নাফরমানীর কাজে ক্রমাগত এগিয়ে গিয়েছে ও গভীর ভাবে পাপ-পংকে নিপতিত হয়ে হাবুডুবু খেতে থেকেছে, তখনই সেই সমাজের উপর আল্লাহর কঠিন আযাব এসেছে এবং সে আযাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ধ্বংস হয়েছে।
মোটকথা, কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল (স) থেকে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজের দুইটি প্রকার বা পর্যায় প্রমাণিত হয়। একটি প্রত্যেক কর্তব্য পর্যায়ের আর অপরটি ক্ষমতাসীন প্রশাসনিক সংস্থার। এই দুই পর্যায়ের আয়াত ও হাদীসের মূল বক্তব্য সমস্ত সমাজ-সমষ্টির উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পক্ষে, আর অনেকগুলি আয়াত ও হাদীসের বক্তব্য একটি বিশেষ সংস্থার উপর এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়ার পক্ষে। প্রথমোক্ত আয়াত ও হাদীসের কথা হচ্ছে, এ দায়িত্ব সমাজের প্রত্যেক ব্যাক্তিকেই পালন করতে হবে। অর্থাৎ সকলকেই সে কাজ করতে হবে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের আয়াত ও হাদীস প্রমাণ করে যে, এ দায়িত্ব সমষ্টিকে পালন করতে হবে তাদের পক্ষ তেকে নিয়োজিত এক জনসমষ্টি বা সংস্থাকে, যার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্বের পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন থাকবে।
প্রশ্ন হতে পারে, কুরআনে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ এর আদেশ এসেছে, প্রথমটির উদ্দেশ্য লোকদেরকে ভালো কাজ করতে বলা এবং দ্বিতীয়টির অর্থ লোকদেরকে উপদেশ দেয়া যে, তোমরা শরীয়াত বিরোধী কাজ করো না, কিন্তু তাতে শরীয়াতের আইন কার্যকর করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে বলে তো মনে হয় না। আর তা না হলে হত্যাকারীকে হত্যাপরাধের দন্ড দান কিংবা ব্যভিচারীকে দোররা মারা বা পাথর মেরে হত্যা করা –প্রভৃতি কুরআন-সুন্নাহর আইন বাস্তবায়িত হবে কি ভাবে?
এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায়, ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ করার যে আদেশ শরীয়াতের দলীলে উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেই কুরআন সুন্নাহর উক্ত আইন কার্যকর করার নির্দেশ ও ক্ষমতা দান রয়েছ্ কেননা ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর অর্থ হচ্ছে, মানুষকে শরীয়াতের খেলাফ কাজ তেকে কার্যত বিরত রাখা –যেন ‘মুনকার’ পর্যায়ের কোন কাজ-ই হতে না পারে। আর তা সম্ভব, যদি হত্যাকারী ও ব্যভিচারীকে কার্যত শরীয়াতের দন্ডে দন্ডিত করা হয়। কুরআনের আয়াতঃ
(আরবী***************)
হত্যাকারীকে হত্যা করা যদিও আরও একটি প্রাণের সংহারকরণ, কিন্তু তা-ই সর্ব মানুষের জন্য পুনরুজ্জীবন –জীবনের নিরাপত্তার ভিত্তি। কিসাস (আরবী**********) এর তা-ই লক্ষ্য। এই কারণেই আরবী ভাষায় একটি বচন প্রচলিত ছিলঃ (আরবী*************) ‘হত্যা হত্যার প্রতিরোধক।‘
মোদ্দা কথা, শরীয়াতের ‘হদ্দ’–নির্দিষ্ট শাস্তিসমূহ কার্যকরকরণ যদিও একটি প্রাণের জন্য নেতিবাচক অবস্থা (Negation) কিন্তু তা-ই সমষ্টির জীবনের জন্য ইতিবাচক।
এই ব্যবস্থা ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’-এর দুইটি প্রকার নির্ধারণ করে এবং সামষ্টিক পর্যায়ে ‘আমর’ ও ‘নিহী’র দায়িত্বশীলের জন্য এমন কতিপয় জরুরী শর্তের উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্যাক্তিগতভাবে এই দায়িত্ব পালনকারীর জন্য করা হয়নি।
বস্তুত শরীয়াত কার্যকরকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বশীলতা। ইসলামী সমাজের প্রাথমিক দায়িত্বশীলেরা তা নিজেরা পালন করতেন তার কল্যাণের সাধারণত্ব ও সওয়াবের বিপুলতার কারণে। আর তাঁরা ‘মা’রূফ’-এর আদেশ করতেন যখন তা পরিত্যক্ত হতে দেখতে পেতেন এবং ‘নিহী আনিল মুনকার’ করতেন যখন দেকা যেত যে, সমাজ ক্ষেত্রে মুনকার ব্যাপক হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনকল্যাণই হতো তার মূল চালিকা। এ পর্যায়েই আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ
(আরবী*************)
লোকদের গোপন পরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য গোপনে কেউ যদি অপর কাউকে দান-খয়রাতের উপদেশ দেয় কিংবা ভাল কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজ-কর্মের সংশোধন সূচিত করার লক্ষ্যে কাউকে কিছু বলে, তাহলে তা নিশ্চয়ই খুবই উত্তম কাজ। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যে-কেউ এই কাজ করবে, তাকে আমরা বড় শুভ প্রতিফল দিব।
এ আয়াতে (আরবী********) অর্থঃ ততোধিক লোকের গোপন কথা-বার্তা বা পরামর্শ করা। অন্যান্য তাফসীরকারের মতে (আরবী**********) হচ্ছেঃ
(আরবী**********)
বিচ্ছিন্নভাবে কয়েকজন বা মাত্র দুই জনের পারস্পরিক কথা-বার্তা বলা –তা গোপনে হোক বা প্রকাশ্য।
এই কথাবার্তা বা পরামর্শ কোন দান বা অর্থনৈতিক কর্তব্য পালনের জন্য হোক বা কি কোন ভাল ও মঙ্গলময় কাজের জন্য হোক অথবা জনগণের পরস্পরের মধ্যে কল্যাণ বিধানের জন্য হোক তাতে অবশ্যই সার্বিক কল্যাণ চিহিত। অবশ্য তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে হতে হবে।
রাষ্ট্রপ্রধান বা তার নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি জনগণের সাধারণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ, তাদের সমস্যার সমাধান করা, তাদের বিপদ-আপদ দূর করা, তাদের সার্বিক কল্যাণের ব্যবস্থা করা –তাদের খাদ্য-পানীয়, বাসস্থান ও পথ-ঘাট উন্নয়ন বা তাদেরকে ভালো ভালো কাজে উদ্বুদ্ধকরণ এবং সকল প্রকারের অন্যায় ও পাপের কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা অবশ্যই করণীয়।
এ কাজের দায়িত্বশীলকে অবশ্যই মুসলিম, স্বাধীন (ক্রীতদাস নয়), পূর্ণবয়স্ক, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী ও সুবিচারকারী-ন্যায়বাদী হতে হবে।
(আরবী টীকা***********)
কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে এ কাজ করার জন্য এসব শর্তের কোন বাধ্যবাধকতা নেই।
এসব শর্ত ও যোগ্যতার প্রয়োজনীয়তাই ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজের দুইটি প্রকারে ও পর্যায়ে বিভক্ত করে দেয় সুস্পষ্টভাবে। আর তা হচ্ছেঃ ব্যক্তিগত পর্যায় ও সমষ্টিগত পর্যায়। প্রথমটি প্রত্যেকটি মুসলমানের কর্তব্য আর দ্বিতীয়টি সরকারী ক্ষমতাসম্পন্ন সংস্থার দাযিত্ব। ইসলামী সমাজে এ দুটি পর্যায়ের কাজই সর্বক্ষণ চালু থাকা একান্তই আবশ্যক।
সরকার সংস্থার দায়িত্ব
সামষ্টিক ও সরকারী পর্যায়ে ‘অমর বিল মা’রূফ’ এ ‘নিহী আনিল মুনকার’ কাজের দায়িত্ব ও ব্যবস্থাকে আরবী ভাষায় এক শব্দে বলা হয় (আরবী**********) অর্থাৎ নির্বাহী কর্তৃত্ব। এই পর্যায়ের দায়িত্ব পালনের জন্য হযরত আলী (রা) ‘খলীফাতুল মুসলিমীন’ হিসেবে তাঁর অধীন নিযুক্ত জনৈক প্রশাসককে লিখেছিলেনঃ
(আরবী********)
তোমার অন্যতম কর্তব্য ও দায়িত্ব হচ্ছে নিজেকে রক্ষা করা এবং জনগণের অবস্থার উপর সজাগ-সতর্ক দৃষ্টি রাখা। এজন্য তোমাকে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। জেনে রাখবে, এ কাজের ফলে তুমি আল্লাহর নিকট থেকে যে সওয়াব পাবে, তা থেকে অনেক উত্তম, যা তুমি জনগণের নিকট থেকে পাবে।
এই পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে –নফল কাজ হিসেবে –এই দায়িত্ব পালনকরী এবং সরকার নিয়োজিত সংস্থার দায়িত্ব পালনকারীর মধ্যে কয়েকটি দিক দিয়ে পার্থক্য করা যেতে পারে। যেমনঃ
১. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থার কর্তব্যই হলো এই কাজ করা। এটা রাষ্ট্রের অর্পিত দায়িত্ব হিসেবেই পালনীয়। তাদের ছাড়া অন্যদের পক্ষে এ কাজ ‘ফরযে কিফায়া’ পর্যায়ের।
২. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেই সার্বক্ষণিকভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হবে। সে কাজ ছাড়া অপর কোন কাজে নিয়োজিত হওয়া বা সময় কিংবা কর্মশক্তি ব্যয় করার কোন অধিকার তার থাকতে পারে না। কিন্তু অন্যান্য লোকদের পক্ষে এ কাজ ছাড়াও অন্যান্য কাজে অংশ গ্রহণে কোন বাধা নেই। কেননা তাদের জন্য তা ‘নফল’ পর্যায়ের।
৩. যে কাজকে বাধাদান তার কর্তব্য, সে কাজের প্রতি তার থাকতে হবে পরম শত্রুতা। সেজন্য প্রয়োজনমত শক্তি প্রয়োগও তার কর্তব্যভুক্ত। অন্যান্যদের জন্য তা নয়।
৪. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থাকে এই কাজের জন্য যখনই এবং যেখান থেকেই ডাক আসবে তাতে মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না করেই সাড়া দিতে হবে। অন্যান্যদের জন্য তা কর্তব্যভুক্ত নয়।
৫. তার অধিকার রয়েছে ‘মুনকার’ দমনের জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী নিয়োগ করার। কেননা তাকে তো কেবল এই কাজের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে এবং যে-কোন ভাবে তাকে তা সম্পন্ন করতেই হবে। আর সেজন্য তাকে অবশ্যই শক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রমশালী হতে হবে। অন্যন্যদের জন্য ততটা করা জরুরী নয়।
৬. প্রকাশ্যভাবে ‘মুনকার’ কাজ সংঘটিত হয়ে থাকলে তাতে ‘তা’জীর’ করা –উপস্থিত ভাবে শাস্তি দান –করার অধিকার রয়েছে। তবে তাতে সীমালংঘনের কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু অন্যান্য লোকদের পক্ষে ‘তা’জীর’ বা শাস্তিদানের –অন্য কথায় আইন হাতে লওয়ার কোন সুযোগ বা অধিকার থাকতে পারে না।
৭. সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থার বেতন-ভাতা বায়তুলমাল থেকে দিতে হবে। নফল কাজ হিসেবে যারা এই কাজ করবে, বায়তুলমাল থেকে তাদেরকে বেতন-ভাতা দেবার কোন ব্যবস্থা থাকতে পারে না।
সরকার নিয়োজিত ব্যক্তি বা সংস্থা এবং নফল কাজ হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে এই কর্তব্য পালনকারীর মধ্যে মোটামুটি এ-ই হচ্ছে পার্থক্যের বিভিন্ন দিক।
(আরবী***********)
উপরে এই কথাগুলি কুরআন ও সুন্নাহ ঘোষিত বিধানের আলোকে-নিঃসৃত। আর ও সবই সাধারণভাবে সর্ব মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ। ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মধ্যে এগুলি নিবিড় ও গুরুত্বপূর্ণ ভাবে অন্তর্ভুক্ত। এই প্রেক্ষিতে একথাও স্পষ্ট যে, সরকারী সংস্থার কাজ নিছক ‘ওয়ায’নসীহতের সাহায্যে ‘মুনকার’ প্রতিরোধ করা নয়, তাদের কর্তব্য, ওয়ায-নসীহতের পর্যায় অতিক্রম করে প্রয়োজনমত শক্তি নিয়োজিত করা। কেননা এ ছাড়া সামষ্টিকভাবে শান্তি শৃঙ্খলা (Law and order) স্থাপিত ও রক্ষিত হতে পারে না, পারে না জনগণের জান-মাল-ইযযত আবরু’র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা। অথচ ইসলামী রাষ্ট্রের এটাই হচ্ছে অন্যতম প্রধান কাজ। শরীয়াত বিরোধী কাজকে কার্যত দমন ও প্রতিরোধ করা না হলে ‘ইসলামী হুকুমাত’ কায়েম করাই অর্থহীন ও নিষ্ফল চেষ্টা-প্রচেষ্ঠা মাত্র।
এই সংস্থার কার্যাবলীর একটি তালিকা এখানে উদ্ধৃত করা যাচ্ছে নমুনাস্বরূপ এ সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা দেয়ার জন্য মাত্রঃ
১. যাবতীয় হারাম যন্ত্রপাতি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, যিনা-ব্যভিচার, দর্ষণ ইত্যাদির ব্যাপারে ব্যাপক সতর্ক দৃষ্টি রাখা, যেন এই ধরনের কোন কাজ সমাজে হতেই না পারে। এই কাজ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বভুক্ত।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম-যিম্মী-নাগরিকদের সাধারণ সার্বিক অবস্থা এবং সেই সাথে তাদের কর্মতৎপরতার প্রতি তীক্ন সজাগ দৃষ্টি রাখা! তাদের অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার দিক দিয়ে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি হতে না পারে, কোনরূপ অবিচার-জুলুম, অধিকার হরণ বা বঞ্চনা ঘটতে না পারে –সেই সাথে তারা কোনরূপ রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হতে না পারে, সে বিষয়ে পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন। এই ব্যাপারও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরই।
৩. সাধারণ জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে সতর্কতা রাখা। কোনরূপ সংক্রামক রোগ বা মহামারী দেখা দিলে অবিলম্বে তা প্রতিরোধেরব্যবস্থা গ্রহণ। বিশেষভাবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই কাজ।
৪. ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেন-দেনের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখা, যেন নিষিদ্ধ পন্থায় এসব কাজ হতে না পারে। সুদ-ঘুষের কোন কাজ হতে না পারে, সে দিকে লক্ষ্য রাখা। এ কাজ অর্থ মন্ত্রণালয়েরও অধীন থাকবে।
৫. সামাজিক ও নৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনরূপ বিপর্যয় দেখা দিতে না পারে –পূর্ব থেকেই সে ব্যাপারে সজাগতা অবলম্বন এবং কোথাও পারস্পরিক ঝগড়া-ফাসাদ ও বিবাদ-সিবম্বাদ দেকা দিলে অনতিবিলম্বে প্রতিরোধমূরক পদক্ষেপ গ্রহণ, যেন বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটতে না পারে। এটি স্বরাষ্ট্র পর্যায়ের কাজ হলেও সামাজিক সংহতি ও সম্প্রীতি রক্ষার গুরুত্বের কারণে একটি স্বতন্ত্র মান্ত্রণালয় গড়ে তোলা যেতে পারে।
৬. জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির –বিশ্লেষণ করে ধাক্য-পানীয়-দ্রব্যাদি-পরিধেয় বস্ত্রাদির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে না পড়ে, সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ –কোন দিকে একবিন্দু অসুবিধা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গেই তা দূর করা। এটা খাদ্য বিভাগের দায়িত্বভুক্ত। খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল মিশ্রণকে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা একান্তই কর্তব্য।
৭. যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে নির্বিঘ্ন ও বাধা-প্রতিবন্ধকতা মুক্ত রাখা, যেন জনগণের যাতায়াত, সংবাদ আদান-প্রদান –প্রেরণ- গ্রহণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে কোনরূপ বিঘ্নতার সৃষ্টি হতে না পারে, পণ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি ও অভ্যন্তরীণ আগমন-নির্গমনে কোন অসুবিধা না হয়, তাও লক্ষ্য করতে হবে। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কোন দুর্নীতি বা ঠকবাজি চলতে দেয়া যাবে না।
৮. পরিমাপ যন্ত্র, নিক্তি, দাড়িপাল্লা, গজ-ফিতা, লিটার-মিটারের ক্ষেত্রে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ চালু করতে হবে। এসব ক্ষেত্রেও যাতে করে শরীয়াতের সীমা-লঙ্ঘিত হতে না পারে, তা অবশ্যই তীক্ন দৃষ্টিতে ও সদা কার্যকর নীতেতে পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
৯. শ্রমজীবীদের প্রতি মালিক বা মনিব পক্ষ থেকে কোনরূপ অবিচার, জুলুম বা পীড়ন না হয়, তা বিশেষ গরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখতে হবে। শ্রমজীবীদের মধ্যে কোনরূপ শ্রেণী-পার্থক্য করা চলতে পারে না। পেশাজীবীদের কার্যে বিঘ্ন না ঘটে, প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অবভাব বা দুষ্প্রাপ্যতা দেখা না দেয়, তাতে কোনরূপ একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা মজুদকরণ (Hoardings) না চলে তা গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে।
১০. শিক্ষাক্ষেত্রে কোন অচলাবস্থা দেখা না দেয়, শিক্ষকদের, ইমাম-মুয়াযযিনদের বেতন-ভাতায় অসুবিধা না ঘটে, ছাত্র শিক্ষকদের পারস্পরিক সম্পর্কের পতন না ঘটে, শিক্ষক ও ইমামগণের স্বকাজের যোগ্যতা-অযোগ্যতা যথার্থভাবে যাচাই-পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে থাকে, তার উপরও কড়া নজর রাখতে হবে।
১১. শিশু, বালক, স্ত্রীলোকদের অযত্ন, লালন-পালন-হিফাযতে কোনরূপ অসুবিধা দেকা দেয়া, কোনরূপ নীতিহীনতার অনুপ্রবেশ, অশিক্ষা-কু-শিক্ষার প্রচলন হওয়া ইত্যাদি ক্ষতিকর দিকগুলির প্রতি তীক্ন দৃষ্টি রাখতে ও তার প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।
১২. সর্বোপরি গোটা সমাজ ও লোক সমষ্টির সার্বিকভাবে ইসলামী আদর্শ পালন ও অনুসরণে কোনরূপ বক্রতা না আসে, জনগণ জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত ও বিভ্রান্ত না হয়, কোন একজন মানুষও ন্যায্য ও সুবিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত থাকতে বাধ্য না হয়, ন্যায়পরতা ও ইনসাফ সর্বাধিক গুরুত্ব পায় –সে ব্যাপারে পূর্ণ সজাগ থাকতে হবে। ইসলামী আইন ভঙ্গকারীরা সঙ্গে সঙ্গে বাধাগ্রস্থ হয় –এক্ষেত্রে কোনরূপ পৌন-পুনিকতার সুযোগ না ঘটে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে। অপরাধীকে উপস্থিত শাস্তি দিয়ে সর্বপ্রকারের অনাচার প্রতিরোধ করতে হবে। এই বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তির অবশ্যই বিশেষ যোগ্যতা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের অধিকারী হতে হবে। এ পর্যায়ে ইতিহাস দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদুন যা লিখেছেন, তার সারনির্যাস হচ্ছেঃ
‘আল-হাসবা’ হিসাব-নিকাশ গ্রহণ বা পর্যবেক্ষণ বিভাগের কাজকর্মও একটা দ্বীনী মন্ত্রণা বা বিভাগ রূপে গণ্য হয়। আর তা দ্বীনের তাবলীগেরই একটি শাখা ছিল। এই কাজের জন্য যোগ্য লোক বাছাই করার দায়িত্ব খলীফাতুল মুসলিমীন-এরই ছিল। সে যাকে পছন্দ করত, এই কাজে নিযুক্ত করত। পরে সে স্বীয় সাহায্যকারী যোগাড় করে নিত। লোকদের খারাপ কার্যকলাপ ও দুষ্কৃতির উপর কড়া নজর রাখত, খোঁজ-খবর নিত। এ ধরনের কাজের খোঁজ পেলে জরুরী প্রশাসনিক –শান্তিদান ও শিক্ষাদানের –পদক্ষেপ গ্রহণ করত। প্রত্যেকটি ব্যাপারে লোকদেরকে বাধ্য করত, যেন তারা সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার মত কোন কাজ না করে। যেমন পথ-ঘাটে ভিড় সৃষ্টি না করা, যানবাহনে ও ভারবাহী পশুর উপর অবাঞ্চনীয় দুর্বহ বোঝা না চাপানো, যেমন ঘর-বাড়ী ধ্বসে পড়ার আশংকা, তা সে সবের মালিকরা নিজেরাই যেন ধ্বসিয়ে দেয়, যেন হঠাৰ করে ধ্বসে গিয়ে পথের লোকদের বিপদে না ফেলে। পাঠশালা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শিক্ষকরা বালক-বালিকা ও শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত মারপিট না করে। মোটকথা, এই ধরনের কাজকর্মের দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের কাজ হতো। এই মন্ত্রণালয় অপেক্ষায় থাকতো না যে, এই ধরনের কাজকর্মের দায়িত্ব এই মন্ত্রণালয়ের কাজ হতো। এই মন্ত্রণালয় অপেক্ষায় থাকতো না যে, এই ধরনের ঘটনাগুলি মামলা হিসেবে তাদের নিকট আসবে, তার পরে তারা পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, বরং তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে এই ধরনের ব্যাপারাদির দেখাশুনা করত। এদিকে তারা কড়া দৃষ্টি রাখত। যা কিচুই তারা জানতে পারত, সে জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করত। সকল প্রকারের দাবি-দাওয়া শ্রবণ করার কোন দায়িত্ব তাদের ছিল না। বরং তাদের অর্থনৈতিক লেনদেন ও ব্যবসায়-ময়দানে যেসব ভুল ও দুর্নীতির কাজকর্ম হতো –যেমন োজনে –মাপে বেঈমানী ও চালবাজি করা, তা বন্ধ করা এই বিবাগের দায়িত্বভুক্ত ছিল। প্রাপ্য দিতে অস্বীকারকারী ও লুট-পাটকারীদের নিকট থেকে ঋণ আদায় করা ও আত্মসাৎ করা সম্পদ ফিরিয়ে দেয়া এই বিবাগের কাজ ছিল। এসব কাজ এমন, যাতে কোনরূপ সাক্ষ্য-সাবুদের প্রয়োজন পড়ে না। বিশেষ ধরনের কোন ‘রায়’ জানাবারও দরকার হয় না। সাধারণভাবে সংঘটিতব্য ও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারাদিই তাদের উপর সোপর্দ করা হতো এবং অতি সহজেই সিদ্ধান্ত ও করণীয় নির্ধারণ করা যেত। বিচার বিভাগের সাথে এ সবের কোন সম্পর্ক থাকত না। এসব কাজ সাধারণ প্রশাসনিকতার আওতার মধ্যে পড়ে।‘….. ফলে এই বিভাগের কর্মকর্তারা বিচার বিভাগীয কাজেরই সম্পূরক বা সহায়তাকারী হতো।
মুকাদ্দমা ইবনে খালদন (ম ৮০৮ হিঃ) পৃঃ ২২৫-২২৬।
সরকারী পর্যবেক্ষক-প্রশাসনিক সংস্থার যেসব দায়িত্বের কথা আল্লামা ইবনে খালদূন বলেছেন, তা প্রায় সবই সংস্কার-সংশোধন কাজ এবং সে জন্য ব্যাপক প্রশাসনিক ও নির্বাহী ব্যবস্থাপনার একান্তই প্রয়োজন। বর্তমান কালে এই ব্যাপক কাজ যথাযথ আঞ্জাম দেয়ার জন্য বিশেষ বিশেষ মন্ত্রণালয় গড়ে তোলা হয়ে থাকে। বর্তমান কালে এই কাজ যেমন ব্যাপক ও বিশাল, তেমনি যথেষ্ট মাত্রায় জটিলও। ইসলামী যুগে এজন্য তেমন ব্যাপক কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হতো না, হয় নাই। তখন কিছু সংখ্যক লোককে এই দায়িত্বে নিযুক্ত করা হলেই এবং তাদের সামান্য তৎপরতায়ই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারত। কেননা মানুষের মধ্যে আদর্শবাদিতা ও ঈমান প্রবল ও তরতাজা ছিল বলে সব দিকের পুঞ্জীভূত সব ক্লেদ-কালিমা ধুয়ে-মুছে পরিচ্ছন্ন করে দিত। সরকারী ‘ইহতিহাস’ বা ‘আল-হাসবা’ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যেমন সেই ঈমান ও আদর্শবাদে শিক্ষিত ও অনুপ্রাণিত ছিলেন, তেমনি জনগণও ছিল সে আদর্শের প্রতি পূর্ণ ঈমানদার ও উদ্বুদ্ধ। হযরত উমর (রা) খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবেই লোকদের সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ
(আরবী*************)
হে জনগণ! আমি তোমাদের নিকট যেসব কর্মচারী প্রেরণ করি, তা এজন্য নয় যে, তারা তোমাদের মারধোর করবে কিংবা তোমাদের ধন-মাল লুটে-পুটে নেবে। বরং আমি তাদেরকে তোমাদের উপর নিয়োগ করে পাঠাই এই উদ্দেশ্যে যে, তারা তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন –তোমাদের যাবতীয় রীতি-নীতি শিক্ষাদান করবে। তা সত্ত্বেও কোন কর্মচারী যদি উপরোক্ত ধরনের কোন সামান্য কাজও করে, তাহলে তা যেন আমার নিকট অবশ্যই পৌঁছানো হয়। যাঁর হাতে উমরের প্রাণ আমি তাঁরই কসম খেয়ে বলছি, আমি তার বিচার অবশ্যই করব।
অপর একটি বর্ণনায় তাঁর এই ভাষণের ভাষা এইরূপ উদ্ধৃত হয়েছেঃ
(আরবী**********)
হে জনগণ! আমি আমার কর্মচারীদের তোমাদের উপর এজন্য নিযুক্ত করিনি যে, তারা তোমাদের উপর বিপদ টেনে আনবে কিংবা তোমাদের ধন-মাল জোরপূর্বক কেড়ে নেবে। বরং আমি তাদের এজন্য নিযুক্ত করেছি যে, তারা তোমাদের উপর বিপদ টেনে আনবে কিংবা তোমাদের ধন-মাল জোরপূর্বক কেড়ে নেবে। বরং আমি তাদের এজন্য নিযুক্ত করেছি যে, তারা তোমাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ বা ঝগড়া-ফাসাদ প্রতিরোধ করতে এবং সরকারী ধন ভাণ্ডার থেকে তোমাদের প্রাপ্য তোমাদের মধ্যে বন্টন করে দেবে। সে লোকেরা এ ছাড়া অন্য কিছু করে থাকলে দাঁড়িয়ে তার বর্ণনা দাও।
(আরবী টীকা***********)
হযরত আলী (রা) খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে তাঁর নিযুক্ত মিসরের শাসনকর্তা মালিক আশতার নখয়ীকে বলেছিলেনঃ
(আরবী***********)
তোমার পরামর্শদাতা ও কর্মকর্তাদের মধ্যে খারাপ হচ্ছে তারা, যারা তোমার পূর্বে খারাপ লোকদের পরামর্শদাতা ও সহকারী ছিল এবং অন্যায় ও পাপের কাজে তাদের সাথে শরীক হয়েছিল। অতএব তাদের সঙ্গে তোমার কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক কখ্খনই হতে পারে না। কেননা তারা হচ্ছে অপরাধীদের সাহায্যকারী এবং জালিমদের ভাই।
(আরবী টীকা**********)
এই সব ঘোষণা থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানকে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালনে পরামর্শ ও সহযোগিতা দান, সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলার সংরক্ষণ, আইন কার্যকরকরণ –সর্বোপরি জনগণকে সব সময়ই দ্বীন-ইসলামের আইন-বিধান ও নিয়ম-নীতি শিক্ষাদানের জন্য সহকারী ও কর্মচারী নিযুক্ত করতে হবে। তারা সরাসরিভাবে জনগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে, তাদের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন ও কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবে এবং যে পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরী বিবেচিত হবে, তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করবে ও দেশের প্রধান দায়িত্বশীল –রাষ্ট্রপ্রধান –কে অবহিত করবে।
এই পর্যায়ে কুরআন-মজীদে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত মূসা (আ) মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছেনঃ
(আরবী****************)
আর আমার জন্য আমার নিজের পরিবারের মধ্য থেকে একজন সহকর্মী নির্দিষ্ট করে দাও। অর্থাৎ হারুন, যে আমার ভাই (তাকে)। তার সাহায্যে আমার হস্ত মজবুত করে দাও এবং আমার কাজে তাকে শরীক বানিয়ে দাও।
আল্লাহ তা’আলা হযরত মূসা (আ)-র এই দোয়া কবুল করেছিলেন। তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ
(আরবী*****************)
এবং আমরা নিশ্চিতভাবেই মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে ‘অজীর’ বানিয়ে দিয়েছিল।
হযরত মূসা (আ)-র দোয়ায় এবং আল্লাহর নিজের ঘোষণার –উভয় আয়াতেই (আরবী*********) ‘অজীর’ শব্দটির ব্যবহার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। (আরবী******) শব্দটি (আরবী*****) থেকে নির্গত। এর অর্থ, বোঝা। আর (আরবী**********) অর্থ উপদেষ্ঠা, সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীলের সাহায্যকারী প্রশাসনিক বোঝা ও দায়দায়িত্ব বহনকারী, তার সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষকতাকারী। (আরবী টীকা**********) নবী করীম (স) নব্যয়্যাত লাভের পর একটি ভাষণে বলেছিলেনঃ আরবের কোন যুবকই সেই লক্ষ্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেনি, যা আমি নিয়ে এসেছি। তোমাদের মধ্যে এমন কে কে আছে, যে এই পদের গুরুদায়িত্ব পালনে আমার ওয়াজীর হতে প্রস্তুত রয়েছে? (আরবী টীকা*******) বস্তুত ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে রাসূলে করীম (স)-এর এই দাবিই অঅমাদের জন্য আইনের ভিত্তি। হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা)-ই সর্ব প্রথম নবী করীম (স)-এর ‘ওয়াজীর’ হিসেবে মক্কায় তাঁর সব দায়িত্ব পালনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। (আরবী টীকা************)
রাষ্ট্রের –যে কোন কাজের –সর্বোচ্চ দায়িত্বশীলের যে সাহায্যকারী, পৃষ্ঠপোষক এবং তার পক্ষ থেকে আইন কার্যকরকরণ ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনকারী লোক নিযুক্ত করা একান্তই প্রয়োজন, তা এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। ইসলাম এ প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছে। নবী করীম (স) ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল হিসেবে বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট কাজের অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির উপর অর্পণ করেছেন, প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রশাসনিক এলাকার বিভিন্ন অংশে দায়িত্বশীল নিয়োগ করেছেন। তবে তাঁর এই নিয়োগকৃত লোকেরা তাঁর ‘ওয়াজীর’ নামে অভিহিত হতেন না, আসলে তারা কেউ গভর্ণর (আরবী*********) বা কেউ কর্মচারী (আরবী*********) রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে। তাঁর সময়ের উপযোগী প্রশাসনিক সংস্থাই তিনি গড়ে তুলেছিলেন এ সব লোকের সমন্বয়ে। উত্তরকালে এলাকার সম্প্রসারণ ও প্রশাসনিক দায়িত্বের গুরুত্ব বৃদ্ধির সাথে এই প্রশাসনিক সংস্থার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ সংঘটিত হয়েছে।
রাসূলে করীম (স)-এর যুগে প্রশাসনিক দায়িত্বশীলদের প্রশিক্ষণ
রাসূলে করীম (স) যখনই কোন সাহাবীকে কোন অঞ্চলের প্রশাসনিক দায়িত্বশীল নিযুক্ত করে পাঠাতেন, তখনই তাকে প্রকৃত ইসলামী আদর্শানুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা ও অন্যান্য প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করতেন। এই পর্যায়ের কয়েকটি ঐতিহাসিক প্রশিক্ষণমূলক ভাষণের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ
হে মুয়ায! তুমি লোকদেরকে আল্লাহর কিতাব –কুরআন-শিক্ষা দান করবে। তাদেরকে অতীব উত্তম ও পবিত্র নৈতিক চরিত্র ও আদব-কায়দা শেখাবে। লোকদেরকে তাদের বাসগৃহে অবস্থান করতে দেবে –যে ভালো লোক তাকেও এবং যে মন্দ লোক তাকেও। আর তাদের মধ্যে আল্লাহর বিধান কার্যকর করবে, তাঁর আদেশ ও নিষেধসমূহ বাস্তবায়িত করবে, তা অনুসরণে তাদেরকে বাধ্য করবে। তাদের কাজকর্মে কোনরূপ অসুবিধার সৃষ্টি করবে না, কারোর ধন-মালের ব্যাপারেও কাউকে কাতর করে তুলবে না। কেননা তা তোমার কর্তৃত্বের অধীন নয়। সে ধন-মালও তোমার নয়। তাদের রেখে যাওয়া আমানত তাদের নিকট ফিরিয়ে দেবে, তার পরিমাণ কত হোক কি বেশী। জনগণের প্রতি দয়ার্দ্রতা, সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা দেখাবে –অবশ্য সত্যের দাবিকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করে নয়। কেননা তা হলে লোকেরা অভিযোগ তুলবে যে, তুমি আল্লাহর হককে পরিহার করেছ। যেসব ব্যাপারে তুমি ভয় করবে যে, তোমার কর্মচারীর দোষক্রটির বোঝা তোমার উপর আসবে, সেসব ব্যাপারে আগেই তাদের সতর্ক করে দেবে। অন্যথায় সব দোষ তোমার উপরই চাপানো হবে। জাহিলিয়াতের সমস্ত নিয়ম-নীতি, প্রথান-প্রচলন ও আনুষ্ঠিানিকতা বন্ধ করে দেবে, চালু রাখবে শুধু তা যা ইসলাম প্রবর্তন বা সমর্থন করেছে।
ইসলামের প্রত্যেকটি কাজ ও ব্যপারকে প্রকাশমান প্রকট ও বিজয়ী করে তুলবে –তা ক্ষুদ্র হোক, কি বৃহৎ। তবে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করবে সালাত কায়েমের ব্যাপারে। কেননা দ্বীন কবুল করার পর তা-ই হচ্ছে ইসলামের শির। লোকদেরকে তুমি নসীহত করবে আল্লাহর নামে –তাদের স্মরণ করিয়ে দেবে আল্লাহ ও পরকালকে। লোকদেরকে উপদেশ দান করতেই থাকবে, কেননা তা-ই মানুষকে আমল করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের বড় হাতিয়ার, যে আমল আল্লাহ খুবই পছন্দ করেন। এছাড়া জনগণের মধ্যে শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ দানের দায়িত্বশীল লোকদেরকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঠিয়ে দেবে তুমি দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহর –তারঁই নিকট ফিরে যেতে হবে। আর এ সব কাজে তুমি কোন উৎপীড়কের উৎপীড়নকে বিন্দুমাত্র ভয় করবে না।
আমি নিজে তোমাকে অসীয়ত করছি আল্লাহকে ভয় করে চলার ও সত্য কথা বলার, ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি পূরণের, আমানত ফিরিয়ে দেয়ার, খিয়ানত –আত্মসাৎ ও বিশ্বাস ভঙ্গ পরিহার করার, নম্র কথা বলার, সালাম দেয়ার, প্রতিবেশীর রক্ষণাবেক্ষণের, ইয়াতীমের প্রতি দয়া-অনুকম্পা প্রদর্শনের, নেক আমলের, কামনা-বাসনা খাটো করার, পরকালকে অধিক ভালোবাসার, বিচার-দিনের হিসাব-নিকাশকে বেশী ভয় করার, সর্বাবস্থায় ঈমান রক্ষা করার, কুরআন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করার, ক্রোধ হজম করার ও খিদমতের বাহু সকলের জন্য বিছিয়ে দেয়ার।
কোন মুসলিমকে গালাগাল করা থেকেও দূরে থাকবে। কোন ন্যায়বাদী ও সুবিচারকারী রাষ্ট্রীয় নেতাকে অমান্য করা কিংবা সত্যবাদীকে অসত্যবাদী মনে করার কাজ কখনই করবে না। মিথ্যাবাদীকেও সত্যবাদী বলে মানবে না। প্রতি মুহূর্তই তুমি তোমার রব্বকে স্মরণ করবে, যখনই কোন গুনাহ হবে, সেজন্য তাঁর নিকট নতুন করে তওবা করবে। গোপনীয় গোপন রাখবে, প্রকাশ্যকে প্রকাশ্যভাবেই করবে।
হে মুয়ায কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমার সাথে আমার আর কখনই সাক্ষাৎ হবে না এই কথা যদি আমি মনে না করতাম তাহলে তোমাকে এই দীর্ঘ ‘অসীয়ত’ করতাম না, সংক্ষিপ্ত কথা বলেই ছেড়ে দিতাম। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সম্ভবত এ দিনুয়ায় তোমার সাথে আর কখনই আমার সাক্ষাৎ হবে না……….
শেষ কথা হিসেবে তুমি জানবে হে মুয়ায! তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হবে ঠিক সেইরূপ’ অবস্থায়, যেরূপ সে আমার নিকট থেকে বলে গিয়েছিল।
(আরবী টীকা**************)
এমনিভাবে রাসূলে করীম (স) হযরত আমর ইবনুল আ’স (রা)-কে বনুল হারিস গোত্রের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। তাদেরকে দ্বীন-ইসলামের সূক্ষাতিসূক্ষ্ম শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, রাসূলের সুন্নাত ও ইসলামের বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব নিদর্শনাদি শিক্ষাদানের জন্য। সেই সাথে যাকাত আদায়করণও তাঁর কর্তব্যভূক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাকেঁ একখানি ‘লিপি’ তৈয়ার করিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে তাকেঁ নিয়োগ দিয়েছিলেন এবং তাঁর ফরমানও লিপিবদ্ধ করিয়েছিলেন। সে ‘লিপি’ নামা ছিল এইঃ
মহান আল্লাহর নামে –যিদি অতীব দয়াবান ও অশেষ অনুগ্রহশীল ‘এটা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে ঘোষণা পত্র’।
হে ঈমানদারগণ, তোমরা চুক্তিসমূহ যথাযথ পূর্ণ কর। মুহাম্মদ আল্লাহর নবী –রাসূল –আমর ইবনে হাজমকে ইয়ামের প্রেরণকালে তার জন্য লিখিত চুক্পিত্র।
তিনি তাঁর সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ তা’আলাকে ভয় করার নির্দেশ দিলেন। কেননা আল্লাজহ তো তাদের সঙ্গে রয়েছেন, যারা তাকেঁ ভয় করে চলে। আর যারা সকল কাজে সর্বোচ্চ মানের কল্যাণ ও দয়াশীলতা অবলম্বন করে।
তিনি তাকেঁ নির্দেশ দিলেনঃ তিনি যেন গ্রহণ করেন সত্যের ভিত্তিতে –যেমন স্বয়ং আল্লাহ তাকেঁ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি যেন জনগণকে পরম কল্যাণের সুসংবাদ দেন এবং তা অবলম্বনের আদেশ করেন। তিনি যেন লোকদেরকে কুরআন শিক্ষা দেন, তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন করান, তার ব্যবহারিক আইন-কানুন জানান। পবিত্র অবস্থা ছাড়া কুরআন স্পর্শ করতে তিনি যেন লোকদেরকে নিষেধ করেন। যে কল্যাণ জনগণের জন্য এবং যা জনগণের কর্তব্য, তা সবই যেন তিনি তাদেরকে জানান। সত্য দ্বীনের ব্যাপারে তিনি যেন লোকদের সাথে নম্রতা রক্ষা করেন, আর জুলুম প্রতিরোধে তিনি সর্বাধিক কঠোরতা অবলম্বন করেন। কেননা আল্লাহ জুলুমকে তীব্রভাবে ঘৃণা ও অপছন্দ করেন। তা করতে তিনি নিষেধ করেছেন। বলেছেনঃ
(আরবী****************)
জেনে রাখো, জালিমদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।
তিনি যেন লোকদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেন, জান্নাত পাওয়ার উপযোগী আমল করতে উদ্বুদ্ধ করেন। লোকদেরকে যেন জাহান্নামের ভয় দেখান। জাহান্নামে যাওয়ার কাজ করতে নিষেধ করেন। তিনি যেন লোকদেরকে নতুন করে দ্বীন-ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন, অবহিত করেন। এ ছাড়া আল্লাহ আর যা যা করতে বলেছেন, তা-ও যেন জানিয়ে দেন আর বড় হজ্জই হচ্ছে বড় হজ্জ, উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ্ব।
(আরবী টীকা**********)
উদ্ধৃত দুইটি নিয়োগপত্র থেকে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে, রাসূলে করীম (স) তাঁর সাহাবীগণের মধ্যে যে লোককে –প্রয়োজনীয় কার্যসমূহের মধ্যে –যে কাজের যোগ্য মনে করতেন, তাকেঁ সেই কাজে নিযুক্ত করতেন, সেই কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব-ও দিতেন। আর শুধু নিয়োগপত্র দিয়েই তাকেঁ পাঠিয়ে দিতেন না, তাকেঁ কাজ সম্পর্কে পূর্ণ প্রশিক্ষণও দিতেন। তাঁর কাজের প্রকৃতি কি, কি মনোভাব নিয়ে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে, কি নিয়ম-নীতি তাকেঁ মেনে চলতে হবে, জনগণের সাথে তাঁকে কিরূপ আচরণ গ্রহণ করতে হবে, সব কথা-ই তিনি তাঁকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতেন। আর এ ভাবেই তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সমগ্র ইসলামী রাজ্যে একটি সুসংবদ্ধ প্রমাসনিক কাটামো গড়ে তুলেছিরেন।
তিনি ডাক যোগাযোগ রক্ষার জন্যও দায়িত্বশীল কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন এবং তাদের জন্যও তিনি তাদের কাজের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। তখনকার সময় চিঠি-পত্রের আদান প্রদান সাধারণত সরকারী পর্যয়েই হতো এবং লোক মারফত সে পত্রাদি প্রেরণ করা হতো। এই কারণে তিনি এ পর্যায়ে নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ
(আরবী*************)
তোমরা যখন আমার নিকট কোন পত্রবাহক পাঠাবে, তখন তোমরা অবশ্যই ভালো চেহারার ও ভালো নামের ব্যক্তিকে পাঠাবে।
-(আরবী টীকা*************)
আর যে লোককে কোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পত্র দিয়ে কোথাও পাঠাতেন, তখন তাকে উপদেশ দিতেনঃ
তুমি যখন তাদের দেশে যাবে,তখন রাত্রি কালে তথায় করবে না। বরং সকাল বেলায় প্রবেশ করবে। উত্তমভাবে পবিত্রতা অর্জন করে প্রবেশ করবে।তার পূর্ব দু ‘রাকয়ত নামায পড়ে নেবে। আর আল্লাহর নিকট সাফল্য ও শুভ গ্রহণের জন্য দোয়া করে নেবে সে জন্য পূর্ব মাত্রায় চেষ্টাও করবে। আর আমার পত্র ডান হাতে নিয়ে তাদের ডান হাতে তুলে দেবে [আরব টীকা………]
তিনি পাহারাদারও নিযুক্ত করতেন। বিশেষ করে রাত্রিকালে সন্দেহভাজন লোকজন দেখা গেলে তাদের উপর নজর রাখার জন্য বিশেষ লোক নিযুক্ত করতেন। পাহারাদার হিসেবে হযরত সায়াদা ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা)-এর নাম উল্লেখ্য। অনেক অনেক অস্বাভাবিক সময়েও তাঁর জন্য পাহারাদার নিযুক্ত থাকত। উল্রেখ্য করা হয়েছে যে, হযরত সায়দা ইবনে মুয়ায (রা) বদর যুদ্ধ কালে তাঁর পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন।[আরবী টিকা……….]
তখন হাটে-বাজারে পণ্য দ্রব্য বহন করে নিয়ে আসা লোকদের নিকট থেকে সস্তায় পণ্য ক্রয়ের জন্য বাজার থেকে দূরে পথের পার্শ্বে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকত এবং পণ্য বহনকারীরা পথিপার্শ্বে দাঁড়িয়ে থাকা এই লোকদের নিকটই পণ্য বিক্রয় করে দিত। ফলে মূল বাজারের পণ্যের আমদানি পর্যন্ত পরিমাণে হতো না। রাসূলে করীম (স) এই কাজ করতে নিষেধের হুকুম দেয়ার জন্য হযরত সাঈদ ইবনে সঈদ আল-আস (রা)-কে নিযুক্ত করেছিলেন [আরবী টিকা……….]
রাসুল করীম (স)-এর রাষ্ট্রীয় পত্রাদি লেখার জন্য বিশেষ বিশেষ লোক নিযুক্ত ছিল। কোন রাজা-বাদশাহ, শাসনকর্তা, দলপতি বা কবীলা-প্রধানের নিকট তিনি যেসব পত্রাদি প্রেরণ করতেন, এই কাজে নিযুক্ত লোকেরা তা লিখত ও রাসূলে করীম (স)-এর মোহর লাগিয়ে তা প্রেরণ করত। যাদের প্রতি এ সব পত্র প্রেরণ করা হতো, তারা ভিবিন্ন ভাষাভাষী হতো বলে ভিবিন্ন ভাষাবিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ করেছিলে। আধুনিক সরকারী ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিতে তা ছিল একটি ছোট-খাটো সচিবালয় [আরবী টিকা……..]
এ ভাবে রাসুলে করীম (স)- তাঁর রাষ্ট্রীয় কাজ সুসম্পন্ন করার জন্য বহু সংখ্যক সাহায্যকারী কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। যোগ্যতা অনুযায়ী এক-একজন বা একাধিক লোকের উপর এক-একটি কাজের দায়িত্ব অর্পিত হতো। আর এই সকালের সমম্বয়েই তখনকার সময় ও প্রয়োজন উপযোগী এক পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর ও বাস্তবায়িত করাই ছিল এ সবের চরম লক্ষ।
প্রশাসনিক দায়িত্ব নিযুক্ত লোকদের জরুরি গুণাবলী
বস্তুত প্রশাসনিক বিভাগ-ই রাষ্ট্রের প্রকৃত আদর্শ, রীতি-নীতি ও সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করার প্রধান হাতিয়ার। এই বিভাগের পূর্ণ দক্ষতা ও কার্যকরতার উপর শধু যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের যর্থাথ বাস্তবায়ন নির্ভরশীল তা-ই নয়, রাষ্ট্রের সাফল্য স্থিতিও এরই উপর নির্ভর করে। কেননা জনগণের সাথে এই বিভাগের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জনগণের যাবতীয় সমস্যার সমাধান, প্রয়োজন পূরণ যেমন এই বিভাগের দায়িত্ব, তেমনি জনগণকে সঠিক পথে পরিচালন, আদর্শের দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন বিচ্যুতি লংঘন-উপেক্ষা দেখা গেলে তা থেকে তাদের বিরত রাখা ও তাদের সংশোধন ইত্যাদি যাবতিয় কাজ প্রশাসনিক বিভাগের আঞ্জাম দিতে হয়। গোটা দেশের সাধারণ শান্তি-শৃঙ্খলা(law and order)রক্ষা করা ও জনগণের অধিকার আদায় করা এই বিভাগেরই কর্তব্যভুক্ত।
এই বিভাগের যাবতীয় কাজ যথার্থভাবে আঞ্জাম পাওয়া এই বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিশেষ গুণের উপর নির্ভরশীল। সেই গুণ না থাকলে তারা যেমন অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে না, তেমনি জনগণের পক্ষে ও একবিন্দু শান্তি. নিরাপত্তা ও অধিকার পাওয়া সম্ভবপর হতে পারে না।
এইখানে কতিপয় প্রয়োজনীয় গুণের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ
১. দক্ষতা ও বিশেষজ্ঞতাঃ যে লোককে যে কাজে নিযুক্ত করা হবে বা যে লোকের উপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হবে, সেই কাজটি নিখুঁতভাবে করার যোগ্যতাই যদি তার না থাকে, তাহলে সবকিছুই নিষ্ফল হয়ে যাওয়া অবধারিত। কুরআন মজিদ এই দিকে যে গুরুত্ব আরোপ করেছে, তা আল্লাহর এই নির্দেশ থেকেই স্পষ্ট হয়ঃ [আরবী লেখা……]
তোমরা নিজের না জানলে জ্ঞানবান লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা কর। এ নির্দেশে প্রত্যেকটি ব্যাপারে দক্ষ-অভিজ্ঞ লোকদের নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয় জ্ঞান গ্রহণের উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা নিজের জানা থাকলে তো সে তার উপর অর্পিত কাজ করতে সক্ষম হবে না। এই কারণেই নবী করীম (স)-ইরশাদ করেছেনঃ[ আরবী লেখা…………..]
কোন কাজের প্রধানত্ব কেবলমাত্র সেই ব্যাক্তির জন্যই শোভন, যে তার যোগ্যতা রাখে।[আরবী টিকা………]
তিনি আরও বলেছেনঃ [আরবী…………] যে লোক না জেনে-শুনে কাজ সে সে কাজটিকেই অনেক বেশী বিনষ্ট করে দেবে তার তুলনায় যে সে কাজের যোগ্যতা রাখে। মূলত যে কা যার জানা নেই বা যা কারার যার যোগ্যতা ও দক্ষতা নেই,তার উপর সেই কাজের দায়িত্ব অর্পণ সেই কাজটিকেই বিনষ্ট ও বিপর্যস্ত করার নামান্তর। সেই কাজটির পরিণতি খারাপ হওয়ার নিশ্চিত ব্যবস্থা মাত্র। সাধারণ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারেও এ কথার যৌক্তিকতা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। তাহলে সমষ্টিক ও রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ র্কাযাবলীর ক্ষেত্রে অযোগ্য লোককে নিয়োগ ও দায়িত্বভার অর্পণ কতখানি মারাত্মক ও সমষ্টিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে ও যুক্তি দিয়ে বলার প্রয়োজন পড়ে না। এ কারণেই এই বচনটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকৃতব্যঃ [আরবী লেখা……]
যোগ্য স্থানে যোগ্য লোক নিয়োগই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। আর যোগ্য স্থানে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ চরম নির্বুদ্ধিতা ছারা আর কিছু নয়।
২. বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতাঃ কর্মের যোগ্যতা-দক্ষতার পর প্রয়োজনীয় বিশেষ গুন হচ্ছে বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতা, সরকারী দায়িত্বশীলের আমানতনদার হওয়া। কেননা সরকারী পর্যায়ে যত অসুবিধা ও জন-জবিনে যত দঃখ্ দুর্দশা ও অবিচারের কারণ ঘটে, তার বেশীর ভাগই হয় দায়িত্বশীল কর্মকর্ত ও কর্মচারীদের অবিশ্বস্ততা, অ-নির্ভরযোগ্যতা ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে-আমানতে খিয়ানত করার কারণে। তাদের মধ্যে উক্ত গুণ না থাকার দরুন কত সরকারী চিন্তা-ভাবনা পরিকল্পনা যে ব্যর্থ হয়ে যায়, আদর্শ বিচ্যুতি ঘটে কত এবং তার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া জনগণের উপর যে কত শোষণ নির্যাতনের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে, তা লিখে শেষ করা যায় না। এ কারণেই কুরআন মজীদ সকল প্রকারের কল্যাণের জন্য কেবলমাত্র যোগ্য ও বিশ্বত্ব কর্মচারীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বেলেছনঃ [আরবী লেখা………….]
তোমার জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হতে পারে সেই ব্যক্তি, যে দক্ষ-শক্তিমান, ব্শ্বিস্ত। মনে করা যেতে পারে,কথাটি বলেছিলেন হযরত মূসা (আ) মাদইয়ান উপস্থিত যে দুইজন যুবতী বোনের জন্তুগুলিকে জনাকীর্ণ কূপ থেকে পানি খাইয়ে দিয়েছিলন, তাদেরই একজন তাঁদের বৃদ্ধ পিতাকে লক্ষ করে। তাঁরা তাঁকে ঘরের কাজকর্ম ও ছাগল চরানোর কাজে ‘মজুর’ হিসদের ঘরে রেখে দিয়ে চেয়েছিলেন। কুরআনে এর উল্লেখ আদৌ তাৎপর্যহীন নয়।
ঘর-গৃহস্থালী ও ছাগল চরানোর কাজে লোককে যদি দক্ষ, শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত হতে হয়- যা একটি বিশষে পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে-তাহলে জাতীয়, সমাষ্টক ও রাষ্ট্রীয় কাজে যোদ্যতাসম্পন্ন দক্ষ ও বিশ্বস্ত-নির্ভরযোগ্য লোক নিয়োগের গুরুত্ব যে কত বেশী, তা না বললেও চলে।
৩. দুনিয়া-বিমুখতা ও সততা-সচ্চরিত্রতাঃ দুনিয়া বিমুখ [ আরবী***** ] বলতে এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে বৈষয়িক সুখ-শান্তি অন্যায়ভাবে লাভ করার প্রতি আগ্রহী নয়, যে লোক অল্প পেলেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।
সরকারী ও প্রসাশনীক দায়িত্বে এই গুণের লোকদের নিয়োগ করা হলে সরকার যন্ত্রে কোনরূপ ঘুণ প্রবেশ করতে পারে না। সে লোক পদাধিকারের সুযোগে দুর্নীতির মাধ্যমে যেমন অর্থপার্জন করতে সচেস্ট হবে না, তেমনি কোন অন্যায় সুযোগ গ্রহন থেকেও পূর্ণ সতর্কতার সাথে দূরে সরে থাকবে। তার দ্বারা যেমন সরকারের কোনরূপ ক্ষতি সাধিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে না, তেমনি জনগণের অধিকার হরণ বা তাদেরকে জ্বালা-যন্ত্রণা দেয়ার-তাদের অধিকার হরণের মত কোন কাজ হওয়ার সম্ভাবনাওনিঃশেষ হোয় যাবে। সে উপস্থিত স্বার্থের জন্য কিছুমাত্র কাতর হবে না, দর্নীতির আশ্রয় দিয়ে জনগণের পকেটেও হাত দেবেনা। এ পর্যায়ে গযরদ আলী (রা)-র এ কথাটির গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্যঃ [আরবি………]
ন্যায়বাদী রাষ্ট্র নেতাদের জন্য আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন যে, তারা যেন জনগণের দুর্বলতার অনুপাতে তাদের জীবিকার পরিমান নির্ধারন করে।
তাহলে তারা তাদের দারিদ্রের সুযোগে কোন অন্যায় কাজ করে বসবে না। শুধু তা-ই নয়, সরকারী-দায়ীত্বশীল লোকদের উচ্চতর ও পবিত্রতর নৈতিক চরিত্রের গুণে ভূষিত হওয়াও আবশ্যক। দুনিয়ার প্রতি লোভহীনতা কোন নেতিবাচক গুণ নয়। বরং তা হওয়া উচিত পুরামাত্রায় ইতিবাচক। তার মধ্যে ধৈর্য-স্থৈর্য ও সহনশীলতাও থাকতে হবে। পুরোপরি ইসলামী আদর্শবাদে উদ্বুদ্ধ হওয়ার কারণেই হতে হবে এইসব মহৎ গুণের অধিকারী।
অন্যথায় জনগণ যেমন তাদের প্রতি একবিন্দু আস্থাশীল হবে না, তেমনি তারাও কোন কাজে জনগণের একবিন্দু সহযোগিতা পাবে না। আর সেই সহযোগিতা না হলে গোটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও যৌক্তিই অর্থহীন হয়ে যাবে।
বিচার বিভাগ
বিচার কার্য ও জনগণের মধ্যকার পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসাকরণ দ্বীন-ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সাধাণরভাবে সমস্ত মানব সমাজেই তা মানবতার সেবায় বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কেননা এ কার্যটি সুষ্ঠরূপে সুসমাপন্ন হওয়ার উপরই গোটা সমাজের নিরাপত্তা, সমাজের লোকদের মনে শান্তি স্বস্তি ও নিশ্চিন্ততা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বস্তুত যে সমাজে বিচার নেই জনগণের ফরিয়াদ পেশ করার কোন স্থান নেই এবং তার প্রতিকার করারও কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই, তা বন্য সমাজ হতে পারে, পাশবিক সমাজ হতে পারে, তা কখনই মানুষের বাসোপযোগী সমাজ হতে পারে না। মানুষের জন্য শুধু বিচার নয়, সুবিচারের প্রয়োজন। ফরিয়াদ পেশ করার একটা স্থান থাকাই যথেষ্ট নয়, তা মনোযোগ সহকারে ও অনুকম্পাপূর্ণ অন্তর নিয়ে শুনবার এবং তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও ইনসাফপূর্ণ প্রতিকারের কার্যকর ব্যবস্থা থাকাও একান্তই আবশ্যক। অন্যথায় মানুষের জীবন মানবোপযোগী জীবন হওয়ার ও সে সমাজ মানুষের মানবীয় মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব হতে পারে না। এই দৃষ্টিতে বিশ্বের সমাজসমূহের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হলে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হবে যে, ইসলামী সমাজ দুনিয়ার সমাজসমূহের মধ্যে যেমন বৈশিষ্টপূর্ণ, তেমনি তুলনাহীন। ইসলামী সমাজে শুধু বিচার নেই, আছে সর্বতোভাবে ন্যায়সঙ্গত নিরপক্ষ ও আদর্শভিত্তিক সুবিচার। এ সুবিচার ও ইনসাফ ইসলামী সমাজে মানুষকে দেয় পূর্ণ মানবীয় মর্যাদা নিয়ে বসবাস করার নির্বিঘ্ন সুযোগ। নিয়ে আসে পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা, প্রতিষ্ঠিত করে স্থিতিশীলতা, প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য নিশ্চিত করে তার মানবীয় অধিকার ও মর্যাদা, মানবিক ও মৌলিক অধিকার, তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা। পরিণামে গোটা সমাজই হয় সর্বদিক দিয়ে পুরোপুরিভাবে ভারসম্যপূর্ণ। বিচারের সাথে সুবিচারের সম্পর্ক গভীর ও ওতপ্রোত।বিচার যদি শুধু বিচার না পরিপূর্ণ সুবিচার হয়, তাহলেই সমগ্র সমাজ হতে পারে ন্যায়পরতায় পরিপূর্ণ। সমাজকে ভরে দিতে পারে অভিনব শান্তি-শৃঙ্খলা,সাহসিকতা ও কর্মোদ্দী পনায়। মানুষ তখন তার নিজের প্রান-মান, ধন-মাল ও ইযযত-আবরুর দিক দিয়ে হতে পারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। আর তার ফলে গোটা রাষ্ট্রই হতে পারে সমৃদ্ধিশালী ও কল্যণময়। কিন্তু তা-ই যদি বিচারের নামে চলে জুলুম-শোসণ-নির্যাতন. সুবিচার বলতে কোথাও কিছু খঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে চতুর্দিক অরজকতা উচ্ছঙ্খলতা, মারামারি, অপহরণ-ছিনতাই, হত্যা নারী হরণ বলাৎকার ও চুরি-ডাকাতি-লুণ্ঠন দেখা দেয়া অবধারিত । সমগ্র সমাজটাই হয় চারমভাবে বিপর্যস্ত। মানুষ তখন বেঁচে থেকে শান্তি পায় না। শান্তির জন্য যমীনের তলায় আশ্রয় নেবার জন্য মানুষ হয়ে উঠে উদগ্রীব। আর তারা ফলে রাষ্ট্র তার সমস্ত মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। শাসনকার্য সম্পূর্ণরূপে ব্যাহত ও বিঘ্নিত হয়ে পড়ে, সার্বভৌমত্ব হয়ে পড়ে বিপন্ন। আর শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত ধ্বসই হয় পড়ে ললট লেখন।
মোটকথা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ন্যায়পরতা ও সুবিচার। ন্যায়পরতা ও সুবিচারহীন রাষ্ট্র ‘ইসলামী’ নামে অভিহিত হতে পারে না। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতেও তা ‘রাষ্ট্র’ নামে পরিচিতি হওয়ার যোগ্য নয়। এক সাথে বসবাসকারী ব্যক্তিগণের উপর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় প্রধানত নাগরিকদেরকে রাষ্টের স্বীকৃত আদর্শের অনুসারী বানবার লখ্যে এবং তাদের মধ্যে স্বভাবতই যেসব মতপার্থক্য, দ্বদ্ধ-সংঘর্ষ ও ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হয়, তা দুর কর-তার মীমাংসা করে, জনমতকে একই আদর্শিক খাতে প্রবাহিত করে,সর্ব দিক দিয়ে মি-মিশ, আন্তরিকতা- সম্প্রীতি বহাল করে শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে চালিত করার উদ্দেশ্যে। সম্মুখের দিকে চলার পতে সব বাধা-প্রতিবন্ধকতাকে দূর করা। আর তার-ই জন্য প্রয়োজন সমগ্র দেশে নিরপেক্ষ সুবিচার ও ন্যায়পরাতার পূণ্য প্রতিষ্ঠা। এই কাজটির জন্যই বিচার বিভাগ অপরিহার্য।
জনগণের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টির কারণ
ব্যক্তিগণের একত্র সমাবেস, সমম্বয় ও সংযোজনের পরিণতিই সমাজ এবং এই সমাজের জন্য রাষ্ট্র। ব্যক্তিগণের মন-মেজাজ,চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, স্বার্থ ও স্বাতন্ত্র অনেক সময় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃর্ষের সৃষ্টি করে। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। মানুষের ইতিহাস এর অকাট্য সাক্ষী। এ অবস্থা নিত্যনৈমিত্তিক। প্রধানত দু’টি কারণেই তা দেখা দিয়ে থাকেঃ
১. ব্যক্তির স্বার্থপরতা-স্বার্থান্ধতা। ধন-মাল, অধিকার ও মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগণের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা, তা-ই এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মৌল কারণ। আর তা-ও ঘটে তখন, যখন ব্যক্তিগণ সামষ্টিক আদর্শ, লক্ষ্য ও আদর্শিক মানবিকতাকে ভুলে যায়। ফলে ব্যক্তিগণ নিজের স্বার্থ লাভ করেই নিরস্ত থাকে না, অন্যদের স্বার্থের উপর হস্তক্ষেপ করতেও দ্বিধা করে না। মানুষ মানসিকভাবে এমন এক পর্যায়েও পৌঁছে যায়, যখন নিজের স্বার্থ উদ্ধার হোক, আর নাই হোক, অন্যদের স্বার্থ বিনষ্ট করাই হয় তার প্রধান কাজ। ব্যক্তি তখন হারিয়ে ফেলে তার ঈমান, নৈতিকতা, লজ্জা-শরম। মানুষ তখন মানবাকৃতির হিংস্র পশুতেই পরিণত হয়ে যায়।
২. ব্যক্তিগণের স্বার্থের বৈপরীত্য বা সংঘাত নয়, অনকে সময় সত্য ও স্বর্থ নির্ধারণেই চরম মতবৈষম্যের সৃষ্ট হয়। এ ব্যাপারটিকেও ‘অস্বাভাবিক’ বলা যায় না। কেননা ব্যক্তি যেমন এক স্বতন্ত্র সত্তা, তার মন-মেজাজ, চিন্তা-ভাবনায়ও সেই স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যেকেই একটা স্বতন্ত্র ধারণা পোষণ করে, যার সাথে অন্যান্য ব্যক্তিদের ধারণা সমঞ্জস্য সম্পন্ন হবে, তা জোর করে বলা যায় না। আর তার ফলে মত পার্থক্যই সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। একজনের নিকট যা সত্য, অন্যজন তাকেই মনে করে সম্পূর্ণ মিথ্যা। একজনের মতের চরম পরাজয়রূপ চিহ্নিত হয়ে।
এমন পরিস্থিতি দেখা দেয়াও অস্বাভাবিক নয় -ইতিহাসে বহুবার দেখা দিয়েছে, যখন উভয় পক্ষই পূর্ণমাত্রার তাকওয়া পরহেযগারীর প্রতীক, উভয়েরই মনোভাব সম্পূর্ণ নির্মল, নির্দোষ! কিন্তু প্রকৃত মত কোথায় নিহিত, তা নির্ধারণে অক্ষম হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের সৃষ্টি করে। আর তা-ই গোটা রাষ্ট্রের জন্য হুকমি হয়ে দাড়ায়, সর্বগ্রাসী ও সর্বধ্বংসী বিপদ টেনে আনে। তখন দুই পক্ষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠে। এর পরিণামে কত মানুষের যে রক্ত প্রবাহিত হয়েছে, তার কোন ইয়ত্তা নেই।
ঠিক এই কারণে কুরআন মজীদ একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ উপস্থাপিত করেছে। তার ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সে রাষ্ট্রের অধীন যেমন একটি শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সে রাষ্ট্রের অধীন যেমন একটি শক্তিশালী আদর্শ রাষ্ট্র কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সে রাষ্ট্রের অধীন যেমন একটি শক্তিশালী ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার নির্দেশ রয়েছে, তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিচার বিভাগ গড়ে তোলারও তাকীদ রয়েছে। এ পর্যায়ে আমি সর্বপ্রথম উল্লেখ করব সূরা ‘আল-হাদীস’-এর আয়াতঃ
[আরবী………………………………………]
আমরা আমাদের রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি (বাইয়্যেনাত) সহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড যেন লোকেরা ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং লৌহও নাযিল করেছি। তাতে রয়েছে বিরাট-অমোঘ শক্তি এবং জনগণের জন্য বিপুল কল্যাণ। এ কাজ রাসূলগণের সাহায্যে এগিয়ে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা’আলা বড়ই শক্তিমান, মহা পরাক্রমশালী দুর্জয়।
ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী কৃত এ আয়াতের তাফসীরকে সম্মুখে রাখলে বলা যায়, আল্লাহ তা’আলা এ আয়অতটি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র প্রশাসন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার কথা অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে বলে দিয়েছেন।
ইসলামের বাহক ও প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন আল্লাহর রাসূলগণ। রাসূলগণকে তিনি কেন পাঠিয়েছেন, কিকি সামগ্রী দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং কি উদ্দেশ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাঠিয়েছেন, তা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে এ আয়াতে বলা হয়েছে।
শুরুতে বলা হয়েছে, রাসূলগণকে ‘বাইয়্যেনাত’ (সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি) দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাফসীর বিশেষজ্ঞগণের মতে তার অর্থঃ প্রকাশ্য মু’জিযা এবং অকাট্য দলীল প্রমাণ। অথমা এমন সব বলিষ্ঠ ও শক্তিদৃপ্ত কার্যাবলী, যা মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করার এবং অ-আল্লাহ থেকে বিমুখ বা ভিন্নমুখী হওয়ার আহবান জানায়। যদিও ইমান রাযীর মতে প্রথম অর্থটিই অধিক সহীহ্। কেননা তাদের আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত হওয়ার বাস্তব প্রমাণই হচ্ছে মু’জিযা ও অকাট্য দলীল।
তার পরে বালা হয়েছে, রাসূলগণকে তিনি কিতাব ও মীযান দিয়েছেন। কিতাব বলতে নিশ্চয়ই জাবুর, তাওরাত, ইনজীল ও ফুরকান (কুরআন) বুঝিয়েছেন। যেমন তিনি তাঁর সর্বশেষ রাসূল (স)-কে দিয়েছেন কুরআন মজীদ।
কিন্তু ‘মিযান’ (আরবী…….) অর্থ কি? আভিধানিকরা এর শব্দার্থ বলেছেনঃ তুলাদণ্ড, দাড়ি-পাল্লা; যা দিয়ে কোন জিনিস ঠিক ঠিকভাবে ওজন করা হয়। আর পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচার, সুবিচারের নীতি ও আইন। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের আভিধানিকরা এর শব্দার্থ বলেছেনঃ তুলাদণ্ড, দাড়ি-পাল্লা; যা দিয়ে কোন জিনিস ঠিক ঠিকভাবে ওজন করা হয়। আর পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচার, সুবিচারের নীতি ও আইন। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের আরও দুটি আয়াত রয়েছে। একটিঃ [আরবী…………………]
পরোক্ষ অর্থ হচ্ছে ন্যায়বিচার, সুবিচারের নীতি ও আইন। কুরআন মজীদে এ পর্যায়ের আরও দুটি আয়াত রয়েছে। একটিঃ [আরবী…………………………..]
আল্লাহ তো তিনিই যিনি পরম সত্যতা সহকারে কিতাব ও ‘মিযান’ নাযিল করেছেন। আর দ্বিতীয়টিঃ [আরবী…………….]
এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে আল-কিতাব, আল-মীযান ও আল-হাদীস (লৌহ) -এই তিনটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি? কয়েকটি দিক দিয়েই বিষয়টি বিবেচ্য। প্রথম, শরীয়াত পালনের বাধ্যবাধকতা আরোপ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীলঃ একটি, যা করা বাঞ্ছণীয় তা করা এবং দ্বিতীয়, যা না করা বা ত্যাগ করা বাঞ্ছনীয় তা না করা বা ত্যাগ করা। প্রথমটি স্বতঃই লক্ষ্য। কেননা ত্যাগ করাই যদি স্বতঃই লক্ষ্য হতো, তা কারোরই সৃষ্টি না হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। সেই অনাদি কালেই তো -যখন সৃষ্টি করা হচ্ছিল -তা অর্জিত ছিল। আর যা করা বাঞ্ছনীয় তা করা নফসের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তা হবে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শরীর বা দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট হলে তা হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ। আল্লাহর কিতাবই মনোলোকের সেই সব কাজ করার পথ দেখায়, হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়, সন্দেহ-সংশয় দূর করে অকাট্য বলিষ্ঠ যুক্তি ও প্রমাণের দ্বারা আর ‘মিযান’ দৈহিক বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা করণীয় কাজ বলে দেয়। সৃষ্টিকুলের পারস্পরিক কার্যাদিই হচ্ছে বড় বড় ও কষ্ট সাপেক্ষ শরীয়াতের বিধান। এ ক্ষেত্রে আল-মীযানই ন্যায়বিচার ও জুলুম-এর মধ্যে পার্থক্য করে দেয়, কোনটা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি আর কোনটা ত্রুটিপূর্ণ, তা নির্দেশ করে। আর লৌহের মধ্যে রয়েছে কঠিন কঠোর শক্তি। যে কাজ অবাঞ্ছনীয় তা থেকে মানুষকে বিরত রাখে। মোটকথা, আল-কিতাব মতাদর্শ ও তত্ত্বগত শক্তি বোঝায়, আল-মীযান কর্মগত শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করে। আর মন ও আত্মা -অন্য কথায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পর্যায়ের কল্যাণেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং তার প্রতি লক্ষ্য আরোপ করা সর্বাধিক প্রয়োজন, তার পরের স্থান হচ্ছে দৈহিক কাজের আর তার পরই বাঞ্ছনীয় নয় এমন কাজ বা ব্যাপারাদির প্রতিরোধের প্রশ্ন উঠে (প্রথম পর্যায়ের দুইটি ইতিবাচক এবং তৃতীয়টি নেতিবাচক) -এই দিকে লক্ষ্য রেখেই বিষয় তিনটির উল্লেখ সেই পরস্পরায় করা হয়েছে (অর্থাৎ প্রথমে আল-কিতাব, তারপরে আল-মীযান এবং শেষে আল-হাদীস এর উল্লেখ হয়েছে)। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিবেচ্য ব্যাপার, হয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সংশ্লিষ্ট হবে -যার পথ এই আল কিতাব দেখায় -অথবা হবে সৃষ্টির সাথে। সৃষ্টির সাথে হলে তা দু ভাগে বিভক্ত হবে। বন্ধু-বান্ধব ও সমপর্যায়ের লোক হলে তাদের সাথে পূর্ণ সমতা রক্ষা করে কাজ করতে হবে এবং সেজন্য আল-মীযান -তুলাদণ্ড দরকার। আর তা শত্রুদের সাথে হলে সেজন্য প্রয়েঅজন তরবারী -যা লৌহ দ্বারা নির্মাণ করতে হয়।
তৃতীয় পর্যায়ে বিবেচ্য, জনগণ তিনটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম, যারা অগ্রবর্তী তাদের সাথে আল-কিতাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে। তারা ইনসাফ করবে, সকল প্রকার শোবাহ সন্দেহ পরিহার করে চলবে। দ্বিতীয়, মধ্যম ধরনের লোক, তারা নিজেরাও ইনসাফ করবে, তাদের উপরও ইনসাফ কার্যকর করা হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন আল-মীযান তৃতীয় হবে জালিম লোক। তাদের উপর ইনসাফ কার্যকর করতে হবে। তাদের নিকট থেকে ইনসাফ পাওয়ার কোন আশা করা যায় না। তাই তাদের দমনের জন্য লৌহ-শক্তি ও অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য।
চতুর্থ পর্যায়ে বিবেচ্য, মানুষ যখন আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে উচ্চতর মানে পৌছে যায়, তখন তারা আল্লাহর কিতাবকে ভিত্তি করে চলে, এই কিতাবের বিপরীত কোন কাজ করতেই তারা প্রস্তুত হয় না। অথবা মানুষ সেই পথের পথিক হবে। তখন তাকে নৈতিকতার বিধান -বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজনের তুলনায় কম হওয়ার বিচ্যুতি থেকে বাঁচার জন্য আল-মীযান-এর প্রয়োজন। তাহলেই তারা সিরাতুল-মুস্তাকীম-এর উপর অবিচল থাকতে পারে। অথবা সে হবে পাপ পথের পথিক। তাহলে তাকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার জন্য শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যা লৌহ থেকে বোঝা যায়।
পঞ্চম, দ্বীন-ইসলাম যেমন কতিপয় মৌল নীতি পেশ করে, তেমনি খুটিনাটি বিষয়েও বিধান দেয়। মৌলনীতি তো আল-কিতাব থেকেই গ্রহণীয়। আর খুটিনাটি পর্যায়ের সে সব কাজই লক্ষ্য যাতে তাদের জন্য কল্যাণ ও ন্যায়পতা মৌলনীতি ও খুটিনাটি বিষয়াদি পালন করবে না, তাদের শায়েস্তা করার জন্য লৌহদণ্ড (শক্তি) প্রয়োগ জরুরী।
ষষ্ঠ পর্যায়ে আল-কিতাব বলতে ন্যায়বিচার ও ইনসাফের বিধান বোঝায়। আর আল-মীযান বলে বোঝানো হয়েছে লোকদেরকে সেই ইনসাফ ও সুবিচারপূর্ণ বিধান পালনের জন্য মানুষকে উদ্ধুদ্ধ করা। আর তা শাসকমণ্ডলীরই দায়িত্ব। যে সব লোক তা পালন করতে প্রস্তুত নয়, যারা বিদ্রোহ করে, তাদের দমন ও শাসনের জন্যই ‘লৌহ’ (শক্তি) প্রয়োগ অপরিহার্য।
এ থেকে একথাও স্পষ্ট হয় য়ে, আল্লাহর কিতাবের আলিম ও ধারকগণই হচ্ছেন সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। তাদেরই দায়িত্ব ‘আল-মীযান’ -তুলাদণ্ড প্রতিষ্ঠিত করা, যেন জনগণ ইনসাফ ও ন্যায়বিচার পে পারে। আর আল-কিতাবের বিধানকে পূর্ণ ন্যায়পরতা ও ইনসাফ সহকারে কার্যকর করার জন্যই প্রয়োজন লৌহ-এর অর্থাৎ শাসন শক্তির -রাষ্ট্রের। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একেই বলা হয়েছে Coercive power বাধ্যকারী শক্তি।
কিতাব নাযিল করার কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু ‘মীযান’ ও ‘লৌহ’ নাযিল করার তাৎপর্য কি? ইমাম রাযী লিখেছেন, এ দুটিকেও আল্লাহ তা’আলা আসমান থেকেই নাযিল করেছেন। হয় জিবরাঈল তা পৌছিয়েছেন, না হয় হযরত আদমই তা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন, যখন তিনি জান্নাত থেকে দুনিয়ায় এসেছিলেন। আর তার অর্থ এ-ও হতে পারে যে, তিনি তা এ দুনিয়ায়ই উৎপন্ন করেছেন, ব্যবস্থা করেছেন। তবে বলা যেতে পারে, আদর্শগতভাবে আল-মীযান কুরআনের মতই আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হওয়া জিনিস, তা এসেছে দুনিয়ায় আল্লাহ সৃষ্ট লৌহশক্তি-রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে (সাধারণ আরবী কথনে এবং কুরআন মজীদে নাযিল হওয়অ কথাটি এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে)।
এই তিনটিই আল-কিতাব, আল-মীযান ও আল-হাদীদ মানুষের আয়ত্তে নিয়ে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য স্বরূপ। উদ্ধৃত্ত আয়াতে বলা হয়েছেঃ [আরবী……………………]
যেন মানুষ সুবিচার ও ন্যায়পরতা নিয়ে দাঁড়াতে পারে (জীবন যাপন করতে পারে)।
এখানে (আরবী……………..) অর্থ প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রাপ্য অংশ পেয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি মানুষকে তার প্রাপ্য দেয়াই ইনসাফ। আর তা না দেয়াই জুলুম। জুলুম উৎখাত করে ইনসাফ কায়েম করাই এ তিনটি জিনিসেরই লক্ষ্য। এ তিনটির মিলিত শক্তিই তা করতে সক্ষম। এই তিনটির মধ্যে নিহিত রয়েছে যেমন শক্তি ও ক্ষমতা, তেমনি বিশ্বমানবতার কল্যাণ। এ তিনটির মধ্যে কোন একটি পারে। কিন্তু ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হতে পারে না।
ইমাস রাযীর মতে বিশ্বমানবের কল্যাণ চারটি মৌলিক জিনিসের মধ্যে নিহিত। তা হচ্ছেঃ কৃষি-শিল্প, গৃহ নির্মাণ ও সার্বভৌম রাষ্ট্রশক্তি। কেননা মানুষের সর্ব প্রথম প্রয়োজন খাদ্য। তা প্রায় সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষিজাত। তারপরই তার প্রয়োজন বস্ত্রের -গাত্রাবরণের। তা বয়নশিল্পের মাধ্যমেই পাপ্য। তৃতীয়ত মানুষ স্বভাবতই সামাজিক জীব বিধায় তাদের একত্রিত হয়ে বসবাস করা এবং প্রত্যেকেরই নিজ নিজ যোগ্যতানুযায়ী শ্রম ও কর্মে আত্মনিয়োগ করা কর্তব্য। এ ভাবেই প্রত্যেকেরই কর্মরত হওয়অয় সার্বিক কল্যাণ লাভ সম্ভব। এ জন্য এক সামষ্টিক ব্যবস্থাপনার প্রয়েঅজন যা পরস্পরের মধ্যে সৃষ্ট ঘাত-প্রতিঘাত ও সংঘর্ষ প্রতিরোধকে পারস্পরিক মিল-মিশ ও সমন্বয়ের মধ্যে নিয়ে আসবে, যা কেবলমাত্র রাষ্ট্রশক্তির দ্বারাই সম্ভব। আর এই চারটি কাজেই লৌহ এক অপরিহার্য উপকরণ। চাষকার্য, বস্ত্রবয়ন ও গৃহ নির্মাণ -এ তিনটি কাজের জন্য লৌহের প্রয়োজন স্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত। আর রাষ্ট্রের কার্যকরতা ও লৌহ নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র বর্তমানে যাকে বলা হয় আগ্নেয়াস্ত্র -তা যতই Sophisticated বা জটিলতর ও অত্যাধুনিকই হোক -লৌহ বা ইস্পাত ছাড়া হতে পারে না। লৌহ ব্যতীত অপর কোন ধাতুই -দুনিয়ার খাওয়া-পরা থেকে শুরু করে নিরাপদে বসবাস ও আত্মরক্ষা পর্যন্ত কোন কাজই সম্পন্ন হতে পারে না।
আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর সাহায্যের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ জানতে চান, কে তাঁর ও রাসূলের সাহায্যে এগিয়ে আসছে। আল্লাহর সাহায্য অর্থ আল্লাহর দ্বীনের সাহায্য। দ্বীনের সাহায্য অর্থ দ্বীনকে বাস্তবায়িত, প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করে তাকে লীন হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। আর রাসূলের সাহায্য হচ্ছে, রাসূলের আগমন যে দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, সেই লক্ষ্য অর্জনে তাঁর সাথে লৌহ শক্তি -আদর্শগত ও বস্তুগতকে পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করা। বস্তুত আল্লাহর কিতাবের কার্যকরতা ও রাসূলের আগমন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা ও রাখার জন্য এই লৌহ শক্তির ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য। বাস্তবায়িত করার জন্য জিহাদই হচ্ছে একমাত্র উপায়। জিহাদের জন্য অস্ত্র প্রয়োজন, আর সে অস্ত্র তো লৌহ দ্বারাই নির্মিত। আর তাকে বাস্তবায়িত রাখার -ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্যও -লৌহশক্তি ও লৌহনির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র একান্তই জরুরী দরকার। এইগুলির ব্যবহার করেই আল্লাহর এবং তাঁর রাসূলের সাহায্য করা যেতে পারে, অন্য কোন ভাবে নয়।
আল্লাহর জানতে চাওয়ার অর্থ, বাস্তবে মানব সমাজে যুগে যুগে দেশে দেশে এই সাহায্য কর্ম অনুষ্ঠিত হতে দেখতে চাওয়া। কেননা আল্লাহর ইলম তো চিরন্তন, বাস্তব-অনুষ্ঠানের মুখাপেক্ষী নয়। তাঁর এই দেখতে চাওয়া নিত্য নতুন করে সংঘটিত হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তাই জিহাদ চিরকালীন।
মোটকথা, আল্লাহর রাসূল প্রেরণ, কিতাব ও মীযান নাযিল করা এবং লৌহ ধাতু ও লৌহশক্তি (রাষ্ট্র) সৃষ্টির মুখ্য ও চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানব সমাজে ইনসাফ সুবিচারের প্রতিষ্ঠা। -[আরবী টীকা………]
মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ’লা মওদূদী ‘এবং আমরা লৌহ নাযিল করেছি’ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লিখেছেনঃ এখানে লৌহ অর্থ রাষ্ট্রীয় ও সামরিক শক্তি। মূল বক্তব্য হলো, আল্লাহ তা’আলা ন্যায়পরতা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার শুধুমাত্র একটি প্রকল্প পেশ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই রাসূলগণকে প্রেরণ করেন নি বরং তা বাস্তবভাবে জারি ও কার্যকর করার চেষ্টা করা, সেজন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য সংগ্রহ করা এবং সে কাজের প্রতিরোধকারী বা তার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী শক্তিসমূহকে যথোপযুক্ত শাস্তি দান করার ব্যবস্থা করাও তাদের দায়িত্বভুক্ত। -[আরবী টীকা…………………]
তাই ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটি বিচার বিভাগ গড়ে তোলা একান্তই জরুরী।
আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ [আরবী………………………………………………]
অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর ও পরস্পরের মধ্যে সঠিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোল এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর।
এ আয়াতটির নাযিল হওয়ার প্রসঙ্গ ভিন্নতর হলেও মৌলিকভাবে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান দুটি উপকরণের সাহায্যে আসল লক্ষ্য অর্জনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে পারস্পরিক সুস্থ নির্মল সম্পর্ক গড়ে তোলা। আর তা সম্ভব আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমে। আল্লাহর ভয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের ভিত্তিতেই সম্ভব ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া, যার চরম লক্ষ্য পারস্পরিক প্রীতি বন্ধুত্বের ও একনিষ্ঠতা-ঐকান্তিকতার সম্পর্ক গড়ে তোলা -[আরবী টীকা…………………..]
আর এ কাজের জন্যই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ অপরিহার্য। বিচারকার্য ও জনগণের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করে পারস্পরিক মিল স্থাপন করার গুরুত্ব বোঝাবার জন্য হযরত আলী (রা) বলেছিলেনঃ [আরবী………………………………………………]
পারস্পরিক মিল-মিশ প্রীতি-বন্ধুত্ব বিবাদহীনতা সৃষ্টি করা সাধারণ নফল নামায-রোযার তুলনায় অনেক উত্তম। [আরবী টীকা…………………]
এ কারণে ইসলামে বিবদমান পক্ষদ্বয়ক মীমাংসাকারী ও বিবাদ ফয়সালাকারী লোকদের নিকট যাওয়ার জন্য এবং তদের বিচারের রায় ও ফয়সালা অন্তরিকতার সাথে মনে নেয়ার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। কেননা পারস্পরিক বিবাদ দূরীভূত হওয়ার এছাড়া আর কোন উপায় নেই। আর এ কারণে সাধারণভাবে প্রায় সর্বপ্রকার রাষ্ট ব্যবস্থায় এবং বিশেষ করে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিচার বিভাগ (judiciary)- কেরাষ্ট্রে একটি অন্যতম জরুরী-তৃতীয়-বিভাগ রূপে নির্দেশ করা হয়েছে। কুরআন মজীদে এই বিচার বিভাগের ভিত্তি উপস্থাপিত হয়েছে এবং রাসুলে করীম (স) ও খুলাফায়ে রাশেদুন এ বিভাগটিকে স্বতন্ত্র মর্যাদয় ও শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কুরআনের ঘোষণানুযায়ী বিচার-ফয়সালার প্রকৃত কর্তৃত্ব স্বয়ং আল্লাহ তা ‘আলারই, তিনিই হচ্ছেন আসল ফয়সালাকারী। ইরশাদ হয়েছেঃ [আরবী………………]
ফয়সালা করার সমগ্র ইখতিয়ার কেবলমাত্র আল্লাহর। তিনিই সত্য কথা বর্ণনা করেন এবং তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী। কিন্তু আল্লাহ তা ‘আলা মানব সমাজের দৈনন্দিন ব্যাপারাদিতে ফয়সালা দেয়ার কাজ নিজে এসে করেন না, তাই তা করার জন্য একদিকে তিনি ফয়সালা করার বিধান দিয়েছেন, ফয়সালা করার দায়িত্ব তাঁর রাসূলের উপর অর্পণ করেছেন এবং তাঁর ফয়সালা সর্বান্তকরেণ মেনে নেয়ার জন্য ঈমানদার জনগণকে স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেনঃ [আরবী……………..]
নিঃসন্দেহে আমরা- হে নবী!-তোমার প্রাতি এই কিতাব-কুরআন -নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, তুমি লোকদের পরস্পরের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে আল্লার দেখানো নিয়ম এবং তুমি কখখনই খিয়ানতকারী লোকদের পক্ষপাতকারী হবে না। নির্দেশ দিয়েছেনঃ [আরবী……………]
তুমি যদি বিচার ফয়সালা কর-হে নবী ! তা ‘হলে তদের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে বিচার-ফয়সলা কর। কেননা ইনসাফকারী ও সুবিচারকারীদের আল্লাহ খুবই ভালোবাতেন।
বলেছেনঃ [আরবী……………..]
হে নবী! আমরা তোমার প্রতি এই কিতাব পরম সত্যতা সহকারে নাযিল করেছি, যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যতা ঘোষণাকারী ও তার সংরক্ষক। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা কর এবং তোমার নিকট আগত পরম সত্য থেকে বিমুখ হয়ে লোকদের ইচ্ছা-বাসনা কামনার অনুসরণ করো না। শুধু তা-ই নয়, মুহাম্মদ (স) -কে একজন বিচারক-ফয়সালাকারী-মীমাংসাকারী রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁর ফয়সালাকে কুন্ঠাহীন চিত্তে মেনে নেয়া ঈমানের অপরিহার্য শর্ত। তাই অত্যন্ত কঠোর ও বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছেঃ [আরবি…….]
না, তোমার রব্ব-এর কসম, এই লোকেরা কখখনই ঈমানদার হতে পরবে না,যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে-হে নবী-তোমাকে বিচারক ও মীমাংসাকারী মেনে না নেবে, অতঃপর তুমি যা ফয়সালা-ই করে দেবে সে ব্যাপারে তারা তাদের মনে কোন রূপ দ্বিধা-দন্ধ না পাবে এবং সর্বন্তকনরণে ও সর্ম্পূর্ণভাবে মাথা পেতে না নেবে। কেবল নবী-রসূলগণের-ই এ দায়ীত্ব নয়। আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে স্বাধীনভাবে বিচার-ফয়সালা করার এবং এজন্য বিচার বিভাগ কায়েম করার দায়িত্ব নির্বিশেষে সকল ঈমানদার লোকেরই। ইরশাদ হয়েছেঃ [আরবি…………]
আল্লাহ তা’আলা নিশ্চিতভাবে তোমাদেরকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমানত সমূহ তাদের মালিক বা প্রকৃত যোগ্যদের নিকট যেন ফিরিয়ে বা পৌছায়ে দেয়। আর তোমরা যখন জনগণের মধ্যে বিচার কার্য সম্পন্ন করবে তখন যেন তোমরা পূর্ণ মাত্রায় ন্যায়পরতা সহকারে ফায়সালা কর ও রায় দান কর। বস্তুত আল্লাহ অতীব উত্তম বিষয়ে তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চিত জানবে, আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। মামলার বিচার কার্য সম্পাদনের সময় কোন পক্ষের প্রতি বিদ্বেষ যেন অবিচার করতে তোমাদেরকে বাধ্য না করে। এ পর্যায়ের নির্দেশ দান প্রসঙ্গে আল্লাহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছেনঃ [আরবি……………..]
কোন বিশেষ দলের প্রতি শত্রুতা-বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন এতদূর ক্ষুদ্ধ আক্রুশ জর্জরিত করে না তোলে যে,(তার ফলে) তোমরা সুবিচার করা থেকে বিরত থেকে যাবে, তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। বস্তুত তা আল্লাহ পরস্তির সাথে খুবই সামঞ্জাস্যশীল। আর তোমরা সব সময়ই আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে। নিশ্চিত জানবে, তোমরা যা কিছুই কর, আল্লাহ সে সর্ম্পকে পুরোপুরিভাবে অবহিত রয়েছেন। এ আয়াতে শুধু যে ন্যায়বিচার করতে বলা হয়েছে তা-ই নয়, এই পথে অন্তরে নিহিত কোন বিদ্ধেষ বা শত্রুতাও যেন বাঁধা হয়ে না দাঁড়াতে পারে, সে কথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে এবং বিশেষভাবে বিচারকার্যে আল্লাহকে ভয় করবার জন্য তাকীদ করা হয়েছে। বস্তুত আল্লাহকে সত্যিকার ভাবে ভয় করলে কারোর পক্ষে অবিচার বা বিচারকার্যে জুলুমের প্রশ্রয় দান সম্ভব হতে পারে না। শুধু বিচারকার্যেই ন্যায়পরায়নতা ও সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে বলেই কুরআন ক্ষান্ত হয়নি, জীবনের সকল ক্ষেত্রে অন্য লোকদের প্রতি যেমন নিজের প্রতিও তেমনি সুবিচার করার নির্দেশ দিয়েছে। এমন কি অন্য লোকদের সাথে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রেও এই ন্যায়পরায়নতা অক্ষুন্ন ও অব্যাহত রাখার নিদের্শ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছেঃ [আরবি…………..]
তোমরা যখন কথাবার্তা বলবে, তখনও অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে-যার সাথে বা যা’র সম্পর্কে কথা বলছ, সে নৈকট্য সম্পন্ন ব্যক্তি হলেও। বস্তুত একজন কথা বলে,অন্যজন শুনে। হয় সরাসরি শ্রোতাকেই কোন কথা বলা হয়,না হয় অন্য কোন মন্তব্য করা হয়। এই সময়ও প্রত্যেক ব্যক্তিকে ন্যায়বাদী হতে হবে। কথা বলেও কারোর প্রতি অবিচার করা কুরআনের নিকট অনভিপ্রেত,অবাঞ্ছনীয়। বলা নিষ্প্রয়োজন, নবী করীম(স) আল্লাহর এই নির্দেশ সমূহকে পরুপুরিভাবে অনুসরণ করেই ন্যাবিচারের তুলনাহীন নিদের্শ সমুহকে পরাপরিভাবে অনুসরণ করেই ন্যায়বিচারের তুলনাহীন নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যদিও তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একাই ছিলেন যেমন রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, প্রধান সেনাধ্যক্ষ, তেমন প্রধান বিচারপতিও। তিনি তাঁর রাষ্ট্রের দূরবর্তী অঞ্চলের জন্য বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে বিচারকার্য সংক্রান্ত কঠিন দায়িত্ব পালনের উপোযাগী উপোদশ ও শিক্ষাদান করেই পাঠাতেন। যেমন, হযরত আলী (র) কে ইয়ামেনের বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন,তখন হযরত আলী (র) বললেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে একটি এলাকার বিচারপতি নিযুক্ত করে পাঠাচ্ছেন। অথচ আমার বয়স অল্প এবং বিচারকার্য সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতাও নাই। তখন রাসূলে করীম (স) তাঁকে বলেছিলেনঃ [আরবি……………]
নিশ্চয় আল্লাহ তোমার দিলকে হেদায়েত দান করবেন, তোমার জিহ্বাকে দৃঢ়বাক করে দেবেন। বিবদমান দু্ই পক্ষ যখন তোমার সম্মুখে বসবে, তখন এক পক্ষের বক্তব্য শুনার পর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষের বক্ত্ব্য না-শুনা পর্যন্ত তুমি কখনই বিচারকার্য সম্পাদন করবে না-রায় দেবে না। এ ভাবে কারাই বিচার কার্য তোমার জন্য সহজসাধ্য ও সুস্পষ্ট করে তোলার খুব বেশী অনুকূল হয়ে দাঁড়াবে। হযরত মুয়ায (র)-কে বিচারপতি নিয়োগ করেও অনুরূপ প্রশিক্ষণই তিনি দিয়েছিলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নবী করীম (স) কুরআনের হেদায়েত অনুযায়ী ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে বিচার বিভাগকে সুষ্ঠরূপে গড়ে তুলেছিলেন। ও পর্যায়ে কুরআনের সবগুলি হেদায়েত ও বিধানকে তিনি নিজেই বাস্তবায়িত করে গেছেন এবং তার মাধ্যমে কুরাআন ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কি করে কার্যকর করতে হয়, তার পন্থা ও পদ্ধতিও তিনি কিয়ামত পর্যন্তকার জন্য চিরভাস্বর করে রেখে গেছেন। কুরআন মজীদে সুবিচার ও ন্যায়পরতার উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তা বোঝা যায়, সুবিচার ও ন্যায়পরতার বিপরীত শব্দ জুলুম-এর উল্লেক কুরআন মজীদে এক শতেরও বেশী আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্য থেকে এখানে কতিপয় আয়াতের উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ [আরবি………..]
বরং জালিমরাই সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে নিমজ্জিত। [আরবি……………….]
জালিম লোকেরা পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। [আরবি………………]
জালিম লোকেরা কখনই কোন কল্যাণ পেতে পারে না। [আরবি………………]
আল্লাহ নিশ্চই জালিম লোকদের ভালোবাসেন না ও পছন্দ করেন না। [আরবি………………..]
শান্তি পাওয়ার যোগ্য সে সব লোক, যারা জনগণের উপর জুলুম করে ও যমীনে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি-সীমালংঘনমূলক কাজ করে। এদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। [আরবি………..]
যে লোক জুলুম করেছে, অনতিবিলম্বে আমরা তাকে সেজন্য শাস্তি দেব। অতঃপর তাকে রব্ব-এর নিকট সোপর্দ করা হবে। তখন তিনি তাকে অত্যন্ত ঘৃণা ধরনের আযাব দেবেন। এ আয়াতটি স্পষ্ট করে বলেছে যে, জালিমকে অনতিবিলস্ব শাস্তিদান আল্লাহর স্থায়ী বিধান। আর এই শাস্তিই জালিমের জন্য চূড়ান্ত বা শেষ কিংবা একমাত্র শাস্তি নয়। এর পর-ও তাকে আল্লাহর নিকট থেকে জঘন্য ধরনের শাস্তি অবশ্যই পেতে হবে, পরকালে নিশ্চিতভাবেই হবে। এভাবে কুরআন মজীদে ‘জুলুম’ -এর বিরুদ্ধে জনগণের মন-মানসিকতা গড়তে চেষ্টা করা হয়েছে এবং ইসলামী রাষ্ট্রই এই জুলুম-এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য-জুলুম-এর পথ বন্ধকরণের জন্য দায়ী। আর তা সম্ভব হতে পারে সর্বাত্নকভাবে সুবিচার কায়েম করার মাধ্যমে। কুরআন মজীদে এই ‘জুলুম’ [আরবী] শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহহৃত হয়েছে, (আরবী) শব্দ। [আরবী] শব্দের অর্থ হচ্ছেঃ সমস্ত মানুষ মানবীয় অধিকার সম্পূর্ণ রূপে সমান- অবশ্য সেই সব মানুষ যদি আইনের অনুসারী হয়। (আরবী)-এর অর্থঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই তার অধিকার পাবে- কেউ-ই নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না- কেউ যদি কারোর সেই অধিকার হরণ করে, তা ‘হলে ‘জুলুম’ হবে এবং তাকে তার শাস্তি অনিবার্যভাবে ভোগ করতে হবে। [আরবী টীকা……….]
ইমাম রাগেব লিখেছেনঃ [আরবী……..] প্রতিশোধ প্রমাণে পরম সমতা রক্ষা করাই হচ্ছে ‘আদল’-সুবিচার বা ন্যায়পরতা’ [আরবী টীকা………]
সাইয়্যেদ শরীফ লিখেছেনঃ [আরবী ……………..] মাত্রাদতিরিক্ততা বা বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজন-অপেক্ষা কম মাত্রার মধ্যবর্তী একটি সমতাবিন্দু [আরবী টিকা…………….]
আবুল বাকা হানাফী বলেছেনঃ [আরবী] জুলুম- এর বিপরীত অর্থবোধক শব্দ [ আরবী ] হচ্ছে, হক্কাদারকে হক্ক নয়, তার নিকট থেকে নিয়ে নেয়া [ আরবী টিকা……………] আল্লামা আইনী লিখেছেনঃ [আরবী টিকা……….] ‘কাজে পরিণত করা কর্তব্য-এমন সব হুকুম পালন করাই হচ্ছে ‘আদল’। ‘হক্ক’ কে সর্মথন করা -মেনে নেওয়া ও জুলুম খতম করাই ‘আদল’। [আরবী টিকা……..] ইসলামে যে বিচার বিভাগ গড়ে তোলার জন্য তাকীদ, তা রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের অধিকার-নিরাপত্তা, স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার ও সমতার সংরক্ষক। বিচারকার্যে বিচার বিভাগই চুড়ান্ত মর্যাদার অধিকারী। আইন বা শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাদান এ বিভাগেরই কাজ। এ বিভাগই আইনের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ব্যবপারে রায়দানের অধিকারী। আইনের ভিত্তিতে প্রমাণিত অধিকার প্রতিষ্টিত ও কার্যকর করা এই বিভাগেরই দায়িত্ব। এ কারণে এ বিভাগকে বলা হয় [আরবী…….]- এ বিভাগকে [আরবী…….] ‘প্রতিফলন ও ‘শাস্তিদান’ ও এ বিভাগের কাজ বলে প্রতিফল ও শাস্তিদানের বিভাগ’ও বলা হয়। হযরত উমর (রা) খলীপা নির্বাচিত হয়ে বলেছিলেনঃ ‘আমি প্রতিফল-শাস্তিতানের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। [আরবী টিকা……………] হযরত উমর (রা)- এরই কথা [আরবী…..]
বিচার একটা কর্তব্য ও সুকঠিন-দৃঢ় দায়িত্ব এবং অবশ্য করণীয় একটি নিয়ম। ইবনে হুম্মাম হানফী বলেছেনঃ বিচার বিভাগ এমন একটি প্রতিষ্টান যা বিরোধ-বিবাদের মামলাসমূহের ফয়সালা দেয়। -[আরবী টিকা………………….] সরখসী বলেছেনঃ পারস্পরিক বিবাদের মূল প্রকৃতি ও স্বরূপ অনুধাবন, পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য শ্রবণ ও তাদের মর্ম অনুধাবন এবং সেই দৃষ্টিতে চুড়ান্ত রায় দানের নাম-ই হচ্ছে ‘কাযা’ -বিচার। -[আরবী টীকা……………]
সাইয়্যেদ শরীফ বলেছেনঃ দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে অবশ্য পূরণীয় হক্ককে মেনে নেয়া ও প্রমাণিত হক্ককে রায়ের মাধ্যমে প্রকাশ করাই হচ্ছে বিচারের মূল কথা।-[আরবী টীকা……………….]
কুরআন মজীদে ‘কাযা’ শব্দ এই অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনঃ [আরবী…………………]
অতঃপর আল্লাহ এবং তার রাসূল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দেন।
[আরবী…………….]
এবং ফয়সালা করে দেয়া হয়েছে তাদের পরস্পরের মধ্যে পূর্ণ ইনসাফ সহকারে এবং তাদের উপর একবিন্দু জুলুম করা হবে না।
নবীর আগমনের পর এমন হয়ে যায়, যেখানে পূর্ণ সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এই বিচার ব্যবস্থার দ্বারা কখনই কারোর উপর একবিন্দু জুলুম বা অবিচার করা হয় না। কেননা নবী তো পূর্ণ ইনসাফের বিধান লয়ে আসেন। আর নবীর নিয়ে আসা বিধানের ভিত্তিতে যে বিচার ব্যবস্থা কায়েম হয়, তার দ্বারা কোনরূপ অবিচারের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। এই কথার দিকই এ আয়াতটিতে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। -[আরবী টীকা………………..]
হাদীসেও এর দৃষ্টান্ত রয়েছে। একটি হাদীসের অংশ [আরবী************] যে লোক হিকমাত-বুদ্ধিমত্তা ও সুস্থ বিবেচনা সহকারে বিচার করল।-[আরবী টীকা******************]
[আরবী*******************]
যুবাইর (র) এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলেন। অতঃপর রাসূলে করীম (স) উভয়ের মধ্যে বিচার করে ফয়সালা করে দিলেন। -[আরবী টীকা********************]
বিচার বিভাগের লক্ষ্য অর্জনের পন্থা
বিচার বিভাগ ও বিচার বিভাগীয় কর্তৃত্ব কি করে তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারে এবং সমাজে সুবিচার ও পরিপূর্ণ ন্যায়পরতা কি করে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তা-ই হচ্ছে এ পর্যায়ে প্রধান আলোচ্য, যেন সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তি স্বীয় জান-প্রাণ, ধন-সম্পদ ও ইযযত-আবরুর পূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করতে সক্ষম হয়, তারা কেউ-ই একবিন্দু জুলুম-পীড়নের শিকার না হয়, কেউ যেন তার সার্বিক নিরাপত্তায় একবিন্দু বিঘ্নের সম্মুখীন না হয়।
বিচার বিভাগের মৌলিক লক্ষ্য চারটি বিষয়ের সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হতে পারেঃ
১. বিচারকে যোগ্যতা, কর্মদক্ষতা এবং বিচারক হওয়ার উপযোগিতা;
২. বিচারকের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা, মুখাপেক্ষীহীনতা ও পূর্ণ স্বাধীনতা;
৩. সুবিচারের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-কানুনের পূর্ণ কার্যকরতা; এবং
৪. বিচারকের নিকট জনগণের অধিকারের সুস্পষ্ট ধারণা, কার্যসূচী এবং ন্যায়বিচার সংক্রান্ত রায়ের বাধা-বিঘ্নহীন কার্যকরতার নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা বর্তমান থাকা।
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার এই সব কয়টি জিনিসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে এ চারটি বিষয়েরই বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা যাচ্ছেঃ
১. বিচারকের যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও বিচার কার্যের উপযুক্ততা
বিচার বিভাগ সমাজে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে কারে, যদি বিচারকের প্রকৃত যোগ্যতা-কর্মক্ষমতা ও সেজন্য প্রয়োজনীয় উপযুক্ততা বিচারকের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান থাকে, যদি বিচারকার্যের যোগ্যতার জন্য জরুরী শর্তসমূহ তার মধ্যে পুরাপুরি পাওয়া যায়।
ইসলাম বিচারকের কতিপয় গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে, যা বিচারকের মধ্যে বর্তমান থাকা একান্তই আবশ্যক। বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে ইসলাম-ই সর্ব প্রথম এই গুণ ও শর্তের উল্লেখ করেছে। এর পূর্বে কোন সময়ই এর প্রতি একবিন্দু গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।
গুণগুলি হচ্ছেঃ
১. পূর্ণবয়স্কতা
২. বিবেক-বুদ্ধির সুস্থতা
৩. ঈমানদার হওয়া
৪. মৌলিকভাবে ন্যায়নিষ্ঠতা ও পক্ষপাতহীনতা
৫. জন্মের পবিত্রতা
৬. আইন সম্পর্কে পূর্ণমাত্রার জ্ঞান ও বিচক্ষণতা
৭. বিচারকের পুরুষ হওয়া
৮. বিচারকের স্মরণশক্তির তীক্ষ্মতা, মেধা ও প্রতিভা।
কেননা বিচারক বিস্মৃতির শিকার হলে তার দ্বারা সঠিকভাবে বিচার কার্য সম্পাদন হতে পারে না।
রাসূলে করীম (স) বিচারকের পদের গুরুত্ব, তার মর্যাদা ও তার দায়িত্ব জবাবদিহির বিরাটত্ব সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোরতা আরোপ করেছেন।
তিনি বলেছেনঃ [আরবী………………….]
বিবাচারকরা তিন ধরনের হয়। এক ধরেনরে বিচরক জান্নাতে যাবে, আর অপর দুই ধরনের বিচারব জাহান্নামে যেতে বাধ্য হবে। জান্নাতে যাবে সেই বিচারক, যে প্রকৃত সত্য অনুধাবন ও হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী বিচার করেছে। পক্ষান্তারে যে লোক প্রকৃত সত্য জানতে ও বুঝতে পেরেও বিচারকার্যে রায় দানে জুলুম করেছে, সে জাহান্নামে যাবে। আর যে বিচার মূর্খতা থাকা সত্তেও লোকদের উপর বিচার চাপিয়ে দিয়েছে, তাকেও জাহান্নামে যেতে হবে। [আরবী টীকা……………..]
এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম জাফর সাদেক ( র ) বলেছেনঃ চার ধরনের বিচারক দেখা যায়। তন্মধ্যে তিন ধরনের বিচারকই জাহান্নামে যাবে, আর মাত্র এক ধরনরেন বিচারক জাহান্নাতে যেতে পারবে। যে ব্যক্তি সজ্ঞানে অবিচার করে সে জাহান্নামে যাবে। যে ব্যক্তি না-জেনে অবিচার করে, সেও জাহান্নামে যাবে। যে বাক্তি না জেনেও সঠিক বিচার করে, সেও জাহান্নামে যাবে। আর যে জেনে-শুনে-বুঝে সুবিচার করে, কেবলমাত্র সে-ই জান্নাতে যেতে পারবে।[আরবী টীকা…………..]
২. অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে বিচারকের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা
একথা সর্বজনবিদিত যে, বিচারকের দায়িত্ব ও জবাবদিহি অত্যন্ত বড় ও কঠিন। এই দিক দিয়ে তার সাথে অপর কোন পদে অভিষিক্ত ব্যক্তিদের কোনই তুলনা হয় না। এ কারণে তার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য সবচাইতে বেশী প্রয়োজন। অন্যথায় তার পক্ষে দায়িত্ব পালন কিছুতেই সম্বব নয়। তাকে যদি এইরূপ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা দেয়া হয়, তাহলেই আশা করা যায়, যথাযথভাবে দায়িত্ব পালনে অনীহা বা বাধা-প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উঠা ও তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অ-প্রভাবিত থাকা সম্বব হবে। আর সে জন্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তার অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন থাকার ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে, যেন সে কখনই লোভের ফাঁদের শিকার হতে না পারে। ইসলাম এজন্য যথাযত গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং ইসলামী হুকুমত বিচারকের জন্য বেতন-ভাতা হিসেবে পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছন।
শুধু অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতাই সুবিচার কার্য সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট নয়। মূলত বিচারকের সেজন্য সকল প্রকার বহিরাগত ও সরকারী বা রাষ্ট্রীয় প্রভাব থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া অপরিহার্য। বিচারকের বিচার কার্যর উপর কোন হস্তক্ষেপ করার-বিচারের নামে অবিচার করার জন্য কোনরূপ চাপ বা প্রলোভন প্রয়োগেরও অধীকার কারোরই থাকতে পারে না। এ জন্যই হযরত আলী (রা) খুলাফায়ে রাশদুনের চতুর্থ খলীফা পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর তাঁর নিয়োগকৃত শাসনকর্তা মালিক আশতার নখয়ীকে লিখে পাঠিয়েছেলেনঃ বিচারককে তোমার নিকট এমন মর্যাদ দেবে, যা পাওযার লোভ তোমার বিশেষ লোকদের মধ্যে অপর কারোই মনে কখনই জাগবে না। তোমার নিকট এইরূপ মর্যাদা থাকলেই বিচারক লোকদের সকল প্রকার প্রভাব ও প্রলোভন থেকে রক্ষা পেতে পারবে। অতএব তুমি সেদিবকে বিশেষভাবে লক্ষ্য নিবন্ধ করবে।[ আরবী টীকা………….]
এর চরম লক্ষ্য হচ্ছে, বিচারক যেন সর্বতোভাবে বহিঃপ্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে এবং কোনরূপ ভয়-ভীতি বা লোভের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকা অবস্থায়ই প্রত্যেকটি মামলার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বিচার চালিয়ে যেতে পারে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (Freedom of judiciary) বলতে বর্তমান এই অব্স্থাই বোঝায় এবং এজন্যই রাষ্ট্রের অন্যান্য সর্বপ্রকারের কর্তৃত্ব থেকে- বিশষ করে নির্বাহী সরকারের (Executive) প্রভাব থেকে তার সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন থাকার দাবি সাবজনীন দাবি হিসেবেই চিরকাল চিহ্নিত হয়ে এসেছে। কেননা জনগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, বিচার বিভাগ সর্বতোভাবে নির্বাহী সরকারের প্রভাবমুক্ত না থাকলে এবং এই বিভাগের ক্ষমতার পরিধি অ-নিয়ন্ত্রিত ও অসংকুচিত না হলে জনগন কখনই সুবিচার পাবে না, বরং তখন সরকার স্বৈরাচার হয়ে জনগণের অধিকার হরন করবে, সে অধিকার ফিরে পাওয়ার আর কোন উপায়ই অবশিষ্ট থাকবে না। ঠিক এ কারণে বিচার বিভাগের পূর্ণ মাত্রার স্বাধীনতা জনগনণের স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
ইসালামী রাষ্ট্রনীতিবিদগণ লিখেছেনঃ সরকারের প্রশাসন কর্তৃত্ব দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ভাগ-বরং প্রথম ভাগ হচ্ছে দেশ শাসন, অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে, জনগণের সংশ্লিষ্ট জটিল সামষ্টিক বিষয়াদিতে স্পষ্ট-অকাট্য রায় দান, পথ নির্দেশনা ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে বিচার কার্য সম্পাদন। রাসুলে করীম (স) এবং খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলে এই দুইটি পদ দুই শ্রেণীর লোকদের উপর অর্পিত ছিল। প্রথম কাজের জন্য যেমন প্রত্যেকটি অঞ্চলে শাসন কর্তা [আরবী…………..] নিযক্ত ছিল, তেমনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে বিচারক ( কাযী ) নিজুক্ত হয়েছিল। অবশ্য কখনও কখনও এ উভয় ধরনের কাজের দায়িত্ব একই ব্যক্তিকেও দেয়া হয়েছে এবং একই ব্যক্তি প্রশাসক ও বিচারক -উভয় পদমর্যাদার দায়িত্ব পালন করেছেন। তাবে তখন তা দেয়া হয়েছে সেই একই ব্যক্তির উভয় দিকের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের বিশেষ যোগ্যতা থাকার কারণে। কিন্তু সাধারণত এইরূপ হতো না বরং দুই কাজের দায়িত্ব দুই স্বতন্ত্র ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হতো। [আরবী টীকা………]
বিচার বিভাগের এই স্বাধীনতা ও সম্পূর্ণ নির্বাহী শক্তি প্রভাবমুক্ত থাকার কারণে রাষ্ট্রপ্রধানকও প্রয়োজনে-বাদী কিংবা বিবদী হয়ে বিচারকরে নিকট উপস্থিত হতে হতো। এবং তথায় তাকে প্রতিপক্ষের সাথে সমান ও সম্পূর্ণ অভিন্ন মর্যাদা পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। তিনি নিজস্বভাবে যেমন কাউকে কোন অপারাধের জন্য দায়ী করে তাকে দন্ডিত করতে পারে না, তেমনি তাঁর নিজের ব্যাপারেও বিচারকের দ্বারস্থ হতে একান্তভাবে বাধ্য। একারণেই হযরত আলী (রা) তাঁর বর্ম হারিয়ে যাওয়ার পর একজন ইহুদীর (কিংবা খৃষ্টান) নিকট তা দেখতে পেয়ে স্বীয় দাপ্ট ব্যবহার করে তাঁর নিকট থেকে তা কেড়ে নিতে পারেন নি। বরং সেজন্য তাঁকে বিচারপতি শুরাইর আদালতে হাযির হয়ে রীতিমত মামল দায়ের করতে হয়েছিল। তিনি দাবি করেছিলেনঃ ওটি আমার বর্ম। আমি ওটি বিক্রয় করিনি, কাউকে দান-ও করিনি। তখন বিচারপতি অভিযুক্তকে তার বক্তব্য বলার নিদের্শ দিয়েছেল। সে বললঃ এ আমার বর্ম। তবে আমি আমীররুল মু ‘মিনীনকে মিথ্যাবাদী ও বলছি না। তখন বিচারপতি হযরত আলীর নিকট প্রমাণ চাইলেন। কিন্তু তিনি বললেনঃ আমার নিকট কোন প্রমাণ নেই। ( অপর এক বর্ণনায় সাক্ষী হিসাবে তাঁর পুত্র ও ক্রীতদাসকে পেশ করা হলে বিচারতি বললেন,পুত্রের সাক্ষ্য পিতার পক্ষে ও ক্রীতদাসকে সাক্ষ্য তার মনিবের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হতে পারে না) তখন বিচারপতি বর্মটি অভিযুক্ত ব্যক্তিরই বলে রায় দিলেন। লোকটি বর্মটি হাতে নিয়ে রওয়ানা দিল। আর খলীফাতুল মুসলিমীন দুই চোখ মেলে তাকিয়েই থাকলেন, তাঁর করার কিছুই ছিল না। কিন্তু লোকটি কিছু দূর যাওয়ার পরই ফিরে এসে বিচারপতিকে লক্ষ্য করে বললঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-এটাকেই বলে নবীর বিধান ও সেই বিধান ভিত্তিক বিচার। এ বর্ম যে আমীরুল মু ‘মিনীনের,তাতে কোন সন্দেহ নেই। আসলে আমিই মিথ্যা দাবি পেশ করেছিলাম।
৩. সুবিচারের জন্য আবশ্যকীয় নিয়ম-নীতির পূর্ণ কার্যকরতা
ইসলাম শুধু বিচারের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেনি। বিচারকের নির্দিষ্ট কয়েকটি গুণ থাকার শর্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি। বিচারকার্য সম্পাদনের জন্য কিতপয় নিয়ম-নীতিও নির্দিষ্ট এবং কার্যকর করেছে। বিচারকের জন্য তা অবশ্যই পালনীয় করে দিয়েছে। অন্যথায় জুলুম ও অসাম্য-অবিচারের কলংক থেকে তার রক্ষা পাওয়া সম্বব নয়। সেই নিয়ম-নীতি যথাযথভাবে পালন করলে সুবিচার করা তার পক্ষে সম্বব হতে পারে।
বিচারকের নিয়ম-নীতি দু ‘ধরনের নিয়ম-নীতি পছন্দনীয় এবং অপর ধরনের নিয়ম-নীতি অপছন্দনীয়। পছন্দীয় নিয়ম-নীতি হচ্ছেঃ
ক. বিচারকের নিজস্ব ক্ষমতাধীন এমন এক-ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতে হবে যে জনগণের যাবতীয় সমস্যা ও মামলা তার সম্মুখে একের পর এক পেশ করবে।
খ. বিচাররে আদালত এমন এক স্থানে হতে হবে, যেখানে সকল লোকের পক্ষেই উপস্থিত হওয়া খুবই সহজ হবে, উপস্থিত হতে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।
গ. বিচারকের আদালত কক্ষ প্রশস্ত, প্রকাশমান ও সুপরিবেশ সম্পন্ন হতে হবে, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সেখানে বসা ও স্বীয় বক্তব্য পেশ করা সহজ হয়।
ঘ. আইনবিদদের এমন একটা সমষ্টি তার নিকট উপস্থিত থাকতে হবে, যেন বিচারক কোনরূপ ভুল করে বসলে তারা তাকে সংশোধন করে দিতে পারে। তা সত্তেও যদি কোনরূপ ভুল হয়ে যায়, তা’হলে তার প্রতিকারের সুযোগ থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়।
ঙ. পক্ষদ্বয়ের মধ্যের কেউ সীমালংঘনমূলক কাজ করলে তাকে নম্রতা সহকারে বুঝিয়ে দিতে হবে ও তাকে ক্ষান্ত হতে বাধ্য করতে হবে।
আর অপছন্দনীয় নিয়ম-নীতি হচ্ছেঃ
ক. বিচারের সময় দ্বাররক্ষী নিয়োগ করা,
খ. ক্রুদ্ধ হয়ে রায় লেখা ও দেয়া,
গ. রায় লেখার ম,য় বিচারকের মন ক্ষুধা, পিপাসা, দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, অত্যধিক আসস্দ-স্ফূর্তি প্রখৃতিতে মশগুল থাকা উচিত নয়।
ঘ. খুব তাড়াহুড়া করে-গভীরভারব চিন্তা-ভাবনা ও বিবেচনা না করে, উভয় পক্ষের বক্তব্য ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য সূক্ষভাবে চুল-চেরা বিশ্লেষণ ও বিবেচণা না করে রায় দেয়াও অনুরূপ।
এ পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী সতর্ক করা হয়েছে ঘুষের ব্যাপারে। োকননা ঘাষ সম্পূর্ণ হারাম। তা গ্যহণ করা যেমন হারাম, তেমনি তা দিয়ে অন্যয়ভাবে নিজের পক্ষে রায় লেখানোর উদ্দেশ্যে য়োও সম্পূর্ণ হারাম। এসব নেতিবাচক কথা। সেই সাথে রয়েছে ইতিবাচক কিছু বাধ্যবাধকতা। এখানে তার মোট সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হচ্ছেঃ
প্রথম-সালাম, সম্মান প্রদর্শন, আসন গ্রহণ, দৃষ্টিদান, কথাবার্তা বালা, লক্ষ্য আরোপ করা প্রভৃতির দিক দিয়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ সমতা রক্ষা করতে হবে।
দ্বিতীয়-এক পক্ষকে অপর পক্ষেরে জন্য ক্ষতিকর বিষয়াদি পরামর্শ না দেয়া।
তৃতীয়-একজনের সাথে সাগ্রহে কথা বলা, যার দরণ অপর পক্ষ নিজেকে অপমানিত ও অসহায় বোধ করতে বাধ্য হয়।
চতুর্থ-দুই পক্ষই যখন মামলায় প্রস্তত হবে এবং বিচার্য বিষয়টিও হবে সুস্পষ্ট, তখন বিচার কার্য সম্পাদন করা কর্তব্য। তবে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা করে দিতে চেষ্টা করা তখনও বাঞ্ছনীয়। তাতে উভয়ের মধ্যে সন্ধি সমঝোতা করে দিতে চেষ্টা করা তখনও বাঞ্ছনীয়। তাতে উভয় পক্ষ অ-রাযী হলে নিশ্চয়ই বিচার করতে হবে। আর বিচার্য বিষয় যদি দুর্বোধ্য ও কঠিন হয়, তাহলে এ কাজটিকেই বিলম্বিত করবে। বিলম্বিত করার সীমা তখন পর্যন্ত প্রসারিত, যখন পর্যন্ত ব্যাপারটি স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে না উঠছে।
পঞ্চম-মামলা যে পরস্সরায় দাখিল হবে, বিচার সেই অনুযায়ী সমাধা করতে হবে।
ষষ্ঠ-বিবাদী যদি এমন কোন দাবি পেশ করে, যার ফলে বাদীর দাবি চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাহলে তা অবশ্যই শুনতে হবে এবং বাদির নিকট থেকে তার জবাবও জেনে দিতে হবে। প্রয়োজন হলে আবার শুরু থেকে মামলার শুনানী শুরু করতে হবে।
সপ্তম-বাদী পক্ষ বা াববাদী নিজ নিজ দাবি প্রত্যাহার করলে মামলা খারিজ করে দেবে।
এই সব কথাই কুরআন বা রাসূলে করীম (স)- এর সুন্নাত থেকে প্রমাণিত। একটি হাদিসে রাসূলে করীম (স) এর এই উক্তি বর্ণিত হয়েছেঃ [আরবি………..]
যে লোক বিচারক হওয়ার বিপদে পড়ে, সে যেন ক্রুদ্ধ অবস্থায় কখনই বিচারের কাজ রা করে।
তিনি বলেছেনঃ [আরবি……………..]
দুই ব্যক্তি যদি তোমার নিকট বিচার প্রার্থী হয়, তাহলে প্রথম জনের জন্য রায় দেয়ার পূর্বেই দ্বিতীয় জনের বক্তব্য শুনে নেবে। তুমি যদি সেরূপ কর তা হলে তোমার বিচার সুষ্ঠ ও সুস্পষ্ট হবে।
সাক্ষাদান
বিচারের ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। সাক্ষী হলো বাদীর দাবীর প্রমাণ এবং বিবাদীর পক্ষে বাদীর দাবি অস্বীকারের উপায়। বাদী যদি তার দাবি বিচারার্থে প্রমাণ করতে চায়, তাহলে তার দাবির পক্ষে সাক্ষ্য পেশ করতে হবে এবং বিবাদী যদি সে দাবি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়, তাহলে তাকেও সেজন্য সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করতে হবে। বিচার কাজে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য এজন্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই উভয় পক্ষের সাক্ষ্য দানে নিশ্চয়ই বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হতে হবে। গোটা বিচারের ব্যাপারটিই এই সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের উপর নির্ভরশীল। সাক্ষী যদি সত্য সাক্ষ্যদান করে তা হলে বিচারকার্য সত্য-ভিত্তিক হবে এবং যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে নিঃসন্দেহে অবিচার হবে। ইসলামে এই ব্যাপারটেকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়েছ। এই পর্যায়ে কুরআন মজীদে অত্যন্ত বলিষ্ট ভাষায় আহবান জানানো হয়েছে ঈমানদার লোকদের প্রতিঃ [আরবি…………..]
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ন্যায়বিচারের জন্য শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও, আল্লাহর জন্য সাক্ষ্যদাতা হিসেবে, যদিও সে সাক্ষ্য তোমাদের নিজেদের কিংবা পিতা-মাতার ও নিকটাত্নীয়দের বিরুদ্ধে পড়ে। সে যদি ধনশীল হয় কিংবা দরিদ্র,তা হলে তো আল্লাহ-ই তাদের জন্য অতীব উত্তম। অতএব তোমরা ন্যায়বিচার না করে নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। [আরবি……………..]
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের সাক্ষ্যদাতা হিসেবে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। দুটো আয়াতেই সাক্ষ্যদাতাকে আল্লাহর জন্য ন্যায়বিচারের পক্ষে শক্ত হয়ে দাঁড়াবার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআনের দৃষ্টিতে মামলার সাক্ষীরা মূলত আল্লাহর সাক্ষী-কোন বিশেষ পক্ষের নয়। তাদের এই সাক্ষ্য হতে হবে ন্যায়বিচারের লক্ষে অর্থাৎ বিচারক ও সাক্ষ্যদাতা সকলেরই সম্মুখে একটি মাত্র লক্ষ্য থাকতে হবে আর তা হচ্ছে মামলার ন্যায়বিচার। অতএব তারা কোন বিশেষ পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেন কোন সাক্ষ্য না দেয় বা তারা যেন এমনভাবে সাক্ষ্য না দেয়, যার দরুন সুবিচার ও ন্যায়বিচার কখনই সম্ভব হতে পারে না। এই জন্য ইসলামে সাক্ষী কি রকমের লোক হতে হবে, সেই বিষয়ে কয়েকটি জরুরী শর্ত আরোপ করা হয়েছে। শর্তসমূহ এইঃ
১. সাক্ষীকে পূর্ণ বয়স্ক হতে হবে। অপ্রাপ্ত বয়স্কের কোন সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।
২. পূর্ণ ও সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে, পাগল বা মতিচ্ছিন্ন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।
৩. সাক্ষীকে অবশ্যই আল্লাহ এবং তার দ্বীনের প্রতি পূর্ণ ঈমান হতে হবে। বে-ঈমান লোকদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।
৪. সাক্ষীকে ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হতে হবে। চরিত্রহীন, অন্যায়কারী বা শরীয়াত লংঘনকারী ব্যাক্তিকে সাক্ষী হিসেবে দাড় করানো যেতে পারে না।
৫. সাক্ষীকে সর্বপ্রকার দুষ্কৃতির অভিযোগ থেকে মুক্ত হতে হবে। দৃষ্কৃতির অভিযোগে পূর্বে অভিযুক্ত হয়েছে-এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যে সন্দেহমুক্ত সত্য কখনই প্রমানিত হতে পারে না। ‘সাক্ষ্যদান’ কে কুরআনের ভাষায় বলা হয়েছে [আরবি…..] এর শাব্দিক অর্থ হলো ‘উপস্থিতি’। অর্থাৎ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময় যে-লোক উপস্থিত ছিল, যে লোক নিজ চক্ষে ঘটনা সংঘটিত হতে দেখেছে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে ঘটনা সম্পর্কে জানতে পেরেছে-সে-ই পারে সাক্ষ্যদান করতে। এইরূপ প্রত্যক্ষ জ্ঞান যার রয়েছে, সে-ই সাক্ষ্য দেবে, সাক্ষ্যদানের অধিকার বা যোগ্যতা কেবল তারই হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে সাক্ষী ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী [আরবি……] হওয়া অতটাই জরুরী যতটা জরুরী স্বয়ং বিচারকের ন্যায়বাদী-ন্যায়পন্থী হওয়া। উপরোদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে এ কথাই বলা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ ‘সাক্ষী যখন ঘটনাকে সূর্যের ন্যায় উজ্জল-উদ্ভাসিত দেখতে পারে, তখন-ই যেন সাক্ষ্য দেয়। নতুবা সাক্ষ্যদানের দুঃসাহস যেন সে না করে’। ‘অকাট্য-সুদৃঢ় বর্ণনা, যা আইনের বিচারালায়ে উপস্থিত হয়ে এমন ব্যাপারে দেয়া, যা বর্ণনাকারী স্পষ্টভাবে দেখেছে’-এটাই হচ্ছে সাক্ষ্যের সংজ্ঞা। এভাবে ইসলামে সাক্ষ্যের উপর এতই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, যার কোন দৃষ্টান্ত দুনিয়ার ইতিহাসে খুব কম-ই পাওয়া যায়। এজন্য সাক্ষ্যকে ন্যায়বাদী ও ন্যায়পন্থী হওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। তার অর্থ, সাক্ষ্য সত্যভিত্তিক হতে হবে, দৃঢ় প্রত্যয়পূর্ণ হতে হবে, কোনরূপ সন্দেহ সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারবে না। তা প্রত্যক্ষ্য ব্যাপার সম্পর্কে হবে, অন্যদের মুখে শোনা বিষয়ে নয়। সাক্ষীকে গণনায় আইনের অনুরূপ হতে হবে। প্রত্যেক সাক্ষীকে বিচক্ষণ ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন হতে হবে। প্রত্যেক্ষ জ্ঞান ও অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্তেও সাক্ষ্য না দেয়া আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার অপরাধ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্টায় অনীহা। পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, দাস-মনিব প্রভৃতি লোকদের পরস্পরের পক্ষে সাক্ষ্যদান গ্রহণীয় নয়। সাক্ষ্যকে বিকৃত করা যেতে পারেনা। সাক্ষ্যদানে অস্বীকৃতি জানানোর কোন অধীকার নেই। সাক্ষ্য গোপন করা অতি বড় গুনাহ-তা আইনবিরোধীও। সাক্ষীকে কেনা চলবে না। সাক্ষীদের সম্মান করতে হবে! কেননা তাদের দ্বারাই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সবই বিভিন্ন হাদীসের কথা। ইসলাম সমস্ত মানুষের মধ্যে পূর্ণ সাম্য ও সমতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। আইনের দৃষ্টিতে-আইনের সম্মুখেও সকল লোক-ই সমান। বিচারকার্যেও লোকদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা যাবে না। এই দৃষ্টিতে বর্তমান পাশ্চাত্য শাসন ও বিচার পদ্ধতি মানুষের উপর জুলুমের ধারক ও বাহক। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বিচার একই আইনের ভিত্তিতে একই আদালতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইসলাম বিচারক নিয়োগে যেসব শর্ত আরোপ করেছে, তা কেবল মাত্র পূর্ণ ঈমানদার, আল্লাহ-ভীরু ও ন্যায়বাদী লোকদের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে। ন্যায়বাদী আল্লাহ ভীরু বিচারক দলীল-প্রমাণ ছাড়া কখনই নিজে ইচ্ছামত বিচার
করে না। ফলে অনেক ভুল থেকেই সে রক্ষা পেয়ে যায়। বর্তমান কালে বিচারকের সেসব গুণ অপরিহার্য মনে হয় না- পাশ্চাত্য বিচার দর্শনে সে ধারণাই অনুপস্থিত-ফলে বিচারের নামে চলছে নানাবিধ অবিচার। হ্যাঁ, কোন বিচারালয়ে অবিচার হয়েছে বা বিচারে ভুল করা হয়েছে মনে হলে অবশ্যই অন্য কোন বিচারক দ্বারা সে মামলার পূনর্বিচার করানো যেতে পারে। এই জন্য বিশেষজ্ঞগণ লিখেছেনঃ [আরবি……………..]
প্রথম বিচারকের রায়ে ভুল প্রকাশিত হলে দ্বিতীয় বিচারক তা বাতিল করে দেবে। প্রথম বিচারক কোন জ্ঞানগত দলীলের বিরুদ্বতা করে থাকলে, যাতে কোন ইজতিহাদের সুযোগ নেই কিংবা কোন ইজতিহাদী দলীলের বিরুদ্বতা করে থাকলে-যার পর আর ইজতিহাদে চলে না, শুধু অসতর্কতার কারণেই ভুল করে থাকে, তাহলে সেই বিচার বাতিল করা যাবে অথবা পক্ষদ্বয় যদি নতুন করে দাবি উত্থাপন করার এবং অপর কোন বিচারকের রায় গ্রহণ করতে রাযী হয়, তখনও পূর্বের রায় বাতিল হয়ে যাবে। এছাড়া অন্য কোনভাবে বিচারের রায় বাতিল হতে পারে না।
৪। ন্যায় বিচার সংক্রান্ত রায়ের বাধাবিঘ্নহীন কার্যকরতা
ইসলাম শুধু বিচার কার্যে ন্যায়পরতা ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণকেই নিশ্চিত করেনি। বিচারের রায়কে যথোচিতভাবে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়তা বিধান করেছে। কেরন বিষয়ে আদালত চূড়ান্তভাবে রায় দান করলে তার কার্যকরতা যাতে কেউ বানচাল করতে না পারে, সে জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলঃ যে অপরাধের সুনির্দিষ্ট শাস্তি (হদ্দ) রয়েছে, তা নিঃসন্দেহে প্রমানিত হওয়ার পর অপরাধীর উপর তা অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। অপরাধী শক্তিমান হোক কি দুর্বল, উচু বংশজাত সম্ভ্রান্ত হোক কি নীচু বংশজাত-অসম্ব্রান্ত এবং সে পুরুষ হোক কি নারী, শাস্তি কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটতে দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কোনরূপ দুর্বলতা দেখানো কিংবা তা বিলম্বিতকরণ অথবা আল্লাহর নিদের্শ কার্যকর করণে কোন রূপ দয়া-মমতা প্রদর্শনের অধিকার কারো নেই। ইসলামী শরীয়াত বিশেজ্ঞরা এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনরূপ শাফায়াত কিংবা সুপারিশ করা এবং সেই সুপারিশ গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। হযরহ আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আ’স (রা)-এর একটিবর্ণনা অনুসারে রাসূলে করীম (স) ইরশাদ করেছেনঃ
[আরবি……………………….]
তোমার আল্লাহর নির্ধারত শান্তি (হ্দ্দ) কার্যকর হওয়ার যোগ্য অপরাধ পারস্পরিক পর্যায়ে ক্ষমা করতে পার: কিন্তু এ ধরণের অপরধের অভিযোগ আমার নিকট পেশ করা হলে তা অবশ্যই হবে। এ পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসুলে করীম (স)-এর এই হাদীসটিও বর্ণনা করেছেনঃ [আরবী…………..]
আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তিগুলোর মধ্যে কোন একটি শাস্তর পথে যদি কারো সুপারিশ বাধা হয়ে ‘দাড়াল। এ প্রসঙ্গে মাখযুমিয়া নাম্নী কুরাইশ মহিলার চুরি সংক্রান্ত ঘটনার কথা উল্লেখযোগ্য। হযরত আয়েশা (রা)-বর্ণনা করছেন, মাখযুমিয়া চুরি করে ধরা পড়লে কুরাইশরা খুব চিন্তিত হয়ে আলোচনার পর স্থির হল যে, রাসুলের নিকট প্রিয় ব্যক্তি উসামা ছাড়া এই কাজ আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়। উসামা এ ব্যাপারে রাসুলে করীম (স)-এর সাথে কথা বলায় তিনি ধমকের সুরে বললেনঃ [আরবী………………]
আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করণের ব্যাপারে তুমি সুপারিশ করছে?
এরপর তিনি উপস্থিত লোকদের সম্বোধন করে বললেনঃ হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এই নীতির অনুসারী ছিল যে, তাদের মধ্য থেকে কোন ভদ্র ব্যক্তি চুরি করলে এমনিই তাকে নিষ্কৃতি দিত। আর কোন হীন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তার উপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি ( হ্দ্দ )কার্যকর করত। আল্লাহর কসম! মুহম্মদ-তনয়া ফাতিমাও যদি চুরি করে, তাহলে মুহাম্মদ তার হাত অবশ্যই কেটে ফেলবে। ইসলামী আদালতের রায় তথা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করণে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি যতটা কঠোর তা এ থেকেই অনুবধন করা চলে।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি