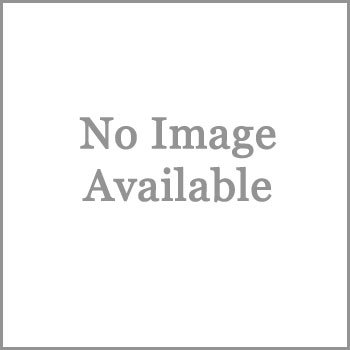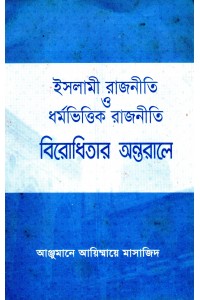দ্বিতীয় খন্ড
ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা : মূলনীতি ও কর্মপন্থা
ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ
ইসলামী সংবিধানের ভিত্তিসমূহ
ইসলামী রাষ্ট্রের দৃষ্টান্তমূরক যুগ
ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ
কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়
ষষ্ঠ অধ্যায়
ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস
১ কুরআন মজীদ
২ রসূলূল্লাহ(স)-এর সুন্নাহ
৩ খিলাফতে রাশেদার কার্যক্রম এবং উম্মদের মুজতাহিদগণের সিদ্ধান্ত
৪ সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা
গ্রন্থের এই দ্বিতীয়ভাগে আমরা ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি ও তার কর্মপন্থার রূপরেখা পেশ করবো। ফলে আমাদের সামনে ইসলামী সংবিধানের একটি সুস্পষ্ট খসড়াও এসে যাবে। পুস্তকের এই অংশে আমরা সর্বপ্রথম ইসলামের সাংবিধানিক আইনের উৎস সম্পর্কে আলোচনা করা যক্তিসংগত মনে করি, যাতে করে পরের সমস্ত আলোচনার ভিত্তিমূল আমাদের সামনে এসে যেতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্র সম্পর্কে যদি প্রথম পদক্ষেপেই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তার মূর উৎস হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ, অন্যান্য রাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা নয়, তাহলে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারবেনা। মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী এবং তথাকথিত আধুনিকতাবাদীদের মূল চিন্তাগত বিভ্রান্তি এই যে, তারা কথা তো বলে ইসলামী রাষ্ট্রের, কিন্তু উৎস হিসেবে রুজু হয় পাশ্চাত্য জাতিসমূহের প্রতি। আমরা নিশ্চয়ই অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারি, তবে তা আমাদের নিজেদের ব্যবস্থার সীমার মধ্যে অবস্থান করে এবং তার প্রাণসত্তাকে অটুট রেখে। এ কারণেই আমরা সর্বপ্রথম সাংবিধানিক আইনের উৎস এবং তাকে কাজে লাগানোর পথের অসুবিধাগুলো তুলে ধরবো।
আরও একটি কারণ এই আলোচনার প্রয়োজন হয়েছে এবং তা হচ্ছে হাদীস অস্বীকার করার ফেতনা। একটি দল হাদীস সম্পর্কে বুদ্ধিবৃত্তিক সন্দিহান করে তোলার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে। তারা হাদীসকে আইনের উৎস ও প্রমাণ্য দলীল [হুজ্জাত] হওয়ার বিষয়ে আপত্তি তোলে। এই দৃষ্টিভংগির সমালোচনার এবং সঠিক ও বাস্তব অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদানের সীমাহীন প্রয়োজন রয়েছে। সত্য কথা হলো, হাদীস ব্যতীত ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার কোনো সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রণীত হতেই পারেনা।
আলোচ্য অধ্যায়ে গ্রন্থকারের বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রয়োজনীয় অংশ সংকলিত করা হয়েছে এবং টীকায় সেসব নির্দেশ করা হয়েছে। (আমরা এসব গ্রন্থে বাংলা সংস্কারণ উল্লেখের চেষ্টা করবো- অনুবাদক)
-সংকলক।
ইসলামে সাংবিধানিক আইনের উৎস
যে রাষ্ট্র আল্লাহ্র সার্বভৌমত্ব এবং খিলাফত আলা মিনহাজিন নবূয়্যত [নবুয়্যতের পদ্ধতিতে শাসনকার্য পরিচালনা]-এর ব্যবস্থাকেতার যাবতীয় বৈশিষ্ট্যসহ প্রতিষ্ঠিত করে, তাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে। আজ পৃতিবীর যেখানেই এরূপ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এবং তার ধরন ও কর্মপন্থা নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালানো হবে সেখানেই কয়েকটি বিশেষ উৎসের দিকে রুজু হতে হবে। সেগুলো হচ্ছে কুরআন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ, খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম এবং উম্মাতের মুজতাহিদ আলেমগণের সিদ্ধান্ত। ইসলামের অলিখিত রাষ্ট্রীয় সংবিধাদেনর উৎস এই চারটি এবং এগুলো অধ্যয়ন করলে ইসলামী রাষ্ট্রের ধরন ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যাবে এবং ইসলামী সংবিধানের আনুষঙ্গিক নীতিমালা ও ধারাসমূহ তা থেকে বের করা যাবে।
১. কুরআন মজীদ
ইসলামী সংবিধানের সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস হচ্ছে কুরআন মজীদ। ইসলামের পরিভাষায় “কিতাব” বলতে সেই গ্রন্থকে বুঝায় যা মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে তাঁর রসূলগণের উপর নাযিল করা হয়। এ অর্থের প্রেক্ষিতে “কিতাব” হচ্ছে সেই পয়গামের সরকারী বিবৃতি [Official Version] অথবা ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী ‘খোদায়ী কালাম’ যা মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে, যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে এবং যাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে দুনিয়ায় পয়গাম্বর প্রেরিত হয়ে থাকে। আল্লাহর স্থায়ী নিয়ম এই যে, পয়গাম্বরের মাধ্যমে মানুষকে যে শিক্ষাদান করা আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্য তার মূলনীতি ও মৌল বিষয়াদি তাঁর তরফ থেকে পয়গাম্বরের হৃদয়ের প্রত্যদিষ্ট হয়। তার ভাষা এবং অর্থ কোনোটাতেই পয়গাম্বরের নিজস্ব বুদ্ধি ও চিন্তা, তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্খার বিন্দু পরিমাণ দখল থাকেনা। এ কারণেই তা শব্দ এবং অর্থ উভয়দিক থেকেই আল্লাহর কালাম, পয়গাম্বরের নিজস্ব রচনা নয়। পয়গাম্বর একজন বিশ্বস্ত দূত হিসেবে এ কালাম আল্লাহ্র বান্দাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকেন। তদুপরি তিনি আল্লাহর দেয়া দূরদৃষ্টির সাহায্যে কিতাবের অর্থ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এসব খোদায়ী মূলনীতির ভিত্তিতে পয়গাম্বর নৈতিকতা, সামাজিকতা এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক পূর্ণাংগ কাঠামো গড়ে তোলেন। তিনি শিক্ষা প্রচার, সদুপদেশ এবং নিজের পূত চরিত্রের মাধ্যমে লোকদের ধ্যানধারণা, ঝোঁক প্রবণতা ও চিন্তাধারায় এক মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে তাকওয়া, পবিত্রতা, নির্মলতা ও সদাচারণের ভাবধারা সঞ্চারিত করেন। শিক্ষাদীক্ষা ও বাস্তব পথ নির্দেশের দ্বারা তাদেরকে এমনভাবে সুসংহত করেন যে, নতুন মানসিকতা, নতুন চিন্তা ও ধ্যান ধারণা, নতুন রীতি নীতি এবং নতুন আইন কানুনের সংগে এক নতুন সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। পরন্তু তিনি তাদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব এবং সেই সংগে নিজের শিক্ষা দীক্ষা ও পূত চরিত্রের এমন নিদর্শন রেখে যান, যা হামেশা সমাজ এবং পরবর্তী বংশধরদের জন্যে হিদায়াতের আলোক বর্তিকার কাজ করে।
আল্লাহ্র নাযিলকৃত কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন মজীদ সর্বশেষ ও পূর্ণাংগ আসমানী কিতাব। মুসলমানগণ তো সমস্ত আসমানী কিতাবের উপর ঈমান রাখে, কিন্তু তাদের জন্য হিদায়াতের বিধান ও জীবন যাপনের আইন কানুন প্রদানের মর্যাদা কেবল কুরআন মজীদের জন্য সংরক্ষিত। আমাদেরকে উত্তমরূপে বুঝি নিতে হবে যে, যেখান থেকে কার্যত আনুগত্য ও অনুসরণের সীমারেখা শুরু হয় সেখান থেকে অন্যান্য আসমানী কিতাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। এই কিতাব আমাদের জন্য হিদায়াত লাভের মূল ও হুজ্জাত [Authority] হবার বিভিন্ন কারণ রয়েছে।
১. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব শব্দসম্ভারে কুরআন মজীদ পেশ করেছেন তা অবিকল সেসব শব্দ সহকারে সংরক্ষিত রয়েছে। প্রথম দিন থেকে হাজারো লাখো ও কোটি কোটি মানুষ প্রত্যেক যুগে তা অক্ষরে অক্ষরে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, লাখো কোটি মানুষ তা দৈনন্দিন তিলাওয়াত করছে সর্বদা তা পুস্তকাকারে লিখিত ও মুদ্রিত হচ্ছে এবং কখনও তার মূল পাঠে ক্ষুদ্রতম মতভেদ পাওয়া যায়নি। অতএব এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের জবানিতে যে কুরআন শ্রুত হয়েছিলো তা আজও অবিকল দুনিয়াতে বিদ্যমান এবং চিরকাল বিদ্যমান থাকবে, তাঁর একটি শব্দেরও পরিবর্তন হয়নি এবং হতেও পারেনা।
২. কুরআন আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, যা আজও একটি জীবন্ত ভাষায়। আজ দুনিয়ায় কোটি কোটি আরবী ভাষাভাষী লোক বর্তমান। কুরআন অবতরণকালে যেসব পুস্তক এ ভাষায় শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ সাহিত্য ছিলো, আজ পর্যন্ত তাই রয়েছে। মৃত ভাষাগুলোর পুস্তকাদি বুঝতে আজ যেসব অসুবিধা দেখা দেয়, এর অর্থ ও মর্ম উপলব্ধি করতে সেরকম কোনো অসুবিধাই নেই।
৩. কুরআন পুরেপুরি সত্য ও অভ্রান্ত এবং আদ্যপান্ত খোদায় শিক্ষায় পরিপূর্ণ। এতে কোথাও মানবীয় আবেগ, প্রবৃত্তির লালসা, জাতীয় বা গোত্রীয় স্বার্থপরতা এবং মুর্খতাজাত গোমরাহীর চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়না। এর ভেতর খোদায়ী কালামের সংগে মানবীয় কালাম অনু পরিমাণ ও মিশ্রিত হতে পারেনি।
৪. এতে গোটা মানবজাতিকেই আহ্বান জানানো হয়েছে এবং এমন আকীদা বিশ্বাস, চরিত্রনীতি ও আচরণবিধি পেশ করা হয়েছে তা কোনো দেশ, জাতি এবং যুগ বিশেষের জন্য নির্দিষ্ট নয়। এর প্রতিটি শিক্ষা যেমন বিশ্বজনীন তেমনি চিরস্থায়ীও।
৫. পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থাবলীতে যেসব সত্যতা, মৌলিকতা এবং কল্রঅন ও সৎকাজের কথা বিধৃত হয়েছিলো, এতে তার সবই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। কেনো ধর্মগ্রন্থ থেকে এমন কোনো সত্য ও সৎকাজের কথা উদ্ধৃত করা যাবেনা, কুরআনে যার উল্লেখ নেই। এমন পূর্ণাংগ গ্রন্থের বর্তমানে মানুষ স্বভাবতই অন্য সমস্ত গ্রন্থ থেকে মুখাপেক্ষাহীন হয়ে যায়।
৬. কুরআন হচ্ছে আসমানী হিদায়াত ও খোদায়ী শিক্ষা সংক্রান্ত সর্বশেষ [Latest Edition] গ্রন্থ। অতীতের গ্রন্থাবলীতে বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে যেসব বিধি ব্যবস্থা দেয়া হয়েছিলো, এতে তা বাদ দেয়া হয়েছে এবং অতীতের গ্রন্থাবলীতে অনুপস্থিত এমন অনেক নতুন শিক্ষাও এতে সংযোজিত করা হয়েছে:
“আমরা কোনো আয়াত রহিত করলে কিংবা বিস্মৃত হতে দিলে তা থেকে উত্তম বা তার সমতুল্য কোনো আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জানোনা যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।” [সূরা আলবাকারা: ১০৬]
কাজেই যে ব্যক্তি পূর্ব পুরুষদের নয়, বরং খোদায় হিদায়াতের অনুসারী তার পক্ষে এই সর্বশেষ আসমানী কিতাবের অনুসরণ করা একান্ত আবশ্যক, পুরনো গ্রন্থাবলীয় নয়। এখন কুরআন মজীদই হচ্ছে হুজ্জাত [Authority], তার পূর্বেকার কিতাবসমূহ নয়। এসব কারণে ইসলাম অন্য সমস্ত আসমানী কিতাবের সাথে আনুগত্যের সম্পর্ক ছিন্ন করে শুধুমাত্র কুরআনের সাথে আনুগত্যের সমর্ক স্থাপন করেছে এবং গোটা মানবজাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে, তারা যেনো এই কিতাবকে তাদের জীবন যাপনের পথনির্দেশিকা বানায় এবং মুসলমানদের জন্য এই কিতাবকে হিদায়াতের প্রথম উৎস সাব্যস্ত করে। মহান আল্লাহ বলেন:
“আমি এ কিতাব তোমার প্রতি সত্যসহ নাযিল করেছি, যাতে তুমি লোকদের মধ্যে আল্লাহ্র দেয়া সত্য জ্ঞানসহ বিচার ফয়সালা করতে পারো।” [সূরা আননিসা: ১০৫]
“অতএব যারা এ নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং যারা তাঁর সাহায্য ও সহায়তা করেছে, এবং তাঁর সংগ অবতীর্ণ নূরের অনুসরণ করে চলেছে, তারাই কল্যাণপ্রাপ্ত।” [সূরা আরাফ: ১৫৭]
“আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে যারা ফয়সালা করেনা তারাই কাফের….. তারাই যালেম…… তারাই সত্য ত্যাগকারী।” [সূরা আলমায়েদা:৪০-৪৭]
“[তাফহীমুল কুরআন, সূরা মায়েদা ৭৭ নং টীকার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।] যেসব লোক আল্লাহ্র নাযিল করা বিধান অনুযায়ী বিচার ফয়সালা করেনা আল্লাহ্ তায়ালা তাদের জন্য এখানে তিনটি উক্তি করেছেন। [এক] তারা কাঅের [দুই] তারা যালেনম [তিন] তারা ফাসেক। এর সুস্পষ্ট অর্থ হলো, যারা আল্লাহর নির্দেশ এবং তাঁর নাযিলকৃত বিধান ত্যাগ করে নিজেদের বা অন্যদের রচিত আইনের ভিত্তিতে বিচার ফয়সালা করে তারা মূলত তিনটি মারাত্মক অপরাধ করে। [এক] তাদের এই কাজ আল্লাহর নির্দেশ পালনে অস্বীকৃতি স্বরূপ, তা কুফর, [দুই] তাদের এই কাজ সুবিচারের পরিপন্থী। কেননা পুরোপুরি সুবিচার অনুযায়ী যা কিছু নির্দেশ বা হুকুম হতে পারে তাতো আল্লাহই নাযিল করেছেন। অতএব আল্লাহর বিধান হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য কোনো ফায়সালা করলে তারা পরিষ্কার যুলুম করে, [তিন] বান্দাহ হওয়া সত্ত্বেও যখন তারা নিজে মালিক ও প্রভুর অমান্য করে এবং নিজস্ব বা অপর কারো আইন জারী করে, তখন সে কার্যত বন্দেগী ও আনুগত্য অস্বীকারের ক্ষেত্রেও সীমালংঘন করে। এটাই হচ্ছে ফিসক বা ফাসেকী [সত্য ত্যাগ]। এই কুফর, যুলুম ও সত্য ত্যাগ মূলতঃ আল্লাহর বিধান অমান্য করারই বাস্তব রূপ। যেখানেই আল্লাহর বিধান লংঘন করা হবে সেখানেই এই তিনটি বিষয় অপরিহার্যরূপে বিদ্যমান থাকবে। অবশ্য আল্লাহর বিধান লংঘনের মাত্রা ও পর্যায়ে যেমন পার্থক্র হতে পারে, এই তিনটি বিষয়েও অনুরূপ পার্থক্য হয়ে থাকে।”
[‘ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা’ থেকে উদ্ধৃত।] মুসলমানদের জন্য আসল সনদ ও প্রমাণ হচ্ছে কুরআন মজীদ। যা কুরআনের পরিপন্থী তা কখনও অনুসরণীয় ও অনুবর্তনযোগ্য নয়।:
“হে মুহাম্মাদ! বলে দাওঃ আমি এ কিতাবকে নিজের তরফ থেকে বদলাবার অধিকার নাই। আমি তো কেবল সেই ওহীরই আনুগত্য করি, যা আমার প্রতি নাযিল করা হয়। আমি যদি আমার প্রভুর অবাধ্য হই তাহলে আমার কঠিন দিন সম্পর্কে ভয় হয়।” [সূরা ইউনুস: ১৫]
“যা কিছু তোমাদের প্রভুর তরফ থেকে তোমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে তা অনুসরণ করো এবং তাকে ছেড়ে অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদের মাত্রই অনুসরণ করোনা।” [সূরা আলআরাফ: ৩]
[‘ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন’ থেকে উদ্ধৃত।] কুরআন মজীদ ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সর্বপ্রথম উৎস। তার মধ্যে আল্লাহ তায়ালার বিধান ও ফরমানসমূহ বিদ্যমান। এসব বিধান ও ফরমান গোটা মানব জীবনের যাবতীয় বিষয়ের উপর পরিব্যপ্ত। কুরআন মজীদে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চারিত্র, নৈতিকতা ও কার্যকলাপ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা দান করা হয়নি বরং সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের [Social Life] প্রতিটি দিক ও বিভাগের সংস্কার, সংশোধন ও সংগঠনের জন্যও কিছু নীতিমালা ও কিছু বিধান প্রদান করা হয়েছে এবং এই প্রসংগে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কোন্সব নীতিমালার ভিত্তিতে কি উদ্দেশ্যে তারে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তুলবে।
২. রাসূরুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ [বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য পাঠ করুন- এই গ্রন্থকারের পুস্তক “সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা” এবং “নির্বাচিত রচনাবলী” ১ম ও ২য় খণ্ড।]
ইসলামী সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হচ্ছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। সুন্নাহ্র সাহায্যে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদের নির্দেশ ও হিদায়াত এবং কুরআন প্রদত্ত মূলনীতিসমূহ আরব ভূমিতে কিভাবে কার্যকর করেছেন, কিভাবে ইসলামের চিন্তাকে বাস্তব রূপদান করেছেন, কিভাবে সেই চিন্তার ভিত্তিতে একটি সমাজ কাঠামো গঠন করেছেন, অতপর কিভাবে ইই সমাজকে সুসংগঠিত করে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোয় দাঁড় করেছেন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগকে কিভাবে পরিচালনা করেছেন। এসব কিছু আমরা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ থেকেই জানতে পারি এবং তার সাহায্যে আও জানতে পারি যে, কুরআনের সঠিক ও যথার্থ লক্ষ ও উদ্দেশ্য কি। সুন্নাহ মূলত কুরআন মজীদ প্রদত্ত নীতিমালার বাস্তব ও প্রয়োগিক রূপ যা থেকে আমরা ইসলামী সংবিধানের জন্য অতীব মূল্যবান নজীর [Precedents] লাভ করতে পারি এবং সাংবিধানিক ঐতিহ্যের [Conventions of Constitution] খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সংগ্রহ করতে পারি।
সুন্নাহ আমাদের সাংবিধানিক আইনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উৎস। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কিছুকাল ধরে একটি সম্প্রদায় তার গুরুত্বকে খাটো করে এবং তার আইনের উৎস হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তাই আমরা এখানে সুন্নাহ্র আইনের উৎসস হওয়ার উপর কিছু আলোকপাত করবো।
এটা [১৯৫৮ সালের ৩৪রা জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সেমিনার এই গ্রন্থকারের একটি নিবন্ধ পাঠের পর জনৈক মুনকিরে হাদীস [হাদীস অস্বীকারকারী] উঠে দাড়িয়ে উক্ত প্রবন্ধের উপর কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। উক্ত সেমিনারেই নিবন্ধকার এই জবাব দেন।] এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা কোনো ক্রমেই অস্বীকার করা যায়না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে শুধু কুরআন পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি বরং একটি ব্যাপক আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। এর ফলস্বরূপ একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, সভ্যতা সংস্কৃতির এক নতুন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এসব কাজ যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তা শেষ পর্যন্ত কি হিসেবে করেছেন? এসব কাজ কি নবীর কাজ হিসেবে সম্পাদিত হয়েছিলো যার মধ্যে তিনি আল্লাহর মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন? নাকি তাঁর নবূয়্যতী মর্যাদা কুরআন শুনিয়ে দেয়ার পর শেষ হয়ে যেতো এবং এরডপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মতো শুধু একজন মুসলমান হিসেবে থেকে যেতেন, যাঁর কথা ও কাজ নিজের মধ্যে কোনো আইনের সনদ ও দলীলের মর্যাদা রাখতোনা? যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয় তাহলে সুন্নাতকে কুরআনের সাথে আইনের সনদ ও দলীল হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য দ্বিতীয় অবস্থায় সুন্নাতকে আইনের মর্যাদা দেয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।
কুরআনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল পত্রবাহক ছিলেননা বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলো এবং যাঁর জীবনকে সমগ্র ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নমুনা হিসেবে বাস্যস্ত করা হয়েছে। বুদ্ধিবৃবেক সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তা একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, একজন নবী কেবল খোদার কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত তো নবী থাকবেন, কিন্তু এরপর তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তিমাত্র রয়ে যাবেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তারা ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে এবং গোটা দুনিয়ার মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ, তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধের আনুগত্যকে বাধ্যাতামূলক বলে স্বীকার করে আসছে। এমনকি কোনো অমুসলিম পণ্ডিতও এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেনা যে, মুসলমানরা সবসময় তাঁর এই মর্যাদা স্বীকার করে আসছে এবং এরই ভিত্তিতে ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে সুন্নাহ্কে কুরআনের সাথে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।
আজি জানিনা, কোনো ব্যক্তি সুন্নাতের এই আইনগত মর্যাদা কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে না বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কুরআন পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত নবী ছিলেন এবং একাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে তাঁর নবূয়্যতী মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া সে যদি এরূপ দাবি করেও তাহলে তাকে বলতে হবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের মর্যাদা সে নিজেই দিচ্ছে, নাকি কুরআন তাঁকে এই ধরনের মর্যাদা দিয়েছেন? প্রথম ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে তার কথার কোনো সম্পর্ক নেই এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাকে কুরআন থেকেতার দাবির সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।
এব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখা হয়নি যে, কুরআন মজীদ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কি মর্যাদা নির্ধারণ করেছে এবং রিসালাতের পদের কোন্ কোন্ কাজ তিনি আঞ্জাম দিয়েছেন।
ক. রসূরুল্লাহ (স) শিক্ষক ও মুরুব্বী হিসেবে [সুন্নাতে রসূলের আইনগত মর্যাদা গ্রন্থ থেকে সংযোজিত।]
আলকুরআনে চার স্থানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের পদমর্যাদা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রয়েছে:
“স্মরণ করো, ইবরাহীম ও ইসমাঈল যখন এই [কা’বা] ঘরের প্রাচীর নির্মাণ করছিলো [তখন এই বলে তারা দোয়া করেছিলো: ]….. হে আল্লাহ! এদের নিকট এদের জাতির মধ্যে থেকেই এমন একজন রসূলু প্রেরণ করো, যিনি তাদেরকে তোমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শুনাবেন, তাদেরকে কিতাব ও জ্ঞানের শিক্ষাদান করবেন এবং তাদের বাস্তব জীবনকে পরিশুদ্ধ করবেন।” [সূরা আলবাকারা: ১২৭-১২৯]
“যেমন আমি তোমাদের নিকট স্বয়ং তোমাদের মধ্য থেকে একজন রসূল পাঠিয়েছি, যে তোমাদের আয়াত পাঠ করে শুনায়, তোমাদের জীবন পরিশুদ্ধ করে, তোমাদের কিতাব ও হিকমতের জ্ঞান দান করে এবং তোমরা যে জ্ঞান সম্পর্কে কিছুই জানতেনা তা তোমাদের শিক্ষা দেয়।” [সূরা আলবাকারা: ১৫১]
“প্রকৃতপক্ষে ঈমানদার লোকদের প্রতি আল্লাহ্ এই বিরাট অনুগ্রহ করেছেন যে, স্বয়ং তাদের মধ্য থেকে এমন একজন নবী বানিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনায়, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করে এবং তাদের কিতাব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের শিক্ষা দেয়।” [আলে ইমরান: ১৬৪]
“তিনিই উম্মীদের মধ্যে [এমন] একজন রসূল স্বয়ং তাদেরই মধ্য থেকে প্রেরণ করেছেন যে তাদেরকে তাঁর আয়াতসমূহ শুনায়, জীবন পরিশুদ্ধ করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দেয়।” [সূরা জুময়া: ২]
উপরোক্ত আয়াতসমূহে বার বার যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পূনর্ব্যক্ত হয়েছে তা হলো, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসূলকে শুধুমাত্র কুরআনের আয়াতসমূহ শুনিয়ে দেয়ার জন্য পাঠাননি বরং তার সাথে নবী হিসেবে প্রেরণের আরও তিনটি উদ্দেশ্য ছিলো:
১. তিনি লোকদের কিতাবের শিক্ষাদান করবেন।
২. এই কিতাবের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কাজ করার কৌশল [হিকমাহ] শিক্ষা দিবেন।
৩. তিনি ব্যক্তি ও তাদের সমাজের পরিশুদ্ধি করবেন। অর্থাৎ নিজের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দোষত্রুটি দূর করবেন এবং তাদের মধ্যে উত্তম গুণাবলী ও উন্নত সমাজব্যবস্থার বিকাশ সাধন করবেন।
প্রকাশ থাকে যে, কিতাব ও হিকমাতের শিক্ষা দান অবশ্যি কুরআনের শব্দ শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কোনো কাজই ছিলো, অন্যথায় পৃথকভাবে তার উল্লেখ অর্থহীন। অনুরূপভাবে ব্যক্তি ও সমাজের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি যেসব উপায় ও পদ্ধতি গ্রহণ করতেন, তাও কুরআনের শব্দ পাঠ করে শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত কিছুছিলো, অন্যথায় প্রশিক্ষণের এই পৃথক কার্যক্রমের উল্লেখের কোনো অর্থ ছিলোনা। এখন বলুন,কুরআন মজীদ পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এই শিক্ষক ও মুরুব্বীর পদ যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ন্যস্ত ছিলো, তা কি তিনি শক্তিবলে দখল করেছিলেন, না আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে এ পদে নিয়োগ করেছেন। কুরআন মজীদের এই সুস্পষ্ট ও পুনরুক্তির পরও এই কিতাবের উপর ঈমান পোষণকারী কোনো ব্যক্তি কি একথা বলার দুঃসাহস করতে পারে যে, এই দুটি পদ রিসালাতের অংশ ছিলোনা এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব পদের দায়িত্ব ও কার্যক্রম রসূল হিসেবে নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে আঞ্জাম দিতেন? সে যদি তা বলতৈ না পারে তবে আপনি বলুন, কুরআন মজীদের পাঠ শুনিয়ে দেয়ার অতিরিক্ত যেসব কথা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাবের শিক্ষা ও হিকমাত [কৌশল] প্রসংগে বলেছেন এবং নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজের যে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বলে স্বীকার করতে এবং তাকে সনদ [দলীল প্রমাণ] হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করলে তা স্বয়ং রিসালাত অস্বীকার করা নয় কি?
খ. রসূরুল্লাহ (স) আল্লাহর কিতাবের ভাষ্যকার হিসেবে
সূরা আননাহল-এ আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“এবং [হে নবী!] এই যিকির তোমার উপর নাযিল করেছি যেনো তুমি লোকদের সামনে সেই শিক্ষা ধারার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে থাকো, যা তাদের উদ্দেশ্য নাযিল করা হয়েছে।” [আননাহল: ৪৪]
উপরোক্ত আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিলো যে, কুরআন মজীদে আল্লাহ তায়ালা যে হুকুম আহ্কাম ও পথনির্দেশ দিয়েছেন, তিনি তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দান করবেন। স্থুলবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও অন্তত এতোটুকু কথা বুঝতে সম্ভব যে, কোনো কিতাবের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শুধুমাত্র সেই কিতাবের মূলপাঠক পড়ে শুনিয়ে দিলেই হয়ে যায়না বরং ব্যাখ্যাদানকারী তার মূলপাঠের অধিক কিছু বলে থাকেন, যাতে শ্রবণকারী কিতাবের অর্থ পূর্ণরূপে বুঝতে পারে। আর কিতাবের কোনো বক্তব্য যদি কোনো ব্যবহারিক [Practical] বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত হয় তাহলে ভাষ্যকার ব্যবহারিক প্রদর্শনী [Practical Demonstration] করে বলে দেন যে, গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এভাবে কাজ করা, তা না হলে কিতাবের বিষয়বস্তু তাৎপর্য ও দাবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীকে কিতাবের মূলপাঠ শুনিয়ে দেয়াটা মকতবের কোনো শিশুর নিটও ব্যাখ্যা বা ভাষ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারেনা। এখন আপনি বলুন, এই আয়াতের আলোকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ভাষ্যকার কি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন, নাকি আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভাষ্যকার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন? এখানে তো আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূলের উপর কিতাব নাযিল করার উদ্দেশ্যই বর্ণনা করেছেন যে, রসূল নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে কিতাবের তাৎপর্য তুলে ধরবেন। অতপর কিভাবে এটা সম্ভব যে কুরআনের ভাষ্যকার হিসেবে তাঁর পদমর্যাদাকে রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে পৃথক সাব্যস্ত করা হবে এবং তাঁর পৌঁছে দেয়া কুরআনকে গ্রহণ করে তাঁর প্রদত্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো হবে? এই অস্বীকৃতি কি সরাসরি রিসালাতের অস্বীকৃতির নামান্তর নয়?
গ. রসূলুল্লাহ (স) নেতা ও অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে
সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“[হে নবী] বলো, তোমরা যদি আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো তবে আমার অনুসরণ করো, আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন…… বলো, আল্লাহ ও রসূলের অনুগত্য করো। অতপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে কাফেরদের আল্লাহ্ পছন্দ করেননা।” [ইমরান: ৩১-৩২]
সূরা আহযাবে আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রসূলের মধ্যে অনুসরণীয় আদর্শ রয়েছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহ্ ও আখিরাতের আকাংখী।” [আহযাব: ২১]
উপরোক্ত আয়াতদ্বয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নেতা সাব্যস্ত করেছেন, তাঁর আনুগত্য করার নির্দেশ দিচ্ছেন, তার জীবন চরিত্রকে অনুসরণীয় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন এবং পরিষ্কার বলছেন যে, তাঁর নীতি অবলম্বন না করলে আমার নিকট কোনো আশা রেখোনা। এছাড়া আমার ভালোবাসা লাভ করা যায়না। তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া কুফরী। এখন আপনি বলুন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি স্বয়ং নেতা ও পথপ্রদর্শক হয়ে গিয়েছিলেন? নাকি মুসলমানগণ তাঁকে নির্বাচন করেছিলো? আর নাকি আল্লাহ তায়ালাই তাঁকে এই পদে সমাসীন করেছেন? কুরআনুল করীমের এ আয়াত দ্ব্যর্থহীনভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত পথপ্রদর্শক ও নেতা সাব্যস্ত করার পরও তাঁর আনুগত্য ও তাঁর জীবন চরিত্র অনুসরণ করার ব্যাপারটি কিভাবে প্রত্যাখ্যান করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের জবাবে একথা বলা সম্পূর্ণ অর্থহীন যে, এর দ্বারা কুরআন মজীদের অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে, যদি তাই অর্থ হতো তবে “[কুরআনের অনুসরণ করো]” বলা হতো “[আমার অনুসরণ করো] বলা হতোনা।” এ অবস্থায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত্রকে উত্তম আদর্শ বলার তো কোনো অর্থই ছিলোনা।
ঘ. শরীয়ত প্রণেতা হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)
সূরা আরাফে মহান আল্লাহ্ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখপূর্ব ইরশাদ করেন:
“সে তাদেরকে ন্যায়ানুগ কাজের আদেশ করে, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে, তাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল এবং নাপাক জিনিসসমূহ হারাম করে, আর তাদের উপর থেকে সেই বোঝা সরিয়ে দেয় যা তাদের উপর চাপানো ছিলো এবং সেই বন্ধনসমূহ খুলে দেয় যাতে তারা বন্দী ছিলো।” [আরাফ: ১৫৭]
উল্লেখিত আয়াতের শব্দসমূহ একটি বিষয় সম্পূর্ণ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করছে যে, আল্লাহ তায়ালা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা [Legislative Powers] প্রদান করেছেন। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ, হালাম হারাম শুধু কুরআন মজীদে বর্ণিতগুলোই নয় বরং এর সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা কিছু হালাল অথবা হারাম ঘোষণা করেছেন, অথবা যেসব জিনিসের হুকুম দিয়েছেন বা নিষেধ করেছেন তাও আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্য তাও আল্লাহ্র বিধানের একটি অংশ। এ কথাই সূরা হাশরে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে:
“রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো, আর যে জিনিস থেকে বিরত রাখে [নিষেধ করে] তা থেকে বিরত থাকো, আল্লাহ্কে ভয় করো, নিশ্চয় আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা।” [হাশর: ৭]
উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের কোনোটিরই এই ব্যাখ্যা করা যায়না যে, তার মধ্যে কুরআনের আদেশ নিষেধ ও কুরআনের হালাল হারামের কথা বলা হয়েছে, এটা ব্যাখ্যা নয় বরং আল্লাহর কালামের পরিবর্তনই হবে। আল্লাহ তায়ালা তো এখানে আদেশ নিষেধ ও হালাল হারামকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কার্যক্রম সাব্যস্ত করেছেন, কুরআনের কার্যক্রম নয়। এরপরও কি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ্ বেচারাকে বলতে চায় যে, আপনার বক্তব্যে ভুল হয়ে গেছে। আপনি ভুল করে কুরআনের পরিবর্তে রসূলের নাম উল্লেখ করেছেন [নাউযুবিল্লাহ]!
ঙ. বিচারক হিসেবে রসূলুল্লাহ (স)
কুরআন মজীদের এক স্থানে নয় বরং অসংখ্য স্থানে আল্লাহ্ তায়ালা এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিচারক নিয়োগ করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো:
“[হে নবী!] আমরা এই কিতাব পূর্ণ সত্যসহকারে তোমার উপর নাযিল করেছি, যেনো আল্লাহ্ তোমাকে সত্যপথ দেখিয়েছেন, তদনুসারে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারো।” [নিসা: ১০৫]
“আর [হে নবী বলো! আল্লাহ্ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো তোমাদের মাঝে সুবিচার করি।” [শূরা: ১৫]
“ঈমানদার লোকদের কাজ তো এই যে, তাদেরকে যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ডাকা হবে, যেনো রসূল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম।” [নূর: ৫১]
“তাদের যখন বলাহয়, আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন সেদিকে এবং তাঁর রসূলের দিকে আসো, তখন এই মুনাফিকদের তুমি দেখতে পাবে যে, তারা তোমার নিকট আসতে ইতস্তত করছে এবং পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে।” [নিসা: ৬১]
“অতএব [হে নবী] তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ তারা নিজেদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারপতিরূপে মেনে না নিবে।” [নিসা : ৬৫]
উপরোক্ত আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হচ্ছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ংসিদ্ধভাবে অথবা মুসলমানদের নিযুক্ত বিচারক ছিলেননা, বরং আল্লাহ তায়ালার নিয়োগকৃত বিচারক ছিলেন। তৃতীয় আয়াতটি বলে দিচ্ছে, তাঁর বিচারক হওয়ার মর্যাদা বা পদ রিসালাতের পদ থেকে স্বতন্ত্র ছিলোনা বরং রসূল হিসেবে তিনি বিচারকও ছিলেন এবং একজন মুমিনের রিসালাতের প্রতি ঈমান তখন পর্যন্ত সঠিক ও যথার্থ হতে পারেনা যতক্ষণ না সে তাঁর এই মর্যাদার সামনেও শ্রবণ ও আণুগত্যের ভাবধারা গ্রহণ করবে। চতুর্থ আয়অতে “[আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন]” অর্থাৎ কুরআন এবং রসূল উভয়ের ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে, যা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, মীমাংসা লাভের জন্য দুটি স্বতন্ত্র প্রত্যাবর্তন স্থল রয়েছে। [এক] কুরআন, আইন বিধান হিসেবে এবং [দুই] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিচারক হিসেবে। আর এই দুই জিনিস থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে ব্যক্তি বিচারক হিসেবে না মানে সে মুনিই নয়, এমনকি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ফায়সালা সম্পর্কে যদি কোনো ব্যক্তি নিজেদের অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব করে তবে তার ঈমান বরবাদ হয়ে যায়। কুরাআন মজীদের এই সুস্পষ্ট ব্যক্তব্যের পরও কি আপনি বলতে পারেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসূল হিসেবে বিচারক ছিলেননা বরং দুনিয়ার সাধারণ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় তিনিও একজন বিচারক ছিলেন মাত্র? তাই তাদের ফায়সালাসমূহের ন্যায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালা ও আইনের উৎস হতে পারেনা? দুনিয়ার কোনো বিচারকের কি এরূপ মর্যাদা হতে পারে যে, তার ফায়সালা যদি কেউ না মানে, অথবা তার সমালোচনা করে অথবা অন্তরে তাকে ভ্রান্ত মনে করে তবে তার ঈামন নষ্ট হয়ে যায়?
চ. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)
কুরআন মজীদ একইভাবে বিস্তারিত আকারে এবং পুনরুক্তি সহকারে অসংখ্য স্থানে একথা বলেছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত রাষ্ট্রপ্রধান ও রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন এবং তাঁকে রসূল হিসেবেই এই পদ প্রদান করা হয়:
“আমরা যে রসলূই পাঠিয়েছি তাকে এজন্য পাঠিয়েছি যে, আল্লাহর অনুমোদন [Sanction] অনুযায়ী তার আনুগত্য করা হবে।” [নিসা: ৬৪]
“যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো, সে মূলত আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।” [নিসা: ৮০]
“[হে নবী] যেসব লোক তোমার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করে তারা মূলত আল্লাহর নিকটই বাইয়াত গ্রহণ করে।” [আল ফাতাহ” ১০]
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলেরও আনুগত্য করো, নিজেদের আমল বিনষ্ট করোনা।” [মুহাম্মাদ: ৩৩]
“কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন স্ত্রীলোকের এই অধিকার নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যখন কোনো বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন তখন সেনিজের সেই ব্যাপারে নিজে কোনো ফায়সালা করার এখতিয়ার রাখবে, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করবে, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে লিপ্ত হলো।” [আহযাব: ৩৬]
“হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্র, আনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন তাদেরও। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যাপারে মতভেদ সৃষ্টি হয় তবে তা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো।” [নিসা: ৫৯]
এসব আয়াত পরিষ্কার বলছে যে, রসূল এমন কোনো রাষ্ট্রনায়ক নন যিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের স্বয়ং কর্ণধার হয়ে গেছেন, অথবা লোকেরা তাঁকে নির্বাচন করে রাষ্ট্রপ্রধান বানিয়েছে। বরং তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োগকৃত রাষ্ট্রপ্রধান। তাঁর রাষ্ট্রনায়কসূলভ কাজ তাঁর রিসালাতের পদমর্যাদা থেকে ভিন্নতর কোনো জিনিস নয়। বরং তাঁর রসূল হওয়াটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর অনুগত রাষ্ট্রনায়ক হওয়ার নামন্তর। তাঁর আনুগত্য করা হলে তা মূলত আল্লাহরই আনুগত্য করা হলো। তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়াটা মূলত আল্লাহর নিকট বাইয়াত হওয়ার শামিল। তাঁর আনুগত্য না করার অর্থ আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং পরিণতি হলো ব্যক্তির কোনো কার্যক্রমই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়া। পক্ষান্তরে ঈমানদার সম্প্রদায়ের [যার মধ্যে বাহ্যত সমগ্র উম্মাহ্, তাদের শাসকগোষ্ঠী ও তাদের “জাতির কেন্দ্রবিন্দু” সব অন্তর্ভুক্ত] সর্বোতভাবেই এ অধিকার নেই যে, কোনো বিষয়ে আল্লাহ্র রসূলের সিদ্ধান্ত দেয়ার পর তারা ভিন্ন কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
এসব সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা থেকে আরও অগ্রসর হয়ে সর্বশেষ আয়াত চূড়ান্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছে যার মধ্যে পরপর তিনটি আনুগত্যের হুকুম দেয়া হয়েছে:
১. সর্বপ্রথম আল্লাহর আনুগত্য।
২. অতপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য।
৩. অতপর তৃতীয পর্যায়ে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণের আনুগত্য।
এর পূর্বেকার কথা থেকে জানা গেলো যে, রসূল উলিল আমর [সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন কর্তপক্ষ] এর অন্তর্ভুক্ত নন বরং তার থেকে পৃথক ও ঊর্ধ্বে এবং তাঁর স্থান আল্লাহর পরে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এ আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে কথা জানা যায় তাহলো, উলিল আমরের সাথে বিতর্ক ও মতপার্থক্য হতে পারে, কিন্তু রসূলের সাথে বিতর্ক বা মতপার্থক্র হতে পারেনা। তৃতীয়ত, জানা গেলো যে, বিতর্ক ও মতবিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য দুটি প্রত্যাবর্তনস্থল রয়েছে: [এক] আল্লাহ্ [দুই] অতপর আল্লাহর রসূল। প্রকাশ থাকে যে, যদি প্রত্যাবর্তনস্থল শুধুমাত্র আল্লাহ হতেন, তবে সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখ সম্পূর্ণ অর্থহীন হতো। তাছাড়া আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থ যখন আল্লাহর কিতাবের প্রতি প্রত্যাবর্তন ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন রসূলে দিকে প্রত্যাবর্তনের অর্থও আর কিছুই হতে পারেনা যে, রিসালাতের যুগে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যাবর্তন এবং এই যুগের পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। [বরং যদি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে জানা যায় যে স্বয়ং রিসালাতের যুগেও ব্যাপক অর্থে রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতই ছিলো প্রত্যাবর্তন স্থল। কারণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ যুগে ইসলামী রাষ্ট্র গোটা আরব উপদ্বীপে বিস্তার লাভ করেছিলো। দশ বারো লাখ বর্গমাইলের এই দীর্ঘ ও প্রশস্ত দেশে প্রতিটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে গ্রহণ করা কোনোক্রমেই সম্ভব ছিলোনা। অধিকন্তু এই যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রের গভর্ণরগণ, বিচারকগণ এবং প্রশাসকগণকে বিভিন্ন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কুরআন মজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় যে উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হতো, তা ছিলো রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত।]
সুন্নাহ আইনের উৎস হওয়ার বিষয়ে উম্মতের ইজমা
এখন আপনি যদি বাস্তবিকই কুর্ন মজীদকে মানেন এবং এই পবিত্র গ্রন্থের নাম নিয়ে আপনার নিজের মনগড়া মতবাদের অনুসারী না হয়ে থাকেন তবে দেখে নিন যে, কুরআন মজীদ পরিষ্কার, সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ দ্ব্যার্থহীন বাক্যে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে নিযুক্ত শিক্ষক, অভিভাবক, নেতা, পথ প্রদর্শক, আল্লাহ্র কালামের ভাষ্যকার, আইন প্রণেতা [Law Giver] বিচারক, প্রশাসক ও রাষ্ট্রনায়ক সাব্যস্ত করছে এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসমস্ত পদ এই পাক কিতাবের আলোকে রিসালাতের পদের অবিচ্ছেদ্য অংগ। কালামে পাকের এই ভাষণের ভিত্তিতে সাহাবায়ে কিরামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলমান একমত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে স্বীকার করেন যে, উপরোক্ত সমস্ত পদের অধিকারী হিসেবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কাজ করেছেন তা কুরআন মজীদের পরে আইনের দ্বিতীয় উৎস। [Source of Law]
সুন্নাহ্কে সরাসরি আইনের একটি উৎস হিসেবে মেনে নেয়ার পর এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তা জানার উপায় কি? আমি এর জবাবে বলতে চাই, আজ চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর এই প্রথমবারের মতো আমরা এ প্রশ্নের সম্মুখীন হই যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে যে নবূয়্যতের আবির্ভাব হয়েছিলো তা কি সুন্নাত রেখে গেছে? দুটি ঐতিহাসিক সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায়না।
১. কুরআন মজীদের শিক্ষা এবং মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের উপর যে সমাজ ইসলামের প্রথম দিন থেকে কায়েম হয়েছিলো, তা সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহতভাবে জীবন্ত রয়েছে, তার জীবনে একটি দিনেরও বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি এবং তার সমস্ত বিভাগ ও সংস্থা এই পুরো সময়ে উপর্যুপরি কাজ করে আসছে। আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি, চরিত্র, নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইবাদত ও পারস্পরিক সামাজিক লেনদেন, জীবনপদ্ধতি ও জীবনপন্থার দিক থেকে যে গভীর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, যার মধ্যে মতভেদের উপাদানের চাইতে ঐক্যের উপাদান বেশী পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে, যা তাদেরকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একটি উম্মতের অন্তর্ভুক্ত রাখার সবচেয়ে বড় বুনিয়াদী কারণ- এগুলোই একথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, এই সমাজকে সুন্নতের উপরই কায়েম করা হয়েছিলো এবং সেই সুন্নাত শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীর্ঘতায় অব্যাহতভাবে জারী রয়েছে। এটা কোনো হারানো বা বিলুপ্ত জিনিস নয় যা অনুসন্ধান করার জন্য আমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াতে হবে।
যেমন আমি বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করে এসেছি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নবূয়্যতকালে মুসলমাদের জন্য শুধু একজন পীর, মুরশীদ ও বক্তাই ছিলেন বরং কার্যত তাদের দলের নেতা, পথপ্রদর্শক, শাসক, বিচারক, আইনপ্রণেতা, অভিভাবক, মুরুব্বী, শিক্ষক সবকিছুই ছিলেন এবং আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁরই দেখানো, শিখানো ও নির্ধারিত পন্থায় মুসলিম সমাজ কাঠামো পরিপূর্ণরূপে গঠিত হয়েছিলো। তাই এরূপ কখনো ঘটতে পারেনি যে, তিনি নামায, রোযা, হজ্জের নিয়মাবলীর যে শিক্ষাদান করেছেন কেবল সেগুলো মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে এবং তাঁর অবশিষ্ট শিক্ষা ওয়াজ নসীহত হিসেবে শ্রবণ করে মুসলমানরা ঐ পর্যন্তই ক্ষ্যান্ত হয়ে গেছে। কখনোও নয় বরং বাস্তবিকপক্ষে যা কিছু হয়েছে তা এই যে, তাঁর শিখানো নামায যেভাবে মসজিদে চালু হয়েছে এবং ঐ সময় নামাযের জামায়াত কায়েম হতে থাকে অনুরূপভাবে বিবাহ শাদী, তালাক ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে যেসব বিধান তিনি নির্ধারণ করেন তা মুসলমানদের পরিবারে বলবৎ হতে থাকে। পারস্পরিক লেনদেনের যে নীতিমালা তিনি নির্ধারণ করেন তা বাজারে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চালু হয়ে যায়। মামলা মোকাদ্দমার যেসব রায় তিনি প্রদান করেন তাই দেশের আইনে পরিণত হ। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শত্রুপক্ষের সাথে এবং বিজয়ের পর বিজিত এলাকার অধিবাসীদের যে ব্যবহার করেন তাই মুসলিম রাষ্ট্রের সংবিধানে পরিণত হয়। স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব নীতিমালার প্রচলন করেন অথবা পূর্ব থেকে প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে যেগুলো তিনি বহাল রেখে ইসলামী নীতিমালার অংশে পরিণত করেন সামগ্রিকভাবে ইসলামী সমাজ ও জীবন ব্যবস্থা তার সমস্ত দিক ও বিভাগসহ সেই নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
এই ছিলো জ্ঞাত ও সুপরিচিত সুন্নাহ্, যার ভিত্তিতে মসজিদ থেকে নিয়ে পরিবার, বংশ, হাট বাজার, ব্যবসা বাণিজ্য, বিচার ব্যবস্থা, সরকারী প্রশাসন এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতি পর্যন্ত মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনের যাবতীয় সংস্থা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই কার্য পরিচালনা করতে থাকে। পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশিদার যুগ থেকে নিয়ে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমাদের সামগ্রিক সংস্থার কাঠামো তার উপর ভিত্তিশীল রয়েছে। গত শতাব্দী পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতায় এক দিনের জন্যও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেয়নি। এরপর যদি কোনো বিচ্ছিন্তা এসে থাকে তাহলে সেটা কেবল সরকার ও বিচার ব্যবস্থা এবং গণ আইনের সংস্থাসমূহের কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার কারণেই হয়েছে।….. এসবের [সুন্নাতের] ব্যাপারে একদিকে হাদীসের নির্ভরযোগ্য রিওয়াতের এবং অপরদিকে উম্মাতের অব্যাহত ও ধারাবাহিক আমল উভয়টি পরস্পরের সাথে সংগিপূর্ণ রয়েছে।
২. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে প্রতিটি যুগের মুসলমানগণ প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সুন্নাহ অর্থাৎ সহীহ হাদীসসমূহ অবগত হওয়ার অবিরাম চেষ্টায় রত থাকেন। একদিকে ছিলো সুপ্রসিদ্ধ হাদীসমূহ যে সম্পর্কে আমি উপরে আলোচনা করেছি এবং অপরদিকে ঐসব হাদীস ব্যতীত অপর এক প্রকারের হাদীস ছিলো যা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত বক্তব্য, আদেশ নিষেধ, অনুমোদন [তাকরীর[ [পরিভাষায় অনুমোদন (তাকরীর)-এর অর্থ এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উপস্থিতিতে কোনো কাজ হতে দেখেছেন, অথবা কোনো প্রথার প্রচলন হয়েছে এবং তিনি তা নিষেধ করেননি। ভিন্ন শব্দে তাকরীর বলতে বুঝায় কোনো জিনিসকে বা কোনো বিষয়কে বহাল রাখা।] ও অনুমতি অথবা কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করে বা শ্রবণকরে ব্যক্তি বিশেষের গোচরে বা জ্ঞানে এসেছে এবং সর্বসাধারণ এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারেনি….. এসব সুন্নাতের জ্ঞান যা বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো, মুসলিম উম্মাহ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পরপরই তা সংগ্রহের কাজ ধারাবাহিকভাবে শুরু করে দেন। কেননা ফকীহগণ, প্রশাসকগণ, বিচারকগণ, মুফতীগণ ও জনসাধারণ সবাই নিজ নিজ কর্মসীমার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যা সম্পর্কে নিজস্ব রায় বা ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত বা কর্মপন্থা গ্রহণ করার পূর্বে ঐ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো পথনির্দেশ বর্তমান আছে কিনা তা অবগত হওয়া জরুরী মনে করতেন। এই প্রয়জনের পরিপ্রেক্ষিতে এমন প্রতিটি লোকের অনুসন্ধান শুরু হয়ে গেলো যার কাছে সুন্নাতের কোনো জ্ঞান বর্তমান আছে এবং এমন প্রত্যেক ব্যক্তি যার কাছে এধরনের জ্ঞান বর্তমান ছিলো তা অন্যদের পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া নিজের জন্য ফরয মনে করতো। হাদীসের রিওয়াতেরে এটাই সুচনাবিন্দু এবং ১১ হিজরী থেকে তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত এই বিক্ষিপ্ত সুন্নতগুলো একত্র করার কাজ অব্যাহত থাকে। জাল হাদীস [মুওদুয়াত] রচনাকারীরা এর মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানোর যতোই চেষ্টা করেছে তা প্রায় সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কেননা যে সুন্নতের সাহায্যে কোনো অধিকার [হক] প্রতিষ্ঠা অথবা প্রত্যাখ্যাত হতো, যার ভিত্তিতে কোনো জিনিস হালাল অথবা হারাম সাব্যস্ত হতো, যার দ্বারা কোনো ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য প্রমাণিত হতো অথবা কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি খালাস পেতে পারতো, মোটকথা যেসব সুন্নাত আইন কানুনের উৎস ছিলো সে সম্পর্কে কোনো রাষ্ট্র সরকার বিচার বিভাগ এবং ফতুয়া বিভাগ এতোটা বেপরোয়া হতে পারতোনা যে, কোনো ব্যক্তি এমনি উঠে দাঁড়িয়েই বলে দেবে যে, “নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন” এবং কোনো প্রশাসক, অথবা বিচারক অথবা মুফতী তা মেনে নিয়ে এর ভিত্তিতে কোনো নির্দেশ জারী করবে। এজন্য আইন ক ানুনের সাথে যেসব সুন্নতের সম্পর্ক ছিলো সে সম্পর্কে পূর্ণ অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সমালোচনার ধারালো ছুরি দিয়ে তাতে অস্ত্রপচার করা হয়েছে, রিওয়াতের মূলনীতির ভিত্তিতে তা পরখ করা হয়েছে এবং দিরায়াতের [বুদ্ধি বিবেক] মূলনীতির ভিত্তিতেও। এবং যেসব তথ্যসূত্রের ভিত্তিতে কোনো রিওয়ায়াতকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সেসবও জমা করে রেখে দেয়া হয়েছে যাতে পরবর্তীকালে যেকোনো ব্যক্তি তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান সম্পর্কে নিজের অনুসন্ধানী রায় কায়েম করতে পারে। তাদের জন্য যেহেতু সুন্নাহ আইন হওয়ার মর্যাদায় সমাসীন ছিলো, তার ভিত্তিতে তাদের আদালতগুলোকে বিচার মীমাংসা করতে হতো এবং তাদের ঘর থেকে নিয়ে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিষয়াবলী তার ভিত্তিতে পরিচালিত হতো তাই এগুলোর আলোচনা পর্যালোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধারে ক্ষেত্রে বেপরোয়া হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। এই তত্ত্বানুসন্ধানের উপায় উপকরণও এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রথম খিলাফতের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রজন্ম পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি এবং প্রত্যেক যুগের লোকদের কাজ কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই সংরক্ষিত রয়েছে।
এই দুটি সত্যকে যদি কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করে নেয় এবং সুন্নাহ্ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার উপায় উপকরণ সম্পর্কে যথারীতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধ্যয়ন করে তবে সে কখনও এই সন্দেহের শিকার হতে পারেনা যে, এটা কোনো অসমাধানযোগ্য গোলক ধাঁধাঁ যার মধ্যে সে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছে।
৩. খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম এবং উম্মাহ্র মুজাতিহদ আলেমগণের সিদ্ধান্ত
ইসলামী সংবিধানের তৃতীয উৎস হচ্ছে খিলাফতে রাশিদার কার্যক্রম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর খোলাফায়ে রাশেদীন যেভাবে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন, তার নজীর ও ঐতিহ্যের বিস্তারিত বিবরণে হাদীস, ইতিহাস ও জীবন চরিতের বিরাট গ্রন্থসমূহ পরিপূর্ণ এবং এসব জিনিসই আমাদের জন্য নমুনা হিসেবে অনুসরণযোগ্য। ধর্মীয় বিধান ও নির্দেশনার যে ব্যাখ্যা সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে করেছেন (ইসলামের পরিভাষায় যাকে বলে ইজ্মা) এবং সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়সমুহে খোলাফায়ে রাশেদীন সাহাবাদের সাথে পরামর্শক্রমে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা আমাদের জন্য অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গণ্য এবং তাকে যাথাযথভাবেই মেনে নিতে হবে। কারণ কোনো ব্যাপারে সাহাবাদের মতৈক্য হওয়ার অর্থ এই যে, তা ইসলামী আইনের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মপদ্ধতি। যে বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছে সে বিষয়ে যে একাধিক ব্যাখ্যার অবকাশ রয়েছে তা পরিষ্কার বুঝা যায়। এসব বিষয়ে যুক্ত প্রমাণের সাহায্যে একটি মতকে অপর মতের উপর অগ্রাধিকার দেয়া যায়। কিন্তু যেখানে তাঁদের পরিপূর্ণ মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে তাঁদের সিদ্ধান্ত অনিবার্যরূপ একই ব্যাখ্যা এবং একইরূপ কর্মনীতিকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য প্রমাণ করে। কারণ তাঁরা সরাসরি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাত্র এবং তাঁর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলেন। কাজেই তাঁদের সকলের সমবেতভাবে দীনের ব্যাপারে ভুল করা কিংবা দীন ইসলামকে বুঝার ও হৃদয়ংগম করার ব্যাপারে সঠিকপথ হতে বিচ্যুত হওয়া কোনো মতেই সমর্থনযোগ্য নয়।
চতুর্থ উৎস হচ্ছে মুসলিম উম্মাহ্র মুজতাহিদগণের সেসব ফায়সালা যা তারা (কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে) নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি দূরদৃষ্টির আলোকে বিভিন্ন সাংবিধঅডিনক সমস্যার সমাধানে পেশ করেছেন। মুজতাহিদদের সেসব সিদ্ধান্ত ইসলামী শরীয়তের অকাট্য প্রমাণ না হলেও ইসলামী সংবিধানের প্রাণসত্তা এবং এর নীতিমালাসমূহ অনুধাবন করার জন্য আমাদেরকে নির্ভুল ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশ দান করে।
এই চারটি হচ্ছে আমাদের ইসলামী সংবীদানের উৎস। ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়ন করতে হলে উল্লিখিত চারটি উৎস থেকেই এর যাবতীয় নীতিমালা একত্র করে তা প্রণয়ন করতে হবে। ঠিক যেমন ইংরেজদেরকে তাদের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে তাদের প্রণীত আইন [State law, Common law] এবং তাদের সাংবিধানিক প্রথা ও ঐতিহ্য [Conventions of the Constitution] হতে এক একটি খুঁটিনাটি পর্যন্ত গ্রহণ করে কাগজে লিখতে হয় এবং অনেক শাসনতান্ত্রিক বিধান ও নীতিমালা তাদেরকে তাদের আদালতসমূহের ‘রায়’ হতে বেছে বেছে গ্রহণ করতে হয়।১.{ইসলামী আইন প্রসংগে অন্যান্য আলোচনার জন্য দৃষ্টব্য এই লেখকের “ইসলামী আইন” শীর্ষক গ্রন্থ [সংকলক]
৪. সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা
ইসলামী সংবিধানের উল্লিখিত চারটি উৎসই লিখিতভাবে আমাদের কাছে বর্তমান আছে। কুরআন মজীদ তো লিখিতভাবে মুসলমানদের ঘরে ঘরে রয়েছে। “সুন্নতে রসূল” এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য প্রন্হাকারে পাওয়া যায়। অতীতকালের মুজতাহিদদের সিদ্ধান্ত ও মতামতসমূহও নির্ভরযোগ্য প্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। এগুলোর মধ্যে একটি জিনিসও দুর্বল নয় এবং দৃষ্প্রাপ্যও নয়। কিন্তু তা সত্ত্বও এসব উৎস হতে এই অলিখিত সংবিধানের নীতিমালা উদ্ধার করে তাকে লিখিত রূপদান কারার ব্যাপারে কয়েকৈটি সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আমি চাই যে, সম্মুখে অগ্রসব হবার পূর্বে এই কথাগুলো আপনার গভীরভাবে হৃদয়ংগম করে নিন।
ক. পারিভাষার অসুবিধা
এই প্রসংগে সর্বপ্রথম হচ্ছে ভাষার অসুবিধা। কুরআন, হাদীস এবঙ ফিক্হ গ্রন্থাবলীতে সাংবিধানিক আইনের বর্ণনা দেয়ার জন্য যেসব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, বর্তমানে তা জনগণের নিকট প্রায় দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। কারণ দীর্ঘকাল ধরে আমাদের এখানে ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং এসব পরিভাষার ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। কুরআন মজীদে এমন অসংখ্য শদ্ব রয়েছে যা আমরা দৈনন্দিন তিলাওয়াত করি, কিন্তু একথা জানিনা যে, এগুলো সাংবিধানিক পরিভাষা। যথা, সুলতান, মালিক, হুকুম, আমর, বিলায়েত ইত্যাদি। এমনকি এই শব্দগুলোর সাংবিধানিক অর্থ ও ভাব আরবীতেও খুব কম লোকই বুঝতে পারে। অন্য কোনো ভাষায় তার অনুবাদ করলে তো তার সম্পূ্র্ণ অর্থই বিকৃত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ঠিক এজন্যই অনেক বড় বড় লেখাপড়া জানা পন্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের সাংবিধানিক আইনের আলোচনা শুনে বিম্মিত হন এবং “কুরআনের কোন্ আয়াত হতে সংবিধান সম্পর্কে তথ্য জানা যায়” বলে বিম্ময়সূচক প্রশ্ন করে বসেন। বস্তুতপক্ষে এ লোকদের বিস্ময় এবং প্রশ্নের মূলীভূত কারণ এই যে, যেহেতু ‘সংবিধান’ [the Constitution] নামে কোনো সূরা কুরআন মজীদে বিদ্যমান নাই এবং বিংশ শতকের পরিভাষা অনুসারে কোনো আয়াতও নাযিল হয়নি।
খ. প্রাচীন ফিক্হ প্রন্থসমূহের হতাশাজনক সংকলন
আরেকটি অসুবিধা হলো আমাদের প্রাচীন ফিক্হশাস্ত্রের প্রন্থাবলীতে সংবিধান সম্পর্কীয় বিষয়সমূহকে আলাদাভাবে কোথোও পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ক্রমে সংকলিত করা হয়নি, বরং সংবিধান ও আইন তাতে পরস্পরের সাথে মিশ্রিতভাবে লিখিত হয়েছে। আপনারা জানেন, সংবিধান ও আইন সম্পর্কে আলাদা আলাদা ধারণা বহু পরবর্তী যুগের উদ্ভুত ব্যাপার বরং সংবিধান শব্দটিকে তার নতুর অর্থে ব্যবহারও সম্প্রতি শুরু হয়েছে।
অবশ্য একথা সত্য যে, যেসব ব্যাপারকে আমরা এখন সংবিধান সংক্রান্ত ব্যাপার বলে মনে করি, সে সকল বিষয়ে প্রাচীন ফিক্হবিদগণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, তাদের এসব আলোচনা বড় বড় ফিক্হের কিতাবের বিভিন্ন অধ্যায়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। একটি বিষয়ে ‘কাযা’ [বিচার] অধ্যায় আলোচনা হলে অন্যটি সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে ‘ইমারত’ [সরকার] অধ্যায়। একটি বিষয় ‘সিয়ার’ [যুদ্ধ ও সন্ধি সংক্রান্ত] অধ্যায় লিখিত হলে অন্যটি আলোচিত হয়েছে “হুদূদ” [ফৌজদারী আইন] অধ্যায়ে। আবার অন্য বিষয়ের আলোচনা হয়েছে ফাই [পাবলিক ফিনান্স] অধ্যায়ে। এতদ্ব্যতীত এগুলোর ভাষা ও পরিভাষা অধুনা প্রচলিত ভাষা ও পরিভাষা থেকে সম্পর্ণ ভিন্নতর। আইনের বিভিন্ন বিভাগ এবং এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্ব যার নেই এবং আরবী ভাষার উপরও যার ব্যুৎপত্তি যথেষ্ট নয়, সে তা থেকে কোনো তথ্যই খুঁজে বের করতে পারবেনা। কোনোখানে দেশীয় আইনের আলোচনা ব্যাপদেশে আন্তর্জাতিক আইনের কোনো বিষয়ের প্রসংগ এসে গেলে কোথায় ব্যক্তিগত [Private] আইনের আলোচনা প্রসংগে হলে তা উপলব্ধি করা তার পক্ষে খুবই কঠিন। বিগত শতাব্দীসমূহে আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞগণ অতিমূল্যবান সম্পদ রেখে গিয়েছেন, কিন্তু আজ তাদের পরিত্যাক্ত এসব মূল্যবান সম্পদ যাচাই বাছাই করে প্রত্যেক বিভাগের আইন সম্পর্কীয় তথ্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করা এবং স্বছ্চ ও সুপরিস্ফুট করে জনসমক্ষে পেশ করা অত্যান্ত শ্রমসাধ্য ব্যাপার। এরূপ সাধনালব্ধ সম্পদ আহরণ করার জন্য আমাদের যুবসমাজ মোটেই আগ্রহান্বিত ও অগ্রসর হচ্ছেনা। যুগ যুগ ধরে তারা অপরের উচ্ছিষ্টংশ পেয়ে যথেষ্ট তুষ্ট। শুধু তাই নয়, তাদের পূর্বপুরুষেদের রক্ষিত এই মূল্যবান সম্পদকে তারা অজ্ঞাতসারে এপেক্ষা করছে, এর প্রতি ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে।
গ. শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি
তৃতীয় সমস্যা হলো, আমাদের এখানে শিক্ষা ব্যবস্থা সুদীর্ঘ কাল ধরে দোষ ত্রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে। আমাদের এখানে যার ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেন তারা বর্তমান কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনৈতিক বিষয়াবলী এবং সাংবিধানিক আইন ও তার সাথে সংশিষ্ট বিষয়সমূহ সম্পর্কে অজ্ঞাত। তাই তারা কুরআন, হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং বুঝাতে ও বুঝাতে যদিও জীবন অতিবাহিত করে দেন, কিন্তু বর্তমান যুগের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়সমূহ আধুনিক কালের ভাষা ও পরিভাষায় অনুধাবন করা এবং সে সম্পর্কে ইসলামের নীতি ও বিধান সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কারা তাদের পক্ষে বড়ই মুশকিল ব্যাপার। তারা যে ভাষা ও পরিভাষা বুঝেন সে ভাষা ও সক্ষম হতে পারেন। তারপরই তারা বলতে পারেন যে, এসব সম্পর্কে ইসলামের নীতি এবং বিধান কি এবং তা কোথায় আলোচিত হয়েছে।
অন্যদিকে আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকেরা কার্যত আমাদের রাজনীতি ও তমদ্দুন এবং আইন ও আদালতের সমগ্র বিভাগের উপর ঝোঁক বসে আছেন। এরা জীবনের আধুনিক সমস্যা সম্পর্কে তো ওয়াকিফহল, কিন্তু দীন ইসলাম সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে তাদের কি পথ নির্দেশ দিয়েছে সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সংবিধান, রাজনীতি ও আইন সম্পর্কে তারা যা কিছু জানে তা সবই পাশ্চাত্যের শিক্ষা ও পাশ্চাত্যের বাস্তব নমুনার সাহায্যেই জ্ঞাত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। কাজেই তাদের মধ্যে যারা বাস্তবিকই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার পুনঃ প্রতিষ্ঠা চান, তাদেরকেও এসব বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ ও বিধি বিধান যে ভাষা ও পরিভাষা তারা বুঝতে পারে সে ভাষা ও পরিভাষায় বুঝিয়ে দিলেই তখন তারা তা হৃদয়ংগম করতে পারেন। কাজেই ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের পথে বর্তমানে এটা অত্যন্ত জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে রেখেছে।
ঘ. অজ্ঞদের ইজতিহাদ করার দাবী
চতুর্থ আর একটি সমস্যা রয়েছে যা বাড়তে বাড়তে বর্তমানে একটি কৌতুকে পরিণত হয়েছ। বর্তমানে একটি অদ্ভুত চিন্তারধারার উন্মেষ ঘটেছে যে, ইসলামে পৌরহিত্যবাদের কোনো অবকাশ নেই, কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াতের উপর মোল্লার একচ্ছত্র আধিপত্য নেই যে, তারাই এর ব্যাখ্যা করবে। ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও ইজতিহাদ করতে মোল্লাদের যেরূপ অধিকার আছে, আমাদেরও তদ্রূপ অধিকার আছে। দীন ইসলাম সম্পর্কে মোল্লাদের কোনো কথা আমাদের কথার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারও কোনোই কারণ নেই।
বস্তুত এসব কথা এমন লোকেরা বলে বেড়ায় যারা না কুরআন ও সুন্নাতের ভাষা জানে, না ইসলামী ঐতিহ্য সম্পর্কে তাদের কিছুমাত্র ধারণা আছে, আর না তারা জীবনের কয়েকটি দিনও ইসলামের তথ্যনুসন্ধানে ব্যয় করেছে। তাদের জ্ঞানের এই ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা অনুভব করা এবং তা দূর করার পরিবর্তে তারা কুরআন হাদীস তথা ইসলাম সম্পর্কে ইজতিহাদ করার ব্যাপারে জ্ঞান থাকার আবশ্যকতাকেই সম্পূর্ণ অস্বীকার করছে। তারা জেদ ধরেছে যে, ইসলামী জ্ঞানের অধিকারী হওয়া ব্যতিরেকেই তাদের মনগড়া ব্যাখ্যার দ্বারা ইসলামের অবয়বকে বিকৃত করার অধিকার তাদের দিতে হবে।
কিন্তু [ইসলাম সম্পর্কে] অজ্ঞতা ও মুর্খতার এই প্লাবনকে বাধা না দিয়ে যদি অগ্রসর হতে দেয়া হয় তবে এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য। কালই হয়তো কেউ বলে উঠবে ইসলামে “উকিলবাদের” স্থান নেই। অতএব আইন সম্পর্কে প্রত্যেকেরই কথা বলার অধিকার আছে। আইন সম্পর্কে সে যদি একটি অক্ষরও না পড়ে থাকে তবুও তাকে সে অধিকার দিতে হবে। তারপর আর একদিন হয়তো কেউ বলবেঃ ইসলামে “প্রকৌশলবাদ” নেই, কাজেই ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে সকলেই কথা বলতে পারবে যদিও এই শাস্ত্রের কিছুই তার জানা নেই। এরপর আবার আর একজন দাঁড়িয়ে বলতে পারে যে, ইসলামে চিকিৎসা বিদ্যাও কেবল ডাক্তারদের একচিটিয়া উপজীবিকা নয়, রোগীদের চিকিৎসা করার অধিকার তাদেরও আছে যদিও চিকৎসা বিজ্ঞানের বাতাসও তাদের স্পর্শ করেনি। আমি অত্যন্ত স্তম্ভিত যে, আধুনিক উচ্চশিক্ষিত ও মহাসম্মানিত ব্যক্তিগণ কিভবে উক্তরূপ হাস্যকর ও বালকোচিত কথা বলতে এগিয়ে এসেছেন। এবং কেন তারা নিজেদের গোটা জাতিকে এরূপ “অপদর্থ মনে করে নিয়েছেন যে, তাদের এসব অন্তঃসারশূণ্য হাস্যকর কথা শুনে তারা তা শিরধার্য করে নিবে। নিঃসন্দেহে ইসলামে পৌরহিত্যবাদ নেই। কিন্তু এই পৌরহিত্যবাদ না থাকার অর্থ কি, তা কি তারা জানে? এর অর্থ কেবল এই যে, ইসলামে বনী ইসরাঈলের ন্যায় দীন ইসলামের জ্ঞান এবং দীন ইসলামের খিদমতের কাজ কোনো বংশ বা গোত্রের একচেটিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। ইসলামে খৃষ্টধর্মের ন্যায় দীন ও দুনিয়াকে পরম্পর বিচ্ছিন্নও করা হয়নি যে, “দুনিয়া কায়জারের নিকট সোপর্দ করা হয়েছে এবং দীন পাদ্রীদের নিকট ইজারা দেয়া হয়েছে। ইসলামে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং শরীয়তের উপর কারো ব্যক্তিগত ইজারাদারী নেই এবং “মোল্লা” কোনো বংশ বা গোত্রের নাম নয় যে, দীন ইসলামের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার তার পৈত্রিক অধিকার। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন আইন পড়ে ড উকিল ও জজ হতে পারে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ইঞ্জিনিয়ার ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিখে যেমন প্রত্যেক ব্যক্তিই ডাক্তার হতে পারে, তদ্রুপ প্রত্যেক ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান শিক্ষালাভ করার জন্য সময় ও পরিশ্রম ব্যয় করে শরীয়তের ব্যাপারসমূহ সম্পর্কে এথা বলার অধিকার অর্জন করতে পারে। ইসলামে ‘পৌরহিত্যবাদ’ নেই- এই কথাটির কোনো বুদ্ধিসম্মত অর্থ থেকে থাকলে তা এটাই, ইসলামে পৌরহিত্যবাদ না থাকার অর্থ এই নয় যে, ইসলামকে ছেলেখেলা ব্যাপারে পরিণত করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে, এখন যার ইচ্ছা উঠে দাড়িয়ে তার বিধান ও শিক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ সূলভ ফায়সালা প্রদান করতে শুরু করে দিবে, চাই সে কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা নাইবা করতে থাকুক। জ্ঞান ব্যতীত রায় দান করার অধিকারী হওয়ার দাবি দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই যদি গ্রহণযোগ্য না হয়ে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত ইসলামের ব্যাপারে উক্তরূপ দাবী প্রহণযোগ্য হবার সূলে কি যুক্তি থাকতে পারে?
ইসলামী সংবিধান প্রণয়ন ও ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণাকে অন্তর্হিত করার ক্ষেত্রে এই চতুর্থ বাধাটিও কমজটিলতার সৃষ্টি করেনি। আর সত্য কথা বলতে গেলে বর্তমানে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাধা। প্রথম উল্লেখিত তিনটি বাধা চেষ্টা সাধনার দ্বারা দূর করা যেতে পারে এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহে তা এক পর্যায় পর্যন্ত দূর করাও হয়েছে। কিন্তু এই নতুন জটিলতর চিকিৎসা বড়ই কঠিন বিশেষত এই জটিলতা বর্তমান শাসন কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে তা আরও অধিক দূরুহ হয়ে পড়েছে।
সপ্তম অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ
১. সার্বভৌমত্ব কার?
২. রাষ্ট্রের কর্মসীমা (অধিক্ষেত্র)
৩. রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা বা অধিক্ষেত্র এবং এগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক
৪. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য
৫. সরকার কিভাবে গঠিত হবে?
৬. শাসকের গুণাবলী ও যোগ্যতা
৭. নাগরিকত্ব ও তার ভিত্তিসমূহ
৮. নাগরিকদের অধিকার
৯. নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার
১৯৫২ সালে ২৪ নভেম্বর করাচী বার এসোসিয়েশনের সভাপতি মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী (র) কে ইসলামী সংবিধান বিষয়ে একটি আলোচনা সভায় অংশগ্রহণের জন্য দা্ওয়াত দিয়েছিলেন। এই আলোচনা সভার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলামী সংবিধান সম্পর্কে দেশের শিক্ষিত মহল, বিশেষত আইনজীবীদের মনে যে সংশয় ও জটিলতা রয়েছে তা দূর করার চেষ্টা করা। এই সময়টি দেশের ইতিহাসে বড়ই গুরুত্বপূর্ণ ছিলো এবং গোটা দেশে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের জোর দাবি চলছিলো। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে নাজিমুদ্দীন রিপোর্ট প্রকাশ এক মাসের জন্য মুলতবি করা হয়েছিলো। স্বাভাবিকভাবেই পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের মনে অনেক প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিলো যার মদুত্তর প্রদান প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিলো। মাওলানা মওদুদী উক্ত আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করে কয়েক ঘন্টার আলোচনা পর্যালোচনার মাধ্যমে এই প্রয়োজন পূরণ করেন। মাওলানা মওদূদীর একটি ভাষণের সাধ্যমে আলোচনা বভার উদ্বোধন হয় এবং এই ভাষণে তিনি ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী সংবিধানের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সুস্পষ্টভাবে তোলে ধরেন। বক্তৃতা শেষে কয়েক ঘন্টা ধরে প্রশ্নেত্তর চলতে থাকে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলোতে মাওলানার সেই ভাষণের বাংলা তরজমা পেশ করা হচ্ছে। -সংকলক
ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিসমূহ
আমি সর্ব প্রথম সংবিধান ও ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি বড় বড় ও মৌলিক বিষয়ের উল্লেখ করে সংক্ষেপে বলবো যে, সে সম্পর্কে ইসলামের আসল উৃৎসে কি মুলনীতিগত নির্দেশ পাওয়া যায়? ইসলাম সাংবিধানিক ব্যাপারে কোনো পথনির্দেশ দান করে কিনা, করলে তা নিছক সুপারিশের পর্যায়ভুক্ত নাকি মসিলমানদের পক্ষে অপরিহার্য ও অবশ্য পালনীয় পথ নির্দেশ, এই সবই আমার পরবর্তী আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে আমি বিস্তারিত আলোচনার দিকে না গিয়ে মোটামুটিভাবে সংবিধানের ৯টি মৌলিক ধারা সম্পর্কে আলোচনা করবো।
১.প্রথম প্রশ্ন হলো, সার্বভৌমত্ব কার? কোনো বাদশাহর? নাকি কোনো শ্নেণীর অথবা গোটা জাতির? নাকি আল্লাহ্ তায়ালার?
২. দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, রাষ্ট্রের কর্মসীমা [Jurisdiction] কি? রাষ্ট্র কতোদূর পর্যন্ত আনুগত্য পেতে পারে? এবং কোন্ সীমায় পৌঁছে তার আনুগত্য পাওয়ার অধিকার খতম হয়ে যায়?
৩. সংবিধান প্রসংগে তৃতীয় মৌলিক প্রশ্ন রাষ্ট্রর বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা সম্পর্কে। অর্থাৎ শাসনবিভাগ [Executive] বিচার বিভাগ [Judiciart] এবং আইনপরিষদ [Legislature] প্রভৃতির আলাদা আলাদা কর্মসীমা [Jurisdiction] কি হবে? এদের প্রত্যেকটি বিভাগ কি কর্তব্য এবং কি দায়িত্ব পালন করবে? কোন্ সীমার মধ্যে অবস্থান করবে এবং তারপর এদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের ধরন কি হবে?
৪. চতুর্থ গুরত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠিত উদ্দেশ্য কি? রাষ্ট্র কোন্ উদ্দেশ্যে কাজ করবে এবং এর শাসনপ্রণালীর মৌলিক নীতি কি হবে?
৫. পঞ্চম প্রশ্ন হলো, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য সরকার কিভাবে গঠন করা হবে?
৬. ষষ্ঠ প্রশ্ন হলো শাসকদের গুণাবলী ও যোগ্যতা [Qualifications] কি হবে? কোন্ ধরনের লোক প্রশাসন চালাবার যোগ্য বিবেচিত হবে?
৭. সপ্তম প্রশ্ন হলো, সংবিধানে নাগরিকত্বের ভিত্তি কি হবে? কিভাবে এক ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক পরিগণিত হবে এবং কিভাবে নয়?
৮. অষ্টম প্রশ্ন হলো, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কি?
৯. নবম প্রশ্ন, নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের কি কি অধিকার আছে?
যে কোনো দেশের সংবিধানে এই প্রশ্নগুলো সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। ইসলাম এই প্রশ্নগুলোর কি জবাব দেয় তাই আমরা লক্ষ্য করে দেখবো।
১. সার্বভৌমত্ব কার?
সর্বপ্রথম আমরা দেখবো ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধান সার্বভৌমত্বের [Sovereignty] স্থান কাকে দান করে?
এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট ও অকাট্য জবাব কুরআন মজীদ থেকেই আমরা জানতে পারি। তাহলো, সার্বভৌমত্ব যে কোনো অর্থে একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যই সংরক্ষিত। কারণ বস্তুতপক্ষে তিনিই প্রকৃত শাসক। অত্এব এটা তাঁর অধিকার যে, কেবল তাঁকেই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী স্বীকার করতে হবে। এই বিষয়টি কেউ আরো গভীর ও ব্যাপকভাবে হৃদয়ংগম করতে চাইলে আমি তাকে পরামর্শ দেবো, প্রথমে তিনি যেনো সার্বভৌমত্বের অর্থ এবং ধারণাকে খুব ভালো ও পরিষ্কারভাবে বুঝে নেন।
সার্বভৌমত্বের অর্থ
রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় এই শব্দটি উচ্চতর ক্ষমতা এবং নিরংকুশ কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কোনো ব্যক্তির বা ব্যক্তিসমষ্টির কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার অর্থ এই যে, তার নির্দেশই আইন। এই আইন রাষ্ট্রের নাগরিকদের উপর জারি করার সর্বসয় কর্তৃত্ব তারই। নাগরিকরা তার শর্তহীন আনুগত্য করতে বাধ্য। তা ইচ্ছায় ওও সাগ্রহে হোক কিংবা বাধ্য হয়ে। তার নিজের ইচ্ছা ব্যতীত বাইরের কোনো শক্তি তার শাসন ক্ষমতাকে বিন্দুমাত্র সীমাবদ্ধ ও সংকুচিত করতে পারেনা। তার বিপরীতে নাগরিকদের কোনো অধিকার নেই। যার যা কিছু অধিকার আছে তা সবই একমাত্র তাঁরই দান। কাজেই যে অধিকার তিনি হরণ করবেন তা আপন আপনিই লুপ্ত হয়ে যায়। আইনদাতা [Low Giver] যখন কারো অধিকার স্বীকার করেন তখনি তা আইনহত অধিকার বলে স্বীকৃত হয়। কাজেই মতো কোনো অধিকার বাকী থাকবেনা। সার্বভৌমত্বের অধিকারীর ইচ্ছা্য়ই আইন অস্তিত্ব লাভ করে এবং তা নাগরিকদেরকে আনুগত্যের রজ্জুতে বেঁধে নেয়। কিন্তু স্বয়ং সার্বভৌমত্বের অধিকারীকে বাধ্য করার মতো কোনো আইন কোথাও নাই। সার্বভৌমত্বের অধীকারী তার নিজসত্তয় নিরংকুশ ও সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক। তার বিধান সম্পর্কে বালো বা মন্দ, বিশুদ্ধ বা ভ্রন্ত- এই ধরনের কোনো প্রশ্নই উত্থাপিত হতে পারেনা। তিনি যা কিছুই করবেন তাই ভালো ও কল্যাণকর। তার অধীন কোনো নেই। তিনি যা কিছু করবেন তাই সঠিক, তার অধীনস্থ কেই এটাকে ‘ভ্রন্ত’ আখ্যয়িত করতে পারেনা। সার্বভৌমত্বের অধিকারীকে “মহান পবিত্র, দোষত্রুটিমুক্ত এবং সকল প্রকার ভুলের ঊর্ধে” মেনে নিতে হবে, চাই তিনি এইসব গুণের অধিকারী হোন বা না হোন। এই হলো আইনগত সার্বভৌমত্বের [Legal sovereignty] ধারণা। যা একজন আইনবিদ [ফকীগ বা [Jurist] পেশ করেন এবং যার কম কোনো জিনিসের নাম “সার্বভৌমত্ব” নয়। কিন্তু এই সার্বভৌমত্ব একেবারে একটি কল্পিত বিষয় হিসেবে থেকে যায় যতক্ষণ না তার পশ্চাতে কোনো বাস্তব সার্বভৌমত্ব কিংবা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় “রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব” [Political sovereignty] বিদ্যামান থাকে। অর্থাৎ কার্যত সেই কর্তৃত্বের মালিক তিনি, যিনি এই আইনগত সার্বভৌমত্বকে প্রয়োগ করবেন।
প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্ব কার?
এখন প্রথমেই এ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, উক্তরূপ কোনো সার্বভৌমত্ব বাস্তবিক পক্ষে মানবীয় পরিমন্ডলে বিদ্যামান আছে কি? যদি থেকে থাকে তবে তা কোথায়? এই সার্বভৌমত্বের মালিক কাকে বলা যেতে পারে?
কোনো রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বাস্তবিকই কোনো বাদশাহ্ কি এরূপ সার্বভৌমত্বের মালিক হয়েছে বা কখনো পাওয়া গিয়েছে বা পাওয়া যেতে পারে? নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী যে কোনো বাদশাহ্র বা শাসন কর্তার কথাই চিন্তা করুন। তার ক্ষমতা ও এখতিয়ারের মূল্যায়ন করলে পরিষ্কার বুঝতে পারবেন যে, কতো দিক দিয়েই না সে বাঁধাগ্রস্ত এবং কতোভাবেই না অসংখ্য বহিঃশক্তি তার ইচ্ছা ও মর্জির বিরুদ্ধে তাকে সীমাবদ্ধ করে রাখছে, তাকে অক্ষম করে দিচ্ছে।
তারপর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনোও স্থানে অংগুলি নির্দেশ করে তথায় “বাস্তব সার্বভৌমত্ব” আছে বলে দাবী করা যায় কি? যাকেই এই সার্বভৌমত্বের মালিক মনে করা হবে, পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, তার বাহ্যিক নিরংকুশ কর্তৃত্বের অন্তরালে প্রচ্ছন্নভাবে আরো কতকগুলো শক্তি বিদ্যমান আছে যাদের হাতে তার কর্তৃত্বের চাবিকাঠি নিহিত।
ঠিক এই কারণেই রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পন্ডিতগণ যখন সার্বভৌমত্বের সুম্পষ্ট ধারণা নিয়ে মানবসমাজে তার “ প্রকৃত ধারকের” সন্ধান করেন, তখন তারা চরমভাবে দিশেহারা হয়ে পড়েন। সার্বভৌমত্বের যোগ্য কোনো ক্ষমতাধর সত্ত্বা খুঁজে পাওয়া যায়না। কারণ মানবতার পরিসীমায় বরং সত্য কথা এই যে, সমগ্র সৃষ্টি জগতের কোথাও সার্বভৌমত্বের প্রকৃত ধারক মোটেই বিদ্যমান নেই। তাই কুরআন মজীদ এই সত্যকে বার বার তুলে ধরেছে যে, বাস্তবিকপক্ষে সার্বভৌমত্বের একমাত্র মলিক আল্লাহ্ তিনি নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক [*****] ১. {“যা কিছু করতে চান তা সম্পূর্ণরূপ করতে পারেন।” [সূরা হূদঃ ১০৭]} তিনি কারো নিকট দায়ী নন। কারো কম্মুখে তাকে জবাবদিহি করতে হয়না। [*****] ২. {“তিনি যা করেন সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদকারী কেউ নেই। [ সূরা আম্বিয়াঃ ২৩]} তিনি সর্বময় ক্ষমতা, এখতিয়ার ও কর্তৃত্বের অধিপতি [****] ৩. {সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব তাঁর হাতে। [সূরা মুমিনুনঃ ৮৮]} তিনি এমন এক সত্ত্বা, যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই [*****] ৪. {“তিনি আশ্রয় দান করেন এবং তাঁর বিপরীতে কেউ আশ্রয় দিতে পারেনা।” [সূরা মুমিনুনঃ ৮৮]} তার সত্ত্বা সকল প্রকার দোষত্রুটি থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। [***********] ৫. {“তিনি আশ্রয় দান করেন এবং পবিত্র সত্ত্বা ও নিরাপত্তা বিধায়ক।” [সূরা হাশরঃ২৩]}
সার্বভৌমত্ব কার অধিকার?
দ্বিতীয় প্রশ্ন এই উত্থাপিত হয় যে, প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে যদি এই সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রদান করাও হয় তবে বাস্তাবেও কি তার হুকুম ‘আইন’ বলে বিবেচিত হবে? তার উপর কারো কোনো অধিকার থাকবেনা? তার শর্তহীন আনুগত্য করতে হবে। এমনকি তার নির্দেশ সম্পর্কে ভালো মন্দ, ভুল ও নির্ভুল হওয়ার প্রশ্ন আদৌ উত্থাপন করা যাবেনা?
আল্লাহ্কে ছাড়া এই অধিকার চাই কোনো ব্যক্তিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে, কিংবা দেশবাসীর সংখ্যাগুরু দলকেই দেয়া হোক, সেই সম্পর্কে নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যাবে যে, শেষ পর্যন্ত কিসের ভিত্তিতে সে এই অধিকার লাভ করলো? কোন্ সনদের ভিত্তিতে সে জনগণের উপর নিরংকুশ কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করলো? এই প্রশ্নের উত্তরে খুব বেশী বললে শুধু এদোটকুই বলা যেতে পারে যে, জনগণের সমর্থনেই তার এই কর্তৃত্বের সনদ। কিন্তু আপনি কি একথা মেনে নিতে প্রস্তুত যে, কোনো ব্যাক্তি যদি নিজেকে স্বেচ্ছায় অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে তবে বিক্রেতার উপর ক্রেতার সংগত মালিকানা অধিকার সত্যিই কি স্থাপিত হবে? এরূপ ইচ্ছাকৃত আত্মবিক্রয় যদি ক্রেতাকে সংগত মালিকানা না দেয়, তাহলে জনগণের নিছক ইচ্ছা ও সম্মতি প্রকাশ কারো সার্বভৌমত্ববে কিরূপে সংগত প্রমাণ করতে পারে? কুরআন মজীদ এই গ্রন্থির জট এভাবে খুলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র সৃষ্টির উপর কোনো সৃষ্টির প্রভুত্ব কায়েমে করার এবং হুকুম চালাবার কোনো অধিকার নেই। এই অধিকার একমাত্র আল্লাহ্র এবং তার এই অধিকারের ভিত্তি এই যে, তিনিই নিখিল সৃষ্টির স্রষ্টা। “সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই, এর উপর প্রভুত্ব চালাবার, একে ‘শাসন’ করার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।” [সূরা আরাফঃ ৫৪] এটা এমন যুক্তিপূর্ণ কথা যাকে অন্তত জ্ঞান, বিবেক ও বুদ্ধিসম্মত লোকেরা যারা আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে, কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করতে পারেনা।
সার্বভৌমত্ব কার হওয়া উচিত?
তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, হক ও বাতিলের কথা না তূলেও সার্বভৌমত্বের এই অধিকার যদি কোনো মানবশক্তিকে দেয়া হয়, তাবে তাতে মানুষের কি প্রকৃত কল্যাণ হতে পারে? মানুষ- সে ব্যক্তি হোক, শ্রেণী হোক কিংবা কোনো জাতি বা সমষ্টিই হোক সার্বভৌমত্বের এতো বিরাট ক্ষমতা সামলানোই তার পক্ষে অসম্ভব। জনগণের উপর হুকুম চালাবার সীমাহীন অধিকার তার থাকবে, তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অন্য কারো থাকবেনা এবং তার সকল সিদ্ধান্তই নির্ভুল মনে করে শিরধার্য করে নেয়া হবে, এরূপ অধিকার ও কর্তৃত্ব যদি কোনো মানবীয় শক্তি লাভ করতে পারে, তবে সেখানে যুলুম, নিপীড়ন ও নির্যাতন হওয়া একেবারে অনিবার্য ব্যাপার। তখন সমাজের মধ্যেও যুলুম হবে, ‘সমাজের বাইরে অন্যান্য পতিবেশী সমাজের উপরও যুলুম হবে। এরূপ ব্যবস্থার মূল প্রকৃতিতেই বিপর্যয়ের বীজ নিহিত রয়েছে। মানুষ যখনই জীবনের এই পথ অবলম্বন করেছে, তখনি ভাঙ্গন, বিপর্যয় ও অশান্তি সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছে। কারণ যার বাস্তবিকপক্ষে সার্বভৌমত্ব নেই এবং যাকে সার্বভৌমত্বের অধিকারও প্রদান করা হয়নি, তাকেই যদি কৃত্রিমভাবে সারভৌমত্বের অধিকার ও কর্তৃত্ব দান করা হয়, তবে সে কিছুতেই এই পদের যাবতীয় ক্ষমতা এখতিয়ার সঠিক পন্থায় ব্যবহার করতে সক্ষম হবেনা। কুরআন মজীদ এই কথাই নিন্মোক্ত ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ
“যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেনা, তারা যালিম।” [সূরা মায়েদাঃ ৪৫]
আল্লাহ্র আইনগত সার্বভৌমত্ব
এসব কারণে ইসলাম চূড়ান্তভাবে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে যে, আইনগত সার্বভৌমত্ব তাঁরই স্বীকার করতে হবে যার বাস্তব সার্বভৌমত্ব স্থাপিত হয়েছে নিখিল বিশ্বের উপর এবং গোটা মানবজাতির উপরও যার সার্বভৌমত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। একথাটি কুরআন মজীদে বার বার বলা হয়েছে এবং তা এতো বলিষ্ঠভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে, কোনো কথা বলার জন্য তা অপেক্ষা জোরালো ভাষা আর হতে পারেনা। উদাহরণস্বরূপ দেখুন কুরআন একস্থানে বলেছেঃ
“হুকুম দিবার ও প্রভুত্ব ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার আল্লাহ্র ছাড়া আর কারো নেই। তিনি আদেশ করেছেন, একমাত্র তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্য করো, এটাই সঠিকপন্থা।” [সূরা ইউসুফঃ ৪০]
অনত্র বলেছেনঃ
একমাত্র সেই বিধানই অনুসরণ করো যা তোমাদের জন্য তোমাদের ‘প্রভুর’ নিকট থেকে নাযিল করা হয়েছে এবং তাকে ত্যাগ করে অন্য পৃষ্ঠপোষকদের অনুসরণ করোনা। সূরা আরাফঃ ৩]
তৃতীয় একস্থান আল্লাহ্র এই আইনগত সর্বভৌমত্ব অমান্য করাকে পরিষ্কার কুফরী বলে ঘোষণা করা হয়েছেঃ
“আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে যারা ফায়সালা করেনা তারা কাফির।” [সূরা মায়েদাঃ ৪৪]
এই আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহ্ তায়ালার আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করার নাম ঈমান ও ইসলাম এবং তা অস্বীকার কারার নামই নিরেট কুফর।
রসূল (স) এর পদমর্যাদা
দুনিয়াতে আল্লাহ্র এই আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিনিধি হচ্ছেন আল্লাহ্ প্রেরিত নবীগণ। অন্য কথায় আমাদের আইন রচয়িত ও সংবিধান দাতা [Low Giver] আমাদের জন্য কি আইন এবং কি নির্দেশ দিয়েছেন তা জানবার একমাত্র উপায় হচ্ছে আম্বিয়ায়ে কিরাম। এ কারণে ইসলামে আল্লাহ্র হুকুমের অধীন নির্দ্বিধায় তাদের অনুসরণ করার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কুরআন শরীফে পরিষ্কার দেখতে পাবেন যে, আল্লাহ্র প্রেরিত নবীই উদাও কন্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ
“আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো।” [সূরা শূয়ারাঃ ১০৮,১১০,১২৬,১৪৪,১৫০,১৬৩,১৭৯]
আর কুরআন মাজীদ একথা সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত নীতি হিসেবে বর্ণনা করেছেঃ
“আমি যে রসূলই প্রেরণ করেছি আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবিক তাঁর অনুসরণ করার জন্যই তাকে পাঠিয়েছি।” [সূরা নিসাঃ ৬৪]
“যে ব্যক্তি রসূলের অনুসরণ করবে, সে মূলত আল্লাহ্রই অনুসরণ করলো।” [সূরা নিসাঃ ৮০]
এমনকি বিতর্কপূর্ণ ও মতবিরোধ সংকুল বিষয়ে রসূলকে যারা “সর্বশেষ মীমাংসাকারী” বলে মানতে অস্বীকার করে কুরআন মজীদ তদেরকে ‘মুসলামান’ গণ্য করতেই সুস্পষ্টরূপে অস্বীকার করেছেঃ
“অতএব না, তোমার রবের শপথ, তারা কখনো ঈমানদার হতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিতর্ক ও বিরোধমূলক বিষয়সমূহে- হে নবী তোমাকেই সর্বশেষ বিচারক মানবে এবং তুমি যা মীমাংসা দিবে তা পরিপূর্ণরূপে মেনে নিবে এবং তা শিরধার্য করে নিতে হৃদয়ে দ্বিধা সংকোচ বোধ করবেনা।” [সূরা নিসাঃ ৬৫]
কুরআন আবার বলছেঃ
“আল্লাহ্র রসূল যখন কোনো ব্যাপারে কোনো ফয়সালা করেন, তাখন মুমিন পুরুষ এবং মুমিন নারীর পক্ষে সেই সম্পর্কে নতুন করে ফয়সালা করার বিন্দুমাত্র এখতিয়ার নেই। কারণ, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করে, সে সুস্পষ্ট ভ্রন্তিতে নিমজ্জিত।” [সূরা আহ্যাবঃ ৬৩]
ইসলামে আইনগত সার্বভৌমত্ব একান্ত ও নিরংকুশভাবে একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের জন্য নির্দিষ্ট। অতপর এই সম্পর্কে সন্দেহ করার আর কোনো অবকাশ থাকেনা।
রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ্র
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সাংবিধানিক ব্যাপারের ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর আর একটি প্রশ্ন বাকি থেকে যায় যে, অতপর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব [Political sovereignty] কার? নিশ্চিতভাবে এর উত্তর এই এবং এই- ই হতে পারে যে, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বও একমাত্র আল্লাহ্র। কারণ আল্লাহ্ তায়ালার আইনগত সার্বভৌমত্ব মানব সমাজে যে প্রতিষ্ঠানই রাজনৈতিক শক্তিবলে কার্যকর [Force] করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হবে, আইন ও রাজনীতির পরিভাষায় তাকে কখনো সার্বভৌমত্বের মালিক বলা যায়না। যে শক্তির আইনগত সার্বভৌমত্ব নেই এবং যার ক্ষমতা ও একতিায়ার এক উচ্চতর আইন আগে থেকেই সীমিত ও অনুগত বানিয়ে দিয়েছে এবং যার পরিবর্তন কারার কোনো ক্ষমতা তার নেই, সে সার্বভৌমত্বের ধারক হতে পারেনা, এটা তো সুস্পষ্ট কথা্ একন এর প্রকৃত অবস্থা বা মর্যাদা কোন্ শব্দ দ্বারা ব্যাক্ত করা যেতে পারে? কুরআন মজীদই এই প্রশ্নর সমাধান দিয়েছে। কুরআন মজীদ এই প্রতিষ্ঠানকে ‘খিলাফত’ নামে ব্যক্ত করেছে। অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠান স্বয়ং “একচ্ছত্র শাসক” নয় বরং একচ্ছত্র শাসকের প্রতিনিধি মাত্র।
গণতান্ত্রিক খিলাফত
আল্লাহ্র প্রতিনিধি শব্দটি শোনার সংগে সংগে ‘জিল্লুল্লাহ্’ [আল্লাহ্র ছায়া]’ পোপবাদ এবং বাদশাহদের খোদায়ী অধিকার [Divine right of the kings] প্রভৃতির দিকে আপনাদের মন ও মানসিকতা যেনো বিচ্যুত না হয়। কুরআনের সিদ্ধান্ত এই যে, আল্লাহ্র এই প্রতিনিধিত্বের অধিাকার বিশেষ কোনো ব্যক্তি, পরিবার, বংশ কিংবা নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নয়। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের সমর্থক এবং কোনো শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত নয়। বস্তুতপক্ষে আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের মসর্থক এবং রসূলের মারফতে প্রাপ্ত আল্লাহ্র বিধানকে উচ্চতর ও চূড়ান্ত আইন হিসেবে মান্যকারী সকল মানুষই আল্লাহ্র দেয়া এই প্রতিনিদিত্বের অধিকারী।
“ আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি পৃথিবীতে ঈমানদার ও সৎকার্মশীল লোকদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বা খলিফা নিযুক্ত করবেন।” সূরা আননূরঃ৫৫]
এই জিনিসই ইসলামী খিলাফতকে রাজতন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, পোপবাদ এবং পাশ্চাত্য ধারণাভিত্তিক ধর্মরাষ্ট্র [Theocracy] প্রভৃতির বিপরীতে এক নিখঁত ও পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু তা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। পাশ্চত্য গণতন্ত্র যেখানে জনগণকেই সার্বভৌমত্বের ‘মালিক’ মনে করে, সেখানে ইসলাম ‘মুসলিম’ জনগণকে কেবল খিলাফতেরই অধিকারী বলে অভিহিত করে। রাষ্ট্রব্যবস্থা পবিচালনর জন্য পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে দেশবাসীর ভোট গ্রহণ করা গ্রহণ করা হয় এবং গণমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়; ইসলামী গণতন্ত্রও তাই দাবী করে। কিন্তু পার্থক্য এই যে, পাশ্চাত্য ধারণায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নিরংকুশ ও সীমাহীন শক্তির মালিক। পক্ষান্তরে ইসলামের ধারণা অনুসারে গণতান্ত্রিক খিলাফত আল্লাহ্ তায়ালার আইনের অনুসরণ করতে বাধ্য।
২. রাষ্ট্রের কর্মসীমা
খিলাফতের উপরোক্ত ব্যাখ্যা এই বিষয়টির সরাসরি সমাধান হয়ে যায় যে, ইসলামী সংবিধানে রাষ্ট্রের কর্মসীমা কতোদূর পর্যন্ত বিস্তৃত? ইসলামী রাষ্ট্র যখন আল্লাহ্র খিলাফত, এখানে যখন একমাত্র আল্লাহ্র আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, তখন তার ক্ষমতা ও ইখ্তিয়ার অনিবার্যরূপেই আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যেই গন্ডিবদ্ধ থাকতে বাধ্য। ইসলামী রাষ্ট্র তার কর্তব্য উক্ত সীমার মধ্যে অবস্থান করেই পালন করবে। সে সাংবিধানিক দিক থেকে এ সীমা লংঘন করতে পারেনা। আল্লাহ্র আইনগত সার্বভৌমত্বের নীতিমালা হতে এই কথা কেবল যুক্তি হিসেবেই যে পাওয়া যায় তা নয়, বরং কুরআন মজীদ স্বয়ং তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছে। কুরআনের স্থানে স্থানে বিধান প্রদান করে সতর্ক করে দেয়া হয়েছেঃ
“এটা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, [তা লংঘন করা তো দূরের কথা] তার নিকটেও যেয়োনা।”
“এটা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা, তা লংঘন করোনা।”
“আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা যারা লংঘন করে তারা যালিম।”
অতঃপর কুরআন একটি মূলনীতি হিসেবে এই হুকুম জারী করেছেঃ
“হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ্র আনুগত্য করো, আল্লাহ্র রসূলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বসম্পন্ন তাদেরও। কোনো বিষয়ে যদি তোমাদের পরস্পরের মধ্যে মতাবিরোধ হয়, তাবে তা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বসী হয়ে থাকো।” [সূরা নিসাঃ ৫৯]
এ আয়াত অনুসারে রাষ্ট্রের আনুগত্য অনিবার্যরূপে আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্যের অধীন হবে, তা থেকে স্বাধীন হবেনা। এর পরিষ্কার অর্থ এই যে, আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান অনুসরণের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত হয়ে জনগণের নিকট আনুগত্য দাবী করার কোনো অধিকারই রাষ্ট্রের নেই। একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলেছেনঃ
“যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করবে, তার আনুগত্য কিছুতেই করা যাবেনা।”
“স্রষ্টার হুকুম অমান্য করে সৃষ্টির আনুগত্য কিছুতেই করা যাবেনা।”
এই নীতিটির সংগে উক্ত আয়াত আর একটি মূলনীতিও নির্ধারণ করে। তা এই যে, মুসলিম সমাজে যে কোনো প্রকার মতবিরোধই হোক, ব্যক্তিগণের পরস্পরের মধ্যে হোক, বিভিন্ন দলের মধ্যে হোক, কিংবা রাষ্ট্র ও প্রজা সাধারণের মধ্যে হোক, অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে হোক তার মীমাংসা কারার জন্য আল্লাহ্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত চূড়ান্ত বিধানের দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এই নীতির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে রাষ্ট্রের অবশ্যই একটি সংস্থা থাকবে যা মতদৈততামূলক বিষয় সমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নহ্ মুতাবিক করবে।
৩. রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের কর্মসীমা ও পারস্পরিক সম্পর্কে
রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের [Organs of states] ক্ষমতা, অধিকার ও এখ্তিয়ারের সীমা ও উপরোক্ত আলোচনা থেকে পরিষ্কাররূপে জানা যায়।
আইন পরিষদের সীমা
আইন পরিষদ [Lagislature] কে আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় বলা হয় “আহলুল-হাল্ল-ওয়াল-আকদ [আইন বিধিবদ্ধকারীগণ]। যে রাষ্ট্র আল্লাহ্ ও রসূলের আইনগত সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে গঠিত হয়েছে তার আইন পরিষদও যে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রসূলের বিরুদ্ধে পরিপূর্ণ মতৈক্যের বলেও কোনো আইন পাশ করার অধিকারী হতে পারেনা, তা একেবারে সুস্পষ্ট। একটু আগেই আমি আপনাদেরকে কুরআনের এই ফয়সালা শুনিয়েছি যে, “আল্লাহ্ এবং আল্লাহর রসূল যে বিষয়ে চূড়ান্তবাবে মীমাংসা করে দিয়েছেন সেই সম্পর্কে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার কোনো ঈমানদার পুরুষ বা নারীর নেই” এবং “যারা আল্লাহ্র দেয়া বিধান অনুসারে ফায়সালা করেনা, তারাই কাফেল।” এসব সুস্পষ্ট নির্দেশের অনিবার্য দাবি হলো আল্লাহ্ এবং রসূলের বিধানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আইন রচনা করা আইন পরিষদের অধিকারের সীমাবহির্ভূত এবং আইন পরিষদ এই ধরনের কোনো আইন পাশ করলেও তা অনিবার্যরূপে সংবিধানের লংঘন [Ultrovires of the constitution] বলে অভিহিত হবে।
প্রসংগত এই প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এমতাবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রে আইন পরিষদকে নিন্মলিখিত অনেক কাজ করতে হবে।
১. যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রসূলের সুস্পষ্ট ও চুড়ান্ত বিধান মওজুদ রয়েছে, আইন পরিষদ যদিও তাতে কোনো রদবদল করতে পারবেনা, কিন্তু সেই বিধান ও নির্দশসমূহকে কার্যকরী করার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন ও পন্থা প্রণালী [Rules and Regulations] নির্ধারণ করা আইন পরিষদের কর্তাব্য।
২.যেসব ব্যাপারে কুরআন হাদীসের বিধানের একাধিক ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রয়েছে তন্মধ্যে কোন্ ব্যাখ্যাটিকে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হবে, তা নির্দষ্ট করা আইন পরিষদেরই কাজ। এজন্য আইন পরিষদে অনিবার্যরূপে এমন সব লোক থাকতে হবে যাদের আল্লাহ্র বিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দক্ষতা ও যোগ্যতা আছে। অন্যথায় ঐসব বিধানের ভূল ব্যাখ্যা ইসলামী শরীয়াতকে বিকৃত ও পরিবর্তিত করে দিতে পারে।
মূলত, এই প্রশ্নটি ভোটদাতাদের নির্বাচনী দৃষ্টিভংগি ও যোগ্যতার সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। নীতিগত ভাবে এই কথা স্বীকার করতে হবে যে, আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ব্যাখ্যার মধ্যে একটি গ্রহণ করা ও তাকে বিধিবদ্ধ করার অধিকার আইন পরিষদের। ফলে আইন পরিষদের গৃহীত ব্যাখ্যাই আইন হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু শর্ত এই যে, সে যেনো ব্যাখ্যার সীমা অতিক্রম করে বিকৃতির সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না যায়।
৩. যেসব ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং রসূলের কোনো নির্দেশ বা বিধান বিদ্যমান নেই, সেসব ব্যাপারে আসলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে নতুন আইন রচনা করা অথবা সেই সম্পর্কে ফিক্হের কিতাবসমূহে পূর্বে হতে প্রণীত কোনো আইন বর্তমান থাকলে তন্মধ্যে কোনো একটিকে গ্রহণ করা আইন পরিষদের কাজ।
৪. যেসব ব্যাপারে নীতিগত কোনো নির্দেশও পাওয়া যায়না, সে সম্পর্কে মনে করতে হবে যে, এই বিষয়ে আইন রচনার অধিকার আল্লা্হ্ তায়ালা আমাদেরকে দিয়েছেন। কাজেই এসব ব্যাপারে আইন পরিষদ যাথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করতে পারে। তবে শর্ত এই যে, সে আইন যেনো শরীয়তের কোনো হুকুম বা নীতির বিরোধী বা তার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। এ সম্পর্কে “যা নিষিদ্ধ নয় তা বৈধ” মূলনীতিটি গৃহীত হয়েছে।
এই চারটি নিয়ম রসূলের সুন্নহ, খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা এবং মুজতাহিদদের অভিমত থেকে আমরা জানতে পারি। প্রয়োজনে এর প্রত্যেকটি নিয়মের উৎস কি তাও আমি বলে দিতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয়, ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ কেউ ভালো করে হৃদয়ংগম করে নিলে তার সাধারণ জ্ঞান [Common Sense] তাকে বলে দিবে যে, এই ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় আইন পরিষদের কর্মসীমা অনুরূপই হওয়া উচিত।
শাসন বিভাগের কর্মসীমা
এখন শাসন বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করবো। একটি ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন বিভগের [Executive] আসল কাজ হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান জারী করা এবং তাকে কার্যকর করার জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা । এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যই তাকে একটি অমুসলিম রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করে। তা না হলে একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং একটি কাফির রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থাক্য থাকেনা। ‘শাসন বিভাগ’ সম্পর্কে কুরআন মজীদে ‘উলিল আমর’ এবং হাদীস শরীফ ‘উমারা’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কুরআন ও হাদীস উভয়ই তাদের আদেশ শোনা এবং মানা’ [Obedience] সম্পর্কে জোর আদেশ দিয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে তাতে এই শর্ত আরোপ করা হয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধানের অনুগত থাকতে হবে। তারা তা লংঘন করে নাফরমানী ও বিদয়াতের পথে পা বাড়াবেনা। কুরআন মজীদ এ সম্পর্কে পরিষ্কার বলে দিচ্ছেঃ
“কখনো এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করোনা যার অন্তর আমার [আল্লাহ্র] স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, এবং যে নিজের নফসের লালসা বাসনা চরিতার্থ করার পথ অবলম্বন করেছে আর সীমা লংঘন করাই যার অভ্যাস।” [সূরা কাহাফঃ ২৮]
“যেসব সীমালংঘনকারী পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সংস্কারের কোনো কা্জই সীমালংঘনকারী পৃথিবীতে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সংস্কারের কোনো কাজই করেনা, তোমরা তাদের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের আনুগত্য করোনা।” [সূরা শুয়ারঃ ১৫১-১৫২]]
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো সুস্পষ্টভাবে বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ
“তোমাদের উপর যদি কোনো নাককাটা ক্রীতদাসকেও আমীর বা ‘রাষ্ট্র পরিচালক’ নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহ্র বিধান অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব দান করে তোমরা তার কথা শোনো এবং আনুগত্য করো।” [মুসলিম]
“মুসলিম ব্যক্তিকে সবসময় আদেশ শ্রবণ ও অনুসরণ করে চলতে হবে, চাই সাগ্রহেই হোক, কিংবা বাধ্য হয়ে- যতক্ষণ না তাকে কোনো পাপ কাজের আদেশ করা হয়। কিন্তু কোনো পাপ কাজের হুকুম দেয়া হলে তা শোনা ও মানা যাবেনা।” [বুখারী, মুসলিম]
“যে ব্যক্তি আমাদের ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোনো নতুন মতবাদের প্রচলন করবে যা তার সামগ্রিক প্রকৃতির সংগে খাপ খায়না, তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত।” [বুখারী, মুসলিম]
“কোনো বিদয়াতী [ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোনো অনৈসলামিক রীতি পদ্ধতি উদ্ভাবনকারী] কে যে ব্যক্তি সম্মান প্রদর্শন করলো সে ইসলামকে মূলোৎপাটনে সাহায্য করলো।” [বায়হাকীর শুয়াবুল ঈমান]
এসব সুস্পষ্ট আলোচনার পর এই সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ বা অস্পষ্টতা অবশিষ্ট থাকতে পারেনা যে, নির্বাহী সরকার ও তার ব্যবস্থাপনার জন্য ইসলামে কি সীমা নির্ধারিত করা হয়েছে? কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমীহ থেকে তা স্পষ্টরূপে বুঝতে পারা যায়।
বিচার বিভাগের কর্মসীমা বা অধিক্ষেত্র
এরপর বিচার বিভাগের [Judiciary] কথা। আমাদের প্রাচীন পরিভাষায় যা ‘কাদা’ [******] র সমার্থবোধক। বিচার বিভাগের অধিক্ষেত্র বা কর্মসীমা আল্লাহ্র আইনগত সার্বভৌমত্বের নীতিমালাই সরাসরি নির্দিষ্ট করে দেয়্। ইসলাম যখনই তার নীতিমালার ভিত্তিতে রাষ্ট্র কায়েম করে, নবীগণই তা সর্বপ্রথম বিচারপতি হয়ে থাকেন এবং আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী জনগণের বিষয়সমূহের মীমাংসা করাই তাঁদের কাজ। নবীদের পরে যারা এই দায়িত্বে অভিষিক্ত হবেন, তারাও আবার নিজেদের বিচার কার্যর ভিত্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল থেকে প্রপ্ত আইনের উপর স্থাপন করতে বাধ্য। কুরআন মজীদের ‘সূরা মায়িদার’ দুই রুকুব্যাপী এই বিষয়েরই আলোচনা রয়েছে। তাতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, আমি তাওরত নাযিল করেছি; তাতে হিদায়াত ও উজ্জ্বল আলোকচ্ছটা ছিলো এবং বণী ইসরাঈলের সকল নবীই এবং তাদের পরে সকল রব্বানী [আল্লাহ্ওয়ালা] ও পন্ডিতগণ তদনুসারে ইহুদীদের ব্যাপারসমূহের মীমাংসা করতেন। তাদের পরে আমি ঈসা ইবনে মারিয়ামকে প্রেরণ করেছি এবং তাকে হিদায়াত ও উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট ইঞ্জীল কিতাব দিয়েছি। অতএব ইঞ্জীল কিতাবধারীদের কর্তব্য আল্লাহ্ প্রদত্ত ইঞ্জীলের হিদায়াত অনুসারে ফায়সালা করা। এই ঐতিহাসিক বিবরণ প্রদানের পর আল্লাহ্ তায়ালা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি এই কিতাব [কুরআন মজীদ] ঠিক ঠিকভাবে পরম সত্যতা সহকারে তোমার প্রতি নাযিল করেছিঃ
“অতএব তুমি জনগণের মধ্যে আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করো এবং তোমার নিকট আগত এই মহান সত্যকে উপেক্ষা করে মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ করোনা।” [সূরা মায়িদাঃ ৪৮]
সামনে অগ্রসর হয়ে আল্লাহ্ তায়ালা নিম্মলিখিত আয়াত দ্বারা এই আলোচনা সমাপ্ত করেনঃ
“অতএব মানুষ কি জাহিলী যুগের ফায়সালা চায়? অথচ আল্লাহ্র প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাদের জন্য আল্লাহ্ ছাড়া উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে?” [সূরা মায়িদাঃ ৫০]
“এই দীর্ঘ আলোচনা চলাকালে আল্লাহ্ তায়ালা তিনবার বলেছেনঃ যারা আল্লাহ্র নাযিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করেনা তারা কাফির…….. তারা যালিম…… তারা ফাসিক।” [সূরা মায়িদাঃ ৪৪-৪৯]
আল্লাহ্ তায়ালার এই কঠোর শাসন বাণীর পর একথা বলার হয়তো আর প্রয়োজন বাকী থাকেনা যে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত কেবল আল্লাহ্র আইন কার্যকর করার জন্য কায়েম হয়, তার বিপরীত ফায়সালা করার জন্য নয়।
রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক
এখন ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লিখিত তিনটি বিভাগের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক কি হবে এই প্রশ্নটির আলোচনা বাকী থাকলো। এ সম্পর্কে কুরআন হাদীসের সরাসরি নির্দেশ তো বিদ্যমান নেই, কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের কার্যক্রম ও ঐতিহ্য [Convention] থেকে আমরা পরিপূর্ণ পথনির্দেশ লাভ করতে পারি। এই উৎস থেকে আমরা এই তথ্য লাভ করতে পারি যে, রাষ্ট্র প্রধান শুধু রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার বলেই রাষ্ট্রের এই তিন বিভাগের প্রধান। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মর্যাদা্য়ই অভিষিক্ত ছিলেন এবং খোলাফায়ে রাশেদীনও কখন এই মর্যাদায় সমাসীন ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্র প্রধানের নীচের পার্যায়ে সেকালেও এই তিনটি বিভাগ পরস্পর থেকে পৃথক ছিলো। কখনকার যুগে “আহলুল হাল্লি-ওয়াল আকদ” সম্পূর্ণ আলাদা ছিলো। খিলাফতে রাশেদার যুগে তাঁদের পরামর্শের আলোকে প্রশাসন পরিচালিত হতো এবং আইন সম্পর্কিত বিষয়ের ফায়সালাও তাদেরই পারমর্শক্রমে সম্পন্ন হতো। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ আলাদা ছিলেন। বিচার বিভাগের উপর তাদের হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকরা ছিলোনা। কাজী [বিচারকগণ পৃথক ছিলেন, তাদের উপর শাসনকার্য পরিচালনার কোনো দায়িত্ব অর্পিত ছিলোনা।
রাষ্ট্রীয় বিষয়সমূহের সুষ্ঠু সমাধান করার যখনি প্রয়োজন দেখা দিতো, কখন খোলাফায়ে রাশেদীন “আহলুল হাল্লি-ওয়াল আকদ” এর সভা ডেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ চাইতেন। এবং পরামর্শভিত্তিকে কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেতো।
সরকারী প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ খলীফার অধীন ছিলেন। খলীফাই তাঁদের নিয়োগ দান করতেন এবং তাঁরই নির্দেশে তারা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।
কাজী [বিচারক]দেরকেও যদিও খলীফাই নিযুক্ত করতেন; কিন্তু একবার কাজী নিযুক্ত হওয়ার পর তার বিচার ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার কোনো অধিকারই খলীফার ছিলোনা। বরং খলীফার ব্যক্তিগত ব্যাপারেই হোক কিংবা শাসন বিভাগের প্রধান হিসাবেই হোক, তার বিরুদ্ধে কারো কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাঁকেও ‘কাজীর’ সন্মুখে জবাবদিহি করার জন্য ঠিক সাধারণ নাগরিকের মতোই উপস্থিত হতে হতো।
একই সময় কোনো ব্যক্তি কোনো এলাকায় শাসকও হয়েছেন এবং বিচারকও হয়েছেন পদস্থ কর্মকর্তা বা গভর্ণর, কিংবা স্বয়ং রাষ্ট্র প্রধান প্রমাণ পাওয়া যায়না। অনুরূপভাবে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা মুকদ্দমায় জবাবদিহি করতে অথবা আদালতে হাজির হওয়ার বাধ্যবাধকতা থেকে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে নিষ্কৃতি দেয়া হয়েছে বলেও কোনো উদাহরণ পাওয়া যায়নি।
বিচার ব্যবস্থার কাঠামোগত ব্যাপারে বৃহৎ পরিসরে বর্তমান কালের প্রয়োজন অনুসারে কিছুটা। রদবদল করা যেতে পারে, কিন্তু তার মূলনীতি যথাযথভাবে অপরিবর্তিত থাকবে। তাতে যে ধরনের খুঁটিনাটি রদবদল করা যেতে পারে, তা এভাবে যে, রাষ্ট্র প্রধানের শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ও এখ্তিয়ারকে খোলাফায়ে রাশেদীন যতোখানি বিশ্বাসযোগ্য ও আস্তাভাজন ছিলেন, অনুরীপ রাষ্ট্র প্রধান বর্তমান যুগে পাওয়া যাবেনা। তাই আমরা রাষ্ট্র প্রধানের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতার উপরও বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারি, যাতে সে ডিক্টেটরে পরিণত হতে না পারে। মামলা মুকাদ্দমা ও শুনানির জন্য সরাসরি সংগত হতে পারে, যাতে সে কোনোরূপ অবিচার করার সুযোগে না পায়।
[মাওলানার বক্তৃতার এ পর্যায়ে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার এই মতের উৎস কি? তার উত্তরে মাওলানা মওদূদী বলেনঃ
আমার এই কথার দলীল এই যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ সম্পূর্ণ পৃথক ছিলো। আর রাষ্ট্র প্রধানের নিকট এই উভয় ক্ষেত্রের ক্ষমতা সে যুগে শরীয়তের কোনো বিধানের ভিত্তিতে একত্র করা হয়নি বরং এই ভরসায় একত্র করা হয়েছেল যে, তিনি বিচারক হিসেবে বিচারালয়ে আসীন হয়ে নিজের শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারসমূহকে কিছুমাত্র প্রভাবশালী হতে দিবেননা। বরং খোলাফায়ে রাশেদীদের প্রতি সেকালের জনগণের এতাদূর আস্থা ছিলো যে, তারা খলীফাকেই “সর্বশেষ মীমাংসাকারী” হিসেবে কামনা করতো, যাতে অন্য কোথাও বিচার না পাওয়া গেলেও তাঁর নিকট অবশ্যই সুবিচার পাওয়া যাবে। বর্তমান যুগে এ রকম আস্থাভাজন ব্যক্তি যদি আমরা লাভ করতে না পারি, তবুও রাষ্ট্র প্রধানকেই যুগপৎভবে প্রধান বিচারপতি ও শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসীন রাখতে হবে ইসলামী সংবিধানের কোনো ধারাই আমাদেরকে সেজন্য কিছুমাত্র বাধ্য করেনা।]
অনুরূপভাবে আমরা এই ব্যাপারে যেসব পরিবর্তন সাধন করতে পারি তা এই যে, আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের বা পার্লামেন্টের নির্বাচন পদ্ধতি এবং তাদের সংসদীয় নীতিমালা আমরা এ যুগের প্রয়োজন অনুসারে প্রণয়ন করতে পারি। এরূপে আরো অনেক ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে।
এখানে আরো দু’টি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে- যার জবাব দেয়াও প্রয়োজন। প্রথম এই যে, বিচার বিভাগ “আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদের” গৃহীত কোনো আইনকে কুরআন ও সুন্নাতের খিলাফ হওয়ার কারণে বাতিল করতে পারে কি? এই সম্পর্কে শরীয়াতের কোনো নির্দেশ আছে বলে আমার জানা নেই। খিলাফতে রাশেদার কর্মপন্থা এই ছিলো যে, সে যুগে বিচার বিভাগের এরূপ কোনো অধিকার বা ক্ষমতা ছিলোনা। কিংবা কোনো কাজী এরূপ করেছে এমন কোনো নজীর পাওয়া যায়না। কিন্তু আমার মতে এর কারণ শুধু এই যে, সেকালের আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ [বা পরামর্শ সভা] এর লোকগণ কুরআন হাদীসে গভীর বুৎপত্তি রাখতেন। বর্বোপরি স্বয়ং খোলাফায়ে রাশেদীনের সম্পর্কে জনগণের এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, তারা বিদ্ধমান থাকতে কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত কোনো ফায়সালা হতে পারেনা। বর্তমান যুগেও আমরা যদি আমাদের সংবিধানের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারি যে, কোনো আইন পরিষদ কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীতে কোনো আইন পাশ করবেনা, তবে আজও বিচার বিভাগকে আইন পরিষদের ফায়সালা মানতে বাধ্য করা যায়। কিন্তু তদ্রূপ নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব না হলে নিরুপায় হয়েই বিচার বিভাগকে আইন পরিষদের গহীত কুরআন ও সুন্নাতের বিপরীত আইনসমূহ বাতিল করার এখ্তিয়ার দিতেই হবে।
দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, ইসলামে আইন পরিষদের [আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ] সঠিক মর্যাদা কি? তা কি রাষ্ট্র প্রধানের নিছক মন্ত্রণাসভা, যার পরামর্শ গ্রহণ কিংবা বর্জনের অধিকার তার রয়েছে? অথবা রাষ্ট্র প্রধান কি আইন পরিষদের সংখ্যাগুরুর কিংবা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ফায়সালাসমূহ গ্রহণ করতে অবশ্যই বাধ্য থাকবেন।
এই প্রসংগে কুরআন মজীদ যা কিছু বলেছে তা এই যে, মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া বাঞ্চনীয় “তাদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।” (সূরা শূরাঃ ৩৮)
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাষ্ট্রধান হিসেবে সমম্বোধন করে আল্লাহ্ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেনঃ
“সামগ্রিক ব্যাপারসমূহে তাদের সাথে পরামর্শ করো। [পরামর্শের পর] যখন তুমি [কোনো কাজের] সংকল্প করবে তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কাজ করো।” [আলে ইমরানঃ ১৫৯]
এই দুইটি আয়াতই সামগ্রিক ব্যাপারসমূহে পরামর্শ করাকে অপরিহার্য করে দিয়েছে। এতে রাষ্ট্র প্রধানকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, পরামর্শের কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছলে পরে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে কাজ করে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের মূল প্রশ্নের কোনো জবাব তা থেকে পাওয়া যাচ্ছেনা। হাদীস থেকেও তার নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত কোনো জবাব পওয়া যায়না। অবশ্য খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা ধেকে ইসলামী আইনজ্ঞাগণ সাধারণভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, রাষ্ট্র প্রধানই গোটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জিম্মাদার এবং পরামর্শ সভার সাথে তিনি পরামর্শ করতে বাধ্য বটে, কিন্তু এর সংখ্যাগুরু বা সংখ্যালঘুর কিংবা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাষ্ট্র প্রধান [সবসময় বাধ্য নন। অন্য কথায়, রাষ্ট্র প্রধানকে ‘ভেটো’ প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছে।
কিন্তু এই মতটির সংক্ষিপ্ততা ও অস্পষ্টতার জন্য ভুল বুঝাবুঝির কারণ হতে পারে। কেননা লোকেরা এই মত বর্তমান পরিবেশে বেখে হৃদয়ংগম করতে চেষ্টা করে এবং সেই পরিবেশ তাদের সামনে নেই যে পরিবেশ [খোলাফায়ে রাশদীনের যুগ] থেকে এই মত গ্রহণ করা হয়েছে। খিলাফতে রাশেদার যুগে যাদেরকে “ আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ” বা পরামর্শ সভার সদস্য নির্দিষ্ট করা হতো, তার ভিন্ন ভিন্ন দলের আকারে সংগঠিত ছিলোনা। কর্তমান যুগের আইন পরিষদসমূহ যেসব পার্লামেন্টারী নিয়ম কানুনে শক্ত করে বাঁধা হয়ে থাকে, সেকালের পরামর্শ সভা সেরূপ ছিলোনা। তারা প্রথমে আলাদা আলাদা ভাবে নীতি নির্ধারণ করে, কার্যসূচী নির্দিষ্ট করে এবং পার্টি মির্টিং- এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টে আসতোনা। পরামর্শের জন্য যখন তাদেরকে আহ্বান করা হতো তখন তারা সম্পূর্ণ উন্মুক্ত মনে পরামর্শেস্থলে এসে বসতো। খলীফা স্বয়ং তাদের মজলিসে উপস্থিত থাকতেন। আলোচ্য বিষয় তথায় পেশ করা হতো, সপক্ষে এবং বিপক্ষে সকল দিক দিয়েই স্বাধীনভাবে আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হতে পারতো। তারপর উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণ তুলনা করে খলীফা নিজের প্রমাণসহ নিজ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করতেন। খলীফার এই মত সাধারণত এমন হতো যে, তা সমগ্র মজলিসই সমর্থন করতো। কোনো কোনো সময় কিছু সংখ্যক সমস্য খলীফার সাথে দ্বিমত পোষণ করতো কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ ভূল বা “সমর্থন অযোগ্য” মনে করতোনা, বরং তাকে অপেক্ষিকভাবে কম অগ্রাধিকারযোগ্য বলে মনে করতো এবং ফায়সালা হয়ে যাওয়ার পর অন্তত তা মেনে নিতো। পরামর্শ সভায় পরামর্শ দাতাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে এবং কখনও এমন মতবিরোধের সৃষ্টি হয়নি যে, কতোজন কোন্ মতের পক্ষে তা গণনা করে দেখার প্রয়োজন হতো। পক্ষান্তুরে খলীফা পরামর্শ সভার প্রায় সম্মিলিত ঐক্যমতের বিরুদ্ধে কাজ করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, খিলাফতে রাশেদার ইতিহাসে তদ্রূপ ঘটনা মাত্র দুইবার ঘটেছিলো্ একবার উসামা বাহিনী প্রেরণের ব্যাপারে এবং দ্বিতীয়বার মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ব্যাপারে। কিন্তু উভয় ঘটনায় সাহাবায়ে কিরাম খলীফার সিদ্ধান্ত শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। তা এই কারণে নয় যে, ইসলামী সংবিধান খলীফাকে ‘ভেটো’ প্রয়োগ ক্ষমতা করার দিয়ে রেখেছিলো এবং সাংবিধানিকভাবে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা খলীফার সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য ছিলেন। বরং তার প্রকৃত কারণ এই ছিলো যে, খলীফা হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর রাজনীতি জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও অন্তদৃষ্টির প্রতি সাহাবায়ে কিরামের পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান ছিলো। তারা যখন দেখলেন, হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার নিজের মতের যথার্থতা সম্পর্কে এতোটা দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং দীন ইসলামের কল্যাণ দৃষ্টিতেই এই মতের প্রতি তিনি এতো বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তখন তাঁরা উদার চিত্ত মতের সপক্ষে নিজেদের মত প্রত্যাহার করলেন। বরং পরে তাঁরা তাঁর মতের সত্যতা ও সুষ্ঠতার প্রকাশ্যভাবে প্রশংসা পর্যন্ত করেছিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারও করেছিলেন যে, এই সংকট মুহূর্তে হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যিনি হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতের সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠভাবে বিরোধিতা করেছিলেন, উদত্ত কন্ঠে বলে বেড়াতেন, আল্লাহ্ তায়ালা আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হৃদয়কে এই কাজের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন এবং আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, হযতর আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ফায়সালাই ছিলো পথার্থ।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে আপনার অনুমান করতে পারেন যে, ইসলামে “ভেটো”র এই ধারণা মূলত কোন পরিবেশের নজির থেকে সৃষ্টি হয়েছে? শূরার কর্মনীতি ও তার অন্তর্নিহিত ভারধারা এবং শূরা সদস্যদের মনোবৃত্তি ও স্বভাব প্রকৃতি খিলাফতে রাশেদার অনুরূপ হলে উক্তরূপ কর্মনীতি অপিক্ষা উত্তম ও উন্নত কর্মপন্থা আর কিছুই হতে পারেনা। এই কর্মপন্থাকে যদি তার অনিবার্য পরিণতি ও শেষ মনযিল পর্যন্ত আমরা নিয়ে যেতে পারি, তবে খুব বেশী বললেও এতোটুকু বলা যায় যে, এই ধরনের মজলিসে শূরার রাষ্ট্র প্রধান ও পরিষদ সদস্যগণ যদি নিজ মত অন্যের সপক্ষে প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত না হয় বরং নিজের উপর জিদ ধরে বসে, তবে তখন গণভোট [Referendum] গহণ করা যাবে। তারপর যার মতকে জনমত বাতিল করে দিবে তাকে ইস্তফা দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে সেরূপ মনোবৃত্তি ও অভ্যন্তরীন ভাবধারা সৃষ্টি করতে এবং সে ধরনের মজলিসে শূরা গঠন করা যতোদিন না সম্ভব হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত শাসন বিভাগেকে আইন পরিষদের সংখ্যাগুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় নেই।
৪. রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য
এখন আমরা আলোচনা করে দেখবো যে, ইসলাম কোন্সব মৌলিক উদ্দেশ্য [Objective] পেশ করে, যার জন্য একটি ইসলামী রাষ্ট্রকে কাজ করতে হবে। কুরআন মজীদ ও সুন্নতে রসূলে এই উদ্দেশ্যসমূহের যে বিশ্লেষণ করা হয়েছে তা এইঃ
কুরআন আমার রসুলদেরকে উজ্জ্বল দলীল প্রমাণ সহকারে পঠিয়িছি এবং তাদের সংগে কিতাব ও ‘মীযান’ নাযিল করেছি, যেনো মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর কায়েম হতে পারে।” [সূরা হাদীদঃ ২৫]
অন্যত্র বলা হয়েছেঃ
“যেসব মুসলমানকে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমতি দেয়া হচ্ছে তাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখবে।” [সূরা হজ্জঃ ৪১]
“আল্লাহ্ তায়ালা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সাহায্যে এমন কাজের পথ রুদ্ধ করেন যা কুরআনের দ্বারা বন্ধ করেননা।” [তফসীরে ইবনে কাছীর]
অর্থাৎ যেসব অনাচার ও পাপাচার কেবল কুরআনে উপদেশ ও যুক্তির দ্বারা দুরীভূত হয়না, সেগুলো নির্মূল করার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োজন।
এ থেকে জানা গেলো যে, মানবতার কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে ইসলাম যেসব সংস্কারমূলক কর্মসূচী পেশ করেছে, রাষ্ট্রের সমগ্র উপায় উপকরণের সাহায্যে তা বাস্তবায়িত করাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা, জাতীয় সীমান্ত রক্ষা এবং জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নত করাই রাষ্ট্রের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম মানবতাকে যেসব কল্যাণকর ব্যবস্থয় সুসজ্জিত ও সমৃদ্ধ করে তুলেতে চায় সেগুলোর উন্নত আর যেসব পাপাচার থেকে পবিত্র করতে চায় সেগুলো নির্মূল, নিস্তেজ ও দূর্বল করতে সকল শক্তি নিয়োজিত করাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই ইসলামী রাষ্ট্রকে অমুসলিম রাষ্ট্র থেকে স্বতন্ত্র ও পৃথক করে দেয়।
৫. সরকার কিভাবে গঠিত হবে
এই মৌলিক বিষয়গুলোর বিশ্লেষণের পর আমাদের সম্মুখে পঞ্চম প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়। সেটি হলো, উপরোল্লিকিত মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার জন্য সরকার কিভাবে সম্পন হবে? এ প্রসংগে রাষ্ট্র প্রধানের [Head of the State] ইসলামী পরিভাষায় যাকে ইমাম, আমীর বা খলীফা বলা হয় নিয়োগের ব্যাপারটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে ইসলামের নীতি হৃদয়ংগম করার জন্য ইসলামের প্রাথমিককালের ইতিহাস পর্যালোচনা করা আমাদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
রাষ্ট্র প্রধানের নির্বচন
যেমন আপনার সকলেই জানেন, আমাদের বর্তমান ইসলামী সমাজের সূচনা মক্কার কুফরী পরিবেশে হয়েছিলো এবং এই প্রতিকূল পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে ইসলামী সমাজের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠাকারী ছিলেন আমাদর নেতা ও পথপ্রদর্শক মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই ইসলামী সমাজ যখন তার সংগঠন ও রাজনৈতিক স্বাধীকারের দিক থেকে উন্নতি লাভ করে একটি রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করার মঞ্জিল পর্যন্ত পৌছে গেলো, তখন তার প্রথম ‘রাষ্ট্রপ্রধান’ ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই ছিলেন এবং তিনি কারো দ্বারা নির্বাচিত ছিলেননা বরং সরাসরি আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছিলেন।
দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথ রূপে পালন করার পর তার শ্রেষ্ঠতম বন্ধুর [আল্লাহ্] সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু তাঁর স্থালভিষিক্ত নির্বাচন সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট, নিশ্চিত ও নির্দিষ্ট কোনো নির্দেশ দিয়ে যাননি। তাঁর এই নীরবতা এবং কুরআন মজীদের বাণী “তাদের সামগ্রিক ব্যাপরসমূহে পারস্পরিক পরামর্শে সম্পন্ন” এর আলোকে সাহাবায়ে কিরাম বুঝতে পারলেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগের দায়িত্ব মুসলমানদের নিজস্ব নির্বাচনের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং এই নির্বাচন মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতেই সম্পন্ন হওয়া বাঞ্চনীয়। ১{সন্দেহ নাই যে, মুসলমানদের মধ্যে শীয় মতাবলস্বীগণ মনে করেন যে, নবীদের ন্যায় ইসলামী সমাজের নেতৃত্ব পদে নিযুক্তিও আল্লাহ্র তরফ থেকেই হয়ে থাকে। কিন্তু এই মতবিরোধ পর তার পুনরাবির্ভাব পর্যন্ত ইমামের পদ যেহেতু শূন্য রয়েছে, তাই বর্তমানে মুসলমানদের সামগ্রিক ব্যাপারসমূহ একজন আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত নয় এমন ব্যক্তির হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত।}
জনসম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। অতপর তাঁর অস্তিম সময় যখন উপস্থিত হলো, তখন তাঁর দৃষ্টিতে খিলাফতের জন্য সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম ব্যক্তি যদিও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্থালাভিষিক্তের নাম তিনি নিজে প্রস্তাব করলেননা, তিনি প্রবীণ ও বিশিষ্ট সাহাবাদের পৃথক প্রথকভাবে ডেকে প্রত্যেকের মত অবগত হলেন। তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সপক্ষে তাঁর নিজের শেষ উপদেশ লেখালেন। অতপর রোগাক্রন্ত অবস্থায়ই তিনি তাঁর ঘরের দরজায় উপস্থিত সকল মুসলমানদের সম্মেলনকে সম্বোধন করে বললেনঃ
“জনমন্ডলি! আমি যাকে আমার স্থালাভিষিক্ত মনোনীত করবো তোমরা কি তাকে সমর্থন করবে? আল্লাহ্র শপথ! চিন্তা ও গবেষণা করে মত নির্ধারণে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি। আমি আমার কোনা আত্মীয় ব্যক্তিকেও নিযুক্ত করছিনা। আমি ওমর ইবনুল খাত্তাবকেই স্থালাভিষিক্ত নিযুক্ত করছি। অতএব তোমরা তাঁর কথা শুনো ও মেনে চলো।”
বিরাট জনসম্মেলন থেকে আওয়াজ উঠলঃ
আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। [তাবারী, ২য় খন্ড, পৃঃ ৬১৮, মাতবায়াল ইসতিকামাহ, মিশর]
এভাবে মুসলমানদের দ্বিতীয় খলীফা নিয়োগ কার্যও মনোনয়নের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি বরং তদানীন্তন খলীফা মুসলমানদের সাথে পরামর্শ করে এক ব্যক্তির নাম প্রস্তাব করেন এবং সমবেত জনগণের সম্মুখে তা পেশ করে মঞ্জুর করিয়ে নেন।
অতপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর অন্তিমকাল উপস্থিত হয়। তখন নবী করমী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্বাধিক বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সাহাবীগণের ছয়জন সাহাবী এমন ছিলেন, খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণের ব্যাপারে যাদের উপর মুসলমানদের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হতে পারে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই ছয়জনের সমন্বয়ে একটি মজলিসে শূরা গঠন করেন এবং পারস্পরিক পরামর্শক্রমে একজনকে খলীফা নিযুক্ত করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করেন। সেই সংগে তিনি ঘোষণা করলেনঃ
“তোমাদের মধ্যে যে কেই মুসলমানেদের সাথে পরামর্শ না করেই জোরপূর্বক রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে বসবে, তোমরা তাকে হত্যা করো।” [মুহাম্মদ হুসায়ন হায়কালঃ আল-ফারুক ওমর, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩১৩]
এই মজলিস খলীফা নির্বাচনের কাজ শেষ পর্যন্ত হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর অর্পন করেন। তিনি মদীনার অলিগলি ঘুরে জনগণের মতামত জেনেছেন, বাড়ী বাড়ী গিয়ে পুরাবাসিনীদের নিকট পর্যন্ত এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রদের মতামতও জানতে চেষ্টা করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হজ্জে আগত লোক-যারা মদীনা থেকে নিজ নিজ দেশে রওনা করছিলো তাদের মতও অবগত হন। এরূপ অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানের পর তিনি নিঃসন্দেহে জানতে পারলেন যে, গোটা জাতির সর্বাধিক আস্থাভাজন ব্যক্তি বর্তমানে দুইজন। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং এদের মধ্যে হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর দিকে আবার অধিক সংখ্যক লোকের ঝোঁক রয়েছে। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সপক্ষেই এই গণমতের ভিত্তিতে অবশেষে ফায়সালা হলো এবং প্রকাশ্য সম্মেলনে তার হাতে ‘বায়াত’ [আনুগত্যের শপথ] গ্রহণ করা হয়।
অতপর হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাতের হৃদয়বিধারক ঘটনা ঘটে। ফলে মিল্লাতে ইসলামিয়ার মধ্যে চরম নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। এই সময় কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ঘরে একত্রিত হন এবং তাঁকে বলেনঃ এই সংকট মুহূর্তে উম্মতের নেতৃত্বের যোগ্যতম ব্যক্তি আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। অতএব আপনি এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করুন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, যদিও তা অস্বীকার করলেন গ্রহণ করতে, কিন্তু তাঁরা তাঁকে বাববার অনুরোধ করতে লাগলেন।
তখন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন- “আপনারা যদি বাস্তবিকই তা চান তবে মসজিদে চলুনঃ
“কারণ আমার আনুগত্যের শপথ [বায়াত] গোপনে অনুষ্ঠিত হতে পারেনা এবং মুসলিম জনসাধারণের সম্মতি ব্যতীত তা সম্পন্নও হতে পারেনা।” [তাবারী ৩য় খন্ড, পৃঃ ৪৫০]
অতপর তারা মসজিদে নববীতে চলে গেলেন। আনসার ও মুহাজিরগণ তথায় সমবেত হলেন। আর সকলের না হলেও অন্তত অধিকাংশ লোকের সমর্থনে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা নির্বাচিত হন এবং তাঁর বায়াত’ গ্রহণ করা হয়।
অতপর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর যখন ঘাতকের আক্রমণ হয় এবং তিনি মুমূর্ষ অবস্থায় উপনীত হন, তখন জনগণ তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করলো, আপনার পরে আমরা আপনার পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকেই কি খলীফা নিযুক্ত করবো এবং তাঁর হাতেই কি বায়াত’ করবো? উত্তরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, শুধু এ টুকুই বলেছিলেনঃ
“আমি এজন্য তোমাদের কোনো হুকুম দিচ্ছিনা, কোনো কিছু করতে তোমাদেরকে নিষেধও করছিনা। তোমরা নিজেরা খুব ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে পারো।” [তাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ১১২]
এই হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের ব্যাপারে খিলাফতে রাশেদার কার্যক্রম এবং সাহাবায়ে কিরামের সর্বসম্মতিমূলক কর্মপন্থা। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নীরবতা এবং “তাদের সামগ্রিক ব্যাপারে তাদের পারস্পরিক পরামর্শক্রমেই আঞ্জাম পেয়ে থাকে”- আল্লাহর এই বাণীর উপর তাদের কর্মনীতির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই নির্ভরযোগ্য সাংবিদানিক ঐতিহ্য থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচন সাধারণ লোকদের সম্মতির উপর নির্ভারশীল। কোনো ব্যক্তিরই জোরপূর্বক রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার অধিকার নাই। [ কোনো কোনো লোকের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে, ইসলামের প্রকৃত নিয়ম যদি তাই হবে, তাহলে রাজতন্ত্রের যুগে নাম করা আলেমগণ জোরপূর্বক রাজ তখত দখলকারী লোকদের খিলাফত ও নেতৃত্ব কিরূপে স্বীকার করে নিলেন? উত্তরে বলা যায় যে, মূলত, এখানে দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিষয়কে পরস্পর তালগোল পাকিয়ে ফেলার কারণে গোলক ধাঁধাঁর সৃষ্টি হয়েছে। একটি বিষয় তো এই যে, ইসলামে খলীফা বা শাসনকর্তা নির্বাচনের সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পন্থা কি? আর একটি এই যে, কখনো ভ্রান্ত পন্থায় কোনো ব্যক্তি যদি খিলাফতের গদী দখল করে বসে তবে তখন কি করা উচিত? প্রথম বিষয়ে আলেমগণের সর্বসম্মত উত্তর এই যে, মুসলিম জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনই হচ্ছে সঠিক কর্মনীতি।
দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, এরূপ পরিস্থিতিতে যেসব আলেম অধিকতর নরমপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তারাও শুধু এতোটুকুই বলেছেন যে, শান্তি শৃংখলা এবং মুসলমানদের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার খাতিরেই এরূপ খলীফাকে বরদাশত করে নিতে হবে। কিন্তু সতর্কতার সাথে রক্ষ্য রাখতে হবে যে, এরূপ জোরপূর্বক শাসন দখলকারী ব্যক্তি দীন ইসলামের মূলবিধান ও ভিত্তিকে যেনো বিগড়ে দিতে না পারে। এরূপ পরিস্থিতিতেও উক্ত শর্ত যদি বহাল পাওয়া যায়, তবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উত্তোলন করা তারা পছন্দ করেননা। কারণ তা করলে সমগ্র দেশে বিচ্ছিন্নতা, অশান্তি ও বিপর্যয় দেখা দিবে। এ কথার অর্থ কখনো এই নয় যে, যারা উপরোক্ত মত পোষণ করতেন তারাও জোরপূর্বক গদি দখল করাকে সুষ্ঠু ইসলামী পন্থা বলে মনে করতেন।] বিশেষ কোনো পরিবার কিংবা শ্রেণীরও এর উপর একচেটিয়া আধিপত্য নাই। [ এই প্রসংগেও কতিপয় লোক সংশয় সৃষ্টি করে যে, তাহলে যেসব হাদীসে কুরাইশদেরকে খিলাফতের অধিক হকদার বলা হয়েছে তার অর্থ কি? এর উত্তর আমরা রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থে পেশ করেছি।] উপরন্তু এই নির্বাচন হবে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, জবরদস্তিমুক্ত এবং মুসলমানদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশের মাধ্যমে। কিন্তু মুসলমানদের স্বাধীন মনোভাব কিভাবে বা কি উপায়ে জানা যাবে? এই ব্যাপারে ইসলাম নির্দিষ্ট ও বাঁধাধরা কোনো পন্থা ঠিক করে দেয়নি। অবস্থা ও প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু বিশেষ শর্ত এই যে, যে পন্থাই গ্রহণ করা হোক- সমগ্র জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তি কে? তা যেনো সেপন্থা দ্বারা সন্দেহাতীতরূপে জানতে পারা যায়।
মজলিসে শূরার গঠন
রাষ্ট্র প্রধান নির্বাচনের পর মজলিসে শূরা বা পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন আমাদের সম্মুখে অধিকতর জটিল বিষয়। এই মজলিস কিভাবে গঠিত হবে, এর সদস্য কিভাবে নির্ধারণ করা হবে এবং কারাইবা তাদেকরকে নির্বাচিত করবে?
যৎসামান্য অধ্যয়নের ভিত্তিতে লোকেরা এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণার শিকার হয়েছে যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে যেহেতু সাধারণ নির্বাচনের [General Election] মাধ্যমে শূরা সদস্যগণ নির্বাচিত হতেননা, তাই ইসলামে জনমত জানবার জন্য মূলতই কোনো পন্থা বিদ্যামান নেই, বরং সমসাময়িক খলীফার বুদ্ধিবিবেচনার উপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়েছে যে, সে নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো লোকের সাথে পরামর্শ করতে পারে। মূলত সেকালের, বিষয়কে একালের পরিবেশে রেখে বুঝার চেষ্টার কারণে এই ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ সেকালের প্রত্যেকটি কথাকে সেকালের পরিবেশে রেখে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তার বাস্তব খুঁটিনাটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সেই নীতিসমূহ হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করতে হবে।
ইসলাম মক্কা মুয়াজ্জামায় একটি আন্দোলন হিসেবেই উত্থিত হয়েছিলো। দুনিয়ার আন্দোলনসমূহের একটি প্রকৃতি এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, সর্বপ্রথম যারাই এই আন্দোলনে যোগদান করেন, আন্দোলনের অগ্রনায়কের তারাই হয় বন্ধু, সংগী, সহকারী, পরামর্শদাতা এবং সাহায্যকারী। তাই যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা অতি স্বাভাবিকভাবেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধু ও পরামর্শদাতা হয়েছিলেন। আল্লাহর নিকট হতে যেসব ব্যাপারে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নাযিল হতোনা, তিনি সেসব বিষয়ে তাঁদের সাথে পরামর্শ করতেন। উত্তরকালে এই আন্দোলনে যখন নতুন নতুন লোক যোগদান করতে লাগলো এবং বিরোধী শক্তিসমূহের সাথে তার দ্বন্দ্ব, সংঘাত ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠলো, তখন যেসব লোক নিজদের ঐকান্তিক নিষ্ঠাপূর্ণ খিদমত, আত্মদান, অনাবিল জ্ঞানবুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির দিক দিয়ে গোটা জামায়াতের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন তারা ভোটে নির্বাচিত হননি। বরং বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমেই তারা নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রথমত, যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন সাবিকুনাল আউয়ালুন। দ্বিতীয়ত, পরবর্তীকালে যেসব পরীক্ষিত সাহাবী জামায়াতের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছেন এই উভয় শ্রেণীর সাহাবীগণের উপর ঠিক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতোই সর্বসাধারণ মুসলমানের আস্থা ছিলো।
এরপর হিজরতের বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়। হিজরতের সূচনা এভাবে হয় যে, দেড়-দুই বছর পুর্বে মদীনার কয়েকজন প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় আওস ও খাজরাজ গোত্রদ্বয়ের ঘরে ঘরে ইসলামের বিপ্লবী বাণী পৌছে গিয়েছিলো। এদেরই আহ্বানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য মুহাজির নিজ নিজ ঘরবাড়ী ত্যাগ করে মদীনায় চলে যান এবং সেখানে ইসলামের এই আন্দোলন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং একটি রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। যাদের প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় ইতোপূর্বে মদীনায় ইসলাম প্রসারিত হয়েছিলো, এই নতুন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতি স্বাভাবিকভাবে তাঁরাই স্থানীয় নেতা হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। তারাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে শূরায় সর্বাগ্রে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবা এবং পরীক্ষিত মুহাজিরদের সংগে তৃতীয় দল হিসেবে শামিল হওয়ার অধিকারী হয়েছিলেন। বস্তুত পক্ষে তারাও অতি স্বাভাবিক নির্বাচন পদ্ধতিতেই নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা এতোদূর আস্থাভাজন ছিলেন যে, তখন আজকালকার আধুনিক পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও এসব লোকই নির্বাচিত হতেন।
অতপর মদীনার সমাজে দুইশ্রেণীর লোক আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। প্রথমতঃ যারা দীর্ঘ আট দশ বছর কালের রাজনৈতিক সামরিক ও প্রচারগত কঠিন কার্যসমূহ আঞ্জাম দিয়েয়েন তাঁরা। প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাদের প্রতিই লোকদের দৃষ্টি পতিত হতে লাগলো। দ্বিতীয়ঃ যারা কুরআন মজীদের জ্ঞান ও দীন ইসলামের সুক্ষ্ম জ্ঞানের দিক দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ফলে দীন ইসলামের তথ্য ও তত্ত্বজ্ঞানের দিক দিয়ে জনগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে তাদেরকেই অগ্রগণ্য ও নির্ভরযোগ্য মনে করতো। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জীবদ্দশায় এসব সাহাবীর নিকট কুরআন শিখবার এবং বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণ করার সাধারণ নির্দেশ দিয়ে তাদের যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততাকে অধিকতর বলিষ্ঠ করেছিলেন। এই দুই প্রকারের লোকও অতি স্বাভাবিক নির্বাচনের নিয়মে মজলিসে শূরায় স্থানে লাভ করেছিলেন। তাদের মধ্যে কাউকে সদস্য হিসেবে গ্রহণ করার জন্য ভোট গ্রহণের কোনো প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। আর ভোট যদি বাস্তবিকই লওয়া হতো, ইসলামী সমাজের সমগ্র জনতার প্রথম দৃষ্টি যে তাদের উপরই পড়তো, তাতো কোনো সন্দেহ নেই।
এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে মজলিসে শূরা গঠিত হয়েছিলো, উত্তরকালে তাই খোলাফায়ে রাশেদীনেরও মন্ত্রণা পরিষদ বলে বিবেচিত হলো। ফলে এই নিয়মটি একটি সাংবিধানিক ঐতিহ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং পরবর্তীকালে এমন সব লোক এই নিয়ম অনুসারে মজলিসে শূরায় প্রবেশ করতে থাকেন যারা নিজেদের অবদান এবং উচ্চতর নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করে এই মজলিসে নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। এই লোকদেরকেই আরবী পরিভাষায় “আহলুল হাল্লি ওয়াল আকদ” [বন্ধনকারী ও বন্ধন মুক্তকারী] বলা হতো। তাদের সাথে পরামর্শ না করে খোলাফায়ে রাশেদীন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেননা। তাদের প্রকৃত মর্যাদা একটি ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাতের ঘটনার পর কয়েকজন সাহাবী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সমীপে উপস্থিত হয়ে তাঁকে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেনঃ
“এটা তোমাদের ফায়সালা করার বিষয় নয়, শূরার সদস্য এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণের কাজ। বস্তুত শূরার সদস্য এবং বদরযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীগণ যাকে মনোনীত করবেন, তিনিই খলীফা হবেন। অতএব এখন আমরা সমবেত হবো এবং এই বিষয়ে বিবেচনা করবো।” [ইবনে কুতায়বা, আল-ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ, পৃঃ ৪১]
একথা পরিষ্কার জানা যায় যে, “মজলিসে শূরার সদস্য সে যুগে কিছু নির্দিষ্ট লোক ছিলেন, যারা পূর্ব থেকেই এই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছিলেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহের চূড়ান্ত মীমাংসা করার ভার তাঁদের উপরই ন্যস্ত ছিলো। কাজেই খলীফা পরামর্শ গ্রহণে বাধ্য ছিলেননা- ইচ্ছা হলে কারো সাথে পরামর্শ করতেন নাহলে নাই করতেন, আর করলেও জাতির গুরুতর বিষয়সমূহের চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী কারা ছিলো তা মোটেই জানা যেতোনা- একথা কিছুতেই বলা যায়না। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উক্ত বাণী থেকেই এরূপ কথার ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়েছে। [এখানে আরো একটি প্রশ্ন জাগে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের সময় কেবল মদীনার লোকগণই কেন শূরার সদস্য হতেন এবং অন্যান্য এলাকা হতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি আহবান করা হয়নি কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, তা না করার মূলে দুইটি অত্যন্ত যুক্তিসংগত কারণ বিদ্যমান ছিলোঃ
প্রথম কারণ এই যে, আরব দেশের এই ইসলামী রাষ্ট্র কোন জাতীয় রাষ্ট্র ছিলোনা, তা সম্পূর্ণ আলাদা পন্থায় অস্তিত্ব লাভ করেছিলো। প্রথমে একটি মতাদর্শের ব্যাপক প্রচার লোকদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলো। এই বিপ্লবের অনিবার্য পরিণতিতে একটি আইননুগ সমাজ দানা বেঁধে উঠেছিলো, তারপর এই সমাজ একটি আইনানুগ রাষ্ট্রের রূপ পরিগ্রহ করে। এই প্রকারের রাষ্ট্রে স্বভাবত কেন্দ্রীয় অস্থাভাজন ব্যক্তি তিনিই ছিলেন যিনি এই বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন। তার পরে সেইসব লোকই এই বিপ্লবী সমাজের কেন্দ্রীয় আস্থাভাজন ব্যক্তি হয়েছিলেন, যারা এই বিপ্লব সৃষ্টিকারীর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। তাদের নেতৃত্বে ছিলো একটি স্বাভাবিক এবং যুক্তিসংগত নেতৃত্ব এবং এই সমাজে তাদের ছাড়া অন্য কেউই জনগণের আস্থাভাজন হতে পারতোনা। ইসলামী সমাজে সমালোচনার অবাধ অধিকার ও পূর্ণ সুযোগ থাকা স্বত্ত্বেও কেবল এই কারণেই তাঁদের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এবং “কেবল মদীনার লোকেরই কেন পরামর্শদানের অধিকার ভোগ করছে” বলে টু শব্দটিও সেকালের সারা আরব দেশের কোথাও ধ্বনিত হয়নি।
দ্বিতীয় কথা এইযে, সেকালের তামাদ্দুনিক অবস্থায় আফকানিস্তান থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট রাজ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া মোটেও সম্ভবপর ছিলোনা। এবং মজলিসে শূরার প্রত্যেক আঞ্চলিক সদস্যের পক্ষে সাধারণ এবং জরুরী অধিবেশসসমূহে এসে যোগদান করাও অসম্ভব ছিলো। ] খিলাফতে রাশেদার এই কার্যক্রম, বরং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই জীবনাদর্শ থেকে যে মূলনীতি নির্গত হয় তা এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অবশ্যই পরামর্শ করবেন, কিন্তু সেই পরামর্শ যার তার কিংবা নিজের খেয়ালখুশি মতো মনোনীত লোকদের সাথে করবেন, যাদের স্বার্থহীনতা, নিষ্ঠাপূর্ণ কল্যাণ কামিতা এবং যোগ্যতা সম্পর্কে জনগণ নিশ্চিন্ত, রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তসমূহে যাদের অংশ গ্রহণ এই বিষয়ের গ্যারান্টি যে, ঐ সিদ্ধন্তের পেছনে গোটা জাতির সমর্থন আছে বলে প্রমাণ করে। আর জনগণের আস্থাভাজন লোক কে কে, তা জানার যে উপায় ইসলামের প্রথম যুগে তখনকার বিশেষ পরিস্থিতিতে কার্যকরী ছিলো, আজ তা কোথাও পাওয়া যেতে পারেনা। আর সেকালের তামুদ্দুনিক অবস্থায় যেসব প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা ছিলো তাও আজ বর্তমান নেই। কাজেই বর্তমান যুগের অবস্থার দৃষ্টিতে ও আজকের প্রয়োজন মুতাবিক জাতির আস্থাভাজন ব্যক্তিদেরকে সঠিকভাবে নির্বাচিত করার জন্য আধুনিককালের উদ্ভাবিত সংগত ও নির্দোষ পন্থাসমূহও গ্রহণ করা যেতে পারে। বর্তমান যুগের নির্বাচন পদ্ধতিও এই সংগত পন্থাসমূহের অন্যতম। এই পন্থাও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু যেসব দুর্নীতি ও অসদুপায় অবলম্বনের অবাধ সুযোগ গণতন্ত্রকে একটি বিদ্রূপে পরিণত করেছে, সেসব কলংকময় ও অবাঞ্ছিত পন্থা কিছুতেই বরদাশত করা যেতে পারেনা।
সরকারের কাঠামো ও তার ধরন
অতপর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে সরকারের কাঠামো ও ধরন কি রূপ? এই প্রসংগে খিলাফতে রাশেদার যুগের প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করলে আমরা সুস্পষ্টরূপে জানতে পারি যে, ঐ যুগে আমীরুল মুমিনীন [ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি] ছিলেন সে মূল ব্যক্তি যার নিকট নির্দেশ শোনার ও আনুগত্য করার শপথ গ্রহণ করা হতো এবং যাকে আস্থাভাজন ব্যক্তি নে করে জনসাধারণ তাদের সামগ্রিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহ, অর্থাৎ সরকার পরিচালনার সর্বময় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব তার উপর ন্যস্ত করতো। আমীরুল মুমিনীনের মর্যাদা ইংলন্ডের রাজা ও প্রধানমন্ত্রী, ফ্রান্স ও আমেরিকার রাষ্ট্রপতি এবং রাশিয়ার ষ্ট্যালিন প্রমুখের মর্যাদা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলো। তিনি নিছক রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেননা বরং মন্ত্রীপরিষদের প্রধানও তিনিই ছিলেন। তিনি সশরীরে মজলিসে শূরায়ও উপস্থিত হতেন এবং সভাপতিত্বও করতেন। প্রত্যেক আলোচনায়ও তিনি সরাসরি অংশগ্রহণ করতেন, নিজ সরকারের সকল কাজের জবাবদিহি করতেন এবং নিজের দায়দায়িত্বের হিসেব নিজেই পেশ করতেন। তাঁর পার্লামেন্টে না ছিলো ‘সরকারী দল’ আর না ছিলো ‘বিরোধী দল’[। তিনি সত্যের অনুগামী হলে গোটা পার্লামেন্ট [শূরা] তার দল হিসেবেই কাজ করতো। আবার সমগ্র পার্লামেন্ট তার বিরোধী হয়ে যেতো, যদি তাকে ভুল বা বাতিল পথে অগ্রসর হতে দেখা যেতো। পার্লামেন্টের প্রত্যেক সদস্যই ছিলো স্বাধীন, যে বিষয়ে তার মতৈক্য হতো তা প্রকাশ্যভাবে সমর্থন করতেন, আবার যে ব্যাপারে তার মতবিরোধ হতো প্রকাশ্যভাবে তার বিরোধীতা করতেন। খলীফার নিজের মন্ত্রীসভা পর্যন্ত পার্লামেন্টে তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে পারতেন। তারপরও ‘রাষ্ট্রপতিত্ব’ এবং মন্ত্রীত্বের মধ্যে পূর্ণ বিশ্বস্ততা ও সহযোগিতা বিদ্যমান থাকতো এবং কোনো পক্ষেরই ইস্তফা দেয়ার প্রশ্নই উঠতোনা। খলীফা কেবল পার্লামেন্টের নিকট দায়ী ছিলেননা, সমগ্র জাতির সামনেই তিনি প্রত্যেক কাজের, এমন কি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কেও জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন। তিনি দিনরাত পাঁচটি সময় মসজিদে জনগণের সম্মুখীন হতেন, প্রত্যেক জুময়ার দিন তিনি জনগণের সম্মুখে বক্তৃতা দিতেন। জনসাধারণ তাদের শহরের অলি গলিতে প্রত্যেক দিন তাঁকে চলাফেরা করতো এবং দেখতো এবং যে কোনো ব্যাপারে কৈফিয়ত তলব করতে বা সমালোচনা করতে পারতো। প্রত্যেক নাগরিকিই যে কোনো সময় তার পরিধেয় টেনে ধরে নিজের প্রাপ্য দাবী করতে পারতো। তার নিকট কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হলে সেখানে বর্তমান কালের ধরাবান্ধা নিয়ম অনুযায়ী পার্লামেন্টারী প্রথায় করার প্রয়োজন হতোনা। তাঁর সাধারণ ঘোষণা ছিলো:
“আমি যদি সঠিক কাজ করি তবে তোমরা আমার সাহায্য করো। আর আমি যদি অসদাচরণ করি তবে তোমরা আমাকে “সোজা” করে দিবে। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের অনুসরণ করতে থাকবো, তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে। আর আমি যদি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নাফরমানী করি, তবে আমার আনুগত্য করা তোমাদের মোটেই কর্তব্র হবেনা।” [মুহাম্মদ হুসাইন হায়কাল, আবুবকর আস-সিদ্দীক, পৃঃ ৬৭]
এরূপ সরকার প্রণালীর সাথে বর্তমান যুগের অসংখ্য রাজনৈতিক পরিভাষার মধ্যে একটি পরিভাষারও সামঞ্জস্য না হলেও এই ধরনের শাসন পদ্ধতির সাথে ইসলামের পূর্ণ সামঞ্জস্য রয়েছে। অতএব এটাই আমাদের আদর্শ নমুনা। কিন্তু এ ব্যবস্থা ঠিক তখন খাপ খেতে পারে, যখন গোটা সমাজ ইসলামের বিপ্লবী দৃষ্টিভংগি অনুসারে পূর্ণরূপে প্রস্তুত হবে। তাই মুসলিম সমাজের যখনই পতন শুরু হয়েছে তখন এরূপ সরকার পদ্ধতির সাথে তাঁর সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে গেলো। এখনো আমরা যদি এই আদর্শ নমুনার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে চাই, তবে প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে তা থেকে চারটি মূলনীতি আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে এবং তা বাস্তবায়িত করতে চেষ্টানুবর্তী হতে হবে।
১. সরকারের প্রকৃত দায়িত্ব যার উপরইন ন্যস্ত করা হবে, তিনি কেবল গণপ্রতিনিধিদেরিই নয় বরং জনগণের সম্মুখীন হতেও বাধ্য থাকবেন এবং নিজের যাবতীয় কাজর্ম শুধু পরামর্শের ভিত্তিতেই চলবেনা বরং নিজের কর্মকর্তাদের জন্যও তাকে জবাবদিহি করতে হবে।
২. বর্তমানে প্রচলিত দলীয় পদ্ধতি থেকে মুক্ত হতে হবে। কারণ এটা গোটা সরকার ব্যবস্থাকেই গোঁড়ামি ও দলীয় কোন্দলে জর্জরিত করে। এই প্রথার সুযোগেই বর্তমান সময় যে কোনো ক্ষমতালিপ্সু ও সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তি ক্ষমতা দখল করে জনসাধারণের অর্থে নিজের একটি মুসাহিব গোষ্ঠী তৈরি করে নিতে পারে। অতপর অজস্র মানুষের গগণবিদারী চিজৎকার উপেক্ষা করে সেই মুসাহিব গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় জেঁকে বসে থাকবে।
৩. সরকার ব্যবস্থাকে বর্তমানের ন্যায় অত্যন্ত জটিল ও পেঁচালো নীতিমালার জালে জড়ানো বন্ধ করতে হবে। কারণ তাকে কর্মচারীদের পক্ষেকাজ করা হিসেব গ্রহণকারীদের পক্ষে হিসেব গ্রহণ করা এবং বিপর্যয়ের জন্য প্রকৃত দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে।
৪. সর্বশেষ, কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি এই যে, রাষ্ট্রপ্রধান ও পার্লামেন্টের সদস্য পদে এমন সব লোককে নিযুক্ত করতে হবে, যাদের মধ্যে ইসলাম প্রদত্ত অপরিহার্য গুণাবলী সর্বাপেক্ষা বেশী বিদ্যমান পাওয়া যায়।
৬. রাষ্ট্রপ্রধানের অপরিহার্য গুণাবলী ও যোগ্যতা
রাষ্ট্র প্রধানের গুণাবলী ও যোগ্যতার [Qualification] প্রশ্ন ইসলামের দৃষ্টিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি আমি এতোদূর বলতে পারি যে, ইসলামী সংবিধান কার্যকরী হওয়া বা না হওয়া সম্পূর্ণ এরই উপর নির্ভর করে।
রাষ্ট্র প্রধান এবং মজলিসে শূরার [পার্লামেন্ট] সদস্য পদের জন্য একপ্রকারের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা তো আইনগত প্রকৃতির, যার ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন বা একজন বিচারক যাচাই করে কোনো ব্যক্তির যোগ্য [Eligigle] হওয়া বা না হওয়ার ফয়সালা করেন। আরও একপ্রকারের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকা জরুরী যার দৃষ্টিতে নির্বাচকমণ্ডলী প্রার্থ বাছাই করার এবং মনোয়ন দান করার কাজ সম্পন্ত করে এবং ভোট দাতাগণ ভোট প্রার্থীদের ভোট দেয়। প্রথম প্রকারের যোগ্যতা একটি দেশের কোটি কোটি বাসিন্দার প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান পাওয়া যায়। কিন্তু এই দ্বিতীয় প্রকারের যোগ্যতা দুর্লভ, কোটি কোটি বাসিন্দাদের মধ্য হতে মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যেই তা পাওয়া যায়। প্রথম প্রকারের যোগ্যতার মানদন্ড শুধু সংবিধানের কয়েকটি কার্যোপযোগী ধারায় অন্তর্ভুক্ত [Operative Clauses] করার জন্য নির্ধারিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের যোগ্যতার মানদন্ড সমগ্র সংবিধানের প্রাণসত্তায় বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। একটি সংবিধানের সাফল্য জনগণের মনমানসিকতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সঠিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত করার উপর নির্ভরশীল। একমাত্র এরূপ নির্বাচন পন্থাই সংবিধানের প্রাণসত্তা অনুসারে যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করা সম্ভব।
কুরআন এবং হাদীস এই উভয প্রকার যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্টরূপে আলোচনা করেছে। প্রথম প্রকারের যোগ্যতার জন্য তা চারটি মানদন্ড নির্ধারণ করেছে।
১. তাকে মুসলমান হতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:
“হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহ্র, আনুগত্য করো তাঁর রসূলের এবং সে লোকদের যারা তোমাদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালক।” [সূরা আননিসা: ৫৯]
২. তাকে পুরুষ হতে হবে। কুরআন মজীদ বলে:
“পুরুষ নারীদের উপর কর্তৃত্ব সম্পন্ন।” [সূরা আননিসা: ৩৪]
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে জাতি নিজের কাজের কর্তৃত্ব নারীর উপর সোপর্দ করলো, সে জাতি কখনো সফলকাম হতে পারবেনা।” [বুখারী]
৩. তাকে সুস্থ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বালেগ হতে হবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:
“তোমাদের ধন সম্পদ যাকে আল্লাহ্ তোমাদের অস্তিত্ব রক্ষার উপকরণ বানিয়েছেন তা নির্বোধ লোকদের হাতে সোপর্দ করোনা।” [সূরা আননিসা: ৫]
৪. তাকে দারুল ইসলামের বাসিন্দা হতে হবে। কুরআন মজীদ সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে:
“যার ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে [দারুল ইসলামে] আসেনি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়, যতক্ষণ না তারা হিজরত করে।” [সূরা আনফাল: ৭২]
এই হচ্ছে সে চারটি আইনগত যোগ্যতা। এ যোগ্যতা যার মধ্যে বিদ্যমান পাওয়া যাবে আইনের দৃষ্টিতে সে রাষ্ট্রপ্রধান বা পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। কিন্তু এই আইনগত যোগ্যতাসম্পন্ন অসংখ্য লোকের মধ্যে কোন্ লোকদের উপরোক্ত দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহের জন্য আমরা নির্বাচিত করবো, আর কাদের নির্বাচিত করবোনা কুরআান ও হাদীসে আমরা এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব পেয়ে যাই:
“আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন যে, আমানতসমূহ [দায়িত্বপূর্ণ পদ] আমানতদার [বিশ্বাসযোগ্য] লোকদের উপর সোপর্দ করো।” [সূরা আননিসা: ৫৮]
“তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক মুত্তাকী-আল্লাহ ভীরু।” [সূরা হুজুরাত: ১৩]
“নবী বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা শাসন কার্যের জন্য তোমাদের উপর তাকে [তালূতকে] অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং তাকে বিদ্যাবুদ্ধি ও দৈহিক শক্তিতে সমৃদ্ধি দান করেছেন।” [সূরা বাকারা: ২৪৭]
“এমন ব্যক্তির আনুগত্য স্বীকার করোনা, যার মন আল্লাহর স্মরণ শূন্য, যে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কাজকর্ম সীমা লংঘনকারী।” [সূরা কাহ্ফ”: ২৮]
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“যে কেউ বিদয়াতপন্থী ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো সে ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সাহায্য করলো।” [বায়হাকী]
“আল্লাহর শপথ! এমন ব্যক্তিকে আমরা কখনো কোনো রাষ্ট্রীয় পদে নিযুক্ত করবোনা, যে নিজে তা পেতে চায় কিংবা তার জন্য ললায়িত হয়।” [বুখারী, মুসলিম]
“আমাদের দৃষ্টিতে পদপ্রার্থীই তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় অবিশ্বস্ত।” [আবু দাউদ]
উল্লেীখত গুণাবলীর কতকগুলোকে আমরা অনায়াসেই আমাদের সংবিধানের ব্যবহারিক ধারা হিসেবে বিধিবদ্ধ করে নিতে পার। যথা: পদপ্রার্থীকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের অযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে। অন্যান্য যেসব গুণকে আইনের আওতার মধ্যে সুনির্ধারিতভাবে গণ্য করা যায়না সেগুলিকে আমাদের সংবিধানের নীতিনির্ধারক মূলনীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ। এবং রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য ইসলামের দৃষ্টিাতে অপরিহার্য গুণাবলী সম্পর্কে প্রত্যেক নির্বাচনের সময় জনগণকে বিস্তারিতভাবে অবহিত করা নির্বাচক মণ্ডলীর অন্যতম কর্তব্য হিসেবে ধার্য করে দিতে হবে।
৭. নাগরিকত্ব ও তার ভিত্তি
এখন নাগরিকত্বের বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। ইসলাম যেহেতু চিন্তা ও কর্মের একটি পূর্ণাংগ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার ভিত্তিতে সে একটি রাষ্ট্রও কায়েম করে। তাই ইসলাম তার রাষ্ট্রের নাগরিকত্বকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে। উপরন্তু সততা ও ন্যায় পরায়ণতা যেহেতু ইসলামের মূল প্রাণসত্তা, তাই কোনো প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণা ব্যতিরেকেই সে নাগরিকত্বের এই দুই শ্রেণীকে সুস্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে। মুখে মুখে সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দানের কথা বলে এবং কার্যত তাদের মধ্যে কেবল পার্থক্য করেই নয় বরং তাদের বিরাট অংশকে মানবীয় অধিকার দিতেও কুণ্ঠিত হওয়ার মতো মারাত্মক প্রতারণা কিছুইতে ইসলাম করতে পারেনা। যেমন আমেরিকায় নিগ্রোদের, রাশিয়ায় অ-কমিউনিষ্টদের এবং দুনিয়ার সমস্ত ধর্মহীন গণতন্ত্রের [Secular Democracy] রাষ্ট্রে দেশের সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার বর্জিত দুরাবস্থার কথা দুনিয়ার কার না জানা আছে?
ইসলাম নাগরিকদের নিম্নোক্ত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে:
১. মুসলিম।
২. জিম্মী [অমুসলিম]
১. মুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে:
“যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে; আর যারা তাদের আশ্রয় দিয়েছে এবং তাদের সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। পক্ষান্তরে যারা [শুধু] ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরত করে [দারুল ইসলামে] চলে আসেনি, তাদের বন্ধুতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব তোমাদের নয়- যতক্ষণ না তারা হিজরত করলো।” [সূরা আনফাল: ৭২]
এ আয়াতে নাগরিকত্বের দুইটি ভিত্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম ঈমান, দ্বিতীয় দারুল ইসলামে [ইসলামী রাষ্ট্রের] প্রজা [পূর্ব থেকেই কিংবা পরে] হওয়া। একজন মুসলমান তার ঈমান আছে; কিন্তু কাফেরী রাজ্যের আনুগত্য ত্যাগ করে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসে যদি বসবাস করতে শুরু না করে, তবে সে দারুল ইসলামের নাগরিক বলে বিবেচিত হতে পারেনা। পক্ষান্তরে দারুল ইসলমের সকল ঈমানদার বাসিন্দাগণ দারুল ইসলামের নাগরিক, তাদের জন্ম দারুল ইসলামে হোক কিংবা দারুল কুফর থেকে হিজরত করেই আসুক এবং তারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী ও সহযোগী। [হিজরত করে যারা আসে তাদের সম্পর্কে কুরআন একটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা বলেছে যে, এই ধরনের লোকদের পরীক্ষা [Examine] করে দেখা আবশ্যক [সূরা মুমতাহিনা, ১০ নং আয়াত দ্রঃ]। এই ব্যবস্থা যদিও মুহাজির স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু তা থেকে এই সাধারণ মূলনীতি জানা যায় যে, বহিরাগত ও হিজরতের দাবিদার ব্যক্তিকে দারুল ইসলামে গ্রহণ করার পূর্বে তার প্রকৃত মুসলমান ও মুহাজির হওয়া সম্পর্কে নিশ্চয়তা লাভ করতে হবে। যাতে করে হিজরতের সুযোগে ভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পন্ কোনো লোক দারুল ইসলামে প্রবেশ করতে না পারে। কোনো ব্যক্তির প্রকৃত ঈমানের অবস্থা আল্লাহ ভিন্ন আর কেউ জানতে পারে না, কিন্তু বাহ্যিক উপায়ে যতদূর যাচাই করা সম্ভব তা করতে হবে।]
এই মুসিলম নাগরিকদের উপরই ইসলাম তার পরিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থার দায়িত্বভার চাপিয়ে দিয়েছে। কারণ তারাই নীতিগতভাবে এই ব্যবস্থাকে সত্য বলে মানে। তাদের উপর ইসলাম তার পরিপূর্ণ আইন জারী করে, তাদেরকেই তার সমগ্র ধর্মীয়, নৈতিক, তামাদ্দুনিক এবং রাজণৈতিক বিধানের অনুসারী হতে বাধ্য করে। তার যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের ভারও সে তাদের উপরই অর্পণ করে। দেশ ও রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা জন্য সকল প্রকার কুরবানী সে কেবল তাদের নিকটই দাবী করে। অতঃপর সে এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্র প্রধান ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা নির্বাচনের অধিকারও তাদেরই দান করে এবং তার পরিচালনার জন্য সংসদে অংশগ্রহণ এবং তার দায়িত্বপূর্ণ পদসমূহে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগও তারাই লাভ করে। যাতে এই আদর্শবাদী রাষ্ট্রের কর্মসূচী ঠিক তার মূলনীতিসমূহের সাথে সংগতি রেখে বাস্তবায়িত হতে পারে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনকাল এবং খিলাফতে রাশেদার স্বর্ণযুগ উল্লিখিত মূলনীতির সত্যতা ও যৌক্তিকতার দৃষ্টান্ত। যেমন এ সময় শূরার সদস্য হিসেবে কোনো প্রদেশের গভর্ণর হিসেবে কিংবা সরকারী কোনো বিভাগের মন্ত্রী, সেক্রেটারী, বিচারক বা সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে কোনো যিম্মীকে নিযুক্ত করা হয়নি। খলীফা নির্বাচনের ব্যাপারেও তাদের অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়নি। অথচ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও ইসলামী রাষ্ট্রে তারা বর্তমান ছিলো। একথা আমাদের বুঝে আসেনা যে, এসব রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে তাদের অংশ গ্রহণের যদি কোনো অধিকারই থাকতো, তবে আল্লাহর নবী তাদের সে অধিকার কিভাবে হরণ করতে পারেন এবং স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের নিকট সরাসরি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকগণ ক্রমাগতভাবে ত্রিশ বছর পর্যন্ত কেমন করে তাদের অধিকার আদায় না করে থাকতে পারেন।
২. যিম্মী নাগরিক বলতে সেসব অমুসলিমকে বুঝায় যারা ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্সীমার মধ্যে বসবাস করে তার আনুগত্য ও আইন পালন করে চলার অংগীকার করবে, চাই তারা দারুল ইসলামে জন্ম গ্রহণ করে থাকুক কি বাইরের কোনো কাফের রাজ্যে [দারুল কুফর] থেকে এসে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা হওয়ার আবেদন করে থাকুক। এই দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়না। ইসলাম এই শ্রেণীর নাগরিকদের ধর্ম, সাংস্কৃতি, ব্যক্তি আইন [Personal Law] এবং জান মাল ও সম্মানের পূর্ণ নিরাপত্তা দান করে। তাদের উপর রাষ্ট্রের কেবল গণসাধারণ [Public Law] জারী করা হবে। এই গণআইনের দৃষ্টিতে তাদেরকেও মুসলমান নাগরিকদের সমান অধিকার ও মর্যাদা দেয়া হয়। দায়িত্বসম্পন্ন পদ [Key post] ব্যতীত সকল প্রকার চাকুরীতেও তাদের নিযুক্ত করা যাবে। নাগরিক স্বাধীনতাও তারা মুসলমানদের সমান ভোগ করবে, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাদের সাথে মুসলমানদের অপেক্ষা কোনোরূপ স্বতন্ত্র আচরণ করা হয়না। রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে তা সম্পূর্ণরূপে মুসলমামনদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।
এই দুই শ্রেণীর নাগরিকত্ব ও তার পৃথক পৃথক মর্যাদা সম্পর্কে কারো আপত্তি থাকলে সে যেনো পৃথিবীর অন্যান্য আদর্শবাদী রাষ্ট্র অথবা জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র- তার মূলনীতিসমূহ মানতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী সংখ্যালঘু নাগরিকদের প্রতি যে আচরণ করে সে দিকে দৃষ্টিপাত করে। বাস্তবিকই একথাই চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলা যায় যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে তার মূলনীতির সম্পূর্ণ পৃথক মূলনীতিতে বিশ্বাসী, যা অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে, ইসলামের চেয়ে অধিক ইনসাফ, সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতার সাথে অন্য কোনো ব্যবস্থা সে জটিলতার সমাধান করেনি। অন্যরা ও জটিলতার সমাধান প্রায়িই দুইটি পন্থায় করেছে; হয় তাকে [সংখ্যা লঘূকে] নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার চেষ্টা করেছে অথবা শূদ্র বা অস্পৃশ্য শ্রেণী বানিয়ে রেখেছে। ইসলাম উপরোক্ত পন্থার পরিবর্তে তার নীতিমালা মান্যকারী ও অমান্যকারীদের মধ্যে ন্যায়ানুগ একটি সীমা নির্ধারণ করে দেয়অর পন্থা গ্রহণ করেছে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে তার নীতিমালা পূর্ণরূপে অনুসরণ করতে বাধ্য করে এবং উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার দায়িত্বভার তাদের উপর অর্পণ করে। আর যারা নীতিমালার অনুসারী নয় তাদেরকে সে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা বহাল রাখার জন্য অত্যাবশ্যক সীমা পর্যন্ত তার বিধান মানতে বাধ্য করে। ইসলাম তাদেরকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অব্যহতি দেয়ার সাথে সাথে তাদের যাবতীয় সাংস্কৃতি ও মানবীয় অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা প্রদান করে।
৮. নাগরিক অধিকার
এরপর আমাকে বলতে হবে যে, ইসলামে নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার [Fundamental Rights] স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।
সর্ব প্রথম ইসলাম নাগরিকদের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর পূর্ণ নিরাপত্তার অধিকার দান করেছে। আইন সংগত বৈধ কারণসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে তাদের উপর হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম প্রচুর সংখ্যক হাদীসে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের প্রাক্কালে তিতিন তাঁর সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। সে ভাষণে তিনি বলেছেন:
“তোমাদের জান, তোমাদের মাল, তোমাদের মান সম্মান তদ্রূপ সম্মানার্হ [হারাম] যেমন আজকের এই হজ্জের দিনটি সম্মানার্হ।”
কেবল একটি অবস্থায় তা সম্মানার্হ [হারাম] থাকবেনা। তা তিনি অপর এক হাদীসে এভাবে বলেছেন:
“ইসলামী আইনের আওতায় কারো জান মাল অথবা ইজ্জত আব্রুর উপর কোনো হক [অধিকার] প্রমাণিত হলে আইন অনুমোদিত পন্থায় অবশ্যই তা আদায় করতে হবে।”
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হচ্ছে, যে কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংরক্ষণ। দেশে প্রচলিত এবং সর্বজন স্বীকৃত আইন সংগত পন্থায় দোষ প্রমাণ না করে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে ইসলামে কারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা যায়না। সুনানে আবু দাউদ- এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে:
একদা মদীনার কিছু সংখ্যক লোক কোনো সন্দেহের কারণে বন্দী হয়েছিলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ভাষণদানরত থাকা অবস্থায় একজন সাহাবী দন্ডায়মান হয়ে তাঁর নিকট আরজ করলেন, আমার প্রতিবেশীদেরকে কোন্ অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয বারে কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব থাকলেন। শহরের পুলিশ প্রধানকে তাদের গ্রেপ্তারের সংগত কোনো কারণ থাকলে তা পেশ করার সুযোগ দেয়ার জন্য তিনি (স) নিরুত্তর থাকলেন। ঐ সাহাবী তৃতীয় বার তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে এবং পুলিশ প্রধান নিরুত্তর থাকলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বললেন:
“তার প্রতিবেশীদের ছেড়ে দাও।” [আবু দাউদ, কিতাবুল কাদা]
উপরোক্ত ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, কোনো সুনির্দিষ্ট অপরাধে দোষী সাব্যস্ত না করা পর্যন্ত কোনো নাগরিককে গ্রেপ্তার করা যাবেনা। ইমাম খাত্তাবী [র] তাঁর “মায়ালিমুস সুনান” গ্রন্থে উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন: “ইসলামে শুধু দুই প্রকারে গ্রেপ্তারী বৈধ। [এক] শাস্তিস্বরূপ আটক করা অর্থাৎ আদালতের রায়ে কোনো নাগরিককে কয়েদীর শাস্তি প্রদান করা হলে তাকে আটক করা। নিঃসন্দেহে এই আটক সম্পূর্ণ সংগত। [দুই] তদন্তের জন্য আটক করা অর্থাৎ অভিযুক্ত ব্যক্তি বাইরে থাকলে তদন্তকার্য ব্যাহত হতে পারে এরূপ আশংকা থাকলে তাকে কয়েদ করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রকারের আটক বৈধ নয়।” [মায়ালিমুস সুনান, কিতাবুল কাদা]
ইমাম আবু ইউসুফ [র] তাঁর “কিতাবুল খারাজ” গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, কোনো ব্যক্তিকে নিছক সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বন্দী করা যাবেনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম কেবল দোষারোপের ভিত্তিতেই কাউকে বন্দী করতেননা। বাদী ও বিবাদী উভয়কে আদালতে হাযির হতে হবে। সেখানে বাদী দলীল প্রমাণসহ তার দাবী উত্থাপন করবে। সে সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করতে ব্যর্থ হলে বিবাদীকে বেকসুর খালাস দিতে হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১০৭]
হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও একটি মুকদ্দমার রায় দিতে গিয়ে ঘোষণা করেন:
“ইসলামে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যাবেনা।” [মুয়াত্তা ইমাম মালেক, বাব শারতিশ শাহিদ]
তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক অধিকার হচ্ছে, মত প্রকাশের এবং ধর্মীয় স্বাধীনতা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বিষয়টি সম্পর্কে ইসলামী আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তাঁর খিলাফত আমলে খারিজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়েছিলো। বর্তমানকালের নৈরাজ্যবাদী [Nihilist] দলসমূহের সাথে তাদের অনেকটা সামঞ্জস্য ছিলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অস্বীকার করতো এবং অস্ত্রবলে এর অস্তিত্ব বিলোপের জন্য বদ্ধপরিকর ছিলো। আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এই অবস্থায় তাদেরকে নিম্নোক্ত পয়গাম পাঠান:
“তোমরা যেখানে ইচ্ছা বসবাস করতে পারো। তোমাদের ও আমদের মধ্যে এই চুক্তি রইলো যে, তোমরা রক্তপাত করবেনা, ডাকাতকি করবেনা এবং কারও উপর যুলুম করবেনা।” [নায়লুল আওতার, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১৩০]
অপর এক জায়গায় তিনি তাদের বলেন:
“তোমরা যতক্ষণ বিপর্যয় ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তোমাদের উপর আক্রণ করবোনা।” [নায়লুল আওতার, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৩৩]
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, কোনো দলের মতবাদ যাই হোক না কেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের মত যেভাবেই প্রকাশ করুক না কেন, ইসলামী রাষ্ট্র তাতে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবেনা। কিন্তু তারা যদি নিজেদের মত শক্তিকে প্রয়োগে [By violent Means] বাস্তবায়িত করতে এবং রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা চূর্ণ বিচূর্ণ করার চেষ্টা করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আরও একটি মৌলিক অধিকারের প্রতি ইসলাম যথেষ্ট জোর দিয়েছে। তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র তার চতুঃসীমার মধ্যে বসবাসকারী কোনা নাগরিককে তার জীবন যাপনের মৌলিক প্রয়েঅজন থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবেনা। ইসলাম এ উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান ফরয করেছে এবং এ সম্পর্কে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“তাদের ধনীদের নিকট থেকে তা আদায় করা হবে এবং তাদের গরীবদের মধ্যে তা বন্টন করা হবে।” [বুখারী ও মুসলিম]
অপর এক হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম মূলনীতি হিসেবে ইরশাদ করেন:
“যার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক নেই, তার পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার।”
অপর এক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন:
“মৃত ব্যক্তি যে বোঝা [ঋণ অথবা পরিবারের অসহায় সদস্য] রেখে গেলো তার দায়িত্ব আমাদের উপর।” [বুখারী ও মুসলিম]
এ ক্ষেত্রে ইসলাম মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে মোটেই পার্থক্য করেনি। কোনো নাগরিককেই অন্ন ব্ত্র ও আশ্রয়হীন অবস্থায় ত্যাগ করা যাবেনা। ইসলাম মুসলিম নাগরিকদের মতো তার অমুসিলম নাগরিকদের অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থানের নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু এক ইহুদী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে তার উপর আরোপিত কর মওকুফ করেন এবং তার জন্য রাজকোষ থেকে ভাতা মঞ্জুর করে রাজকোষে কর্মকরতাকে লিখে পাঠান:
“আল্লাহর শপথ! এ লোকটির যৌবনকালে যদি তার দ্বারা কাজ করিয়ে থাকি এবং এখন তার এই বার্ধক্যে তাকে নিরূপায় অবস্থায় ত্যাগ করি তবে তার সাথে মোটেই সুবিচার করা হবেনা।” [ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭২]
হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হীরা নামক এলাকার অমুসলিম নাগরিকদের জন্য যে চুক্তিপত্র লিখে দিয়েছিলেন তাতে পরিষ্কার ভাষায় বলা হয়েছিলো যে, যে ব্যক্তি বার্ধক্রে পৌঁছবে, অথবা যে ব্যক্তি আকস্মিক বিপদে পিতিত হবে, অথবা যে ব্যক্তি গরীব হয়ে যাবে তার নিকট থেকে কর আদায় করার পরিবর্তে রাজকোষ থেকে তার এবং তার পরিবার পরিজনের জীবিকার ব্যবস্থা করা হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-৮৫]
৯. নাগরিকদের উপর রাষ্ট্রের অধিকার
নাগরিকদের প্রদত্ত এসব অধিকারের বিপরীতে তাদের উপর রাষ্ট্রেরও কতোগুলো অধিকার বর্তায়। এর মধ্যে সর্বপ্রথম অধিকার হচ্ছে, তাদের আনুগত্য লাভের অধিকার। ইসলামী পরিভাষায় একে বলা হয় “শ্রবণ করা ও মেনে চলা”। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম এ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন:
“শ্রবণ করা, অনুসরণ করা ও মেনে চলা অসময়ে ও সুসময়ে এবং আনন্দ ও নিরানন্দ সকল অবস্থায় অপরিহার্য।”
অর্থাৎ কোনো আইন নাগরিকদের পছন্দ হোক বা অপছন্দনীয় হোক, সহজসাধ্য হোক বা কষ্টসাধ্য হোক, তা মান্য করা এবং পালন করা সকলের জন্যই অপরিহার্য।
ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরকগণ হবে ইসলামী রাষ্ট্রের বন্ধু ও হিতাকাংখী। নাগরিকদরে উপর এটা ইসলামী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। কুরআন মজীদে ও সুন্নাতে রসূলে একথা প্রকাশের জন্য ‘নুসহ’ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এই শব্দটির ভাবার্থ [Loyalty] [রাজানুগত্য] ও [Allegiance] [রাজানুগত্য] শব্দদ্বয়ের তুলনায় অধিকতর ব্যাপক। এর দাবী এই যে, প্রত্যেক নাগরিক আন্তরিক ও নিষ্ঠা সহকারে রাষ্ট্রের কল্যাণ কামনা করবে এবং রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর এমন কোনো কাজ বরদাশত করবেনা, রাষ্ট্রের কল্যাণ ও মঙ্গলের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখবে।
শুধু তাই নয়, ইসলামী রাষ্ট্রের বাসিন্দাদের উপর এর চেয়েও কঠিন কর্তব্য চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ইসলামী সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা করা নাগরিকদের অপরিহার্য কর্তব্য। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান এবং তার উদ্দেশ্যের বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনবোধে নিজেদের জান মাল উৎসর্গ করতে তারা বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলে কুরআন মজীদ তাকে “প্রকাশ্য মুনাফিক” বলে সাব্যস্ত করেছে।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে সেই বৈশিষ্ট্যযুক্ত রাষ্ট্রকেই আমরা “ইসলামী রাষ্ট্র” হিসেবে আখ্যায়িত করি। এ পদ্ধতির রাষ্ট্রকে আধুনিকালের পরিভাষায় যে নামেই অভিহিত করা হোক, সেকুলার [ধর্মহীন], গণতান্ত্রিক বা ধর্মতান্ত্রিক ইত্যাদি যাই বলা হোক, তাতে কিচুমাত্র যায় আসেনা। কারণ পরিভাষা বা নাম নিয়ে আমাদের কোনো বিতর্ক নেই। আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যে ইসলামকে মান্য করার দাবী করি, আমাদের জীবন ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা সে ইসলামের নির্ধারিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হোক।
অষ্টম অধ্যায়
ইসলামী সংবিধানের ভিত্তিসমূহ]
১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
২. রিসালাতের মর্যাদা
৩. খিলাফতের ধারণা
৪. পরামর্শের নীতিমালা
৫. নির্বাচনের নীতিমালা
৬. নারীদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ
৭. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য
৮. শাসক ও তার আনুগত্যের নীতিমালা
৯. মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার
১০. জনকল্যাণ
নিবন্ধটি ১৯৫২ সালের শেষ প্রান্তে রচিত। এই সময় একজন খ্যাতনামা উকীল ও লেখক চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যে, কুরআন মজীদ থেকে কোনো সংবিধানে কাঠামো পাওয়া যায় কিনা। এই প্রসঙ্গে তিনি বিস্তারিত আলোকপাত করেন। মাওলানা মওদূদী তখন নিম্নোক্ত প্রবনধ রচনা করেন এবং তাতে সংবিধানের এক একটি ধারার উল্লেখপূর্বক কুরআন ও হাদীসে তার ভিত্তিসমূহ নির্দেশ করেন।
ইসলামী সংবিধানের ভিত্তিসমূহ
দেশের সংবিধান প্রণয়নের কাজ যখন শেষ পর্যায়ে তখন বুদ্ধিজীবী সমাজের দায়িত্ব হচ্ছে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদকে যথার্থ ইসলামী সংবিধান প্রণয়নে যথাসাধ্য সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করা। এ ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য সহযোগিতা করতে থাকবো। ১৯৫১ সালের শুরুতে মুসলমানদের সকল ফের্কার প্রতিনিধি স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। [পরিশিষ্ট-১ দ্রঃ]। কিন্তু একদল লোক অনবরত একদিকে মুসলিম জনসাধারণ ও শিক্ষিত সমাজকে এবং অপরদিকে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদের সদস্যদেরকে যতোদূর সম্ভব ভুলবুঝাবুঝির শিকারে পরিণত করার অপচেষ্টায় নিরত থাকে। তাদের পক্ষ থেকে বার বার বিভিন্ন শব্দের মারপ্যাচের এ ধারণার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে যে, কুরআন মজীদে সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে কোনো পথনর্দেশ প্রদান করা হয়নি এবং ইসলাম কোনো বিশেষ পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থার দাবি করেনা এবং ইসলামী সংবিধান বলতে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। এই বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের পেছনে কোনো যুক্তি নাই। কিন্তু ইসলামী জ্ঞান চর্চার এই পতনযুগে বুদ্ধির বিভ্রান্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই অপপ্রচার প্রভাবশালী হতে পারে। তাই একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সাংবিধানিক বিধির সাথে সংশ্লিষ্ট কুরআন ও হাদীসের বক্তব্যসমূহ একত্র করে পেশ করা প্রয়োজন মনে করছি, যাতে জনগণ জানতে পারে যে, আজ পর্যনত আলেমগণ যেসব মূলনীতিকে ইসলামের সাংবিধানিক নীতিমালা হিসেবে পেশ করেছেন তার মূল উৎস কি এবং সাথে সাথে সংবিধানে প্রণয়ন পরিষদের সদস্যদের সামনে যেনো আল্লাহ্ পাকের দলীল প্রমাণ পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হয় এবং তারা যেনো কখনও এই ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধানসমূহ বলে দেয়া হয়নি।
উপরোক্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য এই নিবন্ধ লেখা হচ্ছে। এতে আমি ক্রমিক নম্বর অনুসারে এক একটি সাংবিধানিক বিষয় সম্পর্কে কুরআনের বাণী এবং সহীহ হাদীসসমূহ পেশ করবো এবং সাথে সাথে এও বলে দেবো যে, তাথেকে কি বিধান নির্গত হয়।
১. আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
হুকুম [সার্বভৌমত্ব] কেবল আল্লাহর জন্য। তাঁর নির্দেশ হলো, তোমরা তাঁর ব্যতীত আর কারো দাসত্ব করবেনা, এটাই সঠিক দীন। [সূরা ইউসুফ: ৪০]
এই আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, ফায়সালা করার এখতিয়ার এবং শাসনকার্যের অধিকার [ভিন্ন শব্দে সার্বভৌমত্ব] আল্লাহ তায়ালার জন্য সুনির্দিষ্ট। এই সার্বভৌমত্বকে শুধুমাত্র “বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্বের” [Universal Sovereignty] অর্থে সীমাবদ্ধ করার মতো কোনো শব্দ বা সম্বন্ধ এখানে বিদ্যমান নেই। আল্লাহ্ তায়ালার এই সার্বভৌমত্ব যেমন বিশ্বজনীন, তদ্রুপ রাজনৈতিক, আইনগত, নৈতিক ও বিশ্বাসগত সব দিকেই পরিব্যপ্ত। স্বয়ং কুরআন মজীদে সর্ব প্রকারের সার্বভৌমত্ব আল্লাহ তায়ালার জন্য সুনির্দিষ্ট হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণসমূহ বিদ্যমান রয়েছে। অতএব কুরআন মজীদ পরিষ্কার বাক্যে বলে যে, আল্লাহ তায়ালা কেবল “রব্বুন নাস” [মানুষের প্রভু] ও “ইলাহুন নাস” [মানুষের উপাস্য]-ইন নন বরং “মালিকুন নাস” [মানুষের শাসক]-ও :
“বলো [হে মুহাম্মাদ], আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রভু, মানুষের শাসক এবং মানুষের উপাস্যের নিকট।” [সূরা নাস: ১-৩]
কুরআন মজদ বলে, আল্লাহ্ তায়ালাই শাসনকর্তৃত্বের মালিক, কর্ণধার এবং এই বিষয়ে তাঁর কোনো অংশীদার নেই:
“বলো : হে আল্লাহ! শাসন কর্তৃত্বের মালিক! তুমি যাকে চাও শাসন কর্তৃত্ব দান করো এবং যার নিকট থেকে চাও তা ছিনিয়ে নাও।” [সূরা আলে ইমরান: ২৬]
“রাজত্বের ব্যাপারে তার কোনো অংশীদার নাই।” [সূরা বনী ইসরাঈল : ১১১]
কুরআন মজীদ আরও পরিষ্কার ভাষায় বলে, নির্দেশ প্রদানের অধিকার কেবল আল্লাহ্ তায়ালার, কারণ তিনিই স্রষ্টা:
“সাবধান! সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও [চলবে] তাঁর।” [সূরা আরাফ: ৫৪]
একথা পরিষ্কার যে, এটা কেবল বিশ্বজনীন সার্বভৌমত্ব নয় বরং সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব এবং তার ভিত্তিতেই কুরআন মজীদ আইনগত সার্বভৌমত্বও আল্লাহ তায়ালার জন্য নির্ধারণ করেছে:
“তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত জিনিসের অনুসরণ করো এবং তাঁকে ত্যাগ করে অন্যান্য অভিভাবকের অনুসরণ করোনা।” [সূরা আরাফ: ৩]
“যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা করেনা সে কাফের।” [সূরা মায়েদা: ৪৪]
আল্লাহ্ তায়ালার রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের এই ধারণা ইসলামের সর্ব প্রাথমিক মৌলিক নীতিমালাসমূহের অন্তর্ভুক্ত এবং প্রাথমিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত ইসরামের আইনবিদগণ [ফুকাহা] এই ব্যাপারে একমত যে, হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ তায়ালার জন্য সুনির্ধারিত। সুতরাং আল্লামা আমিদী উসূলে ফিক্হের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ “আল ইহ্কাম ফী উসূলিল আহ্কাম” এ লিখেছেন:
জেনে রাখো! আল্লাহ্ ছাড়া কোনো হাকিম [শাসক] নাই এবং তিনি যে হুকুম [বিধান] দিয়েছেন তাই কেবল হুকুম [বিধান] হিসেবে গণ্য।
শায়খ মুহাম্মাদ খুদারী তাঁর ‘উসূলুল ফিক্হ’ গ্রন্থে এটাকে গোটা মুসলিম উম্মাহ্র ঐক্যবদ্ধ আকীদা [বিশ্বাস] প্রমাণ করেছেন:
মূলত আল্লাহর ফরমানকে হুকুম বলা হয়। অতএব হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো নাই। এটা এমন একটি কথা, যে সম্পর্কে সমস্ত মুসলমান একমত।
অতএব কোনো সংবিধান যখন সর্ব প্রথম আল্লাহ্ তায়ালার রাজণৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয় এবং অকাট্য বাক্যে একথা তাতে লিখতে হয় যে, এই রাষ্ট্র আল্লাহ্র আনুগত আর তাঁকে সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী স্বীকার করে এবং তাঁর বিধান পালন বাধ্যতামূলক মনে করে, তখনই তা ইসলামী সংবিধান হিসেবে গণ্য হতে পারে।
২. রিসালাতের মর্যাদা
সাধারণভাবে সকল নবী রসূল এবং বিশেষভাবে মহানবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তায়ালার এই রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রতিভু। অর্তাৎ যে মাধ্যমৈ আল্লাহ তায়ালার এই সার্বভৌমত্ব মানুষের মাঝে কার্যকর হয় সে মাধ্যম হলেন আল্লাহর নবী। একজন্য তাঁর নির্দেশাবলীর আনুগত্য করা তার প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করা এবং ফায়সালাসমূহ বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয়া এমন প্রত্যেক ব্যক্তি, দল ও সমাজের জন্য অপরিহার্য, যারা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে। বিষয়টি কুরআন মজীদে বার বার সুস্পষ্ট বাক্যে বিধৃত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ দেখা যেতে পারে:
“যে ব্যক্তি রসূলের আনুগত্য করলো সে মূলত আল্লাহ্রই আনুগত্য করলো।” [সূরা নিসা: ৮০]
“আমরা যে রসূলই প্রেরণ করেছি তাকে এজন্য প্রেরণ করেছি যে, আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে তার আনুগত্য করা হবে।” [সূরা নিসা: ৬৪]
“[হে মুহাম্মাদ!] আমরা এই কিতাব সত্য সহকারে তোমার নিকট নাযিল করেছি, যাতে তুমি মানুষের মাঝে ফায়সালা করো যা তোমাকে আল্লাহ্ হৃদয়ংগম করান তদনুযায়ী।” [সূরা নিসা: ১০৫]
“আর রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে তোমাদের বাধা দেয় তাত্থেকে বিরত থাকো।” [সূরা হাশর: ৭]
“অতএব না! তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা যতক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবেনা যতক্ষণ তোমাকে তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদে মীমাংসাকারী মেনে না নেয়, অতঃপর তুমি যে মীমাংসা করবে তাতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হবেনা এবং তা সন্তোষসহকারে মেনে নিবে।” [সূরা নিসা: ৬৫]
এটি ইসলামী সংবিধানের দ্বিতীয় ভিত্তি। তাতে আল্লাহ তায়ালার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়অর পরে দ্বিতীয় পর্যায়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিষ্ঠিত সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে মেনে নিতে হবে এবং রাষ্ট্রের শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ ও বিচার বিভাগের সুন্নাহ পরিপন্থী বিধান দেয়ার, বিধান প্রণয়নের ও ফায়সালা প্রদানের এখতিয়ার থাকবেনা।
৩. খিলাফতের ধারণা
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি তাদের অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের।” [সূরা নূর: ৫৫]
উপরোক্ত আয়াত থেকে দুটি সাংবিধানিক বিষয় অবগত হওয়া যায়। [এক] ইসলামী রাষ্ট্রের সঠিক মর্যাদা হচ্ছে “খিলাফতের” [প্রতিনিধিত্বের] “সার্বভৌমত্বের” নয়। [দুই] ইসলামী রাষ্ট্রে খিলাফতের বাহক বা দায়িত্ব বহনকারী, কোনো ব্যক্তি, গোত্র পরিবার গোত্র হবে না, শ্রেণী বরং গোটা মুসলিম উম্মাহ হবে তার বাহক, যাদেরকে আল্লাহ্ তায়ালা স্বাধীন রাষ্ট্র দান করবেন।
প্রথমোক্ত বিষয়ের ব্যাখ্যা হলো, সার্বভৌমত্ব তার মূল বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এই দাবি করে যে, সার্বভৌমত্বের অধিকারী সত্তার বাইরে এমন সত্তা থাকবেনা যে তার ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সীমাবদ্ধ করতে পারে এবং তাকে তার বানানো বিধান ও নীতিমালা ব্যতীত উপর থেকে চাপিয়ে দেয়া বিধান ও নীতিমালার অনুগত বানাতে পারে। [এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।] এখন যদি একটি রাষ্ট্র প্রথম পদক্ষেপেই স্বীকার করে নেয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের হুকুম তার জন্য চূড়ান্ত ও অকাট্য বিধান, শাসন বিভাগ এর পরিপন্থী কাজ করতে পারবেনা, আইন প্রণয়ন বিভাগ এর পরিপন্থী কোনো বিধান রচনা করতে পারবেনা এবং তার বিচার বিভাগও এর পরিপন্থী কোনো রায় দিতে পারবেনা, তবে তার পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায়, সে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিপরীতে সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব থেকে বিরত হয়েছে এবং রাষ্ট্রীয় কার্য পরিচালনায় মূলত আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রনিধির [খলীফা] মর্যাদা গ্রহণ করে নিয়েছে। এই অবস্থায় তার জন্য যথার্থ পরিভাষা “সার্বভৌমত্ব” নয় বরং “খিলাফতই” হতে পারে। অন্যথায় উপরোক্ত মর্যাদা বহাল রেখে তার জন্য “সার্বভৌমত্ব” শব্দের ব্যবহার করা কেবল পারিভাষিক বৈপরিত্য ছাড়া আর কি হতে পারে। অবশ্য সে যদি তার সর্বময় কর্তৃত্বকে আল্লাহর হুকুম ও রসূলের সুন্নাতের আনুগত্য করার সাথে শর্তযুক্ত না করে তবে নিঃসন্দেহে তার সঠিক মর্যাদা হবে “সার্বভৌমত্বের,” কিন্তু এ অবস্থায় তার জন্য “ইসলামী রাষ্ট্র” পরিভাষাটি ব্যবহার করাও পারিভাষিক বৈপরিত্য হবে।
দ্বিতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা এই যে, একটি ইসলামী রাষ্ট্রে তার সমস্ত মুসলিম মূলনীতিগত সত্য যার উপর ইসলামে গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছে। ইসলাম পরিপন্থী গণতন্ত্রের ভিত্তি যেভাবে “জনগণের সার্বভৌমত্বের” [Popular Sovereignty] নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত, অনুরূপভাবে ইসলামী গণতন্ত্রের ভিত্তি “সামগ্রিক প্রতিনিধিত্বের” [Popular Vicegerency] উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ব্যবস্থায় সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে খিলাফত পরিভাষা এজন্র গ্রহণ করা হয়েছে যে, এখানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আল্লাহর দান হিসেবে বিবেচিত এবং দানকে আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থান করেই ব্যবহার করা যায়। কিন্তু খিলাফতের এই সীমাবদ্ধ কর্তৃত্ব কুরআনের উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে কোনো এক ব্যক্তি বা শ্রেণীর জন্য নয় বরং রাষ্ট্রের সকল মুসলমানের উপর একটি জামায়াত বা সমষ্টি হিসেবে অর্পণ করা হয়েছে, যার অনিবার্য দাবি হলো, মুসলমানদের মর্জি মতো সরকার গঠিত হবে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করবে এবং তার প্রতি মুসলমানগণ যতক্ষণ সন্তুষ্ট থাকবে সেই সরকার ততক্ষণই ক্ষমতায় থাকবে। এই কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেকে “আল্লাহ্র খলীফা” বলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছিলেন। কারণ খিলাফত মূলত মুসলিম উম্মহকে প্রদান করা হয়েছিলো, সরাসরি তাঁকে নয়। তাঁর মর্যাদা কেবল এই ছিলো যে, মুসলমানগণ তাদের মর্জি মাফিক তাদের খিলাফতের কর্তত্ব তাঁর নিকট অর্পণ করেছিলেন মাত্র।
এই দুইটি বিষয় বিবেচনায় রেখে ইসলামী রাষ্ট্রে সংবিধান এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যা সার্বভৌমত্বের দাবি থেকে মুক্ত হবে এবং যার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য খিলাফত হিসেবে প্রতিভাত হবে।
৪. পরামর্শের নীতিমালা [শূরার আদর্শ]
সামষ্টিক খিলাফতের উপরোক্ত দাবিকে কুরআন মজীদ নিম্নোক্ত বাক্যে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে:
এবং তাদের কাজ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে হয়ে থাকে। [সূরা শূরা: ৩৮]
এ আয়াতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এই বিশেষত্ব বর্ণনা করা হয়েছে যে, এখানে সমস্ত সামাজিক বিষয় পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হয়। এখানে শুধু বৈশিষ্ট্যই বর্ণনা করা হয়নি বরং বাক রীতির আওতায় পরামর্শের নির্দেশও প্রদান করা হয়েছে। এজন্য কোনো সামাজিক সামষ্টিক কাজ পরামর্শ গ্রহণ ব্যতীত সম্পাদন করা নিষেধ, খতীব বাগদাদী (র) হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিম্নোক্ত রিওয়ায়াত উল্লেখ করেছেন:
“আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার পরে এমন বিষয়ের উদ্ভব হবে যে সম্পর্কে না কুরআন মজীদে কিছু অবতীর্ণ হয়েছে, আর না আপনার নিকট থেকে কিছু শোনা গেছে। তিনি [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বললেন, আমার উম্মতের ইবাদত গুজার লোকদের একত্র করো [অর্থাৎ এমন লোক যারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে একনায়কত্ব সুলভ স্বৈরাচারী আচরণ ও বিদ্রোহাত্মক ভূমিকা গ্রহণকারী নয়।] এবং বিষয়টি পরামর্শের জন্য তাদের সামনে উপস্থিত করো, কিন্তু একজনের মতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিওনা।” [তাফসীরে রুহুল মায়ানী]
রসূলুল্লাহ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিম্নোক্ত বাক্যে ঐ পরামর্শের প্রাণসত্তাকে তুলে ধরেছেন:
“যে ব্যক্তি তার ভাইকে এমন পরামর্শ দান করে, যে সম্পর্কে সে জানে যে যথার্থ বিষয় এর বিপরীত রয়েছে, সে মূলত তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলো।” [আবু দাউদ]
এই হুকুম খুবই ব্যঅপক শব্দে প্রদান করা হয়েছে এবং এখানে শূরার [পরামর্শ পরিষদের] কোনো বিশেষ কাঠামো নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। কারণ ইসলামের বিধান গোটা দুনিয়ার জন্য এবং চিরকালের জন্য। যদি পরামর্শ পরিষদের কোনো বিশেষ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়া হতো তবে তা বিশ্বজনীন, সর্বাত্মক ও স্থায়ী হতে পারতোনা। পরামর্শ পরিষদ কি সরাসরি সমস্ত লোকের সমন্বয়ে গঠিত হবে, না তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে? প্রতিনিধিগণ কি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবেন না বিশিষ্ট লোকদের ভোটে? নির্বাচন কি দেশব্যাপী হবে, না কেবল রাজধানী শহরে হবে? নির্বাচন কি ভোটের আকারে হবে, না এমন লোক প্রতিনিধি হিসেবে নেয়া হবে যারা সমাজে নেতৃস্থানীয়? পরামর্শ পরিষদ কি এক কক্ষ বিশিষ্ট হবে, না দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট? এগুলো এমন কতোগুলো প্রশ্ন যার একটিমাত্র উত্তর প্রত্যেক সমাজ ও প্রতিটি সভ্যতার জন্য একইভাবে যুতসই হতে পারেনা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর বিভিন্নরূপ হতে পারে এবং পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন অবস্থার উদ্ভব হতে পারে। এজন্য ইসলামী শরীয়া বিষয়টিকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়েছে, কোনো বিশেষ কাঠামো নির্দিষ্ট করে দেয়নি এবং কোনো বিশেষ কাঠামো নিষিদ্ধও করেনি। অবশ্য নীতিগতভাবে উপরোক্ত আয়াত এবং তার ব্যাখ্যা প্রদানকারী হাদীসমূহ তিনটি বিষয় বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে:
১. মুসলমানদের কোনো সামাজিক সামষ্টিক কাজ পরামর্শ ব্যতীত সম্পন্ন হওয়া উচিত নয়। এ বিষয়টি রাজতন্ত্রের শিকড় কেটে দেয়। কারণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্র প্রধানের নিয়োগ। অন্যান্য বিষয়ে যদি পরামর্শ গ্রহণ বাধ্যতামূলক হয় তবে জোরপূর্বক রাষ্ট্র প্রধানের পদ দখল কি করে বৈধ হতে পারে? অনুরূপভাবে উপরোক্ত বিষয়টি রাষ্ট্র প্রধানের পদ দলখ কি করে বৈধ হতে পারে? অনুরূপভাবে উপরোক্ত বিষয়টি একনায়কত্বকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। কারণ একনায়কত্বের অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছাচার বা স্বৈরাচার এবং স্বৈরাচার এবং স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচার পরামর্শের পরিপন্থী। অনুরূপভাবে সংবিধানকে সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে স্থগিত বা বাতিল করার এখতিয়ারও এ হুকুমের উপস্থিতিতে রাষ্ট্র প্রধানকে দেয়া যেতে পারেনা। কারণ সংবিধান স্থগিত থাকাকালে অবশ্যই সে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং স্বেচ্ছাচার নিষিদ্ধ।
২. পরামর্শের বিষয়টি যেসব লোকের সামাজিক বা সামষ্টিক কাজের সাথে জড়িত তাদের সকলকে পরামর্শে অংশগ্রহণ করতে হবে, চাই তারা সরাসরি অংশগ্রহণ করুক অথবা নিজেদের বিশ্বস্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করুক।
৩. পরামর্শ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নিষ্ঠাপূর্ণ হতে হবে। শক্তি প্রয়োগে অথবা প্রলোভন দিয়ে ভোট বা পরামর্শ লাভ করা মূলত পরামর্শ গ্রহণ না করারই সমতুল্য।
অতএব সংবিধানের বিস্তারিত রূপ যাই হোক তাতে শরীয়াতের এই তিনটি নীতিমালার প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। কোনো সময় জনগণের অথবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রনিধিগণের পরামর্শ গ্রহণ ব্যতিরেকে রাষ্ট্র পরিচালনার সুযেডাগ সংবিধানে রাখা উচিত নয়। সংবিধানে এরূপ নির্বাচন পদ্ধরি ব্যবস্থা রাখা উচিত যাতে গোটা জাতি পরামর্শে অংশগ্রহণ করতে পারে। জনগণকে অথবা তাদের প্রতিনিধিগণকে ভীতি প্রদর্শন করে অথবা প্রলোভন দিয়ে যাতে তাদের মতামত গ্রহণ করা সম্ভব না হয় তার ব্যবস্থাও সংবিধানে থাকতে হবে।
৫. নির্বাচনের নীতিমালা
রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী পরিষদ সদস্য, পরামরশ পরিষদ সদস্য এবং প্রশাসক নির্বাচনে কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে সে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর দিক নির্দেশনা নিম্নরূক:
“আল্লাহ্ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যেনো তোমরা আমানতসমূহ [অর্থাৎ বিশ্বস্ততার যিম্মাদারী] বিশ্বস্ত লোকদের কাছে সোপর্দ করো।” [সূরা নিসা: ৫৮]
“তোমাদের সে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাধিক সম্মানিত, যে সর্বাধিক খোদাভীরু।” [সূরা হুজরাত: ১৩]
মহানবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেন:
“তোমাদের সর্বোত্তম নেতা হলো সেসব লোক যাদের তোমরা ভালোবাসো এবং তারাও তোমাদেরকে ভালোবাসে, যাদেরকে তোমরা দোয়া করো এবং তারাও তোমাদের জন্র দোয়া করে। তোমাদরে নিকৃষ্টতম নেতা হলো সেসব লোক যাদের তোমরা ঘৃণা করা এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, যাদের তোমরা অভিসম্পাত করো এবং তারাও তোমাদেরকে অভিসম্পাত করে।” [সহীহ মুসলিম] “আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের এ জাতীয় কোনো দায়িত্বে এমন কোনো ব্যক্তিকে নিয়ো করবোনা, যে তা পাওয়ার জন্য আবেদন করে অথবা তা পেতে লালায়িত।” [বুখারী ও মুসলিম]
“আমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় খিয়ানতকারী হলো সে ব্যক্তি যে ঐ পদের প্রার্থী হয়।” [আবু দাউদ]
হাদীস অতিক্রম করে একথা ইতিহাসের পাতায়ও স্থান দখল করে নিয়েছে যে ইসলামের পদে প্রার্থ হওয়া খুবই অপছন্দনীয় কাজ। কালকাশানদী তাঁর সুবহুল আ’আশা গ্রন্থে লিখেছেন:
“হযরত আবু বকর [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু] থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সরকারী পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: হে আবু বকর! এই পদ তার জন্র যার উক্ত পদের প্রতি আকর্ষণ নাই, তার জন্য নয় যে, তা পাওয়ার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তা সে ব্যক্তির জন্য, যে উক্ত পদ এড়ানোর জন্য চেষ্টারত থাকে, তার জন্য নয়, যে তার জন্য ঝাপিয়ে পড়ে। ঐ পদ তার জন্য যাকে বলা হয় যে, এটা তোমার প্রাপ্য; তার জন্য নয় যে বলে, এটা আমার প্রাপ্য।” [১খ পৃঃ ২৪০] [উপরোক্ত বর্ণনাটি হুবহু ঐ শব্দসহযোগে আমরা হাদীসের কিতাবে পাইনি বরং এটা একজন ঐতিহাসিকের বর্ণনা। কিন্তু আমরা তা এজন্য উদ্ধৃত করেছি যে, হাদীসের দুইটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা আমরা উপরে বর্ণনা করেছি। যার সাথে এ বর্ণনার অর্থগত সামঞ্জস্য রয়েছে। এ ধনের দুর্বল রিওয়াতের অনুকূলে সহীহ হাদীস বিদ্যমান থাকলে তা অর্থগত দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে যায়।]
উপরোক্ত দিক নির্দেশনা যদিও কেবল নীতিগত পর্যায়ের এবং তাতে একথা বলা হয়নি যে, বাঞ্ছিত গুণাবলীর অধিকারী নেতা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের এবং অবাঞ্চিত লোকদের প্রতিহত করার হাতিয়ার কি, কিন্তু তথাপি এই দিক নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য যুক্তিসংগত পন্থা বা পদ্ধতি আবিষ্কার করা সমকালীন সংবিধান রচয়িতাদের কাজ। তাদেরকে নির্বাচনের এমন ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে যাতে বিশ্বস্ত ও খোদাভীরু এবং জনগণের প্রিয়জনের ও কল্যাণকামী লোক নির্বাচিত হয়েও জনগণের নিকট ঘৃণার পাত্র, যাদেরকে সর্বত্র থেকে অভিসম্পাত করা হয়, যাদেরকে লোকেরা বদদোয়া করে এবং যাদেরকে সরকারী পদ প্রদান করা হয়না বরং তারা স্বয়ং উক্ত পদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে।
৬. নারীদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ
আল কুরআনে বলা হয়েছে:
“পুরুষরা নারীদের কর্তা।” [সূরা নিসা: ৩৪]
একটি হাদীসে নবী করীম (স) বলেছৈন:
“যে জাতি নিজেদের বিষয়সমূহ নারীদের উপর সোপর্দ করে সে জাতি কখনও সফলকাম হতে পারেনা।”[বুখারী]
উপরোক্ত আয়াত এবং রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী এ বিষয়ে অকাট্য দলীল যে, রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ পদ [তা রাষ্ট্র প্রধানের পদ হোক, অথবা মন্ত্রিত্ব হোক, অথবা সংসদের সদস্যপদ হোক অথবা রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্থার প্রশাসনিক পদ হোক] নারীদের উপর সোপর্দ করা যায়না। তাই কোনো ইসরামী রাষ্ট্রের সংবিধানে নারীদের উপরোক্ত পদে নিয়োগের ব্যবস্থা বা সুযোগ রাখা ঐসব সুস্পষ্ট দলীলের পরিপন্থী।আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য স্বীকারকারী রাষ্ট্র উপরোক্ত মূলনীতির বিরোধিতা করাই মোটেই অধিকার রাখেনা। [বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্য এ গ্রন্থের ১১ নং অধ্যায়ে [কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়] পাঠ করা যেতে পারে।]
৭. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য
মহান আল্লাহ:
“আমরা তাদেরকে [মুসলমানদেরকে] পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কার্য নিষিদ্ধ করবে।” [সূরা হজ্জ: ৪১]
উপরোক্ত আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লাভের উদ্দেশ্য ও তার মৌলিক কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কাফের রাষ্ট্রের মতো তার কাজ কেবল রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা করা, সীমান্তরেখা বরাবর দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা এবং দেশের বৈষয়িক উন্নতির জন্য চেষ্টা করাই নয়, বরং একটি ইসলামী রাস্ট্র হওয়ার সুবাদে তার সর্ব প্রথম কর্তব্য হলো নামায ও যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করা, যেসব বিষয়কে আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কল্যাণকর বলেছেন তার প্রসার ঘটানো এবং যেসব বিষয়কে আল্লাহ্ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বলেছেন তার প্রতিরোধ করা। নামায কায়েম হচ্ছে কি হচ্ছেনা, যাকাত প্রদান হচ্ছে কি হচ্ছেনা, কল্যাণকর বিষয় প্রসার লাভ করছে না পরাভূত হচ্ছে এবং নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর বিষয় পরাভূত হচ্ছে না মাথাচারা দিয়ে উঠছে- এসব ব্যাপারে যে রাস্ট্রের কোন মাথা ব্যথা নাই সে রাস্ট্রকে ইসলামী রাস্ট্র বলা যেতে পারেনা। যে রাস্ট্রের সীমার মধ্যে যেনা, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, অশ্লীল সহিত্য ও পত্র পত্রিকা, অশ্লীল বিনোদন ও আনন্দ-স্ফূর্তি, অশ্লীল গানবাজনা, সহশিক্ষা, জাহিলী যুগের দৈহিক সৌন্দর্য প্রদর্শনী এবং নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার ব্যাপক প্রচলন থাকে এবং এসব সুস্পষ্ট নিষিদ্ধ কার্যাবলীর উপর বিধিনিষেধ আরোপিত নাই, কোনো ধরপাকড় নাই- সে রাস্ট্রের নাম ইসলামী রাস্ট্র রাখা খুবই বেমানান। অতএব একটি ইসলামী সংবিধানে অনিবার্যরূপে ইসলামী রাস্ট্রকে সেসব বিষয়ের অনুসরন করতে বাধ্য করতে হবে যেগুলোকে কুরআন মাজীদ মৌলিক কর্তব্যরূপে নির্ধারন করেছে।
৮. কর্তৃত্ব ও আনুগত্যের নীতিমালা
‘‘হে মুমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান এনে থাকো তবে তোমরা অনুগত্য করো আল্লাহর, অনুগত্য করো রসূলের এবং তোমাদের মধ্যে কতৃত্বের অধিকারী তাদের। অতপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হলে তা আল্লাহ্ ও রসূলের প্রতি সোপর্দ করো। এটাই উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। ”
[সূরা নিসাঃ ৫৯]
উপরোক্ত আয়াতে তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। সাংবিধানিক বিষয়ের সাথে এর প্রত্যেকটির গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান।
বিষয়গুলো নিম্নরূপঃ
১. আল্লাহ্ ও তার রসূলের আনুগত্যই হলো আসল আনুগত্য, প্রত্যেক মুসলমানকে ব্যাক্তি হিসেবে এবং মসলিম উম্মাহকে সমষ্টিগতভাবে আল্লাহ ও তার রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্য অন্য যে কোনো প্রকারের আনুগত্যের তুলনায় অগ্রগণ্য। এরপরে হচ্ছে কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকের আনুগত্য, আগে নয় এবং এই আনুগত্য হবে উপরোক্ত আনুগত্যের অধীনে, স্বাধীন আনুগত্য নয়। এ বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা আমরা কুরআনের নিন্মোক্ত আয়াত ও রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস থেকে পেতে পারি।
‘‘কোনো বিষয়ের মীমাংসা আল্লাহ্ ও তার রসূল করে দিলে আবার সে বিষয়ে কোনো মুমিন পুরুষ বা নারীর নিজস্বভাবে মীমাংসা করার অধিকার নাই। যে কেউ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করলে সে পথভ্রষ্টতায় বহু দূরে চলে যাবে।’’
(সূরা আহযাবঃ ৩৬)
‘‘যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক ফায়সালা করেনা তারা কাফের—তারা যালেম— তার ফাসেক।’’ (সূরা মায়েদাঃ ৪৪,৪৫,৪৭)
‘‘স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় মুসলমানের জন্য {নির্দেশ} শোনাও আনুগত্য করা বাধ্যতামূলক, যতক্ষণ না তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হয়। অতএব তাকে পাপাচারের নির্দেশ দেয়া হলে কোনো শ্রবণও নাই, আনুগত্যও নাই।’’ (বুখারী ও মুসলিম)
‘‘যদি কোনো কর্তিতনাসা ক্রীতদাসকেও তোমাদের শাসক নিযুক্ত করা হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব দান করে তবে তার নির্দেশ শোনো এবং মান্য করো।’’ (সহীহ মুসলিম)
‘‘পাপাচারের বেলায় কোনো আনুগত্য নাই, আনুগত্য কেবল সৎকাজে।’’ (বুখারী ও মুসলিম)
‘‘আল্লাহর অবাধ্যচারীর আনুগত্য করা যাবেনা।’’ (তাবরানী)
‘‘স্রষ্টার নাফরমানী হয় এমন কোনো বিষয়ে সৃস্টির আনুগত্য করা যাবেনা।’’ (শারহুস সুন্নাহ)
কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত অকাট্য দলীলসমূহ চুড়ান্তভাবে বলে দিচ্ছে যে, একটি ইসলামী রাস্ট্রে আইন প্রণয়নকারী সংসদের আল্লাহ্ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানের পরিপন্থি আইন প্রণয়নের কোনোই অধিকার নাই। তারা এরূপ কোনো আইন প্রণয়ন করলে তা সাথে সাথে প্রত্যাখ্যান করতে হবে এবং তা কার্যকর হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবেনা।
অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহ একথাও পরিস্কারভাবে বলে দিচ্ছে যে, একটি ইসলামী রাস্ট্রের বিচারালয়সমূহে আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধানই কার্যকর হতে হবে এবং যে কথা কুরআন ও হাদীসের দলীল দ্বারা সত্য প্রমাণিত হবে তাকে কোনো বিচারক একথা বলে রদ করতে পারবেনা যে, আইন প্রণয়নকারী সংসদের প্রণীত আইন তার পরিপন্থি। বৈপরিত্যের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিধান নয় বরং সংবিধানের সে আইন সংবিধান থেকে খারিজ করে দিতে হবে।
অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে একথাও পরিষ্কার বলে দিয়েছে যে, ইসলামী রাস্ট্রের শাসন বিভাগ এমন কোনো নির্দেশ প্রদানের বা নীতিমালা প্রণয়নের অধিকার রাখেনা যার দ্বারা আল্লাহ্ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানী করা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। প্রশাসন যদি এমন কোনো নির্দেশ দেয় এবং জনগণ তা মান্য না করে তবে তারা অপরাধী সাব্যস্ত হবেনা বরং পক্ষান্তরে স্বয়ং সরকারই বাড়াবাড়ি করছে বলে সাব্যস্ত হবে।
দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইযে, কোনো ইসলামী রাস্ট্রের উলীল আমর তথা কর্ণধার কেবল একজন মুসলমানই হতে পারেন। তার দুইটি প্রমাণ স্বয়ং উপরোক্ত আয়াতেই বিদ্যমান রয়েছ। {এক} ‘‘হে ঈমানদারগণ’’ বলার পর‘ তোমাদের মধ্যে যারা কর্তৃত্বের অধীকারী’’ বলার অর্থ কেবল এ হতে পারে যে, এখানে যে কর্তৃত্বের অধিকারীর আনুগত্য করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে তাকে মুসলমানদের মধ্য থেকেই নিযুক্ত করতে হবে। (দুই) বিরোধের ক্ষেত্রে বিরোধপূর্ণ বিষয়ের মীমাংসার জন্য আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রত্যক্ষ নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আর একথা দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, দেশের নাগরিক ও রাস্ট্রের মধ্যে বিবাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তার রসূলের নির্দেশ কেবল মুসলমান উলীল আমরই (কর্তৃত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি) মানতে পারে, কাফের উলীল আমর মানতে পারেনা। উপরন্তু নির্ভরযোগ্য হাদীসসমূহের বক্তব্যও এর সমর্থন বরং জোর তাকিদ করে। এইমাত্র উপরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে, একটি কর্তিতনাসা ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের আমীর বানানো হয় এবং সে আল্লাহর কিতাব অনুসারে তোমাদের নেতৃত্ব দান করে তবে তার কথা শোনো এবং মান্য করো।’’ আরও এইযে, ‘‘ যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যচারী তার আনুগত্য করা যাবেনা’’। আরও একটি হাদীস হযরত উবাদা ইবনুস সামিত [রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু] বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্মোক্ত বাক্যে আমাদের শপথ করিয়েছেনঃ
‘‘আমরা আমাদের শাসকদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবোনা। কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে প্রকাশ্য কুফরীতে লিপ্ত দেখি, যে সম্পর্কে আমাদের নিকট তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রমাণ রয়েছে। [তবে আমরা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করবো]।’’ [বুখারী ও মসলিম]
অপর এক হাদীসে এসেছে যে, সাহাবায়ে কিরাম [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম] যখন নিকৃষ্ট দুরাচার শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অনুমতি চাইলেন তখন রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ
‘‘না, যতক্ষন তার তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করতে থাকে।’’ [মুসলিম]
উপরোক্ত আলোচনার পর এ বিষযে কোনো সন্দেহ থাকতে পারেনা যে, কোনো ইসলামী রাস্ট্রে কোনো অমুসলিম ব্যক্তির ‘‘উলিল আমর’’ হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। ব্যাপারটি ঠিক এরূপ, যেমন কোনো সমাজতান্ত্রিক রাস্ট্রে সমাজতন্ত্রবাদ প্রত্যাখ্যানকারী কোনো ব্যক্তি কর্নধার হতে পারেনা এবং কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণতন্ত্র বিরোধী কোনো ব্যক্তির যুক্তিসংগতভাবে এবং কার্যত ‘‘উলীল আমর’’ হতে পারেনা।
তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, উপরোক্ত আয়াতের আলোকে দেশের নাগরিকগণের কোনো বিষয়ে রাষ্ট্রপ্রধান বা তার প্রতিনিধিদের সাথে মতভেদে লিপ্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এবং এ ধরনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মীমাংসাকারী হবে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ। এ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সনদ যার অনুকূলেই ফায়সালা দান করবে তা সর্বান্তকরণে মেনে নিতে হবে, সে ফায়সালা উলীল আমরের পক্ষেই হোক অথবা নাগরিকগণের পক্ষেই হোক। এখন পরিষ্কার কথা এইযে, এ নির্দেশের দাবি পূরণের জন্য এমন কোনো প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব থাকতে হবে যার নিকট বিবাদপূর্ণ বিষয় উপস্থাপন করা যেতে পারে এবং যার কাজ হবে আল্লাহর কিতাব ও রসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক বিবাদের মীমাংসা করা। এ পতিষ্ঠান চাই বিশেষজ্ঞ আলেমগণের কমিটি হোক অথবা সুপ্রিম কোর্ট হোক অথবা অনা কোনো কিছু- তার বিশেষ কোনো কাঠামো শরীয়ত আমাদের জন্য নির্ধারণ করে দেয়নি যে, তাই মানতে হবে। কিন্তু যাই হোক, রাষ্ট্রের মধ্যে অনুরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান থাকতে হবে এবং তা এতোটা ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে যে, তার নিকট সরকার, সংসদ বা আইন প্রণয়নকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগের বিধান ও সিদ্ধান্তসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে। এ প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নীতিমালা এই হবে যে, সে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবেক সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মীমাংসা করবে।
৯. মৌলিক অধিকার ও সামাজিক সুবিচার
মহান আল্লাহ বলেনঃ
‘‘আমানত তার প্রকৃত প্রাপকের নিকট পৌছে দেয়ার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আর তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে।’’ [সূরা নিসাঃ ৫৮]
‘‘কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেনো তোমাদেরকে কখনও সুবিচার বর্জনে প্ররোচিত না করে। তোমরা সুবিচার করো, এটা তাকওয়ার নিকটতর।’’ [সূরা মায়েদাঃ ৮]
এই আয়াতদ্বয় যদিও ব্যাপক অর্থে মুসলমানদেরকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে সুবিচার কায়েমের জন্য বাধ্য করে, কিন্তু ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার দাবি থেকে ইসলামী রাষ্ট্রও মুক্ত থাকতে পারেনা। অবশ্যম্ভাবীরূপে ইসলামী রাষ্ট্রকেও ন্যায়বিচার ও সুবিচারের অনুাসরী হওয়া উচিৎ বরং তাকে উত্তমরূপেই তার অনুসারী হতে হবে। কারণ মানুষের মাঝে সর্বাধিক শক্তিশালী বিচারক সংস্থা হচ্চে রাষ্ট্র। অতএব তার আইনে বা ফয়সালায় যদি সুবিচার বিদ্যমান না থাকে তবে সমাজের অন্য কোথাও সুবিচার পাওয়ার আশা করা যায়না।
এখন দেখা যাক, রাষ্ট্র সম্পর্কে যদি আমরা চিন্তা করি তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ও খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ [অনুসৃত কার্যক্রম] থেকে মানুষের মাঝে সুবিচার ও ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠার কি পন্থা ও মূলনীতি পাওয়া যায়।
১. বিদায় হজ্জের সুপ্রসিদ্ধ ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব মৌলিক নীতিমালা ঘোষণা করেছিলেন তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ন মূলনীতি এই ছিল যেঃ
‘‘নিশ্চই তোমাদের জীবন, তোমাদের ধন সম্পদ এবং তোমাদের মান ইজ্জত সেরূপ সন্মানিত যেরূপ সন্মানিত তোমাদের আজকের এই হজ্জের দিনট।’’
এই ঘোষণায় ইসলামী রাস্ট্রের সকল নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর নিরাপত্তা ও মর্যাদার মৌলিক অধিকার প্রদান করা হয়েছে। যে রাষ্ট্র নিজেকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে দাবি করবে তাকেই এসব দিকের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। [উপরোক্ত হাদীসে যদিও মুসলমানদের অধিকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু ইসলামী শরিয়াতের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি এইযে, যে অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীনে বসবাস গ্রহন করে সে ইসলামের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অনুসারে মুসলমানদের অনুরূপ অধিকার লাভ করবে।]
২. এ মর্যাদা কোন অবস্থায় এবং কিভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে? তাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিন্মোক্ত বাক্যে বলে দিয়েছেন
‘‘অতএব লোকেরা যখন একাজ [এবত্ববাদের সাক্ষ, রিসালাতের সাক্ষ, নামায কায়েম, যাকাত প্রদান] করবে তখন তার আমার থেকে তাদের জীবন রক্ষা করে নিলো। কিন্তু ইসলামের কোনো অধিকারের ভিত্তিতে অপরাধী সাব্যস্ত হলে স্বতন্ত্র কথা এবং তাদের নিয়্যত তথা উদ্দেশ্যের হিসাব গ্রহন আল্লাহর যিম্মায়।’’ [বুখারী ও মুসলিম]
‘‘অতএব তাদের জানমাল [তাতে হস্তক্ষেপ] আমার জন্য হারাম। কিন্তু জান ও মালের কোনো অধিকার তাদের উপর বর্তাইলে স্বতন্ত্র কথা। তাদের গোপন বিষয়ের হিসাব আল্লাহর যিম্মায়।’’ [বুখারী ও মুসলিম]
‘‘অতএব যে ব্যক্তি এর [কলেমা তাওহীদের] প্রবক্তা হলো সে আমার থেকে তার মাল ও জান বাঁচিয়ে নিলো। তবে আল্লাহর কোনো অধিকার [কোনো অপরাধের কারণে] তার উপর বর্তাইলে স্বতন্ত্র কথা। তার গোপন বিষয়ের হিসেব আল্লাহর যিম্মায়।’’ [বুখারী]
উল্লেখিত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো নাগরিকের জান মাল ও ইজ্জত আব্রুর উপর হস্তক্ষেপ করা বৈধ নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নাগরিক ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তার উপর [অথবা তার বিরুদ্ধে] কোনো অধিকার প্রমাণিত না হয় অর্থাৎ সে কোনো ব্যাপারে আইনত দোষী সাব্যস্ত না হয় ততক্ষণ তার উপর হস্তক্ষেপ করা যাবেনা।
৩. কোনো নাগরিকের উপর [অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে] কিভাবে অধিকার প্রমাণিত হয়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিন্মোক্ত বাক্যে বর্ণনা করেছেন।
‘‘বাদী ও বিবাদী যখন তোমার সামনে উপস্থিত হবে তখন তুমি যেভাবে এক পক্ষের বক্তব্য শুনেছো সেভাবে অপর পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ না করা পর্যন্ত তাদের মধ্যে ফায়সালা প্রদান করবেনা।’’ [আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ] হযরত ওমর ফারূক [রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু] একটি মোকদ্দমার ফায়সালা করতে গিয়ে বলেনঃ
‘‘ইসলামে ন্যায়সংগত পন্থা ব্যতিত কোনে ব্যক্তিকে আটক করা যায়না।’’ [মূয়াত্তা ইমাম মালিক]
উপরোক্ত হাদীসে যদিও মুসলমানদের অধিকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে, কিন্তু ইসলামী শরিয়াতের একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি এইযে, যে অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীনে বসবাস গ্রহন করে সে ইসলামের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আইন অনুসারে মুসলমানদের অনুরূপ অধিকার লাভ করবে।
আলোচ্য মোকদ্দমার যে বিবরণ উক্ত মুয়াত্তা গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে তা থেকে অবগত হওয়া যায় যে, ইরাকের নব-বিজিত এলাকায় মিথ্যা অভিযোগে লোকদের গেপ্তার করা হতে থাকলে এবং তার বিরুদ্ধে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহুর দরবারে অভিযোগ উথ্থাপিত হলে তিনি তদপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত কথা বলেন। এ বর্ণনা থেকে প্রতিভাত হচ্ছে যে, এখানে ‘‘ন্যায়সংগত পন্থা’’ অর্থ ‘যথাযথ বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম’’ [Due Process of Law] অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণ করতে হবে এবং অপরাধীকে নিজের নির্দোষিতার পক্ষে বক্তব্য রাখার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া ইসলামে কোনো ব্যাক্তিকে আটক করা যায়না।
৪. হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতকালে খারেজী সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হলে, যারা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই প্রস্তুত ছিলোনা, তিনি তাদের লিখে পাঠানঃ
‘‘তোমরা যথায় ইচ্ছা বসবাস করো। আমাদের ও তোমাদের মাঝে শর্ত এইযে, তোমরা খুনখারাবি করবেনা, রাহাজানি করবেনা এবং কারো উপর যুলুম করবেনা। তোমার উপরোক্ত কোনো কাজে লিপ্ত হলে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।’’ [নায়লুল আওতার]
অর্থাৎ তোমরা যে মত ইচ্ছা পোষণ করতে পারো। তোমাদের মতামত ও উদ্দেশ্যের জন্য গ্রেপ্তার করা হবেনা। অবশ্য তোমরা যদি তোমাদের মতামতের প্রেক্ষিতে প্রশাসন যন্ত্র জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা করে তবে অবশ্যই তোমাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
উপরোক্ত আলোচনার পর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকেনা যে, ন্যায় ইনসাফের ইসলামী ধারনা কোনো অবস্থায়ই প্রশাসন বিভাগকে প্রচলিত বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ব্যতিত যথেচ্ছভাবে যাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করার, যাকে ইচ্ছা কয়েদ করার, যাকে ইচ্ছা নির্বাসন দেয়ার, ইচ্ছামতো কারো বাকশক্তি রুদ্ধ করার এবং যাকে ইচ্ছা মতামত প্রকাশের মাধ্যম থেকে বঞ্চিত করার এখতিয়ার প্রদান করেনা। রাষ্ট্র সাধারণভাবে এ ধরনের যেসব এখতিয়ার তার প্রশাসন বিভাগকে দান করে তা ইসলামী রাষ্ট্র কখনও দান করতে পারেনা।
উপরন্তু মানুষের মাঝে মীমাংসা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় ইনসাফের অনুসরণের আরেক অর্থ, যা আমরা ইসলামের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য ঐতিহ্য থেকে জানতে পারি, তা এইযে, ইসলামে রাষ্ট্র প্রধান, গভর্নর, পদস্থ কর্মকর্তা ও সর্বসাধারন সকলের জন্য একই আইন এবং একই বিচার ব্যবস্থা। কারো জন্য কোনো আইনগত স্বাতন্ত্র্য নাই, কারো জন্য বিশেষ আদালত নাই এবং কেউই আইনের হস্তক্ষেপ থেকে ব্যতিক্রম নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ সময়ে নিজেকে এভাবে পেশ করেন, আমার বিরুদ্ধে কারো কোনো দাবি থাকলে সে যেনো তা আদায় করে নেয়। হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়লা আনহু জাবালা ইবনে আইহাম সাসানী নামক গভর্ণরের উপর এক বেদুইনের কিসাসের দাবি পূরণ করেন। হযরত আমর ইবনুর আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্ণরের জন্য আইনগত নিরাপত্ত প্রার্থনা করলে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন এবং জনসাধারনকে গভর্নরদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা প্রকাশ্য আদালতে উথ্থাপনের অধিকার প্রদান করেন।
১০. মহান আল্লাহ বলেনঃ
‘‘তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে।’’ [সূরা যারিয়াতঃ ১৯]
‘‘তাদের সম্পদ থেকে যাকাত ও দান খায়রাত করে তাদেরকে [পুতিগন্ধময় স্বভাব থেকে] পবিত্র করো এবং [পুতপবিত্র স্বভাবেরই উন্মেষ ঘটিয়ে] পবিত্র করো এবং তাদের জন্য কল্যাণের দোয়া করো।’’ [সূরা তাওবাঃ ১০৩]
‘‘আল্লাহ্ তায়ালা মুসলমানদের উপর একটি দান ফরজ করেছেন, যা তাদের সম্পদশালীদের নিকট থেকে আদায় করে তাদের গরীরদের নিকট ফেরত দেয়া হবে।’’ [বুখারী ও মুসলিম]
‘‘যার কোনো পৃষ্ঠপোষক বা অভিভাবক নাই তার অভিভাবক ও পৃষ্ঠপোষক হচ্ছে সরকার।’’ [আবু দাউদ, তিরমিযী, মূসনাদে আহমদ, ইবনে মাজা, দারিমী]
‘‘যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় মারা গেছে এবং তা পরিশোধ করার মতো মাল রেখে যায়নি তার ঋণ পরিশোদের দায়িত্ব আমার [সরকারের]। আর যে ব্যক্তি মাল রেখে মারা গেছে তা তার ওয়ারিশদের প্রাপ্য। ‘’
‘‘অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি ঋণ রেখে গেছে অথবা এমন পোষ্য রেখে গেছে যাদের ধ্বংস হওয়ার আশংকা আছে, তারা যেনো আমার নিকট আসে, আমি তাদের পৃষ্ঠপোষক।’’
‘‘অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি মাল রেখে গেছে তা তার ওয়ারিশদের প্রাপ্য। আর যে ব্যক্তি যিম্মাদারীর বোঝা [অসহায় পোষ্য] রেখে গেছে তা আমাদের [সরকারের] যিম্মায়।’’ [বুখারী ও মুসলিম]
‘‘যার কোনো ওয়ারিশ নাই আমি [সরকার] তার ওয়ারিশ। আমি তার পক্ষ থেকে দিয়াত [রক্তপণ] আদায় করবো এবং তার পরিত্যক্ত মাল নিয়ে নিবো। [আবু দাউদ]
উপরে উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার জানা যায যে, ইসলামী রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি দয়িত্ব হচ্ছে যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা এবং তার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো, তার রাষ্ট্রসীমার মধ্যে কেউ সাহায্যের মুক্ষাপেক্ষী হলে, অন্ন বস্ত্র বঞ্চিত হলে তার সাহায্য করা।
এ হলো সেসব গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিধান যা আমরা কুরআন ও হাদীস থেকে পেয়ে থাকি। কুরআন ও হাদীসে যদিও আরও অনেক সাংবিধানিক দিক নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু যেহেতু তার অধিকতর সম্পর্ক সংবিধানের চেয়ে সাংবিধানিক আইনের সাথে রয়েছে, তাই আমরা সেগুলো এখানে বিবৃত করিনি। এখন সংবিধান সম্পর্কে সামান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিও আমাদের পেশকৃত এসব আয়াত ও হাদীস দেখে স্বয়ং সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন যে, এগুলোর মধ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তিসমূহ পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিনা? যদি কোনো ব্যক্তি আস্থার দাবির পরিবর্তে বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তির সাহায্যে প্রমাণ করতে পারে যে, উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহের সংবিধানের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই; এবং আমাদের বলে দেয় যে, সংবিধানের এমন কোনো কোনো বিষয় [বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নাই, শুধু মৌলিক বিষয়] রয়েছে যার সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস থেকে কোনে পথনির্দেশ পাওয়া যায়না, তাহলে আমরা অবশ্যই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু যদি এটা প্রমাণ করা না যায় যে, যেসব বিষয়ে আমরা উপরে আলোচনা করেছি তা সাংবিধানিক বিষয় নয় এবং একথাও বলা যায় না যে, এসব বিষয় সম্পর্কে কুরআন ও হাদীস আলোকপাত করেনি, তবে এরপর যারা মোনাফিক নয় তাদের জন্য দু’টি বিকল্প রাস্তাই খোলা থাকে। হয় তারা সোজা পথে এসে উপরোক্ত বিধানসমূহ মেনে নিবে এবং দেশের সংবিধানে তা অন্তর্ভুক্ত করে বিস্তারিত বিষয় যথাযথভাবে রচনা করতে থাকবে। নয়তো তারা পরিষ্কার বলে দিবে যে, আমরা না কুরআন মানি আর না হাদীস। আমরা সেই গণতন্ত্রের উপর ঈমান এনেছি, যা আমেরিকা, বৃটেন ও ভারতীয় সংবিধানে পাওয়া যায়। এই দুটি পথের যেটিই তারা অনুসরন করবে তা অবশ্যই মোনাফেকী বর্জিত অকপটে লোকেরই কাজ হতে পারে। এখন কোনো ব্যক্তি সূর্যালোক তার উজ্জল আভা নিয়ে বিচ্ছুরিত হওয়া সত্বেও যদি বলে যে, কোথাও আলো বিদ্যমান নাই তবে তার একথায় জেনগণ ধোঁকায় নিমজ্জিত হোক বা না হোক তার মানমর্যাদা ভুলন্ঠিত হবেই।
নবম অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্রের উদাহরণীয় যুগ
খিলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট্য
আগের অধ্যায়গুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিমালার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার সেই বাস্তব আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শিক ও ঐতিহাসিক প্রতিবেদন পেশ করা হচ্ছে, যার সূচনা করেছিলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলিইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এবং যার ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এ রাষ্ট্রটি ছিল একটি আলোর মিনার। ইসলামের ইতিহাসে মুসলমানরা সবসময় এ থেকে আলো গ্রহন করে আসছে। ইসলাম শুধু একটি আদর্শ রাষ্ট্রের ধারনাই পেশ করেনি বরং সেই সাথে সেই আদর্শ রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠাও করে দেখিয়েছে। একটা দীর্ঘ সময় রাষ্ট্রটি তার পূর্ণ আলোকবর্তিকা নিয়ে প্রতিষ্ঠতও ছিলো। পৃথিবীকে একটি অনন্য আদর্শিক রাষ্ট্র উপহার দেবার এই অবদান কেবল ইসলামেরই। বিশ্বের অন্য কোনো আদর্শের দাবীদাররা তাদের পরিকল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র একদিন এমনকি এক মুহূর্তের জন্যও পৃথিবীকে উপহার দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে ইসলাম অনন্য এবং একক মর্যাদার অধিকারী। – সংকলক
১. নববী যুগ
ইসলামের অভ্যুদয়ের পর যে মুসলিম সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে এবং হিজরতের পর রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে তা যে রাষ্ট্রের রূপ গ্রহন করে, তার ভিত্তি পতিষ্ঠিত ছিল কুরআন মাজীদের রাজনৈতিক শিক্ষার উপর। ইসলামী শাসন ব্যবস্থার নিন্মোক্ত বৈশিষ্ট্য তাকে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করেঃ
একঃ আল্লাহর আইনের কর্তৃত্ব
এ রাষ্ট্রে প্রথম মূলনীতি ছিলো এইযে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই সার্বভৌমত্বের অধিকারী এবং ঈমানদারদের শাসন হচ্ছে মূলত খিলাফত বা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বশীল শাসন। কাজেই বলগাহীনভাবে কাজ করার তার কোনো অধিকার নেই। বরং আল্লাহর কিতাব ও তার রসূলের সুন্নাহর উৎস থেকে উৎসারিত আল্লাহর আইনের অধীনে কাজ করা তার অপরিহার্য কর্তব্য। কুরআন মাজীদের যেসব আয়াতে এ মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে আগের অধ্যায়ে আমরা তা উল্লেখ করেছি। তন্মধ্যে বিশেষ করে নিন্মোক্ত আয়াতগুলো এব্যাপারে একান্ত স্পষ্টঃ
সূরা নিসাঃ ৫৯, ৬৪, ৬৫, ৮০, ১০৫; আল-মায়েদাঃ ৪৪, ৪৫, ৪৭; আল-আরাফঃ ৩; ইউসুফঃ ৪০; আন-নূরঃ ৫৪, ৫৫; আল-আহযাবঃ ৩৬ এবং আল-হাশরঃ ৭।
নবী সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার অসংখ্য বাণীতে এ মূলনীতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেনঃ
‘‘আল্লাহর কিতাব মেনে চলা তোমাদের জন্য অপরিহার্য। আল্লাহর কিতাব যা হালাল করে দিয়েছে, তোমরা তাকে হালাল মানো, আর যা হারাম করেছে, তোমরা তাকে হারাম করো।’’ [কানযূল ওম্মাল, ত্বাবরানী এবং মুসনাদে আহমদের উদ্ধৃতিতে, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৯০৭-৯৬৬; দায়েরাতুল মায়ারেফ, হায়দারাবাদ সংস্করণ ১৯৫৫]
‘‘আল্লাহ্ তায়ালা কিছু করণীয় নির্ধারন করে দিয়েছন, তোমরা তা নষ্ট করোনা, কিছু হারাম বিষয় নির্দিষ্ট করেছেন, তোমরা তাতে ঢুকে পড়োনা, কিছু সীমা নির্ধারন করেছেন, তোমরা তা অতিক্রম করোনা, ভুল না করেও কিছু ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করেছেন, তোমরা তার সন্ধানে পড়োনা। ’’ [মিশকাত, দারেকুতনীর উদ্ধৃতিতে-বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন]
‘‘যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব মেনে চলে, সে দুনিয়ায় পথভ্রষ্ট হবেনা, পরকালেও হবেনা সে হতভাগা।’’[ মিশকাত, রাযীন-এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখিত অধ্যায়।]
‘‘আমি তোমাদের মধ্যে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যতক্ষণ তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে থাকবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবেনা,- আল্লাহর কিতাব এবং তার রসূলের সুন্নহ।’’[ মিশকাত মুয়াত্তর উদ্ধৃতিতে, আলোচ্য অধ্যায়, কানযুল ওম্মাল, ১ম খন্ড হাদীস নং-৮৭৭, ৯৪৯, ৯৫৫, ১০০১।]
‘‘আমি তোমাদেরকে যে বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছি, তা গ্রহণ করো, আর যে বিষয় থেকে বারণ করেছি, তা থেকে তোমরা বিরত থাকো।’’[ কানযুল ওম্মাল, ১ম খন্ড, হাদীস নং-৮৮৬।]
দুইঃ সকল মানুষের প্রতি সুবিচার
দ্বিতীয় যে মূলনীতির ওপর সে রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তা ছিলো, কুরআন সুন্নাহর দেয়া আইন সকলের জন্য সমান, রাষ্ট্রের সামান্যতম ব্যক্তি থেকে শুরু করে রাষ্ট পধান পর্যন্ত সকলের উপর তা সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে। তাতে কারো জন্য কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর নবীকে একথা ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছেনঃ
‘এবং তোমাদের মধ্যে সুবিচার কায়েম করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।’’ [সূরা আশ শূরাঃ১৫]
অর্থাৎ পক্ষপাতমুক্ত সুবিচার নীতি অবলম্বন করার জন্য আমি আদিষ্ট ও নিয়োজিত। পক্ষপাতিত্বের নীতি অবলম্বন করে কারো পক্ষে বা বিপক্ষে যাওয়া আমার কাজ নয়। সকল মানুষের সাথে আমার সমান সম্পর্ক- আর তা হচ্ছে আদল ও সুবিচারের সম্পর্ক। সত্য যার পক্ষে, আমি তার সাথী; সত্য যার বিরুদ্ধে, আমি তার বিরোধী। আমার দীনে কারো জন্য কোনো পার্থক্যমূলক ব্যবহারের অবকাশ নেই । আপন পর, ছোট বড়, শরীফ কমীনের জন্য পৃথক পৃথক অধিকার সংরক্ষিত নেই। যা সত্য তা সকলের জন্যই সত্য; যা গুনাহ, তা সকলের জন্যই গুনাহ; যা হারাম, তা সকলের জন্যই হারাম; যা হালাল, তা সকলের জন্যই হালাল; যা ফরয, তা সকলের জন্যই ফরয। আল্লাহর আইনের এ সর্বব্যাপী প্রভাব থেকে আমার নিজের সত্বাও মুক্ত নয়, নয় ব্যতিক্রম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেনঃ ‘‘ তোমাদের পূর্বে যেসব উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে, তারা এজন্য ধ্বংস হয়েছে যে, নিন্ম পর্যায়ের অপরাধীদেরকে আইন অনুযায়ী শাস্তি দান করতো, আর উচ্চ পর্যায়ের অপরাধীদেরকে ছেড়ে দিত। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মদের প্রাণ নিহিত,[মুহাম্মদের আপন কন্যা] ফাতেমাও যদি চুরি করতো, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে ফেরতাম।’’[ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, অধ্যায়১১-১২।]
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ
‘‘আমি নিজে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আপন সত্তা থেকে প্রতিশোধ গহন করতে দেখেছি।’’[ কিতাবুল খারাজ, ইমাম আবু ইউসুফ, পৃষ্ঠা-১১৬, আল মাতবায়াতুস সলফিয়া, মিসর, ২য় সংস্করণ, ১৩৫২ হিঃ মুসনাদে আবু দাউদ]
তিনঃ মুসলমানদের মধ্যে সাম্য
এ রাষ্ট্রের তৃতীয় মূলনীতি ছিলো, বংশ, বর্ণ, ভাষা এবং দেশকাল নির্বিশেষে সকল মুসলমানের অধিকার সমান। এ রাষ্ট্রের পরিসীমায় কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, দল, বংশ বা জাতি কোনো বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারেনা, অন্যের মুকাবিলায় করো মর্যাদা খাটোও হতে পারেনা ।
কুরআন মাজীদে আল্লাহ্ তায়ালা বলেনঃ
‘‘মুমিনরা একে অন্যের ভাই।’’ [সূরা হুজরাতঃ১০]
‘‘হে মানব মন্ডলী! এক পুরুষ এবং এক নারী থেকে আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। আর তোমাদের নানা গোত্র, নানা জাতিতে বিভক্ত করেছি, যেনো তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো। মূলত আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সন্মানার্হ, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করে।’’ [সূরা হুজরাতঃ ১৩]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্মোক্ত উক্তি এ মূলনীতিকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছেঃ
‘‘আল্লাহ তোমাদের চেহারা এবং ধন সম্পদের দিকে তাকাননা বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও কার্যাবলীর দিকে তাকান।’’[তাফসীরে ইবনে কাসীর, মুসলিম এবং ইবনে মাজার উদ্ধৃতিতে, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭, মুস্তফা মুহাম্মাদ প্রেস, মিসর-১৯৩৭।]
‘‘মুসলমানরা ভাই ভাই । একজনের উপর অন্যজনের কোনো মর্যাদা নেই কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে।’’[ তাফসীরে ইবনে কাসীর, তিবরানীর উদ্ধৃতিতে, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৭ ]
‘‘হে মানব জাতি! শোনো, তোমাদের রব এক। অনারবের উপর আরবের বা আরবের উপর অনারবের কোনো মর্যাদা নেই। সাদার ওপর কালোর বা কালোর উপর সাদারও নেই কোনো শ্রেষ্ঠত্ব। হাঁ, অবশ্য তাকওয়ার বিচারে।’’[ তাফসীরে রুহুল মায়ানী, বয়হাকী এবং ইবনে মারদুইয়ার উদ্ধৃতিতে ২৬শ খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৮, ইদারাতুল তাবয়াতিল মুনিরিয়া, মিসর।]
‘‘যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, আমাদের কেবলার দিকে মুখ করে, আমাদের মতো সালাত আদায় করে, আমাদের জবাই করা জন্তু খায়, সে মুসলমান। মুসলমানের যে অধিকার, তারও সে অধিকার, মুসলমানের যে কর্তব্য, তারও সে কর্তব্য।’’[ বুখারী কিতাবুস সালাত, অধ্যায়-২৮।]
‘‘সকল মুমিনের রক্তের মর্যাদা সমান, অন্যের মুকাবিলায় তারা সবাই এক। তাদের একজন সামান্যতম ব্যক্তিও তাদের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নিতে পারে।’’[আবু দাউদ, কিতাবুদ দিয়াত, অধ্যায়-১ , নাসায়ী, কিতাবুন কাসামাত, অধ্যায়-১০, ১৪।]
‘‘মুসলমানদের উপর জিযিয়া আরোপ করা যেতে পারেনা।’’[ আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৩৪।]
চারঃ সরকারের দায়িত্ব ও জবাবদিহি
এ রাষ্ট্রের চতুর্থ গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল, শাসন কর্তৃত্ব এবং তার ক্ষমতা ইখতিয়ার ও অর্থ সম্পদ আল্লাহ এবং মুসলমানদের আমানত। আল্লাহভীরু, ঈমানদার এবং ন্যায়পরায়ণ লোকদের হাতে তা ন্যস্ত করতে হবে। কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছামতো বা স্বার্থবুদ্ধি প্রোণোদিত হয়ে এ আমানতে খেয়ানত করার অধিকার রাখেনা। এ আমানত যাদের সোপর্দ করা হবে তারা এজন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেনঃ
‘‘আমানত বহনের যোগ্য ব্যক্তিদের হাতে আমানত সোপর্দ করার জন্য আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। আন যখন মানুষের মধ্যে ফায়সালা করবে ন্যায়নীতির সাথে ফায়সালা করবে আল্লাহ্ তোমাদের ভালো উপদেশ দিচ্ছেন। নিশ্চই আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন। [সূরা নিসাঃ ৫৮]
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
‘‘সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় নেতা-যিনি সকলের উপর শাসক হন তিনিও দায়িত্বশীল তাঁকেও তাঁর সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।’’[ বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-১। মুসলিম কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৫।]
‘‘মুসলিম প্রজাদের কাজ করাবারের প্রধান দায়িত্বশীল কোনো শাসক যদি তাদের সাথে প্রতারণা এবং খিয়ানতকারী অবস্থায় মারা যায় তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।’’[বুখারী, কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-৮। মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-৬১; কিতাবুর ইমারাত, অধ্যায়-৫।]
‘‘মুসলিম রাষ্ট্রের কোনো পদাধিকারী শাসক যে নিজের পদের দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রাণপণ চেষ্ঠা সাধনা করেনা, নিষ্ঠার সাথে কাজ করেনা; সে কখনো মুসলমানদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা।’’[ মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, অধ্যায়-৫।]
[নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যরকে বলেন] ‘‘আবু যর। তুমি দুর্বল মানুষ, আর সরকারের পদ মর্যাদা একটি আমানত। কিয়ামতের দিন তা লজ্জা এবং অপমানের কারণ হবে; অবশ্য তার জন্য নয়, যে পুরোপুরি তার হক আদায় করে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে।’’ [ কানযুল ওম্মাল, ষষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৩৮, ১২২।]
‘‘শাসকের জন্য আপন প্রজাদের মধ্যে ব্যবসা করা সবচেয়ে নিকৃষ্ট খিয়ানত।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৭৮।]
‘‘যে ব্যক্তি আমাদের রাষ্ট্রের কোনো পদ গ্রহন করে, তার স্ত্রী না থাকলে বিবাহ করবে, খাদেম না থাকলে একজন খাদেম গ্রহন করবে, ঘর না থাকলে একখানা ঘর করে নেবে,[যাতায়াতের] বাহন না থাকলে একটা বাহন গ্রহন করবে। যে ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হয়, সে খিয়ানতকারী অথবা চোর।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৩৪৬।]
হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ
‘‘যে ব্যক্তি শাসক হবে, তাকে সবচেয়ে কঠিন হিসেব দিতে হবে, আর সে সবচেয়ে কঠিন আযাবের আশংকায় পতিত হবে। আর যে ব্যক্তি শাসক হবেনা, তাকে হালকা হিসেব দিতে হবে, তার জন্য হালকা আযাবের আশংকা আছে। কারণ শাসকের দ্বারা মুসলমানদের উপর যুলুমের সম্ভবনা অনেক বেশী। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের উপর যুলুম করে, সে আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২৫০৫।]
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ
‘‘ফোরাত নদীর তীরে যদি একটি বকরীর বাচ্চা ধ্বংস হয় তবে আমার ভয় হচ্ছে, আল্লাহ আমাকে সে জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।’’[কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড হাদীস নং-২৫১২।]
পাঁচঃ শূরা বা পরামর্শ
এ রাষ্ট্রের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিলো মুসলমানদের পরামর্শ এবং তাদের পারস্পরিক সম্মতিক্রমে রাষ্ট্র প্রধান নিযুক্ত হতে হবে। তাঁকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পরিচালনাও করতে হবে পরামর্শের ভিত্তিতে। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছেঃ
‘‘আর মুসলমানদের কাজকর্ম [সম্পন্ন হয়] পারস্পরিক পরামর্শক্রমে।’’[সূরা শূরাঃ ৩৮]
‘‘হে নবী! কাজ কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।’’[সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯]
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করি যে, আপনার পর আমাদের সামনে যদি এমন কোনে বিষয় উপস্থিত হয়, যে সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশ না থাকে এবং আপনার কাছ থেকেও সে ব্যাপারে আমরা কিছু না শুনে থাকি, তখন আমরা কি করবো? তিনি বলেনঃ
‘‘এ ব্যাপারে দীনের জ্ঞান সম্পন্ন এবং ইবাদত গুযার ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করো এবং কোনো ব্যক্তি বিশেষের রায় অনুযায়ী ফায়সালা করবেনা।’’[২২. হাদীসে ইবাদতগুযার অর্থে এমনসব ব্যক্তিদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর বন্দেগী করে, স্বাধীনভাবে নিজের মনমতো কাজ করেনা। এ থেকে এই অর্থ গ্রহন করা ঠিক নয় যে, যাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহন করা হবে, কেবল তাদের ইবাদতগুযারীর গুণটি দেখে নেয়া হবে; মতামত এবং পরামর্শ দানের যোগ্যতা সম্পন্ন হওয়ার জন্য অন্যান্য যেসব গুনাবলী প্রয়োজন, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হবেনা।]
হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ
‘‘মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া যে ব্যক্তি তার নিজের বা অন্য কারো নেতৃত্বের [ইমারাত] প্রতি আহবান জানায়, তাকে হত্যা না করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৭৭। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এ উক্তির তাৎপর্য এই যে, ইসলামী রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তির জোর পূর্বক চেপে বসার চেষ্টা করা এক মারাত্নক অপরাধ, তা বরদাস্ত করা উম্মতের উচিত নয়।]
অপর এক বর্ণনায় হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এ উক্তি বর্ণিত আছেঃ
‘‘পরামর্শ ব্যতীত কোনো খেলাফত নেই।’’[২৪. কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৩৫৪।]
ছয়ঃ ভালো কাজে আনুগত্য
৬ষ্ঠ মূলনীতি-যার ওপর এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল-এই ছিল যে, কেবল মাত্র মারুফ বা ভালো কাজেই সরকারের আনুগত্য অপরিহার্য। পাপাচারে [মা’সিয়াত] আনুগত্য পাওয়ার অধিকার কারোর নেই। অন্য কথায়, এ মূলনীতির তাৎপর্য এই যে, সরকার এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কেবল সেসব নির্দেশই তাদের অধীন ব্যক্তিবর্গ এবং প্রজাবৃন্দের জন্য মেনে চলা ওয়াজিব, যা আইনানুগ। আইনের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেয়ার তাদের কোনো অধিকার নেই; তা মেনে চলাও কারো উচিত নয়। কুরআন মাজীদে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাইয়াত- আনুগত্যের শপথ গ্রহনকেও মারুফে আনুগত্যের শর্তে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাঁর পক্ষে কোনো মা’সিয়াত বা পাপাচারের নির্দেশ আসার প্রশ্নই ওঠেনাঃ
‘‘এবং কোনো মারুফ কাজে তারা তোমার নাফরমানী-অবাধ্যতা করবেনা (সূরা মুমতাহানাঃ ১২)
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা বলেনঃ
‘‘একজন মুসলমানের উপর তার আমীরের আনুগত্য করা শোনা এবং মেনে চলা ফরয; তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যতক্ষণ তাকে কোনো মা’সিয়াত বা পাপাচারের নির্দেশ না দেয় হয়। মা’সিয়াতের নির্দেশ দেয়া হলে কোনো আনুগত্য নেই।’’[বুখারী কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-৪ মুসলিম, কিতাবুল এমারত, অধ্যায়-৮। আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়-৯৫। নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৩। ইবনে মাজা, আবওয়াবুল জিহাদ, অধ্যায়-৪০।]
‘‘আল্লাহর নাফরমানীতে কোনো আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মারুফ কাজে।’’[ মুসলিম, কিতাবুল এমারত, অধ্যায়-৮ আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ, অধ্যায়-৯৫। নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৩]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন উক্তিতে বিভিন্নভাবে এ বিষয়টি উল্লেখিত হয়েছে। কোথাও তিনি বলেছেনঃ
‘‘যে আল্লাহর নাফরমানী করে, তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই,’’ কখনো বলেছেনঃ স্রষ্ট্রার নাফরমানীতে সৃষ্টির কোনো আনুগত্য নেই,’’ কখনো বলেছেনঃ ‘‘যে আল্লাহর আনুগত্য করেনা তার জন্য কোনো আনুগত্য নেই, কখনো বলেছেনঃ ‘’যে শাসক তোমাকে তোমাকে কোনো মা’সিয়াতের নির্দেশ দেয়, তার আনুগত্য করোনা।’’[ কানযুল ওম্মাল ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৯, ৩০১।]
হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার এক ভাষনে বলেনঃ
‘‘যে ব্যক্তিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কোনো কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, কিন্তু সে লোকদের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী কাজ করেনি, তার উপর আল্লাহর অভিসস্পাত।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫০৫।]
একারনেই খলীফা হওয়ার পর তিনি তাঁর প্রথম ভাষনেই ঘোষনা করেছিলেনঃ
‘‘যতক্ষণ আমি আল্লাহ এবং তার রসূলের আনুগত্য করি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। যখন আমি আল্লাহ্ এবং তার রাসূলের অবাধ্য হবো, তখন তোমাদের উপর আমার কোনো আনুগত্য নেই।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২২২৮। অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শব্দগুলো এইঃ আর আমি যদি আল্লাহর নাফরমানী করি, তাহলে তোমরা আমার নাফরমানী করো। কানযুল উম্মাল ৫ম খন্ড, হাদীস-২৩৩০।]
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ
‘‘আল্লাহর নাযিল করা বিধান অনুযায়ী ফায়সালা করা এবং আমানত আদায় করে দেয়া মুসলমানদের শাসকের উপর ফরয। শাসক যখন এভাবে কাজ করে তখন তা শুনা ও মেনে চলা এবং তদেরকে আহ্বান জানালে তাতে সাড়া দেয়া লোকদের কর্তব্য।’’[ কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৩১।]
একদা তিনি তার এক ভাষণে বলেছিলেনঃ
‘‘আল্লাহর আনুগত্য করে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তা মেনে চলা তোমাদের উপর ফরয-সে নির্দেশ তোমাদের পছন্দ হোক বা না হোক। আর আল্লাহর অবাধ্য হয়ে আমি তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেই, তাতে আল্লাহর সাথে মা,সিয়াত বা পাপাচারের ক্ষেত্রে কারো জন্য আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল মারুফে, আনুগত্য কেবল মারুফে, আনুগত্য কেবল মারুফে।’’[ কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৫৮৭।]
সাতঃ পদমর্যাদার দাবী এবং লোভ নিষিদ্ধ
এটাও সে রাষ্ট্রের অন্যতম মূলনীতি ছিলো যে, সাধারনত রাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণে পদ বিশেষত খেলাফতের জন্য সে ব্যক্তি বেশী অযোগ্যে-অনুপযুক্ত, যে নিজে পদ লাভের অভিলাষী এবং সে জন্য সচেষ্ট।
আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে বলেনঃ
‘‘আখেরাতের ঘর আমি তাদেরকে দেবো, যারা জমিনে নিজের মহত্ত্ব খুঁজে বেড়ায়না, বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায়না।’’ [সূরা কাসাসঃ ৮৩]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
‘‘আল্লাহর শপথ, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা এ সরকারের পদ মর্যাদা দেইনা, যে তা চায় এবং তার জন্য লোভ করে।’’[বুখারী কিতাবুল আহকাম, অধ্যায়-৭। মুসলিম কিতাবুল এমারত, অধ্যায়-৩।]
‘‘যে ব্যক্তি নিজে তা সন্ধান করে, আমাদের নিকট সে-ই সবচেয়ে বেশী খেয়ানতকারী।’’[ আবু দাউদ, কিতাবুল এমারাত, অধ্যায়-২]
‘‘আমরা এমন কোনো ব্যক্তিকে আমাদের সরকারী কর্মচারী হিসেবে গ্রহন করিনা, যে নিজে উক্ত পদের অভিলাষী।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড,হাদীস নং ২০৬।]
‘‘আবদুর রহমান ইবনে সামুরা রাদিয়াল্লহু তায়ালা আনহুকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবদুর রহমান সরকারী পদ দাবী করোনা। কেননা চেষ্টা তদবীর করার পর যদি তা তোমাকে দেয়া হয়, তবে তোমাকে তার হাতে সঁপে দেয়া হবে, আর যদি চেষ্টা তদবীর ছাড়াই তা লাভ করো, তবে তার হক আদায় করার ব্যপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে সাহায্য করা হবে।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২০৬। এখানে কারো যেন সন্দেহ না হয় যে, এটা যদি মূলনীতি হয়ে থাকে, তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিশরের বাদশার নিকট সরকারের পদ দাবী করলেন কেনো? মূলত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে এ পদ দাবী করেননি, দাবী করেছিলেন এক কাফের রাষ্ট্রে কাফের সরকারের কাছে। যেখানে এক বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক সন্ধিক্ষণে তিনি উপলব্ধি করেন যে, আমি যদি বাদশার নিকট রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ দাবী করি, তবে তা পেতে পারি। আর তার মাধ্যমে এদেশে আল্লাহর দীন বিস্তার করার পথ সুগম হতে পারে। কিন্তু আমি যদি ক্ষমতার দাবী থেকে বিরত থাকি, তাহলে কাফের জাতির হিদায়াতের যে দুর্লভ সুযোগ আমি পাচ্ছি, তা হাত ছাড়া হয়ে যাবে। এটা ছিল এক বিশেষ পরিস্হিতি, তার উপর ইসলামের নিয়ম আরোপ করা যায়না।]
আটঃ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ
এ রাষ্ট্রের শাসক এবং তার সরকারের সর্ব প্রথম কর্তব্য এই সাব্যস্ত হয়েছিল যে, কোনো রকম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ছাড়াই যথাযথভাবে সে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করবে, ইসলামের চারিত্রিক মানদন্ডানুযায়ী ভালো ও সৎ-গুণাবলীর বিকাশ এবং মন্দ ও অসৎ গুনাবলীর বিনাশ সাধন করবে। কুরআন মাজীদে এ রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ
‘‘[মুসলমান তারা] যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, ভালো কাজের নির্দেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।’’[সূরা হজ্জঃ৪১]
কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলিম মিল্লাতের অস্তিত্বের মূল লক্ষও এটিইঃ
‘‘এমনি করে আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী উম্মত [বা ভারসাম্যপূর্ণ পথে অবিচল উম্মাত] করেছি, যেনো তোমরা লোকদের উপর সাক্ষী হও আর রাসূল সাক্ষী হন তোমাদের ওপর।’’[সূরা বাকারাঃ ১৪৩]
‘‘তোমরা যে সর্বোত্তম উম্মাত, মানুষের [সংশোধন এবং পথ প্রদর্শনের] জন্য যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের নির্দেশ দেবে, মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।’’
এতদ্ব্যতীত যে কাজের জন্য মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার পূর্বেকার সকল নবী-রাসূল আদিষ্ট ছিলেন, কুরআনের দৃষ্টিতে তা ছিলো এইঃ
‘‘দীন কায়েম করো এবং তাতে বিচ্ছিন্ন হয়োনা।’’ [সূরা শূরাঃ ১৩]
অমুসলিম বিশ্বের মুকাবিলায় তার সকল চেষ্টা সাধনাই ছিলো এ উদ্দেশ্যেঃ
‘‘দীন যেনো সর্বতোভাবে আল্লাহর জন্যই নির্ধারিত হয়ে যায়।’’ (সূরা আনফাল ৩৯)
অন্যান্য সকল নবী রসূলের মতো তার ইম্মতের জন্যও আল্লাহর নির্দেশ ছিলোঃ
‘‘তারা নিজের দীনকে একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত করে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর বন্দেগী করবে।’’ [সূরা বাইয়েনাঃ ৫]
এজন্য তার প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সর্বপ্রথম কাজ ছিলো, দীনের পরিপূর্ণ ব্যবস্থাকে কায়েম করা, তার মধ্যে এমন কোনো সংমিশ্রণ হতে না দেয়া, যা মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী নীতি সৃষ্টি করে। এ শেষ বিষয়টি সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবী এবং স্থলাভিষিক্তদের কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছিলেনঃ
‘‘আমাদের এ দীনে যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয় উদ্ভাবন করবে, যা তার পর্যায়ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।’’[ মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।]
‘‘সাবধান! নব উদ্ভাবিত বিষয় থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সকল নব উদ্ভাবিত বিষয়ই বিদয়াত, আর সকল বিদয়াতই গুমরাহী, পথ ভ্রষ্ঠতার অন্তর্ভুক্ত।’’ [মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।]
‘‘যে ব্যক্তি কোনো বিদআত উদ্ভাবকের সন্মাক করে, সে ইসলামের মূলোৎপাটনে সাহায্য করে।’’[মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।]
এ প্রসংগে আমরা তাঁর এ উক্তিও দেখতে পাই যে, তিন ব্যক্তি আল্লাহর সবচেয়ে বেশী না-পছন্দ, তাদের একজন হচ্ছে সে ব্যক্তিঃ
‘‘যে ইসলামে কোনো জাহেলী রীতিনীতির প্রচলন করতে চায়।’’[ মিশকাত, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবে ওয়াস সুন্নাহ।]
নয়ঃ আমর বিল মারুফ ও নাহই আনিল মুনকারের অধিকার এবং কর্তব্য
এ রাষ্ট্রের সর্বশেষ মূলনীতি যা তাকে সঠিক পথে টিকিয়ে রাখার নিশ্চয়তা দেয় তা ছিলো, মুসলিম সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি সত্যবাক্য উচ্চারণ করবে, নেকী ও কল্যানের সহায়তা করবে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই কোনো ভুল এবং অন্যায় কার্য হতে কেখবে, সেখানেই তাকে প্রতিহত করতে নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করে চেষ্টা করবে। মুসলিম সমাজের প্রতিটি সদস্যের এটা শুধু অধিকারই নয়, অপরিহার্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের নির্দেশ হচ্ছেঃ
‘‘নেকী এবং তাকওয়ার কাজে পরস্পর সাহায্য করো এবং গুনাহ ও অবাধ্যতার কাজে সাহায্য করোনা।’’ {সূরা মায়েদাঃ ২}
ঈমানদাররা! আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। {আহযাবঃ ৭০}
‘‘ঈমানদাররা! তোমরা সকলে ন্যায় বিচারে অটল অবিচল থাকো এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষদাতা হও, তোমাদের সাক্ষ্য স্বয়ং তোমাদের নিজেদের বা তোমাদের পিতা মাতা বা নিকটাত্নীয়দের বিরুদ্ধে যাকনা কেন।’’ {সূরা নিসাঃ ১৩৫}
‘‘মুনাফিক নারী পুরুষ একই থলের বিড়াল, তারা মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়, ভালো কাজ থেকে বারণ করে। আর মুমিন নারী পুরুষ একে অন্যের সাথী, তারা ভালো কাজের নির্দেশ দান করে আর মন্দ কাজ থেকে বারণ করে।’’ {সূরা তাওবাঃ ৬৭-৭১}
আল কুরআনে ঈমানদারদের এ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য উক্ত হয়েছেঃ
‘‘তারা নেকীর নির্দেশ দানকারী মন্দ কাজ থেকে বারণকারী এবং আল্লাহর সীমারেখা সংরক্ষণকারী।’’ {সূরা তাওবাঃ ১১২}
এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হলোঃ
‘‘তোমাদের কেউ যদি কোনো মুনকার {অসৎ কাজ} দেখে, তবে তার উচিত হাত দিয়ে তা প্রতিহত করা। তা যদি না পারে, তবে মুখ দ্বারা বারণ করবে, তাও যদি না পারে, তবে অন্তর দ্বারা {খারাপ জানবে এবং বারণ করার আগ্রহ রাখবে}, আর এটা হচ্চে ঈমানের দুর্বলতম পর্যায়।’’[ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায় -২০ । তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়-১২। আবু দাউদ; কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭ ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়-২০।]
‘‘অতঃপর অযোগ্য লোকেরা তাদের স্হানে বসবে। তারা এমনসব কথা বলবে, যা নিজেরা করবেনা, এমনসব কাজ করবে, যার নির্দেশ দেয়া হয়নি তাদেরকে। যে হাতের সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন; যে জিহ্বার সাহায্যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন; অন্তর দিয়ে যে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে, সে মুমিন। ঈমানের এর চেয়ে ক্ষুদ্র সামান্যতম পর্যায়ও নেই।’’[ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়-২০]
‘‘যালেম শাসকের সামনে ন্যায় {বা সত্য কথা} বলা সর্বোত্তম জিহাদ।’’[আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়-১২। নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৬। ইবনে মাজা, আবওয়াবুল ফিতান, অধ্যায়-২০]
‘‘যালেমকে দেখেও যারা তার হাত ধরেনা {বাধা দেয়না} তাদের উপর আল্লাহর আযাব প্রেরণ করা দূরে নয়।’’[ আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহেম, অধ্যায়-১৭। তিরমিযী, কিতাবুল ফিতান, অধ্যায়-১২।]
‘‘আমার পর কিছু লোক শাসক হবে। যে ব্যক্তি মিথ্যার ব্যাপারে তাদেরকে সাহায্য করবে, সে আমার নয় এবং আমি তার নই।’’[নাসায়ী, কিতাবুল বাইয়াত, অধ্যায়-৩৪-৩৫।]
‘‘অনতিবিলম্বে এমনসব লোক তোমাদের ওপর শাসক হবে, যাদের হাতে থাকবে তোমাদের জীবিকা, তারা তোমাদের সাথে কথা বললে মিথ্যা বলবে, কাজ করলে খারাপ কাজ করবে। তোমরা যতক্ষণ তাদের মন্দ কাজের প্রশংসা না করবে, তাদের মিথ্যায় বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ তারা তোমাদের ওপর সন্তুষ্ট হবেনা।
সত্যকে বরদাশত করা পর্যন্ত তোমরা তাদের সামনে সত্য পেশ করে যাও। তারপর যদি তারা সীমালংঘন করে যায়, তাহলে যে ব্যক্তি এজন্য নিহত হবে, সে শহীদ।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-২৯৭।]
‘‘যে ব্যক্তি কোনো শাসককে রাযী করার জন্য এমন কথা বলে, যা তার প্রতিপালককে নারায করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর দীন থেকে খারিজ হয়ে গিয়েছে।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৬ষ্ঠ খন্ড, হাদীস নং-৩০৯।]
২. খিলাফতে রাশেদা ও তার বৈশিষ্ট
আগের অধ্যায়ে ইসলামের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শাসন নীতি বিবৃত হয়েছে, তাঁর পরে সেসব মূলনীতির ওপর খোলাফাফে রাশেদীনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যক্ষ শিক্ষা দীক্ষা ও কার্যকর নেতৃত্বের ভিত্তিতে যে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, তার প্রত্যেক সদস্যই জানতো, ইসলামের বিধি বিধান ও প্রাণসত্তা অনুযায়ী কোন ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়া উচিত। নিজের স্থলাভিষিক্তের ব্যাপারে হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো ফায়সালা না দিয়ে গেলেও ইসলাম একটি শূরাভিত্তিক খিলাফত দাবী করে, মুসলিম সমাজের সদস্যরা এ কথা অবগত ছিলো। তাই সেখানে কোনো বংশানুক্রমিক বাদশাহী প্রতিষ্ঠিত হয়নি, বল প্রয়োগে কোনো ব্যক্তি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়নি, খিলাফত লাভ করার জন্য কেউ নিজের তরফ থেকে চেষ্টা তদবীর করেনি বা নামমাত্র প্রচেষ্টাও চালায়নি। বরং জনগন তাদের স্বাধীন মর্জিমতো পর পর চারজন সাহাবীকে তাদের খলীফা নির্বাচিত করে। মুসলিম মিল্লাত এ খিলাফতকে খিলাফতে রাশেদা {সত্যাশ্রয়ী খিলাফত} বলে গ্রহন করেছে। এ থেকে আপনা আপনিই প্রকাশ পায় যে, মুসলমানদের দৃষ্টিতে এটিই ছিলো খিলাফতের সত্যিকার পদ্ধতি।
একঃ নির্বাচনী খেলাফত
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থলাভিষিক্তের জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম প্রস্তাব করেন। মদীনার সকলেই {বস্তুত তখন তারা কার্যত সারা দেশের প্রতিনিধির মর্যাদার অভিষিক্ত ছিলো} কোনো প্রকার চাপ প্রভান এবং প্রলোভন ব্যতীত নিজেরা সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে পছন্দ করে তাঁর হাতে বাইয়াত।{আনুগত্যের শপথ}করে।
হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর ওফাতকালে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সম্পর্কে ওসীয়াত লিখান, অত:পর জনগনকে মসজিদে নববীতে সমবেত করে বলেনঃ
‘‘আমি যাকে স্থলাভিষিক্ত করছি তোমরা কি তার ওপর সন্তুষ্ট? আল্লাহর শপথ! সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য বুদ্ধি বিবেক প্রয়োগে আমি বিন্দুমাত্র ত্রুটি করিনি। আমার কোনো আত্মীয় স্বজনকে নয় বরং ওমর ইবনুল খাত্তাবকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি। সুতরাং তোমরা তার নির্দেশ শুনবে এবং আনুগত্য করবে।’’
সবাই সমস্বরে বলে ওঠেঃ আমরা তার নির্দেশ শুনবো এবং মানবো।[ আততাবারী-তারীখুল উমাম ওয়াল মুলুক, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬১৮। আল-মাতবায়াতুল ইস্তিকামা, কায়রো ১৯৩৯।]
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর জীবনের শেষ বছর হজ্জের সময় এক ব্যক্তি বললোঃ ওমর মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করবো। কারণ, আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বাইয়াতও তো হঠাৎই হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হয়েছেন।[ তিনি এদিকে ইংগিত করেছেন যে, সাকীফায়ে বনী-সায়িদার মজলিসে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হঠাৎ দাড়িয়ে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম প্রস্তাব করেন এবং হাত বাড়িয়ে তখনই তার হাতে বাইয়াত করেন। তাকে খলীফা করার ব্যপারে পূর্বাহ্নে কোনো পরামর্শ করেননি।] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ সম্পর্কে জানতে পেরে বললেনঃ এ ব্যপারে আমি এক ভাষণ দেবো। জনগনের ওপর যারা জোরপূর্বক নিজেদেরকে চাপিয়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তাদের সম্পর্কে আমি জনগণকে সতর্ক করে দেবো। মদীনায় পৌছে তাঁর প্রথম ভাষণেই তিনি এ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাকীফায়ে বনী সায়েদার ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বলেন যে, তখন এক বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ হযরত আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম প্রস্তাব করে আমি তার হাতে বাইয়াত করেছিলাম। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেনঃ তখন যদি এরকম না করতাম, তবে রাতারাতি লোকদের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত করে বসার আশংকা ছিলো। আর সে ফায়সালা মেনে নেয়া এবং তা পরিবর্তন করা-উভয়ই আমাদের জন্য কঠিন হতো। এ পদক্ষেপটি সাফল্যমন্ডিত হলেও ভবিষ্যতের জন্য একে নযীর হিসেবে গ্রহন করা যেতে পারেনা। আবু বকরের মতো উন্নত মানের এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব তোমাদের মধ্যে আর কে আছে? এখন কোনো ব্যক্তি যদি মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতিরেকে কারো হাতে তাহলে সে এবং যার হাতে বাইয়াত করা হবে-উভয়ই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সোপর্দ করবে। [ বুখারী, কিতাবুল মুহারিবীন, অধ্যায়-১৬। মুসনাদে আহমাদ, ১ম খন্ড, হাদীস নম্বর-৩৯১। তৃতীয় সংস্করণ, দারুল মায়ারিফ, মিসর ১৯৪৯। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আয়ালা আনহুর শব্দগুলো ছিলো এইঃ মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি কোনো আমীরের হাতে বাইয়াত করে, তার কোনো বাইয়াত নেই; এবং যার হাতে বাইয়াত করে, তারও কোনো বাইয়াত নেই। অপর এক বর্ননায় হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এ বাক্যও দেখা যায়-পরামর্শ ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে ইমারাত দেয়া হলে তা কবূল করা তার জন্য হালাল নয়। {ইবনে হাযার, ফাতহুল বারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠ-১২৫, আল-মাতবায়াতুল খাইরিয়া, কায়রো, ১৩২৫ হিজরী।]
তার নিজের ব্যাখ্যা করা এ পদ্ধতি অনুযায়ী হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খিলাফতের ফায়সালা করার জন্য তার ওফাতকালে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে বলেনঃ ‘মুসলমানদের পরামর্শ ব্যতীত যে ব্যক্তি জোর করে আমীর হওয়ার চেষ্টা করবে, তাকে হত্যা করো।’ খিলাফত যাতে বংশানুক্রমিক পদাধিকারে পরিণত না হয়, সে জন্য তিনি খিলাফত লাভের যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা থেকে নিজের ছেলের নাম
সুস্পস্টভাবে বাদ দিয়ে দেন।[ আততাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯২। ইবনুল, আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫। ইদারাতুল তিবরাতিল মুনীরিয়া, মিসর, ১৩৫৬ হিজরী। তাবাকাতে ইবনে সা’দ, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪৪, বৈরুত সংস্করণ ১৯৫৭। ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯।] ছ’ব্যক্তিকে নিয়ে এ নির্বাচনী কমিটি গঠিত হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মতে এরা ছিলেন কওমের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জনপ্রিয়।
কমিটির সদস্য আবদুর রহমান ইবনে আওফকে কমিটি শেষ পর্যন্ত খলিফার নাম প্রস্তাব করার ইখতিয়ার দান করে। সাধারণ লোকদের মধ্যে ঘোরাফেরা করে তিনি জানতে চেষ্টা করেন, কে সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয়। হজ্জ শেষ করে যেসব কাফেলা বিভিন্ন এলাকায় ফিরে যাচ্ছিলো, তিনি তাদের সাথেও আলোচনা করেন। এ জনমত যাচাইয়ের ফলে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অধিকাংশ লোকই হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পক্ষে।[ আততাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬। ইবনুল আসীর, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬। আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৪৬।] তাই তাকেই খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয়। সাধারণ জনসমাবেশে তার বাইয়াত হয়।
হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর শাহাদাতের পর কিছু লোক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে খলীফা করতে চাইলে তিনি বললেনঃ‘‘ এমন করার ইখতিয়ার তোমাদের নেই। এটা তো শূরার সদস্য এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের কাজ। তারা যাঁকে খলীফা করতে চান, তিনিই খলীফা হবেন। আমরা মিলিত হবো এবং এ ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করবো।’’[ ইবনে কুতাইবা, আল-ইমামা ওয়াস সিয়াসা, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪১।] তাবারী হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যে বক্তব্য উদ্ধৃত করেছে, তা হচ্ছেঃ ‘‘ গোপনে আমার বাইয়াত অনুষ্ঠিত হতে পারেনা, তা হতে হবে মুসলমানদের মর্জী অনুযায়ী।’’[আততাবারী, তৃতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০।]
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ওফাতকালে লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, আমরা আপনার পুত্র হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হাতে বাইয়াত করবো? জবাবে তিনি বলেনঃ ‘‘ আমি তোমাদেরকে নির্দেশও দিচ্ছিনা, নিষেধও করছিনা। তোমরা নিজেরাই এ ব্যাপারে বিবেচনা করতে পারো।’’[ আততাবারী, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১২। আল-মাসউদী, মূরুজুয যাহাব, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬। আল-মাতবায়াতুল বাহিয়্যা, মিসর, ১২৪৬ হিজরী।] তিনি যখন আপন পুত্রদেরকে শেষ ওসীয়াত করছিলেন, ঠিক সে সময় জনৈক ব্যক্তি আরয করলো, আমীরুল মু’মিনীন‘‘ আপনি আপনার উত্তরসূরী মনোনয়ন করছেননা কেন? জবাবে তিনি বলেনঃ আমি মুসলমানদেরকে সে অবস্থায় ছেড়ে যেতে চাই, যে অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিলেন রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।’’[ ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, অষ্টম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩-১৪ মাতবায়াতুস সারাদাত, মিসর। আল-মাউদি, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬। ]
এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফত সম্পর্কে খোলাফায়ে রাশেদীন এবং রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের সর্বসম্মত মত
এই ছিলো যে, খিলাফত একটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ এবং তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যমেই তা কায়েম করতে হবে। বংশানুক্রমিক বা বল প্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়া, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব করা তাঁদের মতে খিলাফত নয় বরং তা সৈরতন্ত্র। খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের যে স্পষ্ট ও দ্ব্যতহীন ধারনা সাহাবায়ে কিরামগণ পোষণ করতেন, হযরত আবু মুসা আশয়ারী হাসান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তা ব্যক্ত করেন নিম্মোক্ত ভাষায়ঃ
‘‘ইমারাত {অর্থাৎ খিলাফত} হচ্ছে তাই, যা প্রতিষ্ঠা করতে পরামর্শ নেয়া হয়েছে। আর তরবারীর জোরে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা হচ্ছে বাদশাহী বা রাজতন্ত্র।’’[ তাবকাতে ইবনে সা’দ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-১১৩।]
দুইঃ শূরাভিত্তিক সরকার
এ খলীফা চতুষ্ঠয় সরকারের নির্বাহী এবং আইন প্রণয়নের ব্যাপারে জাতির বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অধিকারী ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ না করে কোনো কাজ করতেননা। সুনানে দারামীতে হযরত মাইমুন ইবনে মাহরানের একটি বর্ণনা আছে যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নীতি ছিলো, তাঁর সামনে কোনো বিষয় উথ্থাপিত হলে তিনি প্রথমে দেখতেন আল্লাহর কিতাব কি বলে। সেখানে কোনো নির্দেশ না পেলে এ ধরনের ব্যাপারে রসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ফায়সালা দিয়েছেন, তা জানতে চেষ্টা করতেন। রসূলের সুন্নায়ও কোনো নির্দেশ না পেলে জাতীয় পরামর্শক্রমে যে মতই স্হির হতো, তদানুযায়ী ফায়সালা করতেন। [ সুনানে দারামী, বাবুল ফুতইয়া ওয়ামা ফীহি মিনাশ শিদ্দাহ।] হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর কর্মনীতিও ছিলো অনুরূপ। [ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস-২২৮১। ]
পরামর্শের ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের দৃষ্টিভংগি ছিলো, শূরার সদস্যদের সম্পূর্ণ স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে। এ ব্যাপারে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক পরামর্শ সভার উদ্ধোধনী ভাষণে খিলাফতের পলিসি ব্যক্ত করেছেন এভাবেঃ
‘‘আমি আপনাদের যে জন্য কষ্ট দিয়েছি, তা এছাড়া আর কিছু নয় যে, আপনাদের কার্যাদির যে ভার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা বহন করার কাজে আপনারাও আমার সঙ্গে শরীক হবেন। আমি আপনাদের মধ্যাকরই এক ব্যক্তি। আজ আপনারাই সত্যের স্বীকৃতি দানকারী। আপনাদের মধ্য থেকে যাদের ইচ্ছা , আমার সাথে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন; আবার যাদের ইচ্ছা আমার সাথে একমতও হতে পারেন। আপনাদের যে আমার মতামতকে সমর্থন করতে হবে-এমন কোনো কথা নেই এবং আমি তা চাই-ও না।‘‘[ ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-২৫।]
তিনঃ বাইতুল মাল একটি আমানত
তারা বাইতুলমালকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানত মনে করতেন। বেআইনীভাবে বাইতুলমালের মধ্যে কিছু প্রবেশ করা ও বেআইনীভাবে তা থেকে কিছু বের হয়ে যাওয়াকে তারা জায়েয মনে করতেননা। শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিগত স্বার্থে বাইতুলমাল ব্যবহার তাদের মতে হারাম ছিলো। তাদের মতে খিলাফত এবং রাজতন্ত্রের মৌলিক পার্থক্যৈই ছিলো এই যে, রাজা বাদশাহরা জাতীয় ভান্ডারকে নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করে নিজেদের খাহেশ মতো স্বাধীনভাবে তাতে তসরুফ করতো, আর খলীফা তাকে আল্লাহ এবং জনগণের আমানত মনে করে সত্য ন্যায় নীতি মোতাবেক এক একটি পাই পয়সা উসূল করতেন, আর তা ব্যয়ও করতেন সত্য ন্যায় নীতি অনুসারে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদা হযরত সালমান ফারসীকে জিজ্ঞেস করেনঃ ‘‘ আমি বাদশাহ, না খলীফা?’’ তিনি তৎক্ষণাৎ জবাব দেনঃ ‘‘মুসলমানদের ভূমি থেকে আপনি যদি এক দিরহামও অন্যায়ভাবে উসূল এবং অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন তাহলে আপনি খলীফা নন; বাদশা।’’ অপর এক প্রসঙ্গে একদা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় মজলিসে বলেনঃ আল্লাহর কসম, আমি এখনো বুঝে উঠতে পারছিনা যে, আমি বাদশা, না খলীফা। আমি যদি বাদশাহ হয়ে গিয়ে থাকি, তবে তা তো এক সাংঘাতিক কথা!’’ এতে জনৈক ব্যক্তি বললোঃ ‘‘আমিরুল মুমিনীন! এতদোভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।’’ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জিজ্ঞেস করলেন, কি পার্থক্য? তিনি বললেনঃ
‘‘খলীফা অন্যায়ভাবে কিছুই গ্রহন করেননা, অন্যায়ভাবে কিছুই ব্যয়ও করেননা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে আপনিও অনূরূপ। আর বাদশাহ তো মানুষের ওপর যুলম করে, অন্যায়ভাবে একজনের কাছ থেকে উসূল করে, আর অন্যায়ভাবেই অপরজনকে দান করে।’’[ তাবাকাতে ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩০৬-৩০৭।]
এ ব্যাপারে খোলাফায়ে রাশেদীনের কর্মধারা প্রণিধানযোগ্য। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু খলীফা হওয়ার পরদিন কাপড়ের থান কাঁধে নিয়ে বিক্রি করার জন্য বেরিয়েছেন। কারণ, খিলাফতের পূর্বে এটিই ছিল তার জীবিকার অবলম্বন। পথে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে দেখা। তিনি বললেন, আপনি একি করছেন? জবাব দিলেন, ছেলে মেয়েদের খাওয়াবো কোথ্থেকে? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, মুসলমানদের নেতৃত্বের ভার আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে। ব্যবসায়ের সাথে খেলাফতের কাজ চলতে পারেনা। চলুন আবু ওবাইদার{বাইতুল মালের খাজা….}সাথে আলাপ করি। তাই হলো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আবু ওবাইদার সাথে আলাপ করলেন। তিনি বললেন, একজন সাধারন মুহাজীরের আমদানীর মান সামনে রেখে আমি আপনার জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিচ্ছি। এ ভাতা মুহাজিরদের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তির সমানও নয়; আবার সবচেয়ে দরিদ্রেরা পর্যায়েরও নয়। এমনিভাবে তাঁর জন্য একটা ভাতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এর পরিমাণ ছিলো বার্ষিক চার হাজার দিরহামের কাছাকাছি। কিন্তু তাঁর
ওফাতের সময় ঘনিয়ে এলে তিনি ওসীয়াত করে যান যে, আমার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আট হাজার দিরহাম বাইতুলমালকে ফেরত দেবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট তা আনা হলে তিনি বলেনঃ
‘‘আল্লাহ আবুবকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রতি রহম করুন! উত্তরসূরীদেরকে তিনি মুশকিলে ফেলে গেলেন।’’[ কানযুল উম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং ২২৮০-২২৮৫।]
বাইতুলমালে খলীফার অধিকার এতোটুকু এ প্রসঙ্গে খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একদা তাঁর এক ভাষণে বলেনঃ
‘‘গ্রীষ্মকালে এক জোড়া কাপড়, শীতকালে এক জোড়া কাপড়, কুরাইশের একজন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির সমপরিমাণ অর্থ আপন পরিবার পরিজনের জন্য-এছাড়া আল্লাহর সম্পদের মধ্যে আর কিছুই আমার জন্য হালাল নয়। আমি তো মুসলমানদের একজন সাধারন ব্যক্তি বৈ কিছুই নই।’’[ ইবনে কাসীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, পৃষ্ঠা-১৩৪।
অপর এক ভাষনে তিনি বলেনঃ
‘‘এ সম্পদের ব্যাপারে তিনটি বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুকেই আমি ন্যায় মনে করিনা। ন্যায়ভাবে গ্রহন করা হবে, ন্যায় মুতাবিক প্রদান করা হবে এবং বাতিল থেকে তাকে মুক্ত রাখতে হবে। এতীমের সম্পদের সাথে তার অভিভাবকের যে সম্পর্ক, তোমাদের এ সম্পদের সাথে আমার সম্পর্কও ঠিক অনুরূপ। আমি অভাবী না হলে তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবোনা, অভাবী হলে মারুফ পন্থায় গ্রহন করবো।’’[ ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭।]
হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বেতনের যে মান ছিলো, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও তাঁর বেতনের মান তাই রাখলেন। তিনি পায়ের হাঁটু ও গোড়ালীর মাঝ বরাবর পর্যন্ত উঁচু তহবন্দ পরতেন। তাও আবার ছিলো তালিযুক্ত।[ ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮।] সারা জীবন কখনো একটু আরামে কাটাবার সুযোগ হয়নি। একবার শীতের মওসূমে জনৈক ব্যক্তি তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান। দেখেন, তিনি একখানা ছেঁড়া কাপড় পরে বসে আছেন আর শীতে কাঁপছেন।[ ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩।] শাহাদাতের পর তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসাব নিয়ে দেখা গেলো মাত্র সাতশত দিরহার। তাও তিনি এক পয়সা এক পয়সা করে জমা করেছেন একটা গোলাম খরিদ করার জন্য । [ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৮।] আমীরুল মু’মিনীন বলে চিনতে পেরে তাঁর কাছ থেকে যাতে কম মূল্য কেউ গ্রহণ না করে এ ভয়ে কোনো পরিচিত ব্যাক্তির কাছ থেকে বাজারে কখনো কোনো জিনিস কিনতেননা।[ ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৮। ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩।] যে সময় হযরত মুয়াবিয় রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে তার সংঘর্ষ চলছিলো, কেউ কেউ তাকে পরামর্শ দেনঃ হযরত মুয়াবিয়া
রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যে রকম লোকদেরকে অঢেল দান দক্ষিণা করে তাঁর সাথী করে নিচ্ছেন আপনিও তেমনি বাইতুল মালের ভান্ডার উজাড় করে টাকার বন্যা বইয়ে দিয়ে সমর্থন সংগ্রহ করুন। কিন্তু তিনি এই বলে হা প্রত্যাখ্যান করলেন ‘‘তোমরা কি চাও আমি অন্যায়ভাবে সফল হই? ’’[ ইবনে আবীল হাদীস, নাহজুল বালাগার ভাষ্য, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৮২। দারুল কুতুবিল আরাবিয়্যা, মিসর, ১৩২৯ হিজরী।] তাঁর আপন ভাই হযরত আকীল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর কাছে টাকা দাবী করেন বাইতুলমাল থেকে। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করে বলেনঃ তুমি কি চাও তোমার ভাইও মুসলমানদের টাকা তোমাকে দিয়ে জাহান্নামে যাক।’’[ ইবনে কুতাইবা-আল-ইমামা ওয়াস সিয়াস, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৭১।]
চারঃ রাষ্ট্রের ধারনা
রাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের ধারনা কি ছিলো, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে নিজের মর্যাদা এবং কর্তব্য সম্পর্কে তারা কি ধারনা পোষণ করতেন, স্বীয় রাষ্ট্রে তারা কোন্ নীতি মেনে চলতেন? খিলাফতের মঞ্চ থেকে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তাঁরা নিজেরাই প্রকাশ্যে এসব বিষয় ব্যক্ত করেছেন। মসজিদে নববীতে গণ বাইয়াত ও শপথের পর হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেছিলেনঃ
‘‘আমাকে আপনাদের শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি নই। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন ন্যস্ত, আমি নিজে ইচ্ছা করে এ পদ গ্রহণ করিনি। অন্যের পরিবর্তে আমি নিজে এ পদ লাভের চেষ্টাও করিনি, এজন্য আমি কখনো আল্লাহর নিকট দোয়াও করিনি। এজন্য আমার অন্তরে কখনো লোভ সৃষ্টি হয়নি। মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধ এবং আরবদের মধ্যে ধর্ম ত্যাগের ফেতনার সূচনা হবে- এ আশংকায় আমি অনিচ্ছা সত্বে এ দায়িত্ব গ্রহন করেছি। এ পদে আমার কোনো শান্তি নেই। বরং এটা এক বিরাট বোঝা, যা আমার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এ বোঝা বহন করার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য আল্লাহ যদি আমাকে সাহায্য করেন। আমার ইচ্ছা ছিলো, অন্য কেউ এ দায়িত্বভার বহন করুক। এখনোও আপনারা ইচ্ছা করলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে হতে কাউকে এ কাজের জন্য বাছাই করে নিতে পারেন। আমার বাইয়াত এ ব্যাপারে আপনাদের প্রতিবন্ধক হবেনা। আপনারা যদি আমাকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মানদন্ডে যাচাই করেন, তবে তার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ, তিনি শয়তান থেকে নিরাপদ ছিলেন, তাঁর ওপর ওহী নাযিল হতো। আমি সঠিক কাজ করলে আমার সহযোগিতা করবেন, অন্যায় করলে আমাকে সোজা করে দেবেন। সততা হচ্ছে একটি আমানত। আর মিথ্যা একটি খেয়ানত। তোমাদের দুর্বল ব্যক্তি আমার নিকট সবল। আল্লাহর ইচ্ছায় যতক্ষণ আমি তার অধিকার তাকে দান না
করি। আর তোমাদের মধ্যকার সবল ব্যক্তি আমার নিকট দুর্বল-যতক্ষণ আল্লাহর ইচ্ছায় আমি তার কাছ থেকে অধিকার আদায় করতে না পারি। কোনো জাতি আল্লাহর রাস্তায় চেষ্টা সাধনা ত্যাগ করার পরও আল্লাহ তার ওপর অপমান চাপিয়ে দেননি-এমনটি কখনো হয়নি। কোনো জাতির মধ্যে অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করার পর আল্লাহ তাদেরকে সাধারণ বিপদে নিপতিত করেননা-এমনও হয়না। আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগত থাকি, তোমরা আমার আনুগত্য করো। আমি আল্লাহ্ ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হলে আমার ওপর তোমাদের কোনো আনুগত্য নেই। আমি অনুসরণকারী, কোনো নতুন পথের উদ্ভাবক নই।’’[ আততাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৫০। ইবনে হিশাম, আস সীরাতুন নববিয়্যা, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৩১১, মাতবায়াতু মুস্তফা আল-বাবী, মিসর-১৯৩৬, কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২২৬১, ২২৬৪, ২২৬৮, ২২৭৮, ২২৯১, ২২৯৯। ]
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার ভাষণে বলেনঃ
‘‘লোক সকল! আল্লাহর অবাধ্যতায় কারোর আনুগত্য করতে হবে-নিজের সম্পর্কে এমন অধিকারের দাবী কেউ করতে পারেনা।… লোক সকল! আমার ওপর তোমাদের যে অধিকার রয়েছে, আমি তোমাদের নিকট তা ব্যক্ত করছি। এসব অধিকারের জন্য তোমরা আমাকে পাকড়াও করতে পারো। আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, খিরাজ বা আল্লাহর দেয়া ফাই {বিনা যুদ্ধে বা রক্তপাত ছাড়াই যে গনীমতের মাল লব্ধ হয়} থেকে বেআইনী কোনো কিছু গ্রহণ করবোনা। আর আমার ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, এভাবে যে অর্থ আমার হাতে আসে, অন্যায়ভাবে তার কোনো অংশও আমি ব্যয় করবোনা।’’[ ইমাম আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৭।]
সিরিয়া ও ফিলিস্তিন যুদ্ধে হযরত ওমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে প্রেরণকালে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হিদায়াত দান করেন, তাতে তিনি বলেনঃ
‘‘আমর! আমর প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করে চলো। তাঁকে লজ্জা করে চলো। কারণ, তিনি তোমাকে এবং তোমার সকল কর্মকেই দেখতে পান।….. পরকালের জন্য কাজ করো। তোমার সকল কর্মে আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখো। সঙ্গী-সাথীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করবে, যেনো তারা তোমার সন্তান। মানুষের গোপন বিষয় খুঁজে বেড়িয়োনা। বাহ্যিক কাজের ভিত্তিতেই তাদের সঙ্গে আচরণ করো।……. নিজেকে সংযত রাখবে, তোমার প্রজা সাধারণও ঠিক থাকবে।’’[ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস নং-২৩১৩।]
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু শাসনকর্তদের কোনো এলাকায় প্রেরণকালে সম্বোধন করে বলতেনঃ
‘‘মানুষের দন্ড মুন্ডের মালিক বনে বসার জন্য আমি তোমাদের মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের ওপর শাসনকর্তা নিযুক্ত করছিনা। বরং আমি তোমাদের এজন্য নিযুক্ত করেছি যে, তোমরা সালাত কায়েম করবে, মানুষের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা করবে, ন্যায়ের সাথে তাদের অধিকার বন্টন করবে।’’[ আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৩।]
বাইয়াতের পর হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রথম যে ভাষণ দান করেন, তাতে তিনি বলেনঃ
‘‘শোনো, আমি অনুসরনকারী, নতুন পথের উদ্ভাবক নই। জেনে রেখো, আল্লাহর কিতাব এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মেনে চলার পর আমি তোমাদের নিকট তিনটি বিষয় মেনে চলার অঙ্গিকার করেছি। একঃ আমার খিলাফতের পূর্বে তোমরা পারস্পারিক সম্মতিক্রমে যে নীতি নির্ধারণ করেছো, আমি তা মেনে চলবো। দুইঃ যেসব ব্যাপারে পূর্বে কোনো নীতি পন্থা নির্ধারিত হয়নি, সেসব ব্যাপারে সকলের সাথে পরামর্শক্রমে কল্যাণাভীসারীদের পন্থা নির্ধারণ করবো। তিনঃ আইনের দৃষ্টিতে তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য না হয়ে পড়া পর্যন্ত তোমাদের ওপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবো।’’[আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৬।]
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত কায়েস ইবনে সা’দকে মিসরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাবারকালে মিসরবাসীদের নামে যে ফরমান দান করেন, তাতে তিনি বলেনঃ
‘‘সাবধান! আমি আল্লাহর কিতাব এবং রসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ মোতাবক আমল করবো-আমার ওপর তোমাদের এ অধিকার রয়েছে। আল্লাহর নির্ধারিত অধিকার অনুযায়ী আমি তোমাদের কাজ কারবার পরিচালনা করবো। তোমাদের অগোচরেও তোমাদের কল্যাণ কামনা করবো।’’
প্রকাশ্য জনসমাবেশে এ ফরমান পাঠ করে শোনাবার পর হযরত কায়েস ইবনে সা’দ ঘোষণা করেনঃ
‘‘আমি তোমাদের সাথে এভাবে আচরণ না করলে তোমাদের ওপর আমার কোনো বাইয়াত নেই।’’[ আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৫০-৫৫১।]
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জনৈক গভর্ণরকে লিখেনঃ
‘‘তোমাদের এবং জনসাধারনের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করোনা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা দৃষ্টির সংকীর্ণতা এবং জ্ঞানের স্বল্পতার পরিচায়ক। এর ফলে তারা সত্যিকার অবস্থা জানতে পারেনা। ক্ষুদ্র বিষয় তাদের জন্য বৃহৎ হয়ে দাঁড়ায়, আর বিরাট বিষয় ক্ষুদ্র। তাদের জন্য ভালো মন্দ হয়ে
দেখা দেয়, আর মন্দ গ্রহণ করে ভালোর আকার; সত্য মিথ্যা সংমিশ্রিত হয়ে যায়।’’[ ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৮।]
‘‘হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কেবল একথা বলে ক্ষান্ত হননি, তিনি অনুরূপ কাজও করেছেন। তিনি নিজে দোররা নিয়ে কুফার বাজারে বেরুতেন, জনগণকে অন্যায় থেকে বারণ করতেন, ন্যায়ের নির্দেশ দিতেন। প্রত্যেকটি বাজারে চক্কর দিয়ে দেখতেন, ব্যবসায়ীরা কাজ কারবারে প্রতারণা করছে কিনা। এ দৈনন্দিন ঘোরাঘুরির ফলে কোনো অপরিচিত ব্যক্তি তাঁকে দেখে ধারণাই করতে পারতোনা যে, মুসলিম জাহানের খলিফা তার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কারণ, তার পোশাক থেকে বাদশাহীর কোনো পরিচয় পাওয়া যেতনা, তাঁর আগে আগে পথ করে দেয়ার জন্য কোনো রক্ষীবাহিনীও দৌড়ে যেতোনা।’’[ ইবনে কাসীর, ৮ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪-৫।]
একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু প্রকাশ্যে ঘোষণা করেনঃ
‘‘তোমাদেরকে পিটাবার জন্য আর তোমাদের সম্পদ ছিনিয়ে নেয়ার জন্য আমি গভর্ণরদের নিযুক্ত করিনি। তাদের নিযুক্ত করেছি এজন্য যে, তারা তোমাদেরকে দ্বীন এবং নবীর তরীকা পদ্ধতি শিক্ষা দেবে। কারো সাথে এই নির্দেশ বিরোধী ব্যবহার করা হয়ে সে আমার কাছে অভিযোগ উথ্থাপন করুক। আল্লাহর কসম করে বলছি আমি তার {গভর্নরের} কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো।’’ এতে হযরত আমর ইবনুল আস {মিসরের গভর্নর} দাঁড়িয়ে বলেনঃ ‘‘কেউ যদি মুসলমানদের শাসক হয়ে শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়ার জন্য তাদেরকে মারে, আপনি কি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবেন?’’ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জবাব দেনঃ ‘‘হাঁ’ আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তার কাছ থেকেও প্রতিশোধ নেবো। আমি আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার নিজের সত্তা থেকেও প্রতিশোধ নিতে দেখেছি!’’[ আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৫। মুসনাদে আবু দাউদ আততায়ালিসী, হাদীস নং-৫৫। ইবনুল আসীর, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩০। আততাবারী, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা-২৭৩।]
আর একবার হজ্জ উপলক্ষে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সমস্ত গভর্নরকে ডেকে প্রকাশ্য সমাবেশে দাড়িয়ে বলেনঃ এদের বিরুদ্ধে কারুর ওপর কোনো অত্যাচারের অভিযোগ থাকলে তা পেশ করতে পারো নির্দ্ধিধায়। গোটা সমাবেশ থেকে মাত্র একজন লোক উঠে হযরত আমর ইবনুল আসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেনঃ তিনি অন্যায়ভাবে আমাকে একশ দোররা মেরেছেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেনঃ ওঠো এবং তার কাছ থেকে প্রতিশোধ নাও। হযরত আমর ইবনুল আস প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, আপনি গভর্ণরদের বিরুদ্ধে এপথ উন্মুক্ত করবেননা। কিন্তু তিনি বললেনঃ আমি আল্লাহর রসূলকে নিজের থেকে প্রতিশোধ দিতে দেখেছি। হে অভিযোগকারী, এসে তার থেকে প্রতিশোধ গ্রহন করো।’’ শেষ
পর্যন্ত আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে প্রতিটি বেত্রাঘাতের জন্য দু’আশরাফী দিয়ে আপন পিঠ রক্ষা করতে হয়।[আবু ইউসুফ, কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠা-১১৬। ]
পাঁচঃ আইনের প্রাধান্য
এ খলীফারা নিজেদেরকেও আইনের ঊর্ধ্বে মনে করতেননা। বরং আইনের দৃষ্টিতে নিজেকে এবং দেশের একজন সাধারন নাগরিককে {সে মুসলমান হোক বা অমুসলিম যিম্মি} সমান মনে করতেন। রাষ্ট প্রধান হিসেবে তাঁরা নিজেরা বিচারপতি {কাযী} নিযুক্ত করলেও খলীফাদের বিরুদ্ধে রায়দানে তারা ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন, যেমন স্বাধীন ছিলেন একজন সাধারণ নাগরিকের ব্যাপারে। একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত উবাই ইবনে কা’ব রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মধ্যে এক ব্যাপারে মতবিরোধ দেখা দেয়। উভয়ে হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে শালিশ নিযুক্ত করেন, বাদী বিবাদী উভয়ে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট উপস্থিত হলেন। যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দাড়িয়ে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে তার আসনে বসাতে চাইলেন, কিন্তু তিনি উবাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাথে বসলেন। অতঃপর হযরত উবাই রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার আর্যী পেশ করলেন, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অভিযোগ অস্বীকার করলেন। নিয়ম অনুযায়ী যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উচিত ছিলো হযরত ওমরের কাছ থেকে কসম আদায় করা। কিন্তু তিনি তা করতে ইতস্তত করলেন, হযরত ওমর নিজে কসম খেয়ে মজলিস সমাপ্তির পর বললেনঃ ‘‘যতক্ষণ যায়েদের কাছে একজন সাধারণ মুসলমান এবং ওমর সমান না হয় ততক্ষণ যায়েদ বিচারক হতে পারেনা।’’[ বাইহাকী, আস-সুনানূল কাবরা, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬। দায়িরাতুল মায়ারিফ, হায়দাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫ হিজরী।]
এমনি এক ঘটনা ঘটে জনৈক খৃষ্টানের সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর। কুফার বাজারে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখতে পেলেন, জনৈক খৃষ্টান তার হারানো লৌহবর্ম বিক্রি করছে। আমীরুল মু’মিনীন হিসেবে তিনি সে ব্যক্তির নিকট থেকে বর্ম ছিনিয়ে নেননি বরং কাযীর দরবারে ফরিয়াদ করলেন। তিনি সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করতে না পারায় কাযী তার বিরুদ্ধে রায় দান করলেন।[ বাইহাকী আস-সুনানূল কুবরা, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৩৬। দায়িরাতুল মায়ারিফ, হায়দাবাদ, ১ম সংস্করণ, ১৩৫৫।]
ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লেকান বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং জনৈক যিম্মি বাদী বিবাদী হিসেবে কাযী শোরাইহর আদালতে উপস্থিত হন। কাযী দাড়িয়ে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অভ্যর্থনা জানান। এতে তিনি {হযরত আলী} বলেন, ‘‘এটা তোমার প্রথম বে-ইনসাফী।’’[ ইবনে খাল্লিকান, ওয়াফায়াতুল আইয়ান, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-১৬৮, মাকতাবাতুন নাহযাতিল মিসরিয়্যাহ, কায়রো, ১৪৮।]
ছয়ঃ বংশ-গোত্রের পক্ষপাতমুক্ত শাসন
ইসলামের প্রাথমিক যুগের আরেকটি বৈশিষ্ট ছিলো এই যে, ইসলামের নীতি এবং প্রাণশক্তি অনুযায়ী তখন বংশ গোত্র দেশের পক্ষপাতের উর্ধ্বে উঠে সকল মানুষের সাথে সমান আচরণ করা হতো, কারো সাথে কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব করা হতোনা।
আল্লাহর রসূলের ওফাতের পরে আরবের গোত্রবাদ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে জঞ্জার বেগে। নব্যয়্যতের দাবীদারদের অভ্যুদয় এবং ইসলাম ত্যাগের হিড়িকের মধ্যে এ উপাদান ছিলো সবচেয়ে ক্রিয়াশীল। মোসাইলামার জনৈক ভক্তের উক্তিঃ আমি জানি, মোসাইলামা মিথ্যাবাদী। কিন্তু রাবীয়ার মিথ্যাবাদী মোদারের সত্যবাদীর চেয়ে উত্তম।[ আততাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫০৮।] মিথ্যা নবূয়্যতের অপর এক দাবীদার তোলাইহার সমর্থনে বনু গোতফানের জনৈক সর্দার বলেনঃ ‘‘খোদার কসম, কুরাইশের নবীর অনুসরণ করার চেয়ে আমাদের বন্ধুগোত্রের নবীর অনুসরণ আমার নিকট অধিক প্রিয়।’’[ আততাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৭।]
মদীনায় যখন হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হাতে বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয়, তখন গোত্রবাদের ভিত্তিতে হযরত সা’দ ইবনে ওবাদা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার খিলাফত স্বীকার করা থেকে বিরত ছিলেন। এমনি করেই গোত্রবাদের ভিত্তিতেই হযরত আবু সুফিয়ানের নিকট তার খিলাফত ছিলো অপছন্দনীয়। তিনি হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিকট গিয়ে বলেছিলেনঃ ‘কুরাইশের সবচেয়ে ছোট গোত্রের লোক কি করে খলীফা হয়ে গেল? তুমি নিজেকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাতে প্রস্তুত হলে আমি পদাতিক এবং অশ্বরোহী বাহিনী দ্বারা সমগ্র উপত্যকা ভরে ফেলবো। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক মোক্ষম জবাব দিয়ে তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেনঃ তোমরা একথা ইসলাম এবং মুসলমানদের সাথে শত্রুতা প্রমাণ করে। তুমি কোনো পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনী আনো, আমি তা কখনো চাইনা। মুসলমানরা পরস্পরের কল্যাণকামী। তারা একে অপরকে ভালবাসে। তাদের আবাস ও দৈহিক সত্তার মধ্যে যতই ব্যবধান থাকনা কেন। অবশ্য মুনাফিক একে অন্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্নাকারী। আমরা আবু বকরকে এ পদের যোগ্য মনে করি। তিনি এ পদের যোগ্য না হলে আমরা কখনো তাঁকে এ পদে নিয়োজিত হতে দিতামনা।[ কানযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস-২৩৭৪। আততাবারী, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৪৯। ইবনুআব্দিল বাব আল-ইস্তিয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৮৯।]
এ পরিবেশে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লহু তায়ালা আনহু এবং তারপর হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতমুক্ত ইনসাফপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে কেবল আরবের বিভিন্ন গোত্র নয় বরং অনারব নওমুসলিমদের সাথেও ইনসাফপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং বংশ গোত্রের সাথে কোনো প্রকার ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এর ফলে সব রকম বংশ গোত্রবাদ বিলীন হয়ে যায়। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দাবী অনুযায়ী একটি আন্তর্জাতিক প্রাণশক্তি
ফুটে ওঠে। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালে আপন গোত্রের কোনো লোককে কোনো সরকারী পদে নিয়োগ করেননি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর গোটা শাসনকালে তার গোত্রের একজন মাত্র ব্যক্তিকে যার নাম ছিলো নো’মান ইবনে আদী-বসরার নিকটে মাইদান নামক এক ক্ষুদ্র এলাকার তহশিলদার নিযুক্ত করেছিলেন। অল্প কিছুদিন পরই আবার এ পদ থেকে তাকে বরখাস্ত করেছিলেন।[ হযরত নু’মান ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্যতম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আগে তিনি ইসলাম গ্রহন করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে যারা মক্কা ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় চলে যান, তাদের মধ্যে তিনি এবং তার পিতা আদীও ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন তাকে মাইসানের তহসিলদার নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন, তখন তার স্ত্রী তার সংগে যাননি। তিনি সেখানে স্ত্রীর বিরহে কিছু কবিতা রচনা করেন। এ সকল কবিতায় কেবল মদের বিষয় উল্লেখ ছিলো। এতে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে পদচ্যুত করেন। শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে তাকে কোনো পদ না দেয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন তিনি। ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীয়াব, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯৬। দায়িরাতুল মায়ারিফ, হায়দরাবাদ, মুজামুল, বুলদান, ইয়াকুত হামাবী, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-২৪২-২৪৩। দারে ছাদির, বৈরুত ১৯৫৭। অপর এক ব্যক্তি, হযরত কুদামা ইবনে মাযউন- যিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ভগ্নিপতি ছিলেন-তিনি তাকে বাহরাইনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি ছিলেন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের অন্যতম। কিন্তু তার বিরুদ্ধে মদ্যপানের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তিনি তাকে বরখাস্ত করে দন্ড দান করেন। {আল-ইস্তীয়াব, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা -৫৩৪, ইবনে হাজর, আল-ইসাবা} ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২১৯-২২০] এদিক থেকে এ দু’জন খলিফার কর্মধার সত্যিকার আদর্শভিত্তিক ছিলো।
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জীবনের শেষ অধ্যায়ে আশংকাবোধ করলেন, তাঁর পরে আরবের গোত্রবাদ {ইসলামী আন্দোলনের বিরাট বিপ্লবী প্রভাবের ফলেও যা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি} পুনরায় যেনো মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে এবং তার ফলে ইসলামের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি না হয় যায়। একদা তার সম্ভাব্য উত্তরসূরীদের সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ব্যাপারে বলেনঃ ‘‘আমি তাকে আমার স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলে তিনি বনী আবমুয়াইত {বনী উমাইয়}-কে লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। আর তার লোকদের মধ্যে আল্লাহর নাফরমানী করে বেড়াবে। আল্লাহর কসম, আমি ওসমানকে স্থলাভিষিক্ত করলে সে তাই করবে। আর ওসমান তাই করলে তারা অবশ্যই পাপাচার করবে। এ ক্ষেত্রে জনগণ বিদ্রোহ করে তাকে হত্যা করবে। [ ইবনে আব্দুল বার, আল-ইস্তীয়ার, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭। শাহ ওয়ালীউল্লাহ, ইযালাতুল খিফা, মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা-৩৪২, বেরিলী সংস্করণ। কেউ কেউ এখানে প্রশ্ন তোলেনঃ হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর ওপর কি ইলহাম [সূক্ষ ওহী} হয়েছিলো, যার ভিত্তিতে তিনি হলফ করে কথা বলেছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে যা অক্ষরে অক্ষরে ঘটে গিয়েছিলো? এর জবাব এই যে, দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি কখনো কখনো পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাকে যুক্তির আলোকে পুনর্বিন্যাস করলে ভাবীকালে ঘটিতব্য বিষয় তাঁর সামনে এমনিভাবে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যেমন ২+২=৪। ফলে ইলহাম ব্যতিতই তিনি দিব্য দৃষ্টি বলে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। আরবদের মধ্যে গোত্রবাদের জীবাণু কতো গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছে, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তা জানতেন। তিনি এ-ও জানতেন যে, ইসলামের ২৫-৩০ বৎসর প্রচার এখনও সেসব জীবানু সমূলে উৎপাটিত করতে পারেনি।] ওফাতকালেও এ বিষয়টি তাঁর স্বরণ ছিলো। শেষ সময়ে তিনি
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত সা’দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রত্যেককে ডেকে বলেনঃ আমার পরে তোমরা খলীফা হলে স্ব স্ব গোত্রের লোকদেরকে জনগণের ওপর চাপিয়ে দেবেনা।[আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৬৪। তাবাকাতে ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৪০-৩৪৪।] উপরন্তু ছয় সদস্যের নির্বাচনী শূরার জন্য তিনি যে হিদায়াত দিয়ে যান, তাতে অন্যান্য বিষয়ের সাথে নিম্মোক্ত বিষয়টিও ছিলোঃ নির্বাচিত খলীফারা একথাটি মেনে চলবেন যে, তারা আপন গোত্রের সাথে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী আচরণ করবেননা।[ ফাতহুল বারী, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৯-৫০। মুহিবুদ্দিন আততাবারী, আর-রিয়াযুন নাযিরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৬, হুসাইনিয়া প্রেস, মিসর, ১২৮৪ হিজরী।
[শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ [রঃ] তাঁর ইযালাতুল খিফায় এ বর্ণনার ইদ্ধৃতি দিয়েছেন। মাকসাদে আউয়াল, পৃষ্ঠা-৩২৪ দ্রষ্টব্য।]] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তৃতীয় খলীফা হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ ক্ষেত্রে ঈপ্সিত মানদন্ড বজায় রাখতে সক্ষম হননি। তাঁর শাসনামলে বনী উমাইয়াকে ব্যাপকভাবে বিরাট বিরাট পদ এবং বাইতুল মাল থেকে দান দক্ষিণা দেয়া হয়। অন্যান্য গোত্র তিক্ততার সাথে তা অনুধাবন করতে থাকে।[ তাবকাতে ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪, ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৬।] তাঁর কাছে এটা ছিলো আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচারের দাবী। তিনি বলতেনঃ ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আল্লাহর জন্য তার নিকটাত্মীয়দের বঞ্চিত করতেন, আর আমি আল্লাহর জন্য আমার নিকটাত্মীয়দের দান করছি। [আততাবারী, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৯১।] একবার তিনি বলেনঃ ‘‘বাইতুল মালের ব্যাপারে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেও অসচ্ছল অবস্থায় থাকা পছন্দ করতেন এবং নিজের আত্মীয় স্বজনদের সেভাবে রাখতে ভালো বাসতেন। কিন্তু আমি এ ব্যাপারে আত্মীয় স্বজনদের সাথে সদাচার পছন্দ করি।[কানুযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস-২৩২৪। তাবকাতে ইবনে সা’দ, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৬৪] অবশেষে এর ফল তাই হয়েছে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যা আশংকা করতেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভ দেখা দেয়। কেবল তিনি যে শহীদ হন তাই নয় বরং গোত্রবাদের চাপা দেয়া স্ফুলিঙ্গ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং অবশেষে এরি অগ্নিশিখা খিলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়।
আটঃ গণতন্ত্রের প্রাণশক্তি
সমালোচনা ও মতামত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতাই ছিলো এ খিলাফতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরাজির অন্যতম। খলীফারা স্বর্বক্ষণ জনগনের নাগালের মধ্যে থাকতেন। তাঁরা নিজেরা শূরার অধিবেশনে বসতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহন করতেন। তাঁদের কোনো সরকারী দল ছিলোনা। তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনো দলের অস্তিত্ব ছিলোনা। মুক্ত পরিবেশে সকল সদস্য নিজ নিজ ঈমান এবং বিবেক অনুযায়ী মত প্রকাশ করতেন। চিন্তাশীল, উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহনের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সামনে সকল বিষয় যথাযথভাবে উপস্থাপিত করা হতো। কোনো কিছুই গোপন করা হতোনা। ফায়সালা হতো দলীল প্রমানের ভিত্তিতে, কারোর দাপট, প্রভাব প্রতিপত্তি, স্বার্থ সংরক্ষণ বা দলাদলির ভিত্তিতে নয়। কেবল শূরার মাধ্যমেই খলীফারা জাতির সম্মুখে উপস্থিত হতেননা; বরং দৈনিক পাঁচবার সালাতের জামায়াতে, সপ্তাহে একবার জুময়ার জামায়াতে এবং বৎসরে দুবার ঈদের জামায়াতে ও হজ্জের সম্মেলনে তাঁরা জাতির সামনে উপস্থিত হতেন। অন্যদিকে এসব সময় জাতিও তাদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতো। তাঁদের নিবাস ছিলো জনগণের মধ্যেই। কোনো দারোয়ান ছিলোনা তাঁদের গৃহে। সকল সময় সকলের জন্য তাঁদের দ্বারা খোলা থাকতো। তাঁরা হাট বাজারে জনগণের মধ্যে চলাফেরা করতেন। তাঁদের কোনো দেহরক্ষী ছিলোনা, ছিলোনা কোনো রক্ষী বাহিনী। এসব সময়ে ও সুযোগে যে কোনো ব্যক্তি তাঁদের প্রশ্ন করতে, সমালোচনা করতে ও তাঁদের নিকট থেকে হিসেবে চাইতে পারতো। তাঁদের নিকট থেকে কৈফিয়ত তলব করার স্বাধীনতা ছিলো সকলেরই। এ স্বাধীনতা ব্যবহারের তাঁরা কেবল অনুমতিই দিতেননা বরং এজন্য লোকদেরকে উৎসাহিতও করতেন। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফতের প্রথম ভাষণেই প্রকাশ্যে বলে দিয়েছিলেন, আমি সোজা পথে চললে আমার সাহায্য করো, বাঁকা পথে চললে আমাকে সোজা করে দেবে। একদা হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জুময়ার খুতবায় মত প্রকাশ করেন যে, কোনো ব্যক্তিকে যেনো বিবাহে চারশ’ দিরহামের বেশী মোহর ধার্যের অনুমতি না দেয়া হয়। জনৈক মহিলা তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করে বলেন, আপনার এমন নির্দেশ দেয়ার কোনো অধিকার নেই। কুরআন স্তূপিকৃত সম্পদ [কেনতার] মোহর হিসেবে দান করার অনুমতি দিচ্ছে। আপনি কে তার সীমা নির্ধারণকারী? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তৎক্ষণাৎ তাঁর মত প্রত্যাহার করেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর, আবু ইয়ালা ও ইবনুল মুনযির, এর উদ্ধৃতিতে, ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৭] আর একবার হযরত সালমান ফারসী প্রকাশ্য মজলিশে তাঁর নিকট কৈফিয়ত তলব করেন, ‘আমাদের সকলের ভাগে এক একখানা চাদর পড়েছে। আপনি দুখানা চাদর কোথায় পেলেন? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ারা আনহু তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সাক্ষ্য পেশ করলেন যে, দ্বিতীয় চাদরখানা তিনি পিতাকে দিয়েছেন। [মুহিবুদ্দীন আত-তাবারী, আররিয়াযুননাযিরা ফী মানাকিবিল আশারা, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৫৬। মিসরীয় সংস্করণ। ইবনুল জাওযী, সীরাতে ওমর ইবনে খাত্তাব, পৃষ্ঠা-১২৭] একদা তিনি মজলিশে উপস্থিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেনঃ আমি যদি কোনো ব্যাপারে শৈথিল্য দেখাই তাহলে তোমরা কি করবে? হযরত বিশর ইবনে সা’দ বললেন, এমন করলে আমরা আপনাকে তীরের মতো সোজা করে দেবো। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, তবেই তো তোমরা কাজের মানুষ। [কুনুযুল ওম্মাল, ৫ম খন্ড, হাদীস- ২৪১৪।] হযরত ওসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সবচেয়ে বেশী সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি কখনো জোরপূর্বক কারো মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেননি। বরং সব সময় অভিযোগ এবং সমালোচনার জবাবে প্রকাশ্যে নিজের সাফাই পেশ করতেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর খিলাফতকালে খারেজীদের অত্যন্ত কটু উক্তিকেও শান্ত মনে বরদাশত করেছেন। একদা পাঁচজন খারেজীকে গ্রেফতার করে তাঁর সামনে হাযির করা হলো। এরা সকলেই প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিচ্ছিলো। তাদের একজন প্রকাশ্যেই বলছিলো, আল্লাহর কসম আমি আলীকে হত্যা করবো। কিন্তু হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এদের সকলকেই ছেড়ে দেন এবং নিজের লোকদের বলেন, তোমরা ইচ্ছে করলে তাদের গালমন্দের জবাবে গালমন্দ দিতে পারো। কিন্তু কার্যত কোনো বিদ্রোহাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিছক মৌখিক বিরোধিতা এমন কোনো অপরাধ নয়, যার জন্য তাদের শাস্তি দেয়া যেতে পারে। [সুরুখসী, আল-মাবুসত, ১০ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১২৫। সায়াদাত প্রেস, মিসর, ১৩২৪ হিজরী।]
ওপরে আমরা খিলাফতে রাশেদার যে অধ্যায়ের আলোচনা করেছি, তা ছিলো আলোর মীনার। পরবর্তীকালে ফুকাহা-মুহাদ্দিসীন এবং সাধারণ দীনদার মুসলমান সে আলোর মীনারের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেন। ইসলামের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, নৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁরা এ মীনারকেই আদর্শ মনে করে আসছেন।
দশম অধ্যায়
ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদ
১. ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র এবং তাতে ইজতিহাদের গুরুত্ব
২. কয়েকটি অভিযোগ ও তার জবাব
৩. আইন প্রণয়ন শূরা ও ইজমা
৪. ইসলামী ব্যবস্থায় বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক পন্থা
১৯৫৮ সালের জানুয়ারীতে লাহোরে আন্তর্জাতিক ইসলামী মজলিশে মুযাকিরা’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে পাশ্চাত্যের প্রাচ্যবিদ এবং সারাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন। এ সম্মেলনেরই একটি অধিবেশনে (৩০ জানুয়ারী ১৯৫৮) মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী আইন প্রণয়ণ ও ইজতিহাদ’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ প্রবন্ধটি অর্থাৎ “ইসলামী রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা” আমাদের এই গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। তাই ওটিকে এখানে সংকলিত করে দেয়া হলো। প্রবন্ধের শেষে সেই প্রশ্নমালার জবাবও দিয়ে দেয়া হলো, যা জনৈক প্রগতিবাদীর জবাবে মাওলানা মওদূদী লিখেছিলেন। প্রসংগক্রমে সেসব আলোচনাও এখানে পেশ করা হলো যেগুলো আইনের ব্যাখ্যার সাথে সম্পর্কিত। সংকলক।
১. ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং তাতে ইজতিহাদের গুরুত্ব [লেখক এই প্রবন্ধটি ১৯৫৮ সালের ৩ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সম্মেলনে পাঠ করেন।]
ইসলামে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতোটুকু এবং তাতে ইজতিহাদের কতোটা গুরুত্ব আছে তা অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টির সামনে দুটি বিষয় পরিষ্কার থাকা দরকারঃ এক, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও দুই, নবূয়্যতে মুহাম্মদী।
আল্লাহর সার্বভৌমত্ব
ইসলামে সার্বভৌমত্ব নির্ভেজালভাবে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার জন্য স্বীকৃত। কুরআন মজীদ তৌহিদের আকীদার যে বিশ্লেষণ করেছে তার আলোকে এক এবং অদ্বিতীয় লা-শরীক আল্লাহ কেবল ধর্মীয় অর্থেই মা’বুদ নন বরং রাজনৈতিক এবং আইনগত অর্থের দিক থেকেও তিনি একচ্ছত্র অধিপতি, আদেশ নিষেধের অধিকারী এবং আইন প্রদানকারী। আল্লাহ তায়ালার এই আইনগত সার্বভৌমত্ব [Legal Sovereignty] কুরআন এতোটা পরিষ্কারভাবে এবং এতোটা জোরের সাথে পেশ করে যতোটা জোরের সাথে এবং পরিষ্কারভাবে তাঁর ধর্মীয় সার্বভৌমত্বের আকীদা পেশ করে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহর এদুটি মর্যাদা তাঁর উলুহিয়াতের [খোদায়ী] অবশ্যম্ভাবী ফল। এর একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়না। এর কোনো একটিকে অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর উলুহিয়াতকে অস্বীকার করা। তাছাড়া ইসলাম এরূপ সন্দেহ করারও কোনো অবকাশ রেখেনি যে, খোদায়ী কানুন বলতে হয়তো প্রাকৃতিক বিধানকে বুঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের গোটা দাওয়াতের ভিত্তি এই যে, মানুষ তার নৈতিক এবং সামাজিক জীবনে আল্লাহর সেই শরয়ী আইন স্বীকার করে নেবে যা তিনি তাঁর নবীদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এই শরয়ী আইন মেনে নেয়া এবং এর সামনে নিজের স্বাধীন সত্তাকে বিলিয়ে দেয়ার নাম তিনি ইসলাম [Surrender] রেখেছেন এবং এখানে যেসব ব্যাপারে ফায়সালা আল্লাহ এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে দিয়েছেন সেসব ক্ষেত্রে মানুষের ফায়সালা করার অধিকার অস্বীকার করা হয়েছেঃ
“আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যখন কোনো ব্যাপারে ফায়সালা করে দেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ বা নরীর নিজের সে ব্যাপারে ভিন্নরূপ ফায়সালা করার অধিকার নেই। আর যেব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়, সে নিশ্চয়ই সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হলো।” [সূরা আহযাবঃ ৩৬]
নবূয়্যত মুহাম্মাদী
আল্লাহর একত্ববাদের মতো দ্বিতীয় যে জিনিসটি ইসলামে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী তা হচ্ছে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সর্বশেষ নবী। মূলত এই সেই জিনিস যার বদৌলতে আল্লাহর একত্ববাদের আকীদা শুধু কল্পনা বিলাসের পরিবর্তে একটি বাস্তব ব্যবস্থার রূপ লাভ করে এবং এর উপরই ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছে। এই আকীদার আলোকে পূর্ববর্তী সমস্ত নবীর আনীত শিক্ষা অনেক পরিবর্ধন সহকারে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেয়া শিক্ষার মধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। এজন্য খোদায়ী হিদায়াত এবং শরীয়তের স্বীকৃত ও নির্ভরযোগ্য উৎস এখন কেবল এই একটিই এবং ভবিষ্যতেও এমন আর কোনো হিদায়াত এবং শরীয়তের আগমন ঘটবেনা যে দিকে মানুষের প্রত্যাবর্তন করা জরুরী হতে পারে। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শিক্ষাই হচ্ছে সর্বোচ্চ আইন [Supreme Law] যা মহান বিচারক আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিধান আমরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দুই আকারে পেয়েছি। এক, কুরআন মজীদ, যা অক্ষরে অক্ষরে মহাবিশ্বের প্রতিপালক নির্দেশ ও হিদায়াতের সমষ্টি। দুই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উসওয়ায়ে হাসানা বা উত্তম আদর্শ তাঁর সুন্নাহ, যা কুরআনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যর ব্যাখ্যা প্রদান করে।
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু আল্লাহর বাণীর ধারকই ছিলেননা যে, কিতাব পৌছে দেয়া ছাড়া তাঁর কোনো কাজ ছিলোনা। তিনি তাঁর নিযুক্ত পথপ্রদর্শক, আইনপ্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেনা। তাঁর দায়িত্ব ছিলো এই যে, তিনি নিজের কথা ও কাজের মাধ্যমে আল্লাহর বিধানের ব্যাখ্যা পেশ করবেন, তার সঠিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করবেন, এই উদ্দেশ্য মুতাবিক লোকদের প্রশিক্ষণ দেবেন, অতপর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদেরকে একটি সুসংগঠিত জামায়াতের রূপ দিয়ে সমাজের সংস্কার সাধনের চেষ্টা করবেন, অতপর এই সংশোধিত সমাজকে একটি কল্যাণকর রাষ্ট্রের রূপ দান করে দেখিয়ে দেবেন যে, ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে একটি পূর্নাংগ সভ্যতার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা কিভাবে কায়েম হতে পারে? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
এই গোটা কাজ যা তিনি নিজের তেইশ বছরের নবূয়্যতী জীবনে আঞ্জাম দিয়েছেন-সেই সুন্নাহ যা কুরআনের সাথে মিলিয়ে হয়ে মহান আল্লাহর উচ্চতর আইনকে বাস্তাব রূপদান ও পরিপূর্ণ করে। ইসলামের পরিভাষায় এই উচ্চতর আইনের নামই হচ্ছে শরীয়া।
আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে
স্থুল দৃষ্টি সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি এ মৌলিক সত্যটি শুনার পর ধারণা করতে পারে যে, এ অবস্থায় কোনো ইসলামী রাষ্ট্রে মানবীয় আইন প্রণয়ন করার মোটেই কোনো সুযোগ নেই। কেননা এখানে তো আইনদাতা হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ। আর মুসলমানদের কাজ হচ্ছে কেবল নবীর মাধ্যমে দেয়া আল্লাহর এই আইনের আনুগত্য করে যাওয়া। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, ইসলাম মানুষের আইন প্রণয়নকে চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ করে দেয়না বরং তাকে আল্লাহর আইনের প্রাধান্যের দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেয়। এই সর্বোচ্চ আইনের অধীনে এবং তার নির্ধারিত সীমার মধ্যে মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র কি তা আমি এখানে সংক্ষেপে বর্ণনা করছিঃ
আইনের ব্যাখ্যা
মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় বিষয়ের মধ্যে এক ধরনের বিষয় এমন রয়েছে, যে সম্পর্কে কুরআন এবং সুন্নাহ সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে, অথবা কোনো বিশেষ মূলনীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। এ ধরনের বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো ফকীহ কোনো কাযী [বিচারক] অথবা কোনো আইন প্রণয়নকারী সংস্থা শরীয়ার দেয়া নির্দেশ অথবা তার নির্ধারিত মূলনীতি পরিবর্তন করতে পারেনা। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, এর মধ্যে আইন প্রণয়নের কোন সুযোগই নেই। এ অবস্থায় মানুষের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে হচ্ছে এই যে, প্রথমে সঠিকভাবে জানতে হবে আসলে নির্দেশটি কি? অতপর তার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য নির্ধারণ করতে হবে এবং কোন অবস্থা ও ঘটনার জন্য এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অনুসন্ধান করতে হবে। অতপর বাস্তব ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা দেখা দিতে পারে তার উপর এই নির্দেশ প্রয়োগের পন্থা এবং সংক্ষিপ্ত নির্দেশের আনুসংগিক ব্যাখ্যা করতে হবে। সাথে সাথে এও নির্ধারণ করতে হবে যে, ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থা ও পরিস্থিতিতে এসব নির্দেশ ও মূলনীতি থেকে সরে গিয়ে কাজ করার সুযোগ কোথায় এবং কোন সীমা পর্যন্ত রয়েছে।
কিয়াস
দ্বিতীয় প্রকারের বিষয় হলো, যে সম্পর্কে শরীয়া সরাসরি কোনো নির্দেশ দেয়নি কিন্তু তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শরীয়া একটি নির্দেশ দান করে। এ ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের কাজ এভাবে হবে যে, নির্দেশের কারণসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করে যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকপক্ষেই এই কারণসমূহ পাওয়া যাবে সেখানে এই জারী করতে হবে এবং যেসব ক্ষেত্রে বাস্তবিকই এই কারণসমূহ পাওয়া যাবেনা সেগুলোকে এ থেকে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে সাব্যস্ত করতে হবে।
ইস্তিন্বাত [বিধান নির্গতকরণ]
এমন এক প্রকারের বিষয়ও রয়েছে যেখানে শরীয়া নির্ধারিত কোনো হুকুম নেই বরং কতিপয় সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্নাংগ মূলনীতি দান করা হয়েছে। অথবা শরীয়তদাতা এই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন যে, কোন জিনিস পছন্দনীয় যার প্রসার ঘটানো প্রয়োজন এবং কোন জিনিস অপছন্দনীয় যার বিলুপ্ত হওয়া প্রয়োজন। এরূপ ব্যাপারে আইন প্রণয়নের কাজ হচ্ছে এই যে, শরীয়তের এই মূলনীতিসমূহ ও শরীয়াতদাতার এই উদ্দেশ্যেকে অনুধাবন করতে হবে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্য এমন আইন কানুন প্রণয়ন করতে হবে যার ভিত্তি এই মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শরীয়াতদাতার উদ্দেশ্যও পূর্ণ করবে।
স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্র
উপরে উল্লেখিত বিষয়সমূহ ছাড়াও এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে শরীয়া সম্পূর্ণ নীরব, এ সম্পর্কে সরাসরি কোনো হুকুমও দেয়না এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে শরীয়াতে এমন কোনো নির্দেশও পাওয়া যায় না যার উপর এটাকে কিয়াস করা যেতে পারে। এই নীরবতা স্বয়ং একথার প্রমাণ বহন করে যে, মহান আইনদাতা আল্লাহ এ ক্ষেত্রে মানুষকে নিজের রায় প্রয়োগ করে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার দিচ্ছেন। এজন্য এ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু এই আইন প্রণয়নের কাজ এমনভাবে হতে হবে যেনো তা ইসলামের প্রাণশক্তি এবং তার সাধারণ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তার মেজাজ প্রকৃতি ইসলামের মেজাজ প্রকৃতির বিপরীত না হয় এবং তা যেনো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সঠিকভাবে সংস্থাপিত হতে পারে।
ইজতিহাদ [গবেষণা]
আইন প্রণয়নের এসব কাজ-যা ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে গতিশীল রাখে এবং যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সাথে তার ক্রমবিকাশে সহায়তা করে- এক বিশেষ ইলমী তাহকীক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। ইসলামের পরিভাষায় একে বলে ইজতিহাদ’। এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে “কোনো কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা।” কিন্তু এর পরিভাষিক অর্থ হচ্ছে- “আলোচ্য কোনো বিষয়ে ইসলামের নির্দেশ অথবা তার উদ্দেশ্য কি তা জানার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করা।” কোনো কোনো লোক ভ্রান্তির শিকার হয়ে মতের সম্পূর্ণ স্বাধীন ব্যবহারকে ইজতিহাদের অর্থের মধ্যে গণ্য করে থাকে। ইসলামী আইনের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত এমন কোনো ব্যক্তি এই ভুল ধারণায় পতিত হতে পারেনা যে, এই ধরনের একটি আইন ব্যবস্থায় স্বাধীন ইজতিহাদের কোনো অবকাশ থাকতে পারে। এখানে তো আইনের উৎস হচ্ছে কুরআন এবং হাদীস। মানুষ যে আইন প্রণয়ন করতে পারে তা অপরিহার্যরূপে- হয় আইনের উৎস থেকে গৃহীত হতে হবে অথবা যে সীমা পর্যন্ত সে স্বাধীন মত প্রয়োগের সুযোগ দেয় তা সেই সীমার মধ্যে প্রণীত হতে হবে। এই বাধ্যবাধকতা উপেক্ষা করে যে ইজতিহাদ করা হবে, তা না ইসলামী ইজতিহাদ আর না ইসলামী আইন ব্যবস্থায় তার কোনো স্থান আছে।
ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলী
ইজতিহাদের উদ্দেশ্য যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত আইনকে মানব রচিত আইনের দ্বারা পরিবর্তন করা নয় বরং তাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করা এবং আইন পরিচালনার ক্ষেত্রে ইসলামের আইন ব্যবস্থাকে যুগের গতির সাথে গতিশীল করে তোলা- এজন্য আমাদের আইন প্রণয়নকারীদের মধ্যে নিম্নেক্ত গুণাবলী বর্তমান না থাকলে কোনো সঠিক এবং সুস্থ ইজতিহাদ হতে পারেনাঃ
১. আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের উপর ঈমান, তা সত্য হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস, তা অনুসরণ করার একনিষ্ঠ সংকল্প, তার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার খায়েশ না থাকা এবং উদ্দেশ্য, মূলনীতি মূল্যবোধ অন্য কোনো উৎস থেকে গ্রহণ করার পরিবর্তে শুধু আল্লাহ্ প্রদত্ত শরীয়া থেকে গ্রহণ করা।
২. আরবী ভাষা, তার ব্যাকরণ ও সাহিত্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কেননা কুরআন এই ভাষায় নাযিল হয়েছে এবং সুন্নাহ্কে জানার উপকরণও এই ভাষার মাধ্যেই রয়েছে।
৩. কুরআন ও সুন্নাহ্র জ্ঞান-যার মাধ্যমে ব্যক্তি শুধু আনুসংগিক নির্দেশ এবং তার প্রয়োগস্থান সম্পর্কেই অবহিত হবেনা বরং শরীয়াতের মূলনীতে এবং তার উদ্দেশ্যসমূহও ভালোভাবে হৃদয়ংগম করবে। তাকে একদিকে জানতে হবে যে, মানব জীবনের সংশোধন ও সংস্করের জন্য শরীয়তের সামগ্রিক পরিকল্পনা কি এবং অন্যদিকে জানতে হবে যে, এই সামগ্রিক পরিকল্পনায় জীবনের প্রতিটি বিভাগের মর্যাদা কি, শরীয়ত তার গঠন কোন্ কাঠামোয় করতে চায় এবং তা গঠন তার সামনে কি কল্যাণ রয়েছে? অন্য কথায় বলা যায়, ইজতিহাদের জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র এমন জ্ঞান দরকার যা শরীয়তের মূলে পৌঁছে যায়।
৪. উম্মতের পূর্ববর্তী মুজতাহিদদের অবদান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। ইজতিহাদের প্রশিক্ষণের জন্যই শুধু এর প্রয়োজন নয় বরং আইনগত বিবর্তন ও ক্রমবিবাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যও প্রয়োজন। ইজতিহাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই এই নয় এবং এই হওয়াও উচিত নয় যে, প্রতিটি উত্তরসূরী [Generation] পূর্বসূরীদের রেখে যাওয়া নির্মাণ কাঠামো ধ্বংস করে দিয়ে অথবা পরিত্যক্ত ঘোষাণা করে সম্পূর্ণ নতুনভাবে নির্মাণ শুরু করবে।
৫. বাস্তব জীবনের অবস্থা, পরিস্থিতি ও সমস্যা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। কেননা এগুলোর উপরেই শরীয়াতের নির্দেশ ও মূলনীতি প্রযোজ্য হবে।
৬. ইসলামী নৈতিকতার মানদন্ড অনুযায়ী উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। কেননা তাছাড়া কারো ইজতিহাদ জনগণের কাছে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য গণ্য হতে পারেনা। চারিত্রহীন লোকের উজতিহাদের মাধ্যমে যে আইন রচিত হয় তার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হতে পারেনা।
এসব বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এই নয় যে, প্রত্যেক ইজতিহাদকারীকে প্রথমে প্রমাণ করতে হবে যে, তার মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্য বর্তমান রয়েছে। বরং এর উদ্দেশ্য কেবল একথা প্রকাশ করা যে, ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলামী আইনের ক্রমবিকাশ যদি সঠিক কাঠামোর উপর হতে হয়, তাহলে তা কেবল সেই অবস্থায়ই হতে পারে যখন আইনের শিক্ষাও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন আলেম তৈরী করতে পারে। এছাড়া যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা ইসলামী আইন ব্যবস্থার মাধ্যে নিজের স্থানও করে নিতে পারবেনা এবং মুসলিম সমাজও তা একটি উপদেয় খাদ্য হিসেবে হজম করতে পারবেনা।
ইজতিহাদের সঠিক পন্থা
ইজতিহাদ এবং তা ভিত্তিতে প্রণীতব্য আইন গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারটিস যেভাবে ইজতিহাদকারীর যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল অনুরূপভাবে এই ইজতিহাদ সঠিক পন্থায় হওয়ার উপরও নির্ভরশীল। মুজতাহিদ চাই আইনের ব্যাখ্যা দান করুক অথবা কিয়াস ও ইস্তিস্বাত করুক অবশ্যই তাকে নিজের যুক্তির ভিত্তি কুরআন ও সুন্নাতের উপর রাখতে হবে। বরং বেধ কাজ [মুবাহ] সমূহের আওতায় স্বাধীনভাবে আইন প্রণয়ন করতে গিয়েও তাকে প্রমাণ করতে হবে যে, কুরেআন ও সুন্নাহ্ বাস্তবিকপক্ষেই অমুক ব্যাপারে কোনো নির্দশ অথবা মূলনীতি নির্ধারণ করেনি এবং কিয়াসের জন্যও কোনো ভিত্তি সরবাসরহ করেনি। অতপর কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যে প্রমাণ পেশ করা হবে তা অবশ্যই বিশেষজ্ঞ আলেমদের স্বীকৃত পন্থায় হতে হবে। কুরআন থেকে প্রমাণ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো আয়াতের এমন অর্থই গ্রহণ করতে হবে, আরবী ভাষার অভিধান, ব্যাকরণ এবং প্রচলিত ব্যবহার যেরূপ অর্থ করর সুযোগ রয়েছে। এই অর্থ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাক্যের পূর্বাপরের সাথে মিল থাকতে হবে, একই বিষয়ে কুরআনের অন্যা্ন্য বর্ণানার সাথে তা সংঘর্ষপূর্ণ হবেনা এবং সুন্নতের মৌখিক অথবা বাস্তব ব্যাখ্যায় তার সমর্থন বর্তমান থাকতে হবে অথবা অন্ততঃপক্ষে সুন্নাহ্ এই অর্থের বিরোধী হবেনা। সুন্নাহ্ থেকে দলীল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ভাষা এবং তার ব্যাকরণ ও পূর্বাপরের দিকে লক্ষ্য রাখার সাথে সাথে এটাও জরুরী যে, যেসব রিওয়ায়াত থেকে কোনো বিষয়ের সমর্থন বা প্রমাণ গ্রহণ করা হচ্ছে তা ইলমে উসূলে হাদীসের নীতিমালা অনুযায়ী নির্ভরযোগ্য হতে হবে, এই বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসও দৃষ্টির সামনে রাখতে হবে এবং কোনো একটি হাদীস থেকে এমন কোনো সিদ্ধান্ত বের করা যাবেনা, যা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত অন্যান্য হাদীসের পরপন্থী।
এসব সতর্কতামূলক ব্যবস্থর প্রতি লক্ষ্য না রেখে পছন্দসই ব্যাখ্যার মাধ্যমে যে ইজতিহাদ করা হবে, তাকে যদি শক্তবলে আইনের মর্যাদা যেয়াও হয়, তবে মুসলমানদের সামাগ্রিক বিবেক তা গ্রহণ করতে পারেনা। আর তা বাস্তবে ইসলামী আইন ব্যবস্থার অংশও হতে পারেনা। যে রাজনৈতিক শক্তি তা কার্যকর করবে তাদের ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার সাথে সাথে এই আইনও আবর্জনার পাত্রে নিক্ষিপ্ত হবে।
ইজতিহাদ কিভাবে আইনের মর্যাদা লাভ করে
কোনো ইজতিহদের আইনের মর্যাদা লাভ করার ব্যাপারে ইসলামী আইন ব্যবস্থায় বিভিন্ন পন্থা রয়েছে। যেমনঃ
১. এর উপর গোটা উম্মাহ্র বিশেষজ্ঞ আলেমগণের ইজমা হওয়া।
২. কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার ইজতিহাদ সাধারণভাবে গৃহীত হওয়া এবং লোকের নিজ থেকেই তা অনুসরণ করতে শুরু করা। যেমন হানাফী, শাফিঈ, মালিকী হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।
৩. কোনো ইজতিহাদকে কোনো মুসলিম সরকার কর্তৃক আইন হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া। যেমন তুর্কী উসমানী রাজত্ব এবং ভারতের মোগল রাজত্ব হানাফী ফিকাহকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় আইন হিসেবে গ্রহণ করেছিলো।
৪. রাষ্ট্রের অধীনে কোনো সংস্থার সাংবিধানিক মর্যাদাবলে আইন প্রণয়নের অধিকার লাভ করা এবং তাদের ইজতিহাদের মাধ্যমে কোনো আইন প্রণয়ন করা।
এসব পন্থা ছাড়া বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ আলেম যেসব ইজতিহাদ করে থাকেন তার মর্যাদ ফতোয়ার অধিক নয়। এখন থাকলো কাযীদের [ইসলামী রাষ্ট্রের বিচারক] সিদ্ধান্ত। তা ঐসব বিশেষ মোকাদ্দমায় তো অবশ্যই আইন হিসেবে প্রযোজ্য হয় যেসব মামলায় ঐ সিদ্ধন্ত কোনো আদালত করেছে। এগুলো কোর্টের নযীর হিসেবেও মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকে। কিন্তু সার্বিক অর্থে তা আইন নয়। এমনকি খোলাফায়ে রাশেদীন কাযী হিসেবে যেসব ফায়সালা করেছেন তাও ইসলামে আইন হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। ইসলামী আইন ব্যবস্থায় কাযীদের প্রণীত আইনের [Judge Made Law] কোনো ধারণা বর্তমান নেই। [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮]
১. জনৈক হাদীস প্রত্যাখ্যানকারীর অভিযোগ ও তার জবাব
ইসলামে আইন প্রণয়ন ও ইজতিহাদের বিষয় সম্পর্কেত আমার প্রবন্ধের উপর যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, আমি এখানে অতি সংক্ষেপে তার জবাব দেয়ার চেষ্টা করবো।
কুরআনের সাথে সুন্নতের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, প্রথম প্রশ্ন তার উপর উত্থাপন করা হয়েছ। এর জবাবে ক্রমিক ধারা অনুযায়ী আমি কয়েকটি কথা বলবো যাতে বিষয়টি আপনাদের সামনে পূর্ণরূপে স্পষ্ট হয়ে যায়।
১. এটা এমন এক ঐতিহাসিক সত্য যা কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায়না যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যতের পদে অভিষিক্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে শুধু কুরআন পৌঁছে দিয়েই দায়িত্ব শেষ করেননি, বরং একটি ব্যাপাক আন্দোলনের নেতৃত্বও দিয়েছেন। এর ফলশ্রুতিতেই একটি মুসলিম সমাজের গোড়াপত্তন হয়, সভ্যতা সংস্কতির এক নতুন ব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করে এবং একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম হয়। এখন প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআন পৌঁছে দেয়া ছাড়াও এসব কাজ যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন- তা শেষ পর্যন্ত কি হিসেবে করেছেন? এসব কাজ কি নবীর কাজ হিসেবে সম্পাদিত হয়েছেলো যার মধ্যে তিনি আল্লাহ্র মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করেছেন- যেমনটি কুরআন আল্লাহ্র মর্জীর প্রতিনিধিত্ব করছে? নাকি তাঁর নবূয়্যতী মর্যাদা কুরআন শুনিয়ে দেয়ার পর শেষ হয়ে যেতো এবং এরপর তিনি সাধারণ মুসলমানদের মতো শুধু একজন মুসলমান হিসেবে থেকে যেতেন, যার কথা ও কাজ নিজের মধ্যে কোনো আইনের সনদ ও দলীলের মর্যাদা রাখতোনা? যদি প্রথম কথাটি মেনে নেয়া হয় তাহলে সুন্নহ্কে কুরআনের সাথে আইনের উৎস ও দলীল হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। অবশ্য দ্বীতিয় অবস্থায় সুন্নাহ্কে আইনের মর্যাদা দেয়ার কোনো কারণ থাকতে পারেনা।
২. কুরআনের ব্যাপারটি সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল পত্রবাহক ছিলেননা বরং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নিযুক্ত করা প্রথপ্রদর্শক, আইন প্রণেতা এবং শিক্ষকও ছিলেন, যাঁর আনুগত্য ও অনুসরণ করা মুসলমানদের জন্য
{১. ১৯৫৮ সালোর ৩ জানুয়ারী লাহোরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সোমিনারে পূর্বোক্ত প্রবন্ধ পাঠের পর জনৈক মুনকিরে হাদীস [হাদীস প্রত্যাখ্যানকারী] উঠে দাঁড়িয়ে তার উপর কতিপয় অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন। ঐ মজলিসেই প্রবন্ধাকারের পক্ষ থেকে এ জবাব দেয়া হয়।}
বাধ্যতামূলক ছিলো এবং যাঁর জীবনকে সমগ্র ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্য নমুনা হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। বুদ্ধিবিবেক সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তা একথা মেনে নিতে অস্বীকার করে যে, একজন নবী কেবল আল্লাহ্র কালাম পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত তা নবী থাকবেন, কিন্তু এরপর তিনি একজন সাধারণ ব্যক্তি মাত্র রয়ে যাবেন। মুসলমানদের সম্পর্কে যতোদূর বলা যায়, তারা ইসলামের সূচনা থেকে আজ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিটি যুগে এবং গোটা দুনিয়ায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদর্শ, তাঁর অনুসরণ অপরিহার্য এবং তাঁর আদেশ নিষেধের আনুগত্যকে বাধ্যতামূলক বলে স্বীকার করে আসছে। এমনকি কোনো অমুসলিম পন্ডিতও এই বাস্তব ঘটনাকে অস্বীকার করতে পারেনা যে, মুসলমানরা সব সময় তাঁর এই মর্যাদা স্বীকার করে আসছে এবং এরই ভিত্তিতে ইসলামের আইন ব্যবস্থায় সুন্নাহ্কে কুরআনের সাথে আইনের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছে।
এখন আমি জানিনা, কোনো ব্যক্তি সুন্নাতের এই আইনগত মর্যাদা কিভাবে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে পরিষ্কারভাবে না বলে যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কুরআন পড়ে শুনিয়ে দেয়া পর্যন্ত নবী ছিলেন এবং একাজ সম্পন্ন করার সাথে সাথে নবূয়্যতী মর্যাদা শেষ হয়ে গেছে? অনন্তর সে যদি এরূপ দাবী করেও তাহলে তাকে বলতে হবে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই ধরনের মর্যাদা সে নিজেই দিচ্ছে না কুরআন তাঁকে এই ধরনের মর্যাদা দিয়েছে? প্রথম ক্ষেত্রে থেকে তার দাবীর সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে।
৩. সুন্নাহ্কে স্বয়ং আইনের একটি উৎস হিসেবে মেনে নেয়ার পর এই প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তা জানার উপায় কি? আমি এর জবাবে বলতে চাই, আজ চৌদ্দশত বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর এই প্রথম বারের মতো আমরা এ প্রশ্নের সন্মূখীন হইনি যে, দেড় হাজার বছর পূর্বে যে নবূয়্যতের আবির্ভাব হয়েছিলো তা কি সুন্নহ্ রেখে গেছে? দুটি ঐতিহাসিক সত্য কোনোক্রমেই অস্বীকার করা যায়নাঃ
একঃ কুরআনের শিক্ষা এবং মুহাম্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের উপর যে সমাজ ইসলামের সূচনার প্রথম দিন কায়েম হয়েছিলো তা সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত অবিরত জীবন্ত রয়েছে, তার জীবনে একটি দিনেরও বিচ্ছিন্নতা ঘটেনি এবং তার সমস্ত বিভাগ ও সংস্থা এই পুরো সময়ে উপর্যুপরি কাজ করে আসছে। আজ সারা দুনিয়ার মুসলমানদের মধ্যে আকীদা বিশ্বাস, চিন্তাপদ্ধতি, চরিত্র নৈতিকতা, মূল্যবোধ, ইবাদত ও মুয়ামালাত, জীবন পদ্ধতি এবং জীবন পন্থার দিক থেকে যে গভীর সামঞ্জস্য বিরাজ করছে, যার মধ্যে মতভেদের উপাদানের চাইতে ঐক্যের উপাদান অধিক পরিমাণে বর্তমান রয়েছে, যা তাদেরকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও একটি উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত রাখার সবচেয়ে বড় বুনিয়াদ। কারণ- এগুলোই একথার পরিষ্কার প্রমাণ যে, এ সমাজকে কোনো একটি সুন্নাতের উপরই কায়েম করা হয়েছিলো এবং সে সুন্নাত শতাব্দীর পর শতাব্দার দীর্ঘতায় অবিরতভাবে জারী রয়েছে। এটা কোনো হারানো জিনিস নয় যা অনুসন্ধান করার জন্য আমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে বেড়াতে হবে।
দুইঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর থেকে প্রতিটি যুগে মুসলমানরা এটা জানার জন্য অবিরত চেষ্টা করতে থাকে যে, প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সুন্নাত কি এবং নতুন কোনো জিনিস তাদের জীবন ব্যবস্থায় কোনো কৃত্রিম পন্থায় অনু্প্রবেশ করছে কিনা? সুন্না্ত যেহেতু তাদের জন্য আইনের মর্যাদা রাখতো, এর ভিত্তিতে তাদের বিচারালয়সমূহে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো এবং তাদের ঘর থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্তকার ব্যবস্থা পরিচালিত হতো, এজন্য তারা এর তথ্যানুসান্ধানে বেপরোয়া ও নির্ভীক হতে পারেনা। এই অনুসন্ধানের উপায় এবং তার ফলাফলও ইসলামের প্রথম খিলাফতের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত আমরা বংশানুক্রমে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে গিছি এবং কোনো বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই প্রতিটি জেনারেশনের অবদান সংরক্ষিত আছে।
এই দুটি সত্যকে যদি কোনো ব্যক্তি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করে নেয়া এবং সুন্নাতকে জানার উপায় ও মাধ্যমগুলো রীতিমতো অধ্যয়ন করে তাহলে সে কখনো এই সন্দেহের শিকার হতে পারেনা যে, এটা কোনো সমাধানের অযোগ্য ধাঁ ধাঁ, তারা যারা সন্মুখীন হয়ে পড়েছি।
৪. সুন্নাতের অনুসন্ধান, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিসন্দেহে অনেক মতবিরোধ হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হতে পারে। কিন্তু এরূপ মতবিরোধ কুরআনের অস্যখ্য নির্দেশ ও বাণীর অর্থ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও হয়েছে এবং হতে পারে। এসব মতবিরোধ যদি কুরআনকে পরিত্যাগ করার জন্য দলীল হতে না পারে তাহলে সুন্নাত পরিত্যাগ করার জন্য্ এই মতবিরোধকে কিভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে? এই মূলনীতি পূর্বেও মান্য করা হয়েছে এবং আজো তা না মেনে কোনো উপায় নেই যে, যে ব্যক্তিই কোনো নির্দেশকে কুরআনের নির্দেশ অথবা সুন্নাতের নির্দেশ বলে দাবী করবে তাকে নিজের একথার সপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। তার কথা যদি বলিষ্ঠ হয় তাহলে উম্মতের বিশেষজ্ঞ আলেমদের দ্বারা অথবা অন্ততপক্ষে তাদের কোনো বিরাট অংশের দ্বারা নিজের মতকে গ্রহণযোগ্য করিয়ে নেবে। আর যেকথা প্রমাণের দিক থেকে দুর্বল হবে তা অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। এই সেই মূলনীতি যার ভিত্তিতে দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী কোটি কোটি মুসলমান কোনো একটি ফিকাহ ভিত্তিক মাযহাবে সম্মিলিত হয়েছে এবং তাদের বিরাট বিরাট জনবসতি কুরআনী নির্দেশের কোনো ব্যাখ্যা এবং প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতের কোনো সমষ্টির উপর নিজেদের সামগ্রিক ব্যবস্থা কায়েম করেছে।
আমার প্রবন্ধের উপর দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করা হয়েছে যে, আমার বক্তব্যে স্ববিরোধীতা রয়েছে। অর্থাৎ আমার এ বক্তব্যঃ “কুরআন ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট এবং চূড়ান্ত নির্দেশসমূহের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করার অধিকার কারো নেই।” প্রশ্নকারীর মতে আমার এই বক্তব্য আমার নিন্মোক্ত বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিকঃ “ব্যতিক্রমধমী অবস্থা ও ঘটনার ক্ষেত্রে এই নির্দেশসমূহ থেকে সরে গিয়ে কাজ করার অবকাশ এবং ইজতিহাদের মাধ্যমে তার প্রয়োগস্থান নির্দিষ্ট করা যেতে পারে।” আমি বুঝতে পারছিনা এর মধ্যে কি বৈপরিত্য অনুভব করা হয়েছে। একান্ত উপায়ান্তরহীন পরিস্থিতিতে সাধারণ নীতির ব্যতিক্রম দুনিয়ার প্রতিটি আইনে রয়েছে। কুরআনেও এধরনের অনুসতির অনেক দৃষ্টান্ত মওজূদ রয়েছে। এই দৃষ্টান্তসমূহ থেকে ফিকাহবিদগণ সেই মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন যাকে অনুমতির সীমা ও তার প্রয়োগস্থান নির্ধারণ করা জন্য বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমনঃ
তৃতীয় প্রশ্ন সেসব লোকদের সম্পর্কে করা হয়েছে যারা এখানে নিজেদের প্রবন্ধসমূহে ইজতিহাদের কতিপয় শর্ত বর্ণনা করেছেন। আমিও যেহেতু তাদের মধ্যে একজন, তাই এর জবাব দেয়ার দায়িত্ব আমারও রয়েছে। আমি আবেদন করবো, অনুগ্রহপূর্বক আর একবার আমার বর্ণনাকৃত শর্তগুলোর উপর দষ্টি নিবদ্ধ করুন। অতপর বলুন, আপনি এর মধ্যকার কোন্ শর্তটি বাদ দিতে চান। এই শর্তটি কি, ইজতিহাদকারীদের মধ্যে শরীয়তকে অনুসরণ করার একনিষ্ঠ ইচ্ছা থাকতে হবে এবং তারা এর সীমা লংঘন করার খাহেশমান্দ হবেননা? নাকি এই শর্তটি যে, তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাতের ভাষা অর্থাৎ আরবী ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে? নাকি এই শর্তটি, তাদেরকে অন্তত কুরআন ও সুন্নাত এই পরিমাণ অধ্যয়ন করতে হবে যাতে তারা শরীয়তের ব্যবস্থা ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হয়? অথবা পূর্বেকার মুজতাহিদদের কৃত কাজের উপরও তাদের দৃষ্টি থাকতে হবে- এই শর্তটি? অথবা তাদের চলমান বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে- এই শর্তটি? অথবা তারা দুশ্চরিত্র এবং ইসলামের নৈতিক মানদন্ড থেকে নীচে অবস্থান করবেননা- এই শর্তটি?
এসব শর্তের যেটিকে আপনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেন তা চিহ্নিত করে দিন। একথা বলা যে, গোটা ইসলামী দুনিয়ায় দশ বারজনের অধিক এমন লোক পাওয়া যাবেনা, যারা এই শর্তের মানদন্ডে উৎরে যেতে পারে-আমার মতে দুনিয়াব্যপী মুসলমানদের সম্পর্কে এটা অত্যন্ত জঘন্য মন্তব্য। খুব সম্বব আজ পর্যন্ত আমাদের বিরোধীরাও আমাদেরকে এতাটা পতিত মনে করেনি যে, চল্লিশ পঞ্চাশ কোটি মুসলমানের মধ্যে এই বৈশিষ্টের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সংখ্যা দশ বারজনের অধিক হবেনা। তদুপরি আপনি যদি ইজতিহাদের দরজা পন্তিত মূর্খ নির্বিশেষে সবার জন্য খুলে দিতে চান তাহলে আনন্দের সাথে খুলে দিন। কিন্তু আমাকে বলুন দুশ্চরিত্র, জ্ঞানহীন এবং অসৎ উদ্দেশ্য সম্পন্ন লোকেরা যে ইজতিহাদ করবে তাকে আপনি আপনি কিভাবে মুসলিম জনতার কন্ঠনালীর নীচে নামাবেন? [তরজমানুল কুরআন, জানুয়ারী ১৯৫৮]
৩. আইন প্রণয়ন, শূরা [পরামর্শ পরিষদ] ও ইজমা
ইসলামী আইন প্রবর্তনের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম মত প্রকাশ করা হচ্ছে। এই প্রসংগে এক বন্ধু নিজের মনের জটিলতা দূর করার উদ্দেশ্যে লিখেছেনঃ
“ইসলামে আইন প্রণয়নের যথার্থতা ও প্রকৃতি এবং তার কর্মপরিসর নির্ধারণে অনেক বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। একদিকে বলা হচ্ছে, ইসলামে আইন প্রনয়নের মূলত কোনো অবকাশই নেই। আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আইন প্রণয়ন করে দিয়েছেন। মুসলমানদের কর্তব্য হচ্ছে তদনুযায়ী কাজ করা এবং তা কার্যকর করা। অপরদিকে কতিপয় লোকের মতে বর্তমানে আইন প্রণয়নের পরিসর এতোটা প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে যে, মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের এই অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তারা ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্ধারিত বিস্তারিত নিয়ম কানুনে পরিবর্তন ও সংকোচন করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, তারা নামায এবং রোযার বাহ্যিক কাঠামোর মধ্যে সংকোচন ও সংযোজন করতে পারেন।
অনুগ্রহপূর্বক বিস্তারিতভাবে বলে দিন যে, ইসলামে আইন প্রণয়নের সীমা এবং তার বিভিন্ন পর্যায় কি কি? তাছাড়া একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিন যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের ব্যক্তিগত এবং শূরাভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও ফিকাহের ইমাম ও মুজতাহিদদের রায়ের আইনগত মর্যাদা কি? এই সাথে যদি শূরা [পরামর্শ পরিষদ] এবং ইজমার [ঐক্যমত] তাৎপর্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয় তাহলে ভালোই হয়।”
১. জবাবঃ আইন প্রণয়নের বুনিয়াদী মূলনীতি
ইসলামে ইবাদতের পরিমন্ডলে চূড়ান্তভাবেই আইন প্রণয়নের কোন অবকাশ নেই। অবশ্য ইবাদত ছাড়া নির্বাহী কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে কেবল সেখানেই আইন প্রণয়নের অবকাশ রয়েছে যেখানে কুরআন ও সুন্নাহ নীরবতা অবলম্বন করেছে। ইসলামে আইন প্রণয়নের ভিত্তি হচ্ছে এই মূলনীতি যে, “ইবাদতের ক্ষেত্রে কেবল সে কাজ করো যা বলে দেয়া হয়েছে এবং নিজের পক্ষ থেকে ইবাদতের কোনো নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করোনা। আর মুয়ামালাতের নির্বাহী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার আনুগত্য করো, যা থেকে বিরত রাখা হয়েছে- তা করা থেকে বিরত থাকো এবং যে জিনিস সম্পর্কে শরীয়া প্রণেতা [আল্লাহ এবং তাঁর রসূল] নীরব থেকেছেন সে ক্ষেত্রে তোমরা নিজেদের সঠিক দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী কাজ করার জন্য স্বাধীন।” ইমাম শাতিবী [রহঃ] তাঁর ‘আল-ই’তিসাম’ গ্রন্থে উল্লেখিত মূলনীতিটি এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ
ইবাদতের নির্দেশ অভ্যাসের নির্দেশ থেকে ভিন্নতর। অভ্যাসের ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে এই যে, যে জিনিস সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে, তাতে যেনো নিজের সঠিক দৃষ্টিকোণের উপর কাজ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে ইবাদতের ক্ষেত্রে এমন কোনো কথা ইস্তিম্বাতের [কারণ দেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ] মাধ্যমে বের করা যায়না যার মূল শরীয়াতে বর্তমান নেই। কেননা ইবাদতের কাঠামো পরিষ্কার নির্দেশ এবং পরিষ্কার অনুমতির সম্পর্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত রয়েছে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে তদ্রূপ নয়। এই পার্থক্যের কারণ এই যে, অভ্যাসের ক্ষেত্রে মোটমুটিভাবে আমাদের জ্ঞান সঠিক পথ জেনে নিতে পারে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা নিজেদের জ্ঞানের সাহায্যে এটা জানতে পারিনা যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ কোনটি।” [২য় খন্ড, পৃঃ ১১৫]
২. আইন প্রণয়নের চারটি বিভাগ
মুয়ামালাত বা আদান প্রদান ও নির্বাহী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আইন প্রণয়নের চারটি বিভাগ রয়েছেঃ
১. ব্যাখ্যা বিশ্লেষণঃ অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা আদেশ অথবা নিষেধের ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন সে সম্পর্কে নসের [কুরআনের আয়াত] অর্থ অথবা তার উদ্দেশ্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা।
২. কিয়াসঃ অর্থাৎ যেসব ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতার সরাসরি কোনো নির্দেশ বর্তমান নেই, কিন্তু যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপারের নির্দেশ বর্তমান আছে। এর মধ্যে নির্দেশের কারণ নির্ধারণ করে এই নির্দেশকে এই ভিত্তির উপর জারী করা যে, এখানেও ঐ একই কারণ পাওয়া যায়- যার ভিত্তিতে ঐ নির্দেশ তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে দেয়া হয়েছিলো।
৩. ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদঃ অর্থাৎ শরীয়তের বর্ণিত ব্যাপক মূলনীতিকে প্রাসংগিক মাসায়ালা ও বিষয়ের অনুকূল করা এবং নসসমূহের ইংগিত, লক্ষণ ও দাবীকে উপলব্ধি করে বুঝে নেয়া যে, শরীয়ত প্রণেতা আমাদের জীবনের ব্যাপারসমূহকে কোন আকারে ঢেলে সাজাতে চান।
৪. যেসব ব্যাপারে শরীয়ত প্রণেতা কোনো পথ নির্দেশ দেননি সেসব ক্ষেত্রে ইসলামের ব্যাপক উদ্দেশ্য ও সার্বিক স্বার্থ সামনে রেখে এমন আইন প্রণয়ন করা, যা প্রয়োজনও পূরণ করবে এবং সাথে সাথে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থার প্রাণসত্ত্বা ও মেজাজ প্রকৃতির পরিপন্থীও হবেনা। ফিকাহবিদগণ এই জিনিসকে ‘মাসালিহে মুরসালা’ ও ‘ইস্তিহসান’ ইত্যাদি নামকরণ করেছেন। মাসালিহে মুরসালার অর্থ হচ্ছে, সেই সার্বিক কল্যাণকর জিনিস যা আমাদের সঠিক দৃষ্টিভংগির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। আর ইস্তিহসানের অর্থ হচ্ছে কোনো একটি ব্যাপারে কিয়াস প্রকাশ্যত একটি হুকুম আরোপ করে, কিন্তু দীনের মহান স্বার্থে অন্যরূপ নির্দেশের দাবী করে। এজন্য প্রথম নির্দেশের পরিবর্তে দ্বিতীয় নির্দেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে তা কার্যকর করা হয়।
৩. মাসালিহে মুরসালা ও ইস্তিহসান
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, কিয়াস ও ইস্তিম্বাতের জন্য তো অধিক আলোচনার কোনো প্রয়োজন নেই। অবশ্য মাসালিহে মুরসালা ও ইস্তিহসানের উপর আরো কিছু আলোকপাত করবো। ইমাম শাতিবী (রহঃ) তাঁর ‘আল ই’তিসাম’ গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা করেছেন এবং এসম্পর্কে এতো মূল্যবান আলোচনা করেছেন যে, এর চেয়ে ভালো আলোচনা উসূলে ফিকহের কোনো কিতাবে দৃষ্টিগোচর হয়নি। এতে তিনি বিস্তারিত দলীলের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, মাসালিহে মুরসালার অর্থ আইন প্রণয়নের অবাধ অনুমতি নয়, যেমন কতিপয় লোক মনে করে থাকে। বরং এর জন্য তিনটি অপরিহার্য শর্ত রয়েছেঃ
একঃ এই পন্থায় যে আইন প্রণয়ন করা হবে তা শরীয়তের উদ্দেশ্যর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, তার পরিপন্থী হতে পারবেনা।
দুইঃ যখন তা জনগণের সামনে পেশ করা হবে, সাধারণ জ্ঞানের কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে হবে।
তিনঃ তা কোনো প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অথবা কোনো প্রকৃত অসুবিধা দূর করার জন্য হতে হবে। [আল-ই’তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১০-১১৪]
অতপর তিনি ইস্তিহসান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, প্রকাশ্যত কোনো দলীলের ভিত্তিতে যদি কিয়াসের দাবী এই হয় যে, একটি ব্যাপারে একটি বিষয়ে নির্দেশ দেয়া প্রয়োজন, কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিতে এই নির্দেশ সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থী, অথবা এর দ্বারা এমন কোনো ক্ষতি বা ত্রুটি সংঘটিত হতে পারে যা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করার যোগ্য, অথবা তা উরফের [প্রচলিত রীতি] পরিপন্থী- তখন এটাকে পরিত্যাগ করে ভিন্নতর নির্দেশ দান হচ্ছে ইহসান। অবশ্য ইস্তিহসানের জন্য শর্ত হচ্ছে এই যে, প্রকাশ্য কিয়াসকে পরিত্যাগ করে কিয়াসের পরিপন্থী নির্দেশ দানের জন্য কোনো শক্তিশালী কারণ বর্তমান থাকতে হবে যাকে যুক্তিসংগত দলীল সহকারে বিবেচনাযোগ্য প্রমাণ করা যেতে পারে। [আল-ই’তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১১৮-১৯]
৪. আদালতের সিদ্ধান্ত এবং রাষ্টীয় আইনের মধ্যেকার পার্থক্য
এই চারটি বিভাগ সম্পর্কে কোনো মুজতাহিদ অথবা ইমামের ব্যক্তিগত রায় এবং পর্যালোচনা একটি পজ্ঞাপূর্ণ রায় এবং পর্যালোচনা তো হতে পারে, যার ওজন রায়দাতার বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিত্বের ওজন অনুযায়ী-ই হবে। কিন্তু তথাপি তা আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। আইন প্রণয়নের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে ইসলামী রাষ্টের আরবাবে হল ওয়াল আকদের [সিদ্ধান্ত এবং সমাধান পেশ করার মত যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের] পরামর্শ পরিষদ থাকবে এবং তারা নিজেদের ইজমা অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে একটি ব্যাখ্যা, একটি কিয়াস, একটি ইস্তিম্বাত ও ইজতিহাদ অথবা একটি ইস্তিহসান ও মুসলিহাতে মুরসালাকে গ্রহণ করে তাকে আইনের রূপ দেবেন। খিলাফতে রাশেদার আমলে আইন প্রণয়নের জন্য এই ব্যবস্থাই ছিলো। আমি আমার “ইসলামী দস্তুর কী তাদবীন” [ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন] পুস্তিকায় এর ব্যাখ্যা করেছি। অতএব এখানে তার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই। [উক্ত পুস্তিকাটি এগ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।] এখানে আমি মাত্র কয়েকটি দৃষ্টন্ত উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করবো। তা থেকেই অনুমান করা যাবে যে, খিলাফতে রাশেদার যুগে জাতীয় প্রয়োজন দেখা দিলে কিভাবে আইন প্রণয়ন করা হতো এবং সে যুগে আইন ও আদালতের ফায়সালাসমূহের মধ্যে কি পার্থক্য ছিলো।
কতিপয় দৃষ্টান্ত
১. মদ সম্পর্কে কুরআন মজীদে কেবল হারাম হওয়ার ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই অপরাধের জন্য শাস্তির কোনো সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এজন্য কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি বরং তিনি যাকে যেরূপ শাস্তি প্রদান উপযুক্ত মনে করতেন তা দিতেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেদের যুগে চল্লিশটি বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করেন, কিন্তু এ জন্য রীতিমতো কোনো আইন প্রণয়ন করেননি। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর যুগে যখন শরাব পানের অভিযোগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো, তখন তিনি সাহাবাদের পরামর্শ পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এক সংক্ষিপ্ত ভাষণে প্রস্তাব দিলেন যে, এজন্য আশি বেত্রদন্ডের ব্যবস্থা করা হোক। পরামর্শ পরিষদ তাঁর সাথে একমত হলেন এবং ভবিষ্যতের জন্য ইজমা সহকারে এই আইন প্রণয়ন করেন। [আল-ই’তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০১]
২. খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এই আইনগত প্রণয়ন করা হলো যে, কারিগর বা শিল্পীদের যদি কোনো জিনিস তৈরী করতে দেয়া হয় [সেলাই করার জন্য কাপড়, অথবা অলংকার বানানোর জন্য সোনা] এবং তা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তাদেরকে এর মূল্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। এই সিদ্ধান্তও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নিম্নোক্ত ভাষণের ভিত্তিতে হয়েছে যে, কারিগরদের যদিও এই অবস্থায় বাহ্যত দোষী সাব্যস্ত করা যায়না, যখন তা তার অবহেলার কারণে ধ্বংস না হয়ে থাকে, কিন্তু যদি এরূপ না করা হয় তাহলে জিনিসপত্রের হিফাজতের ক্ষেত্রে শিল্পীদের অবহেলা প্রদর্শনের আশংকা রয়েছে। এজন্য সামগ্রিক স্বার্থের দাবী হচ্ছে এই যে, তাদেরকে এই জিনিসের জামানতদার সাব্যস্ত করা হবে। সুতরাং এই সিদ্ধান্তও ইজমার সাহায্যে হয়েছে। [ই’তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০২]
৩. হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু সিদ্ধান্ত নিলেন যে, এক ব্যক্তির হত্যাকান্ডে যদি একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকে তাহলে সবার উপর কিসাসের দন্ড কার্যকর হবে। ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফিঈ [রহঃ] এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন, কিন্তু এটাকে আইন হিসেবে মেনে নেয়া হয়নি। কেননা এটি একটি আদালতী ফায়সালা ছিলো, পরামর্শ পরিষদে ইজমার মাধ্যমে অথবা অধিকাংশের মতের ভিত্তিতে আইন হিসেবে বানানো হয়নি। [ই’তিসাম, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৭]
৪. নিখোজ ব্যক্তির স্ত্রী যদি আদালতের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করে নেয়, অতএব তার পূর্বতন স্বামী ফিরে আসে, তাহলে তাকে কি প্রথম স্বামী পাবে না সে দ্বিতীয় স্বামীর কাছে থাকবে? এই প্রসংগে খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্নরূপ ফায়সালা করেন। কিন্তু কোনো ফায়সালাই আইনের মর্যাদা লাভ করেনি। কেননা এই প্রসংগটিকে পরামর্শ পরিষদে পেশ করে ইজমা অথবা অধিকাংশের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে কোনো ফায়সালায় পরিণত করা হয়নি। [ই’তিসাম, ২য় খন্ড পৃঃ ১২৬]
উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, ইংরেজ আইনে আদালতের সিদ্ধান্তের যে মর্যাদা রয়েছে, ইসলামে আদালতের সেদ্ধান্তের সে মর্যাদা নেই। বৃটিশ আইনের বিচারকদের সিদ্ধান্তের দৃষ্টান্তসমূহ আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারে কিন্তু ইসলামে নসের একটি ব্যাখ্যা গ্রহণ করে, অথবা নিজের কিয়াস অথবা ইজতিহাদের ভিত্তিতে করে থাকেবেন, কিন্তু তা একটি স্বতন্ত্র আইনের মর্যাদা লাভ করতে পারেনা। বরং একই বিচারক একটি মামলায় একটি ফায়সালা দেয়ার পর সব সময়ের জন্য নিজের এই ফায়সালা অনুসরণ করা তার জন্য বাধ্যতামূলক নয়। এরপরও তিনি উল্লেখিত মামলার সাথে সামঞ্জ্যসপূর্ণ অন্যান্য মামলায় ভিন্নরূপ ফায়সালা করতে পারেন- যদি তার সামনে পূর্বেকার ফায়সালার ত্রুটি পরিষ্কার হয়ে যায়।
খিলাফতে রাশেদার পর যখন পরামর্শ পরিষদ ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যায়, তখন মুজতাহিদ ইমামগণ ফিকহের যে বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন- তা আধা আইনের মর্যাদা এজন্য লাভ করে যে, কোনো এলাকার অধিবাসীদের সর্বাধিক সংখ্যক আইনের মর্যদা এজন্য লাভ করে যে, কোনো এলাকার অধিবাসীদের সর্বাধিক সংখ্যক লোক কোনো এক ইমামের ফিকাহ গ্রহণ করে নেয়। যেমন ইরাক ইমাম আবু হানীফার ফিকাহ, স্পেনে ইমাম মালেকের ফিকাহ, মিসরে ইমাম শাফিঈর ফিকাহ ইত্যাদি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়। কিন্তু এই ব্যাপক গ্রহণ কোথাও কোনো ফিকাহকে সঠিক অর্থে আইনে পরিণত করেনি। যেখানেই তা আইনে পরিণত হয় তা এই ভিত্তিতে যে, দেশের সরকার তাকে আইন হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।
ইজমার সংজ্ঞা
ইজমার সংজ্ঞা নির্ধারণে বিশেষজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম শাফিঈ [রহঃ]-এর মতে, “কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে সমস্ত বিশেষজ্ঞ আলেমের ঐক্যমত এবং এর পরিপন্থী কোনো মত বর্তমান না থাকলে তাকে ইজমা বলে।” ইবনে জারীর তাবারী [রহঃ] এবং আবু বাকর আল-রাযী [রহঃ]-এর পরিভাষায় অধিকাংশের মতকেও ইজমা বলে। ইমাম আহমদ [রহঃ] যখন কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে একথা বলেন যে, “আমাদের জানা মতে এর পরিপন্থী কোনো মত নেই,” তখন এর এই অর্থ গ্রহণ করা হয় যে, তাঁর মতে এই মাসয়ালার উপর; ইজমা হয়েছে।
ইজমা হুজ্জাত হওয়ার মর্যাদাটি সবার কাছে স্বীকৃত। অর্থাৎ নসের যে ব্যাখ্যার উপর, অথবা যে কিয়াস ও ইজতিহাদের উপর অথবা সামগ্রিক কল্যাণ সম্বলিত যে আইনের উপর উম্মাতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক। ইজমার হুজ্জাত হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই, নিন্তু ইজমার প্রমাণ ও প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্পর্কে মতবিভেদ আছে। খোলাফায়ে রাশেদীনে যুগ সম্পর্কে বলা হয়, এ যুগে যেহেতু ইসলামী সংগঠন ব্যবস্থা যথারীতি কায়েম ছিলো এবং পরামর্শ পরিষদের অধীনে তা পরিচালিত ছিলো, তাই সে সময়কার ইজমা ও অধিকাংশের ফায়সালা জ্ঞাত এবং নির্ভরযোগ্য বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন সংগঠন ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে গেলো এবং পরামর্শ পরিষদ ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হয়ে গেলো তখন এটা জ্ঞাত হওয়ার কোনো উপায় অবশিষ্ট থাকলোনা যে, বাস্তবিকপক্ষে কোন্ জিনিসের উপর ইজমা আছে আর কোন্ জিনিসের উপর নেই। এর কারণে খিলাফতে রাশেদার যুগের ইজমা তো স্বীকৃত এবং তা প্রত্যাখ্যান করার কোনো উপায় নেই। কিন্তু পরবর্তী যুগের কোনো লোক যখন দাবী করে যে, অমুক মাসয়ালার উপর ইজমা হয়েছে, তখন বিশেষজ্ঞ আলেমগণ তার এ দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে আমাদের মতে, কোনটির উপর ইজমা হয়েছে আর কোনটির উপর হয়নি তা জানার জন্য ইসলামী ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা একান্ত প্রয়োজন।
ইমাম শাফিঈ [রহঃ] এবং ইমাম আহমদ [রহঃ] আদৌ ইজমার অস্তিত্বকে স্বীকার করতেননা বলে যে কথা সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে, অথবা অন্য কোনো ইমাম ইজমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন- এসব কিছু উপরে উল্লেখিত কথা না বুঝার কারণেই হয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যখন কোনো মাসয়ালার উপর আলোচনা করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি দাবী করে যে, যখন কোনো মাসয়ালার উপর আলোচনা করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তি দাবী করে যে, সে যা কিছু বলছে তার উপর ইজমা রয়েছে- কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর কোনো প্রমাণ বর্তমান থাকতোনা-তখন এই লোকেরা উল্লেখিত দাবী মেনে নিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। ইমাম শাফিঈ [রহঃ] তাঁর ‘জিমাউল ইলম’ গ্রন্থে এই বিষয়ের উপর ব্যাপক আলোচনা করে বলেছেন যে, ইসলামী বিশ্বের পরিধি বিস্তৃত হওয়া ও বিভিন্ন এলাকায় বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং সংগঠন ব্যবস্থা এলোমেলো হয়ে যাবার পর এখন কোনো আংশিক বা আনুসংগিক মাসয়ালার ব্যাপারে আলেমদের মতামত কি তা জানাটা কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য আনুসংগিক মাসয়ালার ক্ষেত্রে ইজমার দাবী করাটা মূলত ভুল। অবশ্য ইসলামের মূলনীতিসমূহ, তার রুকনসমূহ এবং বড় বড় মাসয়ালা সম্পর্কে এটা অবশ্যই বলা যায় যে, এর উপর ইজমা রয়েছে। যেমন নামাযের ওয়াক্ত পাঁচটি, অথবা রোযার সীমারেখা এই ইত্যাদি। একথাটিকে ইমাম ইবনে তাইমিয়া [রহঃ] এভাবে বলেছেনঃ
“ইজমার অর্থ হচ্ছে, কোনো মাসয়ালার উপর উম্মতের সমস্ত আলেমের একমত হয়ে যাওয়া। আর যখন কোনো মাসয়ালার উপর গোটা উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন কোনো ব্যক্তির তা থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার থাকেনা। কেননা গোটা উম্মত কখনো গোমরাহীর উপর একমত হতে পারেনা। কিন্তু এমন অনেক মাসয়ালাও রয়েছে, যে সম্পর্কে কোনো কোনো লোকের ধারণা হচ্ছে যে, তার উপর ইজমা হয়েছে। কিন্তু মূলত তা হয়নি বরং কখনো কখনো ভিন্নমত অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।” [ফতোয়া ইবনে তাইমিয়া, ১ম খন্ড, পৃঃ ৪০৬]
উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, কোনো মাসয়ালার ক্ষেত্রে শরীয়াতের নসের কোনো ব্যাখ্যার উপর, অথবা কোনো কিয়াস বা ইস্তিম্বাতের উপর, অথবা কোনো মাসালিহে মুরসালার উপর আজো যদি প্রজ্ঞার অধিকারী ব্যাক্তিগণের ইজমা হয়ে যায়, অথবা অধিকাংশের ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা হুজ্জাতের মর্যাদা লাভ করবে এবং আইনে পরিণত হবে। যদি গোটা বিশ্বের মুসলিম মনীষীগন এই ধরনের মাসয়ালায় ঐক্যমত হয়ে যান, তাহলে সেটা গোটা দুনিয়ার জন্য আইনে পরিণত হবে। আর যদি কোনো একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞগণ ঐক্যমত হন, তাহলে অন্ততপক্ষে ঐ রাষ্ট্রের জন্য তা আইনে পরিণত হবে। [তরজমানুল কুরআন, শা’বান ১৩৭৪; মে ১৯৯৫]
৪. ইসলামী ব্যবস্থায় বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিক পন্থা
তাফহীমুল কুরআনের পাঠকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে নিজের একটি জটিলতার বর্ণনা করে লিখেছেনঃ
কুরআন মজীদের আয়াতঃ
“হে ঈমানদারগণ! আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো তাঁর রসূলের এবং তোমাদের মধ্যেকার কর্তৃত্বের অধিকারী লোকদের। অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোনো মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয়, তবে তা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে ফিরেয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ্ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক থেকেও এটাই উত্তম।” [সূরা নিসাঃ ৫৯]
এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আপনি তাফহীমুল কুরআনে লিখেছেন, “আলোচ্য আয়াতে যে কথা স্থায়ী এবং চূড়ান্ত মূলনীতির আকারে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা এই যে, ইসলামী ব্যবস্থায় আল্লাহর নির্দেশ এবং রসূলের তরীকা মৌলিক আইন এবং সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সনদের মর্যাদা রাখে। মুসলমানদের মাঝে অথবা সরকার ও জনগণের মাঝে যে বিষয়কে নিয়েই বিতর্ক সৃষ্টি হবে, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য কুরআন ও সুন্নাতের দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর এখানে যে ফায়সালা পাওয়া যাবে তার সামনে সবাই আত্মসমর্পণ করবে। এভাবে জীবনের যাবতীয় সমস্যার ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নাতকে সনদ, প্রত্যাবর্তনস্থল এবং সর্বশেষ কথা হিসেবে মেনে নেয়া ইসলামী সমাজের এমন একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে পৃথক করে দেয়। [তাফহীমুল কুরআন, ১ম খন্ড, সূরা নিসা, আয়াতঃ ৫৯।]
“আপনার এই ব্যাখ্যার মাধ্যমে একথা পরিষ্কারভাবে সামনে এসে যায় যে, যাবতীয় বিতর্কিত বিষয়ে সর্বশেষ এবং সিদ্ধান্তকারী জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ। এই প্রসংগে একটি জটিলতা হচ্ছে এই যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় এটাতো সম্পূর্ণই সম্ভব ছিলো যে, যখনই কোনো মতবৈষম্য দেখা দিয়েছে সাথে সাথে তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করা হয়েছে। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি আমাদের মাঝে বর্তমান নেই বরং শুধু তাঁর শিক্ষাই আমাদের সামনে উপস্থিত আছে, এ সময় যদি ইসলামের কোনো নির্দেশের ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে একটি ইসলামী ব্যবস্থায় কোন্ ব্যক্তি বা সংস্থা এই বিষয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার লাভ করবে যে, এ ব্যাপারে শরীয়াতের লক্ষ্য কি? আশা করি আপনি এ ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করে বাধিত করবেন।
জবাবঃ
বিরোধ দূরীকরণে কুরআনের তিনটি মৌলিক হিদায়াত
এই প্রশ্নে যে জটিলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা দূর করার জন্য কুরআন, সুন্নাহ্, সাহাবাদের যুগের কার্যাবলী একত্র হয়ে আমাদের সাহায্য করে। সর্বপ্রথম কুরআনকে দেখুন। তা এ ব্যাপারে তিনটি মৌলিক হিদায়াত দান করেঃ
প্রথম হিদায়াতঃ আহলে যিকিরের কাছে প্রত্যাবর্তন
“এই আহলুয যিকর-এর কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো, যদি তোমরা নিজেরা না জানো।” [সূরা নহলঃ ৪৩; আম্বিয়াঃ ৭]
এ আয়াতে “আহলুয যিকর” শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক। কুরআন মজীদের পরিভাষায় ‘যিকির’ শব্দটি বিশেষভাবে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল কোনো জাতিকে যে শিক্ষা দিয়েছেন, তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃহ হয়েছে। আর যে লোকদের এই শিক্ষা দেয়া হয় তাদের বলা হয় ‘আহলুয-যিকর’। এই শব্দের অর্থ কেবল জ্ঞান [Knowledge] মনে করা যেতে পারেনা। বরং এর অর্থ অপরিহার্যরূপে কিতাব ও সুন্নাতের জ্ঞানই হতে পারে। অতএব এই আয়াত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে যে, সমাজে প্রত্যাবর্তন স্থলের অধিকারী কেবল এমন লোকদের হওয়া উচিৎ, যারা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখেন এবং যে পথে চলার জন্য আল্লাহর রসূল শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্পর্কে যারা অবহিত।
দ্বিতীয় হিদায়াতঃ কর্তৃত্বসম্পন্ন লোকদের কাছে প্রত্যাবর্তন
“আর যখনই তাদের সামনে শান্তিপূর্ণ অথবা ভীতিপ্রদ কোনো ব্যাপার এসে যায়, তখন এটাকে সর্বত্র প্রচার করে দেয়। অথচ তারা যদি এটাকে রসূল এবং নিজেদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের পর্যন্ত পৌঁছে দিতো, তাহলে যেসব লোক এর সঠিক ফলাফল বের করতে সক্ষম তারা এটা জানার সুযোগ পেতো।” [সূরা নিসাঃ ৮৩]
এ থেকে জানা গেলো, সমাজ যেসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সম্মুখিন হবে- চাই তা শান্তিপূর্ণ অবস্থার সাথেই সম্পর্কিত হোক, অথবা যুদ্ধকালীন অবস্থার সাথে, ভয়ংকর ধরনের হোক অথবা সাধারণ প্রকৃতির- তাতে কেবল মুসলমানদের কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকেরাই হতে পারেন প্রত্যাবর্তনস্থাল, যাদের উপর সমাজের সামগ্রিক পরিচালনভার অর্পণ করা হয় এবং যারা ইস্তিম্বাত করার যোগ্যতা রাখেন। অর্থাৎ আগত সমস্যার প্রকৃতিও অনুধাবন করতে পারেন যে, এই ধরনের পরিস্থিতিতে কি করা উচিৎ। এই আয়াত সমষ্টিগত সমস্যা এবং সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে সাধারণ আহলে যিকিরদের পরিবর্তে কর্তৃত্বশীল লোকদের প্রত্যাবর্তনস্থল ঘোষণা করে। কিন্তু তাদেরকেও অবশ্যই আহলে যিকিরদের মধ্যেকার ব্যক্তিই হতে হবে। কেননা তাদের সামনে যে সমস্যা এসেছে তাতে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের দেয়া মৌখিক এবং কর্মগত হিদায়াতকে দৃষ্টির সামনে রেখে তারাই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।
তৃতীয় হিদায়াতঃ শূরা বা পরামর্শ পরিষদ গঠন
তারা নিজেদের যাবতীয় সামগ্রিক ব্যাপার পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। [সূরা শূরাঃ ৩৮]
এই আয়াত পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, মুসলমানদের সমষ্টিগত ব্যাপারসমূহের সর্বশেষ ফায়সালা কিভাবে হওয়া উচিৎ?
এই তিনটি মূলনীতিকে যদি একত্র করে দেখা যায় তাহলে সমস্ত বিতর্কিত বিষয়ে “ ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি”র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার বস্তাব পন্থা হচ্ছে এই যে, মানুষের জীবনে সাধারণত যেসব সমস্যা এসে থাকে তা তারা আহলুয যিকিরদের কাছে রুজু করবে এবং তারা তাদের বলে দেবেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের কি নির্দেশ রয়েছে। যেসব বিষয় রাষ্ট্র ও সমাজের দিক থেকে গুরুত্বের দাবীদার, তা কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোকদের (উলিল আমর) সামনে পেশ করতে হবে। তারা পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করার চেষ্টা করবেন যে, আল্লাহর কিতাব ও রসূলুল্লাহর সুন্নাতের আলোকে কোন্ জিনিস হক ও সত্যের অধিক কাছাকাছি?
নববী যুগে উল্লেখিত মূলনীতিসমূহের প্রতি গুরুত্ব আরোপে
এখন দেখা যাক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কল্যাণময় যুগে এবং তাঁর পরে খিলাফতে রাশেদার যুগের কার্যপ্রণালী কিরূপ ছিলো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবদ্দশায় যেসব বিষয় সরাসরি তাঁর কাছে পৌঁছতো, সেগুলোর ক্ষেত্রে আল্লাহ্ ও তারঁ রসূলের উদ্দেশ্য বর্ণনা এবং তদনুযায়ী বিতর্কিত বিষয়ে ফয়সালাকারী ছিলেন তিনি নিজিই। কিন্তু পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে, গোটা ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা জনবসতি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হতো তার সবই সরাসরি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পেশ করা হতোনা এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকে সিদ্ধান্ত অর্জন করা হতোনা। এর পরিবর্তে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে তাঁর পক্ষ থেকে শিক্ষকগণ নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। তারা লোকদের আল্লাহর দীনের শিক্ষা দান করতেন। সাধারণ লোকেরা নিজেদের দৈনন্দিন ব্যাপারসমূহের ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে জেনে নিতো যে, আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ কি এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন্ তরীকা শিখিয়েছেন। তাছাড়া প্রতিটি এলাকায় গভর্ণর, কার্যনির্বাহী অফিসার এবং বিচারক নিযুক্ত থাকতো। তারা নিজ নিজ কর্মপরিসরে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান পেশ করতো। এই লোকদের জন্য ‘ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি’র উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যে পন্থা পছন্দ করেছেন তা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিখ্যাত হাদীসে বর্ণিত হয়েছেঃ
“রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়ায ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে ইয়ামনের কাযী করে পাঠালেন কখন জিজ্ঞেস করলেনঃ তুমি কিভাবে ফায়সালা করবে? তিনি আরয করলেন, আল্লাহর কিতাবে যে হিদায়াত রয়েছে তদনুযায়ী। রসূলুল্লাহ বললেনঃ যদি আল্লাহর কিতাবে না পাওায়া যায়? তিনি আরয করলেন, তাহলে রসূলের সুন্নাহ্ অনুযায়ী। রসূলুল্লাহ বললেনঃ আল্লাহর রসূলের সুন্নাতেও যদি না পাওয়া যায়? তিনি আরয করলেন, আমি আমার রায়ের মাধ্যমে [সত্য পর্যন্ত পৌছার] পূর্ণ চেষ্টা করবো। এর উপর তিনি বললেনদঃ যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আল্লাহর রসূলের দূতকে এমন পন্থা অবলম্বন করার তৌফিক দিয়েছেন যা আল্লাহর রসূলের পছন্দনীয়।“ [তিরমিযীঃ আবওয়াবুল আহকাম, আবু দাউদঃ কিতাবুল আকদিয়া]
রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কল্যাণময় যুগে পরামর্শ পুরষদ [শূরা] ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং এমন প্রতিটি ব্যাপারে, যে সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি কোনো নির্দেশ পাননি- সমাজের রায় প্রদানের যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের সাথে পরামর্শ করতেন। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো, নামাযের ওয়াক্তসমূহে লোকদের একত্র করার জন্য কি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে, এ সম্পর্কে তিনি যে পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা করেছিলেন তা। আর এর ফলশ্রুতিতেই শেষ পর্যন্ত তিনি আযানের পন্থা নির্ধারণ করেন।
খিলাফতে রাশেদার যুগে উল্লেখিত মূলনীতির প্রতি গুরুত্বারোপ
রিসালাত যুগের পর খিলাফতে রাশেদার যুগেও প্রায় এই কর্মপন্থাই কার্যকর ছিলো। শুধু এতোটুকু পার্থক্য ছিলো যে, রিসালাত যুগে স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্তমান ছিলেন। এজন্য যাবতীয় বিষয়ের সর্বশেষ সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগতভাবে তাঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করা যেতো। পরবর্তীকালে তাঁর সত্তা আর প্রত্যাবর্তনস্থল [মারজা] রইলোনা বরং তাঁর রেখে যাওয়া ঐতিহ্য হয়ে গেলো প্রত্যাবর্তনস্থল, যা তাঁর সুন্নাতের আকারে লোকদের কাছে সংরক্ষিত ছিলো। এই যুগে ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এগুলো নিজ নিজ স্থান ও অবস্থানের দিক থেকে “ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রসূলি”র উদ্দেশ্য পূর্ণ করতোঃ
১. সাধারণ আলেম সমাজ, যারা কিতাবুল্লাহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফায়সালাসমূহ, অথবা তাঁর কর্মপন্থা, অথবা তাঁর অনুমোদন [অনুমোদন (তাকরীর) বলতে বুজায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে কোনো কাজ করা হয়েছিল এবং তিনি বহাল রেখেছেন।] সম্পর্কিত কোনো জ্ঞান বর্তমান ছিলো।
কেবল সাধারণ লোকেরাই তাদের জীবনের বিভিন্ন ব্যাপারে এদের কাছ থেকে ফতুয়া জানতেননা বরং খোলাফায়ে রাশেদীনেরও যখন কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এটা জানার প্রয়োজন দেখা দিতো যে, সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো নের্দেশ দিয়েছেন কিনা- তখন এই লোকদের কাছে রুজু করতেন। কখনো কখনো এরূপও হতো যে, সমসাময়িক খলীফা অজ্ঞতা বশত কোনো ব্যাপারে নিজের রায়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দিতেন, অতপর যখন জানা যেতো যে এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিন্নতর সিদ্ধান্ত বর্তমান রয়েছে, তখন তিনি নিজের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। এই আলেম সমাজের বর্তমান থাকাটা শুধু এতোটুকু উপকারীই ছিলোনা যে, ব্যক্তিগতভাবে তারা জনসাধারণ ও ক্ষমতাসীন লোকদের [উলিল আমর] জন্য ইলমের একটি মাধ্যমের কাজ দিতেন বরং এর চেয়েও বড় ফায়দা এই ছিলো যে, তারা সামগ্রিকভাবে সে কোনো আদালত, কোনো সরকার এবং কোনো মজলিশে শূরা যেনো আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাতের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত নিতে না পারে দায়িত্বও পালন করেন। তাদের সুদৃঢ় রায় সাধারণ ইসলামী ব্যবস্থার আশ্রয়াধীন ছিলো। প্রতিটি ভুল সিদ্ধান্তের সমালোচনার জন্য তাদের সজাগ সতর্ক থাকাটা ইসলামী ব্যবস্থার সঠিকভাবে চলার জন্য গ্যারান্টি ছিলো। কোনো বিষয়ে তাদের ঐক্যমত প্রমাণ করতো যে, এই বিশেষ ব্যাপারে দীনের রাস্তা সুনির্ধারিত এ থেকে বিচ্যুত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারেনা। আবার তাদের মতবিরোধের অর্থ এই ছিলো যে, এ ব্যাপারে দুই অথবা ততোধিক মত পোষণের সুযোগ রয়েছে, যদিও সিদ্ধান্ত একটির উপরই হয়েছে। তাদের বর্তমান থাকার কারণে উম্মতের মধ্যে সাধারণভাবে কোনো বিদায়াত চালু হওয়া অসম্ভব ছিলো। কেননা সর্বত্র দীনের জ্ঞানসম্পন্ন লোক এ ব্যাপারে পাকড়াও করার জন্য বর্তমান ছিলো।
২. কাযা অর্থাৎ বিচার বিভাগ। কাযী শূরাইর নামে লিখিত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর একটি নির্দেশনামায় এর ব্যাখ্যা বর্তমান রয়েছেঃ
“আল্লাহর কিতাবের নির্দেশ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। যদি আল্লাহর কিতাবে না থাকে, তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরা সুন্নাহ্ অনুযায়ী ফায়সালা করুন। যদি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সুন্নাতে না থাকে, তাহলে সালিহীনগণ যে ফায়সালা করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করুন। কিন্তু যদি কোনো ব্যাপারের নির্দেশ আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের সন্নাতে পাওয়া না যায় এবং সালিহীনদের ফায়সালার নজীরও না পাওয়া যায় তাহলে আপনার এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে আপনি সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, অথবা অপেক্ষাও করতে পারেন। তবে আমার মতে অপেক্ষা করাটাই আপনার জন্য অধিক কল্যাণকর।”[অপেক্ষা করার দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে। এক, অন্য কোনো আদালত অনুরূপ কোনো ব্যাপারে সামনে অগ্রসর হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত স্থাপন করে কিনা। দুই, বিচারক নিজে ফয়সালা করার পরিবর্তে বিষয়টি পূর্বোল্লেখিত তৃতীয় সংস্থার কাছে রুজু করবে।] [নাসায়ী, কিতাবুল আদাবিল কুদাত]
এই পন্থাকে হযরত আব্দুল্লাহ মাসউদ রাদয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিম্নোক্ত ভাষায় ব্যক্ত করেছেনঃ
“এমন এক যামানা অতীত হয়েছে যখন আমরা ফায়সালা করতামনা এবং ফায়সালা করার মর্যাদাও আমাদের ছিলোনা। [অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ]। এখন তাকদীরে ইলাহীর কারণে আমরা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছো। অতএব এখন তোমাদের সামনে ফায়সালার জন্য কোনো বিষয় উত্থাপিত হলে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফায়সালা করবে। যদি এমন কোনো বিষয় এসে যায় যার হুকুম আল্লাহর কিতাবে বর্তমান নেই, তাহলে এর ফায়সালা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও অনুরূপ বিষয়ের ফায়সালা করেননি তাহলে সালিহীনগণ যে ফায়সালা করেছেন তদনুযায়ী ফায়সালা করবে। যদি এমন কোনো বিষয় সামনে এসে যায় যার হুকুম আল্লাহর কিতাবেও বর্তমান নেই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেন নাই এবং সালিহীনদের থেকেও অনুরূপ বিষয়ের সিদ্ধান্ত বর্তমান নেই, তাহলে সে বিষয়ে ইজতিহাদের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার পূর্ণ চেষ্টা করবে। কিন্তু একথা বলবেনা, আমি ভয় করছি, আমি ভয় পাচ্ছি। কেননা হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট। আর এ দু’টি জিনিসের ক্ষেত্রে এমন ফায়নসালা করতে হবে যা ব্যক্তির মনকে দোদুল্যমান না করতে পারে। আর দোদুল্যমান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে ব্যক্তিকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।” [নাসায়ী, কিতাবুল আদাবিল কুদাত]
এই বিচার বিভাগ কেবল জনসাধারণের পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসা করারই অধিকারী ছিলোনা বরং তা সরকারী প্রাশাসনের [Executive] বিরুদ্ধেও জনগণের অভিযোগ শ্রবণ করতো এবং তা ফায়সালা দান করতো। এই আদালতের সামনে হাযির হওয়ার ব্যাপারে কোনো গভর্নরও আইনের উর্ধ্বে ছিলোনা এবং সমসাময়িক খলীফা এবং সরকারকেও। যদি কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিগত বা সরকারী অভিযোগ থাকতো তাহলে আদালতের সাহায্য নিতে হতো এবং আদালতই সিদ্ধান্ত করতো যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের বিধানের আলোকে এর সঠিক ফায়সালা কি হতে পারে।
৩. উলিল আমর, অর্থাৎ খলীফা এবং তাঁর মজলিসে শূরা। এটা সর্বশেষ কর্তৃত্বশালী সংস্থা যা কুরআনের হিদায়াত অনুযায়ী পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতো যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, সেসব ব্যাপারে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাতে কি হুকুম প্রমাণিত রয়েছে? যদি কোনো ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাতের ফায়সালা বর্তমান না থাকে তাহলে এ ব্যাপারে কোন্ ধরনের কর্মপন্থা দীনের মূলনীতি ও তার প্রাণসত্তা এবং মুসলিম সমাজের সার্বিক স্বার্থের দিক থেকে সত্যের অধিকতর কাছাকাছি? এই সংস্থার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত হাদীস এবং ফিকহের গ্রন্থসমূহে নির্ভরযোগ্য মাধ্যমে সংকলিত হয়েছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফায়সালা গ্রহণ করাকালীন সময়ে শূরার বৈঠকে সাহাবাদের মধ্যে যে আলোচনা পর্যালোচনা হয়েছিলো তাও সংকলিত হয়েছে। তার মূল্যায়ন করলে জানা যায়, এই সংস্থা পূর্ণ কঠোরতার সাথে যে মূলনীতির অনুসরণ করতো তা ছিলো এই যে, প্রতিটি বিষয়ে সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালার কিতাবের দিকে রুজু করতে হবে। অতপর জানতে হবে যে, এই ধরনের কোনো বিষয় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগে উদ্ভূত হলে তিনি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অতপর যদি এ দুটি উৎস থেকে কোনো পথনির্দেশ না পাওয়া যায় তাহলে কেবল তখনই নিজের নির্ভুল চিন্তার সাহায্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যে কোনো ব্যাপারেই আল্লাহর কিতাবের কোনো আয়াত অথবা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ থেকে কোনো নযীর পাওয়া গেলে তারা তা থেকে সরে গিয়ে ভিন্নতর কোনো ফায়সালা করতেননা। সাহাবাদের গোটা যুগে এই মূলনীতি বিরোধী একটি দৃষ্টান্তও পাওয়া যাবেনা। যদিও রাষ্ট্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার এখতিয়ার কার্যত উলিল আমরের হাতেই ছিলো, কিন্তু আইনত কুরআন এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ্ সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী সনদ হিসেবে স্বীকৃত ছিলো। মুসলিম সমাজও এই ভরসার ভিত্তিতে তাদের কর্তৃত্বের আনুগত্য করতো যে, তারা নিজেদের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কুরআন ও সুন্নাতের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যাবেনা। তাদের কারো মন মগজে এই ধারণা পর্যন্ত ছিলোনা যে, তারা কুরআনের অকাট্য প্রমাণের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন অথবা নির্দেশ দেয়ার অধিকারী। অনুরূপভাবে তাদের কারো মনে এরূপ দূরতম ধারণাও ছিলোনা যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর যুগের নির্দেশদাতা ছিলেন এবং আমরা আমাদের যুগের নির্দেশদাতা এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর শাসনকালে যে ফায়সালা দিয়েছেন তার নযীর অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য নই। তাঁর ইন্তিকালের পর যেদিন খিলাফত নামক সংস্থা অস্তিত্ব লাভ করলো, সেদিনই প্রথম খলীফা তাঁর ভাষণে ঘোষণা করলেনঃ “আমি যতক্ষণ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবো তোমরা ততক্ষণ আমার আনুগত্য করবে। আমি যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হই তাহলে আমার আনুগত্য করা তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়।”
উপরোক্ত ঘোষণা থেকে পরিষ্কার জানা যায়, খিলাফতের সংস্থা কেবল এই উদ্দেশ্যেই কায়েম হয়েছিলো যে, খলীফা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবেন এবং উম্মাত খলীফার আনুগত্য করবে। অন্য কথায় জনগণের জন্য খলীফার আনুগত্য ছিলো শর্তসাপেক্ষ আর তা হচ্ছে তিনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশের আনুগত্য করবেন। এই শর্ত বিলীয়মান হয়ে গেলেই উম্মতের উপর থেকে খলীফার আনুগত্য করার কর্তব্য আপনা আপনি রহিত হয়ে যায়।
বিতর্কের সমাধানে সাধারণ জ্ঞানের দাবী
অতপর সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে সামান্য চেষ্টা করে দেখুন, কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি এবং তার দাবী কার্যত কিভাবে পূর্ণ হতে পারে। এই আয়াতে গোটা মুসলিম সমাজকে সম্বোধন করে তাকে ক্রমিক পর্যায়ে তিনটি জিনিসের আনুগত্য করতে বাধ্য করে। প্রথমে আল্লাহর আনুগত্য, অতপর তাঁর রসূলের আনুগত্য এবং সমাজের মধ্য থেকে নির্বাচিত উলিল আমরের আনুগত্য। বিতর্কিত বিষয়ের ক্ষেত্রে এই আয়াতের নির্দেশ হচ্ছে, এর ফায়সালার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু করো। এ থেকে আয়াতের যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রকাশ পায় তা হচ্ছে- আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা সমাজের জন্য বাধ্যতামূলক। আর উলিল আমরের আনুগত্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের অধীন। মতবিরোধ কেবল জনসাধারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। জনসাধারণ এবং উলিল আমরের মধ্যেও মতবিরোধ হতে পারে। মতবিরোধের যাবতীয় ক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্তকারী কর্তৃপক্ষ উলিল আমর নয় বরং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল। তাঁদের যে নির্দেশ পাওয়া যাবে তার সামনে জনসাধারণকেও এবং উলিল আমরেকেও মাথা নতো করতে হবে।
এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, ফায়সালার জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে রুজু করার তাৎপর্য কি? একথা পরিষ্কার যে, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ স্বয়ং সামনে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁর সামনে মুকদ্দমা পেশ করে সিদ্ধান্ত হাসিল করা হবে, বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন করে জানতে হবে বিতর্কিত বিষয়ে তাঁর নির্দেশ কি? অনুরূপভাবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দিকে প্রত্যাবর্তন করার তাৎপর্যও এই হতে পারেনা যে, রসূলের সত্ত্বার কাছ থেকে সরাসরি সিদ্ধান্ত লাভ করতে হবে। কিন্তু নিঃসন্দেহে এর অর্থ হচ্ছে এই যে, রসূলের শিক্ষা এবং তাঁর কথা ও কাজ থেকে পথনির্দেশ লাভ করতে হবে। এটাতো স্বয়ং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ও সম্ভব ছিলোনা যে, এডেন থেকে তাবুক পর্যন্ত এবং বাহরাইন থেকে জিদ্দা পর্যন্ত গোটা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক নিজের প্রতিটি ব্যাপারের সিদ্ধান্ত সরাসরি তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করবে। এ যুগেও রসূলের সুন্নাহই নির্দেশের উৎস।
অতপর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, মতবিরোধের ক্ষেত্রে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ্ থেকে ফায়সালা হাসিল করার পন্থা কি হতে পারে? পরিষ্কার কথা হচ্ছে এই সিদ্ধান্ত মানুষই দেবে, কিতাব ও সুন্নাহ্ নিজে তো আর বলবেনা। কিন্তু অবশ্যই তাকে কিতাব ও সুন্নাতের নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আর কিতাব ও সুন্নাতের ভিত্তিতে ফায়সালাকারী অবশ্যই মতভেদে লিপ্ত পক্ষদ্বয় হতে পারেনা, তাদের ছাড়া এমন কোনো তৃতীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তি বা সংস্থা হতে হবে, যে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। কোন্ ধরনের মতবিরোধের ক্ষেত্রে ফায়সালা দেয়ার জন্য কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত হবে- তা বিতর্কের ধরন ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করবে। এক ধরনের মতবিরোধ এমন রয়েছে যার মীমাংসা যে কোনো জ্ঞানবান ব্যক্তি করতে পারে। অন্য এক ধরনের বিবাদের ক্ষেত্রে অবশ্যই আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার প্রয়োজন হবে। আবার কতিপয় বিবাদের ধরন এমনও হতে পারে যার চূড়ান্ত ফায়সালা উলিল আমর ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেই ফায়সালার উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ্।
এই সেকথা যা সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে আয়াতের শব্দগুলোর উপর চিন্তা করে প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুধাবন করতে পারে। তবে শর্ত হচ্ছে তার মন মগজে কোনোরূপ বক্রতা থাকবেনা। এখন এটাও এক নযর দেখা যাক যে, এই আয়াতের পেশকৃত ব্যবস্থা এবং তার কার্যকর পন্থা অনুধাবন করার ক্ষেত্রে দুনিয়ার প্রসিদ্ধ পন্থা আমাদের কি সাহায্য করে। দুনিয়াতে আজ আইনের শাসনের [Rule of Law] খুব চর্চা চলছে এবং বলা হচ্ছে যে, দুনিয়াতে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনের সার্বভৌমত্ব একান্ত অপরিহার্য। এর সামনে বড় ছোট সবাই সমান বিবেচিত হবে এবং জনসাধারণ, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও স্বয়ং সরকারের উপর নিরপেক্ষ পন্থায় কার্যকর হবে। একটি সংসদেরই এই আইন প্রণয়ন করা উচিৎ। কিন্তু যখন তা আইনে পরিণত হয়ে যাবে তখন এটা বলবৎ থাকা পর্যন্ত স্বয়ং সংসদকেও তার অনুসরণ করতে হবে। আইনের সার্বভৌমত্বের এই মতবাদকে যেখানেই বাস্তবরূপ দান করা হয়েছে, সেখানেই চারটি জিনিসের উপস্থিতি অপরিহার্য মনে করা হয়েছেঃ
১. এমন একটি সমাজ যা আইনের প্রতি হবে শ্রদ্ধাশীল এবং তার আনুগত্য করার প্রকৃতই ইচ্ছা রাখে।
২. সমাজে এমন অনেক লোক থাকতে হবে যারা আইন সম্পর্কে অবগত, যারা জনগণকে আইনের অনুসরণের ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে। এবং তাদের সামগ্রিক জ্ঞান ও প্রভাবের দরুন সমাজও আইনের পথ থেকে বিচ্যুত হতে পারবেনা এবং সরকারী কর্তৃপক্ষও আইনকে উপেক্ষা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারবেনা।
৩. একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ থাকবে, যা জনসাধারণ, সরকারী কর্তৃপক্ষ ও সরকারের মধ্যেকার বিবাদে আইন অনুযায়ী সঠিক সিদ্ধান্ত দান করবে।
৪. একটি অতীব শক্তিশালী সংস্থা থাকবে, যা সমাজে উদ্ভূত যাবতীয় সমস্যার সর্বশেষ সমাধান পেশ করবে এবং তা আইন হিসেবে সমাজে কর্যকর হবে।
এসব বিষয় সামনে রেখে যখন আপনি চিন্তা করবেন তখন জানতে পারবেন, কুরআন মজীদের আলোচ্য আয়াত মূলত ইসলামী সমাজে আইনের শাসন কায়েম করে এবং তাকে কার্যকর করার জন্য উল্লেখিত চারটি জিনিসের প্রয়োজন। যদি কোনো পার্থক্য থেকে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই যে, কুরআন যে আইনের শাসন কায়েম করে সে মূলতই তার অধিকারী আর দুনিয়াতে যে আইনের সার্বভৌমত্ব কায়েম করা হচ্ছে তা তার অধিকারী নয়। কুরআন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আইনকে সার্বভৌম আইন হিসেবে স্বীকৃতি দেয় যার সামনে সবাইকে মাথা নতো করে দিতে হবে এবং যার অধীন হওয়ার ক্ষেত্রে সবাই সমান। তা এমন একটি সমাজকে সম্বোধন করে যা এই আইনের উপর ঈমান রাখে এবং নিজেদের বিবেকের দাবীতে তার আনুগত্য করে। এর উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে- সমাজে আহলুয যিকরের এক ব্যাপক সংখ্যক লোক বর্তমান থাকবে, যাদের সাহায্যে সমাজের সদস্যগণ নিজেদের জীবনের ব্যাপারসমূহে প্রতিটি স্থানে প্রতিটি মুহূর্তে এই সার্বভৌম আইন থেকে পথ নির্দেশ লাভ করতে থাকবে এবং যাদের মাধ্যমে জনমত এই ব্যবস্থার হিফাজতের জন্য সব সময় সজাগ থাকবে। এর আরো দাবী হচ্ছে এই যে, একটি বিচার ব্যবস্থা বর্তমান থাকতে হবে, যা শুধু জনসাধারণের মধ্যেই নয় বরং জনসাধারণ এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের মাঝেও এই সার্বভৌম আইন মুতাবিক ফায়সালা করবে। তা উলিল আমরের এমন একটি সংস্থারও দাবী করে, যে নিজেও এই সার্বভৌম আইনের অধীন হবে এবং সমাজের সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং এর অধীনে ইজতিহাদ করার সর্বশেষ এখতিয়ারও ব্যবহার করবে। [তরজমানুল কুরআন, রজব ১৩৭৭, এপ্রিল ১৯৫৮০]
একাদশ অধ্যায়
কতিপয় সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক বিষয়
১. ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি দিক
২. খিলাফাত ও স্বৈরতন্ত্র
৩. জাতীয় রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ
৪.অমুসলিমদের অধিকার
৫. আরো কয়েকটি বিষয়
মাওলানা মওদূদী দেশে সাংবিধানিক বিতর্ক চলাকালে সৃষ্ট বিভিন্ন সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক (তাত্ত্বিক) বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে বক্তব্য রেখেছেন। কতক বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন লাহোরের দাংগা সংক্রান্ত তদন্ত আদালতে দেয়া জবানবন্দীতে, কতক বিষয়ের ব্যাখ্যা দিয়েছেন পত্রপত্রিকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে ও সভাসমিতিতে প্রদত্ত বক্তৃতায়। আবার কতক বিষয়ের জট খুলে দিয়েছেন লিখিত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। এ জাতীয় সক্তব্যের সংখ্যা যদিও প্রচুর, তবে আমরা এ সবের মধ্য থেকে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বাছাই করে এখানে পেশ করছি। -সংকলক
১. ইসলামী রাষ্ট্রের কয়েকটি দিক
ক. ধর্মেহীন গণতন্ত্র, ধর্মীয় রাষ্ট্রে ও ইসলামী রাষ্ট্র
যে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ আমাদের লক্ষ্য, তা পাশ্চাত্য পরিভাষা অনুযায়ী কোনো ধর্মীয় রাষ্ট্রও [Theocracy] নয়, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও নয়, বরং তা হচ্ছে এই উভয় ব্যবস্থার মধ্যবর্তী এক পৃথক ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা। আজকাল পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের মনে “ইসলামী রাষ্ট্র” সংক্রান্ত ধারণাকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব ও জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে, মূলত সংশ্লিষ্ট পাশ্চাত্য পরিভাষাগুলোর ব্যবহার থেকেই এর উৎপত্তি। পাশ্চাত্যের এই পরিভাষাগুলো স্বাভাবতই এবং অনির্বার্যভাবেই পাশ্চাত্যের ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারা, এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসের একটা ধারবাহিক রূপও পাঠকের মানসপটে তুলে ধরে। পাশ্চাত্য পরিভাষায় ধর্মীয় রাষ্ট্র তথা [Theocracy] দুটো মৌলিক ধারণার সমষ্টিঃ
১. আল্লাহর রাজত্ব, তবে সেটা আইনগত সার্বভৌমত্ব [Legal Sovereignty] অর্থে।
২. পাদ্রী ও ধর্মযাজকদের একটা গোষ্ঠী, যারা আল্লাহর প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হয়ে আল্লাহর এই রাজত্বকে আইনগত ও রাজনৈতিকভাবে কার্যকর করে।
উল্লিখিত দুটো ধারণার ওপর তৃতীয় একটা বাস্তব ব্যাপারও সংযুক্ত হয়েছে।সেটি এই যে, হযরত ঈসা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইঞ্জীলের নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোনো আইনগত নির্দেশাবলী রেখে না যাওয়ার কারণে সেন্টপল শরীয়াতকে অভিশাপ আখ্যায়িত করে খৃষ্টানজগতকে তাওরাতের নির্দেশাবলী থেকে অব্যাহতি দেন। এরপর ইবাদত, সামাজিক আচার আচরণ, লেনদেন ও রাজনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে খৃষ্টানদের যখন বিভিন্ন আইন ও বিধির প্রয়োজন দেখা দিলো, তখন তাদের ধর্মযাজকরা মনগড়া আইন দিয়ে সেই প্রয়োজন পূরণ করলো। আর সেসব আইনকে আল্লাহর আইন বলে চালিয়ে দিলো। ইসলামে এই ধর্মীয় রাষ্ট্রের কেবল একটা অংশ স্থান পেয়েছে। সে অংশটি হলো আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আকীদা, এর দ্বিতীয় অংশটি [অর্থাৎ ধর্মযাজকদের শাসন] ইসলামে আদৌ গৃহীত হয়নি। তৃতীয় অংশটির স্থলে ইসলামে কুরআন স্বীয় সর্বব্যাপী ও বিস্তৃত বিধিবিধানসহ বিদ্যমান। আর তার ব্যাখ্যার জন্য রয়েছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কর্মকান্ডের বিবরণ সম্বলিত হাদীস। এসব হাদীসের শুদ্ধাশুদ্ধি যাচাই করার নির্ভরযোগ্য উপায় উপকরণও আমাদের হাতে রয়েছে। এ দুটি উৎস থেকে আমরা যা কিছু পাই, সেটাই আমাদের আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বিধান। এছাড়া কোনো ফকীহ, ইমাম, ওলী বা আলেমের এ মর্যাদা নেই যে, তার কথা ও কাজকে আল্লাহর হুকুমের মতো নির্বিবাদে মেনে নেয়া যেতে পারে। এই সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে ইসলামী রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্যের পরিভাষা অনুসারে ধর্মীয় রাষ্ট্র [Theocracy] বলা সম্পূর্ণ ভুল।
অপরদিকে পাশ্চাত্যে যে জিনিসকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র [Democracy] বলা হয়। তাও দুটো মৌলিক ধারণার সমন্বিত রূপ। যথাঃ
১. জনগণের আইনগত ও রাজনৈতিক সার্বভৌত্ব, যা কার্যকরী হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে।
২. রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার জনগণের অবাধ ও স্বাধীন ইচ্ছা বলে গঠিত ও পরিবর্তিত হতে পারবে।
ইসলাম এর কেবল দ্বিতীয় অংশকে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ করে। আর প্রথমাংশকে দুইভাগে বিভক্ত করে। আইনগত সার্বভৌমত্বকে সে শুধু আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে। এজন্য কুরআন অথবা হাদীসের মাধ্যমে প্রাপ্ত আল্লাহর আইন ও বিধান রাষ্ট্রের জন্য অকাট্য ও অপরিবর্তনীয় আইনের মর্যাদা রাখে। আর রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে “সার্বভৌমত্বের” পরিবর্তে খিলাফত [অর্থাৎ প্রকৃত শাসক আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব] নামে আখ্যায়িত করে রাষ্ট্রের সাধারণ মুসলিম অধিবাসীদের কাছে সমর্পণ করে। এই খিলাফত মুসলিম জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা তাদের আস্থা সম্পন্ন প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে। এই মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান থাকতে ইসলামী রাষ্ট্রকে পাশ্চাত্য পরিভাষা অনুসারে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র [Democracy] বলাও সঠিক নয়।
খ. ইসলামে আইন প্রণয়ন
উপরোক্ত বিশ্লেষণের আলোকে একথা আপনা থেকেই স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, ইসলাম যে ধরনের রাষ্ট্র গঠন করে তাতে একটা আইনসভা [Legislature] থাকা জরুরী। এ আইনসভা মুসলিম জনগণের আস্থা সম্পন্ন প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হবে এবং তার সর্বসম্মত রায় অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের রায় ইসলামী রাষ্ট্রে আইনরূপে চালু হবে। এই আইনসভার গঠন, তার কার্যপরিচালনা বিধি এবং তার সদস্যদের নির্বাচন পদ্ধতি ইসলামে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি। প্রত্যেক যুগের পরিস্থিতি পরিবেশ ও প্রয়োজনের দাবী অনুসারে এর আলাদা আলাদা ধরণ ও রূপ অবলম্বন করা যেতে পারে। কিন্তু নীতিগতভাবে যে বিষয়গুলো স্থির করে দেয়া হয়েছে, তা হচ্ছেঃ
১. রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মকান্ড পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে।
২. সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতি অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মতিক্রমে গৃহীত হবে।
৩. কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো সিদ্ধান্ত সর্বসমম্মতভাবেও গ্রহণ করা যাবেনা।
৪. কুরআন ও সুন্নাতের বিধির যে ব্যাখ্যা সর্বসম্মতভাবে অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় মুতাবিক গৃহীত হবে, তা রাষ্টীয় আইনে পরিণত হবে।
৫. যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো নির্দেশ থাকেনা। সেসব ব্যাপারে মুসলিম জনপ্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করতে পারেন এবং তাদের সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে।
৬. নাগরিকদের মধ্যে, সরকার ও জনগণের মধ্যে, আইনসভা ও জনগণের মধ্যে অথবা সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা অংশের মধ্যে যে কোনো বিবাদ বিসম্বাদ ঘটুক, তার নিস্পত্তি যাতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে করা যায়, সেজন্য একটা যুৎসই ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হবে।
গ. ইসলামী রাষ্ট্র কেনো?
পাকিস্তানকে এ ধরনের একটা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার সপক্ষে আমাদের দাবীর একাধিক যুক্তিসংগত কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে তিনটিঃ
প্রথমঃ এটি আমাদের ঈমানের ঐকান্তিক দাবী। স্বাধীনতা ও সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পরও এবং কুরআন ও রসূলের বাণীর সত্যতায় বিশ্বাসী হয়েও যদি আমরা কুরআন ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশাবলী কার্যকর করতে না পারি, তাহলে আমরা আমাদের ঈমানে কখনো নিষ্ঠাবান ও আন্তরিক হতে পারিনা।
দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবী করাই হয়েছিলো এজন্য যে, এখানে আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করা হবে। আর এই আকাংখ্যার পেছনেই লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর নারী নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত বিসর্জন দিয়েছিলো। তৃতীয়তঃ পাকিস্তানের অধিবাসীদের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ চায় যে, তাদের জাতীয় রাষ্ট্র একটা ইসলামী রাষ্ট্র হোক এবং সংখ্যাগুরুর এই দাবীর বাস্তবায়ন সর্বাসস্থায় কাম্য। একথা সত্য যে, এখানে মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক এমন রয়েছে যারা পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং তার মতবাদগুলোকে সঠিক মনে করে এবং তাদের পক্ষে ইসলামী রাষ্ট্রের ধারণা মেনে নেয়া দুষ্কর। তাছাড়া পাকিস্তানের আমলা শ্রেণীতেও এমন কিছু লোক বিদ্যমান, যাদের সমস্ত তাত্ত্বিক, মানসিক ও বাস্তব প্রশিক্ষণ পাশ্চাত্য ধাঁচের রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন দেখে তাদের মনে নানা ধরনের ভীতি ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু যে জিনিস অনিবার্য ও অবধারিত, তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করাই সমীচীন, যেমন ইতিপূর্বে তাদের পূর্ব পুরুষেরা ইংরেজ শাসন সমাগত দেখে নিজেদেরকে নবযুগের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। তাদের অধিকাংশ নিজেদেরকে গণতন্ত্রের একনিষ্ঠ সেবক রূপে জাহির করে থাকেন। এখন এটা তাদেরই ভেবে দেখা উচিত যে, মুষ্টিমেয় কিছু লোক বা- পরিবারের সুবিধার খাতিরে দেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যা চায়, তার পথরোধ করা কতোখানি সঠিক এবং কোথাকার গণতন্ত্র?
ঘ. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের মর্যাদা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সেগুলোর জবাব ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ
ক. ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী পরিভাষায় “যিম্মী” তথা “সংরক্ষিত নাগরিক” বলা হয়। “যিম্মী” কোনো গালি নয়। এটা শুদ্র বা ম্লেচ্ছের সমার্থকও নয়। আরবী ভাষার ‘যিম্মা’ শব্দটা [Guarantee] বা নিশ্চয়তার সমার্থক। যিম্মী সে ব্যক্তিকে বলা হয় যার অধিকার প্রদান ও সংরক্ষণের দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। ইসলামী সরকার এ দায়িত্ব শুধু নিজের পক্ষ থেকে বা মুসলিম অধিবাসীদের পক্ষ থেকে নয় বরং আল্লাহ্ ও রসূলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করে। এ দায়িত্বের গুরুত্ব এতো বেশী যে, কোনো অমুসলিম দেশে যদি মুসলমানদেরকে পাইকারী হারে হত্যা করেও ফেলা হয়, তথাপি আমরা আমাদের দেশে অবস্থানরত ঐ দেশের অধিবাসীদের সমধর্মাবলম্বী যিম্মীদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারিনা। একটি ইসলামী রাষ্ট্রের আইনসভা তাদের শরীয়াত সম্মত অধিকারসমূহ ছিনিয়ে নেয়ার আদৌ কোনো অধিকার রাখেনা।
খ. যিম্মীরা তিন শ্রেণীরঃ এক যারা কোনো চুক্তির মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছে। দুই, যারা যুদ্ধে বিজিত হয়েছে। তিন, যারা বিজিতও নয়, চুক্তিবদ্ধও নয়। প্রথম শ্রেণীর যিম্মীদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আচরণ করা হবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যিম্মীদের শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত অধিকার প্রদান করা হবে। আর তৃতীয় শ্রেণীর যিম্মীদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকার তো দেয়াই যাবে, উপরন্ত ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী নয় এবং আমাদের পরিস্থিতির আলোকে সমীচীন হয় এমন কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধাও আমরা তাদেরকে দিতে পারি।
গ. যিম্মীদের [অমুসলিম প্রজাদের] যে ন্যূনতম অধিকার শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তা নিম্নরূপঃ পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি, ধর্মীয় বই পুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশনার অনুমতি, আইনের আওতায় ধর্মীয় আলোচনার অনুমতি, উপাসনালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, পারিবারিক আইনের রক্ষণাবেক্ষণ, জানমাল ও ইজ্জতের হিফাজত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনে মুসলমানদের সাথে পুরোপুরি সমতা, সরকারের সাধারণ কর্মকান্ডে মুসলিম ও অমুসলিম নাগরিকদের মধ্যে বৈষম্যহীনতা, অর্থনৈতিক কায়কারবারের সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের মতো সমান সুযোগ দান। অভাবী হলে মুসলমানের ন্যায় যিম্মীদেরও রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে সাহায্য লাভের সমান অধিকার। এসব অধিকার ইসলামী রাষ্ট্র শুধু কাগজে কলমেই দেয়না বরং সে আপন দীন ও ঈমানের আলোকে কার্যত তা বাস্তবায়ন করতে বাধ্য। এক্ষেত্রে আদৌ একথা বিবেচনায় আনা হবেনা যে, অমুসলিম রাষ্ট্রগুলো মুসলমানদের সাথে কাগজে কলমেই বা কি কি অধিকার দিচ্ছে, আর বাস্তবেই বা কি দিচ্ছে।
ঘ. অমুসলিমদেরকে শহর এলাকা ছাড়া আর কোথাও উপাসনালয় বানাতে নিষেধ করা হয়েনি, তবে শহর এলাকায় অবস্থিত পুরানো উপাসনালয়গুলোর মেরামত করা যাবে। এখানে শহর এলাকা বলতে মুসলমানরা শুধুমাত্র নিজেদের বসবাসের জন্য যেসব শহর নির্মাণ করেছে, সেগুলোকে বুঝানো হয়েছে। যেমন কুফা, বসরা ও ফিসতাত। অন্যান্য শহরে নতুন উপাসনালয় নির্মাণ ও পুরানো উপাসনালয় মেরামতের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে।
ঙ. কিছু কিছু ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থে অমুসলিমদের ওপর পোশাক ইত্যাদির ব্যাপারে যেসব কড়াকড়ি ও বিধিনিষেধের উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা ভুলবুঝাবুঝির শিকার হওয়া উচিত নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের ফকীহগণ পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের তাগিদে যে তিন ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করেছিলেন তা হচ্ছেঃ
১. তাদেরকে সামরিক পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছিলো। মুসলমানদের নিষেধ করা হয়নি। কেননা সে সময় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের ওপর সামরিক চাকুরী করা বাধ্যতামূলক ছিলো। অমুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিলোনা।
২. মুসকলমানদেরকে অমুসলমানদের এবং অমুসলমানদেরকে মুসলমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক পরতে নিষেধ করা হয়েছিলো। কেননা এধরনের সাদৃশ্য দ্বারা নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। এতে আশংকা আছে যে, রকমারি কৃষ্টির মিশ্রণে একটা জগাখিচুড়ি কৃষ্টি তৈরী হয়ে যেতে পারে। এমন আশংকাও আছে যে, মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ে হতোদ্যম হয়ে অমুসলিমদের ভেতরে দাসসুলভ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়ে যাবে। এধরনের দাসসুলভ মানসিকতার কারণে পরাজিত জাতি পোশাক পরিচ্ছদ ও চালচলনে বিজয়ী জাতির অনুকরণ করতে থাকে। ইসলাম এধরনের মানসিকতা কোনো কাফিরের মধ্যেও সৃষ্টি হোক তা দেখতে চায়না। এজন্য অমুসলিমদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা নিজেদের কৃষ্টি সংস্কৃতি, চালচলন, বেশভূষা ও নিজেদের ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো যেনো সংরক্ষণ করে এবং মুসলমানদের অনুকরণ না করে। হানাফী ফিকাহর বিখ্যাত গ্রন্থ “বাদায়েউস্ সানায়ে” তে এ নির্দেশটি এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ
অমুসলিমদের এমন আলামত ও নিদর্শন বহাল রাখতে বাধ্য করা হবে, যা দ্বারা তাদের চেনা যায়। তাদেরকে পোশাক পরিচ্ছদে মুসরমানদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হতে দেয়া হবেনা।[৭ম খন্ড, ১১৩ পৃঃ]
এছাড়া এতে আইনগত জটিলতা সৃষ্টির আশংকাও আছে। উদাহরণ স্বরূপ, মুসলমানদের জন্য মদ খাওয়া, রাখা ও বিক্রয় করা ফৌজদারী অপরাধ। অথচ অমুসলিমদের জন্য সেটা অপরাধ নয়। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান যদি অমুসলিমদের সদৃশ পোশাক পরে, তবে সে এ জাতীয় অপরাধ করেও পুলিশের ধর পাকড় থেকে রেহাই পেতে পারে। আর কোনো অমুসলিম মুসলমানদের সদৃশ্য পোশাক পরলে সে পুলিশের ধর পাকড়ের শিকার হতে পারে।
৩. আরেক ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিলো তৎকালীন বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে। সে সময় সিন্ধু থেকৈ স্পেন পর্যন্ত বহুসংখ্যক দেশ মুসলমানদে দ্বারা বিজিত হয়েছিলো। আর স্বাভাবিকভাবেই ঐসব দেশের অধিবাসীদের মধ্যে সাবেক শাসক গোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যক লোক বিদ্যমান ছিলো। তাদের ভেতরে নিজেদের হারানো ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের উচ্চাভিলাষ তখনো ছিলো। মুসলমনিরা দুনিয়ার অন্যান্য বিজেতাদের ন্যায় এসব জনগোষ্ঠীকে কচুকাটা তো করেইনি বরং ‘যিম্মী’ বানিয়ে তাদেরকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ করেছিলো। কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাদেরকে কিছু না কিছু দমিত রাখাও জরুরী ছিলো, যাতে তারা আবার মাথা তোলার সাহস না করে। এজন্য তাদের বেশভূষায়, যানবাহনে ও অন্যান্য চালচলনে এমন জাকজমক প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, যা দ্বারা তাদের অতীত শাসনামলের স্মৃতি পুনরুজ্জীবিত হয়। তবে এধরনের নির্দেশাবলী নিতান্তই সাময়িক ছিলো, চিরস্থায়ী ছিলোনা। আর এসব বিধি ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ থাকলেও তাকে চিরদিন সকল অমুসলিম প্রজার ওপর প্রয়োগ করা চলেনা।
চ. রাষ্ট্র প্রধান, মন্ত্রী, সেনাপতি, বিচারপতি ও এধরনের অন্য যেসব শীর্ষ পদে আসীন হয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণে অংশীদার হওয়া যায়, সেসব পদে কোনো অমুসলিম সমাসীন হতে পারবেনা। এর কারণও কোনো সংকীর্ণতা বা জাতি বিদ্বেষ নয়। বরং এর সোজা ও সঠিক কারণ এই যে, ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র। তাই এই রাষ্ট্রে এসব পদে এমন ব্যক্তিরাই অধিষ্ঠিত হতে পারবে, যারা এই আদর্শকে ভালোভাবে উপলদ্ধি করে এবং একে বিশুদ্ধ ও সত্য বলে মানে। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে; তাই সে নিজের অমুসলিম প্রজাদের মধ্যে ভাড়াটে মানসিকতা সৃষ্টি করা পছন্দ করেনা। বরঞ্চ সে তাদেরকে বলে যে, তোমরা যদি আমাদের আদর্শকে ও নীতিমালাকে সঠিক মনে করো তাহলে প্রকাশ্যে তাকে সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা করো। তোমাদের জন্য শাসকদলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ উন্মুক্ত রয়েছে। আর যদি তোমরা তার সত্যতায় বিশ্বাসী না হও, তাহলে নিছক পেট ও পদমর্যাদা লাভের খাতিরে এই ব্যবস্থার পরিচালনা ও উৎকর্ষ সাধনের কাজে অংশ নিওনা। কেননা আকীদা বিশ্বাসের দিক দিয়ে তো তোমরা ওটাকে ভ্রান্তই মনে করে থাকো।
ছ. অমুসলিম দেশগুলো আপন আপন রাষ্ট্রীয় পরিমন্ডলে মুসলমানদের সাথে কী আচরণ করে এবং কী আচরণ করেনা, সে প্রশ্ন আমাদের কাছে মোটেই কোনো গুরুত্ব রাখেনা। আমরা যে জিনিসকে সত্য ও সঠিক মনে’করবো, নিজেদের দেশে তাকে বাস্তবায়িত করবো। অন্যেরা যে জিনিসকে সঠিক মনে করে, তাকে তারা বাস্তবায়িত করবে কিনা, সেটা তাদের ব্যাপার। এ ব্যাপারে তারা পুরোপুরি স্বাধীন। আমাদের ও তাদের সামগ্রিক কর্মকান্ড বিশ্বজনমতের সামনে একদিন আমাদের ও তাদের সত্যিকার পরিচয় তোলে ধরবে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই আমরা এরূপ ভন্ডামী করতে পারিনা যে, আমাদের সংবিধানের পাতায় প্রদর্শনীমূলকভাবে অমুসলিমদেরকে সকল অধিকার দিয়ে দেবো, কিন্তু বাস্তবে তাদেরকে ভারতের মুসলমানদের, আমেরিকার বেড ইন্ডিয়ানদের এবং রাশিয়ার অকম্যুনিষ্টদের মতো শোচনীয় দশায় ফেলে রাখবো। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এমতাবস্থায় অমুসলিম সংখ্যালঘুরা কি ইসলামী রাষ্ট্রের অনুগত থাকতে পারবে? এর জবাব এই যে, সংবিধানের কয়েকটি শব্দ থেকেই আনুগত্য ও আনুগত্যহীনতার উৎপত্তি হয়না বরং সামগ্রিকভাবে ও বাস্তবে সরকার ও সংখ্যালগু জনগোষ্ঠী নিজেদের অধীনস্থ সংখ্যালঘুদের সাথে যে আচরণ করে থাকে তা থেকেই তার উৎপত্তি ঘটে।
ঙ. ইসলামে মুরতাদের শাস্তি
ইসলামে মুরতাদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। কেউ যদি বলতে চায়, এমনটি হওয়া উচিত নয়, তাহলে সেকথা বলার স্বাধীনতা তার রয়েছে। কিন্তু সে যদি বলে, এধরনের শাস্তি আসলেই ইসলামে নেই, তাহলে সে হয় ইসলামী আইন সম্পর্কে অজ্ঞ, নচেত “প্রতিবেশীর বিদ্রূপে” লজ্জা পেয়ে নিজ ধর্মের একটা বিধানকে সে গোপন করে। ইসলামের এই আইনকে বুঝতে লোকেরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হয় তার একাধিক কারণ রয়েছেঃ
প্রথমতঃ তারা ধর্ম হিসেবে ইসলাম এবং রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামের পার্থক্য বোঝেনা। ফলে একটার বিধান অপরটার ওপর প্রয়োগ করে। অথচ উক্ত দুটি অবস্থার ধরন ও বিধিতে পার্থক্য রয়েছে।
দ্বিতীয়তঃ তারা বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে এই বিধানটি বিবেচনা করে। বর্তমান পরিস্থিতি এই যে, অমুসলিম দেশের কথা বাদ দিন, খোদ মুসলিম দেশেও অনৈমলামিক শিক্ষা ও অনৈসলামিক কৃষ্টির প্রভাবে মুসলমানদের নতুন প্রজন্মে বহুলোক গোমরাহ হয়ে আর্বিভূত হচ্ছে। অথচ একটা যথার্থ ইসলামী রাষ্ট্র বিদ্যমান থাকলে তার সর্বপ্রথম কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এই যে, যেসব কারণে কোনো মুসলমান সত্যি সত্যিই ইসলাম সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ ও মুরতাদ হবার প্ররোচণা পায়, সেসব কারণ দূর করবে। ইসলামী রাষ্ট্র যদি নিজের যথার্থ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, তাহলে তো অমুসলিমদের পক্ষেও কুফরীর প্রতী সন্তুষ্ট থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানের পক্ষে ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা।
তৃতীয়তঃ তারা একথা ভুলে যায় যে, মুসলিম সমাজই ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রস্তর। এই ভিত্তি প্রস্তর কতোখানি মজবুত, তার ওপরই রাষ্টের মজবুতী নির্ভর করে। পৃথিবীতে এমন রাষ্ট্র কোথায় আছে, যা তার নিজের ভেতরেই নিজের ধ্বংসের উপায় উপকরণ লালন ও সংরক্ষণ করে? আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করবো যাতে রাষ্ট্রের এই ভিত্তি প্রস্তরটির সাথে তার প্রতিটি কণা অন্তর দিয়ে লেগে থাকে। তা সত্ত্বেও যদি এমন কোনো কণা বেরিয়েই পড়ে, যা ঐ প্রস্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকেই অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে আমরা তাকে বলবো যে, তুমি যদি বিচ্ছিন্ন হতেই চাও, তবে আমাদের সীমানা থেকে বেরিয়ে যাও। নচেত এখানে বসে তুমি অন্যান্য কণারও নষ্ট হওয়ার কারণ হবে, তা আমরা হতে দিতে পারিনা এবং সেজন্য তোমাকে স্বাধীন ছেড়ে দিতে পারিনা।
চতুর্থতঃ সকল ধরনের মুরতাদের সর্বাবস্থায় হত্যাই করা হবে তারা এই ভুল ধারণায় নিমজ্জিত আছে। অথচ একটা অপরাধের চরম শাস্তি কেবল অপরাধটির নিকৃষ্টতম ধরনের ওপরই প্রয়োগ করা হয়, সাধারণ পর্যায়ের অপরাধের ওপর নয়। কখনো এমন হয়ে থাকে যে, এক ব্যক্তি কেবল আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। অপর একজন প্রকাশ্যে ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন ধর্ম গ্রহণ করে বসে। তৃতীয়জন শুধু মুরতাদ হয়েই ক্ষ্যান্ত হয়না বরং ইসলামের বিরোধীতায় সক্রিয় তাৎপরতা চালাতে থাকে। এধরনের সকল মানুষকে ইসলামী আইন সর্বাবস্থায় একই দৃষ্টিতে দেখবে, এটা কিভাবে ভাবা যায়? [ মাওলানা মওদূদী রচিত “ইসলামী আইনে মুরতাদের শাস্তি” নামক গ্রন্থে বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য। -সম্পাদক]
চ. ইসলামের সমর আইন ও দাস প্রথা
ইসলামের সমর আইন ও দাস প্রথা নিয়েও কিছু প্রশ্ন উঠেছে। এ প্রসংগে বুঝে নিতে হবে যে, ইসলামের যুদ্ধ আইন বাস্তবিক পক্ষে একটি আইন এবং ইসলামী রাষ্ট্র তাকে অবশ্যই কার্যকর করা হবে, চাই আমাদের সাথে যুদ্ধরত অন্যান্য জাতি এ আইনের বিধিনিষেধ ও সীমা সংরক্ষণ করুক বা না করুক। পক্ষান্তরে যে জিনিসটাকে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইন নামে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, তা আসলে কোনো আইন নয়, বরঞ্চ আন্তর্জাতিক চুক্তিসমূহের একটি সমষ্টি মাত্র। এর সীমা ও বিধিসমূহ মেনে চলতে সকল জাতিই এই আশায় ও এই সমঝোতার ভিত্তিতে রাযী হয়েছে যে, অন্যান্য জাতিও যুদ্ধের সময় এগুলো মেনে চলবে। ইসলাম আমাদেরকে যুদ্ধের কয়েকটি নূন্যতম বিধি ও নৈতিক নীতিমালার আনুগত্য করতে আদেশ দিয়েছে। এগুলো অন্যেরা ভংগ করলেও আমরা ভংগ করতে পারিনা। আর ওগুলোর চেয়ে বেশী আরো কিছু সুসভ্য আইনে যদি অন্যান্য জাতি সম্মত হয়, তাহলে আমরা শুধু যে তাদের সাথে এ ব্যাপারে সমঝোতায় আসতে পারি তা নয়, বরং যুদ্ধে অধিকতর সুসভ্য আচরণ করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা আমাদেরই কর্তব্য। উদাহরণ স্বরূপ, দাস প্রথার ব্যাপারটাই ধরুন। ইসলাম এর অনুমতি শুধু সে অবস্থায় দিয়েছে, যখন শত্রুপক্ষ যুদ্ধবন্দী বিনিময়েও সম্মত হয়না, আবার মুক্তিপণের বিনিময়ে নিজেদের বন্দী মুক্ত করা ও আমাদের বন্দী ছাড়ার প্রস্তাবও গ্রহণ করেনা। এরূপ পরিস্থিতিতে ইসলাম বন্দীদেরকে কারাগারে পাঠানো কিংবা শ্রমশিবিরে রেখে শ্রম খাটাতে বাধ্য করা পছন্দ করেনি। বরং তাদেরকে মুসলিম সমাজের সদস্যদের কাছে ব্যক্তিগতভাবে বন্টন করে দেয়ার নীতিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, যাতে তাদের মুসলমানদের সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সহজতর হয়। একথা সত্য যে, সেকালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশও যুদ্ধবন্দীদেরকে দাসদাসী হিসেবেই রেখে দিতো এবং দাসত্ব বা গোলামী শব্দটা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে সকল জাতির যৌথ সম্পত্তি ছিলো। তবে দাসদাসীদের জীবনে ইসলাম যে পরিবর্তন এনেছিলো, তার যৌথ সম্পত্তি ছিলো। তবে দাসদাসীদের জীবনে ইসলাম যে পরিবর্তন এনেছিলো, তার নজীর পৃথিবীতে বিরল। মুসলিম জাতি ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো জাতিতে এতো বেশী সংখ্যক দাস ও দাসপুত্র উচুঁ স্তরের পন্ডিত ও মনীষী, বিচারপতি, সেনাপতি ও শাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছে- এমন দৃষ্টান্ত দেখানো যাবেনা। ইসলামী আইন আমাদেরকে মানবতা ও সভ্যতার যে ন্যূনতম মানে প্রতিষ্ঠিত করে, তা ছিলো এই যে, দাস প্রথা রহিত করা যখন সম্ভব ছিলোনা তখনও দাসদেরকে সমাজে এতো সম্মানজনক আসন দিয়েছে। এখন যদি দুনিয়ার অন্যান্য জাতি যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের নীতি গ্রহণ করে থাকে, তবে তাকে স্বাগত জানাতে আমাদেরকে বাধা দেবে এমন কিছুই ইসলামে নেই। আমাদের জন্য তো এটা আনন্দের ব্যাপার যে, যে জিনিস গ্রহণের জন্য আমরা শত শত বছর আগে দুনিয়াবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলাম, তা অবশেষে জগতবাসী গহণ করেছে।
ছ. ইসলাম ও শিল্পকলা
এই মর্মেও প্রশ্ন তোলা হয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে শিল্পকলার কী দশা হবে, বিশেষত স্থির চিত্র, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য, নাটক, গানবাজনা ইত্যাদির? আমি এ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দেবো যে, শিল্পকলা তো মানুষের স্বভাব প্রকৃতির একটা জন্মগত চাহিদা। স্বয়ং বিশ্বস্রষ্টাও তার প্রতিটি সৃষ্টিকর্মে শিল্পকলার প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন। তাই গোটা শিল্পকলার অবৈধ হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠেনা। তবে আজকাল পাশ্চাত্য সভ্যতায় শিল্পকলার যে প্রকাশ ও অভিব্যক্তি দেখতে পাওয়া যায়, সেটাই মেনে নেয়া জরুরী একথা ঠিক নয়। বরং প্রত্যেক সভ্যতা স্বীয় চিন্তাধারা, মতাদর্শ ও ভাবপ্রবণতার আলোকে বিভিন্ন পন্থায় মানবীয় স্বভাব প্রকৃতির এই চাহিদার স্ফুরণ ঘটায় এবং অন্যান্য সভ্যতার গৃহীত সেসব বৈধ কি অবৈধ, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। পাশ্চাত্য জগত থেকে যে জিনিস আমদানী করা হচ্ছে, কেবল তারই নাম শিল্পকলা, এটা কোন যুক্তিতে ধরে নেয়া হয়েছে? পাশ্চাত্যের শিল্পকলায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে শিল্পকলায় কোনো বিধিনিষেধ আরোপ করা হলে শিল্পকলাটাই খতম হয়ে যাবে- এমন আশংকাই বা কেন করা হয়? শিল্পকলা সম্পর্কে ইসলামের একটা স্বতন্ত্র মতাদর্শ রয়েছে। মানব মনের এই স্বভাব সুলভ চাহিদাকে সে পৌত্তলিকতা, সৌন্দর্য পূজা ও যৌন লালসার পথে ঠেলে দেয়ার বিরোধী। এর প্রকাশ ও স্ফুরণের জন্য সে ভিন্ন পথ দেখায়। ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলামের নিজস্ব মতাদর্শই কর্তৃত্বশীল হবে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও মতাদর্শের কর্তৃত্ব সেখানে কোনোমতেই চালু থাকতে পারবেনা।
জ. ফিকাহ শাস্ত্রীয় মতভেদ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অন্তরায় নয়
এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে যে, মুসলিম ফের্কাসমূহের মধ্যে আকীদাগত ও বিধিগত মতভেদের ধরন কী? তাদের মধ্যে যখন মৌলিক বিষয়েও মতৈক্য নেই, এমনকি “সুন্নাহ্” পর্যন্ত শীয় ও সুন্নীদের মধ্যে সর্বসম্মত বিষয় নয়, তখন একটা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসন কিভাবে চলবে? এর জবাবে আমি শুধু এতোটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করি যে, কথিত ৭৩ ফের্কার সমস্যাটির অস্তিত্ব কার্যত পাকিস্তানে নেই। আর কোনো ব্যক্তি কোনো পত্রপত্রিকায় যে কোনো একটা উদ্ভট চিন্তা তোলে ধরলেই এবং বিক্ষিপ্তভাবে কিছু লোক তা গ্রহণ করলেই তা কোনো উল্লেখযোগ্য ফের্কার উৎপত্তি ঘটায়না। আমাদের দেশে বাস্তবিক পক্ষে মাত্র তিনটে ফের্কা রয়েছেঃ [১] হানাফী ফের্কা। দেওবান্দী ও বেরেলভী এই দুই উপদলে বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই ফের্কার ফিকাহ্ শাস্ত্রে কোনো বিভেদ নেই। [২] আহলে হাদীস এবং [৩] শীয়া। এই তিন ফের্কার মতভেদ কার্যত একটা উসলামী রাষ্ট্র গঠনে ও পরিচালনায় কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করেনা । যদি এই নীতি সর্বসম্মতভাবে মেনে নেয়া হয় যে, পারিবারিক আইন, ধর্মীয় রসমাদি ও ইবাদত এবং ধর্মীয় শিক্ষার পর্যায়ে প্রত্যেক ফের্কার অনুসৃত রীতি অন্য ফের্কার হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকবে এবং দেশের প্রশাসন সংসদের সংখ্যাগুরু সদস্য কর্তৃক নির্ধারিত আইন ও বিধি অনুসারে চলবে। এ প্রসংগে ৭৩ ফের্কার কল্প কাহিনীটির রহস্য উন্মোচন করে দেয়াও আমি সমীচীন মনে করছি। কেননা লোকেরা খামাখাই এই বিষয়টি নিয়ে মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে। আসল ব্যাপারে এই যে, বিভিন্ন বইপুস্তকে মুসলমানদের যে বিপুল সংখ্যক ফের্কার উল্লেখ পাওয়া যায়, তার একটি বিরিাট অংশের নেহাত কাগজে অস্তিত্ব ছাড়া আগেও কোনো অস্তিত্ব ছিলোনা, এখনো নেই। কোনো ব্যক্তি যখনই কোনো নতুন চাঞ্চল্যকর মতামত পেশ করেছে এবং দুই একশো অনুসারী সৃষ্টি হয়ে গেছে, অমনি আমাদের গ্রন্থকারগণ তাকে একটা ফের্কা হিসেবে গণনা করে ফেলেছেন। এ ধরনের ফের্কাগুলো ছাড়াও বেশ কিছু সংখ্যক ফের্কা এমনও রয়েছে, যা বিগত ১৪শ বছরে জন্মেছেও আবার নিশ্চিহ্নও হয়ে গেছে। বর্তমানে সারা দুনিয়ায় মুসলমানদের বড়জোর ৬/৭টি ফের্কা বা উপদল অবশিষ্ট রয়েছে।
মৌলিক মতপার্থক্যের কারণে এগুলোকে স্বতন্ত্র ফের্কা বলা যায় এবং অনুসারীর সংখ্যার বিচারেও এগুলো মোটামুটি উল্লেখযোগ্য। তবে এগুলোর মধ্যেও কোনো কোনোটি অতিমাত্রায় ক্ষুদ্রাকৃতির। এগুলো হয় বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ, নচেত সারা দুনিয়ায় এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, কোথাও তাদের কোনো উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা নেই। দুনিয়ার বড় বড় মুসলিম ফের্কা মাত্র দুটোঃ সুন্নী ও শীয়া। তন্মধ্যে উম্মাহর বিপুল সংখ্যাগুরু অংশ সুন্নীদের নিয়ে গঠিত। এদের শাখা প্রশাখাগুলোর মধ্যে সত্যিকার অর্থে মৌলিক মতপার্থক্য নেই। শুধুমাত্র খুটিনাটি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী কিছু মাযহাব [School of thought] রয়েছে, যাকে তার্কিকেরা ফের্কাররূপ দিয়ে ফেলেছে। কোনো বাস্তবতাবাদী রাজনীতিক যদি দুনিয়ার কোনো দেশে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাহলে এসব মতভেদ তার পথে কখনো বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনা।
[১. এ পর্যন্ত সমগ্র আলোচনাটি তদন্ত আদালতে প্রদত্ত মাওলানার জবানবন্দী থেকে গৃহীত এবং এটি “কাদিয়ানী সমস্যা এবং তার নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক” নামক গ্রন্থের একটি অংশ। – সংকলক।
২. খিলাফত ও স্বৈরতন্ত্র
ক. ইসলামী রাষ্ট্র ও খিলাফত প্রসংগে কয়েকটি প্রশ্ন
[জনৈক জার্মান ছাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ও খিলাফত সম্পর্কিত কতিপয় সমস্যার ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার উদ্দেশ্যে এ প্রশ্নগুলো করেন। আসল প্রশ্নগুলো ছিলো ইংরেজীতে। নীচে তার অনুবাদ দেয়া হলো।]
প্রশ্নঃ এক. ইসলামী রাষ্ট্র প্রধানের জন্যে কি শুধুমাত্র ‘খলীফা’ শব্দটিই ব্যবহার করা যেতে পারে?
দুই. উমাইয়া খলীফাদের কি সঠিক অর্থে খলীফা বলা যেতে পারে?
তিন. আব্বাসীয় খলীফাগণ বিশেষ করে আল মামুন সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?
চার. হযরত ইমাম হাসান রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত ইমাম হুসাইন রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রাজনৈতিক কার্যক্রমকে আপনি কোন্ দৃষ্টিতে দেখেন? আপনার মতে ৬৮০ইং সালে মিল্লাতে ইসলামীয়ার আসল নেতা কে ছিলো, হুসাইন না ইয়াযীদ?
পাঁচ. ইসলামী রাষ্ট্রে বিদ্রোহ কি একটি সৎকর্ম গণ্য হতে পারে?
ছয়. বিদ্রোহীরা যদি মসজিদ বা অন্যান্য পবিত্র স্থানসমূহে [যেমন কা’বা ও হারাম শরীফ] আশ্রয় নেয়, তাহলে এ অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্র তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করবে?
সাত. ইসলামী রাষ্ট্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধান অনুযায়ী তার নাগরিকদের কাছ থেকে কোন্ ধরনের কর আদায় করতে পারে?
আট. কোনো খলীফা কি এমন কোনো কাজ করতে পারে, যা পূর্ববর্তী খলীফাদের কার্যক্রম থেকে ভিন্নতর?
নয়. গভর্নর ও শাসক হিসেবে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?
দশ. ইসলামী রাষ্ট্র কি এমন কোনো কর আরোপ করার অধিকার রাখে, যা কুরআন ও সুন্নাতে উল্লিখিত হয়নি এবং পূর্ববর্তী খলীফাদের আমলেও যার কোনো নজীর নেই?
জবাবঃ আপনি যে প্রশ্নগুলো পাঠিয়েছেন তার বিস্তারিত জবাব দিতে গেলে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, আর সে সময় আমার নেই। তাই এগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দিচ্ছি।
এক ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানের জন্য ‘খলীফা’ শব্দটি এমন কোনো অপরিহার্য পারিভাষা নয় যে, এছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করা যাবেনা। আমীর, ইমাম, সুলতান ইত্যাদি শব্দগুলোও হাদীস, ফিকহ, কালাম ও ইসলামের ইতিহাসে বিপুল পরিমাণে ব্যবহৃহ হয়েছে। কিন্তু নীতিগতভাবে যে জিনিসটির প্রয়োজন তা হলো, রাষ্ট্রের ভিত্তি খিলাফতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। একটি সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র কখনো রাজতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র হতে পারেনা। আবার তা এমন কোনো গণতন্ত্রও হতে পারেনা, যা জনগণের সার্বভৌমত্বের [Popular Sovereignty] ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। বিপরীত পক্ষে, একমাত্র সে রাষ্ট্রকেই ইসলামী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে, যে রাষ্ট্র আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয়া, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের শরীয়তকে শ্রেষ্ঠ আইন এবং আইনের প্রধান ও প্রথম উৎস বলে মেনে নেয় এবং আল্লাহ্ নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে কাজ করার স্বীকৃতি দেয়। এই রাষ্ট্রে কর্তৃত্বশালীদের কর্তৃত্ব লাভের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় আল্লাহর বিধানের পুনরুজ্জীবন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অসৎ বৃত্তির বিনাশ ও সৎবৃত্তির বিকাশ সাধন। এই রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব কোনো সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নয় এবং এটা হচ্ছে আল্লাহর কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব ও তাঁর আমানতত। এরি নাম খিলাফত।
দুই. উমাইয়া শাসকদের সরকার আসলে খিলাফত ছিলোনা। যদিও ইসলামই ছিলো তাদের সরকারের আইন, কিন্তু শাসনতন্ত্রের অনেকগুলো ইসলামী ধারাকে তারা নকচ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তাদের সরকারের প্রাণসত্তা ইসলামী ধারাকে তারা নাকচ করে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তাদের সরকারের প্রাণসত্তা ইসলামের প্রাণসত্তা থেকে বেশ দূরে সরে গিয়েছিলো। তাদের শাসনকালের প্রথম দিকেই এ বিষয়টি অনুধাবন করা হয়েছিলো। তাই এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মু’য়াবীয়া রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজেই বলেন, ‘আনা আউয়ালুল মুলক’ [অর্থাৎ আমি সর্বপ্রথম বাদশাহ] আর যে সময় আমীর মু’য়াবীয়া রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর ছেলেকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন, তখনই হযরত আবু বকর রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পুত্র আবদুর রহমান রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু উঠে দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, এতো রোমের কাইজারদের পদ্ধতিই হলো, কাইজার মরে গেলে তার পুত্রই কাইজার হয়।’
তিন. নীতিগতভাবে আব্বাসীয় খলীফাদের অবস্থাও বনী উমাইয়াদের মতোই। পার্থক্য শুধু এতোটুকু, উমাইয়া খলীফারা দীনের ব্যাপারে ছিলেন উদাসীন [Indifferent], বিপরীত পক্ষে আব্বাসীয় খলীফারা নিজেদের ধর্মীয় খিলাফত ও আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য দীনের ব্যাপারে ইতিবাচক আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাদের এ আগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দীনের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়। যেমন মামুনের আগ্রহ এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যার ফলে তিনি দর্শনের একটি বিষয়, যা আসলে দীনের বিষিয় ছিলোনা, তাকে অনর্থক দীনের বিষয়ে পরিণত করেন। দীনের একটি আকীদারূপে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং সরকারী ক্ষমতাবলে জোর করে মুসলমানদের কাছ থেকে তার সপক্ষে স্বীকৃতি আদায় করার জন্য অমানুষিক যুলুম নির্যাতন চালান।
চার. যে যুগ সম্পর্কে এ প্রশ্নটি করা হয়েছে সেটি ছেলো আসলে ফিতনার যুগ। সে সময় মুসলমানরা মারাত্মক মানসিক নৈরাজ্যের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময় কার্যত মুসলমানদের আসল নেতা কে ছিলো একথা বলা বড় কঠিন। কিন্তু একথা দিবালোকের মতো সত্য, ইয়াযীদের যা কিছু রাজনৈতিক প্রভাব ছিলো তার মূল ভিত্তি ছিলো মাত্র একটি তার হাতে ছিলো ক্ষমতার চাবিকাঠি। তার পিতা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করে তাকে সে রাষ্ট্রের শাসক বানিয়ে দিয়েছিলেন। ঘটনাটা যদি এভাবে সাজানো না হতো এবং ইয়াযীদ সাধারণ মুসলমানদের কাতারে থাকতো, তাহলে সম্ভবত নেতৃত্বের আসনে বসাবার জন্য মুসলমানদের সর্বশেষ দৃষ্টি তার ওপর পড়তো। বিপরীতপক্ষে হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়ায়াল্লাহু তায়ালা আনহু সে সময় উম্মতের সুপরিচিত ও সর্বজন সমাদৃত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং কোনো অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে সম্ভবত মুসলিম জনতার সর্ব প্রথম দৃষ্টি তাঁর ওপরই পড়তো।
পাঁচ. কোনো সৎ ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকলে যালিম শাসকদের মুকাবিলায় বিদ্রোহ করা কেবল বৈধই নয়, ফরযও। এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফার [রঃ] মতামত অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আবু বকর জাসসাস তাঁত ‘আহকামুল কুরআন’ এবং আল মুওয়াফফিকুল মূলকী তাঁর ‘মানাকিবে আবু হানীফা’ গ্রন্থে এর ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। পক্ষান্তরে সৎ ও ইনসাফ ভিত্তিক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ একটি বিরাট গুনাহ। এই ধরনের বিদ্রোহ দমন করার ব্যাপারে সরকারের সাথে সহযোগিতা করা সমস্ত মুমিন সমাজের অপরিহার্য কর্তব্য। মাঝামাঝি অবস্থায় যখন সরকার ন্যায়নিষ্ঠ নয়, কিন্তু অন্যদিকে সৎ ব্যক্তিদের বিপ্লবের সম্ভাবনাও সুস্পষ্ট নয়, এ ক্ষেত্রে অবস্থা সংশয়িত হয়ে যায়। ফিকহের ইমামগণ এ অবস্থায় বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ এ অবস্থায় কেবল হক কথা বলে দেয়াটাই যথেষ্ট মনে করেছেন, কিন্তু বিদ্রোহকেও বৈধ গণ্য করেছেন। অনেকে বিদ্রোহ বৈধ করেছেন এবং শাহাদতবরণ করাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আবার অনেকে সংশোধনের আশায় সরকারের সাথে সহযোগিতাও করেছেন।
ছয়. ন্যায়নিষ্ঠ সরকারের মুকাবিলায় যারা বিদ্রোহ করে তারা যদি মসজিদে আশ্রয় নেয়, তাহলে তাদেরকে অবরোধ করা যেতে পারে। যদি তারা ভেতর থেকে গোলাবর্ষণ করে, তাহলে তাদের জবাবে গোলাবর্ষণ করা যেতে পারে। তবে যদি তারা বাইতুল হারামে আশ্রয় নেয়, তাহলে এ অবস্থায় কেবলমাত্র তাদেরকে অবরোধ করে তাদের এতোটা সংকটে ফেলা যেতে পারে, যার ফলে তারা নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। হারাম শরীফে রক্তপাত করা বা পাথর ও গোলাবর্ষণ করা জায়েয নয়। বিপরীত পক্ষে, একটি যালিম সরকারের অস্তিত্বই হচ্ছে মূর্তিমান গুনাহ। আর তার প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্বের জন্য প্রচেষ্টা চালানোও কেবল গুনাহ বৃদ্ধিই করে মাত্র।
সাত. কুরআন ও সুন্নাহ কর আরোপ করার জন্য কোনো বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ দিয়নি। বরং মুসলমানদের ওপর ইবাদত হিসেবে যাকাত এবং অমুসলিমদের ওপর আনুগত্যের চিহ্ন হিসেবে জিযিয়া কর আরোপ করার পর দেশের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জনগণের ওপর কর আরোপ করার দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছে।
খারাজ, শুল্ক, আমদানী ও রপ্তানী কর, এগুলো একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কুরআন ও সুন্নাহ শরীয়তের বিধান হিসেবে এগুলো আরোপ করেনি বরং ইসলামী হুকুমতগুলো নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী এগুলো আরোপ করেছিলো। এ ব্যাপারে আসল মানদন্ড হচ্ছে দেশের প্রকৃত প্রয়োজন। কোনো শাসক নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে যদি কোনো কর আদায় করে তাহলে তা হারাম গণ্য হবে। দেশের যথার্থ প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য দেশবাসীর সমর্থন নিয়ে কর আরোপ করলে তা বৈধ ও হালাল বিবেচিত হবে।
আট. জী হ্যাঁ। কেবল এটিই নয় বরং নিজের পূর্বের সিদ্ধান্তগুলোও বদলাতে পারেন।
নয়. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ পার্থিব রাজনীতির দৃষ্টিতে বড়ই যোগ্য ছিলেন, আর দীনি দৃষ্টিতে একজন নিকৃষ্ট যালিম শাসক।
দশ. হ্যাঁ, ৭ নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে। [তর্জমানুল কুরআন, মে ১৯৫৯]
খ. আল খিলাফাত না আল হুকুমাত
প্রশ্নঃ বিংশ শতাব্দীতেও যদি ইসলামের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়, তাহলে বর্তমান ভাবধারা ও মতাদর্শের স্থলে ইসলামের ভাবধারা ও মতাদর্শকে অভিষিক্ত করতে গিয়ে যে বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হবে, তা নিরসনে ইবনে খালদুনের আল হুকুমাহ ও [আল খিলাফাহ] এই দুই তত্ত্বের কোনটি বেশী সহায়ক হবে?
জবাবঃ বর্তমান যুগে ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠার পথে যে জিনিস প্রধান অন্তরায় এবং যে ভাবধারা ও মতাদর্শ তার পথ আগলে রয়েছে, তা পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই বুঝা যায় যে, মুসলিম দেশগুলোতে তা পশ্চিমা জাতিসমূহের দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক আধিপত্য ও প্রভুত্বের সৃষ্টি। পশ্চিমা জাতিগুলো যখন আমাদের দেশগুলোতে আপন কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন তারা আমাদের আইন কানুন বাতিল করে নিজেদের আইন চালু করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করে তারা নিজেদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণকারী লোকদের তারা বরখাস্ত করে এবং তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়ে বেরুনো লোকদের জন্য সকল সরকারী চাকুরী নির্দিষ্ট করে দেয়। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তারা নিজস্ব প্রতিষ্ঠানাদি ও রীতিনীতি চালু করে এবং অর্থনীতির ময়দানও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারক বাহকদের জন্য হয়ে যায় একচেটিয়া। এভাবে তারা আমাদের ভেতরেই আমাদের সভ্যতা, কৃষ্টি ও আদর্শ বিবর্জিত একটি জেনারেশন গড়ে তোলে যা ইসলাম, ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্য থেকে কাজেকর্মেও যেমন সম্পর্কচ্যুত, আবেগ অনুভূতিতে এবং মন মানসিকতায়ও তেমনি সংশ্রবহীন। মূলত এ জিনিসটাই আমাদের ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনে অন্তরায়। আর এ কারণেই এ ভ্রান্ত ধারণারও সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম বর্তমান যুগে কার্যোপযোগী নয়। যাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষা অনৈসলামিক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে, তাদের ইসলামকে অবাস্তব ও অনুপযোগী বলা ছাড়া আর কিইবা বলার থাকতে পারে? কেননা তারা ইসলামকে জানেওনা, তদনুসারে কাজ করার জন্যও তাদেরকে গড়ে তোলা হয়নি। যে জীবন ব্যবস্থার উপযোগী করে তাদেরকে তৈরী করা হয়েছে সেটাকেই কার্যোপযোগী ভাবা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় অনিবার্যভাবে আমাদের সামনে দুটো পথই থাকে। হয় আমাদেরকে জাতি হিসেবে কাফির হয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং অনর্থক ইসলামের নাম নিয়ে বিশ্বকে ধোঁকা দেয়া বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় পরিপূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে [মুনাফিকীর সাথে নয়] আমাদের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করতে হবে। এ শিক্ষা ব্যবস্থার পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে যে, এর কোন্ কোন্ উপাদান আমাদেরকে ইসলাম থেকে বিপথগামী করে দেয় এবং এতে কি কি পরিবর্তন এনে আমরা ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার যোগ্য লোক বানানোর কাজ এর দ্বারা নিতে পারি। আমি অত্যন্ত পরিতাপের সাথে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের শিক্ষা কমিশন এ বিষয়ের দিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ দেয়নি। অথচ এ সমস্যাটা খুব ঠান্ডা মাথার বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিলো। কেননা যতক্ষণ আমরা এ সমস্যার সামাধান না করবো ততক্ষণ ইসলামী বিধানের বাস্তবায়নের পথ কিছুতেই সুগম হবেনা।
ইবনে খালদুনের কোনো মতবাদই এ সমস্যার সমাধানে সহায়ক হবেনা। কেননা এ সমস্যার যে গুণগত অবস্থা এখন সৃষ্টি হয়েছে, তা ইবনে খালদুনের আমলে সৃষ্টি হয়নি। সমস্যাটার প্রকৃত ধরন এই যে, পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ বিদায় নেয়ার সময় আমাদের দেশে তাদের নিজস্ব শিক্ষা সংস্কৃতির দুধকলা দিয়ে পোষা এমন একটি শ্রেণীকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে রেখে গেছে, যারা দৈহিক দিক দিয়ে আমাদের জাতির অংশ হলেও জ্ঞান, চিন্তা, মামসিকতা ও চরিত্রের দিক দিয়ে ইংরেজ, ফরাসী ও ওলন্দাজদের যথার্থ উত্তরাধিকারী। এ শ্রেণীর শাসন থেকে যে সমস্যার উদ্ভব হয় তার সমাধান এতো জটিল যে, তার সমাধান ইবনে খালদুনের মতবাদের সাধ্যতীত। এজন্য অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় চিন্তা ভাবনা করা এবং পরিস্থিতি বুঝে সংস্কারের নতুন পথ উদ্ভাবন করা প্রয়োজন। [তরজামানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১]
গ. ইসলামী রাষ্ট্র এবং পোপতন্ত্রের আদর্শিক পার্থক্য
প্রশ্নঃ আবু সায়ীদ বযমী সাহেব ‘রিসালায়ে হক’ নামক সাময়িকীতে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ সেটাও ইসলামী রাজনীতির একটি ধারণা, ইদানীং মাওলানা আবুল আলা মওদূদী খুব জোরে শোরে যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পেশকৃত ইসলামী রাজনীতির মৌলিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে এই যে, সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহী করবেনা। ঐতিহাসিক দিক থেকে এটা কোনো নতুন মূলনীতি নয়। ইউরোপে দীর্ঘকাল পর্যন্ত থিওক্রেসি [Theocracy] নামে এরি চর্চা হচ্ছিলো। রোমের প্রধান পোপের নেতৃত্ব এই ধারণারই ফলশ্রুতি। কিন্তু লোকেরা মনে করছে, যেহেতু খোদা কোনো বক্তব্য প্রকাশক প্রতিষ্ঠান নয়, তাই খোদার নামে যে ব্যক্তিই ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করে সে খুব সহজেই তা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে পারে। মাওলানা মওদূদীর সমর্থকরা দাবী করছে যে তাদের উপস্থাপিত রূপরেখা পোপতন্ত্রের চাইতে ভিন্নতর, কিন্তু যেহেতু সে সরকার জনগণের সামনে জবাবদিহী করতে বাধ্য নয় এবং এর ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে ভ্রান্ত মনে করে, তাই এ ধারণা এবং পোপতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকেনা।
অতপর বযমী সাহেব নিজের পক্ষ থেকে একটা সমাধান পেশ করেন। কিন্তু সেটাও সন্তোষজনক নয়। মেহেরবাণী করে তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এ ভ্রান্ত ধারণা দূর করে সঠিক দৃষ্টিকোণ পেশ করবেন।
জবাবঃ বযমী সাহেব সম্ভবত আমার “ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ” বইটি পড়ে দেখেননি। পড়লে তিনি দেখতেন, আমার নীতির উপর তিনি যেসব আপত্তি তোলেছেন, সেগুলোর পূর্ণ জবাব তাতে রয়েছে। কিন্তু তিনি যদি বইটি পড়ে থাকেন, তবে তাঁর মন্তব্যের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই আমার করার নেই। এ ব্যাপারে আমার সে বইটির নিম্নোক্ত বাক্যগুলো দেখুনঃ
“কিন্তু ইউরোপ যে থিওক্রেসির সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্রেসি তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইউরোপ তো সেই থিওক্রেসীর সাথেই পরিচিত, যাতে একটা বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী খোদার নাম করে নিজেদেরই মনগড়া আইন কানুন চালিয়ে দেয় এবং কার্যত সকল নাগরিকের উপর নিজেদেরই মনগড়া আইন কানুন চালিয়ে দেয় এবং কার্যত সকল নাগরিকের উপর নিজেদের খোদায়ী চাপিয়ে দেয়। এ রকম রাষ্ট্রকে খোদায়ী রাষ্ট্র বলার পরিবর্তে ভিন্নতর। সেটা কোনো বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণীর মুষ্টিবদ্ধ থাকেনা, বরঞ্চ তা থাকে সাধারণ মুসলমানদের করায়ত্বে। আর মুসলমান সাধারণ এ রাষ্ট্রকে আল্লাহর কিতাব এবং রসূলের সুন্নাহ্ মুতাবিক পরিচালিত করে। আমাকে যদি একটি নতুন পরিভাষা তৈরী করার অনুমতি দেয়া হয় তবে আমি এ পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে “খোদায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র” [Theo Democratic state] নামে অবিহিত করবো। কেননা এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধীনে মুসলমানদেরকে একটি সীমিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দান করা হয়েছে। এর কার্যনির্বাহী পরিষদ তৈরী হবে মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে। এ পরিষদকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও মুসলমানদেরই হাতে থাকবে। যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয় এবং সেসব বিষয়, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহর শরীয়তে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান নেই- সেগুলো মুসলমানদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। আর যেখানে খোদায়ী কানুনের ব্যাখ্যা দান প্রয়োজন হবে সেখানে কোনো তবকা এবং গোত্রের লোকেরা নয়, বরঞ্চ সর্ব সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন।”
অতপর এ বাক্যগুলোর নিচে আমি একটি টিকায় আরো স্পষ্ট করে বলেছিঃ
খ্রীষ্টান পাদ্রী ও পোপদের নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের কয়েকটি নৈতিক শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষের বাস্তব ধর্ম ও সামাজিক জীবনের জন্যে মূলত তাদের নিকট কোনো শরীয়তই ছিলোনা। তাই তারা নিজেদের মর্জী মতো নিজেদের লালসা ও ইচ্ছা বাসনা অনুসারে আইন তৈরী করতো এবং সেটাকেই আল্লাহর দেয়া আইন বলে চালু করতো।
যে ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্ম এবং পোপতন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এ বাক্যগুলোতে আমি যেদিকে ইংগিত করেছি, তিনি তা বুঝতে ভুল করতে পারেননা। ইউরোপের পোপতন্ত্র ছিলো সেন্ট পলের অনুসারী । ইনি মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে কেবল সেসব নৈতিক শিক্ষার উপর খৃষ্টবাদের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন যা নিউ টেষ্টমেন্টে পাওয়া যায়। এসব নৈতিক শিক্ষার মধ্যে এমন কোনো আইন কানুন বর্তমান নেই, যদ্বারা একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু পোপরা যখন ইউরোপে বিনা করণে বা কারণে থিওক্রেসী প্রতিষ্ঠা করলো, তখন তারা একটি আইনের বিধানও তৈরী করলো। একথা সুস্পষ্ট যে তাদের এ বিধান কোনো অহী বা ইলহাম থেকে গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ এ ছিলো তাদের মনগড়া জিনিস। এতে তারা যে আকীদাহ বিশ্বাসের বিধান, ধর্মীয় কর্মকান্ড ও আচার অনুষ্ঠানে যেসব নযর নিয়াজ এবং যেসব সামাজিক বিধি বন্ধন প্রভৃতি তৈরী করে নিয়ে ছিলো, তার কোনোটিই আল্লাহর কিতাব থেকে গ্রহণের কোনো প্রমাণ তাদের নিকট ছিলোনা। এমনি করে আল্লহ এবং বান্দার মাঝখানে তারা ধর্মীয় নেতাদের যে স্থায়ী মিডিয়া নির্ধারণ করেছে, সেটাও সম্পূর্ণই তাদের মনগড়া। এ ছাড়া গীর্জা ব্যবস্থার কর্মীদের জন্যে তারা যেসব ক্ষমতা ও অধিকার ধার্য করেছে এবং লোকদের উপর ধর্মীয় টেক্স ধার্য করেছে এগুলোও তারা গ্রহণ করেছে তাদের নিজেদের ইচ্ছা আকাংখা এবং কামনা বাসনা থেকে। এ ধরনের ব্যবস্থাকে তারা যতোই থিওক্রেসী নাম দিক না কেন প্রকৃত পক্ষে এটা থিওক্রেসী নয়। এটাকে ইসলামী হুকুমাত বা খোদায়ী শরীয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে কিভাবে তুলনা করা যেতে পারে? ইসলামী রাষ্ট্র তো কিতাব ও সুন্নাতের এক অপরিবর্তনীয় রদবদল অযোগ্য সমুদ্ভাসিত চিরস্থায়ী শাশ্বত বিধান। এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষ কোনো ধর্মীয় শ্রেণী ইজারা করে নেয়নি।
বযমী সাহেবের এ বক্তব্য আরো অধিক বিস্ময়কর, যাতে তিনি বলেছেন যে, আমি ইসলামের খলীফাকে সে পজিশন দিয়েছি, খৃষ্টবাদে পোপের যে পজিশন রয়েছে এবং আমি খলীফাকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহী করতে হবেনা বলে মনে করেছি। এর জবাবে আমার সে বইটি থেকেই আরো কয়েকটি অংশ উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছিঃ
“যারা ঈমান এনে আমলে সালেহ্ ( যোগ্যতার সাথে কাজ) করবে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন, তিনি তাদের তেমনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন, যেমন দান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের।” (সূরা আননূরঃ ৫৫)
এ আয়াতটি উল্লেখ করে আমি লিখেছিঃ
“এ আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, খলীফা নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি সকল মুমিনের সংগেই দেয়া হয়েছে। মুমিনদের কোনো একজনকে খলীফা বানাবো,- আয়াতে এ কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূলত সকল মুমিনই খিলাফতের দায়িত্বশীল খলীফা। আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের যে খিলাফত দান করা হয়েছে তা সর্বজনীন খিলাফত।”
আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমি লিখেছিঃ
“এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই খলীফা। মুসলমান জনসাধারণের খিলাফত অধিকারকে হরন করে কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি নিজেরাই নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক ও হর্তাকর্তা হয়ে বসা সম্ভব নয়। শাসন শৃংখলা স্থাপনের জন্যে ইসলামী সমাজের প্রত্যেক নাগরিক-ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী প্রত্যেক খলীফা নিজ নিজ খিলাফত অধিকার যখন স্বেচ্ছায় ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে, তখন সে-ই ইসলামী সমাজের শাসনকর্তা। সে ব্যক্তি এক দিকে আল্লাহর নিকট দায়ী থাকে। অপর দিকে দায়ী থাকে জনগণ তথা সাধারণ খলীফাদের নিকট যারা নিজেদের খিলাফত অধিকার তার হাতে সোপর্দ করেছে।”
অতপর বইয়ের অন্য স্থানে আমি স্পষ্ট করে বলেছিঃ
“ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম, আমীর বা রাষ্ট্রপতির প্রকৃত মর্যাদা হচ্ছে এই যে, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্ প্রদত্ত যে খিলাফত লাভ করেছে, সে ক্ষমতা সে নিজ সমাজ থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় আমানত রাখে মাত্র। তাকে যে খলীফা নামে অভিহিত করা হয় তার অর্থ এ নয় যে, তিনি একাই আল্লাহর খলীফা। বরঞ্চ সর্ব সাধারণ মুসলমানের স্বতন্ত্র খিলাফত তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলেই তাকে খলীফা বলা হয় মাত্র।”
অতপর নিম্নোক্ত প্যারাটিও আমার বইটিতে বর্তমান আছেঃ
“আমীর সমালোচনার উর্ধ্বে নন। প্রত্যেক মুসলমানই তার সমালোচনা করতে পারে। কেবল তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই যে সমালোচনা করা যাবে তা নয়, বরঞ্চ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। [প্রয়োজনে] আমীরকে পদচ্যুতও করা যাবে। আইনের দৃষ্টিতে একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই তার মর্যাদা। তার বিরুদ্ধে আদালতে মুকাদ্দমা দায়ের করা যাবে। আদালতকে তার সাথে বিশেষ সম্মানের আচরণ করতে হবে এ অধিকার তিনি রাখেননা। আমীরকে পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। এমন লোকদের নিয়ে পরামর্শ পরিষদ গঠন করতে হবে, যারা হবে সাধারণ মুসলমানদের আস্থাভাজন। মজলিসে শূরার সদস্যদেরকে মুসলমানরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার ব্যাপারেও শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সর্বাবস্থায় সর্বসাধারণ মুসলমানরা একথার প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে, আমীর তার এই ব্যাপক ক্ষমতা তাকওয়া এবং খোদা ভীতির সাথে ব্যবহার করছে, নাকি নিজের খেয়াল খুশী মতো? অন্য কথায়, জনগণে রায় ইসলামী রাষ্টের আমীরকে পদচ্যুত করতে পারে।”
এ সব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের থিওক্রেসীকে রোমের পাদ্রীদের তৈরী করা থিওক্রেসীর সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে তবে আমরা তো আর তাকে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার রাখিনা। কিন্তু একথা বলার অধিকার অবশ্যি রাখি যে, তার এই মতামত জ্ঞান, যুক্তি ও দলিল প্রমাণের সীমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।
ঘ. ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম রাষ্ট্র
[১. ১৯৫২ সালের ২৪ শে নভেম্বর করাচী বার সমিতির পক্ষ থেকে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। ঘ তে বর্ণিত প্রশ্নোত্তর সেখানে থেকে নেয়া হয়েছে। -সংকলক]
প্রশ্নঃ খিলাফতে রাশেদার পর মুসলমানদের যেসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলো ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো, না অনৈসলামিক রাষ্ট্র?
উত্তরঃ আসলে সেগুলো পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্রও ছিলোনা, পুরোপুরি অনৈসিলামিক রাষ্ট্রও ছিলোনা। ঐসব রাষ্ট্রে ইসলামী শাসনতন্ত্রের দুটো গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে বিকৃত করে ফেলা হয়েছিলো। প্রথমতঃ নেতৃত্বকে নির্বাচিত হতে হবে।
দ্বিতীয়তঃ সরকারের কর্মকান্ড পরামর্শের ভিত্তিতে চালাতে হবে।
এছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্রের বাদবাকী অংশও যথাযথ প্রাণশক্তি সহকারে বহাল ছিলোনা। তবে তাকে পরিবর্তিত বা রহিতও করা হয়নি। ঐসব রাষ্ট্রে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস বলে গণ্য করা হয়েছেলো। আদালতগুলোতে ইসলামী আইনই কার্যকর হতো এবং ইসলামী আইন বাতিল করে তার জায়গায় মানব রচিত আইন চালু করার ধৃষ্টতা মুসলিম শাসকরা কখনো দেখায়ন। আর যদিও বা কখনো কোনো শাসক এই স্পর্ধা দেখিয়ে থাকে। তবে ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে যে, আল্লাহর কোনো না কোনো বান্দা তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক জিহাদ পরিচালনা করেছে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ মহাপাপের উচ্ছেদ সাধিত হয়েছে। ইবনে তাইমিয়া ও মুজাদ্দিদে আলফে সানী [রঃ] এ ধরনের ঘৃণ্য উদ্যোগের বিরুদ্ধে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছেন, ইতিহাস তার সাক্ষী রয়েছে।
৩. জাতীয় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ
ক. আইন সভায় মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রশ্ন
আমার কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, মহিলাদের আইন সভার সদস্য হওয়া কোন্ ইসলামী বিধি বলে বিষিদ্ধ? আইন সভাকে কুরআন ও হাদীসের কোন্ উক্তিতে শুধুমাত্র পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে?
এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে একটি বিষয় আমাদের খুব ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। সেটি হলো, যে আইন সভার সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সম্পর্কে বিতর্ক চলছে, সেই আইন সভার চরিত্র ও প্রকৃতি কি ধরনের?
এসব পরিষদকে আইন সভা নামে আখ্যায়িত করার কারণে এই ভুল ধারণা জন্মে যে, এসব আইন সভার কাজ শুধু আইন প্রণয়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতঃপর মনের অভ্যন্তরে এই ভুল ধারণাকে বহাল রেখে একজন মানুষ দেখতে পায় যে, সাহাবায়ে কিরামের আমলে মহিলারা আইনগত বিষয়ে আলাপ আলোচনা, কর্থাবার্তা ও মতামত প্রকাশ করতেন, অনেক সভায় স্বয়ং খলীফারাও তাদের মতামত নিতেন এবং তার মূল্যও দিতেন। অতঃপর সে অবাক হয়ে ভাবে যে, তাহলে আজ ইসলামী আদর্শের নামে এ ধরনের পরিষদগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণকে ভ্রান্ত বলা যায় কিভাবে? কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, বর্তমান যুগে আইন সভা নামে আখ্যয়িত পরিষদগুলোর কাজ কেবল আইন প্রণয়নে সীমাবদ্ধ নয়, বরং কার্যত এই আইন সভাই সমগ্র দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই পরিষদই মন্ত্রীসভা ভাংগে ও গড়ে, রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নিদ্ধারণ করে। অর্থনীতির সমস্যাগুলোর সমাধান করে এবং যুদ্ধ ও সন্ধির চাবিকাঠি তারই হাতে নিবদ্ধ থাকে। এ দিক থেকে এই পরিষদ শুধু ফকীহ বা মুফতী নয় বরং রাষ্ট্রের “ পরিচালক শক্তি”।
এবার আসুন দেখা যাক, কুরআন এ “পরিচালক” এর মর্যাদা কাকে দেয় এবং কাকে দেয়না।
সূরা নিসায় আল্লাহ্ বলেনঃ
“পুরুষরা নারীদের পরিচালক। আল্লাহ্ তাদের একজনকে অপরজনের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন আর যেহেতু পুরুষ স্ত্রীর ব্যয় নির্বাহ করে। সৎ নারীরা অনুগত ও আল্লাহর রক্ষণাবেক্ষণের আওতাধীনে অনুপস্থিতাবস্থায় রক্ষকের ভূমিকা পালন করে।” (আয়াতঃ ৩৪)
এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুরুষকেই পরিচালকের মর্যাদা দিয়েছেন। আর সৎ স্ত্রীদের দুটো গুণ বর্ণনা করছেন, এক. আনুগত্যশীলতা, দুই. পুরুষের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্ যে সব জিনিসের রক্ষণাবেক্ষণ করাতে চান, তার রক্ষণাবেক্ষণ করা।
আপনি হয়তো বলবেন, এটা তো পারিবারিক শৃংখলার জন্য, রাজনৈতিক ব্যবস্থার জন্য নয়। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সঠিক নয়। কারণ প্রথমতঃ এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা এ কথা বলেননি যে, পুরুষ শুধু ঘরোয়া বা পারিবারিক ক্ষেত্রে নারীর পরিচালক, বরং কথাটা সাধারণ ও শর্তহীনভাবে বলেছেন। তাছাড়া এ ব্যাখ্যা যদি মেনে নেয়াও হয় যে, পুরুষকে পারিবারিক জীবনে নারীর পরিচালক করা হয়েছে, তাহলেও প্রশ্ন ওঠে যে, যে নারীকে আল্লাহ্ ঘরের ভেতরেও পরিচালিকা ও নেত্রী বানালেননা, বরং অনুগত করে রাখলেন, আপনারা তাকে গোটা দেশের পরিচালকে পরিণত করতে চান কোন্ যুক্তিতে? গৃহাভ্যন্তরের পরিচালকের দায়িত্বের তুলনায় তো দেশের পরিচালকের দায়িত্ব অনেক বড়। আল্লাহর সম্পর্কে কি আপনি এরূপ ধারণা পোষণ করেন যে, তিনি স্ত্রী লোককে একটা গৃহের পরিচালিকা বানাবেননা, অথচ লক্ষ লক্ষ গৃহের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল দেশের পরিচালিকা বানিয়ে দেবেন?
আরো দেখুন, কুরআন স্পষ্ট ভাষায় নারীর কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে দিচ্ছে এই বলেঃ “নিজ নিজ গৃহে সসম্মানে অবস্থান করো এবং অতীত জাহিলিয়াতের ন্যায় সেজেগুজে বাইরে বের হয়োনা।” (সূরা আহযাবঃ ৩৩)
আপনি হয়তো আবারও বলবেন যে, এ হুকুম তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের মহিলাদেরকে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আমি জানতে চাই যে, আপনার মহত ধারণা অনুসারে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের মহিলাদের মধ্যে কি এমন কোনো গুরুতর দোষ ছিলো যার দরুণ গৃহের বাইরের দায়িত্ব পালনে তারা অক্ষম ছিলেন? আর অন্য মহিলারা কি এদিক দিয়ে তাদের চেয়ে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী? এখন যদি এ সংক্রান্ত সকল আয়াতকে শুধুমাত্র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহের মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট ধরে নিই, তাহলে স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তেও আসতে হয় যে, অন্যান্য মুসলিম মহিলাদের জন্য জাহিলী কায়দায় সেজেগুজে বাইরে বের হওয়া জায়েয। এটা কি আপনি মেনে নেবেন? তাদের জন্য কি ভিন্ন পুরুষদের সাথে এমনভাবে কথা বলা জায়েয, যাতে তাদের মনে আকর্ষণ জন্মে? আল্লাহ্ কি স্বীয় নবীর গৃহ বাদে সকল মুসলমানের গৃহকে “অপবিত্র” দেখতে চান?
এরপর হাদীসের প্রসংগে আসুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেনঃ
“যখন তোমাদের নেতা ও শাসকগণ তোমাদের সবচেয়ে অসৎ লোক হেব, যখন তোমাদের ধনী লোকেরা কৃপণ হবে এবং তোমাদের সামষ্টিক বিষয়ের দায়িত্ব স্ত্রী লোকদের হাতে থাকবে। তখন পৃথিবীর পেট হবে তোমাদের জন্য তার পিঠের চেয়ে উত্তম।” (তিরমিযী)
“হযরত আবু বকর থেকে বর্ণিত যে, যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন, ইরানীরা তাদের সম্রাটের মেয়েকে সম্রাট বানিয়েছে, তখন তিনি বললেন, যে জাতি কোনো নারীকে নিজেদের শাসক বানায় সে জাতি কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।” (বুখারী)
এই উভয় হাদীস আল্লাহ্ তায়ালার “পুরুষরা স্ত্রীদের পরিচালক” এই উক্তির যথার্থ ব্যাখ্যা প্রদান করে। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, রাজনীতি ও দেশ শাসন নারীর কর্মসীমা বহির্ভূত। প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে স্ত্রীর কর্মসীমা কী? এর জবাব রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নোক্ত বাণীসমূহ থেকে পাওয়া যায়ঃ
“স্ত্রী লোক স্বীয় স্বামীর ঘরবাড়ী ও সন্তানদের রক্ষক। তাদের সম্পর্কে তাকে জবাবদিহী করতে হবে।” (আবু দাউদ)
“তোমরা সসম্মানে নিজ নিজ গৃহে অবস্থান করো” এই আয়াতাংশের যথার্থ তাফসীর উপরোক্ত হাদীসে পাওয়া যাচ্ছে। আরো কয়েকটি হাদীসে মহিলাদেরকে রাজনীতি ও দেশ শাসনের চেয়ে নিম্নতর পর্যায়ের গৃহবহির্ভূত কর্মকান্ডও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঐ হাদীসগুলো দ্বারা উক্ত আয়াতাংশের আরো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ ধরনের দুটি হাদীস নিম্নে দিলামঃ
“জামায়াতে জুময়ার নামায পড়া প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য কেবল চার ব্যক্তি ছাড়াঃ দাস, নারী, শিশু ও রোগী।” (আবু দাউদ)
“উম্মে আতিয়া থেকে বর্ণিত যে, আমাদেরকে কফিনের সাথে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।” (বুখারী)
যদিও আমাদের কাছে নিজ দৃষ্টিভংগির সপক্ষে অকাট্য ও সুদৃঢ় যুক্তি প্রমাণও রয়েছে এবং চ্যালেঞ্জ দিলে আমরা সে সকল যুক্তি তোলে ধরতে পারি। কিন্তু প্রথমতঃ সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়নি। দ্বিতীযতঃ আমি কোনো মুসলমানের এ অধিকার স্বীকার করতে প্রস্তুত নই যে, সে আল্লাহ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ জানার পরও তা পালন করার আগে এবং পালন করার শর্ত স্বরূপ যুক্তি প্রমাণ চাইতে পারে। প্রকৃতই মুসলমান হয়ে থাকলে তাকে প্রথমে হুকুম পালন করতে হবে। তারপর নিজের বিবেকের তৃপ্তির জন্য যুক্তি প্রমাণ চাইতে পারে। কিন্তু সে যদি বলে যে, আমাকে আগে যুক্তি দিয়ে সন্তুষ্ট করো, নচেৎ আমি আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মানবোনা, তাহলে আমি তাকে মুসলমাসই স্বীকার করিনা, ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের অধিকারের তো প্রশ্নই ওঠেনা। হুকুম পালনের শর্ত স্বরূপ যে ব্যক্তি যুক্তির দাবী করে তার স্থান ইসলামের গন্ডীর ভেতরে নয়, বাইরে।
রাজনীতি ও দেশ শাসনে নারীর অধিকারকে যারা শরীয়তসম্মত প্রমাণ করতে চায়, তাদের একমাত্র যুক্তি এই যে, হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যার বিচার দাবী করে হযরত আলীর বিরুদ্ধে উষ্ট্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো। কিন্তু প্রথমতঃ এই যুক্তি নীতিগতভাবেই ভ্রান্ত। কেননা যে ব্যাপারে আল্লাহ্ ও রসূলের সুস্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান সে ব্যাপারে কোনো সাহাবীর ব্যক্তিগত কাজ, যদি সেই নির্দেশের বিপরীত প্রতীয়মান হয়, তবে কোনো মতেই তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। সাহাবায়ে কিরামের পবিত্র আদর্শ জীবন নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য আলোর মশাল স্বরূপ। কিন্তু সেটা শুধু এই উদ্দেশ্যে নয় যে, আল্লাহ্ ও রসূলের পথ নির্দেশ বর্জন করে তাদের কারো ব্যক্তিগত পদস্খলনের অনুসরণ করবো। তাছাড়া যে কাজকে সে যুগেরই বড় বড় সাহাবাগণ ভ্রান্ত আখ্যায়িত করেছিলেন, তাকে কিভাবে ইসলামে একটা নতুন বিদয়াতের সূত্রপাত করার জন্য যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে!
হযরত আয়েশার এই উদ্যোগের খবর পাওয়া মাত্রই উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা তাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তা ইবনে কুতাইবা স্বীয় “আল ইমামাতু ওয়াস্ সিয়াসাহ” নামক গ্রন্থে এবং ইবনে আব্দু রব্বিহি স্বীয় “ইকদুল ফরীদ” নামক গ্রন্থে পুরোপুরি উদ্ধৃত করেছেন। সে চিঠিটা পড়ে দেখলে বুঝা যাবে যে, কত দৃঢ়তা ও তেজস্বীতার সাথে তিনি বলেছেনঃ
কুরআন আপনাকে সংকুচিত করে দিয়েছে, আপনি নিজেকে প্রসারিত করবেননা। ….. আপনার কি মনে নেই যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামে বাড়াবাড়ি করতে আপনাকে নিষেধ করেছেন।….. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি আপনাকে এ ভাবে উটের পিঠে চড়ে কোনো মরুভূমিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ছুটাছুটি করতে দেখতেন, তাহলে আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন?
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের এ উক্তিটাও স্মরণ করার মতো যে, “আয়েশা রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহার জন্য তাঁর গৃহ তার উটের হাওদার চেয়ে উত্তম।”
বুখারী শরীফে হযরত আবু বকর (রা) এই উক্তি লক্ষ্য করুন যে, “আমি উষ্ট্র যুদ্ধের বিভ্রাটে পড়া থেকে শুধু এজন্য বেঁচে গিয়েছিলাম যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণীটি আমার মনে পড়ে গিয়েছিলো, যে জাতি নিজের সামষ্টিক কর্মকান্ডের দায়িত্ব কোনো নারীর হতে সোপর্দ করে, সে জাতির কল্যাণ নেই।”
সে যুগে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর চেয়ে বেশী শরীয়তের পারদর্শী আর কেউ ছিলোনা। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় হযরত আয়েশাকে লেখেন, আপনার এ উদ্যোগ শরীয়তের সীমানা বহির্ভূত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা অতি উচ্চ স্তরের বিদুষী ও বিচক্ষণ মহিলা হওয়া সত্ত্বেও জবাবে কোনো যুক্তি প্রমাণ পেশ করতে পারেননি। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেন, “একথা সত্য যে, আপনি আল্লাহ ও রসূলের খাতিরেই ক্রুদ্ধ হয়ে বাইরে বেরিয়েছেন। কিন্তু আপনি এমন একটা কাজের পেছনে লেগেছেন, যার দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পণ করা হয়নি। যুদ্ধ ও সমাজ সংস্কারের সাথে নারীদের কী সম্পর্ক! আপনি হযরত উসমানের হত্যার বিচার দাবী করছেন, কিন্তু আমি সত্য বলছি যে, যে ব্যক্তি আপনাকে এই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে এবং এই গুনাহর কাজে প্ররোচিত করেছে, সে আপনার জন্য উসমানের হত্যাকারীদের চেয়ে বেশী পাপী।”
দেখুন, এই চিঠিতে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আয়েশার কাজকে সুস্পষ্ট ভাষায় শরীয়ত বিরোধী আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু হযরত আয়েশা এর জবাবে শুধুমাত্র এই কথাটা বলতে পেরেছিলেন, “ঘটনা এখন এতোদূর গড়িয়ে গেছে যে, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করে কাজ হবেনা।”
তারপর উষ্ট্র যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটার পর হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে দেখা করতে তাঁর উষ্টের কাছে গেলেন, তখন তাকে বললেনঃ
“হে উষ্ট্রারোহিনী! আল্লাহ্ আপনাকে ঘরে বসে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু আপনি যোদ্ধার বেশে বাইরে বেরিয়ে এলেন!”
কিন্তু এ সময়েও হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলতে পারেননি যে, আল্লাহ্ আমাদেরকে ঘরে বসে থাকতে বলেননি, রাজনীতি ও যুদ্ধে অংশ গ্রহণের অধিকার আমাদের রয়েছে।
এ কথাও ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, অবশেষে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা অনুতাপ করতে থাকেন। আল্লামা ইবনে আব্দুল বার স্বীয় গ্রন্থ ‘আলইস্তীয়াবে’ লিখেছেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে অনুযোগের সূরে বলেন, “তুমি কেন আমাকে এ কাজে যেতে বাধা দিলেনা?’ তিনি জবাব দিলেন, “আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি [অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের] আপনার মতামতকে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং আপনি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলতে পারবেন বলে আমার আশা ছিলোনা।” তখন উম্মুল মুমিনীন বললেন, “তুমি যদি আমাকে নিষেধ করতে তবে আমি বেরুতামনা।”
এরপর হযরত আয়েশার কাজ দেখিয়ে এই মর্মে যুক্তি প্রদর্শনের আর অবকাশ কোথায় যে, ইসলামে নারীকেও রাজনীতি ও দেশ শসনের দায়িত্বের অংশীদার করা হয়েছে? অবশ্য যারা মনে করে দুনিয়ার বিজয়ী জাতিগুলো যে কাজ করে সেটাই সত্য ও সঠিক এবং যারা সবাই যেদিকে চলে সেদিকেই চলার সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে, তাদেরকে কে বলেছে যে, ইসলামকেও সাথে নিয়ে যাও? তাদের যেদিক ইচ্ছা হয় চলুক। কিন্তু এতোটুকু সৎ সাহস তো তাদের থাকা উচিৎ যে, তারা আসলে যাদের অনুসারী, তাদের নামটাই বলবে এবং যুক্তি প্রমাণ ছাড়া ইসলামের ওপর এমন কোনো জিনিস চাপাবেনা যা আল্লাহর কিতাব, রসূলের হাদীস এবং প্রথম শতাব্দীগুলোর ইতিহাস সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করছে।
খ. ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাদের কর্মক্ষেত্র
প্রশ্নঃ ইসলাম যখন এই দাবীতেই সোচ্চার যে, সে চরম নাজুক মুহূর্তেও নারীকে একটা মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে, তখন এ যুগের ইসলামী সরকার কি তাকে পুরুষদের সমান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈততিক অধিকার দেবেনা? এ যুগে নারীকে কি পুরুষের সমান উত্তরাধিকার দেয়া যাবে? তাদেরকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা অথবা বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের পাশাপাশি কাজ করে দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা সমৃদ্ধিশালী করার অনুমতি দেয়া হবে কি? মনে করুন, ইসলামী সরকার যদি নারীদের ভোটাধিকার দেয় এবং তারা সংখ্যাগুরু ভোটে মন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হয়, তাহলে এই বিংশ শতাব্দীতেও কি তারা ইসলামী নীতি মুতাবিক সর্বোচ্চ পদে আসীন হতে পারবেনা? মহিলাদের সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করার দৃষ্টান্ত তো আজকাল ভুরি ভুরি। শ্রীলংকায় বর্তমানে মহিলা প্রধানমস্ত্রী রয়েছে। নেদারল্যান্ডের সর্বোচ্চ শাসকও একজন মহিলা। বৃটেনের রাজমুকুটও এক মহিলার মাথায় শোভা পাচ্ছে। রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে ভূপালের নবাবের বোন আবিদা সুলতানা দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমান বেগম রানা লিয়াকত আলী নেদারল্যান্ডে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, মিসেস বিজয়লক্ষ্মী পন্ডিত বৃটেনে ভারতের বর্তমান হাই কমিশনার রয়েছেন। এর আগে তিনি জাতিসংঘের সভাপতিও ছিলেন। মোগল সম্রাজ্ঞী নূর জাহান এবং ঝাঁসীর রানী রাজিয়া সুলতানার নজীরও লক্ষ্যণীয়। নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের মহিষী হযরত মহল ইংরেজদের বিরুদ্ধে লক্ষৌতে অনুষ্ঠিত যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন।
এভাবে নারীরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে যোগ্য প্রমাণ করেছেন। এই পটভূমিতে মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহ যদি আজ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হয়ে বসেন, তাহলে ইসলামী বিধানের আলোকে পাকিস্তানের ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় তা কি অনুমোদিত হবে? মহিলারা কি এখনো ডাক্তার, উকিল, ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ, সামরিক কর্মকতা, অথবা বৈমানিক হতে পারবেনা? নার্স হিসেবে মহিলারা রোগীদের কিরূপ পরিচর্যা করে সেটাও দেখার মতো। স্বয়ং ইসলামের প্রথম যুদ্ধে নারীরা যুদ্ধাহতদের পরিচর্যা করেছেন, পানি খাইয়েছেন এবং উৎসাহ যুগিয়েছেন। এমতাবস্থায় আজও কি ইসলামী রাষ্ট্রে অর্ধেক দেশবাসীকে বাড়ীর চৌহদ্দিতে বন্দিনী করে রাখা হবে?
জবাবঃ ইসলামী সরকার দুনিয়ার কোনো ব্যাপারেই ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির বিরুদ্ধে কাজ করার অধিকারী নয়। এমনকি তার ইচ্ছ করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি তার পরিচালনায় প্রকৃত ইসলামী আদর্শের নিষ্ঠাবান বিশ্বাসী ও বাস্তব অনুসারী লোকেরা নিয়োজিত থেকে থাকে। নারীর ব্যাপারে ইসলামের নীতি হলো, তারা সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে পুরুষের সমান, নৈতিক মানের বিচারেও সমান, আখিরাতে কর্মফলেও সমান, কিন্তু উভয়ের কর্মক্ষেত্র এক নয়। রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সামরিক কর্মকান্ড এবং এ জাতীয় অন্যান্য যেসব কাজ পুরুষের কর্মক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট, সেসব কর্মক্ষেত্রে নারীকে টেনে আনার অনিবার্য পরিণাম এই হবে যে আমাদের পরিবারিক জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে, যেখানে নারীর দায়িত্বই বেশী। তাছাড়া এতে নারীর ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব বর্তাবে। একদিকে তাকে তার প্রকৃতিগত দায়িত্বও পালন করতে হবে, যাতে পুরুষ কোনো ক্রমেই অংশীদার হতে পারেনা। তদুপরি পুরুষের দায়িত্বেরও অর্ধেক তার নিজের কাঁধে তুলে নিতে হবে। দ্বিগুণ দায়িত্ব পালন তো কার্যত সম্ভব নয়। কাজেই অনিবার্যভাবে প্রথম পরিণতিটাই দেখা দেবে। পাশ্চাত্য জগতের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, সেখানে তা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে এবং তাদের পারিবারিক জীবনে ধস নেমেছে। অন্যের নির্বুদ্ধিতাকে চোখ বুজে অনুকরণ করা কোনো বুদ্ধিমত্তা নয়।
ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার পুরুষের সমান হবার কোনো অবকাশ নেই। কুরআনের অকাট্য বিধান এ ব্যাপারে অন্তরায়। উভয়ের অংশ সমান হওয়া সুবিচারের পরিপন্থী। কারণ ইসলামী বিধানে পরিবারের লালন পালনের সমস্ত আর্থিক দায়দায়িত্ব পুরুষের ওপর চাপানো হয়েছে। স্ত্রীর মোহরানা এবং ভরণপোষণও তারই দায়িত্ব। অপরদিকে স্ত্রীর ওপর কোনো দায়দায়িত্বই ন্যস্ত হয়নি। এমতাবস্থায় কোন্ যুক্তিতে নারীকে পুরুষের সমান অংশীদার করা যেতে পারে।
নীতিগতভাবেই ইসলাম নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিপক্ষে। পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা চায় এমন কোনো সমাজ ব্যবস্থা অবাধ মেলামেশার পরিবেশ কামনা করেনা। পাশ্চাত্য জগতে এর শোচনীয় পরিণতি দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশের মানুষের যদি সে পরিণতি ভোগ করার সাধ জেগে থাকে তবে সানন্দে তা ভোগ করুক। তাই বলে ইসলাম যে কাজ কঠোরভাবে নিষেধ করে, তা জোরপূর্বক বৈধ প্রমাণ করার কি দরকার পড়ছে?
ইসলামে যদি যুদ্ধের সময় নারীকে আহতদের পরিচর্যার কাজে লাগানো হয়ে থাকে, তবে তার অর্থ এটা হয়না যে, স্বাভাবিক অবস্থায়ও নারীকে অফিস আদালতে, কল কারখানায়, ক্লাবে ও পার্লামেন্টে নিয়ে আসতে হবে। পুরুষের কর্মক্ষেত্রে এসে নারীরা কখনো পুরুষের মুকাবিলায় সফল হতে পারেনা। কেননা তাদেরকে এসব কাজের জন্য তৈরীই করা হয়নি। এসব কাজের জন্য যে ধরনের নৈতিক ও মানসিক গুণাবলীর প্রয়োজন, তা মূলত পুরুষের মধ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।
নারী যদি কৃত্রিমভাবে এসব গুণ কিছু কিছু অর্জনের চেষ্টাও করে তবে তার উল্টো ক্ষতি তার নিজের এবং সমাজের ওপর সমভাবে বর্তে। তার নিজের ক্ষতি এই যে, সে পুরোপুরি স্ত্রীও থাকেনা পুরোপুরি পুরুষও হতে সক্ষম হয়না। ফলে নিজের সহজাত কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়ে যায়। সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতি এই যে, যোগ্য কর্মীর বদলে সে অযোগ্য কর্মীকে কাজে নিয়োগ করে। নারীর আধা মেয়েলী ও আধা পুরুষসুলভ বৈশিষ্ট্য রাজনীতি ও অর্থনীতিকে বিপর্যস্থ করে তোলে। এ ব্যাপারে মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রাচীন মহিলার অবদান উল্লেখ করে লাভ কি? দেখতে হবে, সেখানে লক্ষ লক্ষ কর্মীর প্রয়োজন সেখানে সকল নারী মানানসই হবে কি? সম্প্রতি মিসরের সরকারী ও বাণিজ্যিক মহল অভিযোগ তুলেছে যে, সেখানে কর্মরত সর্বমোট এক লক্ষ দশ হাজার মহিলা কর্মোপযোগী প্রমাণিত হচ্ছেনা। পুরুষের তুলনায় তাদের তৎপরতা শতকরা ৫৫ ভাগের বেশী নয়। মিসরের বাণিজ্যিক মহলের সর্বব্যাপী অভিযোগ হলো, নারীদের কাছে কোনো কিছুর গোপনীয়তা রক্ষিত হয়না। পাশ্চাত্য জগতে গোয়েন্দাগিরির যেসব ঘটনা ঘটে, তাতে সাধারণত কোনো না নোনোভাবে মহিলারা জড়িত থাকে।
ইসলাম নারী শিক্ষায় বাধা দেয়না। যতো উচ্চ শিক্ষা সম্ভব তাদের দেয়ার ব্যবস্থা হওয়া উচিত, তবে কয়েকটা শর্ত আছে। প্রথমত, তারা নিজেদের বিশেষ কর্মক্ষেত্রে কাজ করার জন্য যথাযথভাবে প্রস্তুত হতে পার, এমন শিক্ষাই তাদের দিতে হবে। হুবহু পুরুষদের শিক্ষা তাদেরকে দেয়া যাবেনা। দ্বিতীয়ত, সহশিক্ষা চলবেনা। নারীদেরকে নারীদের দ্বারা পাচালিত প্রতিষ্ঠানে নারী শিক্ষিকা দ্বারাই শিক্ষা দিতে হবে। সহশিক্ষার সর্বনাশা কুফল পাশ্চাত্য জগতে এমন প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে যে, এখন যাদের জ্ঞানচক্ষু একেবারে অন্ধ হয়ে গেছে, তারা ছাড়া আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারেনা। উদাহরণ স্বরূপ, আমেরিকায় ১৭ বছর পর্যন্ত বয়সের যে মেয়েরা হাইস্কুলে পড়ে, সহশিক্ষার কারণে প্রতি বছর তাদের মধ্য থেকে গড়ে এক হাজার জন গর্ভবতী হয়ে পড়ে।[১. এটা ১৯৬২ সালের কথা। বর্তমানে এ সংখ্যা বহুগুণ বেশী। এমনকি বহুবিধ গর্ভনিরোধ আবিষ্কার করেও তারা কুমারীদের গর্ভধারণ ঠেকাতে পারছেনা। সম্পাদক]
যদিও এ পরিস্থিতি এখনো আমাদের দেশে দেখা দেয়নি তবে সহশিক্ষার কিছু কিছু কুফল আমাদের এখানেও দেখা দেতে শুরু করেছে। তৃতীয়ত, উচ্চ শিক্ষিত মহিলাদেরকে এমন প্রতিষ্ঠানাদিতে নিয়োগ করতে হবে, যা শুধুমাত্র মেয়েদের জন্যই নির্দিষ্ট। যেমন মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মহিলা হাসপাতাল ইত্যাদি।
গ. ইসলামী রাষ্ট্রে সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষা কার্যক্রম
প্রশ্নঃ ইসলামী সরকার কি নারী স্বাধীনতার ক্রমবর্দ্ধমান প্রবণতাকে শক্তি প্রয়োগে দমন করবে? বিচিত্র সাজসজ্জা, অর্ধ নগ্ন পোশাক ও নিত্যা নতুন ফ্যাশন ধারণের প্রবণতায় যেভাবে আধুনিক নারীরা মেতে উঠেছে, বিশেষত যুবতী মেয়েরা অত্যন্ত আঁটসাঁট ও মনমাতানো সুরভিত পোশাকে ভূষিত হয়ে রং বেরংগের প্রসাধনী শোভিত হয়ে এবং দেহের অঙ্গ প্রত্যক্ষ ও উচুনীচুর প্রদর্শনী করে যেভাবে প্রকাশ্যে চলাফেরা করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এবং আজকাল উঠতি বয়সের ছেলেরাও হলিউডের ছায়াছবি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যেভাবে টেডি বয় সেজে চলেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার কি প্রত্যেক মুসলিম ও অমুসলিম তরুণ তরুণীর লাগামহীন বেলেল্লাপনা রোধ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে? আইন লংঘনে তাদেরকে শাস্তি প্রদান এবং অভিভাবকদের থেকে জরিমানা আদায় করবে? এটা করলে আবার তাদের নাগরিক অধিকার কি ক্ষুন্ন হবেনা? গার্লস গাইড, মহিলা সমিতি, ওয়াই এম সি এ [খৃষ্টান যুব সমিতি] ওয়াই ডব্লিউ সি এ [খৃষ্টান যুবতী সমিতি ইত্যাকার প্রতিষ্ঠান কি ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় বরদাশত করা হবে? নারীরা কি আদালত থেকে নিজেই তালাক নিতে পারবে এবং পুরুষদের একাধিক বিয়ে নিষিদ্ধ করা হবে? ইসলামী আদালতের সামনে কি যুবক যুবতীরা কোর্ট ম্যারেজ [Civil marriage] করার অধিকারী হবে? নারীদের যুব উৎসব, খেলাধূলা, প্রদর্শনী, নাটক, নৃত্য, ছায়াছবি অথবা সুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ কিংবা বিমানবালা হওয়ার ওপর কি ইসলামী সরকার নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে? জাতীয় চরিত্র বিধ্বংসী সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অশ্লীল গান, অশ্লীল বইপুস্তক, বাজনা, নাচ ও ঢলাঢলিতে পরিপূর্ণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি কি বন্ধ করে দেয়া হবে, না এগুলোকে কল্যাণমূলক খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে?
জবাবঃ ইসলাম সমাজ সংস্কার ও জনশিক্ষার সকল কার্যক্রম কেবল আইনের ডান্ডার জোরে চালায়না। শিক্ষা, প্রচার ও জনমতের চাপ ইসলামের সংস্কার কার্যক্রমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এ সকল উপায় উপকরণ প্রয়োগের পরও যদি কোনো ত্রুটি থেকে যায়, তাহলে ইসলাম আইনগত ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণেও কুণ্ঠিত হয়না। নারীদের নগ্নতা ও বেহায়াপনা আজলেই একটা মারাত্মক ব্যাধি। কোনো যথার্থ ইসলামী সরকার এটা সহ্য করতে পারেনা। সংশোধনের অন্যান্য পন্থা প্রয়োগে যদি এ ব্যাধি দূর না হয়, কিংবা তার কিছুটা অবশিষ্ট থেকে যায়, তাহালে আইনের সাহায্যে তা রোধ করতেই হবে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এর নাম যদি নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করা হয় তাহলে জুয়াড়িদের ধর পাকড় করা এবং পকেটমারদের শাস্তি দেয়াও নাগরিক অধিকার ক্ষুন্ন করার শামিল। সামাজিক জীবনে ব্যক্তির উপর কিছু বিধনিষেধ আরোপ করতেই হয়। ব্যক্তি নিজের স্বভাবগত অসৎ প্রবনতা এবং অন্যদের কাছ থেকে শেখা অপকর্ম দ্বারা সমাজকে দূষিত করুক এজন্য তাকে বলগাহীন ছেড়ে দেয়া যেতে পারেনা।
গার্লস গাইডের স্থান ইসলামে নেই। মহিলাদের সমিতি থাকতে পারে। তবে শত এই যে, কেবল মহিলাদের মধ্যেই তার তৎপরতা সীমিত রাখতে হবে এবং মুখে কুরআনের বুলি কপচানো আর কাজে কুরআন বিরোধী দুর্নীতি চালিযে যাওলা বন্ধ করতে হবে। খৃষ্টান যুবতী সমিতি খৃষ্টান তরুণীদের জন্য থাকাতে পারে। কিন্তু কোনো মুসলিম নারীকে তাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। মুসলিম নারীরা যদি ইসলামী বিধানের আওতায় থেকে মুসলিম তরুণী সমিতি বানাতে চায় তবে বানাতে পারে।
মুসলিম নারী ইসলামী আদালতের মাধ্যমে ‘খুলা’ বিধির আওতায় বিয়ে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। বিয়ে বাতিলকরণ এবং চির বিচ্ছেদ [Judicial seperation] এর ঘোষণাও আদালত দথেকে লাভ করতে পারে। তবে শর্ত হলো, শরীয়তের বিধি মুতাবিক এ ধরনের কোনো ঘোষণা অর্জনের যোগ্যতা তার মধ্যে থাকা চাই। কিন্তু তালাক [Divorce] এর ক্ষমতা কুরআন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় শুধু পুরুষকেই দিয়েছে। পুরুষের এই ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করার অধিকার কোনো আইনের নেই। কুরআনের নাম ভাঙ্গিয়ে যদি কুরআন বিরোধী আইন প্রণয়ন করা হয় তবে সেটা ভিন্ন কথা। তালাক দেয়ার ক্ষমতা পুরুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং কোনো আদালত বা পঞ্চায়েত তাতে নাক গলাবে, এমন ধারণা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান শাতাব্দী পর্যন্ত গোটা ইসলামের ইতিহাসে অপরিচিত। এ ধারণা সরাসরি ইউরোপ থেকে আমাদের দেশে আমদানী হয়েছে। যারা এটা আমদানী করেছে তারা একটিবারও চোখ মেলে দেখেনি যে, ইউরোপে তালাকের এ আইনের পটভূমি কি ছিলো এবং সেখানে এর কি কি কুফল দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে ঘরোয়া কেলেংকারীর হাড়ি যখন ঘর থেকে বেরিয়ে হাটে বাজারে গিয়ে ভাঙ্গবে, তখন আল্লাহর আইন সংশোধন করতে যাওয়ার পরিণতি কি হয় তা মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাবে।
পুরুষদের একাধিক বিয়ের ওপর আইনগত বিধিনিষেধ আরোপ বা রোধ করার ধারণাও একটা বিদেশী পণ্য, যাকে কুরআনের ভূয়া লাইসেন্স দেখিয়ে আমদানী করা হয়েছে। এটা এসেছে এমন সমাজ থেকে, যেখানে কোনো মহিলাকে যদি বিবাহিত স্ত্রীর উপস্থিতিতে রক্ষিতা করে রাখা হয়, তাহলে সেটা শুধু সহনীয়ই নয় বরং তার অবৈধ সন্তানের অধিকার সংরক্ষণের কথাও ভাবা হয় [ফ্রান্সের উদাহরণ আমাদের সামনেই রয়েছে]। অথচ সে মহিলাকেই যদি বিয়ে করা হয় তাহলে সেটা হয়ে যায় অপরাধ। যেনো যতো কড়াকড়ি কেবল হালালের বিরুদ্ধে, হারামের বিরুদ্ধে কিছুই নয় । আমার প্রশ্ন হলো, কেউ যদি কুরআনের ক ও জানে তবে সে কি এই মূল্যবোধ [Value] গ্রহণ করতে পারে? ব্যভিচার আইনত বৈধ হবে আর বিয়ে আইনত নিষিদ্ধ হবে, এমন উদ্ভট দর্শন কি তার কাছে ন্যায়সংগত হতে পারে? এ ধরনের আইন প্রণয়নের একমাত্র পরিণাম এই হবে যে, মুসলমানদের সমাজে ব্যভিচারের ছড়াছড়ি হবে, বান্ধবী ও রক্ষিতার সংখা বাড়াবে, কেবল দ্বিতীয় স্ত্রীর অস্তিত্ব থাকবেনা। এ ধরনের সমাজ কাঠামোগত দিক দিয়ে ইসলামের আসল সমাজ থেকে অনেক দূরে এবং পাশ্চাত্য সমাজের অনেক কাছাকাছি হবে। এ ধরনের পরিস্থিতির কথা ভাবতে কারো ভালো লাগে তো লাগুক, কোনো মুসলমানের কাছে এটা ভালো লাগতে পারেনা।
কোর্ট ম্যারেজের প্রশ্ন কোনো মুসলিম নারীর বেলায় যে ওঠেইনা, তা বলাই নিষ্প্রয়োজন। এ প্রশ্ন ওঠে কেবল কোনো মুশরিক, খৃষ্টান কিংবা ইহুদী নারীকে বিয়ে করার বেলায়। এ ধরনের বিধর্মী মহিলা ইসলামী আইন মতে ইসলাম গ্রহণপূর্বক কোনো মুসলমানকে বিয়ে করতে প্রস্তুত থাকেনা। অথচ মুসলমান পুরুষ তার প্রেমে মজে গিয়ে কোনো ধর্মের কড়াকড়ি তাকে মানতে হবেনা, এই অঙ্গীকার দিয়ে তাকে বিয়ে করে। এ ধরনের কাজ কারোর যদি করতেই হয় তবে তার ইসলামের ফতুয়া নেয়ার প্রয়োজন পড়ে কিসে? ইসলাম তার অনুগত লোককে এ কাজের অনুমতি কেন দেবে? মুসলমানদের এ ধরনের বিয়ে দেয়াটা ইসলামী আদালতের দায়িত্ব হলোই বা কবে থেকে?
একটা ইসলামী সরকারও যদি যুব উৎসব [Youth festival , খেলাধূলা, নাটক, নাচগান ও সুন্দরী প্রতিযোগিতায় মুসলিম যুবতীদের টেনে আনে অথবা বিমানবালা নিয়োগ করে যাত্রীদের মনোরঞ্জনের কাজ নেয়, তাহলে আমি জানতে চাই যে, ইসলামী সরকারের প্রয়োজন কি? এসব কাজ তো কুফরী সমাজে এবং কাফির শাসিত রাষ্ট্রে সহজেই হতে পারে। সেখানে বরং এ কাজ আরো অবাধে হওয়া সম্ভব।
সিনেমা, ফিল্ম, টেলিভিশন, রেডিও ইত্যাদি আল্লাহর সৃষ্টি করা জাগতিক শক্তি ছাড়া কিছু নয়। এগুলোতে সৃষ্টিগতভাবে দোষের কিছু নেই। এগুলোর চরিত্র বিধ্বংসী ব্যবহারটাই শুধু দূষণীয়। এগুলোকে মানুষের কল্যাণার্থে ব্যবহার করা এবং নৈতিক বিচ্যুতির কাজে ব্যবহারের পথ বন্ধ করাই ইসলামী সরকারের একমাত্র কাজ।
৪. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার
ক. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক
প্রশ্নঃ আমি হিন্দু মহাসভার কর্মী। গত বছর হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। কিছুদিন হলো আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি। ইতোমধ্যে আপনার কতিপয় গ্রন্থও পড়েছি। যেমনঃ মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত ১ম ও ৩য় খন্ড, [১. এ গ্রন্থগুলো বর্তমানে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান’ গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত। -সম্পাদক] ইসলামের রাজকনৈতিক মতবাদ, ইসলামী বিপ্লবের পথ ও শান্তি পথ প্রভৃতি। এ গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এ জিনিসটা যদি আরো কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে হিন্দু মুসলমান সমস্যা এতোটা জটিল হতোনা। আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের দাওয়াত দিচ্ছেন, তার অধীনে জীবন যাপন করা গৌরবের বিষয়। তবে কতিপয় প্রশ্ন আছে। এগুলোর জবাবের জন্য চিঠিপত্র ছাড়া প্রয়োজন হলে আমি আপনার সান্নিধ্যে হাযির হবো
আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে হিন্দুদের কি মর্যাদা প্রদান করা হবে? তাদের কি আহলে কিতাবদের সমপর্যায়ের অধিকার দেয়া হবে নাকি যিম্মী ধরা হবে? আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ আপনার উক্ত গ্রন্থগুলোতেও নেই। আরবদের সিন্ধু অভিযানের ইতিহাস আমি যতোটা জানি, তাতে দেখা যায় মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং তার উত্তরসূরীরা সিন্ধুতে হিন্দুদেরকে আহলে কিতাবের অধিকার প্রদান করেছিলো। আশা করি এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পেশ করবেন। আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তাও লিখবেন। তারা দেশের প্রশাসনিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে কি? যদি না পারে তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে আপনি হিন্দুদেরকে কোন্ মর্যাদা প্রদান করতে চাচ্ছেন?
দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে হলো, কুরআনের ফৌজদারী বিধানসমূহ কি মুসলমানদের মতো হিন্দুদের উপরও কার্যকর হবে? হিন্দুদের জাতীয় আইন [Personal Law] তাদের উপর কার্যকর হবে কিনা? আমার বক্তব্য হচ্ছে হিন্দুরা তাদের উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, পালকপুত্র গ্রহণ ইত্যাদি বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী [মনু শাস্ত্রের ভিত্তিতে] জীবন যাপন করতে পারবে কি?
প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নগুলো একজন সত্য সন্ধানীর প্রশ্ন।
জবাবঃ পাত্রে প্রকাশিত আপনার ধ্যান ধ্যারণা আমার নিকট সম্মানার্হ। এটা বাস্তব যে ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে জটিল ও তিক্ত করার ব্যাপারে সেসব লোকেরাই দায়ী, যারা ন্যায় ও সত্য মূলনীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত, বংশগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত এবং জাতিগত মূলনীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছে। এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই তাই হওয়ার ছিলো যা এখন আমরা সচক্ষে দেখছি। আমরা আপনারা সকলেই এ মন্দ পরিণতির সমান অংশীদার। কল্যাণ কেউই লাভ করতে পারেনি।
আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব ক্রমনুসারে নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ
১. ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তার অবস্থা এরূপ হবেনা যে একটি জাতি আরেকটি জাতি বা অন্য জাতিগুলোর উপর শাসক হয়ে বসবে। বরঞ্চ তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই হবে যে, একটি আদর্শের ভিত্তিতে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা পরিষ্কার যে, এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেশের সেসব নাগরিকরাই বহন করতে পারবে যারা হবে উক্ত আদর্শের ধারক ও বাহক। যারা এ আদর্শের ধারক ও বাহক হবেনা, অন্তত এর উপর সন্তুষ্ট হবেনা, স্বাভাবিকভাবেই তারা এ রাষ্ট্রের যিম্মীর মর্যদা লাভ করবে। অর্থাৎ তাদের ‘নিরাপত্তার যিম্মাদারী’ সেসব লোকেরা গ্রহণ করবে যারা উক্ত মূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পরিচালক হবে।
২. আহলে কিতাব এবং সাধারণ যিম্মীদের মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য থাকবেনা। সেটি হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে এবং অন্যদের পারবেনা। কিন্তু অধিকারের ব্যাপারে আহলে কিতাব এবং অন্য যিম্মীদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকবেনা।
৩. যিম্মীদের অধিকাদরের বিস্তারিত বিবরণ তো এ চিঠিতে দেয়া সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে মৌলিক কথা হচ্ছে এই যে, যিম্মী দু’প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে সেসব যিম্মী, যারা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী হয়েছে বা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মী হচ্ছে তারা, যারা কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই যিম্মী হয়েছে। প্রথম ধরনের যিম্মীদের সংগে কৃত চুক্তি মুতাবিক আচরণ করা হবে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মীদের যিম্মী হওয়া দ্বারাই আমাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, আমরা তেমনি করে তাদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর হিফাযত করবো যেমনি করে হিফাযত করি আমাদের নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর। তাদের আইনগত অধিকার তা-ই হবে যা হবে মুসলমানদের। তাদের রক্তমূল্য তা-ই হবে যা মুসলমানদের রক্তমূল্য। নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ আযাদী তাদের থাকবে। তাদের উপাসনালয়সমূহ নিরাপদ থাকবে। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপর ইসলামী শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হবেনা।
আল্লাহ্ চাহেন তো অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক ধারাসমূহ আমরা পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবো। [১. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার’ শিরোনামে এ পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। -সম্পাদক]
৪. অমুসলিমদের “পার্সোনাল ল” তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার আবশ্যিক অংশ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিয়ে, তালাক, উত্তরাধিকার, পালকপুত্র গ্রহণ এবং অনুরূপ অন্যান্য আইন যা দেশীয় আইনের [Law of the land] সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাদের উপর প্রয়োগ করবে। কেবল সেসব ক্ষেত্রে তাদের পার্সোনাল ল’কে বরদাশত করা হবেনা যেগুলোর কুফল জনগণকে প্রভাবিত করবে। যেমন কোনো অমুসলিম জাতি যদি সূদকে বৈধ রাখতে চায় তবে ইসলামী রাষ্ট্রে সূদী লেনদেনের অনুমতি আমরা দেবোনা। কারণ এতে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হবে। কিংবা কোনো অমুসলিম জাতি যদি ব্যভিচার বৈধ রাখতে চায়, তবে এ অনুমতিও আমরা দেবোনা। তারা নিজেদের মধ্যেও এ কুকর্মের [Prostitution] ব্যবসা চালু রাখতে পারবেনা। কেননা এটা সর্ব স্বীকৃতভাবে মানব জাতির নৈতিকতা বিরোধী কাজ। আর এটা আমাদের ফৌজদারী আইনের [Criminal Law] সাথেও সাংঘর্ষিক। এ কথা স্পষ্ট যে, এটাই হবে রাষ্ট্রীয় আইন। এবার এরি ভিত্তিতে আপনি অন্যান্য বিষয়গুলো অনুমান করতে পারেন।
৫. আপনি প্রশ্ন করেছেন, অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন শৃংখলার কাজে সমান অংশীদার হতে পারবে কিনা? যেমন পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করতে পারবে কিনা? যদি না পারে, তবে আপনারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্যে সে অবস্থা মেনে নেবেন কি, ইসলামী রাষ্ট্রে যে মর্যাদা আপনারা হিন্দুদের প্রদান করবেন? আমার মতে আপনার এ প্রশ্নের ভিত্তি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এখানে আপনি একদিকে ‘আদর্শিক অজাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের’ [Idiolgical non-National State] সঠিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। অপরদিকে এ প্রশ্নের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের মানসিকতা পরিস্ফুট বলে মনে হচ্ছে।
পহেলা নম্বর জবাবেও আমি একথা বলেছি যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং তার নিরাপত্তার দিয়িত্ব কেবল সেসব লোকেরাই বহন করতে পারে, যারা সেই আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। তারাই তো এ আদর্শের মূল স্পিরিট অনুধাবন করতে পারবে। এদের থেকেই তো এ আশা করা যেতে পারে যে, পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দীনী ও ঈমানী দায়িত্ব মনে করে তারা এ রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের জীবন কুরবাণী করবে।
যারা এ আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে যদি এ রাষ্ট্র পরিচালনা এবং এর নিরাপত্তার দায়িত্বে অংশীদার করাও হয়, তবে তারা এ আদর্শিক এবং নৈতিক স্পিরিট অনুধাবন করতে সক্ষম হবেনা। সে অনুযায়ী তারা কাজ করতেও সক্ষম হবেনা। আর এ আদর্শের জন্যে তাদের সেরূপ আন্তরিকতা সৃষ্টি হবেনা যার ওপর রাষ্ট্রয় অট্রালিকার ভিত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা যদি বেসামরিক বিভাগে কাজ করে, তবে তাদের থেকে কেবল কর্মচারী সুলভ মানসিকতার প্রকাশ পাবে এবং উপার্জনের জন্যেই তারা নিজেদের সময় ও যাবতীয় যোগ্যতা বিক্রি করবে। আর যদি তাদেরকে সাসরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে তাদের অবস্থা হবে ভাড়াটে সৈনিকের [Meucenaries] মতো। তারা নৈতিক চরিত্রের সেই দাবীও পূর্ণ করতে পারবেনা ইসলামী রাষ্ট্র তার মুজাহিদদের থেকে যা আশা করে থাকে।
এজন্যে আদর্শিক ও নৈতিক কারণে ইসলামী রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীতে যিম্মীদের কোনো খিদমত গ্রহণ করেনা। পক্ষান্তরে যাবতীয় সামরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয় এবং অমুসলিম নাগরিকদের থেকে শুধু একটা প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু কর এবং সামরিক সেবা এ উভয়টাই একত্রে অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নেয়া যেতে পারেনা। যদি অমুসলিম নাগরিকরা স্বয়ং নিজেদেরকে সামরিক সেবার জন্যে পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা হবে এবং এমতাবস্থায় তাদের থেকে প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করা হবেনা।
বেসামরিক বিভাগের key post গুলো তো সামরিক বিভাগ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ এগুলো নীতি নির্ধারণী কাজের সাথে সম্পর্কিত। এগুলোতে কোনো অবস্থাতেই অমুসলিম নাগরিকদের নিয়োগ করা যেতে পারেনা। অবশ্য কর্মচারী হিসেবে তাদের খিদমত নিতে কোনো দোষ নেই। এমনি করে রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভায় [ মজলিসে শূরা] অমুসলিমদের কোনো সদস্য নেয়া হবেনা। অবশ্য অমুসলিমদের ভিন্ন কাউন্সিল বানিয়ে দেয়া হবে। এ পরিষদ তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দেখাশুনা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করবে। তাদের প্রয়োজন, অভিযোগ এবং প্রস্তাবাবলী পেশ করবে। রাষ্ট্রীয় মজলিসে শূরা [Assembly] এগুলো যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করবে।
সোজা কথা হচ্ছে এই যে, ‘ইসলামী রাষ্ট্র’ কোনো জাতির ইজারাকৃত সম্পত্তি নয়। যে কেউ তার আদর্শ গ্রহণ করবে, সে তার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে কোনো হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা কোনো শিখের। কিন্তু যে এ রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করবেনা, মুসলমানের পুত্র হোক না কেন, সে এ রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে বটে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেনা।
আপনি প্রশ্ন করেছেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে কি মুসলমানরা সে অবস্থা গ্রহণ করবে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে হিন্দুদেরকে যে পজিশন দেয়া হবে? এ প্রশ্ন আসলে মুসলিমলীগ নেতাদের কাছে করাই উচিত ছিলো। কারণ লেনদেনের কথা তো তারাই বলতে পারে। আমাদের নিকট জানতে চাইলে আমরা তো নিরেট আদর্শিক জবাবই দেবো।
যেখানে হিন্দুরা রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করবে, সেখানে আপনার মূলত দুই ধরনের রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করতে পারেনঃ
হিন্দু ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কিংবা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।
প্রথমোক্ত অবস্থায় আপনাদের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগ্রত উচিত হবেনা যে, ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুদের যতোটুকু অধিকার দেয়া হবে, আমরা “রামরাজ্যে” ও মুসলমানদেরকে ততোটুকু অধিকারই দেবো। বরঞ্চ এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মে যদি কোনো দিক নির্দেশনা থাকে তবে কোনো প্রকার রদবদল ছাড়া হুবহু সেটাই কার্যকর করুন। নিজেদের ধর্মীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে এ বিষয়ে অন্যদের অনুসরণ করা ঠিক হবেনা। আপনাদের বিধান যদি আমাদের বিধনের চেয়ে উন্নততর হয় তবে নৈতিক ময়দানে আপনারাই বিজয়ী হবেন এবং এমনও হতে পারে যে, আমাদের ইসলামী রাষ্ট্র আপনাদরে রামরাজ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি এর বিপরীত হয়, তবে দেরীতে হোক কিংবা সত্ত্বর পরিণতি এর বিপরীতেই হবে।
আর যদি শেষোক্ত নীতি গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তবে এ অবস্থায় আপনাদরেকে দু’টির যে কোনো একটি পথ গ্রহণ করতে হবে। হয়তো গণতান্ত্রিক [Democratic] নীতি হবে। নয়তো একথা পরিষ্কারভবে বলে দিতে হবে যে, এটা হিন্দু জাতির রাষ্ট্র এবং মুসলমানদেরকে এখানে বিজিত জাতি [Subject nation] হিসেবে থাকতে হবে।
এ দু’টি পন্থার যেটির ভিত্তিতে ইচ্ছা আপনার মুসলমানদের সাথে আচরণ করতে পারেন। সর্ববস্থায় আপনাদের নীতি ও আচরণ দেখে ইসলামী রাষ্ট্র তার সেসব নীতিতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন সাধন করবেনা, অমুসলমানদের ব্যাপারে কুরআন হাদীসে যেগুলো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আপনার যদি আপনাদের রাজ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযানও চালান এমনকি একটি মুসলমান শিশুকেও যদি জীবিত না রাখেন, তবু এসলামী রাষ্ট্র এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার অমুসলিম নাগরিকদের একটি কেশাগ্রও বাঁকা করবেনা। পক্ষান্তরে আপনার যদি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি ইত্যাদি পদে মুসলমান নাগরিক মনোনীত করেন, সে অবস্থায়ও ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের সে একই মর্যদা ও অধিকার প্রদান করা হবে যা কুরআন ও হাদীস নির্ধারিত করে দিয়েছে। [তরজমানুল কুরআনঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং]
উপরোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা
প্রশ্নঃ আপনার রচিত সবগুলো গ্রন্থ এবং পূর্বের চিঠিটা পড়ার পর আমি এ বিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আপনি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। আর এ ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মি এবং আহলে কিতাবের লোকদের পজিশন হবে ঠিক তেমনি, যেমনি হিন্দুদের মধ্যে আছ্যুতদের পরিজশন।
আপনি লিখেছেন, “হিন্দুদের উপাসনালয়সমূহের সংরক্ষণ করা হবে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে।” কিন্তু হিন্দুদেরকে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেয়া হবে কিনা সেকথা তো লিখেননি? আপনি আরো লিখেছেনঃ “যে কেউ এ রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করবে, সে এর পরিচালনা কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা শিখের।” মেহেরবাণী করে একথাটারও ব্যাখ্যা দিন যে, হিন্দু হিন্দু থেকেও কি আপনাদের রাষ্ট্রে নীতিমালার প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনার কাজে শরীক হতে পারবে?
আপনি লিখেছেন আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু আহলে কিতাব মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে কিনা সেকথা পরিষ্কার করেননি। এ প্রশ্নের জবাব যদি না সূচক হয়, তবে এ [Superiority complex] সম্পর্কে আরো ভালোভাবে আলোকপাত কেরবেন কি? এর যথার্থাতার জন্যে আপনি যদি ইসলামের প্রতি ঈমান আনার যিম্মাদারী নেন, তবে কি আপনি একথা মানতে প্রস্তুত আছেন যে, বর্তমানকার তথাকথিত মুসলমান আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এসব্ ইসলামী নীতিমালার মানদন্ডে টিকে যাবে? বর্তমানকালের মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, আপনি কি একথা স্বীকার করবেননা যে, খিলাফতে রাশেদার আমলে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলো? আপনি যদি একথা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হনে, তবে বলুন তো সেই ইসলামী রাষ্ট্রটি কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর টিকেছিলো? হযরত আলীর মতো বিচক্ষণ মুজাহিদের এতো বিরোধিাত কেন হয়েছিলো এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে হযরত আয়েশা পর্যন্ত কেন ছিলেন?
ইসলামী রাষ্ট্রের অভিলাষী হয়েও আপনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করছেন। কোনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছাড়াই কি আপনি আপনার হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? অবশ্যই নয়। তবে তো আপনার হুকুমতে ইলাহিয়ার জন্যে সে ভুখন্ডটিই উপযুক্ত মিঃ জিন্নাহ এবং তার সংগী সাথীরা যেখানে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। পাকিস্তান না চেয়ে সারা ভারতেই কেন আপনি হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন? এমন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে অতি উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী একদল লোক আপনি কোথা থেকে সৃষ্টি করবেন? যেখানে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের মতো তুলনাহীন মনীষীদের হতে ঐ রাষ্ট্রটি মাত্র কয়েক বছরের বেশী টিকেনি। আজ চৌদ্দশ বছর পরে এমন কোন উপযুক্ত পরিবেশ আপনি লক্ষ্য করছেন, যার ভিত্তিতে আপনার দূরদৃষ্টি হুকুমতে ইলাহিয়া বাস্তবসম্মত মনে করছে? একথা সত্য যে, আপনার পয়গাম সব মত ও পথের মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের সাথে আমার যতো মেশার সুযোগ হয়েছে, তাতে আমি দেখেছি তারা আপনার চিন্তর প্রতি সহানুভূতিশীল। তারা বলছেঃ আপনি যা কিছু বলেছেন সেটাই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু প্রত্যেকরে মনে সে একই প্রশ্ন যা আমি আপনার সামনে পেশ করলাম। অর্থাৎ খিলাফতে রাশেদার সে আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সেরূপ উচ্চমানের লোক আপনি কোথায় পাবেন? তাছাড়া সে তুলনাহীন উচ্চমানের লোকেরাই যখন ঐ রাষ্ট্রটিকে অর্ধ শতাদ্বীও সাফল্যের সাথে চালাতে পারেনি, তখন এ যুগে সে ধরনের রাষ্ট্রের চিন্তা একটি অবাস্তব আশা ছাড়া আর কি হতে পারে?
এছাড়া আরেকটি কথাও নিবেদন করতে চাই। কিছুকাল পূর্বে আমার ধারণা ছিলো, আমরা হিন্দুরা এমন একটি জাতি যদির সন্মুখে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্তমান নেই। অথচ মুসলমানদের সামষ্টিক ও সংঘবদ্ধ জীবন রয়েছে এবং তাদের সন্মুখে রয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এখন ইসলামী রাজনীতির গভীর অধ্যয়নের ফলে জানতে পারলাম যে, ওখানকার অবস্থা আমাদের চেয়েও করুণ। বাস্তব অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়। একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আমি বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ের জবাব চেয়ে পাঠাই। তাদের জবাব আমার হতে পৌছার পর আমার পূর্ব ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে। এখন আমি জানতে পারলাম, মুসলমানদের মধ্যেও কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের ব্যাপারে সাংঘাতিক মতবিরোধ রয়েছে। [প্রশ্নকারী এখানে জামায়াতে ইসলামীর সাথে সতবিরোধ রাখেন এমন কতিপয় ব্যক্তির লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন।
দেখলেন তো আপনাদের একই আকীদা বিশ্বাসের নেতাগণ কতো কঠিন মতোবিরোধ নিমজ্জিত। এসব বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে কোনো কিছু কেবল বইয়ের পৃষ্ঠায় মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা এক জিনিস আর সেটার বাস্তবায়ন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। রাজনীতি একটা বাস্তব সত্য ব্যাপার। এটাকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যেতে পারেনা। আমার এ গোটা নিবেদনকে সামনে রেখে আপনি আপনার কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাবেন কি?
জবাবঃ আপনার প্রশ্নবলীর মূল টারগেট এখনো আমার কাছে পৌছায়নি। এ কারণে যে জবাব দিচ্ছি সেগুলো থেকে আপনার আরো এমন কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আমার কাছে নেই। আপনি যদি মৌলিক বিষয় থেকে প্রশ্ন আরম্ভ করেন, অতপর শাখা প্রশাখা এবং সমসাময়িক রাজনীতির [Current politics] দিকে প্রত্যাবর্তন করেন, তবে আপনি আমার জবাবের সাথে পূর্ণ একমত না হলেও অন্ততপক্ষে আমাকে পরিষ্কারভবে বুঝতে পারবেন। এখন তো আমার মনে হয়, আমার পজিশন আপনার নিকট পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।
আপনি লিখেছেনঃ আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্র স্বপ্ন দেখছেন, তাতে “যিম্মী এবং আহলে কিতাবের পজিশন তাই হবে, যা নাকি হিন্দুদের মধ্যে অচ্ছ্যুতদের।” বাক্যটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে লেখার পরও আপনি হয়তো ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম নাগরিকদের পজিশন সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল নন। প্রথম কথা, অচ্ছ্যুতদের যে পজিশন মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায়, তার সাথে ঐ সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলামী ফিকাহ শাস্ত্রে যা যিম্মীদের প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ অস্পৃশ্যবাদের ভিত্তি হচ্ছে বংশগত তারতম্য। পক্ষান্তরে যিম্মীর ভিত্তি হচ্ছে আদর্শ ও বিশ্বাস। কোনো যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি আমাদের নেতা এবং রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারেন। কিন্তু শুদ্র তার বিশ্বাস এবং মত ও পথ পরিবর্তনের পরও কি অরুণ আশ্রমের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারে?
আপনি প্রশ্ন করেছেনঃ “কোনো হিন্দু কি হিন্দু থেকেও আপনাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে?”- আপনার এ প্রশ্ন খুবই বিস্ময়কর। সম্ভবত আপনি চিন্তু করে দেখেননি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি ঈমান আনার পর হিন্দু আর থাকবেনা, বরঞ্চ সে মুসলামান হয়ে যাবে। এ দেশের কোটি কোটি মুসলমান তো আসলে হিন্দু্রই সন্তান। ইসলামী আদর্শের প্রতি ঈমান আনার ফলেই তারা মুসলমান হয়েছে। এমনি করে ভবিষ্যতেও যেসব হিন্দুর সন্তুন এ আদর্শ গ্রহণ করবে, তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে, তখন অবশ্যি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আমদের সংগে সমান অংশীদার হবে।
‘ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাবে কি? আপনার এ প্রশ্নটি যতোটা সংক্ষিপ্ত তার জবাব ততোটা সংক্ষিপ্ত নয়। প্রচার কাজ কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হচ্ছে এই যে, কোনো গোষ্ঠী তার ভভিষ্যতে বংশধর এবং নিজ জনগণকে নিজস্ব ধর্মের শিক্ষা প্রদান করবে। সকল প্রকার যিম্মীরাই এমনটি করার অধিকার লাভ করবে। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজ ধর্মকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট পেম করবে এবং ইসলামসহ অন্য সকল ধর্মের সাথে তাদের মতভেদের কারণ জ্ঞানের যুক্তিতে পেশ করবে। এর অনুমতিও যিম্মীদের প্রদান করা হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী থাকা অবস্থায় আমরা কোনো মুসলমানকে নিজের ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেবোনা। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এ উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবে যে বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে তার নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে, আমদের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে এরূপ প্রচার কার্যর অধিকার কাউকেও প্রদান করবোনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত আমার প্রবন্ধ ইসলামে মুরতাদ হত্যার নির্দেশ’ দেখে নিন। ১. [প্রবন্ধটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে।]
মুসলমানদের জন্যে আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা বৈধ হওয়া এবং আহলে কিতাবের জন্যে মুসলিম নারীদের বিয়ে অবৈধ হওয়ার ভিত্তি এক নিগূঢ় সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষরা সাধারণত প্রভাবিত হয় কম এবং প্রভাব বিস্তার করে অধিক। আর নারীরা সাধারণত প্রভাবিত হয় বেশী এবং প্রভাব বিস্তার করে কম। একজন অমুসলিম নারী যদি কোনো মুসলমানের সংগে বিবহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তবে তার দ্বারা এ মুসলমান ব্যক্তিকে অমুসলিম বানানোর আশংকা খুবই কম, বরঞ্চ তারাই মুসলমান হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু একজন মুসলিম নারী কোনো অমুসলিম ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার অমুসলিম হয়ে যাবার আশংকাই বেশী এবং তার স্বামী ও সন্তানদের মুসলমান বানাতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্যে নিজ কন্যাদের অমুসলিমদের নিকট বিয়ে দেবার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয়নি। অবশ্য আহলে কিতাবের কোনো ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কোনো মুসলানের নিকট বিয়ে দিতে রাজী হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুরআনের যে স্থানে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সেখানে এ ধমকও হয়েছে যে, তোমরা যদি অমুসলিম স্ত্রীদের প্রেমে বিগলিত হয়ে নিজেদের দীন খুইয়ে ফেলো তবে তোমাদের সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ অনুসতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনের সময়ই কার্যকর করা যাবে। এটা কোনো সাধারণ অনুমতি নয় এবং পছন্দনীয় কাজও নয়। বরঞ্চ কোনো কোনো অবস্থায় তো একজন করতে নিষেধও করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সোসাইটিতে অমুসলিম লোকদের আনাগোনার ফলে কোনো অনাকাংখিত নৈতিক ও ধ্যান ধারণার বিকাশ ও লালন হতে না পারে।
ইসলামী রাষ্ট্র কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকেনি আপনার এ প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি যদি খুব মনোযোগের সাথে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তবে এর কারণসমুহ অনুধাবন করা আপনার জন্যে কোনো কঠিন ব্যাপার হবেনা। কোনো আদর্শের পতাকাবাহী দল যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তা তার পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে পরিচালিত হওয়া এবং টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন এর নেতৃত্ব এমন বাছাইকৃত লোকদের হাতে থাকা যারা হবে সে আদর্শের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী। আর এধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব কেবল সে অবস্থায়ই থকতে পারে, যখন সাধারণ লোকদের উপর এদের প্রভাব বজায় থাকবে এবং সাধারণ নাগরিকদের একদল বিরাট সংখ্যক লোক এতোটা শিক্ষা দীক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে, যাতে করে এ আদর্শের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা ঐসব লোকদের কথা শুনতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হয়ে যায়, যারা তাদেরকে তাদের এ নির্দিষ্ট আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো পথে চালাতে উদ্যত হয়। একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়ার জন্য ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয়ে যে নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তার বুনিয়াদী কথা এ ছিলো যে, আরব ভূখন্ডে এক প্রকার নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতুত্বে সৎ লোকদের যে ছোট দলটি তৈরী হয়েছিলো, গোটা আরববাসী তাঁর নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে খিলাফতে রাশেদার যুগে যখন দেশের পর দেশ জয় হতে লাগলো, তখন যতোটা দ্রুত ইসলামী রাজ্যের চৌহদ্দী বিস্তৃত হতে থাকলো, আদর্শিক মজবুতি ততোটা দ্রুততার সাথে এগুলো সম্ভব হয়নি। সেযুগে যেহেতু প্রচার প্রকাশনা এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণের ব্যাপক কোনো মাধ্যম ছিলোনা, যেমনটি রয়েছে বর্তমানে,সেযুগে বর্তমানকালের মতো যানবাহনও যেহেতু ছিলোনা, এসব কারণে তখন যেসব লোক দলে দলে ইসনলামী সমাজে প্রবেশ করছেলো নৈতিক, মানসিক এবং আমলী থেকে তাদের পূর্ণাংগভাবে ইসলামী আন্দোলনের ছাঁচ গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে সাধারণ মুসলমান বাসিন্দাদের মধ্যে খাঁটি ধরনের মুসলমানদের স্যখ্যা আনুপাতিক হরে একেবারে কম হয়ে যায় এবং কাঁচা ধরনের মুসলমানদের আনুপাতিক হার বিপুল সংখ্যায় বেড়ে যায়। কিন্তু আদর্শিক দিক দিয়ে মুসলমানদের ক্ষমতা, অধিকার এবং মর্যাদা খাঁটি ধরনের মুসলমানদের তুলনায় ভিন্নতর হওয়া মোটেই সম্ভব ছিলোনা। এ কারণে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর খিলাফতামলে যখন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনসমূহের ১. [১ অর্থাৎ যেসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে কোনো না কোনো জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়া।] [Reactionary Movements] ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং যারা বিশুদ্ধ ইসলামী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখতেন তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছুটে যায়। এ ঐতিহাসিক নিগূঢ় সত্যাকে উপলব্ধি করার পর খালিস ইসলামী রাষ্ট্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকে ছিলোনা সে প্রশ্ন জাগ্রত হবার কোনো অবকাশই থাকেনা।
আজো যদি আমরা সৎ লোকদের এমন একটি দলকে সুসংগটিত করতে পারি, যাদের ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা এবং সীরাত ও নৈতিক চরিত্র হবে ইসলামের বাস্তব নমুনা, তবে আমি আশা রাখি আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করে আমরা শুধু আমাদের দেশেই নয়, বরঞ্চ অন্যান্য দেশেও একটি নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এমন লোকদের একটি শক্তিশালী সংগঠন কায়েম হয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব তাদের ছাড়া অন্য কোনো পার্টির হাতে যেতে পারেনা। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা থেকে আপনি যে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঐ উজ্জ্বল অবস্থার সংগে তার তুলনা হতে পারেনা যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে।
বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী লোকেরা বাস্তব ময়দানে নেমে এলে শুধু মুসলমান জনসাধারণই নয়, বরঞ্চ হিন্দু, খৃষ্টান, পারসিক, শিখ সকলেই তাদের ভক্ত অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের ত্যাগ করে এদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যাবে। শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এমন একদল লোক তৈরী করার কাজই এখন আমি হাতে নিয়েছি। আমি আল্লাহ্র নিকট বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করছি, তিনি যেনো এ কাজে আমাকে সাহায্য করেন।
খ. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার
প্রশ্নঃ ইসলামী রাষ্ট্রে খৃষ্টান, ইহুদী, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিক প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কি মুসলমানদের মতো যাবতীয় অধিকার ভোগ করতে পারবো? আজকাল পাকিস্তান এবং অন্যান্য দেশে যেভাবে এসব সম্প্রদায়ের লোকেরা অবাধে ধর্ম প্রচারে লিপ্ত, ইসলামী রাষ্ট্রেও কি তারা তেমনিভাবে নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করতে পারবে? মুক্তিফৌজ [Salvation Army], ক্যাথড্রাল, কনভেন্ট, সেন্ট জন, সেন্ট ফ্রান্সিস ইত্যাকার ধর্মীয় অথবা আধা ধর্মীয় প্রতষ্ঠান কি আইন প্রয়োগ করে বন্ধ করে দেয়া হবে? [সম্প্রতি শ্রীলংকায় অথবা অন্যান্য দু’একটি দেশে যেমন হয়েছে।] অথবা, মুসলমান শিশুদের কি ঐসব প্রতিষ্ঠানে অবাধে আধুনিক শিক্ষা লাভের অনুমতি দেয়া হবে? এই শতাব্দীতেও এমব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়া করা সমীচীন হবে কি [বিশ্ব মানবাধিকার সনদের আলোকে বিবেচ্য?] বিশেষত তারা যখন সেনাবাহিনী ও সরকারী চাকরীতে নিয়োজিত এবং সরকারের অনুগত?
জবাবঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো সকল নাগরিক অধিাকর [Civil rights] মুসলমানদের মতোই ভোগ করবে। তাবে রাজনৈতিক অধিকারে [Political Rights] তারা মুসলমানদের সমকক্ষ হতে পারেনা। কারণ ইসলামে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন চালানো মুসলমানদের দায়িত্ব। মুসলমানদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেখানেই তারা শাসন ক্ষমতার অধিকারী হবে, সেখানে যেনো তারা কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা মুতাবিক সরকারী প্রশাসন চালায়। যেহেতু অমুসলিমরা কুরআন ও সুন্নহর শিক্ষাও মানেনা, তার প্রেরণা ও চেতনা অনুসারে বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করতে ও সক্ষম নয়, তাই তাদেরকে এ দায়িত্বে অংশীদার করা চলেনা। তবে প্রশাসনে এমন পদ তাদেরকে দেয়া যেতে পারে, না নীতিনির্ধারক পদ নয়। এ ব্যাপারে অমুসলিম সরকারগুলোর আচরণ হয়ে তাকে মুনাফিকী ও ভন্ডামীতে পরিপূর্ণ। কিন্তু ইসলামী সরকারের আচরণ হয়ে থাকে নিরেট সততার প্রতীক। মুসলমানরা তাদের এ নীতি খোলাখুলিভাবে জানিয়ে দেয়া এবং এর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের বেলায় আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহির অনুভূতি নিয়ে অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সর্বোচ্চ উদারতা ও ভদ্রতার আচরণ করে থাকে। আর অমুসলিমার বাহ্যত লিখিতভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে [National minorities] যাবতীয় অধিকার প্রদান করে বটে, কিন্তু বাস্তবে মানবিক অধিকারও দেয়না। এতে যদি কারো সংশয় থাকে, তবে সে যেনো আমেরিকায় নিগ্রোদের সাথে, রাশিয়ায় অকম্যুনিষ্টদের সাথে এবং চীন ও ভারতের মুসলমানদের সাথে কি আচরণ করা হচ্ছে তা দেখে নেয়। অনর্থক অন্যদের সামনে লজ্জাবোধ করে আমাদের নিজস্ব নীতি খোলাখুলি বর্ণনা করা এবং সে অনুসারে দ্বিধাহীন চিত্তে কাজ না করার কি কারণ থকতে পারে তা আমার বুঝে আসেনা।
অমুসলিমদের ধর্মপ্রচারে ব্যাপারটা অবশ্য আলাদা। এটা আমাদের ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, আমরা যদি একেবারে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত না হই, তাহলে আমাদের দেশে অমুসলিমদের ধর্মপ্রচারের অনুসতি দিয়ে শক্তিশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায় গড়ে উঠতে দেয়ার মতো নির্বুদ্ধিতার কাজ করা সংগত হবেনা। বিদেমী পুঁজির দুধ কলা খেয়ে ও বিদেশী সরকারে আস্কারা পেয়ে সংখ্যালঘুরা লালিত পালিত হোক এবং শক্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি করে ফুলে ফেঁপে উঠে তুরস্কের মতো সংখ্যালঘু খৃষ্টানরা আমাদেরকেও সংকটে ফেলে দিক, এটা কিছুতেই হতে দেয়া হবেনা।
খৃষ্টান মিশনারীদের এখানে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল চালু রেখে মুসলমানদের ঈমান খরীদ করার এবং মুসলমানদের নতুন বংশধরগণকে আপন জাতীয় ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করার [De-nationalise] অবাধ অনুমতি দেয়াও আমার মতে জাতীয় আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শাসকরা এ ব্যাপারে চরম অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। নিকটবর্তী উপকারিতা তো তাদের বেশ চোখে পড়ে কিন্তু সুদূরপ্রসারী কুফল তারা দেখতে পায়না।
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কাছে থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয় কেবল তখনই, যখন তারা বিজিত হয় অথবা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে জিযিয়া দেয়ার সুস্পষ্ট শর্ত অনুসারে তাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব দেয়া হয়। পাকিস্তানে যেহেতু এই দুই অবস্থার কোনোটাই দেখা দেয়নি, তাই এখানে অমুসলিমদের ওপর জিযিয়া আরোপ করা শরীয়তের বিধান অনুসারে জরুরী নয় বলে আমি মনে করি। [তরজমানুল কুরআন, অক্টোবর ১৯৬১]
৫. আরো কয়েকটি বিষয়
ক. সংবিধান ব্যাখ্যার অধিকার
প্রশ্নঃ সংবিধান ব্যাখ্যার অধিকার কার থাকা উচিত? আইনসভার না আদালতের? আমাদের দেশে পূর্বে এ অধিকার আদালতের ছিলো, বর্তমান সংবিধানে এ অধিকার আদালতের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আইসভাবে দেয়া হয়েছে। এতে আপত্তি উঠেছে যে, বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ অধিকার বিচার বিভাগের হতে বহাল রাখার দাবী উঠেছে। এ সম্পর্কে এক ভদ্রলোক বলেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে আদালতের কাজ ছিলো শুধু বিরোধ মীমাংসা করা। আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অধিকার আদালতের ছিলোনা। আইন শুদ্ধ না ভুল, সেটা বলার এখতিয়ার আদালতের ছিলোনা। এই বক্তব্য কতোখানি সঠিক? ১.উল্লেখ্য যে, পরবর্তী সময়ে সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং সংবিধানের ব্যাখ্যার অধিকার বিচার বিভাগকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।]
জবাবঃ বর্তমান যুগের আইনগত ও সাংবিধানিক সমস্যাবলীতে ইসলামের প্রাথমিক যুগের নযীর প্রয়োগ করার প্রবণতা আজকাল খুবই বেড়ে গেছে। কিন্তু যারা এ ধরনের যুক্তি প্রদর্শন করেন, তারা তৎকালীন সমাজের সাথে এ যুগের সমাজের এবং তৎকালীন শাসকদের সাথে এ যুগের শাসকদের আকাশ পাতাল ব্যবধানের দিকটা লক্ষ্য করেননা।
খিলাফতে রাশেদার যুগে খলীফা স্বয়ং কুরআন ও সুন্নাহ সম্পর্কে একজন মস্ত বড় আলেম হতেন। তাঁর ব্যক্তিত্বে খোদাভীতির প্রাবল্যের কারণে জনগণ তাঁর প্রতি আস্থাশীল থাকতো যে, জীবনের কোনো ব্যাপারে তিনি যদি নিজস্ব চিন্তা তাঁর প্রতি আস্থাশীল থাকতো যে, জীবনের কোনো ব্যাপারে তিনি যদি নিজস্ব চিন্তা গবেষণা ও বিচার বিবেচনার [ইজতিহাদ] ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নেন, তবে তা কখনো ইসলামের আদর্শ বিরোধী বিদ্ধান্ত হবেনা। তখন মজলিসে শূরার [পরামর্শ পরিষদ] সদস্যদের সকলেই ব্যতিক্রমহীনভাবে ইসলামের সর্বোত্তম পারদর্শীও জ্ঞানী ব্যক্তি বিবেচিত হওয়ার কারণেই সদস্যপদের মর্যাদা লাভ করতেন। ইসলাম সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী নয়, স্বার্থপ্রণোদিত হয়ে ইসলামকে বিবৃত করে, অথবা তার দ্বারা কোনো বিদয়াতী কর্যকলাপ কিংবা অনৈসলামিক প্রবণতার আশংকা থাকে, এমন কোনো ব্যক্তি তাদের দলে স্থান পেতোনা। সমাজের বিপুল সংখ্যাগুরু অংশের জীবনে কখন ইসলামী ভাবধারার ছাপ বিদ্যমান ছিলো। সেখানে এমন পরিবেশ বিরাজ করতো যে, ইসলামরে বিধান ও তার আদর্শগত চেতনার পরিপন্থী কোনো নির্দেশ বা আইনবিধি জারী করার ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যই কেউ দেখতে পারতোনা। তৎকালীন আদালতের মানও ছিলো একই রকম উন্নত। বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হতেন তারাই, যারা কুরআন ও সুন্নহ্তে গভীর দক্ষতার অধিকারী হতেন, সর্বোচ্চ মানের মুত্তাকী ও পরগেজগার হতেন এবং আল্লাহ্র আইনকে চুল পরিমাণও লংঘন করতে প্রস্তুত ছিলেননা। এ পরিস্থিতিতে আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে সম্পর্কের ধরন যেমন হওয়ার কথা, তেমনই ছিলো। সকল বিচারক মামলার বিচার সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ অনুসারে করতেন, আর যেসব ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নহতে সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় ইজতিহাদ করার প্রয়োজন দেখা দিতো, সে ক্ষেত্রে সাধারণত নিজেরাই ইজতিহাদ করতেন। যেখানে বিচার্য বিষয় এমন হতো যে, বিচারকের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ দ্বারা ফায়সালা করার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি, সেটা ফলীফার মজলিসে শূরা কর্তৃক নির্ণীয় হওয়ার পয়োজন অনুভূত হতো, সে ক্ষেত্রে সামষ্টিক উজতিহাদ দ্বারা ইসলামের মূলনীতিসমূহের সাথে অধিকতর সঙ্গতিশীল একটা বিধি তৈরী করা হতো। এরূপ কর্মপদ্ধতি যেখানে অনুসৃত হতো, সেখানে বিচারকদের মজলিসে শূরার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা বা রদবদলের অধিকার হতেন তবে কেবল এজন্যই হতো পারতেন যে, সে আইন আসল সংবিধানের [অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নহর বিরোধী]। অথচ যে ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে, সে ব্যাপারে তখন আদৌ আইন প্রণয়ন করাই হতোনা। আইন প্রণয়নের প্রয়োজন শুধু সে ক্ষেত্রেই দেখা দিতো, যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ না থাকা হেতু কুরআন ও সুন্নহর সাধারণ নীতিমালা ও ভাবধারার ভিত্তিতে চিন্তা গবেষণা চালিয়ে উপযুক্ত নীতি ও বিধি উদ্ভাবন [অর্থাৎ ইজতিহাদ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিতো। আর এটা সুবিদিত যে, এরূপ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ইজতিহাদের ইজতিহাদ এই সামষ্টিক ইজতিহাদ থেকে ভিন্ন তর হলেও তাতে কিছু আসে যায়না।
সেকালের এই সাংবিধানিক দৃষ্টান্ত আজকের পরিস্থিতিতে কোনোক্রমেই লাগসই হতে পারেনা। আজকের শসকবৃন্দের এবং আইনসভার সদস্যদের যেমন খুলাফায়ে রাশেদীন ও তাদের মজলিশে শূরার সদস্যদের সাথে কোনো তুলনা হয়না তেমনি আজকের বিচারকরাও তৎকালীন বিচারকদের মতো নয়। আর আজকের আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াতেও তৎকালীন আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের শর্তবলী ও মান অনুসৃত হয়না। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রহণযোগ্য কর্মপন্থা হলো, আমাদের সাংবিধানিক বিধিমালা সমসাময়িক পরিস্থিতির আলোকে প্রণয়ন করতে হবে। খিলাফতে রাশেদার দৃষ্টান্তসমূহ প্রয়াগ করার আগে তৎকালীন সে পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে, যার পটভূমিতে ঐ দৃষ্টন্তগুলোর কার্যত উদ্ভাব হয়েছিলো। বর্তমান পরিস্থিতিতে শরীয়ত সংক্রান্ত ব্যাপারে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ভার প্রশানকেরও অর্পণ করা যায়না, আইনসভার হতেও ন্যস্ত করা যায়না, বিচার বিভাগ কিংবা উপদেষ্টা পরিষদের হতেও ছেড়ে দেয়া যায়না। এসব প্রতিষ্ঠানের একটিও এমন নয় যে, শরীয়ত সংক্রন্ত বিষয়ে তাদের ওপর মুসলমান জনগণ পূর্ণমাত্রয় আস্থা করতে পারে। যে ইজতিহাদ শরীয়তকে বিকৃত করে, তা থেকে নিরাপদে থাকার জন্য মুসলিম জনমতকে জাগ্রত করা এবং সামগ্রিকভাবে মুসলিম জাতিকে এ ধরনের যে কোনো ইজতিহাদের প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যেসব শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে শরীয়ত ইতিবাচক ও নেতিবাচক কোনো বিধান দেয়না, সে ক্ষেত্রে আইনসভাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া বর্তমান অবস্থায় নিরাপদ নয়। এজন্য একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে সাংবিধানিক সীমা লংখন করছে কিনা, সেটা পর্যবেক্ষণ করাই ঐ নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানটির কাজ। বিচার বিভাগ ছাড়া আর কোনো প্রতিষ্ঠান যে এ দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়, সেকথা বলাই বাহুল্য [তরজমানুল কুরআন ডিসেম্বব ১৯৬১]
খ. ইসলাম ও গণতন্ত্র
প্রশ্নঃ গণতন্ত্রকে আজকাল উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্থা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কেও এরূপ ধারণই পোষণ করা হয়ে থাকে যে, তা বহুলাংশে গণতান্ত্রিক রীতিসম্মন। কিন্তু আমার দৃষ্টিতে গণতন্ত্রে বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে। আমি জানতে চাই যে, ইসলাম ঐ ত্রুটিগুলো কিভাবে শুধরাতে পারে। ত্রুটিগুলো হলোঃ
১. অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার মতো গণতন্ত্রেও শাসন ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কার্যত গুটিকয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত করা হয় এবং বিবেক বেচা কেনার প্রতিযোগিতায় পর্যবসিত হয়। এভাবে ধনিক শ্রেণীর শাসন [Plutocracy বা Oligrachy] প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপক্রম হয়। এ সমস্যার সমাধানের উপায় কি?
২. জনসাধারণের রকমারি ও পরস্পরবিরোধী স্বার্থ একই সাথে রক্ষা করা মনস্তাত্ত্বিকভাবে খুবই দুরূহ কাজ। সর্বস্তরের মানুষের এ দায়িত্ব পালনে গণতন্ত্র কিভাবে সফল হতে পারে?
৩. জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ নিরক্ষর, সরল অনুভূতিহীন এবং ব্যক্তিপূজারী। স্বার্থপর লোকেরা অনবরত তাদেরকে বিপথগামী করে থাকে। এমতাবস্থায় প্রতিনিধিত্বমূলক ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পক্ষে সাফল্যের সাথে দায়িত্ব পালন করা খুবই কঠিন।
৪.জনগণের ভোটে যেসব নির্বাচিত ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তার সদস্য সংখ্যা খুব বেশী হয়ে থাকে। তাদের পারস্পরিক বিতর্ক ও পরামর্শক্রমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। খুবই জটিল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।
আপনার ধারণামতে ইসলাম স্বীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এসব ত্রুটি থেকে কিভাবে রক্ষা করবে, এটা বুঝতে আমাকে সাহায্য করবেন।
জবাবঃ আপনি গণতন্ত্রের যে ক’টি ত্রুটি তুলে ধরেছেন, তার সব কয়টিই যথার্থ। কিন্তু এ ব্যাপারে চূড়ান্ত মত স্থির করার আগে আরো কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা জরুরী।
পয়লা বিবেচ্য বিষয় হলো, মানুষের সামষ্টিক কর্মকন্ড পরিচানার জন্য নীতিগতভবে কোন্ পদ্ধতিটা সঠিক? এর দু’টো পদ্ধতি হতে পারে। প্রথমটা এই যে, যাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে হবে তাদের ইচ্ছা ও পরামর্শক্রমে কর্মকান্ড পারচালনা করবে এবং যতক্ষণ তাদের আস্থা ঐ পরিচালকের ওপর থাকবে, কেবল ততক্ষণই সে পরিচালক বা শস ক হিসেবে বহাল থাকবে। দ্বিতিয় পদ্ধতি হলো, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেই শাসক বা পরিচালক হয়ে জেঁকে বসবে, নিজের ইচ্ছা মতোই সব কার্যনির্বাহ ও পদচ্যুতিতে তাদের বলার বা করার কিছু থাকবেনা। এ দু’টো পদ্ধতির মধ্যে যাওয়ার পথ হতে পারে সেটাই হওয়ার উচিত একমাত্র আলোচ্য বিষয়।
দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো, গণতান্ত্রের মৌল আদর্শ বাস্তাবায়নের যে রকমারি কর্মপন্থা বিভিন্ন যুগে অবলম্বন করা হয়েছে অথবা উদ্ভাবন করা হয়েছে,তার বিশদ বিবরণে না গিয়েও সেগুলোকে যদি শুধু এ দিক দিয়ে বিচার করা হয় যে, গণতেন্ত্রের মৌল আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে পূরণ করতে তা কতোখানি সফল হলেছে, তাহলে তার ব্যর্থতার তিনটি প্রধান করাণ দৃষ্টিগোচর হয়।
প্রথম কারণটি হলো, জনগণকে সার্বভৌকম [Sovereign] ও সর্বাত্মক শাসক ধরে নেয়া হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে গণতন্ত্রেকে স্বেচ্ছাচার ও স্বৈরাচারে পরিণত কারার চেষ্টা করা হয়েছে। অথচ স্বয়ং মানুষ যখন এ বিশ্ব চরাচরে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, তখন বহু মানুষের সমষ্টি জনগণ কেমন করে সার্বভৌমতের অধিকারী হতে পারে? এ কারণেই স্বেচ্ছাচার সর্বস্ব গণতন্ত্র শেষ পর্যন্ত সে বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ায়, তা জনগণের ওপর কতিপয় ব্যক্তির বাস্তব সার্বভৌমত্ব ছাড়া আর কিছু নয়। ইসলাম শুরুতেই এ গলদ শুধরে দেয়। সে গণতন্ত্রকে এমন একটা মৌলিক আইনের অধীন করে দেয়, যা বিশ্ব জাহানের আসল সার্বভৌম শসকের রচিত। জনগণ এবং তাদের শাসকবৃন্দ এ আইনের আনুগত্য করতে বাধ্য। এজন্য যে স্বৈরাচার শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা আদৌ সৃষ্টি হওয়ারই অবকাশ পায়না।
দ্বিতীয়ত, জনগণের মধ্যে যতক্ষণ গণতন্ত্রের দায়িত্ব বহনের উপযুক্ত চেতনা ও চরিত্র সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে চলতেই পারেনা। ইসলাম এজন্যই এক একজন করে প্রত্যেক সাধারণ মুসলমানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ওপর জোর দেয়। ইসলাম কামনা করে যে, প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে ঈমানদারী, দায়িত্ব সচেতনতা এবং ইসলামের মৌলিক বিধানের আনুগত্য ও অনুসরণের দৃঢ় সংকল্প জন্ম নিক। এ জিনিসটা যতো কম হবে, গণতন্ত্রের সাফল্যের সম্ভাবনা ততোই কম হবে। আর এটা হতো বেশী হবে, তার সাফল্যের সম্ভাবনা ততোই উজ্জ্বল হবে।
তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের সফলতা নির্ভর করে সদাজাগ্রত ও অনমরীয় জনমতের ওপর। সমাজ যখন সৎ লোকদের দ্বারা গঠিত হবে, এই সৎ লোকদেরকে সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ কর হবে এবং সে সংঘবদ্ধ সমাজ এতাটা শক্তিশালী হবে যে, অসততা ও অসৎ লোক সেখানে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পাবেনা এবং শুধুমাত্র সততা ও সৎ লোকই উন্নতি ও বিকাশ লভের সুযোগ পাবে। ইসলাম এজন্য আমাদেরকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে দিয়েছে।
উল্লিখিত তিনটি উপকরণ যদি সংগৃহীত হয়ে যায় তাহলে গণতন্ত্রের বাস্তবায়নকারী সংস্থার রূপকাঠামো, যেরকমই হোক না কেন, গণতন্ত্র সাফল্যের সাথে চলতে পারবে। আর এই সংস্থার কোথাও কোনো অসুবিধা অনুভূত হলে তা সংশোধন করে আরো ভালো সংস্থা গড়ে তোলাও অধিকতর উন্নতি ও পরিশুদ্ধি লাভের জন্য যথেষ্ট। অভিজ্ঞতার সাহায্যে ক্রমান্বয়ে একটা ত্রুটিপূর্ণ অবকাঠামো উৎকৃষ্টতর ও পূর্ণাংগ হয়ে গড়ে উঠতে থাকবে। [তরজমানুল কুরআন, জুন ১৯৬৩]
গ. রাষ্ট্রপ্রধানের ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা
প্রশ্নঃ কিছুদিন যাবত পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই মর্মে প্রস্তাব পেশ করা হচ্ছে যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টেকে ‘খলিফাতুল মুসলিমীন’ বা ‘আমীরুল মুমিনীন’ সূচক সন্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা হোক। এই প্রস্তাবকে আরো জোরদার করার উদ্দেশ্যে একথাও বলা হচ্ছে যে, রাস্ট্রপ্রধানকে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমাতও দেয়া উচিত। কেননা হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা অস্বীকার করেছিলো এবং যারা নবূয়্যতের দাবী করেছিলো, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়ে তিনি সাহাবায়ে কিরামের অভিমত রদ করেন। এই যুক্তির বলে ভোটোর মতো একটা ধান্ধাবাজীপূর্ণ আইনকে শরীয়তের ভিত্তিতে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।
এ পরিস্থিতির আলোকে আপনার কাছে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি। আশা করি আপনি সুস্পষ্ট জবাব দিয়ে আশ্বস্ত করবেন।
১. হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কি আজকের যুগের প্রচলিত অর্থের ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন?
২. যদি তাই করে থাকেন তবে এজন্য তাঁর কাছে কোনো শরীয়তসম্মত যুক্তিপ্রমাণ ছিলো কি?
জবাবঃ খুলাফায়ে রাশেদীনের শাসন ব্যবস্থা এবং বর্তমান যুগের রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসন ব্যবস্থায় আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। যারা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে নিরেট অজ্ঞ, তারা ছাড়া আর কেউ এ দু’টোকে এক বলেতে পারেনা। আমি এ প্রন্থে সপ্তম অধ্যায়ের তয় অনুচ্ছেদে এ পার্থক্য সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছি। সেটি পড়ে দেখবেন। ঐ আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যবে যে, খিলাফতে রাশেদার শাসন ব্যবস্থায় যে জিনিসটাকে “ভেটো” ক্ষমতা বলে অভিহিত করা হয়, তা বর্তমান যুগের সাংবিধানিক পরিভাষা থেকে ভিন্ন জিনিস ছিলো। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর মাত্র দু’টো সিদ্ধান্তকে এ ক্ষেত্রে যুক্তির ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো হচ্ছে। একটি হলো, উসামার নেতৃত্বে যে সেনাদলকে মিথ্য নবূ্য়্যতের দাবীদারদেরকে দমন করার জন্য অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন, কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের দরুণ অভিযান স্থগিত ছিলো, সেটা পুনরায় প্রেরণের সিদ্ধান্ত। দ্বিতিয়টি হলো, যারা ইসলাম পরিত্যাগ করা ঘোষণ দিয়েছিলো, তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ। এই দু’টো ব্যাপারে হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লহু তায়ালা আনহু শুধু নিজের ব্যক্তি মতে সিদ্ধন্ত নেননি। বরং নিজের মতের সপক্ষে কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করেছিলেন। উসামার সেনাদল সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিলো, যে নিয়েছিলেন, সেটিকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলীফা হিসেবে সমাধান করাই আমার দায়িত্ব। সে ফায়সালা পরিবর্তনের অধিকার আমার নেই। ইসলাম পরিত্যাগকারীদের ব্যাপারে তাঁর যুক্তি ছিলো, যেব্যক্তি বা গোষ্ঠী নামায ও যকাতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং বলে যে, আমি নামায পড়বো কিন্তু যাকাত দেবোনা, সে ইসলাম বহির্ভূত, তাকে মুসলমান মনে করাই ভুল। সুতরং যারা বলেঃ ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়া লোকদের বিরুদ্ধে কিভাবে তরবারি উত্তোলন করা যাবে? তাদরে বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই যুক্তির কারণেই সকল সাহাবী তাঁর সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। এটা যদি ‘ভেটো’ হয়ে থাকে তবে তা আল্লাহ্র কিতাব ও রসূলের সুন্নাহর ‘ভেটো’ রাষ্ট্র প্রধানের ভেটো নয়।
আসলে এটাকে ভেটো বলাই ভুল। কেননা হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুর যুক্তি মেনে নেয়ার পর ভিন্নমত পোষণকারী সাহাবায়ে কিরাম খলীফার মতকেই [তরজমানুল কুরআন, নভেম্বর ১৯৬৩]
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি