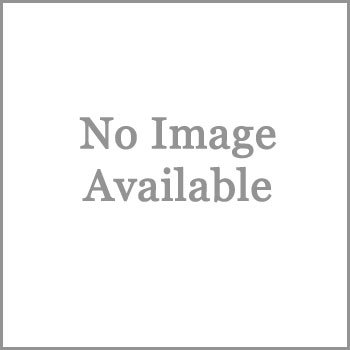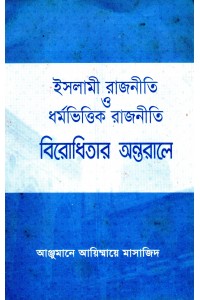প্রথম খন্ড
ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন
ধর্ম ও রাজনীতি
ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ
কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন
খিলাফতের তাৎপর্য
জাতীয়তার ইসলামী ধারণা
প্রথম অধ্যায়
ধর্ম ও রাজনীতি
১. ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি
২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন?
৩. ইসলাম ও কর্তৃত্ব
৪. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক কারার ভ্রান্ত মতবাদ
৫. ধর্ম রাজনীতিকে পৃথক করার মতবাদ খন্ডন
ইসলামের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে অধ্যয়নকালে আমাদের সামনে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন দেখা দেয়, তাহলো ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কি ধারণা পেশ করে আর রাজনীতি, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব এবং সামাজিক জীবনের সামগ্রিক বিষয়েই বা ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি? ধর্ম সম্পর্কে সীমাবদ্ধ ধারণার কারণে ধর্মই অধিকতর বিভ্রান্তিকর ধারণার শিকার হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক মহলই নয়, ধর্মীয় মহলও এ বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। তাই আমরা এ গ্রন্থের সূচনাই করতে চাই ইসলামের রাজনৈতিক দর্শনের আলোচনা মধ্য দিয়ে।
আধুনিক কালের ইসলামী চিন্তা গবেষণার ময়দানে এ বিশেষ অবদান কেবল মাওলানা মাওদূদীরই যে, তিনি ধর্ম ও রাজনীতির পার্থক্যকরণের উপর হেনেছেন এক কার্যকর আঘাত। আয়নার মতো স্বচ্ছ করে পেশ করেছেন ইসলামের পূর্ণাংগ ও বৈপ্লবিক রূপরেখা। এ ধ্যায়টিকে আমরা সজ্জিত করেছি। তাঁর কয়েকটি অমূল্য রচনার সমন্বয়ে। বিভিন্ন সময়ে রচিত এ প্রবন্ধগুলোকে এখানে আমরা মুক্তার মালার মতো গেঁথে দিয়েছি বাস্তব পরস্পরায়।– সংকলন।
ধর্ম ও রাজনীতি [এ অংশ সংকলন করা হয়েছে উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান গ্রন্থ থেকে।]
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়্যত লাভের পূর্বে পৃথিবীর ধর্ম সম্পর্কে সাধারণ ধারণা এই ছিলো যে, জীবনের অনেকগুলো দিক ও বিভাগের মধ্যে এটাও একটা বিভাগ। অন্য কথায়, এটা মানুষের পার্থিপ জীবনের একটা লেজুড় বিশেষ, যা পরপারের জীবনে ত্রাণ লাভের জন্যে একটা সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহৃত হবে। মানুষ ও তার উপাস্যের মধ্যে যে সম্পর্ক, ধর্মের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে কেবলমাত্র সেই সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যে ব্যক্তি মুক্তির উচ্চতর মর্যাদা প্রত্যাশা করে, তার জন্যে পার্থিব জীবনের অন্য সকল বিভাগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে কেবল এ বিভাগটির কাজে নিয়োজিত ও নিবেদিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এতো উচ্চ মর্যাদা যার কাম্য নয়, বরং শুধুমাত্র মুক্তিলাভ করাকেই সে যথেষ্ট মনে করে এবং সেই সাথে এটাও তার প্রত্যাশা যে তার মাবুদ তার উপর অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করতে থাকুক এবং তাকে পার্থিব জীবনের সমস্ত তৎপরতায় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি দান করুক, সে ব্যক্তির জন্যে তার পার্থিব জীবনের সাথে ধর্মের এ লেজুড়টাও জুড়ে রাখা যথেষ্ট। দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম যেমন চলছে তেমনই চলবে, সেই সাথে কিছু কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার মাধ্যমে মাবুদকেও খুশী করা হতে থাকবে। নিজের সত্তার সাথে, সমাজের অন্যান্য লোকদের সাথে এবং আশপাশের সমগ্র জগতের সাথে মানুষের যে সম্পর্ক, তা এক জিনিস। আর আপন মা’বুদের সাথে তার যে সম্পর্ক, সেটা ভিন্ন আরেক জিনিস। এ দু’সম্পর্কের মধ্যে কোনো পারস্পরিক যোগসূত্র নেই। এ ছিলো জাহেলিয়াতের ধ্যান ধারণা। এ ধ্যান ধারনার ভিত্তিতে কোনো মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারত গড়ে ওঠা সম্ভব ছিলোনা। সভ্যতা ও সংস্কৃতি বলতে মানুষের গোটা জীবনকেই বুঝায়। যে জিনিস মানব জীবনের জন্যে নিছক লেজুড় বিশেষ, তার ওপর যে সমগ্র জীবনের ইমারত কিছুতেই তৈরী হতে পারেনা, সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। এ কারনেই দুনিয়ার সর্বত্র ধর্ম এবং সভ্যতা কৃষ্টি সব সময়ই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। যদিও এ উভয় জিনিস পরস্পরের ওপর কমবেশী প্রভাব বিস্তার করেছে ঠিকই, কিন্তু সেটা ছিলো একান্তই পরস্পর বিরোধী কতিপয় বস্তুর একত্র অবস্থানের ফলে সৃষ্টি প্রভাবের মতই। তাই এ প্রভাব কোথাও এ দুটির কোনোটির জন্যই উপকারী ও ফলপ্রসূ হয়ে দেখা দেয়নি। ধর্ম যখন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে প্রভাবান্বিত করেছে, তখন তাতে ঢুকিয়ে দিয়েছে বৈরাগ্যবাদ, বস্তুগত সম্পর্ক ও সংযোগের প্রতি ঘৃণা, পার্থিব স্বাদ সম্ভোগে বিতৃষ্ণা ও অনীহা, জাগতিক উপায় ও উপকরণের সাথে সম্পর্কহীনতা, মানবীয় সম্পর্ক ও বন্ধনসমূহের ব্যাপারে ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, পারস্পরিক বিদ্বেষ ও বৈষম্য এবং সংকীর্ণতা ও গোড়ামীর উপাদান। এ প্রভাব কোনো অর্থেই উন্নতি ও প্রগতির সহায়ক ও পোষাক ছিলোনা। বরং পার্থিব অগ্রগতির পথে তা ছিলো এক বিরাট প্রতিবন্ধক। পক্ষান্তরে সে সভ্যতা ও সংস্কৃতি যা ছিলো আগাগোড়াই বস্তুবাদ ও স্বেচ্ছাচার ভিত্তিক, তা যখনই ধর্মের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তাকে দুষিত ও নোংরা করে ছেড়েছে। প্রবৃত্তি পূজার যাবতীয় পংকিলতা আবীলতা ও কদর্জতা দিয়ে তাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। প্রবৃত্তির প্রতিটি নিকৃষ্ট ও জঘণ্য কামনা বাসানাকে সে ধর্মীয় পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যের পোশাক পরিয়ে দিয়ে সর্বদা এরূপ স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেছে যেনো নিজের বিবেকও তাকে দংশন না করতে পারে এবং অন্য কেউও তার বিরোধিতা করতে সক্ষম না হয়। এরূপ প্রভাব বিস্তারের কারণেই আমরা কোনো কোনো ধর্মের আনুষ্ঠানিক উপাসনাতে পর্যন্ত ভোগাসক্তি ও নির্লজ্জতার এমনসব আচরণ দেখতে পাই। যাকে ধর্মীয় অংগনের বাইরে স্বয়ং সেইসব ধর্মের অনুসারীরাও চরিত্রহীনতার কাজ বলে আখ্যায়িত না করে পারেনা।
ধর্ম ও সভ্যতার এ পারস্পরিক প্রভাব আদান প্রদানকে উপেক্ষা করলেও যে বাস্তব সত্যটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে, তা হলো, পৃথিবীর সর্বত্র সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইমারত ধর্মহীনতার ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত।
প্রকৃত ধর্মপারায়ন লোকেরা আপন মুক্তির দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন থেকেছে। আর দুনিয়াদাররা দুনিয়াবী কর্মকান্ডকে আপন প্রবৃত্তির কামনা ও বাসনা এবং আপন আপন অসম্পূর্ণ ও অপরিপক্ক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতার অধীনে সম্পন্ন করেছে। যদিও তাদের সে অভিজ্ঞতাকে প্রত্যেক যুগেই পরিপক্ক ও নির্ভূল বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এবং সে যুগে অতিক্রান্ত হলেই তা অপরিপক্ক ও ত্রুটিপূর্ণ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। দুনিয়াদাররা দুনিয়াবী কর্মকান্ড স্বেচ্ছাচারীভাবে সম্পন্ন করলেও প্রয়োজন মনে করলে সেই সাথে আপন প্রভুকে খুশী করার জন্য একটু আধটু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও পালন করেছে। যেহেতু ধর্ম তাদের কাছে জীবনের নিছক একটা লেজুড় বিবেচিত হতো, তাই তাদের দুনিয়াবী কর্মকান্ডের পাশাপাশি যেটুকু ধর্মের অবস্থান ছিলো, সেটুকু নেহায়েত লেজুড়ের আকারেই ছিলো। সকল রকমের যুলুম-নির্যাতন, অর্থনৈতিক অবিচার, সামাজিক ভারসাম্যহীনতা এবং সাংস্কৃতিক ভ্রষ্টতা ও অনাচারের সাথেই এ লেজুড়টি সংযুক্ত ছিলো। দুস্যবৃত্তি ও ঠগবাজির সাথে যেমন তার সহাবস্থান ছিলো। আগ্রাসন, লুটতরাজ, শোষণ, ত্রাস, সুদখোরী, অর্থলোলুপতা, অশ্লীলতা ও বেশ্যাবৃত্তির সাথেও তার নিরন্তর সহগামিতা এবং সহযোগিতা ছিলো।
১. ধর্ম সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন যে, ধর্ম সংক্রান্ত জাহেলী ধ্যাণ ধারণার অপনোদন করে একটি যুক্তিসংঙ্গত ও সুষ্ঠ চিন্তা- ধারণা পেশ করবেন। আর পেশ করেই শুধু ক্ষান্ত হবেননা, বরং তার ভিত্তিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির একটি পরিপূর্ণ কাঠামো প্রতিষ্ঠা করে কার্যকরভাবে ও সফলভাবে সাথে তা চালু করে দেখিয়েও দেবেন। তিনি বললেন, ধর্ম যদি জীবনের নিছক একটা বিভাগ বা লেজুড় হয়, তবে তা নেহায়েৎ ফালতু ও অর্থহীন জিনিস। এমন জিনিসকে ধর্ম নামে আখ্যায়িত করাই ভুল। আসলে ধর্ম বা দ্বীন কেবল সেই জিনিসকেই বলে যাবে, যা জীবনের কোনো অংশ বিশেষের নয়, বরং গোটা জীবনের আদর্শ হতে পারে। হতে পারে মানুষের সমগ্র জীবনের প্রেরণার উৎস ও পরিচালিকা শক্তি। হতে পারে বুদ্ধি, বিবেচনা, উপলব্ধি, চিন্তা ও দৃষ্টির পথ প্রদর্শন, ন্যায় ও অন্যায় এবং ভুল ও নির্ভুল যাচাই করার কষ্টিপাথর। যা দেখাতে পারবে জীবনের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে ও প্রতিটি পদক্ষেপে হকপথ ও বাতিল পথের পার্থক্য যা মানুষকে বাঁচাতে পারবে অন্যায় ও অসত্য পথ থেকে আর সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়তার সাথে টিকে থাকা সামনে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি যোগাবে এবং দুনিয়া থেকে আখিরাত পর্যন্ত বিস্তৃতি জীবনের এ সুদীর্ঘ ও অফুরন্ত অভিযাত্রায় মানুষকে কামিয়াবী ও সৌভাগ্যের সাথে প্রতিটি মঞ্জিল অতিক্রম করাতে পারবে।
এ ধর্মের না ইসলাম। এটা জীবনের লেজুড় হয়ে থাকার জন্য আসেনি। তাকে যদি প্রাচীন জাহেলী ধ্যাণ ধারণা অনুসারে জীবনের একটা লেজুড় বলে ধরে নেয়া হয়, তবে তার আগমনের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেতে বাধ্য। ইসলাম মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক নিয়ে যতোটা আলোচনা করে, ঠিক ততোটাই আলোচনা করে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে এবং ঠিক ততোটাই আলোচনা করে মানুষের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়েও। ইসলামের আবির্ভব শুধু এ তত্ত্বটাই মানুষকে জানানোর জন্যে যে, সম্পর্ক ও সম্বন্ধের এ বিবিধ ক্ষেত্রগুলো পৃথক নয় কিংবা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং একটি সমষ্টিরই সমন্বিত ও সংগঠিত অংশ মাত্র। মানুষের সাথে বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক সঠিক হতেই পারেনা যতক্ষণ না মানুষের সাথে বিশ্ব স্রষ্টার সম্পর্ক সঠিক হয়। কাজেই এ দু’সম্পর্ক পরস্পরের পরিপূরক ও পরিশোধক। উভয়ে মিলিত হয়ে একটি সফল জীবন গড়ে তোলে। ধর্মের আসল কাজ হলো, সফল জীবনের জন্যে মানুষকে মানসিক ও চারিত্রিকভাবে প্রস্তুত করা। যে ধর্ম এ কাজটি করেনা তা ধর্মই নয়। আর যে ধর্ম এ কাজটি করে থাকে, তারই নাম ইসলাম। এ জন্যই বলা হয়েছেঃ
“আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র জীবন বিধান।” [আল কুরআন]
ধর্ম ও সংস্কৃতি
বস্তুত ইসলাম হলো চিন্তার একটা বিশিষ্ট প্রণালী [Attitude of mind] এবং গোটা জীবন সম্পর্কে একটা বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভংগিও [Out look on life] । তাছাড়া ঐ বিশেষ চিন্তা প্রণালী এবং জীবন সংক্রান্ত বিশেষ দৃষ্টিভংগির আলোকে নির্মিত একটা অনন্য কর্মপদ্ধতিও। এ চিন্তা প্রণালী ও কর্মপদ্ধতির সংযোগ ও সমন্বয়ে যে কাঠামো গড়ে ওঠে, সেটাই হলো দীন ইসলাম। সেটাই সভ্যতা ও কৃষ্টি। এখানে দীন এবং সভ্যতা সংস্কৃতি কোনো আলাদা আলাদা বস্তু নয়, বরং এসব কয়টি মিলে একটা সুসমন্বিত সমষ্টির জন্ম হয়। এই একই চিন্তা পদ্ধতি ও জীবন যাপন প্রণালী মানব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করে। মানুষের ওপর আল্লাহর অধিকার কি কি, তার নিজের কি কি অধিকার, মা, বাপ, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয় স্বজন, পাড়া পড়শী, লেনদেন ও কায়কারবারের অংশীদারের, স্বধর্মী এবং বিধর্মী শত্রু ও বন্ধু, গোটা মানব জাতি, এমনকি বিশ্ব প্রকৃতির বস্তু ও শক্তি নিচয়ের কি কি অধিকার? এসমস্ত অধিকারের মধ্যে ইসলাম পূর্ণ ভারসাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। একজন মানুষের মুসলমান হওয়াই এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, সে এসকল অধিকার পূর্ণ সততা ও ন্যায় নিষ্ঠাতার সাথে প্রদান করবে এবং অন্যায়ভাবে এক অধিকার আদায় করতে গিয়ে অন্য অধিকার বিনষ্ট করবেনা।
চিন্তার এ বিশিষ্ট পন্থা ও জীবন সংক্রান্ত এ বিশেষ মতবাদ মানব জীবনের জন্য এক অতি উন্নত ও মহৎ নৈতিক লক্ষ্য এবং একটা পবিত্র আধ্যাত্মিক মঞ্জিলে মকসুদ নির্ধারণ করে দেয়। জীবনের সকল চেষ্টা সাধনাকে তা সে যেকোনো কর্মক্ষেত্রেই হোকনা কেন, এমন কতোগুলো রাজপথে নিয়ে পৌছে দেয়, যে রাজপথগুলো সকল দিক থেকে একই কেন্দ্রের দিকে ধাবমান।
এ কেন্দ্র হলো একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী বিষয়। প্রতিটি জিনিসের মান নির্ধরিত হয় এরই নিরীখে এবং প্রতিটি জিনিসের যাচাই হয় এ মানদন্ডে। এ কেন্দ্রীয় মঞ্জিলে মকসুদে পৌছার ব্যাপারে যে জিনিস সহায়ক, তা গ্রহণ করা হয়। আর যা এর পথে অন্তরায় তা করা হয় বর্জন। ব্যক্তি জীবনের ক্ষদ্রাতি ক্ষুদ্র বিষয় থেকে শুরু করে সমাজ জীবনের বড় বড় ব্যাপারেও এ মানদন্ড সমানভাবে প্রযোজ্য। পানাহারে, পোশাকে পরিচ্ছেদে, ব্যবহারে, শিল্প কারখানার পারস্পরিক সম্পর্কে, লেনদেনে, কথাবার্তায় মোটকথা জীবনের প্রতিটি কাজকর্মে কোনো ব্যক্তির কি কি সীমা ও বিধিনিষেধ মেনে চলা দরকার এবং মেনে চললে সে মঞ্জিলে মকসুদ অভিমুখী সোজা পথে অগ্রসরমান থাকতে পারবে এবং বক্র ও ভ্রষ্ট পথে পা বাড়ানোর, তারও ফয়সালা এ মানদন্ড দ্বারাই হয়ে থাকে। একই মানদন্ড এও নির্ণয় করে দেয় যে, সামষ্টিক জীবনে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক কোন নীতিমালার ভিত্তিতে বিধিবদ্ধ হলে সামাজিক আচার আচরণ, অর্থনৈতিক লেনদেন, রাজনৈতিক কর্যকলাপ এক কথায় জীবনের সকল ক্ষেত্রের বিকাশ ও উন্নয়ন উক্ত মঞ্জিলে মকসুদ অভিমুখী পথ ধরেই সম্পন্ন হতে পারবে এবং উক্ত মঞ্জিলে মকসুদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এমন পথে সম্পন্ন হবেনা। আকাশ ও পৃথিবীর যেসকল উপায় উপকরণের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যেসকল জিনিসকে তার অনুগত ও বশীভূত করে দেয়া হয়েছে, তাকে সে কোন কোন পন্থায় ব্যবহার করলে তা তার সাফল্যের পথে অন্তরায় হবে বলে তা তার এড়িয়ে চলা উচিত, সে সম্পর্কেও ঐ মানদন্ডের নিরীখেই সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব। একই মানদন্ডে এ ব্যাপারেও ফয়সালা করা সম্ভব যে, ইসলামী সমাজের লোকদেরকে অনৈসলামী সমাজের সাথে শত্রুতায় ও মিত্রতায়, যুদ্ধে ও সন্ধিতে, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঐক্যে ও বিভিন্নতায়, বিজয়ী অবস্থায় ও পরাজিত অবস্থায়, বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদানে কোন নীতিমালা অনুসরণ করা কর্তব্য, যাতে করে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের এসব বিভিন্ন স্তরে তারা আপন লক্ষ্য হারিয়ে না বসে বরং যতোদূর সম্ভব, মানবজাতির এ অজ্ঞ ও বিপথগামী সদস্যদেরকে দিয়েও ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, সচেতনভাবে কিংবা অবচেতনভাবে, সেই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের কাজ নিতে পারে, যা মূল স্বভাব ধর্মের বিচারে মুসলমানদের মতো তাদেরও জীবনের উদ্দেশ্য।
মোটকথা, মসজিদ থেকে শুরু করে বাজার ও রণাঙ্গণ পর্যন্ত, ইবাদত উপাসনার নিয়মকানুন থেকে শুরু করে রেডিও ও উড়োজাহাজের ব্যবহারবিধি পর্যন্ত; ওজু, গোসল, পবিত্রতা অর্জন ও পেশাব, পায়খানার খুটিনাটি মাসয়ালা মাসায়েল থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক জীবনের মূলনীতি পর্যন্ত, মকতবের হাতে খড়ি শিক্ষা থেকে শুরু করে প্রাকৃতিক নিদর্শনাবলীর পর্যবেক্ষণ ও মহাজাগতিক নিয়মাবলীর সর্বোচ্চমানের তত্বানুসন্ধান ও গবেষণা পর্যন্ত জীবনের সকল চেষ্টা সাধনা এবং চিন্তা ও কর্মের সকল বিভাগকে ঐ একই দৃষ্টিভংগি এমন একটি সুসমম্বিত এককে পরিণত করে, যার সকল অংশ উদ্দেশ্যগতভাবে সুবিন্যাস্ত এবং স্বেচ্ছাগতভাবে মিলিত হয় যে, এগুলোর সম্মিলিত ক্রিয়া ও চালনা দ্বারা একই ফল উৎপন্ন হয়।
ধর্মের জগতে এটা ছিলো এক বৈপ্লবিক ধারণা। নিরেট জাহেলিয়াত থেকে উদগত মস্তিষ্কে এ ধারনা কখনো পুরোপুরিভাবে স্থান লাভ করতে পারেনি। জ্ঞান বিস্তার ও বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে আজকের পৃথিবী খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর চাইতে অনেক বেশী অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও এত সেকেলে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতা বিরাজমান যে, ইউরোপের বিশ্ববিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরাও এ বৈপ্লবিক আদর্শকে উপলব্ধি করতে ঠিক ততখানিই অক্ষম, যতখানি অক্ষম ছিলো আদিম জাহেলী সমাজের গন্ডমূর্খ নির্বোধ লোকগুলো। হাজার হাজার বছর ধরে ধর্ম সম্পর্কে যে ভ্রন্ত ধারণা পুরুষানুক্রমে চলে আসছে, তাদের মস্তিষ্ক আজও তার বজ্র আঁটুনীতে আবদ্ধ। যুক্তিভিত্তিক সমালোচনা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসন্ধানের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণেও সে বন্ধন খোলা সম্ভব হচ্ছেনা। মসজিদ ও খানকার অন্ধকারে প্রকোষ্ঠে অবস্থানকারীরা যদি ধার্মিকতার অর্থ নির্জনে বসে আল্লাহ আল্লাহ জপ করা মনে করে এবং দীনদারী বলতে আনুষ্ঠানিক ইবাদত উপাসনার গন্ডীতে আবদ্ধ থাকা বুঝে, তাহলে সেটা তেমন বিস্ময়ের ব্যাপারে হয়না। কেননা তারা তো আদতেই রক্ষণশীল। অজ্ঞ জনসাধারণ যদি ধর্মকে বাদ্য বাজানো তাজিয়া অনুষ্ঠান এবং গোপূজার মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে তাহলে তাতেও অবাক হবার কিছু থাকেনা। কিন্তু বড় বড় বিদ্বান ও পন্ডিতদের কি হয়েছে যে, তাদের মস্তিষ্ক থেকেও সেকেলে ধ্যান ধারণার অন্ধকার দূরিভূত হলোনা? অমুসলিম প্রাচীন জাহেলী ভাবধারার আওতাধীন ধর্মকে যে অর্থে গ্রহণ করে, ঠিক সেই অর্থেই ইসলামকে একটা ধর্ম মনে করে থাকে এ পন্ডিত মহোদয়রা।
আমাদের রাজনীতিতে জাহেলী চিন্তাধারার প্রভাব
উপলব্ধির ও সীমাবদ্ধতা ও অনুধাবনের এ অক্ষমতার দারুন মুসলিম শিক্ষিত শ্রেণীর একটা বৃহৎ অংশ শুধু যে নিজেরাই ভ্রান্ত পথে চলছে তাই নয়, বরং গোটা দুনিয়ায় তারা ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি সম্পর্কে নিদারুণ ভুল ধারণার প্রসার ঘটাচ্ছে। মুসলিম জাতির যেসব প্রকৃত সমস্যা সমাধানের ওপর তাদের বাঁচা মরা নির্ভরশীল, সেগুলো তাদের একেবারেই বুঝে আসেনা। অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক সমস্যাগুলোকেই তারা আসল সমস্যা মনে করে উদ্ভট পন্থায় সেগুলোর সমাধনের চেষ্টা করছে। এসমস্ত চেষ্টার মধ্য দিয়ে বস্তুত ধর্মের সেই পুরনো সংকীর্ণ ধারাই বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে। কেউ বলেন, আমি প্রথমে ভারতীয়, তারপর মুসলমান। এ কথাটা তারা যখন বলেন, তখন তাদের মন মস্তিষ্কে ধর্ম সম্পর্কে ও ধারণাই বিদ্যমান থাকে যে, ইরানী ইসলাম, মিশরীয় ইসলাম, ভারতীয় ইসলাম, অতপর ভারতীয় ইসলামের মধ্যেও আবার বাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, দাক্ষিণাত্মীয়, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের ইসলাম হতে পারে। প্রত্যেক অঞ্চলের মুসলমানরা নিজ নিজ আঞ্চলিক অবস্থা অনুপাতে আলাদা আলাদা চিন্তাধারা অবলম্বন করতে পারে ও জীবন সম্পর্কে ভিন্ন রকমের দৃষ্টিভংগি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন মূলনীতি ও মতাদর্শ অনুসারে যেসব সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিজেদের মধ্যে চালু করে নিয়েছে তার মধ্য তারাও মিলে মিশে যেতে পারে এবং তার পরেও পার্থিব জীবনের যে কোনো পথ ও পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত হতে সক্ষম।
আরেক ভদ্র লোক বলেন, মুসলমানদের বৈষয়িক ও ধর্মীয় ব্যাপারগুলোর মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করা উচিত। ধর্মের সম্পর্ক হলো মানুষ ও আল্লাহর মধ্যকার ব্যাপারগুলোর সাথে। অর্থাৎ আকিদা বিশ্বাস ও ইবাদতের সাথে। এগুলোর ক্ষেত্রে মুসলমানরা স্বতন্ত্র নিয়য়ে চলতে পারে। কেউ তাদেরকে এ পথ থেকে হটাতে চাইবেওনা, পারবেওনা। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারগুলোর কথা আলাদা। সে ব্যাপারে ধর্মের নাকগলানোর দরকার নেই। দুনিয়ার অন্যান্য লোকেরা যেভাবে বৈষয়িক ব্যাপার আঞ্জাম দিয়ে থাকে, মুসলমানদেরও সেভাবে আঞ্জাম দেয়া উচিত।
অপর এক ভ্রদ্র মহোদয় বলেন, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত অধিকারের ক্ষেত্রে মুসলমানদের একটা আলাদা পদ্ধতি নিসন্দেহে থাকা চাই। কিন্তু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যে তাদের পৃথক সমাজ গঠনের প্রয়োজন নেই। এসব ব্যাপার মুসলিম ও অমুসলিমের ভেদাভেদ নিতান্তই অবান্তর ও কৃত্রিম। এ ক্ষেত্রে অন্য যেসব সম্প্রদায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসারে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাবলীর সমাধানের চেষ্টা করছে, তাদের সাথে মুসলিম জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর নিজ নিজ স্বার্থ ও উদ্দেশ্য অনুসারে ভিড়ে যাওয়াই বাঞ্চনীয়।
মুসলিম জাতির ঝিমিয়ে পড়া সত্তায় নতুন প্রাণ সঞ্চারের উদ্যেক্তারূপে আবির্ভূত আরেক ভদ্রলোকের অভিমত হলো, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন এবং কুরআন সুন্নাহর অনুসরণ আসল জিনিস নয়, বরং জগতের বস্তু নিচয়কে বশীভূত করা, প্রাকৃতিক বিধিসমূহ অবগত হওয়া এবং আইন শৃংখলার শক্তি দিয়ে উক্ত বশীভূত বস্তুনিচয় ও আহরিত বিধিসমূহকে কাজে লাগানোটাই হলো আসল প্রতিপাদ্য বিষয়। এগুলোকে কাজে লাগানোর মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম লাভ করা সম্ভব। এ ভদ্রলোক বস্তুগত ও বৈষয়িক উন্নতিকেই মানুষের আসল ও প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য বলে অভিহিত করেন। তাই এ উন্নতির সহায়ক উপায় উপকরণগুলোই তাঁর কাছে যথার্থ গুরুত্বের অধিকারী। পক্ষান্তরে জ্ঞান ও বুদ্ধির পশ্চাতে যে মন-মগজ ক্রিয়াশীল এবং যা আপন বিশিষ্ট চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভংগির নিরীখে উন্নয়নের উপায়-উপকরণসমূহ ব্যবহারের উদ্দেশ্য, সভ্যতা ও কৃষ্টির উৎকর্ষ ও অগ্রগতির পথ ও পন্থা এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রম লাভের প্রক্রিয়া নির্ণয় করে, সেই মন মগজের কোনো গুরুত্বই তাদের দৃষ্টিতে নেই। সে মস্তিষ্ক জাপানী, জার্মান, বা ইটালিয়ান হোক অথবা তা হোক ওমর ফারুক কিংবা খালেদ বিন ওলীদের মন মস্তিষ্ক, সেটা তাদের আদৌ বিবেচ্য বিষয় নয়। তাদের দৃষ্টিতে এসব একই রকমের “ইসলামী” মন মগজ। কেননা এ সবেরই কর্যক্রম তাদের চোখে একই ফল দর্শায়। অর্থাৎ একই পার্থিব প্রতিষ্ঠা ও পারাক্রম তার দ্বারা অর্জিত হয়। তাদের দৃষ্টিতে “পৃথিবীর উত্তরাধিকার” [অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা ও কর্তৃত্ব] যে পেয়েছে, সেই “ন্যায়নিষ্ঠ ও সৎ”, চাই সে ইবরাহীমের মোকাবিলায় নমরুদেই হোক। অন্য কথায় বলা যায়, যে ব্যক্তি পরাক্রান্ত ও বিজয়ী সেই, “মুনিন”, চাই সে হযরত ঈসার মোকাবিলায় রোম সম্রাটই হোক না কেন।
আর একটা বড় গোষ্ঠী মুসলমানদের জাতীয় স্বার্থ ও অথিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে ময়দানে নেমেছে। তাদের মতে, মুসলমানদের ধর্ম ও সে ধর্মের বিধিবদ্ধ পারিবারিক আইন সংরক্ষণের আশ্বাস প্রদান, তাদের ভাষাকে বর্ণমালা সমেত অন্যতম সরকারী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দান এবং একমাত্র ইসলামী বেশভূষা ধারীদেরকেই মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রদান করা হলেই ইসলাম এবং ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টি সংরক্ষিত হয়। নির্বাচনযোগ্য প্রতিষ্ঠানসমূহে ও সরকারী চাকুরীতে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব তাদের মতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আর যাদি এরূপ স্থির করে দেয়া হয় যে, মুসলিম প্রতিনিধিদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কর্তৃক গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত ইসলামের একন্ত ধর্মীয় ব্যাপারে কোনো নিষ্পত্তি হবেনা, তাহলে তাদের মতে মুসলিম অধিকার যেনো ষোল আনাই আদায় হয়ে গেলো।
দেখলেন তো? বাহ্যিক রূপের কি বিস্তার পার্থক্য, কিন্তু ভেতরের মূল জিনিসটি এর সবকয়টিতে একই থেকে যাচ্ছে। এসবই হচ্ছে ধর্ম সংক্রান্ত জাহেলী ধ্যান ধারণার বিভিন্ন রূপ মাত্র, যা ইসলামী ধ্যান ধারণার বিরুদ্ধে প্রত্যেক যুগেই নিত্য নতুন আকারে বিদ্রোহ প্রকাশ করে আসছে।
তারা যদি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেন যে, মুসলমান কাকে বলে এবং সত্যিকার অর্থে ইসলামী সমাজ বা উম্মাহ বলতে কোন গোষ্ঠিকে বোঝায়, তাহলে তাদের সকল ভুল ধারণার অপনোদন হওয়া সম্ভব। আইনগতভাবে তো যে ব্যক্তি মুখে কালেমা পড়ে এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে নেয়, সে মুসলিম হিসেবে গন্য। কিন্তু যিনি এ অর্থে মুসলমান তাঁর মর্যাদা শুধু এতোটাকুই যে, তিনি ইসলামের চৌহদ্দীর ভেতরে আছেন। আমরা তাকে কাফের বলতে পারিনা এবং শুধুমাত্র ইসলাম গ্রহণের কারণে মুসলিম সমাজে তার যেসব অধিকার প্রাপ্য হয়, তা দিতে অস্বীকারও করতে পারিনা। এটুকুই আসল ইসলাম নয়, বরং কেবলমাত্র ইসলামের সীমানায় প্রবেশের অনুমতিপত্র। আসল ইসলাম হলো এই যে, গোটা মন মানস ইসলামের সাথে গড়ে ওঠবে। তার চিন্তা ভাবনার পদ্ধতি হবে হুবহু কুরআনের চিন্তাপদ্ধতি। জীবন ও তার সকল তৎপরতা ও আচরণের ব্যাপারে তার দৃষ্টিভংগি হবে অবিকল কুরআনের দৃষ্টিভংগি। কুরআন সকল জিনিসের মূল্যবান নির্ণয়ের যে মানদন্ড নির্ধারণ করে দিয়েছে, ঠিক সেই মানদন্ডই সে সকল জিনিসের মান নির্ণয় করবে। তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে অবিকল তাই, যা কুরআন দেখিয়ে দিয়েছে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে রকমারি মত ও পথ বর্জন করে তারা একটিমাত্র পথ বেছে নেবে এবং সেই বাছাই কাজটাও সম্পন্ন করবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে যা কুরআন ও রাসূলের পথনির্দেশ থেকে তারা লাভ করেছে।
কোনো মুসলমানের মন মগজকে যদি এটা আকৃষ্ট করতে না পারে এবং কুরআনের মনোভংগির আলোকে তার মনোভংগি গড়ে উঠতে প্রন্তুত না হয়, তাহলে ইসলামের চৌহদ্দীর মধ্যে ঢুকতে বা বহাল থাকতে কেউ তাকে বাধ্য করেনা। সততা ও বুদ্ধিমত্তার দাবী এই যে, এমতাবস্থায় তাদেরকে ইসলামের চৌহদ্দীর বাইরেই নিজের জন্যে উপযুক্ত স্থান খুঁজে নেয়া উচিত। পক্ষান্তারে তার মন মগজ যদি এ জিনিসটাকে গ্রহণ করে এবং সে নিজের মন মানসিকতাকে কুরআনের মতো করে গড়ে তুলতে চায়, তাহলে কুরআন যাকে মুমিনদের পথ বলে অভিহিত করা হয়েছে, তাথেকে তার মত ও পথ কোনো ব্যাপারেই স্বতন্ত্র বা পৃথক হতে পারেনা।
কুরআনী দৃষ্টিভংগি
ইসলামী মন-মানস বা কুরআন অনুসারী মন-মানস আসলে এক এবং অভিন্ন জিনিস। তা যে বিশেষ জীবন বিধানের আওতাধীন কতিপয় আকীদার ওপর ঈমান আনে, কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদত নির্ধারণ করে, কাতিপয় ধর্মীয় রীতিনীতি অবলম্বন করে, ঠিক সেই একই জীবন বিধানের অধীন সে পানাহারের দ্রব্যাদিতে, পরিধানের পোশাক পরিচ্ছদে, পোশাকের ধরন ও আকৃতিতে, সামাজিক রীতিনীতি ও চালচলনের পদ্ধতিতে, বাণিজ্যিক আদান প্রদানে, অর্থনৈতিক বন্দোনস্ত ও লেন দেনে, রাজনীতির নিয়ম প্রক্রিয়ায়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির রকমারি বহিপ্রকাশে, আর বস্তুগত উপায় উপকরণ ও প্রাকৃতিক নিয়ম বিধি সংক্রান্ত জ্ঞান প্রয়োগের বিবিধ কর্মপন্থায় কতোগুলোকে বর্জন ও কতোগুলোকে গ্রহণ করে থাকে। এ সবগুলোর ব্যাপারে যেহেতু দৃষ্টিভংগি, চিন্তা পদ্ধতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং গ্রহণ ও বর্জনের মাপকাঠি এক ও অভিন্ন, তাই জীবন যাপনের পদ্ধতি, চেষ্টা ও তৎপরতার পন্থা এবং পার্থিব জীবনের আচার আচরণের নীতি নিয়ম বিভিন্ন রকমের হতে পারেনা। একথা সত্যি যে, খুঁটিনাটি বিষয়ে বাস্তব কর্মপদ্ধতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র আর নির্দেশমালার ব্যাখ্যায় ও নিত্যদিনের ঘটনাবলীতে মূলনীতির প্রয়োগে কমবেশী মতপার্থক্য ঘটা স্বাভাবিক। একই মস্তিষ্কের চিন্তাধারার রকমারি রূপ পরিগ্রহ করাও বিচিত্র নয়। কিন্তু এ বিভিন্নতা নিছক বাহ্যিক রূপগত বিভিন্নতা, মৌলিক ও উপাদানগত বিভিন্নতা কখনো নয়। যে মূল ভিত্তির ওপর ইসলামে গোটা জীবনের জন্যে পূর্ণাংগ বিধান রচনা করা হয়েছে এবং জীবনের সকল অংশ ও বিভাগকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, তাতে কোনো ধরনের বিভিন্নতার অবকাশ নেই। আপনি ভারতীয় হোন কিংবা তুর্কী, কিংবা মিশরীয়, তাতে কিছু আসে যায়না। আপনি যদি মুসলমান হন, তাহলে আপনাকে এ পূর্ণাংগ বিধান পূরোপুরিভাবে তার অন্তর্নিহিত ভাবধারা সহকারেই গ্রহণ করতে হবে। আর যে কোনো বিধান স্বীয় মূলনীতি ও ভাবধারার বিচারে এ বিধানের বিরোধী হবে তাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।
এখানে আপনার পক্ষে পার্থিব ও ধর্মীয় অংশগুলোকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করাই সম্ভব নয়। ইসলামের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখিরাত একই ধারাবাহিক জীবনের দুটি ধাপ মাত্র। প্রথম ধাপটা হলো চেষ্টা ও কর্মের আর দ্বিতীয়টা কর্মফলের। জীবনের প্রথম ধাপে আপনি দুনিয়াকে যেভাবে গ্রহণ করবেন, পরবর্তী ধাপে সে ধরনের ফলই প্রকাশিত হবে। ইসলামের লক্ষ্য হলো আপনার চিন্তা ও কর্মকে এমনভাবে তৈরী করে দেয়া, যাতে জীবনের এ প্রাথমিক ধাপে আপনি দুনিয়াকে সঠিকভাবে গ্রহণ করেন এবং ফলশ্রুতিতে দ্বিতীয় ধাপে সঠিক ও সুষ্ঠু ফল লাভ করতে পারেন। কাজেই ইসলামে সমগ্র পার্থিব জীবনই ‘ধর্মীয় জীবন’। এতে আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদত বন্দেগী থেকে শুরু করে সভ্যতা, কৃষ্টি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ধারা উপধারা পর্যন্ত সবকিছু একই নৈতিক ও উদ্দেশ্যগত যোগসূত্র বাঁধা।
আপনি যদি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে ইসলামের নির্দেশিত বিধান ছাড়া অন্য কোনো বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে চান, তাহলে এটা হবে আংশিকভাবে ইসলামকে পরিত্যাগ করার শামিল, যা শেষ পর্যন্ত ইসলামকে পূরোপূরিভাবে পরিত্যাগ করার পর্যায়ে পৌছিয়ে দিয়ে থাকে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আপনি ইসলামের শিক্ষাগুলোকে যাচাই বাছাই করে তার কতককে গ্রহণ ও কতককে বর্জন করলেন। ইসলামের আকিদা বিশ্বাস ও মৌলিক ইবাদতসমূহকে তো আপনি গ্রহণ করেছেন আর এসব ইবাদতের ভিত্তিতে যে সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রথমত এ যাচাই বাছাই করাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে ভুল। ইসলামের প্রতি যথার্থভাবে ঈমান রাখে এমন কোনো মুসলমান এ ধরনের কাজে প্রবৃত্ত হতেই পারেনা। কেননা তাহলে আল্লাহ যে সূরা বাকারার ৮৫ আয়াতে বলেছেনঃ
“তোমরা কি আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ করবে অস্বীকার?”
সেই কথাটাই সত্য হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি এ যাচাই করে আংশিক ইসলামকে গ্রহণ করে ইসলামের গন্ডীর মধ্যে টিকে থাকারও সংকল্প নেন, তাহলেও আপনি এ গন্ডীর ভেতর বেশী দিন টিকে থাকতে পারবেননা। কারণ বাস্তব জীবন যাপন পদ্ধতির সাথে সংশ্রবহীন হওয়ার পর ইসলামী আকীদা ও ইবাদত সবই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ওসবের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়। অনৈসলামিক জীবনাদর্শের ওপর ঈমান আনার পর কুরআনের ওপর ঈমান বজায় থাকতেই পারেনা। কেননা কুরআন তো প্রতি পদে পদে ওসব বাতিল জীবনাদর্শকে খন্ডন করে।
পক্ষান্তরে আপনি যদি ইসলামী বিধান অনুসারে নিজের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করতে চান, তাহলে আপনার আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হবার দরকার নেই। একই দল অর্থাৎ আল্লাহর দল এসব কাজের জন্যে যথেষ্ট। কেননা এখানে পুঁজিপতি ও শ্রমিক, ভূস্বামী ও চাষী, শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই। বরং তাদের মধ্যে সমন্বয় ও অংশীদারীত্ব সৃষ্টিকারী মূলনীতি বিদ্যমান। এসব মূলনীতি অনুসারে আপন জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংহতি ও সমন্বয় সৃষ্টির চেষ্টা আপনি কেন করবেননা? যাদের কাছে এসব মুলনীতি নেই, তারা যদি অনন্যোপায় হয়ে শ্রেণী সংগ্রামের আগুনে ঝাঁপ দেয়, তাহলে আপনিও সেই আগুনে ঝাঁপ দেবেন কোন কারণে?
অনুরূপভাবে আপনি যদি বস্তুগত উন্নতি চান, পৃথিবীতে মাথা তুলে দাঁড়াতে ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চান, তাহলে ইসলাম নিজেই এ ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তবে সে শুধু এটুকু চায় যে, আপনি ফেরাউন ও নমরূদের পরাক্রম এবং মূসা ও ইবরাহীমের পরাক্রমের মধ্যে যেনো পার্থক্য করেন। আজকের জাপান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যান্ড পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আবার সাহাবায়ে কিরাম এবং ইসলামের প্রাথমিক শতাব্দীগুলোর মুসলমানরাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। দুটোই প্রতিষ্ঠা এবং দুটোই পার্থিব উপায় উপকরণকে করায়ত্ব করা, প্রয়োগ ও ব্যবহার করা এবং প্রাকৃতিক নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞান ও তা কাজে লাগানোরই ফসল। কিন্তু উভয়ের উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভংগিতে আকাশ পাতাল ব্যাবধান। এ উভয় ফসলের বাহ্যিক এবং একেবারেই আপাত দৃশ্যমান সাদৃশ্য আপনার চোখে পড়ছে। অথচ উভয়ের মধ্যে মৌলিক ও নৈতিক দিক দিয়ে যে সুমেরু কুমেরুর ব্যবধান বিরাজমান, তা আপনার নজরে আসছেনা। দুনিয়া পূজারীদের উন্নতি ও প্রতিষ্ঠা প্রাকৃতিক উপায় উপকরণ করায়ত্ব করণের এমন এক প্রক্রিয়ার ফল, যার মূলে সক্রিয় রয়েছে জীবনের পাশবিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে যে ধরনের প্রতিষ্ঠা ও পরাক্রমের প্রতিশ্রুতি কুরআন দিয়েছে যদিও সেটি পার্থিব উপায় উপকরণ করায়ত্ব করা ও প্রয়োগ করার দ্বারাই অর্জিত হওয়া সম্ভব, কিন্তু তার গভীরে জীবনের উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য বর্তমান থাকা প্রয়োজন। আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস যতক্ষণ পূরোপূরিভাবে বদ্ধমূল না হয় এবং নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাতের সাহায্যে যে লৌহ বেষ্টনীকে অধিকতর মজবুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তার অধীন জীবনের সকল কর্যকলাপ ও চেষ্টা সাধনা নিয়ন্ত্রিত না হয়, ততক্ষণ সেই উচ্চতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করা অসম্ভব। অথচ ইসলামের উক্ত বুনয়াদী স্তম্ভগুলোকে আপনারা মোল্লা মৌলবীদের ভ্রান্ত ধর্ম বিশ্বাসের উদ্ভট আবিষ্কার বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজন কেন? [এক আহম ইস্তেফতা পুস্তক থেকে এ অংশ নেয়া হয়েছে।]
আমরা আগেই একথা পরিষ্কার করে বলেছি, মুসলমানরা যদি মুসলমান হিসেবে জীবনযাপন করতে চায়, তাবে তাদের নিজেদের গোটা জীবনকে আল্লাহর আনুগত্যের অধীন করে দিতে হবে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের সকল বিষয়ের ফয়সালা কেবলমাত্র আল্লাহর আইন ও শরীয়াহ মোতাবেক করতে হবে, এছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিকল্প নেই। আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি ঈমান পোষণ করার ঘোষণা করবেন আর জীবনের সামগ্রিক বিষয়াদি পরিচালনা করবেন আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের আইন অনুযায়ী, ইসলাম কোনো অবস্থাতেই এমনটি বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। এর চাইতে বড় স্ববিরোধিতা আর কিছু হতে পারেনা। এই স্ববিরোধিতাকে বরদাশত করার জন্যে নয়, নির্মূল করার জন্যে ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছে। আমরা যে ইসলামী রাষ্ট্র ও শাসনতন্ত্র দাবী করছি, তার পেছনে এই অনুভূতিই কাজ করছে যে, মুসলমান যদি আল্লাহর আইনই মেনে না চলে, তবে তো তার মুসলমান হবার দাবীই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। গোটা কুরআনই এই নির্জলা সত্য কথাটির প্রমাণঃ
১. কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহই সমস্ত জগত ও সম্রাজ্যের মালিক। তিনি স্রষ্টা, সৃষ্টিজগত তাঁর। তাই স্বাভাবিকভাবেই শাসনের অধিকার [Right to Rule] কেবল তাঁরই থাকা উচিত। তাঁর রাজ্যে [Dominion] তাঁর সৃষ্টির উপর তাঁর ছাড়া অপর কারো শাসন সার্বভৌমত্ব চলা মূলতই ভ্রান্ত। সঠিক পন্থা কেবল একটিই। তাহলো, তাঁর খলীফা ও প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর প্রদত্ত আইন ও বিধান অনুযায়ী শাসন পরিচালিত হবে এবং কার্যসম্পাদিত হবে। তাঁর অকাট্য ঘোষণা হলোঃ
ক. বলোঃ হে সাম্রাজ্য ও সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে চাও রাজ্যক্ষমতা দান করো। আর যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। [সূরা আলে ইমরানঃ ২৬]
খ. তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রভূ প্রতিপালক। গোটা সাম্রাজ্য তাঁর। [সূরা ফাতিরঃ ১৩]
গ. রাজত্বে তাঁর কোনো অংশীদার [Partner] নেই। [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ১১১]
ঘ. সুতরাং সমস্ত কর্তৃত্ব সমুচ্চ মহান আল্লাহর। [সূরা আল মুমিনঃ ১২]
ঙ. তিনি তাঁর কর্তৃত্বে কাউকেও অংশীদার বানাননা। [সূরা আল কাহাফঃ ২৬]
চ. সাবধান! সৃষ্টি তার, কর্তৃত্বও তাঁর। [সূরা আ’রাফঃ ৫৪]
ছ. ওরা জিজ্ঞেস করছেঃ কর্তৃত্বে আমাদেরও অংশ আছে কি? বলোঃ কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট। [সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৪]
২. এই মূলনীতির ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের অধিকার মানুষের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে। কারণ, মানুষ তো হলো আল্লাহর সৃষ্টি এবং তাঁর রাজত্বের প্রজা। তাঁর দাস এবং তাঁর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধীন। তাই মানুষের কাজ হলো কেবল তার স্রষ্টা রাজাধিকারাজের আইন মেনে চলা। এক্ষেত্রে তাঁর প্রদত্ত আইনের সীমার মধ্যে অবস্থান করে ইজতিহাদ ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাসংগিক বিধি প্রণয়নের নিয়ন্ত্রিত অধিকারই কেবল মানুষের রয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যেসব বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি কোনো হুকুম প্রদান করেননি, সেসব ক্ষেত্রেও শরীয়তের প্রাণসত্তা এবং ইসলামের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল বিধি প্রণয়নের অধিকারও মুমিনদের দেয়া হয়েছে। কেননা এসব ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রসূলের সরাসরি কোনো বক্তব্য না থাকাটাই একথার প্রমাণ যে এসব ক্ষেত্রে নিয়ম বিধি প্রণয়নের আইনগত অধিকার মুমিনদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে মৌলিক কথাটি সূর্যালোকের মতো সম্মুখে স্পষ্ট থাকতে হবে, তাহলো, আল্লাহ প্রদত্ত আইনের আওতামুক্ত হয়ে যে ব্যক্তি বা সংস্থা নিজেই স্বাধীনভাবে কোনো আইন প্রণয়ন করবে, কিংবা অপর কারো রচিত আইন মেনে চলবে, সে তাগুত, বিদ্রোহী এবং খোদার আনুগত্য থেকে বিচ্যুত। আর এমন ব্যক্তির কাছে যে-ই ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত চাইবে এবং তার প্রদত্ত ফায়সালা ও সিদ্ধান্ত মেনে নেবে সেও বিদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। এসব ফায়সালা স্বয়ং আল্লাহরঃ
ক. আর তোমাদের মুখ যেসব জিনিসের কথা উচ্চারণ করে, সেসব বিষয় তোমরা মনগড়াভাবে বলোনা যে, এটা হালাল [lawfull] আর এটা হারাম [unlawfull] । [সূরা আন নহলঃ ১১৬]
খ. তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যাকিছু অবতীর্ণ হয়েছে, তারই অনুসরণ করো। তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো [মনগড়া] কর্তা ও পৃষ্ঠপোষকের অনুসরণ করোনা। [সূরা আ’রাফঃ ৩]
গ. আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী যারা ফায়সালা করেনা, তারা কাফির। [সূরা আল মায়িদাঃ ৪৪]
ঘ. হে নবী! তুমি সেইসব লোকদের দেখনি যারা মুখেতো সেই হিদায়াতের প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবী করে যা তোমার এবং তোমার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে? কিন্তু তারা নিজেদের যাবতীয় বিষয়ে ফায়সালা করিয়ে নিতে চায় তাগুতদের দিয়ে। অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তাগুতকে অস্বীকার করতে। [সূরা আন নিসাঃ ৬০]
৩. বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা’য়ালার এই পৃথিবীতে সঠিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও বিচার ব্যবস্থা কেবল সেটাই, যা তাঁর নবী রসূলদের মাধ্যমে প্রেরিত আইনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এরি নাম হলো, খিলাফত। কুরআন বলেঃ
ক. আমি যে রসূলকেই পাঠিয়েছি, এজন্যেই পাঠিয়েছি, যেনো আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে তার আনুগত্য করা হয়। [সূরা আন নিসাঃ ৬৪]
খ. হে নবী! পূর্ণ সত্যতার সাথে আমরা এ কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে করে আল্লাহর দেখানো সত্যালোকের মাধ্যমে তুমি মানুষের মধ্যে ফায়সালা করতে পারো। [সূরা আননিসাঃ ১০৫]
গ. আর আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী তুমি তাদের মাঝে ফায়সালা করো। তাদের ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করেনা। সাবধান থেকো, তারা যেনো তোমাকে ফিতনার নিমজ্জিত করে আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান থেকে এক বিন্দুও বিভ্রান্ত করতে না পারে। [সূরা আল মায়িদাঃ ৪৯]
ঘ. তারা কি জাহিলিয়াতের শাসন ফায়সালা চায়। [সূরা আল মায়িদাঃ ৫০]
ঙ. হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানিয়েছি। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সত্যের ভিত্তিতে শাসন চালাও। ইচ্ছা বাসনার অনুসরণ করোনা। তাহলে তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। [সূরা সোয়াদঃ ২৬]
৪. পক্ষান্তরে এমন প্রতিটি রাষ্ট্র ও বিচার ব্যবস্থাই খোদাদ্রোহী, যার ভিত্তি বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা’য়ালার নবী রসূলদের আনীত আইনবিধানের পরিবর্তে অপর কারো রচিত আইনবিধানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এসব রাষ্ট্র ও আদালতের ধরন প্রকৃতির মধ্যে যতোই বিভিন্নতা থাকুকনা কেনো, তাতে কিছু যায় আসেনা। এগুলোর সমস্ত কর্মকান্ড ভিত্তিহীন, বৈষম্যপূর্ণ ও ভ্রান্ত। শাসন পরিচালনা এবং রায় প্রদানের মুলতই তাদের কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। রাজ্যও সাম্রাজ্যের প্রকৃত মালিকই যখন তাদেরকে Charter প্রদান করেননি তখন কী করে তাদের রাষ্ট্র ও আদালত পরিচালনা বৈধ হতে পারে? [এমন সরকার ও আদালতই বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা’য়ালার Charter লাভ করে, যারা তাঁকেই বিশ্বজগতের মালিক এবং নিজেদেরকে তার খলীফা [প্রতিনিধি, স্বাধীন নয়] মনে করে, তাঁর প্রেরিত নবী রসূল ও কিতাবকে স্বীকার করে এবং তাঁর প্রদত্ত শরীয়ার অধীনে থেকে কাজ করতে নিজেদেরকে বাধ্য মনে করে। স্বয়ং কুরআনেই এ Charter প্রদান করা হয়েছেঃ “তাদের মধ্যে শাসন ফায়সালা কারো আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী” [আল মায়িদাঃ ৪৯]। Charter প্রদান বলতে আমরা এখানে একথাই বাঝিয়েছি।] তারা যা কিছু করছে, আল্লাহর আইনের দৃষ্টিতে তাতো সবই নাস্তি। মুমিনরা [আল্লাহর অনুগত প্রজা] তাদের অস্তিত্বকে একটি Defacto হিসেবে স্বীকার করতে পারে, কিন্তু একটি Dejure হিসেবে স্বীকার করতে পারেনা। নিজেদের প্রকৃত মালিক [আল্লাহ]-র বিদ্রোহীদের আনুগত্য করা এবং তাদের কাছে নিজেদের বিষয়াদির ফায়সালা চাওয়া মুমিনদের কাজ নয়। যদি কেউ এমনটি করে, তাবে নিজেকে মুমিন ও মুসলিম দাবী করা সত্ত্বেও সে আল্লাহর অনুগতদের দল থেকে বিচ্যুত। একথা সরাসরি বিবেক বুদ্ধির সাথেও সাংঘর্ষিক যে, কোনো সরকার একটি গোষ্ঠীকে বিদ্রোহী বলেও আখ্যায়িত করবে, আবার স্বীয় প্রজাদের উপর সেই বিদ্রোহীদের কর্তাগিরি করাকেও বৈধ বলে মেনে নেবে এবং প্রজাদের তাদের শাসন মেনে চালারও অনুমতি দেবে। দেখুন কুরআন কি বলেঃ
ক. হে নবী, তাদের বলোঃ আমরা কি তোমাদের বলবো, নিজেদের আমলের দিক থেকে সবচে’ ব্যর্থ ও অসফল লোক কারা? তারা হলো সেইসব লোক, পার্থিব জীবনে যাদের যাবতীয় চেষ্টা সাধনা বিপথগামী হয়েছে। [অর্থাৎ মানুষের চেষ্টাসাধনার মূল উদ্দেশ্য হাসিলের পথে ধাবিত হয়েছে।] অথচ, তারা মনে করছে যে তারা দারুণ ভালো কাজ করছে। এরা হলো সেইসব লোক, যারা তাদের মালিকের আয়াতসমূহ মেনে নিতে অস্বীকার করেছে এবং তাঁর নিকট উপস্থিত হবার বিষয়টিও বিশ্বাস করেনি। তাই তাদের যাবতীয় আমল নিষ্ফল [শূণ্য] হয়ে গেলো। কিয়ামতের দিন আমরা তাদের কোনো গুরুত্বই দেবনা। [সূরা আল কাহাফঃ ৩-৫]
খ. এ হচ্ছে আ’দ [জাতি], যারা তাদের প্রভুর বিধান মানতে অস্বীকার করেছিলো এবং তাঁর রসূলদের আনুগত্য পরিহার করেছিলো আর অনুগামী হয়েছিলো সত্যদীন অমান্যকারী প্রত্যেক দাম্ভিক দুর্দন্ড দুশমনের। [সূরা হুদঃ ৫৯]
গ. আমরা আমাদের নিদর্শন ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদিসহ মূসাকে ফিরাউন আর তার রাজন্যবর্গের প্রতি পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা ফিরাউনের নির্দেশেরই অনুগামী হলো, অথচ ফিরাউনের নির্দেশ সঠিক ছিলোনা [অর্থাৎ বিশ্বসম্রাটের হুকুমের অনুগামী ছিলোনা]। [সূরা হুদঃ ৯২]
ঘ. এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করোনা, যার অন্তরকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে [অর্থাৎ আমি যে তার প্রকৃত মালিক ও মনিব ও অনুভূতি থেকে] গাফল করে দিয়েছি এবং যে স্বীয় কমনা বসনার অনুগামী হবার নীতি গ্রহণ করেছে আর যার কর্মনীতিই সীমালংঘমূলক। [সূরা আল কাহাফঃ ২৮]
ঙ. হে মুহাম্মদ! বলো, আমার প্রভু অশ্লীলতাকে তার গোপনীয় ও প্রকাশ্য সকল দিক সমেত, পাপ কাজকে, অন্যায়ভাবে পরস্পরের প্রতি বাড়াবাড়ি করাকে এবং আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণ ছাড়াই কাউকেও আল্লাহর [কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে] প্রতিপক্ষ বানানোকে হারাম করে দিয়েছেন। [সূরা আল আ’রাফঃ ৩৩]
চ. আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের দাসত্ব করছো, তারাতো কতগুলো নাম ছাড়া আর কিছু নয়, যে নাম তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা নিজেরাই রেখেছিলে। আল্লাহ সেগুলোর সপক্ষে কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। সার্বভৌম ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর। তাঁর নির্দেশ হলো, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো গোলামী করোনা। [ সূরা ইউসূফঃ ৪০]
ছ. সঠিক পথ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেবার পরও যে ব্যক্তি রসূলের সাথে বিরোধ করবে এবং মুমিনদের নীতি আদর্শের বিপরীত পথে চলবে, তাকে আমরা সিদিকে চালাবো, যেদিকে সে নিজেই মোড় নিয়েছে। আর তাকে আমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ করবো, যা খুবই নিকৃষ্ট স্থান। [সূরা আন নিসাঃ ১১৫]
জ. তোমার প্রভূর শপথ [হে মুহাম্মদ], তারা কিছুতেই মুমিন হতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যাপারে তোমাকে বিচারপতি মেনে নেবে। [সূরা আন নিসাঃ ৬৫]
ঝ. যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেদিকে এসো এবং রসূলের নীতি গ্রহণ করো, তখন তুমি এই মানুফিকদের দেখতে পাবে, তারা তোমার কাছ থেকে কেটে পড়ছে। [সূরা আননিসাঃ ৬১]
ঞ. আর তিনি কাফিরদের [অর্থাৎ তাঁর রাজত্বের বিদ্রোহীদের] জন্যে মুমিনদের [তাঁর অনুগতদের] উপর জয়লাভ করার কোনো পথই খোলা রাখেননি। [সূরা আন নিসাঃ ১৪১]
এগুলো হলো কুরআনের অকাট্য সুস্পষ্ট নির্দেশনাবলী। এগুলোতে সন্দেহ সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। আর এই হলো সেই কেন্দ্রীয় আকীদা বিশ্বাস, যার উপর ইসলামের চিন্তাদর্শন, নৈতিক চরিত্র ও সমাজ সভ্যতার ভিত স্থাপন করা হয়েছে। আর মুসলমানরা ততক্ষন পর্যন্ত তাদের ঈমানের দাবী পূরণ করতে পারেনা, যতক্ষণ না তারা ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে। আল্লাহর আইনের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা ছাড়া মুসলমানরা মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করতে পারেনা। তাই তাদের দীন ও ঈমানের দাবীই হলো ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা [খিলাফত] প্রতিষ্ঠিত করা এবং নিজেদের যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহর আইনের ভিত্তিতে মীমাংসা ও পরিচালিত করা। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যেই নবীগণ প্রেরিত হয়েছেন। সে জন্যেই তো হিজরতের পূর্বে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানীতে এই দোয়া করানো হয়েছেঃ
“প্রার্থনা করোঃ প্রভূ, আমাকে যেখানেই নিয়ে যাবে সত্যতার সাথে নিয়ে যেয়ো। আর যেখানে থেকেই বের করবে সত্যতার সাথেই বের করো। আর তোমার পক্ষ থেকে একটি ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।” [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৮০]
অর্থাৎ, হয় আমাকেই ক্ষমতা দান করো, নয়তো অপর কোনো রাষ্ট্রকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও, যেনো আমি তার ক্ষমতার সাহায্য নিয়ে বিশ্বের এই মহাবিপর্যয়কে প্রতিরোধ ও সংশোধন করতে পারি। যেনো অশ্লীলতা ও পাপের এই প্লাবনের মোকাবিলা করতে পারি। যেনো তোমার সুবিচারপূর্ণ আইনকে কার্যকর করতে পারি। হাসান বসরী এবং কাতাদা (র) এ আয়াতের এই তাফসীরই করেছেন। ইবনে কাসীর এবং ইবনে জরীরের মতো মর্যাদাবান মুফাসসিরগণও এ মতই প্রকাশ করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটিও এ ব্যাখ্যারই সমর্থন করে। তিনি বলেনঃ
“আল্লাহ রাষ্ট্র ক্ষমতার সাহায্যে সেইসব জিনিসও বন্ধ করে দেন, যা কেবল কুরআন দ্বারা বন্ধ হয়না।”
এ থেকে প্রমাণ হলো, ইসলাম বিশ্বে যে সংস্কার সংশোধন চায়, তা শুধুমাত্র উপদেশ নসীহতের মাধ্যমে সম্পন্ন হতে পারেনা। তা কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্রক্ষমতাও অপরিহার্য। তাছাড়া আল্লাহ নিজেই যখন তার নবীকে এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তা থেকে তো একথা পরিষ্কারভাবেই প্রমাণ হয় যে, আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর শরীয়াকে কার্যকর করা এবং তার আইন ও বিধানকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে চাওয়া এবং তা পাওয়ার জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা যে শুধু জায়েয তাই নয়, বরঞ্চ কাম্য এবং মংগলজনকও বটে। যারা এই কাজকে দুনিয়া পূজা বা দুনিয়াদারী বলে মনে করে, তারা সাংঘাতিক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তবে একথা সত্য, যদি কেউ নিজের জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে চায়, তবে তা নিসন্দেহে দুনিয়া পূজা। কিন্তু ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর করার জন্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা পেতে চাওয়া কোনোক্রমেই দুনিয়া পূজা হতে পারেনা। বরঞ্চ আল্লাহর গোলামী করার প্রকৃত দাবীই এটা।
৩. ইসলাম ও কর্তৃত্ব [এ নিবন্ধটি তরজমানুল কুরআন ১৯৪২ইং সেপ্ট-নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।]
এ যাবতকার আলোচনা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তার কথা সুস্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু যেহেতু বিভিন্ন কারণে ধর্ম রাজনীতিকে আলাদা করণের শয়তানী দর্শন স্বয়ং মুসলমানদের মন মগজকেও প্রভাবিত করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রয়োগ করে তারা এই বিভক্তির সপক্ষে অবকাশ সৃষ্টির অপচেষ্টা করছে, সেজন্যে এখন আমরা খতিয়ে দেখবো, আসলে ইসলাম কোন ধরনের বিপ্লব সংঘটিত করতে চায় আর এ ব্যাপারে যেসব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রচার করা হচ্ছে সেগুলোর উৎস কোথায়? সূরা বাকারায় ১৯৩ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ
“যতক্ষন ফিতনার অবসান না ঘটে এবং দীন একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে না হয়ে যায় ততক্ষন তাদের সাথে লড়াই চালিয়ে যাও। এরপর যদি তারা ক্ষ্যান্ত হয় তাহলে যালেমদের ওপর ছাড়া আর কারো ওপর বাড়াবাড়ি করা বৈধ নয়।”
তাফহীমুল কুরআনে এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে, “ক্ষ্যন্ত হওয়ার অর্থ কাফিরদের শিরক ও কুফরী পরিত্যাগ করা নয়, বরং ফিতনা থেকে ক্ষ্যান্ত হওয়া।” কাফির, মুশরিক, নাস্তিক প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে, যার যা ইচ্ছা আকীদা পোষণ করুক, যার খুশী পূজা উপসনা করুক অথবা একেবারেই কারো পূজা উপাসনা না করুক। এ ভ্রষ্টতা থেকে তাকে বের করে আনার জন্য আমরা তাকে বুঝাবো এবং উপদেশ দেবো ঠিকই, কিন্তু তার সাথে লড়াইতে লিপ্ত হবোনা। তাবে এ অধিকার তার কখনো নেই যে, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে নিজের বাতিল আইন চালু করবে এবং আল্লাহর বান্দাদেরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করবে।
“তারবারী দিয়েই এ ফিতানার উচ্ছেদ ঘটাতে হবে এবং কাফিররা যতক্ষণ তাদের বর্তমান আচরণ থেকে বিরত না হবে, ততক্ষণ মুমিনরা অস্ত্র সংবরণ করবেনা।”
তফসীরের এ রেখাচিহ্নিত অংশটুকু সম্পর্কে তরজুমানুল কুরআনের পাঠকবর্গের মধ্য থেকে জনৈক বিদ্ব্যান নিম্নরূপ আপত্তি তুলেছেনঃ
ক. এর মানে হলো, ইসলাম যা কিনা শান্তি ও নিরাপত্তার সমর্থক, সে অন্যদের ধর্মে হস্তক্ষেপ এবং সে জন্য লড়াইয়ের অনুমতি দেয়। অথচ এ কাজটা সূরা বাকারার ২৫৬ নং আয়াতের لاَ اِكْرَاهُ فِى الدِّيْنِ “ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই” – এর বিপরীত।
খ. ইসলাম বিরোধীদের নিজ নিজ ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর অবিচল থাকার স্বাধীনতা সূরা কাফিরুনের শেষ আয়াতঃ
“তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম আর আমার জন্য আমার ধর্ম।”
এ থেকেও সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি আকীদা ও বিশ্বাসে স্বাধীন, তার সে আকীদা বিশ্বাস প্রচার করারও স্বাধীনতা থাকা উচিত, কেননা সে ঐসব আকীদাকেই সঠিক মনে করে। কুরআনের বক্তব্য থেকে এ স্বাধীনতার সমর্থন পাওয়া যায় এবং পারস্পরিক বিতর্কেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমনঃ
“সর্বোত্তম পন্থায় ব্যতীত আহলে কিতাবের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়োনা।” [সূরা আনকাবূতঃ ৪৫]
তাদের উপাসনালয় এবং উপাসনা পদ্ধতি ইসলামের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থেকেছে। এমনকি মসজিদে নববীতে পর্যন্ত আহলে কিতাবকে নিজস্ব পদ্ধতিতে উপাসনা করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। মিসরের শাসক আযীয যার আকীদা ও কার্যকলাপ মুশরিকদের মতো ছিলো- হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তার চাকরি করেছিলেন।
অবশ্য তিনি শন্তিপূর্ণ উপায়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে ইসলামের প্রচার চালিয়ে গেছেন। যেমন সূরা ইউসুফের ৩৯ নং আয়াতঃ
“হে আমার কারাগারের সাথীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন প্রভু থাকা ভালো, না এক, অদ্বিতীয় ও মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ ভালো?
এ থেকে বুঝা যায় যে, এভাবে অন্যদেরও নিজ নিজ ধ্যান ধারণা প্রচার করার অধিকার রয়েছে।
গ. রেখাচিহ্নিত কথা কয়টির আলোকে মুসলমানরা কোথাও মিশ্র জনবসতিতে নিরূপদ্রব জীবন যাপন করতে পারেনা। অমুসলিমরা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়েও মুসলমানদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও উদায় নীতির ভিত্তিতে আচরণ করবে কোন কারণে যখন তাদের রাজনৈতিক ও মৌলিক আকীদাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়? এ ধরনের মুসলমানরা ইরান ও তুরস্কে বসবাস করলেও আপনার কথামতো তাদেরকে সেখানেও জিহাদের পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কেননা সেসব দেশে ইসলামের আইন ও ফৌজদারী বিধি চালু নেই। এযুগে বিশ্বরাজনীতি এমন ধারায় প্রবাহিত যে, কোনো দল অস্বাভাবিক ও অপ্রচলিত পন্থায় অমুসলিমদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও লেনদেন চালাতে পারেনা। কেননা আপনার কথিত যুক্তি যে কোনো ধরনে যৌথ কর্মকান্ডের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। মুসলিম জনগোষ্ঠী যদি স্বীয় আকীদা বিশ্বাস প্রচার করার অধিকার হয়, তাহলে অমুসলিমদেরকেও সে অধিকার দিতে হবে, বিশেষত তারা যদি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। যে জিনিস নিজের জন্য পছন্দ নয়, তা অন্যের জন্য পছন্দ করোনা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার ইহুদী জনগোষ্ঠির সাথে পারস্পরিক আচরণবিধি স্থিরপূর্বক যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, যে চুক্তি এ ধরনের শর্তের ভিত্তিতেই সম্পাদিত হয়েছিলো? মক্কী জীবনের প্রাথমিক স্তরটা আপনার যুক্তির পক্ষে নয়। অন্য কথায়, একটি অমুসলিম সরকারের জন্য এ ধরনের জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব একটা প্রকাশ্য হুমকি, যে জনগোষ্ঠী সুযোগ পেলেই ঐ সরকারের আইন ও শাসন ব্যবস্থা উৎখাত করার জন্য অস্ত্র ধারণ করবে । তাদেরকে কে বরদাশত করবে?
এ আপত্তির সংক্ষিপ্ত জবাব কয়েকটি মাত্র বাক্যে দিয়েও দেয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ আপত্তিটার মূলে রয়েছে ভুল বুঝাবুঝির এক বিরাট স্তূপ। মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণাসমূহ ব্যাপক আকারে ছাড়িয়ে পড়েছে। এমনকি এর ফলে মুসলিম জনগণ সামগ্রিকভাবে নিজেদের ধর্মের মৌলিক দাবী বুঝতেও অক্ষম হচ্ছে। এজন্য এখানে ব্যাপারটা নিয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো।
ইসলামী মিশন
ইসলাম শান্তির ধর্ম কোন অর্থে? আরবী************* এবং আরবী************ এর প্রকৃত মর্ম কি? আর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের লক্ষ্য নবূয়্যতের দায়িত্ব পালন করা ছিলো নাকি জীবিকার অন্বেষণ করা? সেসব আলোচনা পরে করা যাবে। এসব বিষয়ের আগে যে প্রশ্নের সমাধান হওয়া প্রয়োজন তাহলো, পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি? স্বৈরাচারী লোকেরা যাতে মানুষের ঘাড়ে চড়াও হতে পারে, তারই সুবিধা করে দেয়ার জন্য মানুষকে তৈরী করতে কি ইসলামের আবির্ভাব ঘটেছিলো? এক একজন স্বৈরাচারী একনায়ক যখনই পৃথিবীতে আপন প্রভুত্ব কায়েম করতে আসবে, তখন ইসলামের অনুসারীদেরকে যাতে নিজের অনুগত ভৃত্য হিসেবে পেতে পারে, সেজন্যই কি ইসলাম এসেছিলো? সে কি সারা পৃথিবীর সরকারসমূহের ও সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য শান্তিপ্রিয় প্রজা সংগ্রহ করে দেয়ার ইজারা নিয়েছিলো যে, যেকোনো ধরনের মতাদর্শের অনুসারী শাসকরা নিজেদের রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার জন্য েইসলামের কারখানা থেকে তৈরী যন্ত্রাংশ পেয়ে কৃতার্থ হবে? ইসলামের কাজ কি শুধু এই যে, কিছু মৌলিক আকীদা ও নৈতিক আদর্শ শিক্ষা দিয়ে মানুষকে এতটা বিনয়াবনত ও নমনীয় করে গড়ে তুলবে যাতে সে সকল ধরনের সমাজ ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে? ব্যাপার যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে ইসলাম বৌদ্ধ ধর্ম ও সেন্ট পলের গড়া খৃষ্ট ধর্ম থেকে পৃথক কিছু নয়। আর তেমনটি হলে এটা আমাদের জন্য দুর্বোধ্য যে, এমন ধের্মের গ্রন্থে قَاتِلُوْهُم [তাদের সাথে লড়াই কর] এর মতো ভয়ংকর শব্দ উচ্চারণই বা হলো কেমন করে? এরতো নিজের অনুসারীদেরকে জিহাদ ও যুদ্ধের নির্দেশ দেয়ার পরিবর্তে শত্রুদেরকেই এবলা উচিত ছিলোঃ
“আমরা হতভাগাদের তোমরা কেন মারছ? আমরা শাসন ব্যবস্থায় কোনো বিপ্লবও আনতে চাইছিনা, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায়ও কোনো রদবদল ঘটাতে চাইছিনা। ক্ষমতা যার হাতেই থাক, তার অধীনে শান্তশিষ্ট নাগরিক হিসেবে বাস করাই আমাদের নীতি এবং ক্ষমতাশীন সরকারের আনুগত্যই আমাদের ঈমান ও ধর্ম। এমতবস্থায় আমাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা পোষণের কি কারণ থাকতে পারে? আমাদের ধর্ম বিশ্বাস ও পূজা উপাসনার রীতি প্রথা নিয়ে আপত্তি? কিন্তু এতে তোমাদের অসুবিধা কি? তোমাদের কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং কোন স্বার্থ আমাদের উপাসনায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?
এ জবাব যদি যথার্থ লাগসইভাবে দেয়া হতো এবং কার্যত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর অনুসারীগণ আনুগত্য সহকারে সমাজ সেবার কাজ চালিয়ে যেতেন, তাহলে মক্কার মুশরিকরা আমাদের ইংরেজ প্রভুদের তুলনায় এতো বেশী গোঁয়ার ও কান্ডজ্ঞানহীন ছিলোনা যে, মসজিদে আযান ও নামাযের স্বাধীনতা এবং ধর্ম প্রচারণামূলক সমিতি ইত্যাদি করার স্বাধীনতাও দিতোনা। [উল্লেখ যে, এ নিবন্ধ ১৯৪২ সালে লেখা হয়েছিলো।]
কিন্তু বাস্তব ব্যাপার যদি সেরকম না হয়ে থাকে, বরং ইসলামের যদি নিজস্ব জীবন ব্যবস্থা যাতে আকীদা বিশ্বাস এবং আখলাক ও ইবাদতের পাশাপাশি ব্যক্তিগত কর্মকান্ড ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় তৎপরতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিধি নির্দেশ থেকে থাকে, যদি ইসলামের আহবান তার সমগ্র জীবন ব্যবস্থাই সত্য ও নির্ভুল এবং একমাত্র তাতেই মানুষের সঠিক কল্যাণ নিহিত, আর এছাড়া অন্য প্রত্যেকটি জীবন ব্যবস্থাই বাতিল ও ভ্রান্ত, তাহলে এসবের সাথে সাথে এটাও অনিবার্য হয়ে উঠে যে, ইসলাম পৃথিবীতে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে বিজয়ী এবং অন্য সকল ব্যবস্থাকে পরাভূত করার দাবী জানাবে। একটি জীবন ব্যবস্থাকে সত্য ও সঠিক বলে দাবী করার পর কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার দাওয়াত না দেয়া একটা সম্পূর্ণ অর্থহীন ব্যাপার। আর এর চেয়েও অর্থহীন ব্যপার হলো, অন্যান্য জীবন ব্যবস্থাকে বাতিলও বলা হবে আবার তার বিজয়কেও বরদাশত করা হবে। তাছাড়া একটা জীবন ব্যবস্থার অধীন বসবাস করে আর একটা জীবন ব্যবস্থার অনুকরণ ও অনুসরণ করা একেবারেই অসম্ভব। তাই একই সময় নিজের উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার অনুকরণেরও দাবী জানানো আবার সেই সাথে অন্য ব্যবস্থার অধীন শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের শিক্ষা দেয়া একজন উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব।
সুতরাং ইসলাম যদি নিজের বিশেষ ধাঁচের জীবন ব্যবস্থার দিকে দাওয়াত দিযে থাকে, তাবে সেই দাওয়াতের স্বাভাবিক তাগিদেই তার এ দাবী জানানোও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় যে, অন্যান্য ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার স্থলে তার নিজস্ব ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা হোক। তাছাড়া যতো উপায়ে চেস্টা তদবীর ও সংগ্রাম করলে এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে থাকে, তার সব ক’টি উপায় অবলম্বনের দাবী জানানোও তার জন্য অনিবার্য হয়ে ওঠে। এমনকি যারা তার অনুসারী হবার দাবীদার, তারা জান মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে এই চেষ্টা সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়, না বাতিল ব্যবস্থার অধীন জীবন যাপন করতে রাজী থাকে এ প্রশ্নকেই সে উক্ত দাবীদারদের ঈমান যাচাইয়ের মানদন্ড নির্ধারণ করা জরুরী মনে করে। কুরআন ও হাদীস দুটোই খুলে দেখুন। সুস্থ মন দিয়ে অধ্যয়ন করলে আপনি দেখতে পাবেন, ইসলামের আসল নীতি এটাই, আপনি যেটা বলছেন সেটা নয়।
এই যখন ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ এবং স্বরূপ জেনেই যখন আমরা ইসলামের প্রতি ঈমান এনেছি, তখন যেকোনো ইসলাম বিরোধী সরকারের জন্য আমাদের অস্তিত্বই যে হুমকি বলে বিবেচিত হবে, সেটা তো বলাই বাহুল্য। কেউ সহ্য করুক বা না করুক এবং অমুসলিমদের সাথে আমাদের সহযোগিতা ও পারস্পরিক সদ্ভাব সম্ভব হোক বা না হোক, আমরা আমাদের ঈমানে নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী হলে সেখানেই আল্লাহর আইন চালু নেই সেখানে তা চালু করার যথাসাধ্য চেষ্টা আমাদের করতেই হবে। আমাদের মুসলমান হওয়া এরূপ শর্ত যুক্ত নয় যে, যারা আল্লাহর অবধ্য তারা আমাদের এই চেষ্টা সাধনাকে বরদাশত করলেই আমরা মুসলমান থাকবো এবং আল্লাহর আইন চালু করার চেষ্টা করবো অন্যথায় নয়। অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা ও সদ্ভাবও আমাদের জন্য এমন ব্যাপার নয় যে, যে জীবন ব্যবস্থার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি, তার বাস্তবায়নের চেষ্টা করলে অমুসলিমদের সাথে সহযোগিতা ও সদ্ভাব সম্ভব হবেনা বলে আমরা সে চেষ্টা পরিত্যাগ করবো। নিঃসন্দেহে ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার রক্ষক ও সমর্থক। তবে তার দৃষ্টিতে যে শান্তি ও নিরাপত্তা আল্লাহর বিধান কার্যকর করার মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেটাই প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা। শয়তানী শাসন ব্যবস্থার অধীন যাবতীয় কাজকারবার নিরূপদ্রবে চলতে থাকবে আর মুসলমানরা তাতে কিছুমাত্র বিব্রতবোধ করবেনা, এটাকে যারা শন্তি ও নিরাপত্তা অর্থ মনে করছেন তারা ইসলামের দৃষ্টিভংগিকে মোটেই বোঝাননি। তাদের জানা উচিত যে, ইসলাম কখনো এ ধরনের শন্তি ও নিরাপত্তার সমর্থন ও পক্ষপাতী নয়। বাতিল শক্তির প্রতিষ্ঠিত শান্তি নয়, বরং নিজের প্রতিষ্ঠিত শান্তিই তার কাম্য এবং এতেই সে মানুষের সার্বিক কল্যাণ দেখতে পায়।
এখন প্রশ্ন জাগে, তাহলে “ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই” একথাটার মর্ম কি? এর মর্ম শুধু এই যে, ইসলাম তার আকীদা বিশ্বাসকে মেনে নিতে কাউকে বাধ্য করেনা। কেননা এটা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার জিনিস নয়। অনুরূপভাবে, তার আকীদা বিশ্বসাসের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ইবাদতকেও সে কারোর ওপর বল প্রয়োগ চাপিয়ে দেয়না। কেননা সুষ্ঠু ঈমান ছাড়া এসব ইবাদত একেবারেই অর্থহীন। এই দুটো ব্যাপারেই সে প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ইসলাম এটা সহ্য করতে প্রস্তুত নয় যে, সমাজ ও সভ্যতাকে পরিচালনাকারী যে আইন ও বিধানের ওপর রাষ্ট্রের কাঠামো ও বিধিব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় তা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ রচনা করে দিক, আল্লাহর বিদ্রোহী ও অবাধ্য লোকেরা আল্লাহর যমীনে তার প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন করুক এবং মুসলমানরা তাদের তাবেদার হয়ে থাকুক। এব্যাপারে একটি জনগোষ্ঠীকে অন্য জনগোষ্ঠীর “ধর্মে” অবশ্যই হস্তুক্ষেপ করতে হবে। মুসলমানরা যদি “কুফরী ধর্মে” হস্তক্ষেপ না করে তাহলে কুফরী আদর্শের অনুসারীরা “ইসলাম ধর্মে” হস্তক্ষেপ করেই ছাড়বে। আর এর ফল এই দাঁড়াবে যে, মুসলমানদের জীবনের একটা বিরাট অংশে কুফরী ব্যবস্থা প্রচলিত হয়ে পড়বে। সুতরাং হস্তক্ষেপটা খোদাদ্রোহীদের পক্ষ থেকে না হয়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে হোক এবং মুসলমানরা সামনে অগ্রসর হয়ে গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রকে দখল করে নিক এটাই ইসলামের দাবী ও তাগিদ। একাজটা সম্পন্ন হওয়ার পর কেবলমাত্র আকীদা বিশ্বাস ও ইবাদত উপাসনার প্রশ্নে অমুসলিমদের সাথে “ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই” এই নীতি অনুসরণ করতে হবে।
উদারতার ভ্রন্ত ধারণা ও তার পর্যালোচনা
আলোচ্য আপত্তি উত্থাপক ভদ্রলোক যেসব যুক্তির আশ্রয় নিয়েছেন এবং যার ওপর তার সমমনা লোকেরা সাধারণত আস্থাশীল হয়ে থাকেন এবার সেই যুক্তিগুলোর ওপর একটা নজর বুলানো যাক।
তার পয়লা যুক্তি হলো, আপনি যখন ফিতনা শব্দটি কুফরী ব্যবস্থার বিজয় এবং কুফরী ব্যবস্থার ধারকবাহক ও অনুসারীদের পরাক্রম ও প্রভুত্ব অর্থে গ্রহণ করেন, আর আপনার এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সে জিনিস ফিতনা পদবাচ্য তাকে উৎখাত করে তদস্থলে আল্লাহর দীন কায়েম করাকেই যখন জিহাদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করেন, তখন এটা স্বীকার না করে উপায় থাকেনা যে, ইসলাম একটা দুমুখো ও পরস্পর বিরোধী ভূমিকা অবলম্বন করবে। একদিকে সে ঘোষণা করছে যে, ইসলামে কোনো জবরদস্তি ও বল প্রয়োগের স্থান নেই। অপরদিকে সে অমুসলিমদের নিজস্ব আদর্শ ও মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার দিতে অস্বীকার করছে এবং তাদের আইন প্রয়োগ বন্ধ করে জোরপূর্বক তাদের ওপর “আল্লাহর দীন” চাপিয়ে দিতে চাইবে। একদিকে সে তোমার জন্য তোমার ধর্ম এবং আমার জন্য আমরা ধর্ম” বলে সকল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে নিজ নিজ ধর্মমতের ওপর অবিচল থাকার স্বাধীনতা দেয়। অপরদিকে, তারা নিজেদের নীতি আদর্শ অনুসারে দুনিয়ার কর্মকান্ডে পরিচালনা কেন করে এ প্রশ্ন তুলেই তাদের সাথে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। ইসলামে এতো বড় স্ববিরোধিতা যে থাকতে পারেনা, তা সর্বজন বিদিত। অতএব, আপনার ব্যাখ্যাটিই আসলে ভুল।
দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ইসলাম বিরোধী সরকারের অস্তিত্বই যদি ইসলামের দৃষ্টিতে ফিতনা হতো এবং তার উচ্ছেদ ঘটানোর জন্য যদি মুসলমানরা আদিষ্ট হতো, তাহলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিসরের অনৈসলামিক সরকারে মন্ত্রীত্ব চাওয়া কিভাবে সম্ভব হয়েছিলো এবং স্বীয় মন্ত্রীত্বের আমলে মিসরের রাজকীয় আইনের অনুগত থেকে কাজ করাই বা তার পক্ষে কিভাবে সঙ্গত হয়েছিলো। সূরা ইউসূফের ৭৬ নং আয়াতেঃ
“রাজকীয় আইনে আপন ভাইকে গ্রেফতার করা তাঁর সম্ভব ছিলোনা।”
এ থেকে বুঝা যায় যে, তিনি রাজকীয় আইনের ঊর্ধে ছিলেননা।
তৃতীয় যুক্তি এই যে, আয়াতের যে ব্যাখ্যা আপনি দিয়েছেন তি সঠিক বলে মেনে নিলে এটা স্বীকার করতে হয় যে, ইসলাম পৃথিবীতে একটা চিরস্থায়ী যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে সচেষ্ট এবং তার অনুসারীদেরকে আগ্রাসী যুদ্ধ চালানোর এমন দায়িত্ব অর্পন করে যার দরুন মুসলমানরা দুনিয়ার কোথাও শান্তিতে থাকতে পারেনা। সত্যি বলতে কি, এ তফসীর অনুসারে, শুধু দুনিয়ার সকল অমুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই নয়, বরং যেসব মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী আইন চালু নেই তার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ ঘোষণা করা আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে। আর এটাই যখন আমাদের আদর্শ এবং ধর্মীয় কর্তব্য, তখন অমুসলিমরা আমাদেরকে তাদের শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশী ভেবে আমাদের সাথে নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে এবং অমুসলিম রাষ্ট্রসমূহ তাদের আওতাভুক্ত এলাকায় আমাদের অস্তিত্ব বরদাশত করবে এটা কিভাবে সম্ভব?
১. উল্লিখিত যুক্তিগুলোর মধ্যে প্রথমটা একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে উত্থাপন করা হয়েছে। কোনো ব্যক্তির একান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়ে একটা মতবাদে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং নিজের ব্যক্তিগত জীবনে একটা বিশেষ নিয়ম নীতি অনুসরণ করা এক কথা, আর তার নিজ মতাদর্শ অনুসারে সামষ্টিক জীবনের জন্য একটা পদ্ধতি গড়ে তোলে এবং সেই পদ্ধতিটা জোরপূর্বক একটি দেশের জনজীবন চালু করে দেয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। [উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্র মূলত বল প্রয়োগ ও জবরদস্তিরই Coercive আর এক নাম। যে মতবাদ, মূলনীতি ও আইন কোনো রাষ্ট্রের ভিত্তিরূপে বিবেচিত হবে, সেটা যে ঐ রাষ্ট্রের আওতায় বসবাসকারী সকল মানুষের ওপর বল প্রয়োগই চালু করা হবে, সেটা সর্বজনবিদিত।] আপত্তি উত্থাপনকারীরা এই দুটো বিষয়কে এক মনে করে বসেছেন এবং দুটোর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা উপেক্ষা করে “ইসলামে জোর জবরদস্তি নেই” এবং “তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম” এ দুটো আয়াতকে উক্ত দুটো বিষয়ের ওপর সামষ্টিকভাবে প্রয়োগ করেছেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ আয়াত দুটোর সম্পর্ক প্রথম ব্যাপারটার সাথে। একথা সত্য যে, আমরা কোনো অমুসলিমকে তার আকীদা বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস গ্রহণ ও নিজস্ব ধর্মীয় পূজা অর্চনা পরিত্যাগ করে নামায, রোযা পালন করতে বাধ্য করবোনা। তবে আমরা তার এ অধিকার স্বীকার করতে পারিনা যে, সে নৈতিকতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি ও আইন ইত্যাদি সামষ্টিক ব্যাপারে আপন মতবাদগুলোকে নিজস্ব নিয়মনীতি অনুসারে চলতে দেয়া নিঃসন্দেহে পরমত সহিষ্ণুতা। কিন্তু আমাদের নিজস্ব নিয়মনীতির বিরুদ্ধে আমাদের ওপর অন্যদের মতাদর্শ ও রীতিনীতি চাপিয়ে দেয়াকে বরদাশত করা কোনো পরমত সহিষ্ণুতা নয়। দেশের শাসন ব্যবস্থা যে জীবন দর্শনের ভিত্তিতে গঠিত হবে ঐ দেশের সমস্ত আইন কানুন, সমগ্র প্রশাসনিক নীতি এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম সেই দর্শনের ভিত্তিতে চলতে বাধ্য। আর এ ধরনের শাসনব্যবস্থার অধীনে বাস করে আমাদের জীবনধারাকে আমাদের নিজস্ব ধর্ম ও মতাদর্শ অনুসারে পরিচালিত করা আমাদের পক্ষে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা রাজী হই বা না হই, বিরুদ্ধবাদী ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের রাজনৈতিক পরাক্রম ও আধিপত্যের দাপটে আপন মতাদর্শকে, জোরপূর্বক আমাদের সমগ্র জীবনে প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করে ছাড়বে। এব্যাপারে নমনীয়তা, উদারতা বা পরমতা সহিষ্ণুতা প্রদর্শনের অর্ত হলো, তারা যদি ব্যভিচারকে বৈধ মনে করে এবং জনগণকে এ ব্যাপারে আবাধ অনুমতি দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের সরকারের নিরুপায় প্রজা হিসেবে স্বয়ং আমাদের সমাজে ব্যভিচারের বিস্তার ঘটতে থাকবে আর আমরা তা নীরবে বরদাশত না করে পারবোনা। তারা যদি সুদকে বৈধ মনে করে এবং তাদের সরকার স্বয়ং সুদভিত্তিক লেনদেন করতে অভ্যস্ত হয়ে থাকে, তাহলে দেশের প্রশাসন তাদের হাতে থাকার কারণে আমাদের একজন অতি বড় পরহেজগার লোকও সুদের কুলষতা থেকে রেহাই পাবেনা। এমনকি একটা দিয়াশলাই এবং এক টুকরো রুটিও আমরা কিনতে পারবোনা যতক্ষণ না তার মূল্য থেকে সুদের একটা অংশ পরোক্ষ করের আকারে আমাদের পকেট থেকে বেরিয়ে যায়। তারা যদি নাস্তিক্যবাদী মতবাদে বিশ্বাসী হয় তাহলে দেশের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা কাঠামো এই নাস্তিক্যবাদী চরিত্রের আলোকেই গড়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, এহেন নরকের দরজা ছাড়া দেশবাসীর জন্য উন্নতি ও সমৃদ্ধির অন্য সকল দরজা রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর আমাদের অতি বড় কোনো খোদাভীরু লোকও আপন বংশধরকে সেই সান্তিক্যবাদী মতাদর্শ ও নৈতিকতার প্রভাব থেকে বাঁচাতে সক্ষম হবেনা। তারা যদি আল্লাহর আইনকে বাতিল করে নিজস্ব আইন রচনা করে এবং দেশের সমাজব্যবস্থাকে নিজেদের রচিত আইনের ভিত্তিতে গড়ে তোলে, তাহলে আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের একটা বিরাট অংশ আমরা যে আইনবিধির ওপর ঈমান এনেছি, তার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যেতে বাধ্য হবে এবং সে আইনবিধিতে আমাদের ঈমান ও আস্থা নেই তার অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে। এটা কি ধরনের পরমত সহিষ্ণুতা এবং কি ধরনের উদার নীতি? “ধর্মে জোর জবরদস্তি নেই” আয়াতটার এ অর্থ কোন যুক্তিতে এবং কোন বিবেকের রায় অনুসারে শুদ্ধ হতে পারে যে, অন্যদের পক্ষ থেকে আমাদের ধর্মের ওপর যে বল প্রয়োগ করা হবে তা আমরা বরদাশত করবো?
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা
একথা অনস্বীকার্য যে, সামষ্টিক জীবনের শৃংখলা বহাল রাখার জন্য সর্বাবস্থায়ই একটা বল প্রয়োগকারী শক্তি Coercive Power থাকা প্রয়োজন এবং তাকেই রাষ্ট্র বলা হয়। নৈরাজ্যবাদীরা ছাড়া কেউ এর প্রয়োজনীয়তা আজ পর্যন্ত অস্বীকার করেনি। সমাজতান্ত্রিক দর্শনেও এমন একটা স্তর কল্পনা করা হয়েছে, যেখানে পৌছে মানুষের সামষ্টিক জীবন রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা আর অনুভাব করেনা। [এখানে গ্রন্থকার সমাজতন্ত্রের সর্বশেষ স্তরের প্রতি ইংগিত করছেন। এ সম্পর্কে স্বয়ং এঞ্জলস এবং লেলিনের বক্তব্য হলো, এতে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ কাঠামো তিরোহিত হয়ে যাবে এবং এমন একটি শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা পরিচালিত হবে সামাজিক সহযোগিতার ভিত্তিতে এবং যাতে রাষ্ট্রের কোনো অস্তিত্ব থাকবেনা। লেলিন লিখেছেনঃ
কেবল সমাজতন্ত্রই রাষ্ট্রকে নির্ঘাত নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত করে দেয়। তাই সেখানে এমন কোনো শ্রেণী অবশিষ্ট থাকেনা যাকে দমন ও নির্মূল করা যেতে পারে। [Lenin: the state and revolution, N.Y. 1935, P-75] এ প্রক্রিয়ার রাষ্ট্রকে সমাজতন্ত্রের পরিভাষায় বলা হয় The State within away [সংকলক]] কিন্তু এসব কথাবার্তা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। এসব কথার সপক্ষে কোনো অভিতজ্ঞতা বা চাক্ষুস সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করা সম্ভব নয়। বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা এবং মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞান থেকে একথাই জানা যায় যে, সুসভ্য ও সমাজবদ্ধ মনব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য একটা “দমনমূলক শক্তি”র প্রয়োজনীয়তা সন্দেহাতীত। তথাপি এ কথাও অবস্বীকার্য যে, আপন অজেয় ক্ষমতা ও পরাক্রমশীলতার জোরে সমাজ ও সভ্যতার অবকাঠামোকে সংরক্ষণকারী এই দমনমূলক শক্তি তথা রাষ্ট্র শক্তি নিজেও কোনো না কোনো মতবাদ এবং কোনো না কোনো সামষ্টিক নীতির প্রবক্তা ও পাতাকাবাহী হয়ে থাকে। সেই মতবাদ ও নীতির আলোকে সে নিজের জন্য একটা কর্মসূচী রচনা করে। সে আপন দোর্দন্ড ক্ষমতা প্রয়োগ করে সমাজ এই কর্মসূচীকেই জীবনে বাস্তবায়িত করে। আর এই দোর্দন্ড ক্ষমতার ধরন এবং এই কর্মসূচীর নীতিগত ও বিস্তারিত রূপটির ভূমিকা সভ্য সমাজ জীবনের ভাঙ্গাগড়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবল সামষ্টিক জীবন নয়, ব্যক্তিগত জীবনও অনেকাংশে ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, রাষ্ট্রিয় আধিপত্য ও পরাক্রমের প্রভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবিত হয়ে যেতে বাধ্য হয়। একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীরা ঐ রাষ্ট্রের মতবাদ ও বিস্তারিত কর্মসূচীতে বিশ্বাসী ও সম্মত না হলেও তাদেরকে বাধ্য হয়ে নিজেদের বিশ্বাস ও আদর্শের শতকরা ৯০ ভাগকে পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রিয় আকীদা ও আদর্শ অনুসারে চলতে হয়। আর বাদবাকী ১০ ভাগেও তাদের আকীদা ও আদর্শের নিয়ন্ত্রণ ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে যেতে থাকে। রাষ্ট্রের এই বৈশিস্ট্যের প্রতি দৃষ্টি দান এবং সামষ্টিক জীবনে রাষ্ট্রের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করার পর একজন চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে একথা বুঝা মোটেই কঠিন নয় যে, কোনো মানবগোষ্ঠী যদি প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে কেবল ধর্মের অনুসারী না হয়ে একটা সর্বব্যাপী জীবন ব্যবস্থা অর্থাৎ দীনের প্রতি বিশ্বাস হয়, তারা আপন বিশ্বাসে নিষ্ঠাবান ও সত্যবাদী হয় এবং আপন বিশ্বাসের বিপরীত জীবন যাপন করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে যে রাষ্ট্র সমাজ জীবনের সর্বাত্মকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা এবং আপন শক্তি দ্বারা তাকে বহাল রাখার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, সেই রাষ্ট্রকে করায়ত্ত্বে করার চেষ্টা করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর নেই। তারা যদি রাষ্ট্রকে করায়ত্ত্ব না করে, তবে অন্যরা করবে এবং তখন এই গোষ্ঠী নিজেদের জীবনের অন্তত শতকরা ৯০ ভাগ ব্যাপারে নিজেদের পছন্দসই দীন বা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্যদের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করতে বাধ্য হবে। সুসভ্য মানব জীবনে বল প্রয়োগের এ কাজটা আমাদের কোনো না কোনো পক্ষকে করতেই হবে। আমরা না করলে খোদাদ্রোহীরা করবে। সুতরাং ইসলাম বিরোধীরা এ পরিমন্ডলে আমাদের ওপর বলপ্রয়োগ করবে এবং আমাদেরকে টেনে হিচঁড়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে তার চেয়ে ভালো আমরাই তাদের ওপর বল প্রয়োগ করে তাদের এমন অবস্থান গ্রহণ করতে বাধ্য করি, যেখানে থেকে তারা ইচ্ছা করলে সহজেই বেহেশতের পথের সন্ধান লাভ করতে পারে।
এ হলো ব্যাপারটার একটা দিক। এর আর একটা দিক হলো, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ তায়ালা। তাঁর পৃথিবীতে বাস করে তাঁর নেয়ামতরাজি ভোগ করা এবং তাঁর মালিকানাধীন সম্পদ ব্যবহার করার অধিকার কেবল তাঁর বান্দাদেরই থাকতে পারে, যারা তাঁর প্রাকৃতিক ও শরীয়তী আইন কানুন অনুসরণ করে। যারা তা করেনা তারা যালিম, অনধিকার চার্চাকারী ও বিদ্রোহী। তাদের এই অনধিকার চর্চা কেবল অন্যায়ই নয়, বরং পৃথিবীর প্রশানসে অরাজকতা সৃষ্টি এবং পৃথিবীবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ও অতিষ্ঠ করে তোলার নামান্তর। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, যারা খোদাদ্রোহী এবং খোদার প্রাকৃতিক ও শরীয়তী বিধানের বিরুদ্ধাচারণে লিপ্ত, তাদের পৃথিবীতে বেচেঁ থাকার অধিকারও থাকা উচিত নয়। কিন্তু আল্লাহর অতিশয় দয়া ও মহানুভবতা এবং তাঁর চরম সহনশীলতার গুণে তিনি তাদেরকে শুধু যে জীবন ধারণের সুযোগ দিয়েছেন তা নয়, বরং তাদেরকে তাদের কুফরী, শিরক ও নাস্তিকতার ওপর টিকে থাকারও এতোখানি সুযোগ দিয়েছেন, যাতে তাদের খোদাদ্রোহিতা আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের জীবন অরাজকতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারে। তাদেরকে এ অধিকার তিনি কখনো দেননি যে, আল্লাহর শরীয়তী বিধান বাতিল করে তারা নিজেদের মনগড়া আইন কানুন দ্বারা তার পৃথিবীর প্রশাসন চালাবে এবং এভাবে তার যমীনে অরাজকতার তান্ডব সৃষ্টি করবে। তাই ইসলাম তার শরীয়তী বিধানকে যারা মেনে নিয়েছে তাদেরকে নির্দেশ দেয় যে, অমুসলিমদেরকে আল্লাহর সত্য দীন গ্রহণ করতে বাধ্য করোনা। কিন্তু কুফরী ব্যবস্থার আধিপাত্য ও প্রাধান্য এবং কাফিরদের কর্তৃত্ব প্রভুত্ব যা কিনা সাধারণ মানুষ ও মুমিনদের জন্য আল্লাহর সত্য দীনের আনুগত্য করার পথে প্রতিবন্ধক তাকে সর্বশক্তি দিয়ে উৎখাত করো, যেনো পৃথিবীর ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন কার্যত আল্লাহর দীনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে যারা আল্লাহর দীনকে মানেনা, তারা “কতৃত্বশীল” নয়, এবং প্রতাপান্বিত নয় বরং “অধিনস্ত” বরং বিনীত হয়ে থাকবে। সূরা তওবার ২৯ নং আয়াতে এ কথাই বলা হয়েছেঃ
“যতক্ষণ না তারা বিনীতভাবে স্বহস্তে জিজিয়া দেবে ততক্ষণ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাও।” [এ লড়াই করার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এর ফলে তারা ঈমান আনবে এবং ইসলাম পালন করতে শুরু করবে। বরঞ্চ এর উদ্দেশ্য হলো, এর ফলে তাদের স্বাধীনতা ও কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে তারা শাসক ও কর্তৃত্বসম্পন্ন হয়ে থাকতে পারবেনা। বিশ্বের জীবন ব্যবস্থার বাগডোর এবং কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের ক্ষমতা অর্পিত হবে সত্যদীনের অনুসারীদের হাতে। আর ওরা এদের অধীনে অনুগত ও বাধ্যগত হয়ে থাকবে।
ইসলাম রাষ্ট্র যিম্মীদের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণের যে দায়িত্ব পালন করে, জিযিয়া তারই বিনিময়। আর তারা যে ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনতা মেনে নিয়েছে, তারও নিদর্শন বটে। স্বহস্তে জিযিয়া দেয়ার অর্থ সোজাসোজি ও সুস্পষ্ট আনুগত্যের ভাবধারা অনুযায়ী জিযিয়া প্রদান করা। আর বিনীতভাবে মানে বিশ্বে তারা কোনোদিক দিয়ে বড় বলে বিবেচিত হবেনা। বড় বিবেচিত হবে কেবল সেই মুমিনরা, যারা আল্লাহর খিলাফতের দায়িত্ব পালনে নিরত।]
ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব
২. উল্লেখিত তথ্যসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার পর দ্বিতীয় যুক্তির প্রখরতা আপনা থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যদি যথার্থই আল্লাহর প্রেরিত নবী থেকে থাকেন তাহলে অন্যান্য নবীগনের পৃথিবীতে আসার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যা ছিলো, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও নিশ্চিতভাবে তাই ছাড়া আর কিছু থাকতে পারেনা। অর্থাৎ অন্যসকল জীবন ব্যবস্থার ওপর আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করা। এটা একটা মৌলিক তত্ত্ব। সকল নবীর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ তত্ত্বটাকে একটা সাধারণ মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আমরা যদি একথা স্বীকার করি যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর শাসনামলে মিশরে আল্লাহর দীনের পরিবর্তে রাজকীয় বিধি বিধান চালু করতেন, তাহলে তো তাঁর মধ্যে এবং স্যার সিকান্দার হায়াত খান ও একে ফজলুল হকের [এ নিবন্ধ লেখার সময়ে পাঞ্জাবে স্যার সিকান্দার হায়াত ও বাংলায় এ কে ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এখন তাদের স্থলে যেকোনো অনৈসলামী সরকারের মুসলমান মন্ত্রীকে ধরে নেয়া যেতে পারে।] মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকেনা। দুঃখের বিষয় যে, অনেকে এ ব্যাপারে প্রকৃত ঘটনা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তারা আসলে ইউসুফ আলাইহিস সালামের কিসসাটা বুঝতেই পারেননি। তাদের ধারণা, ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে সমসাময়িক বাদশাহকে বলেছিলেনঃ
“আমাকে এই ভুখন্ডের সহায় সম্পদের তদারকীর দায়িত্ব দিন।” [সূরা ইউসুফঃ ৫৫]
সেটা ছিলো নেহায়েতই তাঁর পক্ষ থেকে একটা চাকরির আবেদন। আর এর ফলে তিনি সম্রাট আকবরের দরবারে টোডর মল্লের পদের মতো একটা পদ সেখানে লাভ করেছিলেন। অথচ সেখানকার ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।
মহান নবী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শুরুতে আল্লাহর সত্য দীন কায়েমের জন্য সকল নবীদের চিরাচরিত পন্থাই অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ প্রথমে সাধারণ দাওয়াত ও অতপর যারা ঐ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত ও সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা, অতপর তাদেরকে সাথে নিয়ে দীন কায়েমের জন্য চেষ্টা সাধনা। দাওয়াতের কাজটা তিনি কারাগার থেকেই শুরু করে দিয়েছিলেন। সূরা ইউসুফের ৫ম রুকুতে তাঁর দাওয়াতী স্তরের একটা অতুলনীয় ভাষণ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আকস্মিকভাবে তিনি এমন একটা মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেলেন, যার মাধ্যমে তিনি সংক্ষিপ্ত পথ ধরে আপন লক্ষ্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, মিশর সরকারের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব আযীযের স্ত্রী ও তার সঙ্গীদের ব্যাপারে তিনি যে পবিত্র ও অনমনীয় চরিত্রের পরিচয় দিয়েছিলেন এবং তার পরে স্বপ্নের তাবীর করার মধ্যদিয়ে তিনি যে প্রজ্ঞার প্রমাণ দিয়েছিলে, তার কারণে মিসরের বাদশাহ তার প্রতি এতো অনুরক্ত হয়ে গেছেন যে, তিনি যদি তখন দেশ শাসনের পূর্ণাংগ ক্ষমতা তার কাছে চেয়ে বসেন তবে বাদশাহ নির্দিধায় তা দিয়ে দেবেন। এজন্য গণআন্দোলনের দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চাইতে সরকারী ক্ষমতা অবিলম্বে দখল করে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর কাছে নিকটতর ও সহজতর পথ মনে হলো। তাই তিনি বাদশাহের কাছে اِجْعَلِى عَلى خَزَائِنُ الْاَرْضِ “দেশের যাবতীয় উপায় উপকরণ আমার কর্তৃত্বে দিয়ে দিন” এই দাবী করে বসলেন। এটা কেবল অর্থমন্ত্রীর গদী লাভের দাবী ছিলোনা, যদিও কেউ কেউ এটাই মনে করে থাকেন। বরঞ্চ এটা ছিলো সর্বাধিনায়ক ও সার্বভৌম শাসকের পদের দাবী। এর ফলে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যে পদমর্যাদা ও ক্ষমতা লাভ করলেন তা বর্তমানে ইতালীতে মুসোলিনী যে পদমর্যাদায় সমাসীন, তার প্রায় অনুরূপ। [এ প্রবন্ধ লেখার সময় মুসোলিনী ইতালীর একনায়ক ছিলেন] পার্থক্য শুধু এতোটুকু যে, ইতালীর রাজা মুসোলিনীর ভক্ত নন, কেবল তার দলের প্রভাব প্রতিপত্তির দাপটে নতি স্বীকার করেছেন। আর মিসরের বাদশাহ স্বয়ং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের মুরীদ হয়ে গিয়েছিলেন। [প্রখ্যাত তাফসীরকার ইমাম মুজাহিদ বলেন যে, বাদশাহ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের হাতে ইসলামও গ্রহণ করেছিলেন। [ইবনে জারীর]]
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ক্ষমতা কিরূপ ছিলো সে সম্পর্কে আল্লাহর স্বয়ং সাক্ষ্য দেন যেঃ
“এভাবে আমি ইউসুফেকে সেই ভূখন্ডে ক্ষমতাসীন করলাম। সে ঐ ভূখন্ডের যে অংশে ইচ্ছা নিজের স্থান করে নিতে সক্ষম ছিলো।” [সূরা ইউসূফঃ ৫৬]
অর্থাৎ গোটা দেশে তার একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করতো। সূরা মায়েদাতে আমরা এ সম্পর্কে আরো সাক্ষ্য পাই। সেখানে হযরত মুসা আলাইহিস সালাম স্বীয় জনগণকে বলেনঃ
“হে আমার জাতি! আল্লাহ তোমাদের প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তা স্মরণ করো। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর আবির্ভাব ঘটিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসন জাতি বানিয়েছেন এবং পৃথিবীতে কাউকে যা দেননি, তা তোমাদেরকে দিয়েছেন।” [সূরা মায়েদাঃ ২০]
এ থেকে পরিস্কার বুঝা যায় যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরে যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন, তাঁর কল্যাণে সেখানে পরিপূর্ন বিপ্লব সংঘটিত হয়, ফিরাউনদের পরিবর্তে বনী ইসরাঈলের শাসন চালু হয় এবং তারা উন্নতির এতো উচ্চ শিখরে আরোহণ করে, যা তাদের সমকালীন জাতিগুলোর মধ্যে আর কারো ভাগ্যে ঘটেনি। তাছাড়া হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরে যে ধর্মীয় প্রভাব প্রতিপত্তি রেখে যান, তার বিবরণ আমরা সূরা মুমিনে পাই। সেখানে জনৈক ঈমানদার কিবতী হযরত মূরা আলাইহিস সালামের ফিরাউনকে সম্বোধন করে বলেনঃ
“ইতিপূর্বে ইউসুফ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু প্রথমে তো তোমরা তাঁর নিয়ে আসা নিদর্শনের ব্যাপারে সন্দেহে লিপ্ত ছিলে। আর যখন সে মারা গেলো তখন তোমরা বললেঃ এখন আল্লাহ আর কোনো রসূল পাঠাবেননা।” [সূরা মুমিনঃ ৩৪]
অর্থাৎ তোমরা বললে যে, অমন উচু দরের মানুষ এখন আর আসতে পারেনা। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে এই নিগূঢ় তত্ত্ব জানার পর এরূপ যুক্তি প্রদর্শনের সাহস কে করতে পারে যে, তাই যেহেতু একজন নবী এরকম কাজ করেছেন? অবশ্য সূরা ইউসূফের ৭৬ নং আয়াতঃ
“তার পক্ষে রাজীয় আইনের অধীন আপন ভাইকে আটক করা সম্ভব ছিলোনা।”
এর আলোকে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়ে থাকে যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম ফিরাউনী আইন মেনে চলতেন। এ আয়াতের মর্ম ও তাৎপর্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলার অবকাশ রয়েছে। তথাপি এর যে অর্থ সচরাচর বর্ণনা করা হয় তা যদি সঠিক মেনে নেয়াও হয়, তবু তা থেকে বড় জোর একথাই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের শাসন আমলের যে পার্যায়ে এ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে [পূর্বাপর বর্ণনা থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, এটা প্রাথমিক যুগেরই ঘটনা। কেননা তাঁর মিসরের শাসক হওয়ার কয়েক বছর পরই সাত বছরব্যাপী ইতিহাসখ্যাত সেই দুর্ভিক্ষ শুরু হয়, যার করাল গ্রাসে পতিত হয়ে তার ভাইদেরকে খাদ্যশস্য নেয়ার জন্য মিসর আসতে হয়েছিলো।] তখন পর্যন্ত মিসরে পূর্বতন ফৌজদারী আইনই চালু ছিলো। একটা দেশের রাষ্ট্রিয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকে যে রাতারাতি পাল্টানো যায়না, সেকথা সবার জানা। এ কাজ পর্যায়ক্রমেই সমাধা করা সম্ভব। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেও আরবের আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা পাল্টাতে দশ বছর লেগে গিয়েছিলো। উত্তরাধিকার আইন বদলানো হয়েছিলো ৩য় অথবা ৪র্থ হিজরীতে। বিয়ে ও তালাকের বিধি হিজরতের পর পাঁচ ছয় বছরে সম্পূর্ণরূপে কার্যকরী করা হয়েছিলো। ফৌজদারী বিধি সম্পূর্ণ করতে পুরো আট বছর লাগে। দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো পর্যায়ক্রমে ৯ বছর পাল্টানো হয়। মদ চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ হয় ৮ম হিজরীতে এবং সুদ পুরোপুরিভাবে রহিত করা হয় ৯ম হিজরীতে। এভাবে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামও যদি দেশের আইন সংস্কারের কাজ পর্যায়ক্রমে করে থাকেন এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাঁর শাসনামলে সাবেক আইন চালু থেকে থাকে, তাহলে তার ভিত্তিতে একথা কিছুতেই বলা চলেনা যে, একজন নবী আল্লাহর আইন বাদ দিয়ে মানব রচিত অনৈসলামিক আইনকে বৈধ মনে করে তা মেনে চলতেন।
৩. আবার আসুন তৃতীয় যুক্তির প্রসংগে। এটাকে আসলে যুক্তি বলে অজুহাত বলাই সমীচীন। এ অজুহাতের জবাব আমি পূর্বেই দিয়েছি। এখানে শুধু আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
“আমি যখন বনূয়্যত লাভ করেছি তখন থেকেই জিহাদের সূচনা এবং এই উম্মতের শেষ জনগোষ্ঠির দাজ্জালের সাথে যিহাদে লিপ্ত হওয়ার সময় পর্যন্ত তা চালিয়ে যাওয়া উচিত। কোনো অত্যাচারীর অত্যাচার এবং কোনো ন্যায়বিচারকের ন্যায়বিচার জিহাদের রহিত করতে পারেনা।”
অর্থাৎ আজ আমাদের ওপর চরম স্বৈরাচারী শাসকরা চেপে বসেছে, এই অজুহাতে যেমন জিহাদ বন্ধ করা চলবেনা, তেমনি কাফির শাসক হলেও মুসলমানদের প্রতি সুবিচার হচ্ছে এবং তারা শান্তিতে আছে এই বাহানা দিয়েও তা থেকে বিরত হওয়া চলবেনা। এমনকি মুসলমানদের নিজ দেশে সুবিচার ও ইনসাফের রাজত্ব থাকলেও তাদের নিশ্চিন্ত হওয়া এবং বাইরের জগত যে যুলুম, নির্যাতন ও অশান্তির আগুন জ্বলছে, তার দিক থেকে চোখ বুজে থাকা বৈধ নয়।
৪. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার বাতিল মতবাদ এবং ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে ভ্রান্ত যুক্তি গ্রহণ
তরজমানুল কুরআনের [এ অংশটি তরজমানুল কুরআন রবিউসসানী ১৩৬৩ হিজরী মোতাবেক এপ্রিল ১৯৪৪ ঈসায়ী সংখ্যায় প্রকাশ হয়। – সংকলক।] জনৈক পাঠক লিখেছেনঃ
সূরা ইউসূফের দুটো জায়গা সম্পর্কে আপনার কুরআন বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান থেকে উপকৃত হতে চাই।
কুরআন থেকে জানা যায়, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামকে পৃথিবীতে ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠা দান করা হয়েছিলো এবং তিনি বিশিষ্ট পদমর্যাদা নিয়ে সরকারে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু তিনি যে একজন রসূল ছিলেন এবং সেজন্য নবূয়্যতের দায়িত্ব পালনও তাঁর জন্য জরুরী ছিলো সেকথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ফিরাউনের দরবারের একজন অকুতোভয় মুমিন তাঁর ভাষণে এ আভাস দিয়েছিলেন যে, ফিরাউনের লোকেরা হযরত ইউসূফ আলাইহস সালামের নবূয়্যতের প্রতি ঈমান আনেনি। তিনি এও উল্লেখ করেছেন যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম নিজের ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত নমনীয় ভাব বজায় রেখেছিলেন। এথেকে বুঝা যায়, তিনি নিজের নবূয়্যতের প্রতি ঈমান আনার আহবান জানিয়েছিলেন। কিন্তু ফিরাউন ও তার লোকজন ঈমান আনেনি। এতদসত্ত্বেও হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম তাদের সরকারে অন্তর্ভূক্ত থাকেন। এখন প্রশ্ন উঠে, আল্লাহর একজন নবী একটি অনৈসলামিক সরকারে কিভাবে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারলেন? অথচ তিনি সেই জাতির কাছে নিজের বনী হওয়ার কথা ব্যক্তও করেছিলেন এবং সেই জাতি তাঁর নবূয়্যত মেনে নেয়নি। ইসলামের দাওয়াতকে এভাবে যারা প্রত্যাখান করলো, তাদের সাথে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের জিহাদ করা উচিত ছিলো। নতুবা নিদেন পক্ষে তাঁর সেখান থেকে হিজরত করা উচিত ছিলো। কিন্তু তিনি না করলেন হিজরত, আর না করলেন তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ, এমনকি তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ কিংবা অসন্তোষ ব্যক্ত করতেও তাঁকে দেখা যায়না। এ জটিল রহস্যের কোনো সমাধান কি আপনি দিতে পারেন?
জবাব
বনী ইসরাঈলের ইতিহাসের যে যুগটি হযরত মুসা আলাইহিস সালামের পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে। বলতে গেলে সেটা একেবারেই অন্ধকারাচ্ছন্ন। এজন্য কুরআনের সংক্ষিপ্ত ইংগীতসমূহের বিস্তারিত তথ্য অবগত হওয়া খুবই কঠিন। তবু কুরআনের এই সব সংক্ষিপ্ত ইংগিত থেকেও একথা সন্দেহাতীতভাবে জানা যায়, মিসরে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম সরকারের একজন সাধারণ অংশীদার ছিলেননা। বরং একচ্ছত্র ক্ষমতাসম্পন্ন শাসক ছিলেন। তিনি শাসন ক্ষমতা হাতে নিয়েছিলেনই এই শর্তে যে, তাঁর হাতে সার্বিক ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। নিম্নের আয়াত দুটি মনোনিবেশ সহকারে পড়ে দেখুনঃ
“ইউসূফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমাকে দেশের যাবতীয় সহায়-সম্পদের কর্তৃত্ব দান করুন। নিশ্চয়ই আমি যথাযথভাবে সংরক্ষক এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞানের অদিকারী। এভাবে আমি ইউসূফকে ঐ ভূখন্ডের কর্তৃত্ব দান করেছিলাম। সেখানে সে যথায় খুশী স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।” [বাইবেল এবং তালমুদ থেকেও এ সম্পর্কে তেমন কোনো তথ্য জানা যায়না। আর মিসরের প্রাচীন ইতিহাস এবং প্রাচীন নিদর্শনাবলী থেকেও এ ব্যাপারে কিছু জানা যায়না।] [সূরা ইউসূফঃ ৫৫-৫৬]
এই রেখা চিহ্নিত ব্যক্যগুলো তেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে, তিনি সার্বিক ক্ষমতাই চেয়েছিলেন আর পেয়েছিলেনও সার্বিক ক্ষমতাই। “দেশের সহায় সম্পদ” কথাটা দেখে কেউ কেউ ভুল ধারণায় লিপ্ত হয়েছেন যে, এ পদটা বোধহয় অর্থমন্ত্রীর অথবা রাজস্ব কর্মকর্তা পর্যায়ের। অথচ প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হলো দেশের সমগ্র উপায় উপকরণ [Resources] । হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের দাবী ছিলো, মিসর সাম্রাজ্যের সমস্ত উপায় উপকরণ তাঁর কর্তৃত্ব সমর্পণ করা হোক। আর এ দাবীর ফলে তিনি এমন ক্ষমতা লাভ করেছিলেন যে, গোটা মিসর ভূখন্ড তাঁর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। “সেখানে যে যথায় খুশী স্বীয় আবাস প্রতিষ্ঠা করতে পারতো।” কথাটারও অনেকে অত্যন্ত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাদের দৃষ্টিতে এর মর্ম শুধু এতটুকু যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম সর্বত্র বসবাস করার বা বাড়ী তৈরী করার অবাধ অনুমতি পেয়েছিলেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে একথাটা দ্বারা এটাই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, এক ভূস্বামীর তার স্বভূমিতে যেরূপ অবাধ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকে, সমগ্র মিসর ভূখন্ডে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঠিক তদরূপ একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো।
এরপর যে প্রশ্নটি অবশিষ্ট থাকে তা হলো, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের কারায়াত্ব এই নিরংকুশ ক্ষমতা দ্বারা তিনি দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, নৈতিকতা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ইসলামী আদর্শ অনুসারে পরিবর্তিত করতে কতোখানি চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতে তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করেছিলেন? ইতিহাসে আমরা এ প্রশ্নের কোনো বিস্তারিত জবাব পাইনা। তবে সূরা মায়েদার একটি উক্তি থেকে পরোক্ষভাবে আমরা এতোটুকু নিশ্চতভাবে জানতে পারি যে, মিসরে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের শাসন কোনো ব্যক্তি বিশেষের ক্ষণস্থায়ী শাসন ছিলোনা। বরং তার পরেও দীর্ঘকালব্যাপী তাঁর উত্তরসূরীরা মিসরের শাসন ক্ষমতার অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁরা নিঃসন্দেহে মুসলমান ছিলেন। শুধু তাই নয়, এই শাসকবর্গ সমসাময়িক পৃথিবীতে নজীরবিহীন প্রভাব প্রতিপত্তি ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। আয়াতটি নিম্নরূপঃ
“স্মরণ করো, যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিলোঃ হে আমার জাতি তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, তিনি তোমাদের মাঝে নবীদেরকে আবির্ভূত করেছেন। তোমাদের শাসক বানিয়েছেন এবং পৃথিবীর কাউকে যা দেননি, তা তোমাদের দিয়েছেন।” [সূরা মায়েদাঃ ২০]
এথেকে অনুমান করা চলে যে, এই সর্বাত্মক ইসলামী আধিপত্য ও বিজয় অনিবার্যভাবে দেশের সমগ্র কর্মকান্ডে প্রভাব বিস্তার করেছিলো।
সূরা আলমুমিনের যে আয়াত থেকে আপনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, কিবতী সম্প্রদায় হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামকে মেনে নেয়নি, আসলে সে আয়াতটি থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যুক্তিসঙ্গত নয়। আমার উপলব্ধি এই যে, সেখানে ভারতের মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিলো। দেশের জনসংখ্যার একটি উল্লেখ্যযোগ্য অংশ ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং বিরাট সংখ্যাগুরু অংশ মুশরিক থেকে গিয়েছিলো। [বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী মিসর থেকে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে যেসব লোক বের হয়ে এসেছিলো তাদের মধ্যে ছয় লাখ কেবল যোদ্ধা পুরুষই ছিলো। এথেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, তাদের মোট সংখ্যা বিশ লাখের কম ছিলোনা এবং মিসরের জনসংখ্যার সমপক্ষে তারা ১০% শতাংশ ছিলো।] যে অংশ ইসলাম গ্রহণ করে সে অংশটিই দীর্ঘকালব্যাপী ক্ষমতাসীন ছিলো। কিন্তু ক্রমাগত নৈতিক ও আকীদাগত অধপতন তাদের গোলামী ও গোমরাহীর গভীর আবর্তে নিক্ষেপ করে। শেষ পর্যন্ত এই জনগোষ্ঠীটি ব্যক্তিপূজা ও ধর্মীয় বাড়াবাড়ীর বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়ে এমন অবস্থার শিকার হয় যে, অন্যান্য পৌত্তলিকদের সাথে তাদের কার্যত কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভেদ ছিলোনা। ফিরাউনের দরবারের ঈমানদার লোকটি এ বিষয়ের দিকে ইংগিত করেই বলেছেনঃ
“ইতোপূর্বে ইউসূফ তোমাদের কাছে সুম্পষ্ট নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি যা নিয়ে এসেছিলেন, তা নিয়ে তোমরা অনবরত সন্দেহে লিপ্ত রইলে। অতপর তিনি যখন ইন্তিকাল করলেন, তখন তোমরা বললে, এখন ওর পরে আল্লাহ আর কোনো রসূল পাঠাবেননা।” [সূরা মুমিনঃ ৩৪]
রেখা চিহ্নিত কথাগুলোর মধ্যে প্রথমটি থেকে বুঝা যায়, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের জীবদ্দশায় দেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর নবূয়্যত সম্পর্কে সন্ধিহান ছিলো, যেমনটি অধিকাংশ নবীদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। দ্বিতীয় কথাটি থেকে বুঝা যায়, তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর ভক্তরা তাঁর ব্যক্তিত্বের পূজারী হয়ে বাড়াবাড়ী শুরু করে দেয় এবং বলতে থাকে যে, এখন আর কোনো রসূল আসতে পারেনা! এরই ভিত্তিতে তারা পরবর্তী নবীদেরকে অগ্রাহ্য করে। পরবর্তী সময়ে ইহুদী ও খৃষ্টানরা এ কাজই করেছিলো। অথচ হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কিংবা হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, এঁদের কারো পরেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবুয়্যত সমাপ্তির ঘোষণা দেয়া হয়নি।
তবে কোনো অবস্থাতেই আয়াতটির এরূপ মর্মোদ্ধারের অবকাশ নেই যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ওপর দেশের কেউ ঈমান আনেনি। বরং অন্যান্য আভাস-ইংগীত থেকে এটাই অনুমিত হয় যে, দেশে মুমিনদের একটি গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো। তারা বনী ইসরাঈলের সাথে মিলিত হয়ে দীর্ঘদিন ইসলামী শাসন চালু রেখেছিলো। তবে পরবর্তী সময় তারা ক্রমান্বয়ে অধোপতনের [Degenerate] শিকার হয়ে পড়ে।
৫. ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করার মতবাদ খন্ডন এবং তার পর্যালোচনা
[“সূরা ইউসূফ সংক্রান্ত কাতিপয় প্রশ্ন” শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর একজন খ্যাতনামা মনীষী, যিনি এখন জীবিত নেই, যিনি খান বাহাদুর উপাদিতে ভূষিত ছিলেন এবং ইউপিতে কালেক্টর ও ভারতের একটি রাজ্যে দেওয়ানে পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, আমার উক্ত নিবন্ধের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। উক্ত মনীষীর সমালোচনা না পড়ে আমার জবাব বুঝা সম্ভব নয় বিধায় আমরা এখানে প্রথমে তার সমালোচনার সংশ্লিষ্ট অংশ উদ্ধৃত করছি। এরপর আমাদের জবাব উদ্ধৃত করবো।][এ পার্যালোচনাটি তরজমানুল কুরআন জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ সংখ্যা থেকে সংকলিত।]
প্রশ্নকর্তা যেকথা জানতে চেয়েছিলেন এবং যেকথা প্রকৃতপক্ষে বিবেচ্য বিষয়, তা শুধু এতোটুকুই যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের এ কাজটি ইসলামী দৃষ্টিভংগিতে জায়েয ছিলো কি না? মাওলানা মওদূদী সাহেব জবাবে বলেন, “হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের পদমর্যাদা মিসরে অনৈসলামিক সরকারের একজন অংশীদারের অনুরূপ ছিলোনা।” আশ্চার্য্যর বিষয় তিনি তাঁর এই মতের সমর্থনে কুরআনের সেই আয়াতই অর্থাৎ [সূরা ইউসূফঃ ৫৫] পেশ করেন, যা প্রকৃতপক্ষে এর বিপরীতটাই প্রমাণ করে।
উক্ত আয়াতের শাব্দিক অনুবাদ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসানের ভাষায় নিম্নরূপঃ
“ইউসূফ বললেন, আমাকে নিযুক্ত করুন দেশের ধন ভান্ডার সমূহের দায়িত্বে। আমি প্রচুর জ্ঞানের অধিকারী এবং রক্ষক। এভাবে আমি ইউসূফকে ক্ষমতা দিলাম সেই ভূখন্ডে। তিনি স্থান গ্রহণ করতেন সেই ভূখন্ডে যেখানে চাইতেন।”
লক্ষ্য করুন, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম ফেরাউনের কাছে আবেদন জানালেন, আপনি আমাকে দেশের ধন ভান্ডারের দায়িত্বে নিযুক্ত করুন। ফিরাউন তার আবেদন মঞ্জুর করেন এবং তিনি অর্থ বিভাগের কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। স্পষ্টতই এর ফল দাঁড়ালো এই যে, তিনি ফিরাউনের সরকারের একজন সদস্য বা অংশীদার হয়ে গেলেন। এই স্বাভাবিক ফলশ্রুতিকে পাশ কাটানোর ব্যর্থ প্রয়াস চালাতে গিয়ে মাওলানা মওদূদী বলেন, “দাবী ছিলো নিরংকুশ ক্ষমতার এবং পেয়েছিলেনও নিরংকুশ ক্ষমতা।”……
প্রথমত নিরংকুশ বা সার্বিক ক্ষমতাবোধক শব্দ কুরআনে নেই। এ শব্দটা মাওলানা সাহেব নিজের পক্ষ থেকে কুরআনে সংযোজন করতে চান, যাতে কুরআন মাওলানার ব্যক্তিগত মতাদর্শের বাহক হয়ে যায়, এ জন্য নয় যে, মাওলানা নিজের ব্যক্তিগত মতবাদকে কুরআন অনুযায়ী শুধরে নেবেন। এ ধরনের মনোবৃত্তি সম্পর্কে সম্ভবত মরহুম কবি ইকবাল বলেছিলেনঃ “তারা নিজেরা শুধরায়না। বরং কুরআনকে বদলায়।” কিন্তু এই সার্বিক বা নিরংকুশ শব্দটার অবৈধ সংযোজন সত্ত্বেও মাওলানার গবেষণা বা মতবাদের সমর্থন পাওয়া যায়না। ধরে নিলাম, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম অর্থ সম্পদ সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা চেয়েছিলেন এবং পেয়েছিলেনও সার্বিক ক্ষমতাই। কিন্তু এই ক্ষমতা তিনি মিসরের ফিরাউনের কাছেইতো চেয়েছিলেন এবং মিসরের ফিরাউনইতো সেটা দিয়েছিলো। সুতরাং নিরংকুশ ও সার্বিক ক্ষমতা লাভ করা সত্ত্বেও তখনকার শাসন ব্যবস্থায় তাঁর অবস্থান একজন সদস্য বা অংশীদারের উর্ধের কিছু হতে পারেনা।
মাওলানা মওদূদী সাহেবের এ উক্তিও বাস্তবতার বিপরীত যে, “হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের দাবী ছিলো, মিসর সম্রাজ্যের সকল উপায় উপকরণ আমার দায়িত্বে সমর্পণ করা হোক এবং দাবীর পরিণতিতে তিনি যে ক্ষমতা লাভ করলেন তাতে সমগ্র মিসরের ভূমি তাঁর নিজস্ব ভূমিতে পরিণত হলো।” একথা যদি মেনে নেয়াও হয় যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম অর্থ সংক্রান্ত সার্বিক ক্ষমতা দাবী করেছিলেন এবং অর্থ সংক্রান্ত একচ্ছত্র কর্তৃত্ব তার হাতে অর্পন করা হয়েছিলো। তথাপি একথা সবার জানা, একটি রাষ্ট্রে অর্থ ছাড়া আরো বহু বিভাগ থাকে। যেমন- পুলিশ, সশস্ত্রবাহিনী ও বিচার বিভাগ। এসবের কোনেটির দায়িত্ব ইউসূফ আলাইহিস সালাম চানওনি, এগুলো তাঁর দায়িত্বে অর্পিতও হয়নি। তা যখন হয়নি, তখন মাওলানার একথা বলা যে, “তিনি যে ক্ষমতা লাভ করেছিলেন তাতে সমগ্র মিসরের ভূমি তাঁর নিজের ভূমিতে পরিণত হয়েছিলো” সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।
অতএব হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম বিসরের সমস্ত অর্থ সম্পদের দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেও তাঁর সাম্রাজ্যের ক্ষমতার প্রকজন অংশীদার বা সরকারের সদস্যের পর্যায়েই থাকে যতক্ষণ কোনো উপায়ে প্রমাণিত না হয় যে, মিসরের ফিরাউন সাম্রাজ্যের শাসন থেকে অবসর নিয়েছিলো এবং হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের তাঁর স্থলে মিসরের সম্রাট হয়ে গিয়েছিলো। অথচ তাঁর সম্রাট হওয়ার কথা ইতিহাস থেকেও প্রমাণিত হয়না, কুরআন থেকেও নয়। বরং কুরআন থেকে এ ধারণা দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যাত। আলোচ্য আয়াতের অব্যবহিত পূর্বের আয়াতটি লক্ষ্যণীয়ঃ
“সম্রাট বললো, তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের জন্য মনোনীত করবো। অতপর সে যখন ইউসূফের সাথে কথা বললো, বললো যে, নিশ্চয়ই আপনি আজ আমাদের কাছে সম্মানিত ও বিশ্বস্ত।” [সূরা ইউসূফঃ ৫৪]
উভয় আয়াত থেকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট যে, মিসরের ফিরাউন হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামকে স্বীয় সাম্রাজ্যের সম্মানিত ও বিশ্বস্ত সদস্য এবং নিজের বিশেষ উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। এ আয়াত দুটিতে এমন কোনো আভাসও নেই যে, মিসরের ফিরাউন স্বীয় সম্রাজ্য অথবা ক্ষমতা পরিত্যাগ করেছিলেন। এছাড়া পরবর্তী একটি আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম কর্তৃক মিসরের সকল অর্থ সম্পদের দায়িত্ব গ্রহণেরও অনেক পর পর্যন্ত মিসরে ফিরাউনের রাজত্ব বহাল ছিলো এবং তাঁর ধর্মই দেশে চালু ছিলো। কেননা ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যখন দ্বিতীয়বার খাদ্যশস্য আনার জন্য মিসরে আসে তখন হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ইচ্ছা মোতাবেক তাঁর আপন ভাই বিন ইয়ামিনকেও নিয়ে আসে। হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম তাঁর ভাই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দেন এবং তাকে জানিয়েও দেন যে, তিনি তাঁর আপন ভাই, কিন্তু তাঁর অন্যান্য ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেননি। এই সময় যেহেতু ইউসূফ আলাইহিস সালাম ভাইদের কাছে বিন ইয়ামীন তার আপন ভাই একথা প্রকাশ না করেই বিন ইয়ামিনকে নিজের কাছে রেখে দিতে চেয়েছিলেন, তাই এ উদ্দেশ্যে তিনি একটি কৌশল অবলম্বন করলেন। ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভাইদের জন্য যখন তাদের আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হলো, তখন বিন ইয়ামিনের আসবাবপ্রত্রের ভিতর একটা পানপাত্র লুকিয়ে রাখা হলো। অতপর কাফেলা রওনা দিতে আরম্ভ করলে এ ঘোষক চিৎকার করে বললো, ওহে কাফেলার লোকেরা! তোমরা নিশ্চয়ই চোর। ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা একথা অস্বীকার করলে ঘোষখ বললো, তোমরা যদি মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও, তাহলে এর কি শাস্তি গ্রহণ করবে? হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা বললো, যার আসবাবপত্রে এটা পাওয়া যাবে, সেই তার বদলায় যাবে। আমরা অপরাধীদের এরকম শাস্তিই দিয়ে থাকি। এরপর তাল্লাশি চালানো হলে পানপাত্রটি বিন ইয়ামিনের আসবাবপত্র থেকে বের হলো। এভাবে পানপাত্রের বদলায় বিন ইয়ামিনকে আটক করা হলো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেনঃ
“আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া ইউসূফের পক্ষে বাদশাহের ধর্ম অনুসারে আপন ভাইকে আটক করা সম্ভব ছিলোনা।” [সূরা ইউসূফঃ ৭৬]
এ আয়াত থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়, মিসরের রাজকীয় আইন তখনো দেশে প্রচলিত ছিলো এবং সে আইন অনুসারে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম স্বীয় ভাই বিন ইয়ামিনকে চুরির দায়ে ভাইদের কাছ থেকে ধরে রাখতে পারতেননা। কিন্তু আল্লাহ স্বয়ং তাঁর ভাইদের মুখ দিয়ে একথা বলিয়ে নিলেন যে, যার আসবাবপত্র থেকে পানপত্র পাওয়া যাবে তাকেই তার বিনিময়ে থেকে যেতে হবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসংগে মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী বলেনঃ
“অর্থাৎ ভাইদের মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরুলো, যার কাছে জিনিসটা পাওয়া যাবে তাকে গোলাম বানিয়ে নাও। এজন্যই তাকে গ্রেফতার করা হলো। নচেৎ মিসরের আইন এরকম ছিলোনা।”
তাই বলে একথা বলা চলেনা যে, মিসরের মন্ত্রীত্বে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি কিংবা নিজের নবূয়্যতের কথা ব্যক্ত করা থেকে বিরত থেকেছেন। বরঞ্চ তিনি জেলে থাকাকালেই তাওহীদের মর্মবাণী প্রচার করা শুরু করে দিয়েছিলেন। হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম নিজের সহবন্দীদ্বয়কে সম্বোধন করে বলেনঃ
“হে আমার কারা বন্দীদ্বয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রভু ভালো, না একমাত্র মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ? তোমরা যেসব সত্ত্বার পূজা করো সেগুলোতে কেবল তোমাদেরই নির্ধারিত কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছু নয়। যার সমর্থনে আল্লাহ কোনো প্রমাণ নাযিল করেননি। বিচার ফায়সালা ও শাসন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তিনি আদেশ দিয়েছেন, তাঁর ব্যতীত আর কারোর ইবাদত করোনা।” [সূরা ইউসূফঃ ৩৯-৪০]
এমনিভাবে এটাও ধরে নেয়া যায় যে, মন্ত্রী হওয়ার পরও হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ অবশ্যই অব্যাহত রেখেছিলেন। তবে এ আয়াতগুলো থেকে একথা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম একটা অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হয়েছিলেন নিজেরই আগ্রহ ও আবেদনক্রমে। আর তাঁর সরকারের সদস্য হওয়ার পরও দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং অনৈসলামিক আইনই চালু ছিলো। তাঁর এ কাজে আল্লাহর তরফ থেকে কোনো তিরস্কারতো করাই হয়নি, অধিকন্তু তাঁর এ রকম প্রশংসাই করা হয়েছে। কেননা হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের মিসরের ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করাকে আল্লাহর পুরস্কার বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেনঃ
“এভাবেই আমি ইউসূফকে সেই ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে সে তার যেখানেই ইচ্ছা নিজের স্থান করে নিতে পারে। আমি যাকে চাই, আমার অনুগ্রহে সিক্ত করি আর সৎকর্মশীলদের পুরস্কার আমি কখনো বিনষ্ট করিনা।”
এথেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সাধারণ মুসলমানতো দূরের কথা নবীদের পক্ষেও অনৈসলামিক সরকারের সদস্য হওয়া বৈধ। শুধু বৈধই নয়, ক্ষেত্র বিশেষে ফরযে কিফায়ার মতো অপরিহার্য কর্তব্যও বটে। কেননা হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের নিজ আগ্রহে মিসরের অর্থ ভান্ডারের দায়িত্বশীল হওয়া থেকে প্রমাণিত হয়, এ কাজকে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম নিজের জন্যে কেবল বৈধ নয়, কর্তব্যও মনে করতেন। তা না হলে ফিরাউনের কাছে তিনি কখনো এ ব্যাপারে নিজের অভিলাষ প্রকাশ করতেননা এবং এরূপ অভিলাষ প্রকাশ করার সময় নিজের অভিজ্ঞ ও রক্ষক হওয়ার কথাও ব্যক্ত করতেননা। কেননা তাঁর মতে যদি মিসরের ওজারতীর দায়িত্ব গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে অবশ্য কর্তব্য না হতো, তাহলে তাঁর পক্ষে নিজেকে অভিজ্ঞ ও রক্ষক বলা অবান্তর আত্মপ্রশংসার পর্যায়ে পড়ে।
[এরপর তিনি নিজ বক্তব্যের সমর্থনে কয়েকজন মনীষীর বক্তব্য উল্লেখ করেন। নিজের পক্ষ থেকে কিছু যুক্তিও পেশ করার চেস্টা করেন। তাছাড়া হাবশার হিজরত থেকেও যুক্তি গ্রহণ করেন। যেহেতু তার যুক্তি প্রমাণের মণিমুক্তা উপরে এসে গেছে তাই দীর্ঘয়িত হবার ভয়ে বাকী অংশ এখানে উল্লেখ করা হলোনা।]
জবাব
আমি জনাব খান বাহাদুর সাহেবের নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি প্রশ্নটার অবতারণা ক আমাকে আরো একবার আমার দৃষ্টিভংগি পরিস্কারভাবে তুলে ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমি শুধু এই আশায় এ আলোচনায় সময় ব্যয় করছি যে, এতে করে বহু সংখ্যক ছাড়া অন্যান্য শক্তি বা কর্তৃপক্ষের আনুগত্য করা অথবা অন্য কথায় আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য শক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করাকে বৈধ এবং কুফরী শাসন ব্যবস্থার গোলামী করাকে মুবাহ এমনকি ফরজে কিফায়া সাব্যস্ত করার জন্য পেশ করা হয়ে থাকে।
হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনার আলোচ্য দিকটি নিয়ে ইতিপূর্বে আমি দুবার আলোচনা করেছি। তন্মধ্যে প্রথম আলোচনাটা অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে ও যুক্তিপূর্ণভাবে তুলে ধরা হয়েছিলো। আর দ্বিতীয়টা ছিলো সংক্ষিপ্ত। কিন্তু খান বাহাদুর সাহেব বিস্তারিত আলোচনাটা বাদ দিয়ে সংক্ষপ্তি আলোচনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুলেছেন। এটা কোন কারণে করলেন জানিনা। অথচ তিনি স্বীয় নিবন্ধে যেসব আপত্তি তুলেছেন, তার অধিকাংশ বরং সম্ভবত সব কটারই জবাব আমার প্রথম আলোচনায় পাওয়া যেতে পারে। [এ বইয়ের ইসলাম ও কর্তৃত্ব শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য] সে যা হোক, এ পাশ কাটানোর কারণ যেটাই হোকনা কেন, আমাদের সামনে এর কল্যাণকর দিকটাই প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে। যে কথাগুলো আমরা নিজেরা বারংবার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিস্কার করে বলতে পারতাম না, অন্যদের খোঁচানোতে তা স্পষ্ট করে বলার সুযোগ আমাদের হস্তগত হয়েছে।
ইসলামে কি স্বাবিরোধীতা আছে?
দুনিয়াতে একজন কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন ও সুস্থ বিবেকধারী মানুষের কাছ থেকে যেসব জিনিস আশা করা হয়, তার মধ্যে পয়লা জিনিস সম্ভবত এটাই যে, তার কথাবার্তা যেনো পরস্পর বিরোধী না হয়। একজন স্বল্প বৃদ্ধির মূর্খ গোঁয়ার লোকও যখন কাউকে এ ধরনের পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা বলতে দেখে, তখন সংগে সংগেই তাতে আপত্তি তোলে। কেননা তারা অমন স্থুল বুদ্ধিও স্ববিরোধী কথাবর্তার বোকামী সহ্য করতে পারেনা। কিন্তু এটা বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, অত্যন্ত নিন্মমানের বুদ্ধির লোকের কাছ থেকেও যা আশা করা যায়না, সেটাই সেই আল্লাহর কাছ থেকে আশা করা হচ্ছে, যিনি নিজেই বিবেকবুদ্ধির সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত প্রজ্ঞা ও সৃক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী। আরো আশ্চার্যর ব্যাপার হলো, আল্লাহর কাছ থেকে এহেন চরম নির্বুদ্ধিতা যার আশা করছে, তারা কোনো অজ্ঞ ও নির্বোধ লোক নয়, বরং সারা দুনিয়ার মানুষকে জ্ঞান ও বুদ্ধির সবক শেখানোর কাজে নিয়োজিত বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ। দুনিয়ার যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে এই পন্ডিতদের ক্ষুরধার বুদ্ধি নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত। এমন সচেতন ও জাগ্রত বিবেকের অধিকারী হয়েও তারা চান এবং আশা করেন যে, আল্লাহর কথার স্ববিরোধীতা থাকুক। অর্থাৎ তিনি একদিকে বলবেন যে, আমি আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট। আবার অপরদিকে তিনি পৃথিবীর কোনো কোনো অংশে অন্যের রাজত্ব ও আধিপত্য বহাল থাকাকেও স্বীকার করে নেবেন। একদিকে তিনি বলবেন, তোমরা সকলে একমাত্র আমার হুকুমের আনুগত্য করো। পরক্ষণে তিনিই আবার মানুষকে সেইসব শাসকের আনুগত্য করার অনুমতি দেবেন, এমনকি আনুগত্য করাকে ফরয পর্যন্ত ঘোষণা করবেন, যেসব শাসক আল্লাহর আদেশের সার্টিফিকেট ছাড়াই বরঞ্চ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাঁর আদেশের বিরুদ্ধে আদেশ দান করে থাকে। তিনি মানুষের জন্য একটা আইন রচনাও করবেন এবং একথাও ঘোষনা করবেন যে, এটাই আমার আইন, এ আইন ছাড়া আর সব কিছুই বাতিল। আবার সেই সাথে অন্যান্য আইন প্রবর্তন ও প্রচলনকেও বৈধ করে দেবেন এবং যে মানুষের জন্য তিনি নিজে আইন রচনা করেছেন, সেই মানুষকেই এ “অধিকার” দেবেন যে, ইচ্ছা হয় তারা নিজেরা নিজেদের জন্য কোনো আইন রচনা করে নিক, নতুবা অন্য কারো আইন ধার করে এনে অনুসরণ করতে থাকুক। পৃথিবীর অধিবাসীদেরকে আল্লাহর দীন গ্রহণের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশ্য তিনি তাঁর নবীদেরকেও পাঠাবেন, আবার সেই নবীদেরকেই বা তাঁদের কাউকে এ অনুমতিও দেবেন [এমনকি খান বাহাদুর সাহেবের বক্তব্য অনুসারে এজন্য তাদেরকে অভিনন্দিতও করবেন] যে, আল্লাহর এ দীন ছাড়া অন্য কোনো দীনের আওতাধীন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কর্মচারীও ভৃত্য হয়ে যাক এবং তাকে সফলতার সাথে পরিচালনা করতে নিজেদের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাক। তিনি সারা দুনিয়ার অধিবাসীদের মধ্য থেকে বাছাই করে একটি বিশেষ উম্মত এ উদ্দেশ্য তৈরী করবেন যে, তারা আল্লাহ কর্তৃক নির্দেশিত সৎ কাজগুলোর আদেশ দেবে এবং আল্লাহ কর্তৃক ধিক্কৃত অসৎ কাজগুলোকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করবে। আবার খোদাদ্রোহীদের দৃষ্টিতে ভালো লাগা অসৎ কাজগুলোকে কায়েম করা ও চালু রাখার কাজে অংশ গ্রহণ এবং তাদের দৃষ্টিতে খারাপ বলে বিবেচিত সৎ কাজগুলোকে উৎখাত করা ও দমিয়ে দেয়ার কাজে ব্যবহৃত ও নিয়োজিত হওয়াকে সেই উম্মতের জন্যই বৈধও করে দেবেন, এমনকি তার কোনো কোনো “মনোনীত” বান্দার জন্য এ কাজকে ফরযে কিফায়াও ঘোষণা করবেন, এগুলো এমন সুস্পষ্ট স্ববিরোধী ব্যাপার যে, এগুলোর স্বরিরোধীতা বুঝতে কোনো গভীর চিন্তা গবেষণার প্রয়োজন পড়েনা। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, যারা কুরআনের তাফসীর লেখা এবং ফিকহ ও অন্যান্য যুক্তিনির্ভর বিদ্যায় অধ্যাপনা করার মতো পারদর্শিতা রাখেন, যারা কালেক্টরী, তারা এসব দুমুখো কার্যকলাপে যেনো কোনো স্বরিরোধীতাই দেখতে পাননা। এমনকি স্বয়ং বিশ্বপ্রতিপালক সম্পর্কে তাদের ধ্যান ধারণা এতোই খারাপ যে, একজন নিরেট মুর্খ গোঁয়ার লোকও তার আশপাশের কোনো বন্ধুর মধ্যে যেসব বেকুফী ও গোঁয়ার্তুমী দেখে তা সহ্য করতে পারেনা। তা স্বয়ং আল্লাহর মধ্যেও থাকা সম্ভব বলে তারা মনে করেন। খান বাহাদুর সাহেব তাঁর উক্ত নিবন্ধের এক জায়গায় লিখেছেনঃ
“পরবর্তী একটি আয়াত থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণিত হয়, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের মিসরীয় অর্থ ভাণ্ডারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব লাভের পরও ফিরাউনের রাজত্ব বহাল ছিলো এবং ফিরাউনের বিধি বিধানই মিসরে প্রচলিত ছিলো।
“বাদশাহর প্রচলিত বিধান অনুযায়ী তিনি কখনো আপন ভাইকে নিতে পারতেননা, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত।” [সূরা ইউসূফঃ ৭৬]
এবাক্যটি সুস্পষ্টরূপে বলে দিচ্ছে যে, ফিরাউনের রাজকীয় আইনই তখন পর্যন্ত মিসরে চালু ছিলো।”
দীন বলতে কি বুঝায়?
এ কথাগুলো লেখার সময় খান বাহাদুর সাহেবকে একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রমাণ করার নেশায় এমনভাবে পেয়ে বসেছিলো যে, তাঁর এই মনগড়া তাফসীরের দারুন এখানে কুরআনের বর্ণনায় যে সুস্পষ্ট স্ববিরোধীতার উদ্ভব হয়, তা ক্ষণিকের জন্যও ভেবে দাখার ফুরসত তিনি পাননি। তাঁকে অনুরোধ করি, তিনি যেনো আমার দৃষ্টি আকর্ষণে সাড়া দিয়ে এখন অন্তত একটু ভেবে দেখেন। তাঁর উদ্ধৃত আয়াতে ফিরাউনের সার্বভৌমত্ব ভিত্তির রাষ্ট্রিয় আইন ও বিধানকে “দীনুল মালিক” অর্থাৎ “রাজকীয় দীন” শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এথেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, দীন শুধু উপাসনালয়ে যে পূজা অর্চনা করা হয় তার নাম নয়, বরং যার বলে পুলিশ অপরাধীদেরকে পাকড়াও করে, যার অধীনে আদালত দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচার ফয়সালা করে, যার অনুসরণে দেশের শাসনকার্য পরিচালিত হয় এবং যার ওপর সমাজ ও সভ্যতার গোটা কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, সেই আইন কানুন ও বিধি বিধানের নাম দীন। মানব জীবনের এই সকল দিক ও বিভাগ সামগ্রিকভাবে যে নিয়ম নীতি ও প্রথা পদ্ধতি অনুসারে চলে, কুরআনী পরিভাষায় তাকেই দীন বলা হয়। যেহেতু মিসরে প্রচলিত তৎকালীন নিয়ম নীতি ও প্রথা পদ্ধতি ফিরাউনের ইচ্ছা থেকেই উদগত ও উৎপন্ন হতো এবং তার সার্বভৌম ও নিরংকুশ ক্ষমতাই ছিলো তার উৎপত্তির উৎস ও ভিত্তি, তাই কুরআন সেটাকে “দীনুল মালিক” [রাজার দীন] বলে আখ্যায়িত করেছে। এথেকে বুঝা গেল যে, দীন” শুধু মসজিদের চার দেয়ালে এবং নামায রোযার মধ্যেই সীমিত উপাসনা ও পূজা পার্বনের অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং এটাও আল্লাহর গোটা শরীয়ত ব্যবস্থার আনুগত্যের নাম, যার উদ্ভব ঘটে আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টি থেকে, যার উৎপত্তি আল্লাহর সার্বভৌমত্ব থেকে এবং যা মানুষের সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগ নিয়ে ব্যস্ত ও বিস্তিৃত। এখন প্রশ্ন হলো, হযরত ইউসূফ আল্লইহিস সালাম কোন কাজের জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন? “আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিতে, না রাজার দীন কে চালু করতে এবং উৎকর্ষ দিতে? খান বাহাদুর সাহেবের ব্যাখ্যা এবং তিনি যে মনীষীদের নামোচ্চারণ করে আমাদেরকে ভড়কিয়ে দিতে চান তাদের তাফসীর যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে এ কথাও মেনে নিতে হয় যে, আল্লাহ তায়ালা একদিকে তাঁর নবীকে এই মর্মে নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি যেনো তাঁর বান্দাদেরকে- বিশেষত মিসরবাসী বান্দাদেরকে “আল্লাহর দীন” গ্রহণের দাওয়াত দান, আর অপরদিকে সেই নবী স্বয়ং আল্লাহর নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে “রাজার দীন” কায়েম করা ও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে নিয়োজিত হয়ে গেলেন। আরো মজার ব্যাপার হলো, এমন সুস্পষ্ট পরস্পর বিরোধী কার্যকালাপে কোনো বৈপরিত্য ও বৈসাদৃশ্য আছে কিনা আল্লাহ তা টেরই পেলেননা, বরং নবীর ঐ কার্যকালাপকে খানবাহাদুর সাহেবের ভাষায় অভিনন্দন জানাতে ও প্রশংসা করতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাঁর নবীর ওজারতী লাভকে “খোদায়ী পুরস্কার” বলে আখ্যায়িত করতে লাগলেন। অর্থাৎ কিনা আল্লাহ মিয়া, নাউজুবিল্লাহ, আমাদের যামানার সেইসব ধর্মপ্রাণ মুরব্বীদের মতো, যারা নিজেরা তো কপালে কালো দাগ নিয়ে জায়নামাযে সিজদার ওপর সিজদা দিয়ে যান, কিন্তু স্বীয় পুত্ররত্ন যখন এম এ পাস করে আধা ইংরেজ হয়ে খৃষ্টান সরকারের অধীনে কাস্টম ইনসপেক্টরের চাকরি পায়, তখন সেই আপাদমস্তক ধর্মের সাজে সজ্জিত মুরব্বী এজন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করেন যে, তিনি তার বংশধরকে স্বীয় অনুগ্রহে সিক্ত করেছেন। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে খান বাহাদুর সাহেব আবার বলেনঃ
“তাই বলে একথা বলা যায়না যে, মিসরের ওজারতীতে অভিষিক্ত হবার পর হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম ইসলাম প্রচারের কাজ করেননি, কিংবা নিজের নবূয়্যতের ঘোষণা দেয়া থেকে বিরত থেকেছেন। বরঞ্চ তিনি জেলে থাকাকালেই তাওহীদের মর্মবাণীর প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। ….. তবে যেকথা এ আয়াত থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় তা হলো, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম একটি অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থায় নিজ আগ্রহে এবং আবেদনক্রমেই সদস্য হয়েছিলেন এবং হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের সে সরকারের সদস্য হওয়ার পরও দেশে অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং অনৈসলামিক আইনই কার্যকর ছিলো।”
এখানেও আবার সেই একই স্ববিরোধীতা স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। অথচ খান বাহাদুর সাহেব নিজ মতের চিন্তায় বিভোর থাকার সেদিকে মনোযোগ দিতে পারেননি। হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম যে তাওহীদ বা একত্ববাদ প্রচার করেছিলেন সেটা কি ধরনের একত্ববাদ ছিলো? এই একত্ববাদের অর্থ যদি এটাই হয়ে থাকে যে, উপাসনালয়ে যে উপাসনা করা হয় এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রশাসন ও নিয়ম শৃংখলা যে আইনানুগত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তার সবই হবে একমাত্র আল্লাহর জন্য, অন্য কথায় যার অর্থ হলো, সমগ্র জীবন আল্লাহর আনুগত্যের আওতাধীন হয়ে যাওয়া, তাহলে দেখা যায়, খান বাহাদুর সাহেবের ব্যাখ্যা অনুসারে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম বাদশাহর চাকরী করে নিজেই নিজের প্রচারিত সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। আর যাদি তাঁর প্রচারিত তত্ত্ব এই হয়ে থাকে যে, উপাসনালয়ে আল্লাহর বিধান চালু হবে আর দেশ ও সমাজের গোটা ব্যবস্থা চলতে থাকবে রাজার বিধান অনুসারে, তাহলে এটা যে একত্ববাদের নয় বরং দ্বিত্ববাদের তথা দুমুখো নীতির প্রচার ছিলো, সেটা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।
এখানে এ প্রশ্নও না উঠে পারেনা যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম তাহলে কোন অর্থে নিজের নবূয়্যতের ঘোষণা দিয়েছিলেন? তিনি যদি বাদশাহসহ সকল মানুষকে বলে থাকেন যে, আমি আসমান ও যমীনের মালিকের প্রতিনিধি! সুতরাং তোমরা আমার আনুগত্য করো। যেমন সকল নবী বলতেনঃ
“আল্লাহকে ভয় করো ও আমার আনুগত্য করো।” [সূরা শুয়ারাঃ ১০৮]
তাহলে এরূপ ঘোষণার সাথে তাঁর একজন অমুসলিম রাজার প্রভূত্ব মেনে নেয়া এবং তাঁর আনুগত্যের আওতায় ইসলামী রাষ্ট্রের পরিবর্তে ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্রের খিদমত করা কিছুতেই সামঞ্জস্যশীল হতে পারেনা। আর যদি তিনি একথা বলে থাকেন যে, ওহে জনগণ! আমি যদিও আকাশ ও পৃথিবীর রাজাধিরাজের প্রতিনিধি, তথাপি আমার নীতি হলো, মিসরের বাদশাহর আনুগত্য করবো আর তোমাদেরকেও দাওয়াত দিচ্ছি যে, আমার নয় বরং বাদশারই আনুগত্য করো, তাহলে এটা একটা সুস্পষ্ট স্ববিরোধী বক্তব্য, যাকে স্বাভাবিক ভাবগাম্ভীর্যর সাথে গ্রহণ করার তো প্রশ্নই উঠেনা, বরং তা অট্টহাসি দিয়ে উড়িয়ে দেয়ারই যোগ্য। আর এ ধরনের ঘোষণাকারীর মন্ত্রণালয়ে নয় বরং পাগলা গারদেই স্থান পাওয়ার কথা ছিলো। শুধু তাই নয়, কোনো আসমানী কিতাব যদি একদিকে এরূপ মূলনীতি বর্ণনা করে যে, আল্লাহ যাকেই রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছেন আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করতে হবে।
“আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি, পাঠিয়েছি এজন্য যেনো আল্লাহর নির্দেশ তাঁর আনুগত্য করা হয়।” [সূরা আননিসাঃ ৬৪]
অপরদিকে সেই কিতাবই যদি এমন এক ব্যক্তিকে আল্লাহর রসূল বলেও ঘোষণা করে যিনি আনুগত্য লাভ করাতো, দূরে থাক, নিজেই আল্লাহ ছাড়া অন্যের আনুগত্য করেছেন এবং জনগণকেও গায়রুল্লাহর আনুগত্য করতে বলেছেন, তাহলে এ ধরনের কিতাবের ওপর আদৌ ঈমান আনা সমিচীন হতে পারেনা। কুরআন যে স্বয়ং আল্লাহর পক্ষে থেকেই প্রেরিত গ্রন্থ, সেকথা প্রমাণ করার জন্য সে যে মাপকাঠি দিয়েছে সেটি হচ্ছেঃ
“এ কিতাব যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর পাঠনো কিতাব হতো তাহলে মানুষ এতে অনেক স্ববিরোধী ও পরস্পর বিরোধী কথাবার্তা দেখতে পেতো।” [সূরা আননিসাঃ ৮২]
কিন্তু আমরা যদি জনাব খান বাহাদুর সাহেব ও তার সমমনা লোকদের ধ্যান ধারণা মেনে নিই, তাহলে দেখা যাবে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআনের বর্ণনায় এমন প্রকাশ্য স্ববিরোধীতা বিদ্যমান, যার দরুন কুরআন তার নিজেরই প্রতিষ্ঠিত মাপকাঠি অনুসারে আল্লাহর নয় বরং অন্য কারো গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাও কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক বিশিষ্ট মানুষের গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবেনা।
আসল ব্যাপার হলো, খান বাহাদুর সাহেব যে চিন্তাধারার প্রতিধ্বনি করছেন, তার পশ্চাতে নৈতিক অধোপতনের এক দীর্ঘ ও মর্মন্তুদ ইতিহাস রয়েছে।
ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে বিভাজনের ঐতিহাসিক এবং মানসিক পার্যালোচনা
মুসলমানরা যখন তাদের আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে এবং তাদের সত্যিকার করণীয় কাজ পরিত্যাগ করে দুনিয়া পূজায় লিপ্ত হয়েছে, যখন দীনদারীর অর্থ তাদের কাছে হয়েছে ইবাদাত ও আচার আচরণে কিছু শরীয়তসম্মত রীতি নীতি মেনে চলা, তা সে জীবনের উদ্দেশ্য দুনিয়া পূজারীদের মতোই হোক না কেন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার কর্তৃত্ব নেককার কিংবা পাপিষ্ঠ যাদের হাতেই থাকুক না কেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব নীতিগত ও আদর্শগতভাবে ইসলাম হোক কিংবা ইসলামী বিরোধী। তখন এই উদাসীনতা ও শৈথিল্যের শাস্তি আল্লাহর তরফ থেকে এভাবেই দেয়া হয়েছে যে, তাদের বিরাট বিরাট অঞ্চল ও জনগোষ্ঠী একে একে কাফেরদের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তারা ও তাদের আলেম সমাজ তাকে শাস্তি মনে না করে এবং যে পাপের জন্য তাদের এ শাস্তি হয়েছে তার প্রতিকার না করে উল্টো এটাই ভাবতে শুরু করেছে যে, কাফের শাসিত ঐ রাষ্ট্র ও সমাজে কিভাবে “মুসলমানী জীবন” যাপন করা যায়। এজন্য “ইজতিরার” তথা “অনন্যোপায় অবস্থা”র ওজুহাত তুলে শরীয়তসম্মত মুসলমানী জীবনের এমন এক চিত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে, যা অনৈসলামিক ও শরীয়ত বিরোধী সমাজ ও রাষ্ট্রে চালু রাখা যায়।
এর ফলে আল্লাহর তরফ থেকে আরো শাস্তির পালা শুরু হলো। তারা অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, না গোমরাহীতে আরো দূরে সরে যায়, সেটা পরীক্ষা করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। যে অবস্থাটাকে প্রথমে একটা অনন্যোপায় অবস্থা ভাবা হয়েছিলো, আল্লাহর চিরন্তন রীতি অনুসারে তা আরো বেড়ে গেলো এবং স্থায়ী ক্রমবর্ধমান ও অফূরন্ত আযাবের রূপ ধারণ করলো। প্রতিটি গোলামী মুসলমানদেরকে প্ররোচিত করতে থাকলো যে, একটা কুফরী ব্যবস্থার অধীন এবং তার অভ্যন্তরে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য তোমরা যে কর্মপন্থা অবলম্বন করেছো, তা সংশোধিত করো এবং ক্রমান্বয়ে সুংকুচিত করতে থাকো। কিন্তু আল্লাহর তরফ থেকে আগত এসব আযাব মুসলমানদের সচেতন করতে পারলোনা। তারা স্থায়ীভাবে এই নীতি অবলম্বন করলো যে, অনন্যোপায় অবস্থায় যখন পড়েছি, তখন ইসলামী জীবনের পরিধি সংকুচিত করাই দরকার এবং কুফরীর আধিপত্য সম্প্রসারিত হতে থাকুক।
কিছুদিন যেতে না যেতে এই অনন্যোপায় গোলামীদশা তাদের বিবেককে দংশন করতে আরম্ভ করলো। কেননা অনন্যোপায় অবস্থার পশ্চাতে নিষিদ্ধতার ধারণা অবশ্যম্ভাবীরূপে বিদ্যমান থাকে। কোন বিবেকবান মানুষ ও সস্পষ্ট ব্যাপারটা অনুভন না করে পারেনা যে, আপনি যখন নিছক অনন্যোপায় হওয়ার কারছে শূকরের গোশত খাচ্ছেন, তখন শূকরের গোশত যে হারাম, সে কথাটাতো আপনার ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। অতপর যখন ওটা মূলত হারাম জেনেও বাধ্য হয়ে খান, তখন আপনার মনে তার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা না থেকে পারেনা। এটা একেবারেই অসম্ভব যে, আপনি মজা করে পেট ভরে খাবেন এবং ওটার কাবাব কোর্মা ও পোলাও বানানের চিন্তা করবেন। এধরণের ঘৃণা ও অবস্থার মানসিকতা সেই ক্ষেত্রেও অবিবার্যভাবে সৃষ্টি হয়, যেখানে আপনি সামগ্রিক জীবন ধারাকে মৌলিকভাবে হারাম বলে জানা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অপরাগতা ও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকার কারণে সাময়িকভাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। কিন্তু গোটা একটা জাতির পক্ষে এ ধরনের দোটানা জীবন যাপন সম্ভব নয়। একটি জাতির পক্ষে সফল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে সার্বক্ষণিকভাবে এরূপ জীবন ধারণ করা কার্যত সম্ভব নয় যে, নিজেকে শরীয়তের দিক দিয়ে এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে অনন্যোপায় ও অক্ষমও ভাবতে থাকবে, আবার সে সমসাময়িক জীবনধারা থেকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সাথে পাশ কাটিয়েও চলতে থাকবে এবং শুধুমাত্র যতোটুকু না হলেই চলেনা ততোটুকু সম্পর্ক বজায় রাখবে। এধরনের পরিস্থিতি অল্প সময়ের জন্য ছাড়া বরদাশত করা সম্ভব নয়। অচিরেই মানুষ এর আঘাতে জর্জরিত হয়ে ক্লান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়ে। মুসলমানদের মধ্যে এই ক্লান্তি ও অবসাদ যথাসময়েই এসেছে। কিন্তু আগে থেকে বলে আসা ধর্মীয় পশ্চাদপদতা এই অবসন্ন মস্তিষ্কগুলোকে নিজেদের ত্রুটি খতিয়ে দেখার দিকে মনোনিবেশ করতে দেয়নি। “কুফরী ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় ইসলামী জীবন যাপন সম্ভব” এই মর্মে তারা ইতিপূর্বে যে মত স্থির করেছিলো, তা যে কতখানি ভ্রন্ত, সেকথা পুনরায় ভেবে দেখতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেনি। যে অনন্যোপায় অবস্থার কারণে তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ জিনিষের মধ্যে আটকা পড়ে গিয়েছিলো এবং নোংরা অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলো, সেই অনন্যোপায় অবস্থার অবসান কিভাবে ঘটানো যায়, তা চিন্তা করার সুযোগ দেয়নি। বরং ক্রমাগত ধর্মীয় অধপতনের দারুন তারা একথাই ভাবতে প্ররোচিত হয়েছে যে, এই “অনন্যোপায় অবস্থার” অজুহাতটাকেই শেষ করে দেয়া দরকার, যাতে যেসব বিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুর বাধা বিপত্তিতে কফূরী সমাজ ব্যবস্থায় তাদের উন্নতি ও বিলাসিতা ব্যাহত হয়ে চলেছে, তার অবসান ঘটে এবং তা হালাল ও বৈধ হয়ে যায়।
এই উদ্দেশ্যে ধর্ম সম্পর্কে এক নতুন মতবাদ সৃষ্টি করা হয়েছে। মতবাদটা হলো, ধর্মের সম্পর্ক শুধু আকীদা বিশ্বাস, ইবাদত, উপসনা ও বিয়ে তালাকের মতো কয়েকটা সামাজিক ব্যাপারের সাথে। কোনো শাসন ব্যবস্থা যদি এসব ব্যাপারে মুসলমানদেরকে নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলেই ইসলামী জীবনের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে যায়। এটুকু হলেই কুফরী রাষ্ট্র মুসলমানদের জন্য শান্তির আবাস ভূমিতে পরিণত হয়। তার আনুগত্য করা ও আইন মান্য করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। সেই রাষ্ট্রের অধীন যাবতীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড [যা কিনা উক্ত নয়া মতবাদ অনুসারে ধর্মের বিপরীত দুনিয়াবী বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়] উক্ত কুফরীভিত্তিক আইন কানুন অনুসারেই সম্পন্ন হওয়া উচিত। আর এ রাষ্ট্রের আইনগত ও প্রশাসনিক অবকাঠামোকে পরিচালনা, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করাতে মুসলমানদের জন্যে কোনো আপত্তি নেই।
কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র “আপত্তি না থাকা” এবং হালাল ও বৈধ হয়ে যাওয়া পর্যন্তই থেমে থাকলোনা। অচিরেই অনৈসলামিক রাষ্ট্রে মুসলমানরা জৈবিক প্রয়োজনের তাগিদে তাদের নব্য বংশধরকে কুফরী ব্যবস্থার সেবায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টায় নিয়োজিত হতে বাধ্য হলো, যাতে করে প্রথম দিকের কিছুকাল ”আপত্তি” থাকার কারণে যে ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ হয়। এজন্য সর্বশেষ যে যুক্তিটি তুলে ধরা হয় তা এই জন্য যে, মুসলমানদের উন্নতি, সমৃদ্ধি এবং কোনো ক্ষেত্রে তাদের বেঁচে থাকাটাই সম্ভব নয়- যদি না তারা অনৈসলামি রাষ্ট্রের বিচার বিভাগে, আইন সভায়, প্রশাসনে, সামরিক বাহিনীতে, শিল্পকারখানায়- এক কথায় সকল বিভাগে বেশী বেশী করে অংশ গ্রহণ না করে। নচেৎ মুসলিম উম্মাহর সার্বিক ধ্বংস অথবা কমপক্ষে উন্নতি ও অগ্রসরতার প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ার আশংকা রয়েছে। এ যুক্তির ফলে সহসাই যে জিনিস একদিন আগে বৈধ বা মোবাহের পর্যায়ে ছিলো তা ফরযের পর্যায়ে উন্নীত হলো। আর সবাই যদি নাও পারে, তবু অন্তত মুসলমানদের মধ্য থেকে একটা গোষ্ঠী যেন এ ফরয পালন করতে এগিয়ে আসা অব্যাহত রাখে। অর্থাৎ কিনা, আল্লাহর হুকুম যেখানে এরূপ ছিলোঃ
“মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে অন্তত একদল লোকের ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া উচিত, যাতে তারা ফিরে এসে নিজ জাতিকে সতর্ক করতে পারে। এভাবে আশা করা যায় যে, তারা সংশোধিত হবে।”
সেখানে আল্লাহর হুকুম তাদের দাবীতে এরূপ দাঁড়ালোঃ
“মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী থেকে অন্তত একটি গোষ্ঠীর কুফর সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জনের জন্য বেরিয়ে পড়া উচিত, যাতে তারা ফিরে এসে নিজ জাতিকে পথভ্রষ্ট্র করতে পারে। এভাবে আশা করা যায়, তারা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে।”
আর যেখানে আল্লাহর হুকুম ছিলোঃ
“তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদল লোক অবশ্যই গড়ে ওঠা চাই যারা মানুষকে কল্যাণের পথে ডাকবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।”
সেখানে এই নব্য মতবাদের ধারক বাহকদের দবীতে আল্লাহর হুকুম দাঁড়ালো এরূপঃ
“তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি গোষ্ঠী অবশ্যই গড়ে উঠা চাই যারা মানুষকে অকল্যাণের দিকে ডাকবে, মন্দ কাজের আদেশ দেবে ও ভালো কাজ থেকে বিরত রাখবে।”
ইসলামকে বিকৃত করার এই সর্বনাশা অপকীর্তির বদৌলতেই বড় বড় পরহেজগার ও ধর্মপ্রাণ লোক তসবীহ টিপতে টিপতে ইংরেজদের অধীনে ওকালতি ও মুনসেফীর পেশায় প্রবেশ করলেন। এভাবে তারা যে আইনের প্রতি তাদের ঈমান নেই, সেই আইন অনুসারে মানুষের বিরোধের মীমাংসা ও ফয়সালা করতে লাগলেন, আর যে আইনের প্রতি তাদের ঈমান ছিলো, তা কেবল ঘরে বসে তেলাওয়াত করতে লাগলেন। এ বিকৃতির দরুনই বড় বড় মুত্তাকী ও নেক্কার লোকদের সন্তানরা আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তি হলো এবং সেখান থেকে ধর্মহীনতা, বস্তবাদ ও চরিত্রহীনতার সবক নিয়ে নিয়ে বেরুলো। অতপর তারা সেই অনৈসলামিক রাষ্ট্র ও সমাজের শুধু কর্মের মাধ্যমে নয় বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে চরিত্র ও আকীদা বিসর্জন দিয়েও খিদমত করতে লাগলো। অথচ সেই সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় ব্যবস্থা শুরুতে তাদের পূর্বপুরুষদের দুর্বলতা ও শৈথিল্যের কারণে তাদের ওপর কেবল ওপর থেকেই চাপিয়ে দেয়া হয়েছিলো। এই বিকৃতি শেষ পর্যন্ত এমন সর্বাত্মক রূপ ধারণ করলো যে, পুরুষদেরকে অতিক্রম করে নারীদেরকেও তার সর্বব্যাপী জাহেলিয়াম, গোমরাহী ও চরিত্র ভ্রষ্টতার সয়লাবে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। তথাকথিত সেই “ফরযে কিফায়া” যা পালন করার জন্য প্রথমে পুরুষরা এগিয়ে গিয়েছিলো, এখন নারীদের ওপরও তা আরোপিত হলো। আর এই বেচারীরাও শেষ পর্যন্ত এই “ধর্মীয় খিদমত” আঞ্জাম দিতে এগিয়ে আসতে বাধ্য হলো। এগিয়ে না এলে অমুসলিমরা তাদেরকে পেছনে ফেলে যাবে এই আশংকা ছিলো। [পাকিস্তান হওয়ার পর এব্যাপারে আরো অগ্রগতি হয়েছে। এখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা যদি উন্মক্ত ময়দানে সামরিক কুচকাওয়াজ না করে, মুসলিম মেয়েরা যদি নার্সিংয়ের ট্রেনিং নিতে পাশ্চাত্য দেশে না যায় এবং বিদেশে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পুরুষরা ছাড়া মেয়েরাও পালন না করে তাহলে তা মুসলিম উম্মাহর টিকে থাকর আর কোন উপায়ই নেই।]
এরূপ মনে করার কোনো কারণ নেই যে, ইসলামের এই বিকৃত উপলব্ধি ও ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দানের পালা আজকেই নতুন শুরু হলো। আজ থেকে কয়েক শ’ বছর আগে যখন তাতারী কাফিররা মুসলমানদের ওপর চড়াও হয়, তখন থেকেই এর সূচনা। “কূফরী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন কিভাবে ইসলামী জীবন যাপন করা যায়” সে ফর্মূলা যে সেযুগের আলেমরা শুধু আবিষ্কারই করেননি, বরং বড় বড় আলেম ও নেক্কার লোকেরা স্বয়ং সে আমলেই অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সেবা করতে আরম্ভ করেন। তাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যাও প্রচুর, যাদের লেখা কিতাব পড়ে পড়ে আজকাল আমাদের আরবী মাদ্রাসাগুরোতে আলেম ও মুফতী তৈরী হয়ে থাকে। এই প্রচীনত্বের কারণেই এ ভুল এখন একটা পবিত্র ভুলে পরিণত হয়েছে। এযুগের প্রায় সকল মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফিকাহবিদকে যদি একই বিভ্রান্তিতে লিপ্ত দেখা যায়, তাহলে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। তবে একথা বলাই নিষ্প্রয়োজন যে, একটা ভুল অনেকদিন ধরে চলে আসছে বলেই তা বিশুদ্ধ ও নির্ভূল হয়ে যেতে পারেনা। আর বহু নামজাদা ব্যক্তি এতে আক্রান্ত- এই যুক্তিতেও তা সঠিক হয়ে যেতে পারেনা। সত্যকে প্রমাণিত করতে হলে একমাত্র আল্লাহর কিতাব ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহ দ্বারাই করতে হবে।
অধপতনের এই যুগটা শুরু হয়েছে প্রাথমিক অনন্যোপায় অবস্থা থেকে উদ্ভুত “কুফরীর অধীনে ইসলাম” এই মতবাদ দিয়ে। অতপর ক্রমান্বয়ে কুফরী ব্যবস্থার খেদমত করা জায়েয হলো, তারপর মুস্তাহাব হলো, অতপর তা ফরযে কিফায়া’ পর্যন্ত গিয়ে পৌছলো। এমনকি সর্বশেষ নামতে নামতে “ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদানকারী শাসকদের আনুগত্যই ইসলামের যথার্থ দাবী” এহেন চরম অবমাননাকর ধারণা পোষণের মত সর্বনিম্ন গহ্বরে গিয়ে তা পতিত হলো। পতনোন্মখ যুগের মুসলমানদের বরাবর এই চেষ্টায় নিয়োজিত থাকতে হয়েছে যে, পতনের প্রত্যেকটা স্তরে তাদের আরো নীচে নামার জন্য দলীল প্রমাণ যা কিছু প্রয়োজন, আল্লাহর দীন থেকেই সংগ্রহ করা চাই। এই তাগিদ অনুভব করার মূলে তো তাদের ধারণা মোতাবেক এই ফর্মূলাই কার্যকর ছিলো যে, “যেহেতু আল্লাহর দীন আমাদের সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট, তাই এখন যে প্রয়োজন দেখা দিয়েছে তা পূরণের জন্যও এই দীন থেকেই আমাদের পথ নির্দেশ লাভ করতে হবে।” কিন্তু আসলে এই লোক দেখানো ফর্মূলার পেছনে যে প্রকৃত ফর্মূলা লুকিয়ে ছিলো এবং যার ভিত্তিতে তারা বাস্তবে কর্মতৎপর ছিলো তা ছিলো এই যে, “আমরা যখন আল্লাহর দীনের প্রতি এতো অনুগ্রহ করেছি, তার প্রতি ঈমান এনে তাকে ধন্য করেছি, তখন এর বিনিময়ে ইসলামের ওপর অন্ততপক্ষে এটুকু দায়িত্ব বর্তায় যে, সে আমাদের আগে আগে না চলে পেছনে চলতে আরম্ভ করবে। অর্থাৎ এখন আর তার সাথে আমাদের এরূপ সম্পর্ক থাকবেনা যে, আমরা তাদের নিজেদের ওপর ও আল্লাহর যমীনের ওপর কায়েম করার চেষ্টা চালাবো এবং এই চেষ্টার ক্ষেত্রে আমরা যেসব প্রয়োজনের সম্মুখীন হই, তা পূরণ করার দায়িত্ব সে গ্রহণ করবে। বরং এখন সম্পর্কের রূপরেখা হবে এরকম যে, আমরা ইসলামকে কায়েমের চেষ্টা তো দুরের কথা, তা চিন্তাও করবোনা। বরং নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণের জন্য আমরা যেমন খুশী, যেখানে খুশী যাবো, ইসলাম আমাদের পেছনে পেছনে ঘুরতে থাকবে। আমরা যে কোনো বাতিল ধর্মের অনুসারী হই, যে কোনো বাতিল ব্যবস্থার গোলামী করি, ইসলামের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে ধরনের জীবন পদ্ধতিই অবলম্বন করি, ইসলাম সেক্ষেত্রে আমাদের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ করার নিশ্চয়তা দেবে।” এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভংগি নিয়েই তারা কুরআন ও হাদীস মন্থন করে পথ নির্দেশের সন্ধানে ব্যাপৃত হলো। এর ফলে এই দাঁড়ালো যে, সমগ্র কুরআনের আর কোথাও তাদের দৃষ্টি পড়লো না- সূরা আনকাবুতেও না, কাবারাতেও না, আল ইমারানেও না, আনফালেও না, তাওবাতেও না- বরং শুধুমাত্র সূরা ইউসূফের ওপর গিয়েই তাদের দৃষ্টি থমকে দাঁড়ালো। আর তাও শুধু খান বাহাদুর সাহেবের যুক্তি সংগ্রহের পছন্দমাফিক জায়গাগুলোতে। অনুরূপভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনীরও আর কোথাও তাদের অনুকরণীয় আদর্শ মিললোনা, মক্কার তপ্ত মরুতেও নয়, তায়েফের পাথর বর্ষণেও নয়, বদর ও ওহুদের ময়দানেও নয় বরং শুধু এই ঘটনায় যে, মুসলমানদের একটি দল হিজরত করে আবিসিনিয়ায় গিয়েছিলো এবং সেখানে এক খৃষ্টান রাজার অধীন কয়েক বছর প্রজা হিসেবে বসবাস করেছিলো।
কিন্তু যে ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মানসিকতা নিয়ে নয়, বরং সত্যসন্ধানী মনোভাব নিয়ে প্রকৃত সত্য উদঘাটন করতে চায়, তার জন্য এ প্রশ্নটা অত্যন্ত গুরুত্ববহ যে, প্রকৃত পক্ষে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের আলোচ্য ঘটনাবলী এবং আবিসিনিয়া হিজরতের বৃত্তান্ত থেকে এই বিশেষ মহলটি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চান, সত্যিই কি সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অবকাশ আছে? বেশ আপাতত না হয় ধরে নিলাম, অবকাশ আছে। অর্থাৎ একথা মেনে নেয়ার অবকাশ আছে যে, জনৈক নবী আল্লাহর নির্দেশে একটি অনৈসলামিক রাষ্ট্রের খিদমত করা এবং অনৈসলামিক আইন [রাজকীয় আইন] চালু করা ও কার্যকরী করার দায়িত্ব এই জন্য গ্রহণ করছিলেন যে, এটা মুলতই একটা অভিষ্ঠ ও করণীয় কাজ ছিলো। একথাও না হয় মেনে নিলাম যে, একটি মুসলিম কোন অমুসলিম রাষ্ট্রে কেবল মসজিদের ভেতরে ইচ্ছামত ইবাদত উপাসনা করা, বুকের ভেতরে কিছু আকীদা বিশ্বাস পোষণ করা এবং মুখ দিয়ে সেই বিশ্বাসের সপক্ষে কিছু উচ্ছাস প্রকাশের অনুমতি দিলেই সেই সমাজ ও রাষ্ট্রে মুসলমানদের সম্পূর্ণ উপযোগী আবাসভূমিতে পরিণত হয় আর এজন্যেই মুসলমানরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন। কিন্তু এরপর আরো কতগুলো প্রশ্ন জন্ম নেয়। সে প্রশ্ন গুলো উপরোক্ত প্রশ্নের তুলনায় অনেক বেশী মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী। কেননা উপরোক্ত কথা দুটো মেনে নেয়ার পর নিম্নের প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে বের করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে।
কতিপয় মৌলিক প্রশ্ন ও সেগুলোর জবাব
১. আল্লাহ তায়ালা নবীদের মাধ্যমে মানব জাতির জন্য যে দীন বা জীবন বিধান পাঠিয়েছেন, তা কি শুধু উপাসনালয়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিলো, না সমগ্র মানব জীবনের জন্য?
২. যে সমস্ত নবী এই দীন নিয়ে এসেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি একটাই ছিলো, নাকি এক এক জন এক এক রকমের কিংবা পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলেন?
৩. মানুষের কাছে আল্লাহর প্রকৃত দাবী কি? সমগ্র জীবনের তাঁর দাসত্ব করুক এবং তাঁরই আইন ও বিধান অনুসারে কাজ করুক, নাকি কেবল পূজাটা তার করুক, আর বাদবাকী সমস্ত কর্মকান্ড যেভাবে ইচ্ছা পরিচালনা করুক?
এ প্রশ্নগুলোর একটা জবাব এরূপ হতে পারে যে, আল্লাহ যে দীন পাঠিয়েছেন তার সম্পর্ক শুধু আজকাল “ধর্মীয় জীবন” বলতে যে সীমাবদ্ধ জীবন বুঝায় তার সাথে। কিন্তু একথা মেনে নিলে কুরআনে ও অন্যান্য আসমানী কিতাবে রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিধি, সাক্ষ্যদানের বিধি এবং যুদ্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি সম্পর্কে যেসব নিয়মনীতি ও নির্দেশ দান করা হয়েছে, তা সব নিরর্থক হয়ে যায়। সেসব নির্দেশতো নির্দেশ নয় বরং নিছক উপদেশ ও সুপারিশমালার পরিণত হয়। অর্থাৎ ওগুলো কার্যকরী করতে পারলে ভালো। আর না করলেও তাতে আল্লাহর বিশেষ কোনো আপত্তি থাকবেনা।
অনুরূপভাবে দ্বিতীয় প্রশ্নের একটা সম্ভাব্য জবাব সম্ভাব্যই বা বলি কেন, আজকাল নবূয়্যত সম্পর্কে সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণাই এই যে, বিভিন্ন নবী বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন। এমনকি এক নবী যদি কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে উৎখাত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম চালাতে এবং তার স্থালে ইসলামী বিধানকে পৃথিবীতে শাসন ব্যবস্থা হিসেবে কায়েম করতে এসে থাকেন, তবে অন্য আরেক নবী ঠিক তার বিপরীত কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন সীমিত ধর্মীয় ও নৈতিক সংস্কার সাধন করেই ক্ষ্যান্ত থাকা, এমনকি সেই কুফরী ব্যবস্থার অনুগত থাকা মওকা পেলে তার পরিচালনার ও উৎকর্ষ সাধনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণেও প্রস্তুত থাকার লক্ষ্য নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এ বক্তব্য কি কুরআনের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল? আসলে তা বিবেকের কাছেও গ্রহণযোগ্য নয়। কুরআন অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করছে, সকল নবীকে একই উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে বিবেকেও একথা বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে, আল্লাহ তায়ালা এমন স্ববিরোধী ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর কাজ করতে পারেন। আল্লাহ যদি মানব জাতির কাছে এক সময় এক উদ্দেশ্য এবং অন্য সময় ঠিক তার বিপরীত উদ্দেশ্যে নবী পাঠান, তবে তাকে কোনো সাধারণ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও বিজ্ঞ ও মহাজ্ঞানী বিশ্ববিধাতা হিসেবে মেনে নিতে পারেনা। এটাতো ভিন্ন কথা যে, কোনো নবী ইসলামী বিধান বাস্তাবায়নের সংগ্রামে সাফল্যের সর্বশেষ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেন, অপর নবী মধ্যবর্তী অথবা প্রাথমিক স্তরেই সারা জীবন কাজ করে যেতে পারেন আর তৃতীয় আর কোন বনী দাওয়াত, প্রচার অথবা যুদ্ধবিগ্রহের পরিবর্তে বিকল্প কোনো কর্মপন্থাকে নিজের সময়কার বিশেষ ধরণের পরিস্থিতিতে কার্যপযোগী পেয়ে সেটাই গ্রহণ করে নিতে পারেন। কিন্তু কর্মপদ্ধতির এতোসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকলের উদ্দেশ্য একই থাকে। সকলেই আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে পরিপূর্ণভাবে দুনিয়ায় বাস্তবায়িত করার চেষ্টায় নিয়োজিত থাকাকেই নিজেদের অভিন্ন লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিয়ে থাকেন। কিন্তু এই পদ্ধতিগত ও প্রক্রিয়াগত বিভিন্নতার অর্থ যদি কারো কাছে এই হয় যে, নবীদের প্রেরণের উদ্দেশ্যই বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী ছিলো, তবে সেটা হবে আল্লাহর ওপর জঘন্যতম অপবাদ আরোপের শামিল।
অনুরূপভাবে তৃতীয় প্রশ্নরও একটা সম্ভাব্য জবাব এবং আজকালকার মুসলমানদের কাছে সচরাচর সহজবোধ্য কথাও এটাই যে, আল্লহর কেবল পূজা উপাসনা করবে এবং ওযু গোছল, পাক নাপাক ও কতিপয় নির্দিষ্ট হালাল হারামের বিধি মেনে চলবে, মানুষের কাছে এতোটুকুই আল্লাহর দাবী। এর চেয়ে বেশী কিছু তিনি চানও না, আর মানুষ তার জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে নিজের প্রবৃত্তির আইন মেনে চলে, নাকি আল্লাহর বিশাল পৃথিবীতে জেঁকে বসা মানুষ শয়তান ও জিন শয়তানদের কথামতো চলে, তা নিয়েও আল্লাহর কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে এই জবাব এযুগের জড়বাদী মানুষের কাছে যতো তৃপ্তিদায়কই হোক না কেন এবং “সরল ও সহজ পন্থাই ইসলাম” এই হাদীস এবং “আল্লাহ তোমার ওপর ইসলামে কোনো কঠিন বিধি আরোপ করেননি।” এই আয়াতের মর্ম স্বেচ্ছাচার ও লাগামহীন ভোগাধিকার ধরে নিয়ে নিজের জন্য যত আয়েসী জীবনের পথই সুগম করুক না কেন, এটা যে আল্লাহর দাসত্ব ও গোলামীর প্রকৃত তত্তের পরিপন্থী, সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।
একজন বন্দা ২৪ ঘন্টার মধ্যে মাত্র দুঘন্টার জন্য বান্দা হবে, আর বাদবাকী সময় স্বাধীন থাকবে অথবা মনিবকে শুধু সালাম ঠুকেই গোলামীর দায়িত্ব চুকিয়ে দেবে আর অন্যসব কাজ প্রভুর ইচ্ছার তোয়াক্কা না করে নিজের অথবা অন্যদের ইচ্ছামতো করার অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করবে, দাসত্বের এর চেয়ে হাস্যকর চিত্র বোধ হয় আর কিছু হতে পারেনা। তাছাড়া এমন খোদাকে তো খোদা মানার প্রশ্নই উঠেনা, যিনি নিজেকে একদিকে মানুষের স্রষ্টা ও পালনকর্তাও বলেন, অপরদিকে মানুষের সমগ্র সত্তা, সকল শক্তি সামর্থ এবং সময় ও উপকরণ বাদ দিয়ে তার একটা অতি ক্ষুদ্র ও গুরুত্বহীন অংশে নিজের প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব এবং তার গোলামী ও দাসত্বকে সীমিত রাখতে রাজী হয়ে যান। কোনো পিতা স্বীয় পুত্রের ওপর নিজের পিতৃত্বকে এরূপ সংকীর্ণ গন্ডিতে সীমিত করতে রাজী হতে পারেননা যে, আনুগত্যের প্রতীকস্বরূপ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কাজ করেই সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারপর যখন যাকে খুশী পিতার আসনে বসাবে। অনুরূপ কোনো স্বামী স্বীয় স্ত্রীর ওপর নিজের স্বামীত্বের গন্ডি সীমাবদ্ধ করে বাদবাকী সময় সে স্বেচ্চাচারিনী হয়ে যখন যার খুশী মনোরঞ্চন করে বেড়াবে এ অধিকার স্বীকার করতে পারেনা। একজন শাসকও পারেনা আপন প্রজাদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও শাসন ক্ষমতাকে এভাবে সংকুচিত করতে যে, প্রজারা কাতিপয় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ দ্বারা আনুগত্য প্রকাশ করেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে এবং তারপর যার খুশী তার আইন মানবে, যাকে খুশী কর খাজনা দেবে এবং যার ইচ্ছা তার হুকুমের আনুগত্য করবে। অথচ কেবল বিশ্ববিধাতা আল্লাহই এমন মনিব হয়ে গেলেন যে, যে মানুষ সম্পূর্ণরূপে তাঁরই সৃষ্টি, তাঁরই লালিতপালিত এবং তাঁরই সহায়তায় তার অস্তিত্ব টিকে আছে, তার ওপর কিনা তিনি নিজের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব সীমিত করে ফেলতে রাজী এবং তার কাছ থেকে গোলামীর স্বীকৃতিস্বরূপ কয়েকটি আনুষ্ঠানিক কথা ও কাজ পেয়েই তিনি আহলাদে আটখানা হয়ে গিয়ে তাকে স্বাধীন করে দিতে বা যেকোনো মনিবের গোলামী করার অনুমতি দিতে প্রস্তুত!
দীন, নবূয়্যত এবং দাসত্বের দাবী সম্পর্কে এসব ধ্যান ধারণা যদি সঠিক না হয়ে থাকে, আল্লাহর প্রেরিত দীন যদি বাস্তবিক পক্ষে মানুষের সমগ্র ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে, বিশ্বপ্রভুর দাবী যদি তাঁর বান্দাদের কাছে এই হয়ে থাকে যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সকল অবস্থায় তাঁর আইনেরই অনুগত এবং তাঁর হিদায়েতেরই অনুসারী ও আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে হবে এবং আল্লাহ যদি তাঁর নবীদেরকে এক খোদার আনুগত্য ভিত্তিক একমাত্র সত্য ও নির্ভুল জীবন বিধান কায়েম করার জন্য মানুষকে দাওয়াত দেয়া ও সেই জীবন বিধান কায়েমের চেষ্টায় নিজেদেরকেও নিয়োজিত রাখার জন্য পাঠিয়ে থাকেন, তবে একজন বিবেকসম্পন্ন মানুষের পক্ষে একথা মেনে নেয়া অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে যে, সমস্ত নবীদের মধ্যে একমাত্র হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামই এই সাধারণ নিয়মের বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত ছিলেন। কোনো কান্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষই একথা স্বীকার করতে পারেনা যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম এমন ব্যতিক্রমধর্মী অভিনব ধরনের নবী হয়ে এসেছেন, যাকে কিনা আল্লাহর দীন কায়েমের চেষ্টা বাদ দিয়ে ফিরাউনের কুফরী রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীন অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাকরি করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।
অনুরূপভাবে কোনো বিবেকবান মানুষ এ দুটো বেখাপ্পা কথাকেও খাপ খাওয়াতে অক্ষম যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতো একদিকে আরবের অনৈসলামিক সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন, অপরদিকে তাঁর কাছে আবিসিনিয়ার অনৈসলামিক ব্যবস্থাও এতোটা সঠিক ছিলো যে, একদল মুসলমানের জন্য তা একটা মানানসই স্থয়ী বাসস্থান হবার যোগ্য ছিলো। যারা ইসলামকে একটা যুক্তিসংঙ্গত ও সুসংবদ্ধ জীবন দর্শন হিসেবে বিবেচনা করেনা বরং তাকে কতকগুলো বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর অসংবদ্ধ তত্ত্বের সমষ্টি মনে করে, তাদের পক্ষে তো নবীদের জীবনেতিহাস, কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের বিধিসমূহকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যেকটির আলাদা আলাদাভাবে এমন ব্যাখ্যা করা খুবই সহজ যাতে করে তার একাংশ অপরাংশের এবং একদিক অপরদিকের সম্পূর্ণ বিপরীতরূপ ধারণ করে। কিন্তু যারা একে এক মহাবিজ্ঞানী সত্তার রচিত সুসংবদ্ধ, সুশৃংখল ও সুবিন্যস্ত বিধান হিসেবে বিবেচনা করে, তাদের পক্ষে এর প্রতিটা অংশ ও প্রতিটা দিকের এমন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অবলম্বন না করে উপায় থাকেনা, যা সামগ্রিক বিধানের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা এর এমন কোনো ব্যাখ্যা মেনে নিতেই পারেনা, যাকে আল্লাহর এই সনাতন বিধানের মধ্যে বৈপরিত্য এবং এর শিক্ষার সাথে নবীদের কাজের সংঘাত অবির্য হয়ে দেখা দেয়।
এবার আমরা সূরা ইউসূফের আলোচ্য আয়াতগুলো এবং আবিসিনিয়া হিজরতের ঘটনাবলী নিয়ে সরাসরি আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো।
ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনা থেকে ভ্রান্ত যুক্তি গ্রহণ
হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ঘটনা সূরা ইউসূফে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তা নিবিষ্টচিত্তে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তিনি নবূয়্যত লাভের পূর্বে নিজের ভাইদের বিশ্বাসঘাতকতা ও একটি বণিক দলের অসততার কারণে মিশরের “আযীয” উপাধিধারী জনৈক প্রভাবশালী মন্ত্রীর ক্রীতদাসে পরিণত হন। এই দাসত্বের সময় অথবা জেলখানায় আটক থাকাকালে আল্লাহ তাকে নবূয়্যত অভিষিক্ত করেন। খুব সম্ভবত কারাবন্দী থাকাকালেই তিনি নবূয়্যত লাভ করেন। কেননা বন্দী হবার আগে তার কথাবার্তা নবীসূলভ উচ্চমার্গের না হয়ে একজন পূণ্যবান সদাচারী ব্যক্তিসূলভ মনে হয়। এ অবস্থায় নবূয়্যত লাভের সংগে সংগেই তিনি নবী হিসেবে দাওয়াতের কাজ শুরু করে দেন। নিজের সহবন্দী কয়েদীদেরকেই তিনি সর্বপ্রথম দাওয়াত দেন। সূরা ইউসূফে এই দাওয়াতের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এটি অধ্যয়ন করে যেকোনো ব্যক্তি বুঝতে পারে যে, তাঁর ডাক “ভিন্ন ভিন্ন মনিব”- এর দিকে ছিলোনা, বরং একমাত্র মনিবের গোলামী করার দিকে ছিলো। তিনি বার বার মিসরবাসীকে হুশিয়ার করেছেন যে, যে বাদশাহকে তারা খোদার আসনে বসিয়ে রেখেছে সে আমার প্রভু নয়। বরং আমার প্রভু হচ্ছেন আল্লাহ। আমি যে ধর্মের অনুসরণ করি তা আল্লাহর দাসত্বের জীবন ব্যবস্থা। জেলখানায় ইসলাম প্রচারের এই কাজ চালানোর সময়েই আকস্মিকভাবে এক অভাবনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তাঁর ব্যক্তিত্ব থেকে যে অসাধারণ সততা, বিশ্বস্ততা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার নিদর্শনাবলী ফুটে ওঠে, মিসরের সম্রাট তাদ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হন। এতে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের মনে এরূপ প্রত্যয় জন্মে যে, তিনি তার কাছে সম্রাজ্যের নিরংকুশ ক্ষমতা চাইলেও তিনি তা তাঁর কাছে হস্তান্তর করতে রাজী হয়ে যেতে পারেন। ফলে এসময় হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের সামনে দুটো পথ উন্মুক্ত হয়। একটি হলো, ইসলামী বিপ্লবের লক্ষ্যে ব্যাপক দাওয়াত ও প্রচারাভিযান চালানো, কঠোর চেষ্টা সাধনা, সংগ্রাম, সংঘাত ও যুদ্ধের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যা সাধারণ অবস্থায় অবলম্বন করতে হয়। দ্বিতীয়টি হলো, আল্লাহর অসীম ক্ষমতার কল্যাণে যে সুবর্ণ সুযোগটি তাঁর মঠোর ভিতর এসে গেছে সেটাকে কাজে লাগানো এবং তাঁর গুণমুগ্ধ ও অনুরক্ত বাদশাহর কাছ থেকে যে সুদূর প্রসারী ক্ষমতা লাভের সম্ভবনা দেখা দিয়েছে, তা হস্তগত করে দেশের চিন্তায় এ বিশ্বাসে, চরিত্রে, সমাজ ব্যবস্থায় ও রাজনীতিতে পরিবর্তন আনয়নের চেষ্টা করা। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে যে প্রজ্ঞা দূরদর্শিতা দান করেছিলেন, তার আলোকে তিনি প্রথম পথটির চাইতে দ্বিতীয় পথটিকে অধিকতর সহায়ক ও নিজের লক্ষ্যের নিকটতর মনে করলেন এবং সেটাই গ্রহণ করলেন।
এটা তাঁর পক্ষে প্রতিষ্ঠিত অনৈসলামিক শাসন ব্যবস্থার অধীন নিছক জীবিকা উপার্জন, ব্যক্তিগত সম্মান ও মর্যাদা লাভ অথবা বাতিল ও দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্র ব্যবস্থার আংশিক সংশোধনের লক্ষ্যে গৃহীত একটি চাকরি ছিলোনা। বরঞ্চ এটা ছিলো একটা কৌশল। অন্যসকল নবীর মত হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম যে উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছিলেন, সেই একই উদ্দেশ্যে এ কৌশল অবলম্বন করা হয়েছিলো। যারা এটাকে নিছক একটা চাকরি মনে করেছেন এবং ধারণা করেছেন যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম ইসলামী জীবন ব্যবস্থা বাস্তাবায়নের উপায় হিসেবে নয় বরং খোদাদ্রোহী ব্যবস্থা যাথরীতি বহাল রাখা এবং তার ক্রীড়নক অর্থমন্ত্রী হিসেবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই চাকরিটা গ্রহণ করেছিলেন, তাদের দৃষ্টিতে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের মর্যাদা বর্তমান (ইংরেজ) সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারীদের চেয়ে উচ্চতর কিছুই নয়। এমনকি আমাদের এ দেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী সভাগুলোর যতোটুকু মর্যাদা, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের মর্যাদা তারা ততোটুকুও মনে করেনা। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ এদেশের সকল মানুষই প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের লক্ষ্য ছিলো ভারতের স্বাধীনতা। মন্ত্রীত্ব সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে, এব্যাপারে তাদের পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মা চিন্তাও করেনি। অতপর মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পর যখন তারা দেখেছে যে, আসল ক্ষমতা [Substance of power] তাদের কাছে হস্তান্তরিত হয়নি। তখন তারা মন্ত্রীত্বের মুখে লাথি মেরে বিদায় নিয়েছে।
বাদশাহর কাছ থেকে ক্ষমতা চেয়ে নেয়া হয়েছিলো না কেড়ে নেয়া হয়েছিলো নাকি হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ক্ষমতাসীন হওয়ার সংগে সংগেই বাদশাহকে গদিচ্যুত করা হয়েছিলো, না তিনি ক্ষমতায় বহাল ছিলেন, সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। প্রকৃত গুরুত্ববহ প্রশ্ন এখানে এই যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম অনৈসলামিক ব্যবস্থাটাকেই চালিয়ে যাওয়া এবং তার অধীনে চাকরি করার উদ্দেশ্যেই কি তার উমেদার হয়েছিলেন, নাকি নিজের নবূয়্যতের লক্ষ্য তথা ইসলামী বিধান কায়েমের জন্যই উদ্যোগী হয়েছিলেন? দ্বিতীয় যে প্রশ্ন গুরুত্বের অধিকারী তা হলো, দেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমূল ও সর্বাত্মক পরিবর্তন সূচিত করা যায় এমন ক্ষমতা তিনি যথার্থই পেয়েছিলেন কিনা? ইসলাম ও নবূয়্যত সম্পর্কে যে তত্ত্ব আমাদের মনে বদ্ধমূল, তার আলোকে আমি মনে করি, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম “দেশের উপায় উপকরণ আমার দায়িত্বে সমর্পণ করুন” কথাটা বলে আসলে দেশের সমস্ত উপায়- উপকরণকে তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বে সমর্পন করার দাবীই জানিয়েছিলেন। খান বাহাদুর সাহেব অনর্থক খাজায়েন শব্দটাকে ’অর্থ দফতর’ অর্থে গ্রহণ করেছেন। অথচ কুরআনের কোথাও এ শব্দটা অর্থ দফতর বা অর্থ বিষয়ক কর্যক্রম অর্থে ব্যবহৃত হয়নি।
কুরআনের নির্দেশাবলী অনসন্ধান করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, “উপায়-উপকরণ” বলতে যা বুঝায়, এ শব্দটার মর্মার্থ ঠিক তাই। [উদাহরণস্বরূপ নিম্নের আয়াত কয়টি লক্ষ্যণীয়”
“তোমার প্রভুর যাবতীয় উপকরণ কি ওদের কাছে?” [তুরঃ ৩৭]
“প্রতিটি জিনিসেরই উৎস আমার কাছে।” [সূরা হিজরঃ ২১]
“আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় উপায় উপকরণ একমাত্র আল্লাহর।” [মুনাফিকুনঃ ৭]
“দোজখবাসীরা জাহান্নামের কর্মকর্তাদেরকে বলবে…………….” [মুমিনঃ ৪৯]
এসব আয়াতে ‘খাজনা শব্দটি রেখাংকিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।] একটি দেশের যাবতীয় উপায় উপকরণ কারো হস্তগত হওয়া এবং সেই দেশের যাবতীয় বিষয়ে তার সর্বাত্মক এ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হওয়া একই অর্থবোধক। বাইবেল থেকেও এ কথার সমর্থন মেলে। সেখানে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় বলা হয়েছে, মিসরের ফিরাউন নামমাত্র রাজা ছিলো। কার্যত গোটা দেশ হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের কর্তৃত্বাধীন হয়ে গিয়েছিলো। [বাইবেলে হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের কাহিনী বর্ণনা প্রসংগে ফিরাউনের যে সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ
“ফিরাউন তার ভৃত্যদেরকে বললো!আল্লাহর আত্মধারী এই মহান ব্যক্তির মতো কোনো ব্যক্তি কি আমি খুঁজে পাবো? আর ফিরাউন ইউসূফকে বললো যেহেতু আল্লাহ তোমাকে এই সবই দিয়েছেন, তাই তোমার মত জ্ঞানবান ও বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। সুতরাং তুমি আমার বাড়ীর মালিক হবে এবং আমার সমস্ত প্রজা তোমার হুকুম মতো চলবে কেবল সিংহাসনের মালিক বলে আমি শ্রেষ্ঠতর হবো। অতপর সে তাকে সমগ্র মিসরের শাসক বানিয়ে দিলো। ফিরাউন ইউসূফকে আরো বললো আমি ফিরাউন। তবে তোমার হুকুম ছাড়া সমগ্র মিসরে কেউ হাত পা পর্যন্ত নাড়াতে পারবেনা।” [আবির্ভাব পুস্তক, অধ্যয় ৪১, আয়াত ৩৮-৪৪
উপরোক্ত রেখাচিহ্নিত কথাগুলো থেকে বুঝা যায় ফিরাউন হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভক্ত হয়ে গিয়েছিলো। সে যদি তাঁর নবূয়্যত স্বীকার নাও করে থাকে, তথাপি সে প্রথম সাক্ষাতেই ঈমান আনার কাছাকাছি চলে গিয়েছিলো। এর সাত আচ বছর পর যখন হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা মিসরে এলো, তখন হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম তাদেরকে বললেনঃ এখানে তোমরা নয়, আল্লাহই আমাকে পাঠিয়েছেন এবং তিনি আমাকে বলতে গেলে ফিরাউনের পিতা এবং তার পুরো বাড়ীর শাসক বানিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তোমরা তাড়াতাড়ি আমার পিতাকে গিয়ে বলো তোমার ছেলে ইউসুফ জানিয়েছে যে, আল্লাহ তাকে সমগ্র মিসরের মালিক বানিয়ে দিয়েছে।” [আবির্ভাব পুস্তক, অধ্যায় ৪৫, আয়াতঃ ৮-৯]]
এবার আর একটি দাবীর বিচার বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেটি হলো, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ক্ষমতা গ্রহণের পরও নাকি দেশে ফিরাউনের আইনেরই শাসন চালু থাকে।
“বাদশাহের দীনের ভিত্তিতে তার ভাইকে গ্রহণ করা সংযত ছিলোনা।” [সূরা ইউসূফঃ ৭৬]
এ আয়াতটি থেকেই নাকি এই ধারণা জন্মে। এ সম্পর্কে পয়লা কথা হলো, এ আয়াতের সচরাচর যে অনুবাদ করা হয় তা সঠিক নয়। অনবাদকরা এ আয়াতের এরূপ অর্থ করে থাকেন যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম রাজকীয় আইন অনুসারে তার ভাইকে গ্রেফতার করতে পারতেননা। অথচ এর বিশুদ্ধ অনুবাদ হলো, রাজকীয় আইন অনুসারে স্বীয় ভাইকে গ্রেফতার করাটা হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের পক্ষে শোভন বা সমিচীন ছিলোনা। কুরআনের অন্যান্য স্থানেও আরবী ভাষার এই বাকধারাটা অক্ষমতা ও অপারগতা অর্থে গ্রহণ করা হয়নি বরং অশোভন ও অনুচিত অর্থেই গৃহীত হয়েছে। যেমন সূরা আল ইমরানের ১৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ
এ বাক্যটার অর্থ এ নয় যে, আল্লাহ তোমাদেরকে অদৃশ্য বিষয়ে অবহিত করতে পারেননা, বরং এর তাৎপর্য হলো, তোমাদেরকে অদৃশ্য তথ্য ও তত্ত্ব জানানো আল্লাহর রীতি নয়। অনুরূপভাবে وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ [সূরা বাকারাঃ ১৪৩] فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ এবং مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ এসব আয়াতে আল্লাহর অক্ষমতা বা অপারগতার কথা বলা হয়নি, বরং যুলুম করা, ঈমান ব্যর্থ করে দেয়া এবং মুমিন ও মুনাফিকদেরকে বাছাই না করে একাকার রেখে দেয়া আল্লাহর রীতিবিরুদ্ধ, একথাই বলা হয়েছে। সূরা ইউসূফেরই আলোচ্য আয়াতের পূর্বের একটি আয়াতে বলা হয়েছে যে, مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ [আয়াতঃ ৩৮] এর অর্থও এটা নয় যে, আমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে অক্ষম। বরং এর অর্থ হলো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। সুতরাং আলোচ্য আয়াতেও এরূপ অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালাম রাজকীয় আইন অনুসারে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু সে আইনে তার ভাইকে গ্রেফতার করতে পারছিলেননা। কুরআনের অনুসৃত বাকরীতি অনুসারে এর প্রকৃত মর্মার্থ এটাই যে, রাজকীয় আইনে স্বীয় ভাইকে আটক করা তার পক্ষে শোভন ছিলোনা। অবশ্য এ আয়াত দ্বারা নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ক্ষমতাসীন হওয়া সত্ত্বেও অনৈসলামিক ফৌজদারী বিধি অন্তত সাত আট বছর [হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ভাইরা যখন সেখানে আসে] পর্যন্ত মিসরে কার্যকর ছিলো। তবে এ সম্পর্কে আমি ইহিপূর্বে বলেছি যে, একটি দেশের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দেয়া সম্ভব নয়। ক্ষমতা হাতে আসা মাত্রই জাহেলী যুগের সমস্ত রীতিপ্রথাকে তাৎক্ষনিকভাবে পাল্টে ফেলতে হবে ইসলামী বিপ্লবের এ ধারণা ঠিক নয়। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলেও দেশের সমাজ ব্যবস্থাকে আমূল বদলে দিতে পুরো দশ বছর সময় লেগেছিলো। সুতরাং হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের শাসনামলে কয়েক বছর অবধি অনৈসালামিক ফৌজদারী বিধি এবং সেই সাথে আরো কিছু অনৈসলামিক আইন যদি চালু থেকেও থাকে, তবে সেজন্য এ সিদ্ধান্ত আসা সঙ্গত নয় যে, ইসলামী আইন চালু করার ইচ্ছাই হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের ছিলোনা এবং তিনি অনৈসলামিক বিধি ব্যবস্থাই বহাল রাখতে চেয়েছিলেন।
হাবশার হিজরত থেকে ভ্রন্ত যুক্তিগ্রহণ
এবার আসুন আলোচনার সমাপ্তি টানার আগে আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয়টার ওপরও একবার নজর বুলিয়ে নেয়া যাক।
এ ব্যাপারটাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়ে থাকে তা হলো, আবিসিনিয়ায় একটি অমুসলিম সরকার প্রতিষ্ঠিত ছিলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের একটি দলকে সেখানে ঐ সরকারের প্রজা হিসেবে বসবাস করার জন্য পাঠান। অতপর সাহাবায়ে কিরাম সেথানে গিয়ে অমুসলিম শাসকের অনুগত হয়ে গেলেন। কেননা তারা সেখানে নিজস্ব আকীদা বিশ্বাস পোষণ ও ইবাদত উপসনা করার স্বাধীনতা ভোগ করতেন। অতপর যখন এ প্রতিবেশী রাজা তার রাজ্যের ওপর আক্রমণ চালায় তখন তারা তার সাফল্যের জন্য দোয়া করেন। কিন্তু এটা ঘটনার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বিবরণ।
১. প্রথমত, মুসলমানদের একটা দলকে আবিসিনিয়ায় পাঠানোর সময়ই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধারণা ছিলো, নাজ্জাশী একজন সত্য নিষ্ঠ ও ন্যায়পরায়ণ খৃষ্টান। হাদীসের ভাষা এরূপ, তিনি হিজরতকারীদেরকে নাজ্জাশীর রাজ্য সম্পর্কে বলেছিলেন যে, وَهِيَ اَرْضَ صِدْقِ “ওটা সত্যের দেশ।”
২. দ্বিতীয়ত, মোহাজেরদেরকে সেখানে স্থায়ী প্রজা হয়ে বসবাস করা জন্য পাঠনো হয়নি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোহাজেরগণকে হিজরতের পরামর্শ দেয়ার সময় বলেছিলেনঃ
“আল্লাহ তা’য়ালা তোমাদের জন্য একটা উপায় বের না করা পর্যন্ত তোমরা যদি আবিসিনিয়ায় চলে যেতে………..।”
একথা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায়, কাফিরদের সাথে সংঘাতের ঐ স্তরে যেসব মুসলমান অসহনীয় বিপদ মুসিবতের শিকার হচ্ছিলেন, তাদেরকে তিনি সাময়িকভাবে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ বলে মনে হয় এমন একটি জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। পরে যখন পরিস্থিতি অনুকূল হবে, তখন তারা আবার ফিরে আসবেন এটাই ছিলো উদ্দেশ্য। এ ঘটনাকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করে এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিভাবে সঠিক হতে পারে যে, কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে আকীদা ও ইবাদতের স্বাধীনতা পাওয়া গেলে সেটাই ঐ রাষ্ট্রের অনুগত প্রজা হয়ে চিরস্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য যথেষ্ট হবে এবং এর চেয়ে বেশী কিছুর প্রয়োজন হবেনা?
৩. এরপর যখন মুসলমানরা সেখানে পৌছলো এবং মক্কার কাফিররা নাজ্জাশীর কাছ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য একটা প্রতিনিধিদল পাঠালো, তখন হাদীসবেত্তাগণ ও সীরাত বিশারদগণের সর্বসম্মত মত অনসারে হযরত জাফর ও নাজ্জাশীর কথোপকথনের পর নাজ্জাশী হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআন বর্ণিত তত্ত্বকে সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়্যতকেও সত্য বলে স্বীকৃতি দেন। এরপর নাজ্জাশীর মুসলমান হওয়ার ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে? ইমাম আহমদ এই ঘটনার চাক্ষস সাক্ষী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের বরাত দিয়ে নাজ্জাশীর নিন্মরূপ উক্তি করেছেনঃ
“তোমাদেরকে মুবারকবাদ এবং তোমরা যার কাছ থেকে এসেছো তাকেও মাবুরকবাদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রসূল, তিনি সেই ব্যক্তি যার বর্ণনা আমরা ইনজিলে পাই, তিনি সেই রসূল, যার সম্পর্কে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।”
এ উক্তি কি কোনো অমুসলিমের হতে পারে? বায়হাকীতে স্বায়ং আমল ইবনুল আস থেকে [যিনি মোহাজেরদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য মক্কার কাফিরদের তরফ থেকে আবিসিনিয়ায় প্রেরিত হয়েছিলেন] বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ফিরে এসে মক্কাবাসীকে বলেনঃ
“আসহাবা [নাজ্জাশী] বলে যে, তোমাদের সঙ্গী [মুহাম্মদ] নবী।”
প্রশ্ন হলো, কোনো মানুষ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবূয়্যত স্বীকার করে নেয়ার পরও কি অমুসলিম বিবেচিত হতে পারে?
সীরাতে ইবনে হিশাম হযরত আমর ইবনুল আসের ইসলাম গ্রহণের যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে তা থেকে বুঝা যায়, প্রথম প্রথম নাজ্জাশীর প্রচারের ফলেই তার মনে ঈমানের জন্ম হয়। হোদাইবিয়ার সন্ধির আগে তিনি নাজ্জাশীর হাতে হাত দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এই সময় নাজ্জাশী আমর ইবনুল আসকে যে কথাগুলো বলেন তা হলোঃ
“আমার কথা শোনো এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়ে যাও।
কেননা নিশ্চিতভাবেই তিনি সত্যের ওপর রয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালাম যেভাবে ফিরাউন ও তার বাহিনীর ওপর বিজয়ী হয়েছিলেন, সেইভাবে তিনিও তার বিরোধীদের ওপর অবশ্যই বিজয়ী হবেন।”
আল্লামা ইবনে আব্দুল বার স্বীয় গন্থ আল ইসতিয়াবে হযরত উম্মে হাবীবার সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়েবানা বিয়ে পড়ানোর সময় নাজ্জাশী যে খুৎবা দেন, তা উদ্ধৃত করেছেন। এই খুৎবায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নাজ্জাশী বলেনঃ
“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, যার আগমন সম্পর্কে মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম সংবাদ দিয়েছিলেন।”
এর চেয়েও একাট্য ও বিশ্বস্ত বর্ণনা বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃতি হয়েছে যে, নাজ্জাশীর মৃত্যুর খবর শুনে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গায়েবানা জানাযা নামায পড়েন এবং বলেনঃ
“আজ একজন পূণ্যবান মানুষ মারা গেছে। তোমরা প্রস্তুত হও এবং তোমাদের ভাই আসহামার জানাযার নাময পড়।”
এ রেওয়ায়েতের পর আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনার সূত্র ধরে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয়, তার ভিত্তিই চুরমার হয়ে যায়।
[তরজমানুল কুরআন, মুহাররম-সফর, ১৩৬৪ হিঃ জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫]
দ্বিতীয় অধ্যায়
ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ
১। ইসলামী রাজনীতির উৎস
২। রাজনীতির গোড়ার কথা
৩। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন
৪। খিলাফত ও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য
হিমালয়ান উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক জাগরণ সাথে করে নিয়ে আসে অনেক প্রশ্ন ও জটিলতা। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ছিলো ভবিষ্যতে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা কেমন হবে? প্রতিটি মুসলমানদের উদগ্র আন্তরিক আকংখা এই ছিলো এবং আছে যে, তার সামাজিক ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের সবচাইতে বড় দুর্ভাগ্য হলো, তারা ইসলামকে ভালোবাসে বটে, কিন্তু ইসলামের সঠিক ধারণা তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এর কারণেই তারা ইসলামের জন্যে জান দিতে তৈরী থেকেও ইসলামের ভিত্তিতে বেঁচে থাকতে জানেনা।
মুসলমানদের এই মানসিক অবস্থা অনুধাবন করেই মাওলানা মওদুদী [র] ইসলামী জীবনব্যবস্থার মৌলিক বিষয়গুলোকে উপযোগী ব্যাখ্যার সাথে উপস্থাপন করেছেন। এ প্রসংগে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি লাহোর ইন্টার কলেজিয়েট মুসলিম ব্রাদার হুড- এর সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এ সময় পর্যন্ত মুসলমানরা নিজেদের কোনো সুস্পষ্ট জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারেনি। মাওলানা তাঁর এই প্রবন্ধে মুসলিম উম্মাহকে জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি কি? কি কি উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার বুনিয়াদী আদর্শই বা কি কি?
সামনের পৃষ্ঠাগুলোতে প্রবন্ধটির পুনরীক্ষণ করার পর উপস্থাপন করা হলো। পুনরালাচনা থেকে বাঁচার জন্যে প্রবন্ধটির সে অংশ এখানে থেকে বাদ দেয়া হলো যাতে নির্বাহী বিষয়ের আলোচনা ছিলো। কারণ সম্মুখের অধ্যায়গুলোতে সম্মানিত গ্রন্থাকারের আরো যেসব লেখা সংকলিত হয়েছে, সেসব অধ্যায়ে সে আলোচনা সবিস্তারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। -সংকলক
ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ
ইসলাম সম্পর্কে আপনারা প্রায়ই শুনে থাকেন, “ইসলাম একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা” “ইসলাম একনায়কতন্ত্রের সমর্থক”, “ইসলাম সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী”, ইত্যাদি ইত্যাদি। বিগত শতাব্দীর শেষভাগ থেকে এধরনের কথা বার বার উচ্চারণ করা হচ্ছে। কিন্তু কথাগুলো যাদের মুখ থেকে বের হচ্ছে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস তাদের মধ্যে হাজারে একজনও এমন নেই, যিনি ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে যথাযথ অধ্যয়ন করেছেন এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। তারা একথাও বুঝার চেষ্টা করেননি যে, ইসলামে গণতন্ত্রের ধরন ও মর্যাদা কি, কিংবা সামাজিক সুবিচার ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্যে সে কি মূলনীতি পেশ করেছে? তাদের কেউ কেউতো ইসলামের সাংগঠনিক কাঠামোর দু’চারটি বাহ্যিক রূপ দেখে ইসলামের উপর গণতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্রের নামাংকিত করে দিয়েছেন। আর তাদের অধিকাংশের মানসিক অবস্থা হলো, পৃথিবীতে [বিশেষ করে নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের জগতে অধিষ্ঠিত শক্তিসমূহ এবং নিজ নিজ দেশের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত লোকদের মধ্যে] যে জিনিস সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে, সেটাকে কোনো না কোনো ভাবে ইসলামের মধ্যে বর্তমান আছে বলে প্রমাণ করে দেয়াই তাদের দৃষ্টিতে এই ধর্মটির সবচাইতে বড় খেদমত। সম্ভবত তারা ইসলামকে ঐ এতীম শিশুটির মতো মনে করে, যে কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেই ব্যস ধ্বংস থেকে রক্ষা পেতে পারে। অথবা সম্ভবত তাদের ধারণা হলো, কেবল মুসলমান হিসেবে আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা, বরঞ্চ আমাদের নীতির মধ্যে বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত কোনো অস্তিত্ব দেখাতে পারলেই আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এই মানুসিকতার পরিণতি হলো, বিশ্বে যখন সমাজতন্ত্রের ধুম পড়ে গেলো, তখন মুসলমানদের মধ্যেই কিছু লোক চিৎকার করে উঠলো, সমাজতন্ত্রতো কেবল ইসলামেরই একটি নতুন সংস্করণ। আবার যখন একনায়কতন্ত্রের শাসন শুরু হলো, তখন আবার অন্য কিছু লোক এখানে আমীরের আনুগত্যের নমুনা দেখতে পেলো এবং বলতে শুরু করলো, ইসলামের গোটা সাংগঠনিক ব্যবস্থাই একনায়কতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।
মোটকথা, আজকে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ একটি প্রহেলিকা ও ধুম্রজালে পরিণতি হয়ে আছে। এখান থেকে এমন সব জিনিসই বের করে দেখানো হয়, যার বাজার গরম। বাস্তবিকপক্ষে ইসলামের রাজনৈতিক মতাদর্শ কি, তার যথাযথ বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণ হওয়া প্রয়োজন। এর ফলে চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা এসব ভ্রান্ত ধারণাই কেবল দূর হবেনা, কেবল ঐসব লোকের মুখই বন্ধ হবেনা যারা ইদানিং প্রকাশ্যে লিখিতভাবে নিজেদের ও অজ্ঞাতার ঘোষণা দিয়েছে যে, “ইসলাম আদতেই কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রস্তাব করেনা।” বরঞ্চ অন্ধকারে হাবুডুবু খাওয়া বিশ্বের সামনে এমন এক আলোর প্রদীপ উদ্ভাসিত হবে, বিশ্ব আজ যার বড় মুখাপেক্ষী। অবশ্য এই মুখাপেক্ষীতার চেতনাই সে আজ হারিয়ে বসেছে।
১. ইসলামী রাজনীতির উৎস
সর্বপ্রথম একথাটি ভালোভাবে বুঝে নিন যে, ইসলাম কেবল গুটিকয়েক বিক্ষিপ্ত বিশ্বাস এবং কর্মপন্থার সমষ্টিই নয়, যাতে এদিক ওদিক থেকে বিভিন্ন ধরনের মতের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বস্তুত, ইসলাম একটি সুসংবদ্ধ ও সুষ্ঠু জীবন ব্যবস্থা। এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে কতিপয় আদর্শ ও মূলনীতির উপর। এর বড় বড় স্তম্ভ হতে শুরু করে একেবারে আনুষংগিক বিষয়াদি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের সাথে এর আদর্শ ও মূলনীতির এক যুক্তিসংগত সম্পর্ক রয়েছে। ইসলাম মানব জীবনের সকল বিভাগ ও বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যতো নিয়ম কানুন ও বিধি বিধান পেশ করেছে, তার সবগুলোরই আভ্যন্তরীণ প্রাণসত্তা ও বাহ্যিক রূপকাঠামো এর সেই প্রাথমিক মূলনীতিও আদর্শ থেকেই গৃহীত হয়েছে। এই আদর্শ ও মূলনীতি থেকে যাবতীয় আনুষংগিক বিষয়াদিসহ একটি পূর্ণাংগ ইসলামী জীবন ব্যবস্থা ঠিক সেভাবে গঠিত হতে পারে, যেভাবে একটি গাছের ক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পান বীজ থেকে শিকড়, শিকড় থেকে কান্ড, কান্ড থেকে শাখা এবং শাখা থেকে প্রশাখা ও পত্র পল্লব ফুটে বের হয়। গাছটি ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হয়ে পড়লেও তার দূরবর্তী পাতাটি পর্যন্ত মূল শিকড়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে। সুতরাং ইসলামী জীবন ব্যবস্থার যেকোনো দিক ও বিভাগকে বুঝার জন্যে এর মূলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা অপরিহার্য। কেননা এছাড়া এর প্রাণসত্তা এবং মূল ভাবাধারা কিছুতেই হৃদয়ংগম করা যেতে পারেনা।
নবীদের মিশন
ইসলাম সম্পর্কে দুটি কথা প্রায় সকল মুসলমানেরই জানা আছে। একটি হলো, সব নবীর মিশনই ছিলো ইসলাম। এটা কেবল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের মিশনই নয়। বরঞ্চ মানব ইতিহাসের প্রাচীনতম অধ্যায় হতে আল্লাহর পক্ষ থেকে যতো নবীই এসেছেন , তাদেঁর সকলের এই একই মিশন ছিলো। দ্বিতীয় কথাটি হলো, সকল নবীই মানুষকে এক আল্লাহর কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করানো এবং একমাত্র তাঁরই আনুগত্য করানোর উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।
মুসলমান মাত্রই এ দুটি সত্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অতিসাধারণ ব্যাপার। প্রত্যেক মুসলমান একথা শুনেই বলবে, এটাতো জানা কথা, একজন গ্রাম্য মুসলমানও এটা জানে। কিন্তু আমি চাই এ সংক্ষিপ্ত কথাটির আবরণ উন্মুক্ত করে আপনারা এর গভীর প্রবেশ করুন। আসল ব্যাপার এই আবরণের অন্তরালে চাপা পড়ে আছে। অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ভালোভাবে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহর প্রভুত্ব স্বীকার করানোর উদ্দেশ্য কি? একমাত্র তাঁরই আনগত্য দাসত্ব করানোর অর্থ কি? আর এতে এমন কি কথাটি ছিলো যে, যখন আল্লাহর এক বান্দা [নবী] “আল্লাহ ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো ইলাহ নেই” বলে ঘোষণা করলেন, তখন সকল আল্লাহদ্রোহী শক্তি তাঁকে জংগলের বিষাক্ত কাঁটার মতো বিদ্ধ করতে শুরু করে দিলো? বিষয়টা কেবলমাত্র যদি এরকমই হতো, যেমন আজকাল মনে করা হয় যে, মসজিদে গিয়ে আল্লাহর সামনে সিজদা করো আর মসজিদের বাহিরে এসে ক্ষমতাসীন সরকারের [ক্ষমতায় যে-ই অধিষ্ঠিত থাকনা কেনো] শর্তহীন আনুগত্য ও অনুবর্তনে লেগে যাও, তবে এমন কোন সরকার আছে যে তার এধরনের অনুগত ও বাধ্যগত প্রজাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে?
আসুন, আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি, আল্লাহ সম্পর্কে আম্বিয়ায়ে কিরাম ও বিশ্বের অন্যান্য শক্তিগুলোর মধ্যে আসলে কোন কথাটির ব্যাপারে বিরোধ ও বিবাদ হয়েছিলো?
কুরআন মজীদ একাধিক স্থানে বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে, যেসকল কাফিরও মুশরিকদের সাথে নবীদের সংঘাত সংঘর্ষ হয়, মূলত তাদের কেউই আল্লাহর সত্তার অস্বীকারকারী ছিলোনা। তাদের সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তারা স্বীকার করতো এবং বিশ্বাস করতো, আল্লাহই আসমান যমীনের স্রষ্টা এবং স্বয়ং সেই কাফির মুশরিকদেরও স্রষ্টা। বিশ্ব জগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তাঁরই ইংগিতে পরিচালিত হয়। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তাঁর হুকুম অনুযায়ী বায়ু গতিশীল। চন্দ্র, সূর্য এবং পৃথিবী সবকিছুই তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীনঃ
“তাদের জিজ্ঞেস করো, পৃথিবী এবং এতে যাকিছু আছে তা কার, বলো, যদি তোমাদের জানা থাকে? তারা অবশ্যি বলবেঃ আল্লাহর। বলো, তবে কেন তোমরা ভেবে দেখনা? তাদের জিজ্ঞেস করো, সাত আসমান ও মহান আরশের মালিক কে? তারা বলবেঃ আল্লাহ। তুমি বলো, তাহলে তোমরা তাঁকে ভয় করনা কেন? তাদের জিজ্ঞেস করো, প্রতিটি জিনিসের কর্তৃত্ব কার হাতে, যিনি সকলকে আশ্রয় দান করেন, যাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কাউকেও আশ্রয় দান করতে পারেনা, তিনি কে, বলো, যদি তোমরা জেনে থাকো! তারা বলবেঃ আল্লাহ। তুমি বলো, তাহলে তোমরা কোন প্রতারণায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো?” [সূরা মুমিনঃ ৮৪]
“আকাশ ও পৃথিবীকে কে সৃষ্টি করেছে? এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মানুগত করেছে, তা তাদের জিজ্ঞেস করলে তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ। কিন্তু তবুও এরা বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলে যাচ্ছে?” [সূরা আনকাবুতঃ ৬১]
“তাদের যদি জিজ্ঞেস করো, আকাশ হতে কে পানি বর্ষণ করে আর তা দিয়ে মৃত যমীনকে জীবন দান করে কে? তাবে তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ। [সূরা আনকাবুতঃ ৬৩]
“তাদের যদি জিজ্ঞেস করো, তোমাদের কে সৃষ্টি করেছে? তবে তারা নিশ্চয়ই বলবেঃ আল্লাহ তা সত্ত্বেও তারা বিভ্রান্ত হয়ে কোথা চলে যাচ্ছে?” [সূরা যুখরুফঃ ৮৭]
অতএব এ আয়াতগুলো থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে এবং তাঁর সৃষ্টিকর্তা, আকাশ ও পৃথিবীর একচ্ছত্র মালিক ও প্রভূ হওয়ার ব্যাপারে মানব সমাজে কোনো কালেই কোনো মতভেদ ছিলোনা। জনগণ চিরদিনই এসব কথা স্বাভাবিকভাবেই স্বীকার করতো। কাজেই এসব কথার পুনঃ প্রচার এবং জনগণের দ্বারা তা স্বীকার করানোর জন্য নবী পাঠাবার কোনো প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে ছিলোনা। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, দুনিয়ায় নবীদের আগমণের উদ্দেশ্য কি ছিলো? আর প্রতিপক্ষের সাথে তাদের বিরোধ বিবাদই বা ছিলো কী বিষয়ে?
কুরআন মজীদ এর সুস্পষ্ট জবাব দিয়েছে। কুরআন বলে, সমস্ত বিরোধ বিবাদের মূল কারণই ছিলো নবীদের এই বক্তব্যঃ “যিনি তোমাদের এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, বস্তুত তোমাদের রব এবং ইলাহও একমাত্র তিনিই। অতএব তাঁকে ছাড়া আর কাউকেও রব এবং ইলাহ বলে স্বীকার করোনা। কিন্তু মানুষ নবীদের এই বক্তব্য মেনে নিতে মোটেও প্রস্তুত ছিলোনা।
আসুন একটু অনুসন্ধান করে দেখি কেন তারা নবীদের সাথে বিরোধ করলো? ‘একমাত্র ইলাহ’ বলতে কি বুঝায়? রব কাকে বলে? আল্লাহকেই রব ও ইলাহ, স্বীকার করো একথার উপর নবীরা কেন এতোটা অটলতা অবলম্বন করেছিলেন? আর প্রতিপক্ষই বা কেন একথার বিরোদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলো?
’ইলাহ’ ও ‘রবে’র অর্থ কি?
ইলাহ শব্দের অর্থ মা’বুদ বা উপাস্য, একথা সবাই জানে। পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন, মা’বুদ এর অর্থ মুসলমানরা ভুলে গেছে। মা’বুদ শব্দটা আবদ’ ধাতু থেকে এসেছে। আবদ অর্থ হলো বান্দা, গোলাম বা দাস। ইবাদাতের অর্থ নিছক পূজা নয়। একজন বান্দা, গোলাম বা দাস যে জীবন দাসত্ব ও গোলামীর অবস্থায় অতিবাহিত করে, তার পুরোটাই আগাগোড়া ইবাদত। খিদমত বা সেবার জন্য দাঁড়ানো, ভক্তিভরে বুকে হাত বাঁধা, দাসত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ মাথা নোয়ানো, আনুগত্যের মনোভাব ও জজবায় সর্বক্ষণ উজ্জীবিত থাকা, হুকুম পালনের জন্য চেষ্টাসাধনা ও ছুটোছুটি করা, যে কাজ সম্পাদনের ইংগিত দেয়া হয় তা সম্পন্ন করা, মনিব যা চান তা প্রদান করা, তার শক্তি ও প্রতাপের সামনে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা, তার প্রবর্তিত আইনের আনুগত্য করা, যার বিরুদ্ধে তিনি নির্দেশ দেন তার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা, যে ব্যাপারে তার নির্দেশ থাকবে তার জন্য প্রয়োজনে জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়া এসব হলো ইবাদাতের আসল অর্থ ও মর্ম। মানুষ এভাবে যার ইবাদত করে, তিনিই তার প্রকৃত মা’বুদ।
আর রব অর্থ কি? আরবী ভাষায় রবের মূল অর্থ হচ্ছে লালনপালনকারী। যেহেতু দুনিয়ার রীতি হলো, যে লালনপালন করে, তারই আনুগত্য ও ফরমাঁবরদারী করা হয়। তাই রবের আরেকটি অর্থ দাঁড়ালো মালিক ও মনিব। একারণেই আরবীতে সম্পদের মালিককে রব্বুল মাল’ [সম্পদের মালিক] এবং বাড়ীর মালিককে রব্বুল দার’ বলা হয়ে থাকে। মানুষ যাকে নিজের রিযিকদাতা ও লালনপালনকারী বলে জানে, যার কাছ থেকে অনুগহ ও উন্নতির আশা করে, যার কাছ থেকে সম্মান, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার প্রত্যাশী হয়, যার দর্য়াদ্র সৃষ্টি না পেলে নিজের জীবন বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশংকা করে, যাকে নিজের মালিক ও মনিব বলে স্বীকার করে এবং কার্যত যার আনুগত্য করে, সে-ই তার রব। [উক্ত পরিভাষা দুটির বিশদ ব্যাখ্যার জন্য গ্রন্থকারের ‘কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা’ গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য।]
এই দুটো শব্দের অর্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে একটু গভীরভাবে ভেবে দেখুনতো, মানুষের সামনে, আমি তোমার ইলাহ, আমি তোমার রব, এবং আমার ইবাদত ও দাসত্ব করো এই দাবী নিয়ে কে দাড়াতে পারে? গাছ কি পারে এমন দাবী করতে? পাথর কি এমন দাবী করার যোগ্যতা রাখে? সমুদ্র কি এরূপ দাবী করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? এমন ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে কি কোনো জীব জানোয়ার, চাঁদ, সূর্য বা নক্ষত্র? মানুষের সামনে এসে এই দাবী করার স্পর্ধা কি কারো আছে? না, কক্ষনো নয়। মানুষের ওপর খোদায়ী দাবী করা কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব এবং মানুষই এ অপকর্মটি করে থাকে। প্রভুত্ব করার সখ ও সাধ একমাত্র মানুষের মাথায়ই জন্মে, অন্য কারো নয়। সীমাতিরিক্ত ক্ষমতার লালসা ও মাত্রাতিরিক্ত ভোগের স্পৃহা মানুষকে প্ররোচিত করে অন্য মানুষদের প্রভু হতে তাদেরকে নিজের দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করতে তাদেরকে নিজের সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে, তাদের ওপর নিজের হুকুম জারী করা, এবং তাদেরকে নিজের প্রবৃত্তির লালসা চরিতার্থ করার হাতিয়ারে পরিণত করতে। মানুষের প্রভু বা খোদা হওয়া এতো মজাদার জিনিস যে, মানুষ আজ পর্যন্ত এর চেয়ে মজাদার কোনো জিনিসের সন্ধান পায়নি। যার যতটুকু শক্তিসামর্থ, ধনসম্পদ, চালাকী চাতুরী, বিচক্ষনতা ও প্রজ্ঞা অথবা অন্য কোনো ধরনের কোনো ক্ষমতা থাকনা কেন, সে এটাই কামনা করে যে, তাকে যেভাবেই হোক নিজের বৈধ ও স্বভাবসিদ্ধ সীমানা অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে যেতে হবে, চারদিকে নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং নিজের খোদায়ীর দাপট ও প্রতাপ ছড়িয়ে দিতে হবে।
এ ধরনের প্রভুত্ব অভিলাষী মানুষ দু ধরনের হয়ে থাকে এবং দুটো ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করে থাকে।
১. সরাসরি দাবীদার
এক ধরনের মানুষ অপেক্ষাকৃত সাহসী হয়ে থাকে, অথবা তাদের কাছে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রচুর উপকরণ বিদ্যমান থাকে। তারা সরাসরি নিজেদের খোদায়ী বা প্রভুত্বের দাবী তুলে থাকে। এর একটি দৃষ্টান্ত হলো ফেরাউন। নিজের রাজকীয় ক্ষমতা ও সৈন্য সামন্তের ওপর নির্ভর করে সে মিসরের অধিবাসীদেরকে বলেছিলোঃ “আমি তোমাদের সর্বোচ্চ প্রভু” [সূরা আননাযিয়াতঃ ২৪]। সে আরো বললোঃ “আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ আছে বলেতো আমার জানা নেই।” [সূরা কাসাসঃ ৩৮]। যখন হযরত মুসা আলাইহিস সালাম তার সামনে আপন জাতির স্বাধীনতার দাবী পেশ করলেন এবং তাকে বললেন, তুমি নিজেও বিশ্বপ্রভুর দাসত্ব মেনে নাও, তখন সে বললো, আমি তোমাকে জেলে পাঠাতে পারি, কাজেই তুমি আমাকে খোদা মনে নাও। “তুমি যদি আমাকে ছাড়া আর কাউকে খোদা মানো তাহলে আমি তোমাকে বন্দী করবো” [সূরা আশশুয়ারাঃ ২৯]। অনুরূপ আর একটি দৃষ্টান্ত হলো হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাথে যার বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেই রাজা। কুরআনে যে ভাষায় এটি উল্লেখ করা হয়েছে তা লক্ষ্য করুনঃ
“তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহীমের সাথে ইবরাহীমের প্রভু কে, তাই নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিলো? এ বিতর্কে সে লিপ্ত হয়েছিলো এজন্য যে, আল্লাহ তাকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেছিলেন। ইবরাহীম যখন বললো, জীবন ও মৃত্যু যার হাতে ন্যস্ত, তিনিই আমার প্রভূ। তখন সে বললোঃ জীবন ও মৃত্যুতো আমার হাতে। ইবরাহীম বললোঃ বেশ, আল্লাহতো সূর্যকে পূর্বদিক থেকে উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিক থেকে ওটা উদিত করোতো দেখি! একথা শুনে সেই কাফের হতচকিত হয়ে গলো।” [সূরা আল-বাকারাঃ ২৫৮]
ভেবে দেখুনতো, এই কাফের কি কারণে হতচকিত হয়ে গেলো? কারণ সে আল্লহর অস্তিত্ব অস্বীকার করতোনা। আল্লাহই যে, সমগ্র বিশ্বনিখিলের একমাত্র অধিপতি ও শাসক তিনিই যে সূর্যকে উদিত ও অস্তমিত করেন তাও সে জানতো। বিশ্বনিখিলের মালিক ও মনিব কে? সেটা বিতর্কের বিষয় ছিলোনা। বিতর্কের বিষয় এই ছিলো যে, মানুষের বিশেষত ইরাকের অধিবাসীদের মনিব ও প্রভুকে। সে আল্লাহ হবার দাবী করতোনা, তার দাবী ছিলো শুধু এইযে, ইরাক সম্রাজ্যের অধিবাসীদের প্রভু ও মালিক মোক্তার আমি। আর এ দাবী সে এজন্য করতে যেহেতু শাসন ক্ষমতা তার হাতেই ছিলো। দেশবাসীর প্রাণ ছিলো তার হাতের মুঠোয়। সে যাকে ইচ্ছা ফাঁসিতে ঝুলাতে এবং যাকে খুশী ফাসি থেকে অব্যাহতি দিতে পারতো। সে মনে করতো, তার মুখ থেকে যেকথা বেরোয় সেটাই আইনের মর্যাদা রাখে এবং সকল প্রজার ওপর তার শাসন চলে। তাই হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সে আদেশ দিয়েছিলো, তুমি আমাকে প্রতিপালক মেনে নাও এবং আমার ইবাদত ও দাসত্ব করো। কিন্তু হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন বললেন, যিনি পৃথিবী ও আকাশের প্রভু এবং এই সূর্যও যার আনুগত্য করে, আমি শুধু তাঁকেই প্রভু ও প্রতিপালক মানবো এবং তাঁরই ইবাদত ও দাসত্ব করবো। তখন সে হতভম্ব হয়ে গেলো এবং শুধু এই ভেবে হতভম্ব হলো যে, এ ধরনের লোককে আমি কিভাবে বশীভূত করি। [বিষয়টির আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য গ্রন্থকারের “কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা” দেখুন।]
খোদায়ীর এই যে দাবী নমরুদ এবং ফেরাউন করেছিলো তা শুধু তাদের দুজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলোনা, দুনিয়ার সকল জায়গায় সকল শাসকের দাবী এটাই ছিলো এবং এটাই আছে। ইরান সম্রাটের জন্য খোদা খোদাওয়ান্দ শব্দটি ব্যবহৃত হতো। আর তার সামনে বন্দনার যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হতো। অথচ কোনো ইরানী তাকে সকল খোদার বড় খোদা তথা আল্লাহ মনে করতোনা। এমনকি স্বয়ং রাজারাও সে দাবী করতোনা। এমনিভাবে ভারতেও শাসকরা নিজেদেরকে দেবতাদের বংশধর বলে দাবী করতো। এজন্য সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ইত্যাকার বংশীয় খেতাব এখনো প্রসিদ্ধ। রাজাকে অন্নদাতা বলা হতো এবং তাঁর সামনে সিজদা করা হতো। অথচ কোনো রাজা যেমন নিজেকে পরমেশ্বর বা পরমাত্মা বলে দাবী করতোনা, তেমনি প্রজারাও তেমনটি ভাবতোনা। দুনিয়ার অন্যান্য দেশের অবস্থাও ছিলো তখন তথৈবচ এবং এখনো আছে। কোথাও কোথাও শাসকের জন্য ইলাহ ও রবের সমার্থক শব্দ এখনো খোলাখুলিভাবে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু যেখানে যেখানে এসব শব্দ প্রয়োগ করা হয়না, সেখানেও এসব শব্দের অর্থের ভেতর যে প্রেরণা ও ভাবধারা সুপ্ত রয়েছে সেটাই কার্যত বিরাজমান। এধরনের খোদায়ী দাবী করার জন্য স্পষ্ট ভাষায় ইলাহ বা রব হবার কথাই ঘোষণা করতে হবে এটা জরুরী নয়। নমরুদ ও ফেরাউন মানুষের ওপর যে নিরংকুশ ও সার্বভৌম ক্ষমতা, যে স্বৈরাচারী শাসন এবং যে প্রভুত্ব ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলো, অবিকল সেই জিনিস যারাই প্রতিষ্ঠা করবে, তারা আসলে ইলাহ’ ও রব’ দ্বারা যা বুঝায় তারই দাবী জানায়, চাই মুখে ইলাহ এবং রব শব্দ উচ্চারণ করুক বা না করুক। আর যারা তাদের আনুগত্য ও দাসত্ব করে তারা মুখ দিয়ে যাই বলুক না কেন আসলে তারা তাদেরকে ইলাহ ও রব বলেই মেনে নেয়।
২. পরোক্ষ দাবীদার
সারকথা হলো, এক ধরনের মানুষ সরাসরি ও প্রত্যক্ষভাবে নিজের খোদায়ী ও প্রভুত্বের দাবী করে থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় আর এক প্রকারের মানুষ আছে, যাদের কাছে এতো শক্তিও থাকেনা, উপায় উপকরণও থাকেনা যে, নিজেই এধররেন দাবী নিয়ে ময়দানে নামবে এবং জনগণকে তা মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে ফেলবে। তবে তাদের কাছে চাতুর্যও ধড়িবাজীর অস্ত্র থাকে এবং তা দিয়ে তারা সাধারণ মানুষের মনমগজে যাদু করতে সক্ষম হয়। এসমস্ত উপায় উপকরণ প্রয়োগ করে তারা কোনো আত্মা, দেবতা, প্রতিমা, কবর, নক্ষত্র, অথবা কোনো গাছকে খোদা বানিয়ে দেয়। তারপর তারা জনগণকে বলে, এরা তোমাদের ক্ষতি ও উপকার করতে সক্ষম, তোমাদের মনস্কামনা পূরণ করতে সক্ষম এবং এরা তোমাদের অভিভাবক, রক্ষক ও সাহায্যকারী। এদেরকে যদি সন্তুষ্ট না করো তাহলে এরা তোমাদের রোগ, মহামারি, দুর্ভিক্ষ ও নানা রকমের দুর্যোগ আক্রান্ত করবে। আর যদি ওদেরকে সন্তুষ্ট করে মনস্কামনা পূরণের প্রার্থনা করো, তাহলে তারা তোমাদের সাহায্য করবে। কিন্তু তাদেরকে কিভাবে খুশী করা যায় এবং কিভাবে তাদেরকে তোমাদের প্রতি আকৃষ্ট করা যায় সেটা আমাদের জানা আছে। তাদের সান্নিধ্যে উপনীত হওয়ার মাধ্যম একমাত্র আমরাই হতে পারি। সুতরাং আমাদের বড়ত্ব ও বুজুর্গী মেনে নাও। আমাদরেকে খুশী করো এবং আমাদের হাতে তোমাদের জানমাল ও ইজ্জত সব সোপর্দ করে দাও। বহু নির্বোধ মানুষ এই ফাঁদে আটকা পড়ে। আর এভাবেই ভূয়া খোদাদের আড়ালে পুরোহিত, পূজারী ও খাদেমদের খোদায়ী প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।
এই শ্রেণীর মধ্যেই আর একটা গোষ্ঠী আছে। তারা জ্যোতির্বিদ্যা, তাবীজ-তুমার ও যাদুমন্ত্র ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত হয়। তাছাড়া আরো কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর বন্দেগী ও দাসত্বের স্বীকৃতি দেয় বটে, তবে তারা এও বলে যে, তোমরা সরাসরি আল্লাহর কাছে পৌছতে পারবেনা। তাঁর দরবারে পৌছার মাধ্যম আমরা। ইবাদতের আচার অনুষ্ঠান আমাদের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। তোমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিটি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আমাদের হাতেই সম্পন্ন হবে। এমন আরো কিছু লোক আছে, যারা আল্লাহর কিতাবের রক্ষক ও পারদর্শী, কিন্তু সাধারণ লোকদেরকে তার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে, আর নিজেরা আল্লাহর স্বকল্পিত বরকন্দাজ সেজে হালাল হারামের মনগড়া বিধি চালু করতে থাকে। এভাবেই তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত প্রতিটি কথাই আইনে পরিণত হয়। তারা মানুষকে আল্লাহর নয় বরং নিজেদের হুকুমের দাসে পরিণত করে। পৃথিবীর আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন নামে ও ভিন্ন ভিন্ন আকৃতিতে দেশে দেশে ও অঞ্চলে অঞ্চলে যে ভ্রাক্ষ্মণ্যবাদ ও পোপতন্ত্র চালু রয়েছে, তার মূল কথা এটাই, এরই বদৌলতে কোনো কোনো বংশ, বর্ণ ও শ্রেণী সাধারণ মানুষের ওপর নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে।
বিভ্রান্তির উৎস
এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে জানা যাবে, পৃথিবীতে সকল বিভ্রান্তি এবং সকল বিপর্যয় ও অশান্তির মূল উৎস হলো মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব- চাই তা প্রত্যক্ষভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে। যাবতীয় অনাচার ও দুস্কৃতির সূচনা এই জিনিস থেকেই হয়েছে এবং এথেকেই আজও প্রস্ফুটিত হচ্ছে হাজারো বিষাক্ত ঝর্ণা। মানব স্বভাব প্রকৃতির যাবতীয় রহস্য আল্লাহ তায়ালারতো এমনিই জানা আছে। কিন্তু এখন হাজার হাজার বছরের অভিজ্ঞতা দ্বারা খোদ আমাদেরও একথা পুরোপুরিভাবে জানা হয়ে গেছে যে, মানুষ কাউকে না কাউকে ইলাহ বা রব না মেনে থাকতেই পারেনা। কেউ তার প্রভু বা ইলাহ না হলে তার যেনো বাঁচতে অসম্ভব। সে যদি আল্লাহকে না মানে, তাহলেও ইলাহ ও প্রভুর হাত থেকে তার নিস্কৃতি নেই। বরং সেক্ষেত্রে তার ঘাড়ের ওপর অসংখ্য ইলাহ ও প্রভু চেপে বসবে। আজও আপনি যেদিকেই তাকান দেখবেন, কোথাও একজাতি অপর জাতির ইলাহ বা খোদা হয়ে বসে আছে। কোথাও এ শ্রেণী অপর শ্রেণী বা গোষ্ঠীর প্রভু হয়ে রয়েছে। কোথাও একটি দল ইলাহ ও রবের পদটি দখল করে বসে আছে। কোথাও জাতীয় রাষ্ট্র খোদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। আবার কোথাও কোনো স্বৈরাচারী হুংকার ছাড়ছে যে, “আমি ছাড়া তোমাদের কোনো খোদা আছে বলেতো জানিনা” [সূরা কাসাসঃ ৩৮]। দুনিয়ার কোনো একটি স্থানেও মানুষ ইলাহ বা প্রভু ছাড়া জীবন যাপন করেনি।
এরপর মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তার ফল কি দাড়ায় তাও ভেবে দেখা দরকার। একজন অযোগ্য লোককে পুলিশ কমিশনার বা একজন মূর্খ লোককে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে দিলে যে ফলাফল দেখা দিয়ে থাকে, এখানেও সেটাই দেখা দেবে। একেতো প্রভুত্বের নেশাটাই এমন যে, কোনো মানুষ এই মদ খেয়ে স্থির থাকতেই পারেনা। আর যদি ধরেও নেয়া যায় যে, স্থির থাকতে পারবে, তথাপি প্রভুত্বের দায়িত্ব পালন করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন এবং যেরূপ নিঃস্বার্থ ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক, তা মানুষ কোথায় পাবে? একারণেই যেখানে যেখানে মানুষের প্রভুত্ব ও নিরংকুশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কোনো না কোনো উপায়ে যুলুম, নিপীড়ন, আগ্রাসন, অবৈধ স্বার্থভোগ, অবিচার ও অসম আচরণের প্রাদুর্ভাব না ঘটে ছাড়েনি। মানবাত্মা আপন স্বাভাবিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয়ে পারেনি। মানুষের মনমগজের ওপর এবং তার সহজাত ক্ষমতা, যোগ্যতা ও প্রতিভার ওপর এমন কড়াকড়ি আরোপিত না হয়ে পারেনি, যা মানবীয় ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও উন্নয়নকে থামিয়ে দিয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যথার্থই বলেছেনঃ
“আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ আমি আমার বান্দাদেরকে নিখুত ও নির্মল স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছিলাম। পরে শয়তান তাদেরকে এসে ঘিরে ধরলো, তাদেরকে তাদের স্বভাবসুলভ নির্ভুল পথ থেকে বিচ্যুত করলো এবং আমি যা কিছু তাদের জন্য হলাল করেছিলাম তা থেকে শয়তানরা তাদের বঞ্চিত করলো।” [হাদীসে কুদসী]
বস্তুতঃ এই জিনিসটাই মানুষের সকল বিপদ মুসিবত, সকল ধ্বংস ও বিপর্যয় এবং সকল বঞ্চনার মূল কারণ। তার উন্নতির পথে এটাই অন্তরায়। এটাই সেই সর্বনাশা রোগ যা তার নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে, তার জ্ঞান ও চিন্তা শক্তিকে, তার সমাজ ও সভ্যতাকে, তার রাজনীতি ও অর্থনীতিকে, এক কথায় তার সমগ্র মনুষ্যত্বকে যক্ষারোগের মতো খেয়ে ফেলেছে। আদিমতম যুগ থেকে খেয়ে আসছে এবং আজও সমানে খেয়ে চলেছে। এ রোগের একমাত্র চিকিৎসা হলো, মানুষ সকল রব ও সকল ইলাহকে অস্বীকার করে শুধুমাত্র বিশ্বপ্রভূ আল্লাহকে নিজের প্রভু, ইলাহ ও রব বলে ঘোষণা করবে। এছাড়া তার মুক্তির আর কোনো পথ নেই। কেননা নাস্তিক ও ধর্মদ্রোহী হলেও তো অসংখ্য জাগতিক খোদা ও প্রভুর হাত থেকে তার নিস্কৃতি নেই।
নবীগণের আসল সংস্কারমূলক কাজ
নবীগণ মানুষের জীবনে যে মৌলিক সংস্কারমূলক কাজটি করে গেছেন সেটি হলো এই কাজ। আসলে মানুষের ওপর থেকে মানুষের প্রভুত্বের অবসান ঘটাতেই তারা এসেছিলেন। মানুষকে এই যুলুম থেকে, এসব মিথ্যা ও ভূয়া খোদাদের দাসত্ব থেকে এবং এই আগ্রাসন ও শোষণ থেকে মুক্তি দেয়াই ছিলো তাদের আসল ব্রত ও লক্ষ্য। যে মানুষ মনুষ্যত্বের সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে আবার সীমার মধ্যে ফিরিয়ে আনা এবং যাদেরকে এই সীমার নিচে নিক্ষেপ করা হয়েছিলো তাদেরকে এই সীমা পর্যন্ত উঠিয়ে আনাই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। সবাইকে তারা এমন একটা সুষম ও সুবিচার ভিত্তিক জীবনব্যবস্থার অনুগত করতে চেয়েছিলেন, যেখানে কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের দাসও হবেনা, মনিবও হবেনা। উপাস্যও হবেনা, উপাসকও হবেনা। বরং সবাই এক আল্লাহর গোলামে পরিণত হবে। আদিকাল থেকে এযাবত যতো নবী দুনিয়ায় এসেছেন তাদের সকলের একই বানী ছিলো যে, “হে জনতা! তোমরা সবাই আল্লাহর দাসত্ব করো। তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ নেই।” হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, হযরত হুদ আলাইহিস সালাম, হযরত সালেহ আলাইহিস সালাম ও হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামও একথাই বলেছেন। আর সর্বশেষ আরবের মাটিতে জন্ম নেয়া বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একথাই ঘোষণা করেছেনঃ
“আমি কেবল একজন সাবধানকারী। সেই আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই যিনি একও সকলের ওপর জয়ী। যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভু।” [সূরা সাদঃ ৬৫-৬৬]
“নিশ্চয় সে আল্লাহই তোমাদের প্রভু, যিনি আকাশ ও পৃথিবীকে……………. এবং সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রকে সৃষ্টি করেছেন। সবাই তার আদেশের অনুগত। সাবধান, সৃষ্টি তাঁর এবং শাসনও তাঁরই। [সূরা আরাফঃ ৫৪]
“সেই এক আল্লাহই তোমাদের প্রভু। তিনি ছাড়া কোনো মা’বুদ নেই। তিনি সকল জিনিসের স্রষ্টা। কাজেই তোমরা তাঁরই আনুগত্য করো, তিনি সকল জিনিসের সংরক্ষক।” [সূরা আনয়ামঃ ১০২]
“একনিষ্ঠ আনুগত্যও একাগ্রতা সহকারে আল্লাহর দাসত্ব করা ছাড়া মানুষকে আর কোনো কাজের আদেশ দেয়া হয়নি।” [সূরা আলবাইয়িনাঃ ৫]
“যেকথা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন তার দিকে এসো। সেটি হলো, আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবোনা, তাঁর খোদায়ীতে আর কাউকে শরীক করবোনা এবং আমাদের মধ্য থেকে কেউ কাউকে আল্লাহর বিকল্প প্রভু বানিয়ে নেবোনা।” [সূরা আল ইমরানঃ ৬৪]
এ আহবানই মানুষের আত্মাকে, তার চিন্তা ও বুদ্ধিকে এবং তার মানসিক ও বস্তুগত শক্তিগুলোকে বিদ্যমান গোলামীর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিয়েছিলো। এটি ছিলো মানুষের জন্য সত্যিকার স্বাধীনতার সনদ। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কীর্তি সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছেঃ
“মানুষ যে বোঝার নিচে পিষ্ট হচ্ছিলো, এই নবী তাথেকে তাদের উদ্ধার করেন এবং যেসব বন্ধনে তারা আবদ্ধ ছিলো তা তিনি ছিন্ন করেন।” [সূরা আরাফঃ ১৫৭]
২. রাজনীতির গোড়ার কথা
নবী আলাইহস সালামগণ মানবজীনের জন্য যে বিধিব্যবস্থা তৈরী করে দিয়েছেন তার কেন্দ্রবিন্দু ও ভিত্তি, তার মূল প্রাণশক্তি এবং সার নির্যাসই হচ্ছে এই আকিদা ও বিশ্বাস। ইসলামী রাজনীতির গোড়ার কথাই হচ্ছে এই মূলনীতি যে, আদেশ প্রদান ও আইন রচনার ক্ষমতা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষের কাছ থেকে এবং সামষ্টিকভাবে সকল মানুষের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে। কারো জন্য এ অধিকার মেনে নেয়া হবেনা যে, সে নির্দেশজারী করবে এবং অন্যেরা তার আনুগত্য করবে। এ অধিকার ও ক্ষমতা কেবলমাত্র আল্লাহর রয়েছে, আর কারো নয়।
“আল্লাহ ছাড়া আর কারো শাসন চলবেনা, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করোনা, এটাই সঠিক জীবন ব্যবস্থা।” [সূরা ইউসুফঃ ৪০]
“তারা জিজ্ঞাসা করে, ক্ষমতায় আমাদের কিছু অংশ আছে কি? তুমি বলে দাও, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর। [সূরা আলা ইমরানঃ ১৫৪]
“নিজ নিজ মুখ দিয়ে ভ্রান্তভাবে একথা বলোনা যে, এটা হালাল আর এটা হারাম।” [সূরা আননাহলঃ ১১৬]
“আল্লাহর নাযিল করা শরীয়া মোতাবেক যারা ফায়সালা করেনা তারাই কাফের।” [সূরা মায়েদাঃ ৪৪]
এ মতাদর্শ অনুসারে সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার। আইন রচনাকারী আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ নয়। কোনো মানুষ, চাই নবীই হোকনা কেন, স্বতন্ত্রভাবে হুকুম দেয়া ও নিষেধ করার অধিকারী নয়। নবী নিজেও আল্লাহর আদেশেরই অনুগত।
“আমি শুধু ওহীযোগে প্রাপ্ত নির্দেশই মেনে চলি।” [সূরা আনয়ামঃ ৫০]
সাধারণ মানুষকে নবীর আনুগত্য করা নির্দেশ শুধু এজন্যই দেয়া হয়েছে যে, তিনি নিজের হুকুম নয় বরং আল্লাহর হুকুম জারী করেন।
“আমি যাকেই রসূল করে পাঠিয়েছি, আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর আনুগত্য করা হবে- এজন্যই পাঠিয়েছি।” [সূরা আননিসাঃ ৬৪]
“এই সকল ব্যক্তিবর্গকেই আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়্যত দান করেছি।” [সূরা আনয়ামঃ ৮৯]
“কোনো মানুষের এ অধিকার নেই যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবূয়্যত দান করবেন আর সে জনগণকে বলবে, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার দাস হয়ে যাও। বরং সে শুধু একথাই বলবে যে, তোমরা আল্লাহর দাস হয়ে যাও।” [সূরা আল ইমরানঃ ৭৯]
সুতরাং কুরআনের উপরোক্ত আয়াতসমূহ থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের যে কয়টি প্রাথমিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায় তা নিম্নরূপঃ
১. কোনো ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা গোষ্ঠী এমনকি রাষ্ট্রের সমগ্র জনগোষ্ঠী মিলিত হয়েও সার্বভৌমত্বের অধিকারী নয়। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক শুধু আল্লাহ তায়ালা। বাদবাকী সবাই নিছক প্রজার মর্যাদা রাখে।
২. আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। সকল মুসলমান মিলিত হয়ে না পারে নিজেদের জন্য কোনো আইন বানাতে, আর না পারে আল্লাহর প্রণীত কোনো আইন সংশোধন করতে।
৩. আল্লাহর নবী আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আইন দিয়েছেন, তার ভিত্তিতেই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই রাষ্ট্র পরিচালনাকারী সরকার শুধুমাত্র আল্লাহর আইন প্রয়োগ ও বাস্তবায়নকারী সরকার হিসেবেই এবং যতক্ষণ আল্লাহর আইন প্রয়োগ করতে থাকবে ততক্ষণই আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী হবে।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও ধরন
যে কোনো ব্যক্তি উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি একটি নজর বুলিয়েই বুঝতে পারে যে, এটা পাশ্চাত্য ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র Secular Democracy] নয়। কেননা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গণতন্ত্রতো বলাই হয় এমন শাসন ব্যবস্থাকে, যাতে দেশের সাধারণ অধিবাসীদের সার্বভৌমত্ব থাকে, তাদের মতেই দেশের আইন তৈরী হয় এবং তাদের মতানুসারেই আইনের সংশোধন ও রদবদল হয়ে থাকে। যে আইন তারা চাইবে তা চালু আর যে আইন তারা চাইবেনা তাকে আইনের বই থেকে খারিজ করে দেয়া হবে। ইসলামে একথা খাটেনা। এখানে একটা সর্বোচ্চ মৌলিক বিধান স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা স্বীয় রসূলের মাধ্যমে দেন, যার আনুগত্য সরকার ও রাষ্ট্রকে করতেই হয়। সুতরাং এ অর্থে তাকে গণতন্ত্র বলা যায়না। এর জন্য অধিকতর নির্ভুল নাম হচ্ছে “খোদায়ী শাসন” যাকে ইংরেজীতে [Theocracy] বলা হয়ে থাকে। তবে ইউরোপ যে থিওক্র্যাসীর সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্র্যাসী তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপ যে থিওক্র্যাসীর সাথে পরিচিত, তাতে একটা বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী [Priest class] আল্লাহর নামে নিজেদের বানানো আইনকুনুন চালু করে। [খৃষ্টান পোপ ও পাদ্রীদের কাছে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের কিছুসংখ্যক নৈতিক শিক্ষা ছাড়া কোনো শরীয়ত তথা আইন বিধান আদৌ ছিলোনা। তাই তারা নিজেদের ইচ্ছামতো আপন প্রবৃত্তির খায়েশ মোতাবেক আইন বানাতো আর তাকে আল্লাহর আইন আখ্যায়িত করে বাস্তবায়িত করতো। সূরা বাকারার ৭৯ নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ “যারা নিজ হাতে বই লেখে এবং বলে যে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে, তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ পরিণাম।”] এভাবে তারা কার্যত জনসাধারণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়। এধরনের শাসনকে খোদায়ী শাসন বলার চেয়ে শয়তানী শাসন বলাই অধিকতর মানান সই। পক্ষান্তরে ইসলাম যে থিওক্র্যাসী পেশ করে, তা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকেনা, বরং সাধারণ মুসলমানদের হাতে নিবদ্ধ থাকে। আর এই সাধারণ মুসলমানরা আল্লাহর কিতাব ওরসূলের সুন্নাহ অনুসারে তা পরিচালনা করে। আমাকে যদি একটা নতুন পরিভাষা উদ্ভাবনের অনুমতি দেয়া হয়, তবে আমি এই শাসন ব্যবস্থাককে “ইসলামী গণশাসন” নামে অভিহিত করবো। কেননা এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীন মুসলমানদেরকে একটা সীমিত গণসার্বভৌমত্ব [Limited popular sovereignty] দেয়া হয়েছে। এতে শাসন বিভাগ [Executive] ও আইনসভা [Legrslature] মুসলিম জনগণের মতানুসারে গঠিত হবে। মুসলিম জনগণই এই দুটিকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকারী হবে। প্রশাসনিক ও অন্যান্য যেসব বিষয়ে আল্লাহর শরীয়তে কোনো সুস্পষ্ট বিধান নেই, তা মুসলিম জনগণের ঐক্যমতেই নিষ্পন্ন হবে। আল্লাহর আইন যেখানে ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে, সেখানে কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা প্রজন্ম নয়, বরং সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তিই ইজতিহাদের যোগ্যতা অর্জন করেছে, সে তার ব্যাখ্যা দেয়ার অধিকারী হবে। এদিক থেকে এটা গণতন্ত্র বটে। কিন্তু একটু আগেই যেমন বললাম, যেখানে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অকাট্য নির্দেশ বিদ্যমান থাকবে, সেখানে মুসলমানদের কোনো নেতা, কোনো আইনসভা, কোনো মুজতাহিদ, কোনো আলেম, এমনকি সারা দুনিয়ার মুসলমানরাও যদি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়, তথাপি তাদের উক্ত নির্দেশের এক চুল পরিমাণ সংশোধন করারও অধিকার নেই। এদিক থেকে এটা থিওক্র্যাসী বা ধর্মীয় শাসন।
সম্মুখে অগ্রসর হবার আগে আমি এ ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা দিতে চাই যে ইসলামে গণতন্ত্রের ওপর এসব বিধিনিষেধ ও কড়াকড়ি কি জন্য আরোপ করা হয়েছে এবং কি ধরনের বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে। যারা আপত্তি তোলে, তারা বলতে পারে, এভাবে তো আল্লাহ তা’য়ালা মানুষের বিবেক ও আত্মার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়েছেন। অথচ আপনারা বলে থাকেন, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি, চিন্তা, দেহ ও প্রাণের স্বাধীনতা দেয়। এর জবাব হলো, আল্লাহ তা’য়ালা যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন, সেটা মানুষের স্বাভাবিক ও জন্মগত স্বাধীনতা হরণ করার জন্য নয়, বরং তা রক্ষা করার জন্যই রেখেছেন। মানুষকে বিপথগামী হওয়া ও নিজের পায়ে কুড়াল মারা থেকে রেহাই দেয়াই এর উদ্দেশ্য।
পাশ্চাত্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র সম্পর্কে দাবী করা হয় যে, তাতে গণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু উক্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পর্যালোচনা কারলে এই দাবীর সারবত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যে জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে একটা রাষ্ট্র গড়ে ওঠে, তারা সবাই স্বয়ং আইন প্রণয়নও করেনা, তা কার্যকারীও করেনা। কতিপয় নির্দিস্ট ব্যাক্তির হাতে নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর করতে তারা বাধ্য হয়, যাতে ঐ ব্যক্তিবর্গ তাদের পক্ষ থেকে আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এ উদ্দেশ্যেই নির্বাচনের একটা ব্যবস্থা ও অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়। যেহেতু সমাজ সামগ্রিকভাবে নৈতিকতা, সততা ও আমানতদারীর মতো অমুল্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং এসব ধারণার তেমন কোনো গুরুত্বও স্বীকার করেনা, তাই যারা জনগণকে নিজ নিজ বিদ্যাবুদ্ধি, ধনসম্পদ, চালাকী-চাতুরী ও মিথ্যা অপপ্রচার দ্বারা বোকা বানাতে পারে, তারাই এই নির্বাচনে অধিক সংখ্যায় নির্বাচিত হয়। শুধু তাই নয়, তারা জনগণের ভোটেই নির্বাচিত হয়ে তাদের ইলাহ বা প্রভু হয়ে বসে। আর নির্বাচিত হয়ে তারা জনগণের উপকারার্থে নয়, বরং নিজেদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থের তাগিদ আইন রচনা করে। অতঃপর জনগণের দেয়া ক্ষমতা বলেই এসব গণবিরোধী আইন জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়। আমেরিকাই বলুন, বৃটেনই বলুন কিংবা অন্য যেসব দেশ নিজেকে গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য বলে মনে করে তাদের কথাই বলুন, সকল দেশেরই এই একই শোচনীয় দশা।
তারপর এদিকটা যদি উপেক্ষা করে মেনেও নিই যে, ওসব দেশে সাধারণ মানুষের ইচ্ছা অনুসারেই আইন প্রণীত হয়ে থাকে, তথাপি অভিজ্ঞতা থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, সাধারণ জনগণ নিজেরা নিজেদের ভালো মন্দ পুরোপুরি বুঝতে পারেনা। মানুষের এটা একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা যে, নিজের জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তবতার কিছু দিক সে উপলব্ধি করে এবং কিছু উপলব্ধি করতে পারেনা। এজন্য তার সিদ্ধান্ত সাধারণত একপেশে হয়ে থাকে। ভাবাবেগ ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনা তার ওপর এতো প্রবল হয়ে উঠে যে, সে সম্পূর্ণ নির্ভজাল জ্ঞানগত ও যুক্তিসংগত উপায়ে নির্ভুল ও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত ও মতামত খুব কমই গ্রহণ করতে পারে। এমনকি অনেক সময় জ্ঞানগত ও যৌক্তিক দিক দিয়ে যে বিষয়টি তার কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়, তাকেও সে ভাবাবেগে ও প্রবৃত্তির কামনা বাসনার মোকাবিলায় আগ্রাহ্য করে। এর প্রমাণ হিসেবে বহু সংখ্যক উদাহরণ আমি দিতে পারি। তবে দীর্ঘ সূত্রিতা এড়ানোর জন্য আমি আমেরিকার মদ নিষিদ্ধকরণ আইনের উদাহরণটি তুলে ধরবো। যাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, তথ্য ও যুক্তির আলোকে এ বিষয়টি সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিলো যে, মদ স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তিগুলোর ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে এবং মানব সভ্যতার বিকৃতি ও বিপর্যয় আনয়ন করে। এই তথ্যের ভিত্তিতে মার্কিন জনমত মদ নিষিদ্ধ করণের আইন পাশ করার পক্ষে সম্মতি দেয়। জনগণের সেই রায় অনুসারেই মার্কিন কংগ্রেস ১৯১৮ সালে এই আইন পাশ করে। কিন্তু আইনটি যখন কার্যকর হলো, তখন যে জনতার রায়ে তা পাশ হয়েছিলো তারাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো। তারা অবৈধভাবে আরো খারাপ মদ বানানো এবং পান করলো। আগের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী মদ ব্যবহৃত হলো, অপরাধ আরো বৃদ্ধি পেলো। অবশেষে যে জনতার ভোটে মদ একদিন হারাম হয়েছিলো, তাদের ভোটেই পুনরায় তাকে হালাল করা হলো। ১৯৩৩ সালে মাত্র ১৫ বছরের ব্যবধানে এই হারাম হওয়ার ফতোয়াটি যে হালাল হওয়ার ফতোয়ায় পরিবর্তিত হয়ে গেলো, তার কারণ এ ছিলোনা যে, তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে তখন মদ খাওয়া উপকারী সাব্যস্ত হয়ে গিয়েছিলো। বরং এর একমাত্র কারণ এই ছিলো যে, জনগণ তাদের জাহেলী প্রবৃত্তির লালসার গোলামে পরিণত হয়ে গিয়েছিলো। তারা তাদের সার্বভৌমত্বকে নিজ নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিলো, আপন কামনাবাসনাকে নিজেদের খোদা বানিয়ে নিয়েছিলো এবং এই খোদার গোলামী করতে গিয়ে তারা যে আইনকে একদিন তাত্ত্বিক ও যৌক্তিকভাবে সঠিক মনে করেছিলো, তাকে পরিবর্তন করতে বদ্ধপরিকর হয়ে গিয়েছিলো। এধরনের আরো বহু নজীর রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মানুষ তার নিজের জন্য আইন প্রণেতা [Legislature] হবার পুরোপরি যোগ্যতা রাখেনা। সে অন্যান্য প্রভুর গোলামী থেকে রেহাই পেলেও নিজের অবৈধ খায়েশের গোলাম হয়ে যাবে এবং নিজ প্রবৃত্তির পরিচালক শয়তানের খোদা বানিয়ে নেবে। সুতরাং তার নিজ স্বার্থেই তার স্বাধীনতার ওপর যুক্তিসংগত সীমারেখা ও বিধিনিষেধ আরোপ করা প্রয়োজন।
এ কারণেই আল্লাহ তা’য়ালা কতিপয় বিধিনিষেধ আরোপ করেছেন। এগুলোকে ইসলামী পরিভাষায় “হুদুদুল্লাহ” তথা আল্লাহর সীমারেখা [Divine Limits] বলা হয়। জীবনের প্রত্যেক বিভাগে কতিপয় মূলনীতি, বিধি ও অকাট্য নির্দেশাবলীর সমন্বয়ে রচিত এই বিধিনিষেধ সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভারসাম্য ও সুষমতা বজায় রাখার জন্য আরোপ করা হয়েছি। এগুলো দ্বরা মানুষের স্বাধীনতার শেষ সীমা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে এবং বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই সীমারেখার মধ্যে থেকে তোমরা নিজেদের আচরণের জন্য প্রাসংগিক বিধি প্রণয়ন করে নিতে পারো। কিন্তু তোমাদের এই সীমা লংঘন করার অনুমতি নেই। এই সীমা অতিক্রম করলে তোমাদের জীবন বিপর্যয় ও বিকৃতির শিকার হয়ে যাবে।
উদাহরণ স্বরূপ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের কথাই ধরুন। এতে আল্লাহ তা’য়ালা ব্যক্তি মালিকানার অধিকার নিশ্চিত করে, যাকাতের ফরয করে, সূদকে হারাম করে, জুয়াকে নিষিদ্ধ করে, উত্তরাধিকারের আইন জারী করে এবং সম্পদ উপার্জন, সঞ্চয় ও ব্যয় করার ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কয়েকটি সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করে দিয়েছেন। মানুষ যদি এই সীমান্ত চিহ্নগুলো ঠিক রাখে এবং এগুলোর আওতাধীন থেকে লেনদেন ও কায়কারবার সংগঠিত করে, তাহলে একদিকে ব্যক্তিস্বাধীনতাও বহাল থাকবে, অপরদিকে শ্রেণী সংগ্রাম এবং এক শ্রেণীর ওপর অন্য শ্রেণীর আধিপত্যের সেই পরিবশও সৃষ্টি হতে পারেনা, যা শোষণ-নিপীড়নমূলক পুঁজিবাদ থেকে শুরু হয়ে শ্রমিকদের একনায়কত্বে গিয়ে সমাপ্ত হয়।
অনুরূপভাবে পারিবারিক জীবনে আল্লাহ তায়ালা শরীয়ত সম্মত পর্দা, পুরুষের আধিপত্য, স্বামী, স্ত্রী, সন্তান ও পিতামাতার অধিকার ও কর্তব্য, তালাক ও খুলার বিধান, শর্ত সাপেক্ষে একাধিক বিয়ের অনুমতি এবং ব্যভিচার ও ব্যভিচারের অপবাদজনিত শাস্তির বিধান দিয়ে এমন সীমানা চিহ্নিত করে দিয়েছেন যে, মানুষ যদি এই সীমানা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করে এবং এর গন্ডীর মধ্যে অবস্থান করে নিজের ঘরোয়া জীবনকে সুশৃংখলভাবে গড়ে তোলে, তাহলে গৃহ যেমন যুলুম নির্যাতনের নিগড়ে পরিণত হবেনা, তেমনি যে লাগামহীন নারী স্বাধীনতার উদ্দাম পৈশাচিক বন্যা সমগ্র মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের হুমকি দিচ্ছে তাও এর সেখান থেকে ফুটে বেরুবেনা।
অনুরূপভাবে মানবীয় সমাজ ও সভ্যতার সংরক্ষণের জন্য আল্লাহ কিসাসের [হত্যার দায়ে প্রাণদন্ড] আইন, চুরির দায়ে হাত কাটা, মদের নিষিদ্ধ হওয়া, শারীরিক সতর ঢাকার সীমা এবং এধরনের কয়েকটি স্থায়ী বিধি নির্ধারণ করার মাধ্যমে বিকৃতির দুয়ার চিরতরে রুদ্ধ করে দিয়েছেন।
আল্লাহর এসব সীমা নির্ধারণী বিধিসমূহের একটা পূর্ণাংগ তালিকা পেশ করা এবং তার প্রত্যেকটি বিধি যে মানব জীবনে ভারসাম্য ও সুষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কতো জরুরী তা এখানে বিশদভাবে বিশ্লেষণ করার অবকাশ নেই। এখানে আমি শুধু এতোটুকু কথা পাঠকের মনে বদ্ধমূল করতে চাই যে, আল্লাহ এভাবে এমন একটা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান মানুষকে দিয়েছেন যা তার স্বাধীনতার প্রাণশক্তিকে এবং তার চিন্তাশক্তি ও বোধশক্তিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়না। বরং তার জন্য একটা সুস্পষ্ট ও নির্ভুল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়, যাতে সে নিজের অজ্ঞতা ও দুর্বলতা বশত পথভ্রষ্ট হয়ে ধ্বংসের দিকে ধাবিত না হয়। তার শক্তি ও প্রতিভাগুলো ভুল পথে অপব্যয়ের শিকার হয়ে বিনষ্ট না হয়, বরং সে যেনো নিজের সত্যিকার কল্যান ও সমৃদ্ধির পথে সোজাসুজিভাবে এগিয়ে যেতে পারে। পাঠক, আপনার যদি কখনো দুর্গম পার্বত্য পথ চলার অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে আপনি নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন, পেঁচানো পার্বত্য পথের একদিকে গভীর খাদ এবং অপরদিকে উচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর দাঁড়ানো থাকে। আর সেই পথের দুই কিনারকে এমনসব প্রতিবন্ধক দ্বারা সুরক্ষিত করা হয় যাতে পথিক খাদের দিকে চলে যেতে না পারে। এসব প্রতিবন্ধক স্থাপনের উদ্দেশ্য কি পথিকের স্বাধীনতা হরণ করা? না তা নয়। বরং এর উদ্দেশ্য শুধু তাকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করা এবং প্রত্যেক মোড়ে ও প্রত্যেক সম্ভাব্য শংকার সময় তাকে বলে দিয়া যে, তোমার পথ ওদিক এদিক। তোমাকে ওদিকে নয় এদিকে মোড় ঘুরতে হবে, যাতে তুমি নিরাপদে আপন মানযিলে মাকসুদে পৌছে যেতে পারো। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সংবিধানে যে কড়াকড়ি বিধি আরোপ করেছেন, তা উদ্দেশ্যও এটাই। এসব সীমারেখা মানুষের জীবন পথে পরিভ্রমণের সঠিক দিক নির্দেশ করে এবং প্রত্যেক বিপদজ্জনক মোড়ে তাকে জানিয়ে দেয় যে, শান্তি ও নিরাপত্তার পথ এদিকে এবং তোমাকে ওদিকে নয় বরং এদিকে যেতে হবে।
আল্লাহর রচিত ও সংবিধান অপরিবর্তনীয়। আপনি ইচ্ছা করলে অন্যান্য পাশ্চাত্যভক্ত মুসলিম দেশের ন্যায় ও সংবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন, কিন্তু তাকে বদলাতে পারবেননা। এটা কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য অটল ও অপরিবর্তনীয় সংবিধান। ইসলামী রাষ্ট্র যখন প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এ সংবিধানের ভিত্তিতেই হবে।যতদিন কুরআন ও রসূলের সুন্নাহ পৃথিবীতে বহাল থাকবে, ততদিন এ সংবিধানের একটি ধারাকেও স্থানান্তরিত করা যাবেনা। যে মুসলমান থাকতে চাইবে তাকে এর অনুসরণ করতেই হবে।
ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য
এ সংবিধানের আওতায় যে রাষ্ট্র গঠিত হবে, তার জন্য একটা লক্ষ্যও আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং কুরআনের একাধিক স্থানে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেমনঃ
“আমি রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দিয়ে পাঠিয়েছি আর তাদের সাথে কিতাব এবং মানদন্ড দিয়েছি, যাতে লোকেরা সুবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আমি লোহা নাযিল করেছি, এতে প্রচন্ড শক্তি এবং জনগণের জন্য উপকারিতা রয়েছে।” [সূরা হাদীদঃ ২৫]
এ আয়াতে লোহা দ্বারা রাজনৈতিক শক্তি বা প্রয়োগ ক্ষমতাকে [coercive Power] বুঝানো হয়েছে। আর রসূলের কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে এই যে, আল্লাহ তাদেরকে যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন এবং নিজের কিতাবে যে দাড়িপাল্লা অর্থাৎ যে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার প্রতি তাদেরকে আহবান জানিয়েছেন সে অনুসারে সামাজিক ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠা করবেন। অন্যত্র বলেছেনঃ
“তারাই এসইসব লোক, যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা দিলে নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের আদশে দান করবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।” [সূরা আল হজ্জঃ ৪১]
অন্যত্র বলেনঃ
“মানব জাতির কল্যাণার্থে আবির্ভূত সর্বশ্রেষ্ট জাতি তোমরাই। সৎ কাজের আদেশ দান, অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখাই তোমাদের কাজ” [সূরা আল ইমরানঃ ১১০]
ইসলামী রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য
ক. ইতিবাচক ও সর্বাত্মক কর্মকান্ডঃ উপরোক্ত আয়াত কয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায়, কুরআন যে রাষ্ট্রের ধারণা ও পরিকল্পনা পেশ করে তার উদ্দেশ্য নেতিবাচক [Negative] নয় বরং তার সামনে একটা ইতিবাচক [Positive] উদ্দেশ্য রয়েছে। তার লক্ষ্য শুধু মানুষের পারস্পরিক বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার প্রতিহত করা, তাদের স্বাধীনতা রক্ষা করা ও দেশকে বিদেশী আক্রমণ থেকে হিফাযত করা নয়; বরং আল্লাহর কিতাবে সামাজিক সুবিচারের যে সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা পেশ করা হয়েছে তা বাস্তবায়িত করাও তার লক্ষ্য। আল্লাহ তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশাবলীতে অন্যায় অনাচারের যতো রূপ ও ধরনের উল্লেখ করেছেন তার উচ্ছেদ সাধন এবং যতো রকমের ন্যায় ও সৎ কাজের বিবরণ দিয়েছেন তার প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন ও রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য। এ কাজে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক শক্তিও প্রয়োগ করা হবে। দাওয়াত ও প্রচারণার মাধ্যমেও কাজ চালানো হবে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপায় উপকরণও কাজে লাগানো হবে এবং দলীয় প্রভাব ও জনমতের চাপও প্রয়োগ করা হবে।
এ ধরনের রাষ্ট্র যে স্বীয় তৎপরতা ও কর্মকান্ডের গন্ডীকে সীমিত করতে পারেনা তা সহজেই বুঝা যায়। এটা একটা বহুমুখী ও সর্বাত্মক রাষ্ট্র। গোটা মানবজীবনই এর কর্মক্ষেত্র। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পৌর ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি বিভাগকে সে নিজের স্বতন্ত্র নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও সংস্কারমূলক কর্মসূচী অনুযায়ী পুনর্গঠন করতে চায়। এখানে কোনো ব্যক্তি নিজের কোনো বিষয়কে ব্যক্তিগত বিষয় বলতে পারেনা। এদিক থেকে এই রাষ্ট্র কম্যুনিষ্ট ও একনায়ক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে এক ধরনের সাদৃশ্যের দাবীদার বটে। তবে আর একটু অগ্রসর হয়ে পাঠক দেখতে পাবেন যে, এহেন সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েও ইসলামী রাষ্ট্র এযগেও নিরংকুশ আধিপত্যবাদী [Totalitarian] ও [Authoritarian] সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র সমূহের মতো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করেনা, একনায়কত্ব [Dictatorship] চাপিয়ে দেয়না। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্র যে সর্বোচ্চ পর্যায়ের ভারসাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং হক ও বাতিলের মাঝে যে নাযুক ও সুক্ষ্ম সীমান্ত প্রাচীর স্থাপন করেছে তা দেখে একজন সত্যিকার অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের বিবেক স্বতস্ফুর্তভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা উদ্ভাবন প্রকৃতপক্ষে মহাবিজ্ঞানী ও সুক্ষ্মদর্শী আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।
খ. দলীয় ও আদর্শবাদী রাষ্ট্রঃ ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও সংস্কারমূখী চরিত্র নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আপনা আপনিই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ রাষ্ট্র শুধু তারাই চালাতে পারে যারা এর শাসনতন্ত্রে বিশ্বাসী, যারা এর উদ্দেশ্যকে নিজেদের জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে, যারা এর সংস্কারবাদী কর্মসূচীর সাথে পুরোপুরি একমত, যারা এর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীলই শুধু নয় বরং এর প্রাণশক্তিকে ভালোভাবে হৃদয়ংগমও করে এবং এর খুঁটিনাটিও জানে। ইসলাম এক্ষেত্রে কোনো ভৌগলিক, বর্ণগত ও ভাষাগত বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। সে নিজের শাসনতন্ত্র, উদ্দেশ্য ও সংস্কারমুখী কর্মসূচীকে সকল মানুষের সামনে তুলে ধরে। যে ব্যক্তি তা মেনে নেবে, চাই সে যে কোনো বর্ণ, বংশ, দেশ ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত হোক না কেন, সে এই রাষ্ট্র পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত দলে প্রবেশ করতে পারে। আর যে তা গ্রহণ করবেনা তাকে রাষ্ট্রীয় কাজে সম্পৃক্ত করা চলবেনা। তবে সে রাষ্ট্রের নিরাপত্তাধীন নাগরিক [Protecter Citizen] হিসেবে বসবাস করতে পারে। তার জন্য ইসলামী আইনে সুনির্দিষ্ট অধিকার ও সুযোগ সুবিধা নির্ধারিত রয়েছে। তবে তাকে সরকারে অংশীদারের মর্যাদা দেয়া হবেনা। কনেনা এটা একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র যার প্রশাসনিক কাজ শুধু এর আদর্শে বিশ্বাসী লোকেরাই চালাতে পারে। [অত্র গ্রন্থের ১৬শ অধ্যায় আরো বিশদ আলোচনা দ্রষ্টব্য]
এখানেও ইসলামী রাষ্ট্রে ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ভিন্ন মতাবলম্বিদের সাথে যে আচরণ সম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র করে থাকে, ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণের সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই। বিজয় অর্জন ও ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথেই আপন সাংস্কৃতিক রীতিনীতিকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়া, বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, হত্যা ও রক্তপাত চালানো এবং হাজার হাজার মানুষকে দুনিয়ার জাহান্নাম সাইবেরিয়ায় পাঠিয়ে দেয়ার যে অব্যাহত ধারা কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে শুরু হয়, ইসলামে সে সবের কোনো অস্তিত্ব নেই। ইসলাম স্বীয় রাষ্ট্রীয় সীমানায় অমুসলিমদের প্রতি যে উদার আচরণ করে থাকে এবং এ ব্যাপারে যুলুম ও ন্যায়বিচার এবং সত্য ও অসত্যের মাঝে যে সুম্পষ্ট ভেদরেখা টেনে দেয়, তা দেখে যেকোনো ইনসাফপ্রিয় মানুষ একনজরেই বুঝতে পারে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সংস্কারকগণ আসে তারা কিভাবে কাজ করে। আর পৃথিবীতে যেসব সকল ও স্বকথিত সংস্কারদের আবির্ভাব ঘটে তাদের কর্মপদ্ধতি কিরূপ হয়ে থাকে।
৪. খিলাফত ও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য
এবার আমি ইসলামী রাষ্ট্রের অবকাঠামো ও তার কর্মপদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা দেবো। আমি আগেই বলেছি, ইসলামে আসল সার্বভৌম শাসক হচ্ছেন আল্লাহ। এই মূলনীতির আলোকে যখন আপনি এ প্রশ্ন নিয়ে ভাববেন যে, পৃথিবীতে যারা আল্লাহর আইন চালু করতে উদ্যোগী হবে তাদের মর্যাদা ও অবস্থান কি রকম হওয়া উচিত, তখন আপনার মন আপনা থেকেই বলে উঠবে, তাদের আসল সার্বভৌম শাসকের প্রতিনিধি বলেই আখ্যায়িত হওয়া উচিত। ইসলামেও তাদের ঠিক এই মর্যাদাই দেয়া হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ
“তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও নেক আমল করবে, তাদের সাথে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি [খলীফা] বানাবেন, ঠিক যেভাবে তাদের পূর্বে অন্যদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছিলেন।” [সূরা নূরঃ ৫৫]
এ আয়াত ইসলামের রাষ্ট্র তত্ত্বের ওপর অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আলোকপাত করে। এতে দুটো মৌলিক বিষয় আলোচিত হয়েছেঃ
প্রথমতঃ ইসলাম সার্বভৌম শাসনের পরিবর্তে খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব পরিভাষাটি ব্যবহার করে। যেহেতু তার মতাদর্শ অনুসারে সার্বভৌমত্ব আল্লাহর, তাই ইসলামী শাসনতন্ত্র অনুসারে যে ব্যক্তি পৃথিবীর কোথাও শাসক পদে অধিষ্ঠিত হবে তাকে অবশ্যই সর্বোচ্চ শাসক আল্লাহর প্রতিনিধি হতে হবে। সে শুধুমাত্র অর্পিত ক্ষমতা [Delegated power] প্রয়োগের অধিকারী।
দ্বিতীয়তঃ এ আয়াত থেকে অকাট্যভাবে জানা যায় যে, খলীফা বা প্রতিনিধি বানানোর ওয়াদা সকল মুমিনের সাথে করা হয়েছে। একথা বলা হয়নি যে, মুমিনদের মধ্য থেকে কাউকে প্রতিনিধি বানাবো। এথেকে বুঝা যায়, প্রত্যেক মুমিন খিলাফতের অধিকার প্রাপ্ত। আল্লাহর পক্ষ থেকে যে খিলাফত মুমিনদেরকে দেয়া হয় তা সার্বজনীন খিলাফত। কোনো ব্যক্তি, পরিবার, শ্রেণী বা বর্ণের জন্য তা নির্দিষ্ট নয়। প্রত্যেক মুমিন স্ব স্ব স্থানে আল্লাহর খলীফা। খলীফা হিসেবে প্রত্যেকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য। একটি বিখ্যাত হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
“তোমাদের প্রত্যেক এক একজন রাঁখাল। প্রত্যেকে নিজ নিজ অধীনস্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।”
আল্লাহর এই সার্বজনীন খিলাফতের আওতায় এক খলীফা অপর খলীফার চেয়ে কোনো দিক দিয়েই নিকৃষ্ট নয়।
ইসলামী গণতন্ত্রের মর্যাদা
এই হলো ইসলামে গণতন্ত্রের প্রকৃত ভিত্তি। সার্বজনীন খিলাফতের উল্লিখিত তত্ত্বটি পর্যালোচনা করলে নিন্মোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহে উপনীত হওয়া যায়।
১. যে সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তি আল্লাহর খলীফা এবং খিলাফতে সমান অংশীদার সে সমাজে শ্রেণীভিত্তিক বিভক্ত ও বৈষম্য এবং জন্মগত বা সামাজিক আভিজাত্য ও বৈষম্যের কোনো অবকাশ নেই। সে সমাজে সকল ব্যক্তি সমান মর্যাদাসম্পন্ন হবে। শ্রেষ্ঠত্ব যেটুকুই হবে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সততার ভিত্তিতেই হবে। এ বিষয়টা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম একাধিকবার দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরেছেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি বলেনঃ
“ওহে জনতা! শুনে নাও, তোমাদের প্রতিপালক একজন। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং কোনো আরবের ওপর অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কোনো কালো মানুষের ওপর সাদা মানুষের এবং সাদা মানুষের ওপর কালো মানুষের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্ব কেবল খোদভীরুতা তথা সততার ভিত্তিতে নির্ণিত হবে। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সবচেয়ে খোদাভীরু, সেই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে সম্মানের পাত্র।” [তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ২৬মত খন্ড, পৃঃ ১৪৮]
মক্কা বিজয়ের পর যখন সমগ্র আরব জগত ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হলো তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লামের পরিবারের লোকেরা আরবে পুরোহিতের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলো। তাদের তিনি বললেনঃ
“আল্লাহর শোকর, তিনি তোমাদেরকে জাহেলিয়াতের দোষ ও অহংকার থেকে পবিত্র করেছেন। হে জনমন্ডলী! শোনো মানুষ দুরকমের হয়ে থাকেঃ এক যারা সৎ ও সংযত। তারা আল্লাহর কাছে সম্মানিত। দুই, যারা অসৎ ও দুষ্কর্ম পরায়ন। তারা আল্লাহর কাছে নিকৃষ্ট। মূলতঃ সকল মানুষ আদমের সন্তান। আর আদমকে আল্লাহ মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, হে মানব মন্ডলী! আমি তোমাদেরকে একই পুরুষ ও স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি।…………….”
২. এ ধরনের সমাজে কোনো ব্যক্তি বা কোনো জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের জন্ম, সামাজিক মর্যাদা অথবা পেশার দিক দিয়ে এমন কোনো বাধাবিপত্তি থাকা উচিত নয়, যা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার বিকাশে এবং তার ব্যক্তিত্বের উৎকর্ষ সাধনে কোনোভাবে প্রতিবন্ধক হয়ে দেখা দিতে পারে। এখানে সমাজের সকল ব্যক্তিবর্গের উন্নতির সমান সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান থাকে। মানুষ নিজের ক্ষমতা ও যোগ্যতার বলে যতদুর সম্মুখে অগ্রসর হতে সক্ষম ততদুর যেনো অগ্রসর হতে পারে, সেজন্য একদিকে যেমন তার নিজের পথ খোলা থাকা চাই অপরদিকে তেমনি অন্য কারো অগ্রসরতা যেনো তার দ্বারা বাধাগ্রস্ত না হয় তারও বিশ্চয়তা থাকা চাই। ইসলামে এ জিনিসটা সর্বাধিক পরিমাণে ও পূর্ণাংগভাবে বিদ্যমান। ইসলামের ইতিহাসে বহু ক্রিতদাস ও তাদের সন্তানরা সেনাপতি ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছে এবং বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের অধীনে কাজ করেছে। বহু চামার জুতো সেলাই করতে করতেই সহসা ইমামের মসনদে আসীন হয়ে গেছেন। বহু জোলা [কাপড় প্রস্তুতকারী] মুফতী, কাযীও ফকীহ হয়েছেন আজ তাদের নাম ইসলামের মহাপুরুষদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম বলেছেনঃ
“তোমাদের ওপর যদি কোনো হাবশী ক্রিতদাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় তবু তার আদেশ শোনো এবং মান্য করো।” [বুখারী]
৩. এ ধরনের সমাজে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একনায়ক সুলভ শাসক হয়ে জেঁকে বসার, কোনো অবকাশ নেই। কেননা এখানে প্রত্যেকেই খলীফা। সাধারণ মুসলমানদের থেকে তাদের খিলাফত কেড়ে নিয়ে স্বৈরাচারী শাসকে পরিণত হওয়ার অধিকার কারো নেই। এখানে যাকে শাসক করা হয় তার প্রকৃত অবস্থা হলো, সকল মুসলমান অথবা পরিভাষিক শব্দে বলতে গেলে সকল খলীফা সেচ্ছায় নিজ নিজ খিলাফতকে প্রশাসনিক উদ্দেশ্যে তার হাতে কেন্দ্রীভূত করে দেয়। সে একদিকে আল্লাহর সামনে অপরদিকে যারা তার কাছে নিজ নিজ খিলাফতকে অর্পণ করেছে সেই সমস্ত খলীফার সামনে জবাবদিহী করতে বাধ্য। এখন সে যদি দায়িত্বহীন একনায়কে রূপান্তরিত হয় তাহলে সে আর খলীফা থাকেনা বরং শোষক ও জবরদখলকারীতে পরিণত হয়। কেনান একনায়কত্ব আসলে জনগণের সার্বজনীন খিলাফতের অস্বীকৃতি। যদিও একথা সত্য যে, ইসলামী রাষ্ট্র একটা সর্বাত্মক ব্যবস্থার ভিত্তি হলো আসলে আল্লাহর যে আইন দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালিত হবে সেই আইনই সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী। আল্লাহ তায়ালা জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কে যেসব নির্দেশ জারী করেছেন তা অবশ্যই সর্বোতভাবে কার্যকর করা হবে। কিন্তু ঐসব নির্দেশের প্রতিকুল ইসলামী রাষ্ট্র স্বয়ং জনগণের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে পারেনা। সে জনগণকে কোনো পেশা গ্রহণে বা বর্জনে, কোনো কারিগরী শিখতে বা না শিখতে, শিশুদেরকে কোনো বিশেষ বিষয় শেখাতে বা না শেখাতে, বিশেষ কোনো ধরনের টুপি পরতে বা না পরতে, ভাষার জন্য বিশেষ ধরনের বর্ণমালা ব্যবহার করতো বা না করতে এবং মেয়েদেরকে কোনো বিশেষ ধরনের পোশাক পরাতে বা না পরাতে বাধ্য করতে পারেনা। রাশিয়া, জার্মানী ও ইটালীর একনায়কগণ এসব সেচ্ছাচারমুলক ক্ষমতা প্রয়োগ করেছিলেন এবং আতাতুর্কও তা তুরস্কে প্রয়োগ করেন। কিন্তু ইসলাম কখনো তার শাসকদেরকে এধরনের ক্ষমতা দেয়ানি। তাছাড়া একটা গরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হলো, ইসলামে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী। এই ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও জাবাবদিহী এমন একটি ব্যাপার যাতে তার কোনো অংশীদার নেই। সুতরাং আইনের সীমানার মধ্যে তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, যাতে সে নিজের জন্য যেকোনো পথ অবলম্বন করতে পারে এবং যেদিকেই তার ঝোঁক হয় সেদিকেই নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভাকে কাজে লাগাতে পারে। শাসক যদি তার পথে বাধা দেয় তাহলে সে যুলুমকারী হিসেবে আল্লাহর কাছে জবাবদিহীর সম্মুখীন হবে। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে প্রজাদের ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণের নামনিশানাও চোখে পড়েনা।
৪. এধরনের সমাজে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম নর-নারীর ভোটাধিকার থাকা চাই। কেননা সে খিলাফাতের অধিকারী। আল্লাহ এই খিলাফাতকে কোনো বিশেষ পর্যায়ের যোগ্যতা বা ধনসম্পদের শর্তযুক্ত করেননি। শুধুমাত্র ঈমান ও সৎকর্মশীলতার শর্ত আরোপ করেছেন। সুতরাং রায় বা ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান অধিকার ভোগ করে।
একদিকে ইসলাম এহেন সর্বোচ্চ ও পূর্ণাংগ পর্যায়ের গণতন্ত্র কায়েম করেছে। অপরদিকে সামষ্টিক জীবনের সাথে সংঘর্ষশীল হয় এমন ব্যক্তি স্বাধীনতার [Individualism] বিকাশ রোধ করেছে। এখানে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যাতে কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের সামষ্টিক সমাজ কাঠামোর ন্যায় সমাজের মধ্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা হারিয়ে না যায়। আবার পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ন্যায় ব্যক্তিস্বাধীনতা এতো সীমাহীন না হয় যে, সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ইসলামে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জীবনের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সেটি হচ্ছে আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। উপরন্ত ইসলামে ব্যক্তির অধিকার পুরোপুরি মেনে নেয়ার পর তার জন্য সমাজের প্রতিও কিছু কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এভাবে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামষ্টিকতার মধ্যে এমন সমন্বয় সৃষ্টি হয়েছে যে, ব্যক্তি স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা বিকাশের পুরো সুযোগও লাভ করে, আবার সে নিজের উৎকর্ষ প্রাপ্ত শক্তিগুলিকে নিয়ে সমাজ কল্যাণের কাজেও সহায়ক হয়। এটা একটা স্বতন্ত্র বিষয়। এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। ইসলামী গণতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা আমি কিছু আগে করেছি তার ফলে যেসব ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো তার প্রতিনিধানের উদ্দেশ্যেই এ বিষয়ে কিছু সংক্ষিপ্ত ইংগিত করলাম।
তৃতীয় অধ্যায়
কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন
রাজনীতি বিজ্ঞানের মৌলিক জিজ্ঞাসা
১. কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব
২. জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি
৩. দীন এবং আল্লাহর আইন
৪. রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
৫. সার্বভৌমত্ব ও খিলাফতের ধারণা
৬. আনুগত্যের মূলনীতি
কুরআনুল করীম আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত সেই সর্বশেষ গ্রন্থ, যাতে আসমান ও যমীনের স্রষ্টা মানব জীবনের সকল মৌলিক বিষয়ে তার হিদায়াতের পূর্ণাংগরূপ মানুষকে প্রদান করেছেন। সাথে সাথে এই শাম্বত মূলনীতিও ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, এ হিদায়াতকে যারা মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং এর নির্দেশিত পথে জীবন যাপন করবে, তারাই হবে সফলকাম ও সৌভাগ্যবানঃ
“যারা আমার হিদায়াতের অনুসরণ অনুবর্তন করেছে, তাদের কোনো ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই। আর যারা তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে আর আমার আয়াতকে মিথ্যে বলেছে, তারা আগুনের সাথী হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে।” [আল কাবারাঃ ৩৮-৩৯]
কুরআন মানব জীবনের সকল বিভাগ সম্পর্কে মৌলিক হিদায়াত প্রদান করেছে। কুরআনের আসল আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করা। জন্ম থেকে মৃত্যু এবং মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্যেও এতে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা রয়েছে। সুতরাং মৌলিক রাজনৈতিক বিষয়ে আল্লাহর এই মহান কিতাব নীরব থাকার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। কুরআন দীন ও দুনিয়ার বিভক্তিকে বিপর্যয় বলে আখ্যায়িত করেছে। কুরআন তার অনুসারীদের কাছে দাবী করেঃ “উদখুলূ ফিস, সিলমি কাফফাতান- ইসলামে প্রবেশ করো পরিপূর্ণরূপে” কুরআনের রাজনৈতিক দর্শণ’ শিরোনামের অধীনে কুরআনের রাজনৈতিক ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।
তাফহীমুল কুরআন মাওলানা মুওদূদীর খ্যাতনামা তাফসীর গ্রন্থ। এ গ্রন্থে মাওলানা যুগসমস্যা এবং মুসলমানদের আধুনিক মনমানসিকতাকে সামনে রেখে পবিত্র কুরআনের হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। এ গ্রন্থ থেকেই আমরা এখানে রাজনৈতিক নিবন্ধগুলো সন্নিবেশিত করে দিয়েছি। – সংকলক।
রাজনীতি বিজ্ঞানের মৌলিক জিজ্ঞাসা
রাজনীতি বিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের পারস্পারিক সম্পর্কের সাথে জড়িত। এই বিজ্ঞানের কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন হলোঃ
১. রাষ্ট্রের প্রয়োজন কি?
২. রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হবেন কে?
৩. আনুগত্যের মূলনীতি কি হবে?
৪. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও মৌলিক কার্যাবলী কি?
সম্মুখের পাতাগুলোতে কুরআনের আলোকে এই প্রশ্নগুলোর জবাব উপস্থাপন করা হলো। কুরআনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি উপলব্ধি করা জন্যে বিশ্বজগতে মানুষের মর্যাদা ও গোটা জীবন সম্পর্কে কুরআনের দৃষ্টিভংগি কি, সেকথাটি আগেই বুঝে নেয়া জরুরী। তাই কুরআনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগি উপস্থাপন করার আগে জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি কি? সেবিষয়ে কিছু মৌলিক বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে। এরপরই কুরআনের রাজনৈতিক ধারণা উপস্থাপন করা হবে।
১. কয়েকটি মৌলিক তত্ত্ব
পাঠককে সর্বপ্রথম মূল কুরআনের সাথে পরিচিত হতে হবে। এর প্রতি তার বিশ্বাস থাকা না থাকার প্রশ্ন এখানে নেই। তবে কি কিতাবকে কুঝতে হলে প্রারম্ভিক সূত্র হিসেবে এ কিতাব নিজে এবং এর উপস্থাপক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসল্লাম যে মূল বিঝয় বিবৃত করেছেন তা গ্রহণ করতে হবে। এ মূল বিষয় নিম্নরূপঃ
১. সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রভু, সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও একচ্ছত্র শাসক সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ বিশেষ ও পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দান করেছেন জানার, বাঝার ও চিন্তা করার ক্ষমতা। ভালো ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য, করার, নির্বাচন, ইচ্ছা ও সংকল্প করার এবং নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করার স্বাধীনতা দান করেছেন। এক কথায় মানুষকে এক ধরনের স্বাধীনতা [Autonomy]দান করে তাকে দুনিয়ায় নিজের খলীফা বা প্রতিনিধি পদে অভিষিক্ত করেছেন।
২. মানুষকে এই পদে নিযুক্ত করার সময় বিশ্ব জাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানুষের মনে একথা দৃঢ় বদ্ধমূল করে দিয়েছিলেনঃ আমিই তোমাদের এবং সমগ্র বিশ্ব জগতের একমাত্র মালিক, মাবুদ ও প্রভু। আমার এই সাম্রাজ্যে তোমরা স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী নও, কারোর অধীনও নও এবং আমার ছাড়া আর কারোর তোমাদের বন্দেগী, পূজা ও আনুগত্য লাভের অধিকারও নেই। দুনিয়ার এই জীবনে তোমাদরেকে কিছু স্বাধীন ক্ষমতা ইখতিয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে। এটি আসলে তোমাদের জন্য পরীক্ষাকাল। এই পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তোমাদের কাজগুলো যাঁচাই বাছাই করে আমি সিদ্ধান্ত নেবো তোমাদের মধ্য থেকে কে সফল হলো এবং কে হলো ব্যর্থ। তোমাদের জন্য সঠিক কর্মনীতি একটিইঃ তোমরা আমাকে মেনে নেবে তোমাদের একমাত্র মাবুদ ও শাসক হিসেবে। আমি তোমাদের জন্য যে বিধান পাঠাবো সেই অনুযায়ী তোমরা দুনিয়ায় কাজ করবে। দুনিয়াকে পরীক্ষাগৃহ মনে করে এই চেতনা সহকারে জীবন যাপন করবে যেনো আমার আদালতে শেষ বিচারে সফলকাম হওয়াই তোমাদের জীবনের আসল উদ্দেশ্য। বিপরীত পক্ষে এর থেকে ভিন্নতর প্রত্যেকটি কর্মনীতি তোমাদের জন্য ভুল ও বিভ্রান্তিকর। প্রথম কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে [যেটি গ্রহণ করার স্বাধীন ক্ষমতা তোমাদরে দেয়া হয়েছে] তোমরা দুনিয়ায় শান্তি, নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা লাভ করবে। তারপর আমার কাছে ফিরে আসলে আমি তোমাদের দান করবো চিরন্তন আরাম ও আনন্দের আবাস জান্নাত। আর দ্বিতীয় কর্মনীতিটি গ্রহণ করলে [যেটি গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা তোমাদের দেয়া হয়েছে] তোমাদের দুনিয়ায় বিপর্যয় ও অস্থিরতার মুখোমুখি হতে হবে এবং দুনিয়ার জীবন শেষ করে আখিরাতে প্রবেশকালে সেখানে জাহান্নাম নামক চিরন্তন মর্মজ্বালা দুঃখ কষ্ট ও বিপদের গভীর গর্ভে তোমরা নিক্ষিপ্ত হবে।
৩. একথা ভালোভাবে বুঝিয়ে দেয়ার পর বিশ্ব জাহানের মালিক সর্বশক্তিমান আল্লাহ মানব জাতিকে পৃথিবীতে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানব জাতির দুই সদস্য [আদম ও হাওয়া] বিশিষ্ট প্রথম গুপকে তিনি পৃথিবীতে জীবন যাপন করার জন্য বিধান দান করেন। এই বিধান অনুযায়ী তাদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের দুনিয়ার সমস্ত কাজ কারবার চালিয়ে যেতে হবে। মানুষের এই প্রাথমিক বংশধারা মুর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্ট হননি। আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁদের জীবনের সূচনা করেন সম্পূর্ণ আলোর মধ্যে। তারা সত্যকে জানতেন। তাদেরকে জীবনবিধান দেয়া হয়েছিলো। আল্লাহর আনুগত্য [অর্থাৎ ইসলাম] ছিলো তাদের জীবন পদ্ধতি। তাঁরা তাঁদের সন্তানদেরও আল্লাহর অনুগত বান্দাহ [মুসলিম] হিসেবে জীবন যাপন করার কথা শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে শত শত বছরের জীবনাচরণে মানুষ ধীরে ধীরে এই সঠিক জীবন পদ্ধতি [অর্থাৎ দীন] থেকে দুরে সরে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের ভুল কর্মনীতি অবলম্বন করেছে। গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে তারা এক সময় এই সঠিক জীবন পদ্ধতি হারিয়ে ফেলেছে। আবার শয়তানী প্ররোচনায় একে বিকৃতও করেছে। তারা পৃথিবী ও আকাশের মানব ও অমানব এবং কাল্পনিক ও বস্তুগত বিভিন্ন সত্তাকে আল্লাহর সাথে তাঁর কাজ কারবারে শরীক করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত যথার্থ জ্ঞানের [আল ইলম] মধ্যে বিভিন্ন প্রকার কল্পনা, ভাববাদ, মনগড়া মতবাদ ও দর্শনের মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা অসংখ্য ধর্মের সৃষ্টি করেছে। তারা আল্লাহ নির্ধারিত ন্যায়নিষ্ঠ ও ভারসাম্যপূর্ণ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নীতি [শরীয়ত] পরিহার বা বিকৃত করে নিজেদের প্রবৃত্তি, স্বার্থ ও ঝোঁক প্রবণতা অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য নিজেরাই এমন বিধান তৈরী করেছে যার ফলে আল্লাহর এই যমীন যুলুম নিপীড়নে ভরে গেছে।
৪. আল্লাহ যদি তাঁর স্রষ্টাসুলভ ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিপথগামী মানুষদের জোরপূর্বক সঠিক কর্মনীতি ও জীবনধারার দিকে ঘুরিয়ে দিতেন তাহলে তা হতো মানুষকে আল্লাহ প্রদত্ত সীমিত স্বাধীনতাদান নীতির পরিপন্থী। আবার এ ধরনের বিদ্রোহ দেখা দেয়ার সাথে সাথেই তিনি যদি মানুষকে ধ্বংস করে দিতেন তাহলে সেটি হতো সমগ্র মানব জাতিকে পৃথিবীতে কাজ করার জন্য তিনি যে সময় ও সুযোগ নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সাথে অসামঞ্জস্যশীল। সৃষ্টির প্রথমদিন থেকে তিনি যে দায়িত্বটি গ্রহণ করেছিলেন সেটি ছিলো এই যে, মানুষের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রেখে কাজের মাঝখানে যেসব সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে তার মধ্যে দিয়েই তিনি তাকে পথ নির্দেশনা দেয়ার ব্যবস্থা করবেন। কাজেই নিজের ওপর আরোপিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি মানব জাতির মধ্য থেকে একদল লোককে ব্যবহার করতে শুরু করেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান রাখতেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে যেতেন। এদেরকে তিনি করেন নিজের প্রতিনিধি। এদের কাছে পাঠান নিজের অলংঘনীয় বাণী। যথার্থ সত্য জ্ঞান ও জীবন যাপনের সঠিক বিধান এদেরকে দান করে তিনি বনী আদমকে ভুল পথ থেকে এই সহজ সত্য পথের দিকে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়ার জন্য এদেরকে নিযুক্ত করেন।
৫. এরা ছিলেন আল্লাহর নবী। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাঁর নবী পাঠাতে থাকেন। হাজার হাজার বছর থেকে তাদের আগমনের এ ধারাবাহিকতা চলতে থাকে। তাঁদের সংখ্যা ছিলো হাজার হাজার। তাঁরা সবাই একই দীনের তথা জীবন পদ্ধতির অনুসারী ছিলেন। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমদিন থেকেই মানুষকে যে সঠিক কর্মনীতির সাথে পরিচিত করানো হয়েছিলো তাঁরা সবাই ছিলেন তারই অনুসারী। তাঁরা সবাই ছিলেন একই হিদায়াতের প্রতি অনুগত। অর্থাৎ প্রথম দিন থেকেই মানুষের জন্য নৈতিকতা ও সমাজ সংস্কৃতির যে চিরন্তরন নীতি নির্ধারণ করা হয়েছিলো তাঁরা ছিলেন তারই প্রতি অনুগত। তাঁদের সবার একই মিশন ছিলো। অর্থাৎ তাঁরা নিজেদের বংশধর, গোত্র ও জাতিকে এই দীন ও হিদায়াতের দিকে আহবান জানান। তারপর যারা এ আহবান গ্রহণ করে তাদেরকে সংগঠিত করে এমন একটি উম্মতে পরিণত করেন যাঁরা নিজেরা হন আল্লাহর আইনের অনুগত ও দুনিয়ায় আল্লাহর আইনের আনুগত্য কায়েম করার এবং তাঁর আইনের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা প্রতিরোধ করার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাতে থাকেন। এই নবীগণ প্রত্যেকেই তাঁদের নিজেদের যুগে অত্যন্ত সুচারুরূপে এ মিশনের দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু সবসময় দেখা গেছে মানব গোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুতই হয়নি। আর যারা এই দাওয়াত গ্রহণ করে উম্মতে মুসলিমার অংগীভুত হয় তারাও ধীরে ধীরে নিজেরাই বিকৃতির সাগরে তলিয়ে যেতে থাকে। এমনকি তাদের কোনো কোনো উম্মত আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতকে একেবারেই হারিয়ে ফেলে। আবার কেউ কেউ আল্লাহর বাণীর সাথে নিজেদের কথার মিশ্রণ ঘটিয়ে এবং তার মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে তার চেহারাই বিকৃত করে দেয়।
৬. সবশেষে বিশ্বজাহানের প্রভু সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরব দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমকে পাঠান । ইতিপূর্বে বিভিন্ন নবীকে তিনি যে দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলেন মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপরও সেই একই দায়িত্ব অর্পণ করেন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে পূর্বের নবীদের পথভ্রষ্ট উম্মতদেরকেও তিনি আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানান। সবাইকে সঠিক কর্মনীতি ও সঠিক পথ গ্রহণের দাওয়াত দেন। সবার কাছে নতুন করে আল্লাহর হিদায়াত পৌছিয়ে দেয়া এবং এই দাওয়াত ও হিদায়াত গ্রহণকারীদেরকে এমন একটি উম্মতে পরিণত করাই ছিলো তাঁর কাজ, যারা একদিকে আল্লাহর হিদায়াতের ওপর নিজেদের জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করবে এবং অন্যদিকে সমগ্র দুনিয়ার সংশোধন ও সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালাবে। এই দাওয়াত ও হিদায়াতের কিতাব হচ্ছে এই কুরআন। মুহাম্মদ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আল্লাহ এই কিতাবটি অবতীর্ণ করেন। [তাফহীমুল কুরআনের ভুমিকা থেকে গৃহীত।]
২. জীবন সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভংগি
কুরআন এ বিশ্বে মানুষের সঠিক মর্যাদা ও জীবন সম্পর্কে তার পূর্ণাংগ দৃষ্টিভংগি একটি আয়াতেই বলে দিয়েছেঃ
“প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের প্রাণ ও ধনসম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং মারে ও মরে। তাদের প্রতি তাওরাত, ইনজীল ও কুরআনে [জান্নাতের ওয়াদা] আল্লাহর জিম্মায় একটি পাকাপোক্ত ওয়াদা বিশেষ। আর আল্লাহর চাইতে বেশী নিজের ওয়াদা পূরণকারী আর কে আছে? কাজেই তোমরা আল্লাহর সাথে যে কেনাবেচা করেছো সেজন্য সুসংবাদ গ্রহণ করো। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।” [সূরা আততওবাঃ ১১১]
আল্লাহ ও বান্দাহর মধ্যে ঈমানের যে ব্যাপারটা স্থিরকৃত হয় তাকে কেনাবেচা বলে এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এর মানে হচ্ছে, ঈমান শুধুমাত্র একটা অতি প্রাকৃত আকীদা বিশ্বাস নয়, বরং এটা একটা চুক্তি। এ চুক্তির প্রেক্ষিতে বান্দাহ তার নিজের প্রাণ ও নিজের ধনসম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেয়। আর এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ওয়াদা কবুল করে নেয় যে, পরবর্তী জীবনে তিনি তাকে জান্নাত দান করবেন। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু অনুধাবন করার জন্য সর্বপ্রথম কেনাবেচার তাৎপর্য ও স্বরূপ কি তা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।
নিরেট সত্যের আলোকে বিচার করলে বলা যায়, মানুষের ধনপ্রাণের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। কারণ, তিনিই তার এবং তার কাছে যা কিছু আছে সব জিনিসের স্রষ্টা। সে যা কিছু ভোগ ও ব্যবহার করছে তাও তিনিও তাকে দিয়েছেন। কাজেই এদিক দিয়ে তো কেনাবেচার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। মানুষের এমন কিছু নেই, যা সে বিক্রি করবে। আবার কোনো জিনিস আল্লাহর মালিকানার বাইরেও নেই, যা তিনি কিনবেন। কিন্তু মানুষেল মধ্যে এমন একটি আছে, যা আল্লাহ পুরোপুরি মানুষের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছেন। সেটি হচ্ছে তার ইখতিয়ার অর্থাৎ নিজের স্বাধীন নির্বাচন ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি [Free will and freedom of choice] । এ ইখতিয়ারের কারণে অবশ্যি প্রকৃত সত্যের কোনো পরিবর্তন হয়না। কিন্তু মানুষ এ মর্মে স্বাধীনতা লাভ করে যে, সে চাইলে প্রকৃত সত্যকে মেনে নিতে পারে এবং চাইলে তা অস্বীকার করতে পারে। অন্য কথায়, এ ইখতিয়ারের মানে এ নয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রাণের, নিজের বুদ্ধিপৃত্তি ও শারীরিক শক্তির এবং দুনিয়ায় সে যে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা লাভ করেছে, তার মালিক হয়ে গেছে। এ সংগে এ জিনিসগুলো সে যেভাবে চাইবে সেভাবে ব্যবহার করার অধিকার লাভ করেছে, একথাও ঠিক নয়। বরং এর অর্থ কেবল এতোটুকুই যে, তাকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার জোর জবরদস্তি ছাড়াই সে নিজেই নিজের সত্তার ও নিজের প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর আল্লাহর মালিকানা ইচ্ছা করলে স্বীকার করতে পারে আবার ইচ্ছা করলে নিজেই নিজের মালিক হয়ে যেতে পারে এবং নিজেই একথা মনে করতে পারে যে, সে আল্লাহ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের ইখতিয়ার তথা স্বাধীন কর্মক্ষমতার সীমানার মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করার অধিকার রাখে। এখানেই কেনাবেচার প্রশ্নটা দেখা দেয়। আসলে এ কেনাবেচা এ অর্থে নয় যে, মানুষের একটি জিনিস আল্লাহ কিনতে চান। বরং প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যে জিনিসটি আল্লাহর মালিকানাধীন, যাকে তিনি আমানত হিসেবে মানুষের হাতে সোপর্দ করেছেন এবং যে ব্যাপারে তিনি মানুষের কাছে দাবী করেন, আমার জিনিসকে তুমি স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে [বাধ্য হয়ে নয়] আমার জিনিস বলে মেনে নাও এবং সারা জীবন স্বাধীন মালিকের মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে নয় বরং আমানতদার হিসেবে তা ব্যবহার করার বিষয়টি গ্রহণ করে নাও। এ সংগে খেয়ানত করার যে স্বাধীনতা তোমাকে দিয়েছি তা তুমি নিজেই প্রত্যাহার করো। এভাবে যদি তুমি দুনিয়ার বর্তমান অস্থায়ী জীবনে নিজের স্বাধীনতাকে [যা তোমার অর্জিত নয় বরং আমার দেয়া] আমার হাতে বিক্রি করে দাও তাহলে আমি পরবর্তী চিরন্তন জীবনে এর মূল্য জান্নাতের আকারে তোমাকে দান করবো। সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কেনাবেচার এ চুক্তি সম্পাদন করে সে মুমিন। ঈমান আসলে এ কেনাবেচার আর এক নাম। আর সে ব্যক্তি এটা অস্বীকার করবে অথবা অঙ্গীকার করার পরও এমন আচরণ করবে যা কেবলমাত্র কেনাবেচা না করার অবস্থায় করা যেতে পারে, সে কাফের। আসলে এ কেনাবেচাকে পাস কাটিয়ে চলার পরিভাষিক নাম কুফরী।
কেনাবেচার এ তাৎপর্য ও স্বরূপটি অনুধাবন করার পর এবার তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করা যাকঃ
এক. এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ মানুষকে দুটি বড় বড় পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। প্রথম পরীক্ষাটি হচ্ছে, তাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেবার পর সে মালিককে মালিক মনে করার এবং বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহের পর্যায়ে নেমে না আসার মতো সৎ আচরণ করে কিনা? দ্বিতীয়টি হচ্ছে, নিজের প্রভু ও মালিক আল্লাহর কাছ থেকে আজ নগদ যে মূল্য পাওয়া যাচ্ছেনা বরং মরার পর পরকালীন জীবনে যে মূল্য আদায় করার ওয়াদা তাঁর পক্ষ থেকে করা হয়েছে, তার বিনিময়ে নিজের আজকের স্বাধীনতা ও তার যাবতীয় স্বাদ বিক্রি করতে স্বেচ্ছায় ও আগ্রহে রাজী হয়ে যাবার মত আস্থা তাঁর প্রতি আছে কিনা।
দুই. যে ফিকহের আইনের ভিত্তিতে দুনিয়ায় ইসলামী সমাজ গঠিত হয় তার দৃষ্টিতে ঈমান শুধুমাত্র কতিপয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির নাম। ও স্বীকৃতির পর নিজের স্বীকৃতি ও অংগীকারের ক্ষেত্রে মিথ্যুক হবার সুস্পষ্ট প্রমাণ না পওয়া পর্যন্ত শরীয়াতের কোনো বিচারক কাউকে অমুমিন বা ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত ঘোষণা করতে পারেনা। কিন্তু আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্য ঈমানের তাৎপর্য ও স্বরূপ হচ্ছে, বান্দাহ তার চিন্তা ও কর্ম উভয়ের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ক্ষমতা আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দিবে এবং নিজের মালিকানার দাবী পুরোপুরি তাঁর সপক্ষে প্রত্যাহার করবে। কাজেই যদি কোনো ব্যক্তি ইসলামের কালেমার স্বীকৃতি দেয় এবং নামায রোযা ইত্যাদির বিধানও মেনে চলে, কিন্তু নিজেকে নিজের দেহ ও প্রাণের, নিজের মন, মস্তিষ্ক ও শারীরিক শক্তির, নিজের ধনসম্পদ, উপায়, উপকরণ ইত্যাদির এবং নিজের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণাধীন সমস্ত জিনিসের মালিক মনে করে এবং সেগুলোকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করার স্বাধীনতা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে, তাহলে হয়তো দুনিয়ায় তাকে মুমিন মনে করা হবে, কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অবশ্যি অমুমিন গণ্য হবে। কারণ কুরআনের দৃষ্টিতে কেনাবেচার ব্যাপারকে ঈমানের আসল তাৎপর্য ও স্বরূপ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ সে আল্লাহর সাথে আদতে কোনো কেনাবেচার কাজই করেনি। যেখানে আল্লাহ চান সেখানে ধনপ্রাণ নিয়োগ না করা এবং যেখানে তিনি চান না সেখানে ধনপ্রাণ নিয়োগ ও ব্যবহা করা এ দুটি কার্যধারাই চূড়ান্তভাবে ফায়সালা করে দেয় যে, ঈমানের দাবীদার ব্যক্তি তার ধনপ্রাণ আল্লাহর হাতে বিক্রি করেইনি অথবা বিক্রির চুক্তি করার পরও সে বিক্রি করা জিনিসকে যথারীতি নিজের জিনিস মনে করছে।
তিন. ঈমানের এ তাৎপর্য ও স্বরূপ ইসলামী জীবনাচরণকে কাফেরী জীবনাচরণ থেকে সম্পূর্ন আলাদা করে দেয়। যে মুসলিম ব্যক্তি সঠিক অর্থে আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে সে জীবনের সকল বিভাগে আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করে। তার আচরণে কোথাও স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী দৃষ্টিভংগী প্রকাশ ঘটতে পারেনা। তবে কোনো সময় সাময়িকভাবে সে গাফলতির শিকার হতে পারে এবং আল্লাহর সাথে নিজের কেনাবেচার চুক্তির কথা ভুলে গিয়ে স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী ভূমিকা অবলম্বন করাও তার পক্ষে সম্ভ। এটা অবশ্যি ভিন্ন ব্যাপার। অনুরূপভাবে ঈমানদারদের সমন্বয় গঠিত কোনো দল বা সমাজ সমষ্ঠিগতভাবেও আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর শরয়ী আইনের বিধিনিষেধ মুক্ত হয়ে কোনো নীতি পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক পদ্ধতি এবং কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক আচরণ অবলম্বন করতে পারেনা। কোনো সাময়িক গাফলতির কারছে যদি সেটা অবলম্বন করেও থাকে তাহলে যখনই সে এ ব্যাপারে সতেচন হবে তখনই স্বাধীন ও স্বৈরাচারী আচরণ ত্যাগ করে পুনরায় বন্দেগীর আচরণ করতে থাকবে। আল্লাহর আনুগত্য মুক্ত হয়ে কাজ করা এবং নিজের ও নিজের সাথে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে নিজে নিজেই কি করবো না করবো, সিদ্ধান্ত নেয়া অবশ্যি একটি কুফরী জীবনাচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাদের জীবন যাপন পদ্ধতি এরকম তারা “মুসলমান” নামে আখ্যায়িত হোক বা “অমুসলিম” নামে তাতে কিছু যায় আসেনা।
চার. এ কেনাবেচার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহর যে ইচ্ছার আনুগত্য মানুষের জন্য অপরিহার্য হয় তা মানুষের নিজের প্রস্তাবিত বা উদ্ভাবিত নয় বরং আল্লাহ নিজে যেমন ব্যক্ত করেন তেমন। নিজে নিজেই কোনো জিনিসকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ধরে নেয়া এবং তার আনুগত্য করতে থাকা মূলত আল্লাহর ইচ্ছার নয় বরং নিজেরই ইচ্ছার আনুগত্য করার শামিল। এটি এ কেনাবেচার চুক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। যে ব্যক্তি ও দল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর হিদায়াত থেকে নিজের সমগ্র জীবনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে একমাত্র তাকেই আল্লাহর সাথে কৃত নিজের কেনাবেচার চুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হবে।
এ হচ্ছে এ কেনাবেচার অন্তর্নিহিত বিষয়। এ বিষয়টি অনুধাবন করার পর এ কেনাবেচার ক্ষেত্রে বর্তমান পার্থিব জীবনের অবসানের পর মূল্য [অর্থাৎ জান্নাত] দেবার কথা বলা হয়েছে কেন তাও আপনা আপনিই বুঝে আসে। “বিক্রেতা নিজের প্রাণ ও ধনসম্পদ আল্লাহর হাতে বিক্রি করে দেবে” কেবলমাত্র এ অংগীকারের বিনিময়েই যে জন্নাত পাওয়া যাবে তা নয়। বরং “বিক্রেতা নিজের পার্থিব জীবনে এ বিক্রি করা জিনিসের ওপর নিজের স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার প্রত্যাহার করবে এবং আল্লাহ প্রদত্ত তৎপরতার বিনিময়েই জান্নাত প্রাপ্তি নিশ্চিত হতে পারে। সুতরাং বিক্রেতার পার্থিব জীবনকালে শেষ হবার পর যখন প্রমাণিত হবে যে, কেনাবেচার চুক্তি করার পর সে নিজের পার্থিব জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত চুক্তির শর্তসমূহ পুরোপুরি মেনে চলেছে একমাত্র তখনই এ বিক্রি সম্পূর্ণ হবে। এর আগে পর্যন্ত ইনসাফের দৃষ্টিতে সে মূল্য পাওয়ার অধিকারী হতে পারেনা।
৩. দীন এবং আল্লাহর আইন
“ব্যভিচারী নারী ও পুরুষ প্রত্যেককে এক’শ কোড়া মারো। তাদের উপর আল্লাহর আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে তোমাদের মনে যেনো অনুকম্পা না জাগে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখো।” [সূরা নুরঃ ২]
এ আয়াতে প্রথম উল্লেখযোগ্য জিনিসটি হচ্ছে, এখানে ফৌজদারী আইনকে “আল্লাহর দীন” বলা হচ্ছে। এথেকে জানা যায, শুধুমাত্র নামায, রোযা হজ্জ ও যাকাতই দীন নয়, বরং দেশের আইনও দীন। দীন প্রতিষ্ঠার অর্থ শুধু নামায প্রতিষ্ঠা নয় বরং আল্লাহর আইন ও শরীয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও। যেখানে এসব প্রতিষ্ঠিত হয়না যেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলেও অসম্পূর্ণ দীন প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে বলে মনে করা হবে। যেখানে একে বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অবলম্বন করা হয় সেখানে অন্য কিছু নয় বরং আল্লাহর দীনকেই প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।
৪. রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
“আর হে নবী দোয়া করোঃ আমার পরওয়ারদিগার! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে যাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো। এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত শক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও।” [সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৮০]
অর্থাৎ এ আয়াতে আল্লাহ নবীকে এভাবে প্রার্থনা করতে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, তুমি বলো, হে আল্লাহ! তুমি নিজেই আমাকে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ব্যবহার করে আমি দুনিয়ার বিকৃত জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারি, অশ্লীলতা ও পাপের সংলাব রুখে দাঁড়াতে পারি এবং তোমার ন্যায় বিধান জারি করতে সক্ষম হই। হাসান বসরী ও কাতাদাহ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীরের ন্যায় মহান তাফসীরকারগণও এ ব্যাখ্যাই গ্রহণ করেছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস থেকেও এরি সমর্থন পাওয়া যায়ঃ
“আল্লাহ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে এমনসব জিনিসের উচ্ছেদ ঘটান কুরআনের মাধ্যমে যেগুলোর উচ্ছেদ ঘটাননা।”
এথেকে জানা যায়, ইসলাম দুনিয়ায় যে সংশোধন চায় তা শুধুমাত্র ওয়ায নসীহতের মাধ্যমে হতে পারেনা বরং তাকে কার্যকর করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতাও প্রয়োজন হয়। তারপর আল্লাহ নিজেই যখন তাঁর নবীকে এ দোয়া শিখিয়েছেন তখন এথেকে একথাও প্রমাণ হয় যে, দীন প্রতিষ্ঠা ও শরীয়তী আইন প্রবর্তন এবং আল্লাহ প্রদত্ত দন্ডবিধি জারী করার জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা হাসিল করার প্রত্যাশা করা এবং এজন্য প্রচেষ্টা চালানো শুধু জায়েযই নয় বরং কাংখিত ও প্রশংসিতও এবং অন্যদিকে যারা এ প্রচেষ্টা ও প্রত্যাশাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা ও দুনিয়াদারী বলে আখ্যায়িত করে তারা ভুলের মধ্যে অবস্থান করছে। কোনো ব্যক্তি যদি নিজের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চায় তাহলে তাকে বৈষয়িক স্বার্থ পূজা বলা যায়। কিন্তু কেউ আল্লাহর দীনের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা লাভ করতে চাইলে ও চাওয়া বৈষয়িক স্বার্থ পূজা নয় বরং আল্লাহর আনুগত্যের প্রত্যক্ষ দাবী।
এ জিনিসটাই হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের জীবনাদর্শে আমরা দেখতে পাই। তিনি যে নৈতিক ও সংস্কার বিপ্লবের আহবায়ক ছিলেন কর্তৃত্ব ছিলো তার জন্য অপরিহার্য। যখন পরিবেশ পরিস্থিতি অনুকূল দেখা দিলো তখন তিনি সে সুযোগ গ্রহণ করে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিষয়টিই কুরআন মজীদে চিত্রিত হয়েছে এভাবেঃ
“বাদশাহ বললো, “তাকে আমার কাছে আনো, আমি তাকে একান্তভাবে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করে নেবো।” ইউসূফ যখন তার সাথে আলাপ করলো, সে বললো, “এখন আপনি আমাদের এখানে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী এবং আপনার আমানতদারীর ওপর পূর্ণ ভরসা আছে।” ইউসূফ বললো, “দেশের অর্থসম্পদ আমার হতে সোপর্দ করুন। আমি সংরক্ষণকারী এবং জ্ঞানও রাখি।” [সূরা ইউসূফঃ ৫৪-৫৫]
এর আগে যেসব আলোচনা হয়েছে তার আলোকে পর্যালোচনা করলে একথা পরিষ্কার বুঝা যাবে যে, কোন পদলোভী ব্যক্তি বাদাশাহর ইশারা পাওয়ার সাথে সাথেই যেমন কোনো পদলাভের জন্য আবেদন করে বসে এটি তেমনি ধরনের কোনো চাকরির আবেদন ছিলোনা। আসলে এটি ছিলো একটি বিপ্লবের দরজা খোলার জন্য সর্বশেষ আঘাত। হযরত ইউসূফ আলাইহিস সালামের নৈতিক শক্তির বলে বিগত দশ বারো বছরের মধ্যে ও বিপ্লব ক্রমবিকাশ লাভ করে আত্মপ্রকাশ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলো এবং এখন এর দরজা খোলার জন্য শুধুমাত্র একটি হালকা আঘাতের প্রয়োজন ছিলো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম একটি সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পরীক্ষার অংগন অতিক্রম করে আসছিলেন। কোনো অজ্ঞান স্থানে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। বরং বাদশাহ থেকে শুরু করে মিসরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাই এ সম্পর্কে অবগত ছিলো। এসব পীক্ষার মাধ্যমে তিনি একথা প্রমান করে দিয়েছিলেন যে, আমানতদারী, সততা ধৈর্য, সংযম, উদারতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতার ক্ষেত্রে অন্তত সমকালীন লোকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর ব্যক্তিত্বের ও গুণগুলো এমনভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিলো যে, এগুলো অস্বীকার করার সাধ্য কারোর ছিলোনা। দেশবাসী মুখে এগুলোর পক্ষে সাক্ষ দিয়েছিলো। তাদের হৃদয় এগুলোর দ্বারা বিজিত হয়েছিলো। বাদশাহ নিজেই এগুলোর সামনে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। এখন তাঁর “সংরক্ষণকারী” ও “জ্ঞানী” হওয়া শুধুমাত্র একটি দাবীর পর্যায়ভুক্ত ছিলোনা বরং এটি ছিলো একটি প্রমাণিত ঘটনা। সবাই এটা বিশ্বাস করতো। এখন শুধু রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা কর্তৃত্ব পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষেত্রে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্মতিটুকুই বাকি ছিলো। বাদশাহ, তাঁর মন্ত্রীপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ একথা ভালোভাবেই জেনেছিলেন যে, তিনি ছাড়া এ রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার মতো আর দ্বিতীয় কোনো যোগ্য ব্যক্তিত্বই নেই। কাজেই নিজের এ উক্তির সাহায্যে তিনি এ সম্মতিটুকুরই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন মাত্র। তাঁর কন্ঠে এ দাবীটুকু উচ্চারিত হবার সাথে সাথেই বাদশাহ ও তাঁর রাজ পরিষদ যেভাবে দুহাত বাড়িয়ে তা গ্রহণ করে নিয়েছেন তা একথাই প্রমাণ করে যে, ফল পুরোপুরি পেকে গিয়েছিলো এবং তা ঝরে পড়ার জন্য শুধুমাত্র একটা ইশারার অপেক্ষায় ছিলো। [তালমূদের বর্ণনামতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করার ফায়সালাটি কেবল বাদশাহ একাই করেননি। বরং সমগ্র রাজপরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর পক্ষে রায় দিয়েছিলো।
৫. সার্বভৌমত্ব ও খিলাফতের ধারণা
ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট। আল্লাহ এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা এবং তিনি সর্বোচ্চ শাসক। সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব কেবল তারই। মানুষের মর্যাদা হলো, সে সর্বোচ্চ শাসকের প্রতিনিধি এবং তার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হবে সর্বোচ্চ শাসকের আইনের অনুগামী। প্রতিনিধির কাজ হলো, সর্বোচ্চ শাসকের আইনকে তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য অনুযায়ী কার্যকর করা এবং তাঁর নির্দেশিত পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনা করা। কুরআনের ভাষ্য দেখুনঃ
ক. “হে জেলখানার সাথীরা! তোমরা নিজেরাই ভেবে দিখো, ভিন্ন ভিন্ন বহু সংখ্যক রব ভালো, না এক আল্লাহ যিনি সবার ওপর বিজয়ী। তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের গোলামী করছো তারা শুধুমাত্র কতকগুলো নাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছো, আল্লাহ এগুলোর পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। শাসন কর্তৃত্ব আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই। তাঁর হুকুম হলো, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারোর দাসত্ব করবেনা। এটিই সরল সঠিক জীবন পদ্ধতি, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানেনা।” [সূরা ইউসূফঃ ৩৯-৪০]
এটি ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাষণের একটি অংশ। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাওহীদের ব্যাপারে এটি সর্বোত্তম ভাষণসমূহের একটি। এতে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম শ্রোতাদের সামনে দীনের এমন একটি সুচনা বিন্দু তুলে ধরেন যেখানে থেকে সত্যপন্থী ও মিথ্যাবন্থীদের পথ পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেছে। অর্থাৎ তিনি তাওহীদ শিরকের পার্থক্য তুলে ধরেছেন। আবার এ পার্থক্যকে এমন যুক্তিসংগত পদ্ধতিতে সুস্পষ্ট করেছেন, যার ফলে সাধারণ বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন যেকোনো ব্যক্তিই তা অনুভব না করে পারেননা। বিশেষ করে সে সময় যাদেরকে সম্বোধন করে তিনি একথা বলছিলেন তাদের মন মস্তিষ্কে তীরের মতো একথা গেঁথে গিয়ে থাকবে। কারণ তার ছিলো কর্মজীবি গোলাম। নিজেদের মনের গভীর তারা একথা ভালোভাবে অনুভব করতো যে, একজন প্রভুর গোলাম হওয়া ভালো, না একাধিক প্রভুর গোলাম হওয়া? আর সারা দুনিয়ার একক প্রভু যিনি, তার দাসত্ব করা ভালো, না তার দাসদের দাসত্ব করা? তারপর তিনি একথাও বলেননা যে, তোমাদের ধর্ম ত্যাগ করো এবং আমার দীন গ্রহণ করো। বরং চমৎকার কৌশল বলছেন, আল্লাহর কতোবড় মেহেরবানী, তিনি আমাদের তাঁর ছাড়া আর কারো দাস হিসেবে পয়দা করেননি , অথচ অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা বরং অনর্থক নিজেরাই মনগড়া প্রভু তৈরী করে তাদের পূজা ও দাসত্ব করছে। তারপর তিনি শ্রোতাদের অনুসৃত ধর্মের সমালোচনাও করেছেন, কিন্তু অত্যন্ত যুক্তিসংগতভাবে এবং কোনো প্রকার মনোকষ্ট না দিয়ে। তিনি এতোটুকু বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন যে, এই যেসব মাবুদ যাদের কাউকে তোমরা অন্নদাতা, কাউকে অনুগ্রহদাতা ও করুণানিধি, কাউকে ভূমির অধিপতি এবং কাউকে ধনসম্পদের মালিক অথবা স্বাস্থ্য ও রোগের একচ্ছত্র অধিপতি ও পরিচালক ইত্যাদি বলে থাকো- এরা নিছক কিছু অন্তসারশূন্য নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নামগুলোর পিছনে কোনো সত্যিকার অন্নদাতা, অনুগ্রহকারী, তোমরাও বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক বলে স্বীকার করে থাকো। তিনি এসব মালিক ও প্রভূদের কাউকে মালিকানা, প্রভুত্ব ও উপাস্য হবার ছাড়পত্র দেননি। তিনি সার্বভৌমত্ব ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় অধিকার ও ক্ষমতা নিজের জন্য নির্ধারিত করে রেখেছেন এবং তাঁরই আদেশ হচ্ছে, তোমরা তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবেনা।
খ. “আর ফেরাউন বললো, হে সভাসদবর্গ! আমি তো আমাকে ছাড়া তোমাদের আর কোনো ইলাহ আছে বলে জানিনা।” [সূরা আল কাসাসঃ ৩৮]
এ উক্তির মাধ্যমে ফেরাউন যে বক্তব্য পেশ করেছে তার অর্থ এ ছিলোনা এবং তা হতেও পারতোনা যে, আমিই তোমাদের এবং পৃথিবী ও আকাশের স্রষ্টা। কারণ কেবলমাত্র কোনো পাগলের মুখ দিয়েই এমন কথা বের হতে পারতো। অনুরূপভাবে এর অর্থ এও ছিলোনা এবং হতে পারতোনা যে, আমি ছাড়া তোমাদের আর কোনো মাবুদ নেই। কারণ মিসরবাসীরা বহু দেবতার পূজা করতো এবং স্বয়ং ফেরাউনকেই যেভাবে উপাস্যের মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো তাও শুধুমাত্র এই ছিলো যে, তাকে সূর্য দেবতার অবতার হিসেবে স্বীকার করা হতো। সবচেয়ে বড় সাক্ষী কুরআন মজীদ নিজেই। কুরআনে বলা হয়েছে ফেরাউন নিজে বহু দেবতার পূজারী ছিলো।
এদিক দিয়ে চিন্তা করলে যেসব রাষ্ট্র আল্লাহর নবী প্রদত্ত শরীয়তের অধীনতা প্রত্যাখ্যান করে নিজেদের তথাকথিত রাজনৈতিক ও আইনগত সার্বভৌমত্বের দাবীদার, ফেরাউনের অবস্থাক তাদের থেকে ভিন্নতর ছিলোনা। তারা আইনের উৎস এবং আদেশ নিষেদের কর্তা হিসেবে অন্য কোনো বাদশাকে মানুক অথবা জাতির ইচ্ছার আনুগত্য করুক, যতক্ষণ তারা এরূপ নীতি অবলম্বন করে চলবে যে, দেশে আল্লাহ ও তার রসূলের নয় বরং আমাদের হুকুম চলবে, ততক্ষণ তাদের ও ফেরাউনের নীতি ও ভূমিকার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকবেনা। এটা ভিন্ন কথা যে, অবুঝ লোকেরা একদিকে ফেরাউনকে অভিসম্পাত করতে থাকে, অন্যদিকে ফেরাউন রীতিনীতির অনুসারী এসব শাসককে বৈধতার ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্যের জ্ঞান রাখে, সে শব্দ ও পরিভাষা নয়, অর্থ ও প্রাণশক্তি দেখবে। ফেরাউন নিজের জন্য ইলাহ শব্দ ব্যবহার করেছিলো এবং এরা সেই একই অর্থে “সার্বভৌমত্বের” পরিভাষা ব্যবহার করছে।
“তিনি হলেন সেই সত্ত্বা, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের মালিক। তিনি কাউকেও পুত্র বানাননা। তাঁর রাজত্বে কোনো অংশীদার নেই। প্রতিটি জিনিস তিনি সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর একটি তাকদীর নির্ধারণ করেছেন।” [সূরা আল ফুরকানঃ ২]
মূলে মুলক’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি বাদশাহী, রাজত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের [Sovereignty] অর্থে বলা হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহই এ বিশ্ব জাহানের সর্বময় কর্তৃত্বের মালিক এবং তাঁর শাসন ক্ষমতায় কারো সামান্যতমও অংশ নেই। একথার স্বতঃস্ফূর্ত ও অনিবার্য ফল এই যে, তাহলে তিনি ছাড়া আর কোনো মা’বুদ নেই। কারণ, মানুষ যাকেই মা’বুদে পরিণত করে একথা মনে করেই করে যে, তার কাছে কোনো শক্তি আছে, যে কারণে সে আমাদের উপকার বা ক্ষতি করতে পারে এবং আমাদের ভাগ্যের ওপর ভালো মন্দ প্রভাব ফেলতে পারে। শক্তিহীন ও প্রভাবহীন সত্তাদেরকে আশ্রয়স্থল করতে কোনো একান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও রাজি হতে পারেনা। এখন যদি একথা জানা যায় যে, মহান আল্লাহ ছাড়া এ বিশ্ব জাহানে আর কোনো শক্তি নেই তাহলে বিনয় নম্রতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করার জন্য কোনো মাথা তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে ঝুঁকবেনা, কোনো হাতও তাঁর ছাড়া আর কারো সামনে নজরানা পেশ করার জন্য এগিয়ে যাবেনা, কোনো কণ্ঠও তাঁর ছাড়া আর কারো প্রশংসাগীতি গাইবেনা বা কারো কাছে প্রার্থনা করবেনা ও ভিক্ষা চাইবেনা এবং দুনিয়ার কোনো নিরেট মূর্খ অজ্ঞ ব্যক্তিও কখনো নিজের প্রকৃত ইলাহ ছাড়া আর কারো অনুগত্য ও দাসত্ব করার মতো বোকামী করবেনা অথবা কারো স্বয়ংসম্পূর্ণ শাসনাধিকার মেনে নেবেনা। “আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই এবং তাঁরই জন্য” ওপরের এ বাক্যাংশটি থেকে এ বিষয়বস্তুটি আরো বেশী শক্তি অর্জন করে।
ঘ. “ আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমাদের অন্তরে যা কিছু আছে তা প্রকাশ কারো কিংবা গোপন রাখো সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ সেগুলোর হিসেবে নেবেন। অতপর তিনি যাকে চাইবেন মাফ করে দেবেন, আর যাকে চাইবেন শাস্তি দেবেন, তিনি সবকিছু কারতে সক্ষম।” [সূরা আল বাকারাঃ ২৮৪]
এটি হচ্ছে দীনের প্রথম বুনিয়াদ। আল্লাহ এই পৃথিবীর ও আকাশ সমূহের মালিক এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁর একক মালিকানাধীন, প্রকৃতপক্ষে এই মৌলিক সত্যের ভিত্তিতেই মানুষের জন্য আল্লাহর সামনে আনুগত্যের শির নতো করা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো কর্মপদ্ধতি বৈধ ও সঠিক হতে পারেনা।
এই বাক্যটিতে আরো দুটি কথা বলা হয়েছে। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর কাছে দায়ী হবে এবং এককভাবে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। দুই, পৃথিবী ও আকাশের যে একচ্ছত্র অধিপতির কাছে মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তিনি অদৃশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞান রাখেন। এমনকি লোকদের গোপন সংকল্প এবং তাদের মনের সংগোপনে যেসব চিন্তা জাগে সেগুলিও তাঁর কাছে গোপন নয়।
এটি আল্লাহর নিরংকুশ ক্ষমতারই একটি বর্ণনা। তাঁর ওপর কোনো আইনের বাঁধন নেই। কোনো বিশেষ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য তিনি বাধ্য নন। বরং তিনি সর্বময় ও একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী। শাস্তি দেয়ার এবং মাফ করার পূর্ণ ইখতিয়ার তাঁর রয়েছে।
কুরআনে ঈসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য উল্লেখ হয়েছে এভাবেঃ
ঙ. “আমি সেই শিক্ষা ও হিদায়াতের সত্যতা ঘোষণা করার জন্য এসেছি, যা বর্তমানে আমার যুগে তাওরাতে আছে। আর তোমাদের জন্য যেসব জিনিস হারাম ছিলো তার কতকগুলি হালাল করার জন্য আমি এসেছি। দেখো, তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে আমি নিশানী নিয়ে এসেছি। কাজেই আল্লাহকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য করো। আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কাজেই তোমরা তাঁর দাসত্ব করো। এটিই সোজাপথ।” [সূরা আল ইমরানঃ ৫০-৫১]
এথেকে জানা গেলো অন্যান্য সকল নবীর মতো হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতেরও তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু ছিলোঃ
এক, সার্বভৌম কর্তৃত্ব, যার দাসত্ব ও বন্দেগী করতে হবে এবং যার প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে নৈতিক ও তামদ্দুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্ধারিত বলে স্বীকার করতে হবে।
দুই, ঐ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর প্রতিনিধি হিসেবে নবীর নির্দেশের আনুগত্য করতে হবে।
তিন, মানুষের জীবনকে হালাল ও হারাম এবং বৈধতা ও অবৈধতার বিধিনিষেধে আবদ্ধকারী আইন ও বিধিবিধান একমাত্র আল্লাহ দান করবেন। অন্যদের চাপানো সমস্ত আইন ও বিধি নিষেধ বাতিল করতে হবে।
কাজেই হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যান্য নবীর মিশনের মধ্যে আসলে সামান্যতম পার্থক্যও নেই। যারা বিভিন্ন নবীর মিশন বিভিন্ন বলে গণ্য করেছেন এবং তাদের মিশনের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য দেছিয়েছেন, তারা মারাত্মক ভুল করেছেন। বিশ্বজাহানের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রজাদের জন্যে যে ব্যক্তিই নিযুক্ত হয়ে আসবেন তাঁর আসার উদ্দেশ্য এছাড়া আর দ্বিতীয় কিছুই হতে পারেনা যে, তিনি প্রজাদেরকে অবাধ্যতা, স্বেচ্ছাচরিতা ও শির্ক [অর্থাৎ সার্বভৌম প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিশ্বজাহানের একচ্ছত্র মালিক ও প্রভু আল্লাহর সাথে আর কাউকে অংশীদার করা এবং নিজের বিশ্বস্ততা ও ইবাদাত বন্দেগীকে তাদের মধ্যে বিভক্ত করে দেয়া] থেকে বিরত রাখবেন এবং আসল ও প্রকৃত মালিকের নির্ভেজাল আনুগত্য, দাসত্ব, পূজা, আরাধনা ও ইবাদত করার আহবান জানাবেন।
দুঃখের বিষয়, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মিশনকে উপরে কুরআনে যেমন সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, বর্তমান ইনজীলে তেমনটি করা হয়নি। তবুও উপরে যে তিনটি মৌলিক বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে তা বিক্ষিপ্তভাবে ইশারা ইংগিতের আকারে হলেও বর্তমানে ইনজীলে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একমাত্র আল্লাহর বন্দেগীর দাওয়াত দিয়েছিলেন, একথা ইনজীলের নিন্মোক্ত ইংগিত থেকে সুস্পষ্ট হয়ঃ
তোমার ইশ্বর প্রভুকে প্রতিপাত [সিজদা] করো এবং একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো। [মথি ৪ : ১০]
তিনি যে কেবল এরি দাওয়াত দিয়েছিলেন তা নয়, বরং তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যেই ছিলো, আকাশ রাজ্যে যেমন সার্বভৌম ক্ষমতাসম্পন্ন আল্লাহর নিরংকুশ আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, অনুরূপভাবে পৃথিবীতেও একমাত্র তাঁরই শরিয়াত আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।
তোমার রাজ্য আসুক। তোমার ইচ্ছা যেমন আকাশে পূর্ণ হয় তেমনি পৃথিবীতেও পূর্ণ হোক। [মথি ৬:১০]
তাছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম নিজেকে নবী ও আসমানী রাজত্বের প্রতিনিধি হিসেবেই পেশ করতেন এবং এ হিসেবেই লোকদেরকে নিজের আনুগত্য করার দাওয়াত দিতেন। তাঁর ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্যগুলো থেকে জানা যায়, তিনি নিজের জন্মভূমি ‘নাসেরা’ [নাজারাথ] তে নিজের দাওয়াতের সূচনা করলে তাঁর আত্মীয় স্বজন ও শহরবাসীরাই তাঁর বিরোধীতায় নেমে পড়ে। এ সম্পর্কে মথি, মার্ক ও লুক একযোগে বর্ণনা করেছেন যে, ‘নবী তাঁর স্বদেশে জনপ্রিয় হননা।” তারপর জেরুসালেমে যখন তাঁর হত্যাক চক্রান্ত চলতে লাগলো এবং লোকেরা তাঁকে অন্য কোথাও চলে যাবার পরামর্শ দিলো তখন তিনি জবাব দিলেনঃ “নবী জেরুসালেমের বাইরে মৃত্যুবরণ করবে, এটা সম্ভব নয়” [লুক ১৩:৩৩] শেষবার যখন তিনি জেরুসালেম প্রবেশ করছিলেন তখন তাঁর শিষ্যবর্গ উচ্চস্বরে বলতে লাগলোঃ “ধন্য সেই রাজা যিনি প্রভুর নামে আসছেন।” একথায় ইহুদী আলেমরা অসন্তুষ্ট হলেন এবং তারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বললেনঃ “আপনার শিষ্যদের মুখ বন্ধ করুন।” হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেনঃ “ওরা যদি মুখ বন্ধ করে তাহলে পাথরগুলি চিৎকার করে উঠবে।” [লুক ১৯: ৩৮-৪০]
আর একবার তিনি বললেনঃ
হে শ্রমজীবিরা! হে ভারবহনে পিষ্ট লোকেরা! আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের বিশ্রাম দান করবো। আমার জোয়াল তোমাদের কাঁধে উঠিয়ে নাও।——– আমার জোয়াল সহজে বহনীয় এবং আমার বোঝা হালকা। [মথি ১১: ১৮-৩০]
এছাড়া হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম মানব রচিত আইনের পরিবর্তে আল্লাহ প্রদত্ত আইনের আনুগত্য করতে চাইতেন একথাও মথি ও মার্কের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। তাদের বর্ণনার সার নির্যাস হচ্ছেঃ ইহুদী আলেমগণ অভিযোগ করলেন, আপনার শিষ্যরা পূর্ববর্তী সম্মানীয় বুযুর্গদের ঐতিহ্যের বিপরীত হাত না ধূয়েই আহার করে কেন? হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম এর জাবাবে বললেনঃ তোমাদের মতো রিয়াকারদের অবস্থা হচ্ছে ঠিক তেমনি যেমন হযরত ইয়ারয়া নবীর কণ্ঠে এ তিরস্কার করা হয়েছেঃ “এই উম্মত মুখে আমার প্রতি মর্যাদার বাণী উচ্চারণ করে, কিন্তু তাদের হৃদয় আমার থেকে দূরে। কারণ এরা মানব রচিত আইনের শিক্ষা দেয়।” তোমরা আল্লাহর হুকুমকে বাতিল করে থাকো এবং নিজেদের বানোয়াট আইনকে প্রতিষ্ঠিত রাখো। আল্লাহ তাওরাতের মধ্যমে তোমাদের হুকুম দিয়েছিলেন, মা বাপের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো এবং যে ব্যক্তি মা বাপকে সম্মান করবেনা তার প্রাণানাশ করো। কিন্তু তোমরা বলছো যে ব্যক্তি মা বাপকে একথা বলে দেয়, আমার যে খিদমত তোমার কাজে লাগতে পারে তাকে আমি আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছি, তার জন্য মা বাপের খিদমত না করা সম্পূর্ণ বৈধ। [মথি ১৫: ৩-৯, মার্ক ৭: ৫-১৩]
চ. “প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই তোমাদের রব, যিনি আকাশ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি নিজের কর্তৃত্বের আসনে সমাসীন হয়েছেন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেকে দেন তারপর রাতের পেছনে দিন দৌড়িয়ে আসে। তিনি সূর্য ও চন্দ্র ও তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন। সবাই তাঁর নির্দেশের অনুগত। জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং নির্দেশও তাঁরই। আল্লাহ বড়ই বরকতের অধিকারী। তিনি সমগ্র বিশ্বজাহানের মালিক ও প্রতিপালক।” [সূরা আ’রাফঃ ৫৪]
আল্লাহর “কর্তৃত্বের আসণে সমাসীন হওয়া” র বিস্তারিত স্বরূপ অনুধাবন করা আমাদের পক্ষে কঠিন। খুব সম্ভবত সমগ্র বিশ্বজাহান সৃষ্ট্রির পর মহান আল্লাহ কোনো একটি স্থানকে তাঁর এ অসীম সাম্রাজ্যের কেন্দ্র নির্ধারণ করেন এবং সেখানে নিজের আলোক রশ্মীর বিচ্ছুরণকে কেন্দ্রীভূম করে দেন আর তারই নাম দেন “আরশ” [কর্তৃত্বের আসন] সেখান থেকে সমগ্র বিশ্বজাহানে নব নব সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে ও ক্রমাগত শক্তির বিচ্ছুরণ ঘটছে। সেই সাথে সৃষ্টি জগতের পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনাও অব্যাহত রয়েছে। আবার এও সম্ভব হতে পারে যে, আরশ অর্থ শাসন কর্তৃত্ব এবং আরশের ওপর সমাসীন হয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ এ বিশ্বজাহান সৃষ্টি করার পর এর শাসনদন্ড নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। মোটকথা আরশের ওপর সমাসীন হওয়ার বিস্তারিত অর্থ যাই হোক না কেন মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহ যে এ বিশ্বজগতের নিছক স্রষ্টাই নন বরং এর পরিচালক এবং ব্যবস্থাপকও সেকথা ভালোভাবে হৃদয়ংগম করানোই কুরআনে এর উল্লেখের আসল উদ্দেশ্য। তিনি এ দুনিয়াকে অস্তিত্বশীল করার পর এর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে কোথাও বসে যাননি। বরং কার্যত তিনিই সারা বিশ্বজাহানের ছোট বড় প্রত্যেকটি বস্তুর ওপর কর্তৃত্ব করছেন। পরিচালনা ও শাসন কর্তৃত্বের যাবতীয় ক্ষমতা কার্যত তারই হাতে নিবদ্ধ। প্রতিটি বস্তু তাঁর নির্দেশের অনুগত। অতি ক্ষুদ্র অনু পরমাণুও তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। প্রতিটি বস্তু ও প্রাণীর ভাগ্যই চিরন্তনভাবে তাঁর নির্দেশের সাথে যুক্ত। যে মৌলিক বিভ্রান্তিটির কারণে মানুষ কখনো শিরকের গোমরাহীতে লিপ্ত হয়েছে, আবার কখনো নিজেকে স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ঘোষণা করার মতো ভ্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, কুরআন এভাবে তার মুলোৎপাটন করতে চায়। বিশ্বজাহানের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা থেকে আল্লাহকে কার্যত সম্পর্কহীন মনে করার অনিবার্য ফল দাঁড়ায় দুটি। হয় মানুষ নিজের ভাগ্যকে অন্যের হাতে বন্দী মনে করবে এবং তার সামনে মাথা নতো করে দেবে অথবা নিজেকেই নিজের ভাগ্যের নিয়ন্তা মনে করবে এবং নিজেকে সর্বময় কর্তৃত্বশালী স্বাধীন সত্তা মনে করে কাজ করে যেতে থাকবে।
এখানে আরো একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। স্রষ্টা ও সৃষ্টির ম্যধকার সম্পর্ক সুস্পস্ট করার জন্য কুরআন মজীদে মানুষের ভাষা থেকে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এমনসব শব্দ, পরিভাষা, উপমা ও বর্ণনাভংগী গ্রহণ করা হয়েছে, যা রাজত্ব ও শাসনের সাথে সম্পর্ক রাখে। এ বর্ণনাভংগী কুরআনে এতো বেশী স্পষ্ট যে, অর্থ বুঝে কুরআন পাঠকারী যেকোনো ব্যক্তিই এ বিষয়টি অনুভব না করে থাকতে পারবেননা। কোনো কোনো অর্বাচীন সমালোচক স্বীয় বিকৃত চিন্তা ও মানসিকতার কারণে ও বাচনভংগী থেকে বুঝেছেন যে, এ কিতাবটি যে যুগের ‘রচনা’ সে যুগে মানুষের মনমস্তিষ্কে রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তৃত ছিলো। তাই এ কিতাবের রচয়িতা [এ বিবেকহীন নিন্দুকদের মতে এর রচয়িতা নাকি হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহকে একজন রাজা ও বাদশাহ হিসেবেই পেশ করেছেন। অথচ কুরআন যে শাশ্বত ও অনাদি অনন্ত সত্য উপস্থাপন করছে তা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সে সত্যটি হচ্ছে, ভূমন্ডলে ও নভোমন্ডলে একমাত্র আল্লাহর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। সার্বভৌমত্ব [Sovereignty] বলতে যা বুঝায় তা একমাত্র তারই সত্তার একচেটিয়া অধিাকর ও বৈশিষ্ট্য। আর বিশ্বজাহানের এ ব্যবস্থাপনা একটি পূর্ণাংগ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা বিশেষ, যেখানে ঐ একক সত্তা সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। কাজেই এ ব্যবস্থার মধ্যে যে ব্যক্তি বা দল নিজের বা অন্য কারুর আংশিক বা পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবীদার হয়, সে নিজেকে নিছক প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে রেখেছে। তাছাড়া এ ব্যবস্থার মধ্যে অবস্থান করে মানুষের পক্ষে ঐ একক সত্তাকে একই সাথে ধর্মীয় অর্থেও একমাত্র মা’বুদ এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থেও একমাত্র শাসক [Sovereign] হিসেবে মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সঠিক দৃষ্টিভংগী ও কর্মনীতি হতে পারেনা।
“আরশের উপর সমাসীন হলেন” বাক্যটির মাধ্যমে সংক্ষেপে যে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে এখানে তারই কিছুটা অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ নিছক স্রষ্টাই নন, তিনি হুকুমকর্তা এবং শাসকও। তিনি সৃষ্টি করার পর নিজের সৃষ্ট বস্তুসমূহকে অন্যের কর্তৃত্বের সোপর্দ করে দেননি অথবা সমগ্র সৃষ্টিকে বা তার অংশ বিশেষকে ইচ্ছামতো চলার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেননি। বরং কার্যত সমগ্র বিশ্বজগতের পরিচালনা ব্যবস্থা আল্লাহর নিজের হিতেই কেন্দ্রীভুত রয়েছে। দিন রাত্রির আবর্তন আপনা আপনিই হচ্ছেনা। বরং আল্লাহর হুকুমে হচ্ছে। তিনি যখনই চাইবেন দিন ও রাতকে থামিয়ে দেবেন আবার যখনই চাইবেন এ ব্যবস্থা বদলে দেবেন। সূর্য, চন্দ্র, তারকা এরা কেউ নিজস্ব কোনো শক্তির অধিকারী নয়। বরং এরা সবাই সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন। এরা একান্ত অনুগত দাসের মতো সেই কাজই করে যাচ্ছে যে কাজে আল্লাহ এদেরকে নিযুক্ত করেছেন।
ছ. “নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।” [সূরা মায়েদাঃ ১]
অর্থাৎ আল্লাহ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছামতো যে কোনো হুকুম দেবার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। তাঁর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য করার বা আপত্তি জানানোর কোনো অধিকার মানুষের নেই। তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার মুসলিম যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর বলেই তার আনুগত্য করেনা বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর হুকুম বলেই তাঁর আনুগত্য করে। যে জিনিসটি তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা কেবল তাঁর হারাম করে দেবার কারণেই হারাম হিসেবে গণ্য। আর ঠিক তেমনি যে জিনিসটি তিনি হালাল করে দিয়েছেন সেটির হালাল হবার পেছনে অন্য কোনো কারণ নেই বরং যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এসব জিনিসের মালিক তিনি নিজের দাসদের জন্য এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলেই এটি হালাল। তাই কুরআন মজীদ সর্বোচ্চ বলিষ্ঠতা সহকারে এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কোনো বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো ভিত্তিরে আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ যে কাজটিকে বৈধ গণ্য করেছেন সেটি বৈধ এবং যেটিকে অবৈধ গণ্য করেছেন সেটি অবৈধ, এছাড়া মানুষের জন্য কোনো কাজের বৈধ ও অবৈধ হবার দ্বিতীয় কোনো মানদন্ড নেই।
জ. “আর তোমাদের কণ্ঠ ভূয়া হুকুম জারী করে বলতে থাকে এটি হালাল এবং ওটি হারাম, এভাবে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করোনা। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তারা কখনোই সফলকাম হবেনা। [সূরা আননাহলঃ ১১৬]
এ আয়াতটি পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, হালাল ও হারাম করার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই। অথবা অন্য কাথায়, একমাত্র আল্লাহই আইন প্রণেতা। অন্য যে ব্যক্তিই বৈধতা ও অবৈধতার ফয়সালা করার ধৃষ্টতা দেখাবে, সে নিজের সীমালংঘন করব। তাবে যদি সে আল্লাহর আইনকে অনুমতিপত্র হিসেবে মেনে নিয়ে তার ফরমানসমূহ থেকে প্রমান সংগ্রহ করে বলে, অমুক জিনিসটি অথবা কাজটি বৈধ এবং অমুকটি অবৈধ তাহলে তা হতে পারে। এভাবে নিজের হালাল ও হারাম করার স্বাধীন ক্ষমতাকে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ বলে অভিহিত করার কারণ হলো, যে ব্যক্তি এ ধরনের বিধান তৈরী করে তার এ কাজটি দুটি অবস্থার বাইরে যেতে পারেনা। হয় সে দাবী করছে যে, যে জিনিসকে সে আল্লাহর কিতাবের অনুমোদন ছাড়াই বৈধ বা অবৈধ বলছে তাকে আল্লাহ বৈধ বা অবৈধ করেছেন। অথবা তার দাবী হচ্ছে, আল্লাহর নিজের হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা প্রত্যাহার করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তার নিজের জীবনের শরীয়া তৈরী করার জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। এ দুটি দাবীর মধ্য থেকে যেটিই সে করবে তা নিশ্চিতভাবেই মিথ্যাচার এবং আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ ছাড়া আর কিছুই হবেনা।
ঝ. “হে নবী তাদের বলো, তোমরা কি কখনো একথা চিন্তা করেছো যে, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন তার মধ্য থেকে তোমরা নিজেরাই কোনোটাকে হারাম ও কোনোটাকে হালাল করে নিয়েছো? নাকি তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করছো?” [সূরা ইউনুসঃ ৫৯]
রিযিক বলতে আমাদের ভাষায় শুধুমাত্র পানাহারের জিনিসপত্র বুঝায়। এ কারণে লোকেরা মনে করে ধর্মীয় সংস্কার ও রসম রেওয়াজের ভিত্তিতে খাদ্য সামগ্রির ক্ষুদ্রতর পরিসরে লোকেরা যেসব আইন কানুন প্রণয়ন করে রেখেছে এখানে শুধুমাত্র তারই সমালোচনা করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তিতে শুধুমাত্র অজ্ঞ অশিক্ষিত ও সাধারণ মানুষরাই ভুগছেনা, শিক্ষিত সমাজ এবং আলেমরাও এর শিকার হয়েছেন। অথচ আরবী ভাষায় রিযিক শব্দটি নিছক খাদ্যের অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং রকমারি দান, অনুদানও এর আওতাভুক্ত রয়েছে। আল্লাহ দুনিয়ায় মানুষকে যা কিছু দিয়েছেন তা সবই তাঁর রিযিক। এমনকি সন্তান সন্ততিও রিযিক। আসমাউর রিজাল তথা রাবীদের জীবনী গ্রন্থসমূহে রিযক, রুযাইক ও রিযকুল্লাহ নামে অসংখ্য রাবী পাওয়া যায়। আমাদের দেশে আল্লাহ বখশ, খোদা বখশ নামগুলো প্রায় এই একই অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি বহুল প্রচলিত দোয়ার ভাষা হলোঃ
“হে আল্লাহ! সত্যকে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে দাও এবং আমাদের তার অনুসরণ করার রিযিক দাও।
প্রচলিত আরবী প্রবাদে বলা হয় অর্থাৎ رزق علما অর্থাৎ অমুক ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক জ্ঞান দেয়া হয়েছে। হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ প্রত্যেক গর্ভবতীর পেটে একজন ফেরেশতা পাঠান। তিনি শিশুর রিযিক এবং তার আয়ু ও কর্ম লিখে দেন। এখানে রিযিক মানে শুধু খাদ্য নয়, যা ভূমিষ্ঠ হবার পরে এশিশু লাভ করবে। বরং এ দুনিয়ায় তাকে যা কিছু দেয়া হবে সবই রিযিকের অন্তরভুক্ত।
ঞ. “আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তারাই কাফির………..যালিম……….ফাসিক……..।” [সূরা মায়েদাঃ ৪৪-৪৭]
যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করেনা তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এখানে তিনটি বিধান দিয়েছেন। এক, তারা কাফের। দুই, তারা যালিম। তিন, তারা ফাসিক। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুম ও তাঁর নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফয়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে। প্রথমত তার এ কাজটি আল্লাহ্র হুকুম অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এটি কুফরী। দ্বিতীয়ত তার এ কাজটি সুবিচার ও ভারসাম্যনীতের বিরোধী। কারণ, আল্লাহ্ পথার্থ ইনসাফ ও বারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহ্র হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করলো তখন সে আসলে যুলুম করলো। তৃতীয়ত, দাস হওয়া সত্ত্বেও যখনই সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করলো তখনই সে আসলে দাসত্ব ও আনুগত্যের গন্ডীর বাইরে পা রাখলো। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসিকী। এ কুফরী, যুলুম ও ফাসিকী তার নিজের ধরন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরোপুরি আল্লাহ্র হুকুম অমান্যেরই বাস্তব রূপ। যেখনে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবেনা, এটা কোনোক্রমেই সম্বব নয়। তবে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করার যেমন পর্যায়ভেদ আছে তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কোনো মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহ্র হুকুম বিরোধী ফায়সালা করে সে পুরোপুরি কাফির, যালিম ও ফাসিক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধে ফালসালা করে, সে ইসলামী মিল্লাত বহির্ভুত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফুরী, যুলুম ও ফাসিকীর সাথে মিশিয়ে ফেলছে। অনুরীপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্র হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফির, ফাসিক ও যালিম। আর সে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীরনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী , যুলুম ও ফাসিকীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যে হারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে একসাথে মিশিয়ে রেখেছে। কোনো কোনো তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে আহ্লি কিতাবদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে গণ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহ্র কালামের শব্দের মধ্যে এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোনো অবকাশ নেই। হযরত হুযইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর বক্তব্যই এ ধরনের ব্যাখ্যার সঠিক ও সর্বোত্তম জবাব। তাঁকে একজন বলেছেলো এ আয়াত তিনটিতো বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বুঝাতে চাচ্ছিলো যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নাযিল করা হুকুমরে বিরুদ্ধে ফালসালা করে সে-ই কাফির, যালিম ও ফাসিক। একথা শুনে হযরত হুযাইফা বলে ওঠেনঃ
“এ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী তোমাদের কেমন চমৎকার ভাই, তিতোগুলো সব তাদের জন্য আর মিঠাগুলো সব তোমাদের জন্য। কখ্খনো নয়, আল্লাহ্র কসম তাদেরই পথে তোমরা কদম মিলিয়ে চলবে।”
আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের এটাই একেবারে গোড়ার কথা। এ বিষয়ে কুরআনের বিভিন্নস্থানে বক্তব্য এসেছে। আল্লাহ্ ছাড়া যাকেই স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী মানা হবে কুরআনের পরিভাষায় সে হলো তাগুত। আর এটা আল্লাহ্র দাসত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত।
ট. “এখন যে কেই তাগুতকে অস্বীকার করে আল্লাহ্র ওপর ঈমান আনে, সে এমন একটি মজবুত অবলম্বন আঁকড়ে ধরে, যা কখনো ছিন্ন হয়না। আর আল্লাহ্ [যাঁকে সে অবলম্বন হিসেবে আকড়ে ধরেছে] সবকিছু শোনেন ও জানেন।” [সূরা আল বাকারাঃ ২৫৬]
আভিধানিক অর্থে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে “তাগুত” বলা হবে, যে নিজের বৈধ অধিকারের সীমানা লংঘন করেছে। কুরআনের পরিভাষায় তাগুত এমন এক দাসকে বলা হয়, যে দাসত্বের সীমা অতিক্রম করে নিজেই প্রভু ও খোদা হবার দাবীদার সাজে এবং আল্লাহ্র বান্দাদেরকে নিজের দাসত্বে নিযুক্ত করে। আল্লাহ্র মোকাবিলায় বান্দার প্রভুত্বের দাবীদার সাজার এবং বিদ্রোহ করার তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম পর্যায় বান্দা নীতিগতভাবে আল্লাহ্র শাসন কর্তৃত্বকে সত্য বলে মেনে নেয় কিন্তু কার্যত তার বিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে। একে বলা হয় ফাসেকী। দ্বিতীয় পর্যায়ে সে আল্লাহ্র শাসন কর্তৃত্বকে নীতিগতভাবে মেনে না নিয়ে নিজের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয় অথবা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে অন্য কারো বন্দেগী ও দাসত্ব করতে থাকে। একে বলা হয় কুফ্রী। তৃতীয় পর্যায়ে সে মালিক ও প্রভুর বিরুদ্ধে ঘোষণা করে তার রাজ্যে এবং তার প্রজাদের বলা হয় “তাগুত।” কোনো ব্যক্তি এই তাগুতকে অস্বীকার না করা পর্যন্ত কোনো দিন সঠিক অর্থে আল্লাহ্র মুমিন বান্দা হতে পারেনা।
অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ
“হে নবী! তুমি কি তাদেরকে দেখোনি, যারা এই মর্মে দাবী করে চলছে যে, তারা ঈমান এনেছে সেই কিতাবের প্রতি যা তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং সেইসব কিতাবের প্রতি যেগুলো তোমার পূর্বে নাযিল করা হয়েছেলো; কিন্তু তারা নিজেদের বিষয়সমূহের ভায়সালা করার জন্য ‘তাগুতে’র দিকে ফিরতে চায়, অথচ তাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছিলো তাগুতকে অস্বীকার করার।” [সূরা আননিসাঃ ৬০]
এখানে ‘তাগুত’ বলতে সুস্পষ্টভাবে এমন শাসককে বুঝানো হয়েছে, যে আল্লাহ্র আইন বাদ দিয়ে অন্য কোনো আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে এবং এমন বিচার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়েছে যা আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতার আনুগত্য করেনা এবং আল্লাহ্র কিতাবকে চূড়ুন্ত সনদ [Final Authority] হিসেবে স্বীকৃতিও দেয়না। কাজেই যে আদালত তাগুতের ভূমিকা পালন করছে, নিজের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালার জন্য তার কাছে উপস্থিত হওয়া যে একটি ঈমান বিরোধী কাজ , এ ব্যাপারে এ আয়াতটির বক্তব্য একেবারে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। আর আল্লাহ্ ও তাঁর কিতাবের ওপর ঈমান আনার অপরিহার্য দাবী অনুযায়ী এই ধরনের আদালতকে বৈধ আদালত হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানানোই প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তির কর্তব্য। কুরআনের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনা ও তাগুতকে অস্বীকার কার, এদুটি বিষয় পরস্পরের সাথে অংগাংগীভাবে সংযুক্ত এবং এদের একটি অন্যটির অনিবার্য পরিণতি। আল্লাহ্ ও তাগুত উভয়ের সামনে একই সাথে মাথা নতো করাই হচ্ছে সুস্পষ্ট মুনাফিকী।
উপরোক্ত আলোচনা থেকে কুরআনের সার্বভৌমত্বের ধারণা হয়ে যায়। এই ধারণা অনুযায়ী সার্বভৌমত্বে মানুষের বিন্দুমাত্র অংশ থাকতে পারেনা। তাই কুরআনমানুষকে পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি বলে ঘোষণা করেছে। আর প্রতিনিধির প্রকৃত মিশন এই বলে জানিয়েছে যে, সে পৃথিবীতে তার মালিকের নির্দেশ মাফিক কাজ করবে। এ বিষয়ের প্রতি ইংগিত করছে নিন্মেক্ত আয়াতঃ
“যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাদের বললেন আমি এ পৃথিবীতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করবো”। [সূরা আলবাকারাঃ ৩০]
যে ব্যক্তি কারো অধিকারের আওতাধীনে তারাই অর্পিত ক্ষমতা ইখতিয়ার ব্যবহার করে, তাকে খলীফা বলে। খলীফা নিজে মালিক নয় বরং আসল মালিকের প্রতিনিধি। সে নিজে ক্ষমতা ব্যবহার করে। সে নিজের ইচ্ছে মতো কাজ করার অধিকার রাখেনা। বরং মালিকের ইচ্ছে পূরণ করাই হয় তার কাজ। যদি সে নিজেকে মালিক মনে করে বসে এবং তার ওপর অর্পিত ক্ষমতাকে নিজের ইচ্ছে মতো ব্যবহার করতে থাকে অথবা আসল মালিককে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে মালিক বলে স্বীকার করে নিয়ে তারই ইচ্ছে পূরণ করতে এবং তার নির্দেশ পালন করতে থাকে, তাহলে এগুলো বসই বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য হবে।
৬. আনুগত্যের মূলনীতি্
উপরে বর্ণিত সার্বভৌমত্ব ও প্রতিনিধিত্বের স্বাভাবিক ও যৌক্তিক দাবী হলো, আনুগত্যও করতে হবে স্রষ্টার এবং স্রষ্টার নির্দেশের। বাকী সমস্ত আনুগত্য হবে এই মূল আনুগত্যের অনুগামী। এ মূলনীতিটি কুরআন এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ
“হে ঈমানদারগণ, আনুগত্য করো আল্লাহ্র এবং আনুগত্য করো রসূলের আর সেইসব লোকের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ও ক্ষমতার অধিকারী। এরপর যদি তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যাপারে বিরোধ দেখা দেয়, তবে তা আল্লাহ্ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা যথার্থই আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর ঈমান এনে থাকো। এটিই একটি সঠিক কর্মপদ্ধতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটিই উৎকৃষ্ট।” [সূরা আননিসাঃ ৫৯]
এ আয়াতটি ইসলামের সমগ্র ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনের বুনিয়াদ। এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্রের কশসনতন্ত্রের পয়লা নম্বর ধারা। এখানে নিম্নলিখিত মূলনীতিগুলি স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়া হয়েছেঃ
এক, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আসল আনুগত্য লাভের অধিকারী আল্লাহ্। একজন মুসলমানের সর্বপ্রথম পরিচয় হচ্ছে, সে আল্লাহ্র দাস। এরপর সে অন্যকিছু। মুসলমানের ব্যক্তিগত্য জীবন এবং মুসলমানদের সমাজ ব্যবস্থা উভয়ের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ্র আনুগত্য করা ও বিশ্বস্ততার সাথে তাঁর নির্দেশ মেনে চলা। অন্যান্য আনুগত্য ও অনুসৃতি কেবলমাত্র তখনই গৃহীত হবে যখন তা আল্লাহ্র আনুগত্য ও অনুসৃতির বিপরীত হবেনা, বরং তার অধীন ও অনুকূল হবে। অন্যথায় এই আসল ও মৌলিক আনুগত্য বিরোধী প্রতিটি আনুগত্য শৃংখলকে ভেংগে দূরে নিক্ষেপ করা হবে। একথাটিকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিম্মোক্ত বক্তব্যে পেশ করেছেনঃ
“স্রষ্টার আনুগত্য পরিহার করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।”
দুই, ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হচ্ছে, রসূলের আনুগত্য। এটি কোনো স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ আনুগত্য নয়। বরং আল্লাহ্র আনুগত্যের এটিই একমাত্র বাস্তব ও কার্যকর পদ্ধতি। রসূলের আনুগত্য এজন্য করতে হবে যে, আল্লাহ্র বিধান ও নির্দেশ আমাদের কাছে পৌছার তিনিই একমাত্র বিশ্বস্ত ও অকাট্য মাধ্যম। আমরা কেবলমাত্র রসূলের আনুগত্য করার পথেই আল্লাহ্র আনুগত্য করতে পারি। রসূলের সনদ ও প্রমাণপত্র ছাড়া আল্লাহ্র কোনো আনুগত্য গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। আর রসূলের আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া আল্লাহ্র বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নামান্তর। নিম্মোক্ত হাদীসে এই বক্তব্যটিই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছেঃ
“যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আসলে আল্লাহ্র আনুগত্য করলো এবং যে ব্যক্তি আমার নাফরমানি করলো সে আসলে আল্লাহ্র নাফারমানি করলো।”
তিন, উপরোল্লিখিত দুটি আনুগত্যের পর তাঁদের অধীনে তৃতীয় আর একটি আনুগত্য ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আওতাধীন মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব। সেটি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্য থেকে ‘উলিল আমর’ তথা দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারীদের আনুগত্য। মুসলমানদের সামাজিক ও সামষ্টিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে দায়িত্বসম্পন্ন ও নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি মাত্রই ‘উলিল আমর’ এর অন্তর্ভুক্ত। তারা মুসলমানদের মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিকে ও চিন্তাগত ক্ষেত্রে নেতৃত্বদানকারী উলামায়েকিরাম বা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হতে পারেন। আবার দেশের শাসনকার্য পরিচালনাকারী প্রশাসকগণ হতে পারেন, অথবা আদালতে বিচারের রায় প্রদানকারী বিচারপতি বা তামদ্দুনিক ও সামাজিক বিষয়ে গোত্র, মহল্লাও জনবসতির নেতৃত্বদানকারী শেখ সরদার প্রধানও হতে পারেন। মোটকথা কোনো ব্যক্তি যে কোনো পর্যায়েই মুসলমানদের নেতৃত্বদানকারী হবেন তিনি অবশ্যি আনুগত্য লাভের অধিকারী হবেন। তার সাথে বিরোধ সৃষ্টি করে মুসলমানদের সামাজিক জীবনে বাধাবিপত্তি ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করা যাবেনা। তবে এক্ষেত্রে শর্ত হচ্ছে, তাকে মুসলিম দলভুক্ত হতে হবে এবং আল্লাহ্ ও রসূলের অনুগত হতে হবে। এই আনুগত্যের জন্য এই শর্ত দুটি হচ্ছে অপরিহা্র্য ও বাধ্যতামূলক। কেবলমাত্র উল্লেখিত আয়াতটির মধ্যভাগেই এ সুস্পষ্ট শর্তটি সংশ্লিষ্ট হয়নি বরং হাদীসেও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিপূর্ণ ব্যাপকতার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটি বর্ণনা করেছেন। যেমন নিন্মোক্ত হাদীসগুলি দেখা যেতে পারেঃ
“নিজের নেতৃবৃন্দের কথা শোনা ও মেনে চলা মুসলমানের জন্য অপরিহার্য, তা তার পছন্দ হোক বা না হোক, যে পর্যন্ত না তাকে আল্লাহ্র অবাধ্য হবার হুকৃম দেয়া হয়। আর যখন তাকে আল্লাহ্র অবাধ্য হবার হুকুম দেয়া হয় তখন তার কিছু শোনা ও আনুগত্য করা উচিত নয়।” [বুখারী ও মুসলিম]
“আল্লাহ্ ও রসূলের অবাধ্য হতে হবে এমন কোনো আনুগত্য নেই, আনুগত্য করতে হবে শুধুমাত্র “মারূফ” বা বৈধ ও সৎকাজে।” [বুখারী ও মুসলিম]
“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ “তোমাদের ওপর এমনসব লোকও শাসক কর্তৃত্ব চালাবে যাদের অনেক কথাকে তোমরা ‘মারূফ’ [বৈধ] ও অনেক কথাকে ‘মুনকার’ [অবৈধ] পাবে। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি তাদের মুনকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে, সে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তা অপছন্দ করবে, সেও বেঁচে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি তাতে সন্তুষ্ট হয় এবং তার অনুসরণ করে সে পাকড়াও হবে।” সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করেন, “তাহলে এ ধরনের শাসকদের শাসনামলে কি আমরা তাদের সথে যুদ্ধ করবোনা?” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দেনঃ “না” যতদিন তারা নামায পড়তে থাকবে [ততদিন তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারবেনা।” [মুসলিম]
অর্থাৎ নামায পরিত্যাগ করা এমন একটি আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে, যা থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, তারা আল্লাহ্ ও রসূলের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেছে। এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা ন্যায়সংগত হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
“তোমাদের নিকৃষ্টতম নেতা হচ্ছে তারা যারা তোমাদেরকে ঘৃণা করে এবং তোমরা তাদেরকে ঘৃণা করো, তোমরা তাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকো এবং তারা তোমাদের প্রতি লানত বর্ষণ করতে থাকে। সাহাবাগণ আরজ করেন, হে আল্লাহ্র রসূর! যখন এ অবস্থায় সৃষ্টি হয় তখন কি আমরা্ তাদের মোকাবিলা করার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াবোনা? জবাব দেনঃ না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নমায কায়েম করতে থাকবে! না, যতদিন তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করতে থাকবে!” [মুসলিম]
এই হাদীসটি উপরে বর্ণিত শর্তটিকে আরো সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে। উপরের হাদীসটি থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক ছিলো যে, যতদিন তারা ব্যক্তিগত জীবনে নামায পড়তে থাকবে ততদিন তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যবেনা। কিন্তু এই হাদীসটি থেকে একথা জানা যায় যে, নামায পড়া মানে আসলে মুসলমানদের সমাজ জীবনে নামাযের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অর্থাৎ কেবলমাত্র তাদের নিজেদের নিয়মিতভাবে নামায পড়াটাই যথেষ্ট হবেনা বরং সেই সংগে তাদের আওতাধীন যে রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে সেখানেও কমপক্ষে ‘ইকামতে সালাত’ তথা নামায প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাপনা থাকা জরুরী বিবেচিত হবে। তাদর রাষ্ট্রব্যবস্থা তার আসল প্রকৃতির দিক দিয়ে যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা এটি হবে তারই একটি আলামত। অন্যথায় যদি এতোটুকুও না হয়, তাহলে এর অর্থ হবে, তারা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের শাসন ব্যবস্থাকে উল্টে ফেলার জন্য প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালানো মুসলমানদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে। এ কাথাটিকেই অন্য একটি হাদীসে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছেঃ
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের থেকে অন্যান্য আরো বিভিন্ন বিষয়ের সাথে এ ব্যাপারেও অংগীকার নিয়েছেনঃ
“আমরা আমাদের সরদার ও শাসকদের সাথে ঝগড়া করবোনা, তবে যখন আমার তাদরে কাজে প্রকাশ্য কুফরী দেখতে পাবো যার উপস্থিতিতে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে পেশ করার জন্য আমাদের কাছে প্রমাণ থাকবে।” [বুখারী ও মুসলিম]
চার, চতুর্থ যে মূলনীতিটি এ আয়াতটি থেকে স্থায়ী ও চূড়ান্তভাবে স্থিরীকৃত হয়েছে সেটি হলো, ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আল্লাহ্র হুকুম ও রসূলের সুন্নাহ্ হচ্ছে মৌলিক আইন ও চূড়ান্ত সনদ [Fimal Authority]। মুসলমানদের মধ্যে অথবা মুসলিম সরকার ও প্রজাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে বিরোধ দেখা দিলে তার মীমাংসার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে ফিরে আসতে হবে। কুরআন ও সুন্নাহ এ ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবে তার সামনে মাথা নতো করে দিতে হবে। এভাবে জীবনের সকল ব্যাপারে কুরআন ও রসূলের সুন্নাহকে সনদ, চূড়ান্ত ফায়সালা ও শেষ কথা হিসেবে মেনে নেয়অর বিষয়টি ইসলমী জীবন ব্যবস্থার এমন একটি বৈশিষ্ট্য, যা তাকে কুফরী জীবন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়। যে ব্যবস্থায় এ জিনিসটি অনুপস্থির থাকে সেটি আসলে একটি অনৈসলামী ব্যবস্থা।
এ প্রসংগে কউ কেউ সংশয় প্রকাশ করে বলে থাকেন যে, জীবনের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যাওয়া কিভাবে সম্ভব হতে পারে? কারণ মিউনিসিপ্যালিটি, রেলওয়ে, ডাকঘর ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় সম্পর্কিত কোনো নিয়ম কানুনের উল্লেখই সেখনে নেই। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে দীনের মূলনীতি সঠিকভাবে অনুধাবন না করার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। একজন মুসলমানকে একজন কাফির থেকে যে বিষয়টি আলাদা ও বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করে সেটি হচ্ছে, কাফির অবাধ স্বাধীনতার দাবীদার। আর মুসলমান মূলত আল্লাহ্র বান্দাহ ও দাস হবার পর তার রব মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাকে যতোটুকু স্বাধীনতা দান করেছেন, সে শুধুমাত্র ততোটুকু স্বাধীনতাই ভোগ করে। কাফির তার নিজের তৈরী মূলনীতি ও আইন বিধানের মাধ্যমে তার যাবতীয় বিষয়ের মীমাংসা করে। এইসব মূলনীতি ও বিধানের ক্ষেত্রে কোনো ঐশী সমর্থন ও স্বীকৃতির প্রয়োজন আছে বলে সে মনে করেনা এবং নিজেকে সে এর মুখাপেক্ষীও ভাবেনা। বিপরীত পক্ষে মুসলমান তার প্রতিটি ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহ ও তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিকে ফিরে যায়। সেখান থেকে কোনো নির্দেশ পেলে সে তার অনুসরণ করে। আর কোনো নির্দেশ না পেলে কেবলমাত্র এই অবস্থায়ই সে স্বাধীনভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। এক্ষেত্রে তার এই কর্মের স্বাধীনতার মূল ভিত্তি একথার ওপরই স্থাপিত হয় যে, এই তিনি এক্ষেত্রে কর্মের স্বাধীনতা প্রদান করেছেন।
কুরআন মজীদ যেহেতু নিছক একটি আইনের কিতাব মাত্র নয় বরং একই সংগে এটি একটি শিক্ষা ও উপদেশমূলক গ্রন্থও, তাই প্রথম বাক্যে যে আইনগত মূলনীতির বিবরণ দেয়া হয়েছিলো এই দ্বিতীয় বাক্যে তার অন্তর্নিহিত কারণ ও যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দুটি কথা বলা হয়েছে। প্রথমত, উপরোল্লিখিত চারটি মূলনীতি মেনে চলা ঈমানের অপরিহার্য দাবী। একদিকে মুসলমান হবার দাবী করা এবং অন্যদিকে এই মূলনীতিগুলো উপেক্ষা করা, এ দুটি পরস্পর বিরোধী জিনিসের কখনো একত্র সমাবেশ হতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, এই মূলনীতিগুলির ভিত্তিতে নিজেদের জীবন বিধান নির্মাণ করার মধ্যেই মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত। কেবলমাত্র এই একটি জিনিসই তাদেরকে দুনিয়ায় সত্য সরল পথের ওপর প্রতিষ্ঠত রাখতে পারে এবং এর সাধ্যমেই তারা পরকালেও সফলকাম হতে পারে। যে ভাষণে ইহুদিদের নৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার ওপর মন্তব্য করা হচ্ছিলো এই উপদেশ বাণীটি ঠিক তার শেষে উক্ত হয়েছে। এভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে বলা হয়েছে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মত দীনের এই মূলনীতিগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যেভাবে অধপতনের গভীর হর্তে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তা থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। যখন কোনো জনগোষ্ঠী আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রসূলের হিদায়াত পেছনে ফেলে দিয়ে এমনসব নেতা ও সরদারের আনুগত্য করতে থাকে, যারা আল্লাহ্ ও রসূলের হুকুম মেনে চলোনা এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতা ও রাষ্ট্রীয় শাসকাদের কাছে কুরআন ও সুন্নাহর সনদ ও প্রমাণপত্র জিজ্ঞেস না করেই তাদের আনুগত্য করেত থাকে তখন তারনা এই বনী ইসরাঈলদের মতোই অসৎ ও অনিষ্টকর কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে এমনসব দোষত্রুটি সৃষ্টি হয়ে যায়, যার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়।
চতুর্থ অধ্যায়
খিলাফতের তাৎপর্য
এটা কেবল ইসলামের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগিই নয়, বরঞ্চ গোটা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় মানুষ আল্লাহ্র প্রতিনিধি হবার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিগত অধ্যায়গুলোতে ইসলামরে রাজনৈতিক দর্শনের উপর যেসব কথা বলা হয়েছে, তাতেও এই ধারণা কেন্দ্রীয় গুরুত্বের মর্যাদা লাভ করেছে। এ নিবন্ধে খিলাফত বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। এখানে নিবন্ধটির শেষাংশ উদ্ধত করা হলো। মাওলানার এ নিবন্ধটি তরজমানুল কুরআন ফেব্রুয়ারী ১৯৩৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। -সংকলক
খিলাফতের তাৎপর্য
কুরআনের দিক নির্দেশনা
এবার আমি কুরআনের কতিপয় দিক নির্দেশনার দিকে আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করবো। এ থেকে জানা যাবে, মানুষকে যে খিলাফত দান করা হয়েছে তা আসলে আল্লাহ্রই খিলাফত।
কুরআন বলছে, আল্লাহ্ মানুষকে সর্বোত্তম কাঠামো দিয়ে সৃষ্টি করেছেনঃ
তাকে তিনি নিজই তৈরী করেছেন। [সূরা ত্বীনঃ ৪]
তিনি নিজের পক্ষ থেকে তার মধ্যে রূহ সঞ্চারিত করেছেন। [সূরা সোয়াদঃ ৭৫]
তাকে জ্ঞানের মত সম্পদে সমৃদ্ধ করেছেন। [সূরা সিজদাঃ ৯]
আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসকে তার অনুগত ও অধীনস্থ করে দিয়েছেন। [সূরা আল-বাকারাঃ ৩১]
এই সমস্ত গুণ বৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষকে যখন সৃষ্টি করা হলো, তখন আল্লাহ্ ফেরেশতাদেরকে তার সামনে সিজাদা করার নির্দেশ দিলেন। [সূরা জাসিয়াঃ ১৩]
এ নির্দেশটা সূরা সোয়াদের শেষাংশে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা বিশেষভাবে বিবেচনার দাবী রাখেঃ
“যখন তোমার প্রভু ফেরেমতাদের বললেন, আমি মাটি দিয়ে মানুষ সুষ্টি করতে যাচ্ছি। সেটা যখন সম্পূর্ণরূপে বানানো হয়ে যাবে এবং তাতে আমি নিজের হতে আত্মা সঞ্চারিত করবো, তখন তোমরা তার সামনে সিজাদায় পতিত হয়ো। অতপর সকল ফেরেশতা সিজদা করলো। কিন্তু ইসলীস সিজদা করলোনা। সে দাম্ভিকতায় লিপ্ত হলো এবং আদেশ লংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলো। আল্লাহ্ বললেন, হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে গড়লাম, তাকে সিজদা করতে তোমাকে বাধা দিলো কিসে? তুমি কি নিজেকে খুব বড় মনে করে বসেছো, না সত্যই বড় কিছু হয়ে গেছো? সে বললো, আমি ওর চেয়ে ভালো। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছো আর ওকে সৃষ্টি করেছো মাটি থেকে। তখন আল্লাহ্ বললেনঃ “তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা। কেননা তুই ধিক্কৃত।” [সূরা সোয়াদঃ ৭১-৭৭]
এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায়, মানুষকে সিজদা করার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো তার কারণ এই ছিলো যে, আল্লাহ্ তাকে স্বহস্তে নির্মান করেছিলেন, অর্থাৎ সে ছিলো আল্লাহ্র অসীম ক্ষমতা ও শিল্প নৈপুণ্যের চূড়ান্ত প্রতীক। আর তার ভেতরে তিনি নিজের পক্ষ থেকে একটা অসাধারণ রূহ সঞ্চারিত করেছিলেন এবং যে গুণাবলী সর্বোচ্চ মাত্রয় স্বয়ং আল্লাহ্র মধ্যেই পাওয়া যায়, সেই গুণাবলীই সীমিত মাত্রায় তার মধ্যে সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন। এরূপ মর্যাদা ও গুণবৈশিষ্ট্য সহকারে মানুষকে সৃষ্টি করার পর ঘোষণা করা হলো, আমি তাকে পৃথিবীতে খলীফা নিয়োগ করতে যাচ্ছি। সূরা বাকারার চতুর্থ রুকুতে এ বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। ফেরেশতারা এ ব্যাপারে নিজেদের কিছু সন্দেহ সংশয় প্রকাশ করলে আল্লাহ্ তাদের সামনে মানুষের শ্রেষ্ঠতম বৈশিষ্ট্য জ্ঞানের প্রদর্শনী করলেন। এভাবে খিলাফতের জন্য মানুষের যোগ্যতা প্রমাণিত করার পর ফেরেশতাদের হুকুম দেয়া হলো, তার খিলাফত মেনে নাও এবং মেনে নেয়ার আলামত হিসেবে তাকে সিজদা করো। সকল ফেরেশতা মেনে নিলেন এবং সিজদা করলেন। কিন্তু শয়তান তার খিলাফত প্রত্যাখ্যান করলো এবং দরবার থেকে বিতাড়িত হলো।
এথেকে কি বুঝা গেলো? এ দ্বারা সকল সৃষ্টির ওপর মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা হলো। আনুষ্ঠানিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে তার শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হলো। বলা হলো, মানুষ আমার গুণাবলীর পূর্ণতম ও উৎকৃষ্টতম বাহক এবং তার মধ্যে আমি নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ রূহ সঞ্চারিত করেছি। তাকে সিজদা করার নির্দেশ দেয়া হলো, তাও আর কাউকে নয় ফেরেশতাদেরকে। এসব করার সাথে সাথে তাকে খলীফা বানানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হলো। এতো প্রস্তুতি ও আড়ম্বর সহকারে যে খলীফার খিলাফত ঘোষিত হলো, সে কি কেবল পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদেরই খলীফা ছিলো? ব্যাপার যদি কেবল এতাটুকুই হয়ে থাকে যে, প্রাচীন অধিবাসীর জায়গায় অন্য এক অধিবাসীকে অধিষ্ঠিত করা হচ্ছে, তাহলে ফেরেশতাদের সামনে তার খিলাফতের ঘোষণা দেয়া এবং এভাবে তার শ্রেষ্ঠত্ব যাহির করার কি দরকার ছিলো? আর ফেরেশতাদেরকে এ নির্দেশই বা দেয়া হলো কেন যে, ভূমন্ডলের এই নতুন অধিবাসীকে যে কি না কেবল অন্যদের পরিত্যক্ত জায়গায় বসতি স্থাপন করতে যাচ্ছিলো সিজদা করো?
আল্লাহ্র খিলাফতের মর্ম কি?
পবিত্র কুরআনের অন্যত্র অন্য যে উক্তিটি করা হয়েছে, তা আল্লাহ্র খিলাফতের মার্ম কি সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোকপাত করে। আল্লাহ্ বলেনঃ
“আমি আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের কাছে এ আমানত পেশ করেছিলাম, কিন্তু তারা কেউ এর ভার গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি এবং তারা ভয় পেয়ে যায়। এর ভার মানুষ গ্রহণ করলো। বস্তুত সে যালেম ও অপরিণামদর্শী সাব্যস্ত হয়েছে।” [সূরা আহযাবঃ ৭৩]
এ আয়াতে আমানতের অর্থ নির্বাচনের স্বাধীনতা [Freedom of choic] এবং দায়িত্ব ও জবাবদিহী [Responsibility] আল্লাহ্র এ উক্তির মর্মার্থ হলো, আকাশ, পৃথিবী ও পাহাড় পর্বতের এ দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করার ক্ষমতা ছিলোনা। মানুষের পূর্বে এ দায়িত্ব গ্রহণের ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো সৃষ্টিরই অস্তিত্ব ছিলোনা। অবশেষে মানুষের আবির্ভাব ঘটলো এবং সে এ দায়িত্ব গ্রহণ করলো। এ বক্তব্য থেকে কয়েকটি তথ্য জানা যায়ঃ
১. মানুষের পূর্বে আকাশ ও পৃথিবীতে কোনো সৃষ্টি এ দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। মানুষই এ দায়িত্ব গ্রহণকারী প্রথম সৃষ্টি। সুতরাং আমানত গ্রহণের ক্ষেত্রে সে কারো স্থালাভিষিক্ত [Successor] নয়।
২. সূরা বাকারায় যে জিনিসকে খিলাফত বলা হয়েছে এখানে ‘আমানত’ শব্দ দ্বারা সেটাই বুঝানো হয়েছে। কেননা সেখানে ফেরেশতাদের সামনে প্রমাণ করে দেয়া হয়েছিলো যে, তারা খিলাফতের উপযুক্ত নয়, মানুষই তার উপযুক্ত। আর এখানে বলা হয়েছে যে, আকাশ ও পৃথিবীর কোনো সৃষ্টি আমার আমানতের ভার কাঁধে নেয়ার যোগ্য ছিলোনা, শুধু মানুষই তা বহন করতে পেরেছে।
৩. খিলাফতের তাৎপর্য আমানত শব্দ দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই দু’টো শব্দ একত্রে বিশ্ব প্রকৃতির অবকাঠামোতে মানুষের প্রকৃত অবস্থান নির্দেশ করে। মানুষ হলো পৃথিবীর শাসক ও পরিচালক। তবে তার এই শাসনকর্তৃত্ব মৌলিক নয়, বরং অর্পিত [Delegated] । সুতরাং আল্লাহ্ তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্বকে [Delegated power] আমানত বলে অভিহিত করেছেন। মানুষ এই অর্পিত ক্ষমতাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই ব্যবহার করে বলে তাকে খলীফা [Vicegerent] বলা হয়েছে। এ হিসেবে খলীফা বলতে সে ব্যক্তিকে বুঝায়, যে কারো অর্পিত বা প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে। [Person exercising delegated power] [তরজমানুল কুরআন, জ্বিলকদ ১৩৫৩ হিঃ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫]
পঞ্চম অধ্যায়
১. ইসলামী জাতীয়তার ধারণা
২. ইসলামী জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্য
দেশ বিভাগের পূর্বে উপমহাদেশের রাজনৈতিক বাকবিতন্ডার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো জাতীয়তা। মুস-লমানরা সবসময় নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধারণা পোষণ করে এসেছে। তারা অমুসলিমেদের সাথে মিলিত হয়ে এক জাতিতে পরিণত হওয়ার ধারণাকে কখনো মেনে নেয়নি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্যের প্রভাব ও হিন্দু রাজনীতের যোগসাজশে সম্মিলিত জাতীয়তার বিভ্রান্তিকর আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। শিক্ষিত জনগোষ্ঠির ওপর এ আন্দোলন সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। আল্লামা ইকবাল, মাওলানা মওদুদী ও অন্যান্য চিন্তানায়কগণ এ চ্যালেঞ্জের জবাব দেন এবং সম্মিলিত জাতীয়তার ধারণার কঠোর সমালোচনা করেন। এই সময়োচিত সমালোচনার সুফল হলো এই যে, মুসলমানরা সম্মিলিত জাতীয়তার বিভ্রন্তি থেকে রক্ষা পেলো এবং দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান আন্দোলন গড়ে উঠলো। মাওলানা মওদুদীর রচনাবলী এই জাগরণ সুষ্টিতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। আমাদের বর্তমান সংকলনটিতে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্যের পরিপ্রেক্ষিতে মাওলানার দুটো প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করা হচ্ছে। এ প্রবন্ধ দুটো মাসিক তরজমানুল কুরআন নভেম্বর ডিসেম্বর ১৯৩৩ সংখ্যা এবং জুন ১৯৩৯ সংখ্যা থেকে নেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেও এ প্রবন্ধ দুটি অন্যান্য সংকলনে সন্নিবেশিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে এবং বহু পাঠকের চিন্তায় তা আলোড়ন তুলেছে। -সংকলক
ইসলামী জাতীয়তার ধারণা
আদিম বন্য জীবন থেকে সভ্য জীবন অভিমুখে মানব জাতির অভিযাত্রার প্রথম পদক্ষেপেই এটা অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, বিশাল মানব সমাজের মধ্যে থেকে একটি স্বতন্ত্র ঐক্যের ধারা গড়ে ওঠবে এবং সম্মিলিত উদ্দেশ্যে ও স্বার্থে কতিপয় ব্যক্তি মিলিত হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ তৎপরতার কর্মসূচী গ্রহণ করবে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে এই সামষ্ঠিক ঐক্যের পরিধিও সম্প্রসারিত হতে থাকবে। অবশেষে এক সময় এর আওতায় চলে আসবে বিপুল সংখ্যাক মানুষ। এই সম্মিলিত মানবসমষ্টির নামই “জাতি”। “জাতি” ও “জাতীয়তা” এ দুটি শব্দ যদিও এদের বিশিষ্ট পারিভাষিক অর্থে আধুনিক কালের সৃষ্টি। কিন্তু এ শব্দ দুটি উচ্চরণ করা মাত্রই যে জিনিসটি বুঝে আসে, তা ঠিক সভ্যতার মতোই প্রাচীন। ‘জাতি’ ও ‘জাতীয়তা’ যে কাঠামোর নাম, তা আজকের ফ্রান্স, বৃটেন, জার্মানী ও ইটালিতে যেমন আছে, প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, রোম ও গ্রীসেও তেমনিই ছিলো।
জাতীয়তার অবিচ্ছেদ্য উপাদান সমূহ
একথা সন্দেহাতীত যে, জাতীয়তার সূচনা একটি নিস্প্রাণ আবেগ থেকেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ তার প্রাথমিক উদ্দশ্য এটাই হয়ে থাকে যে, একটি বিশেষ গোষ্ঠির লোকেরা নিজেদের সম্মিলিত স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য কাজ করবে এবং নিজেদের সামগ্রিক প্রয়োজনে একটি “জতি” হিসেবে বসবাস করবে। কিন্তু তাদের ভেতরে যখন “জাতীয়তার”উদ্ভব ঘটে, তখন অনিবার্যভাবে তাতে “গোষ্ঠীপ্রীতি”র বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়। “জতীয়তাবাদের” আবেগ যতোই তীব্রতর হয় “গোষ্ঠীপ্রীতি” ততোই প্রকট আকার ধারণ করতে থাকে। যখনই কোনো জাতি স্বীয় স্বার্থের সেবা ও কল্যাণের সংরক্ষণের জন্য নিজেকে একটি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবে অথবা অন্য কথায় বলা যায়, নিজের চারপাশে “জাতীয়াতর” দেয়াল গড়ে তুলবে, তখন সে অনিবার্যভাবে ঐ দেয়ালের বাইরের লোক ও ভেতরের লোকদের মধ্যে আপন ও পরের বাছবিচার করবেই। আপন লোকদেরকে সকল ব্যাপারে পরের ওপর অগ্রাধিকার দেবেই। পরের মোকাবিলায় সে আপনদেরকে সমর্থন না দিয়ে পারবেনা। দুই গোষ্ঠীর স্বার্থ ও কল্যাণের বিষয়ে যখন বিরোধ দেখা দেবে, তখন সে নিজের স্বার্থের হিফাজত করবে এবং অপরের স্বার্থকে বিসর্জন দেবে। এসব কারণে তাদের মধ্যে যুদ্ধও হবে, সন্ধিও হবে। কিন্তু যুদ্ধের ময়দান হোক, কিংবা আলোচনার বৈঠক হোক সর্বত্র তাদের উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে জাতীয়তার সীমারেখা বহাল থাকবেই। এ জিনিসটার নামই গোষ্ঠীপ্রীতি ও জাতিগত বৈষম্য। এটা জাতীয়তার অপরিহার্য ও সহজাত বৈশিষ্ট্য।
জাতীয়তার উপাদান সমূহ
ঐক্য ও অংশীদারত্বের যেকোনো একটি উপাদান থেকে জাতীয়তার পত্তন হতে পারে। তবে শর্ত হলো, যে উপাদান থেকে জাতীয়তার পত্তন হবে, তাতে সংযোগ ও নিয়ন্ত্রণের এমন দুরন্ত শক্তি থাকা চাই যে, মানুষের বিপুল সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও তা যেনো সকলকে একই বাণী, একই চিন্তা, একই লক্ষ্য ও একই কর্মসূচীতে ঐক্যবদ্ধ করে দেয় এবং জাতীর বিপুল সংখ্যক বিচিত্র জনমন্ডলীকে জাতীলতার বন্ধন এমন মজবুতভাবে আবদ্ধ ও সম্পৃক্ত করে দেয় যে, তারা একটা জমাট পাথরে পরিণত হয়। ঐক্য ও অংশীদারত্বের যে উপাদানটি এই জাতীয়তার ভিত রচনা করবে, তার সমগ্র জনমন্ডলীর মন ও মগজের ওপর এতো বেশী আধিপত্য, প্রতপ ও নিয়ন্ত্রণের অধিকারী হওয়া চাই যে, জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে তারা সবাই ঐক্যবদ্ধ থাকবে এবং অর্জনে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার প্রস্তুত থাকবে।
ঐক্য ও অংশীদারিত্বের উপাদানতো অনেক থাকতে পারে। কিন্তু ইতিহাসের সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যতোগুলো জাতীয়তার উদ্ভব ঘটেছে, তন্মধ্যে একমাত্র ইসলামী জাতীয়তা ছাড়া আর সবগুলোই নিম্মলিখিত ঐক্যসমূহের কোনো একটির ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। ঐত্যের এই উপাদানের সাথে আনুসংগিকভাবে অন্যান্য উপাদানও শামিল হয়ে গেছেঃ
ক. বংশীয় ঐক্য। একে প্রজাতিক ঐক্যও বলা হয়।
খ.জন্মভূমির ঐক্য। একে দেশীয় বা ভুমিগত ঐক্যও বলে।
গ.ভাষাগত ঐক্য। চিন্তার ঐক্য সৃষ্টির একটা প্রভাবশালী মাধ্যম হওয়ার কারণে এটি জাতীয়তা গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।
ঘ. বর্ণগত ঐক্য। এটি একই বর্ণের লোকদের মধ্যে স্বজাত্যবোধ গড়ে তোলে।
অতঃপর এই স্বজাত্যবোধ আরো অগ্রসর হয়ে তাদেরকে ভিন্ন বর্ণের লোকদেরকে এড়িয়ে চলতেও অবজ্ঞা করতে প্ররোচিত করে।
ঙ. অর্থনৈতিক স্বার্থগত ঐক্য। এ উপাদানটি এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্মলিত সমাজের লোকদেরকে ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধারী ব্যবস্থা সম্মলিত সমাজের লোকদেরকে ভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধারী সমাজ থেকে পৃথক করে। এর ভিত্তিতে উভয় সমাজের মানুষ পরস্পরের মোকাবিলায় নিজ নিজ অর্থনৈতিক অধিকার ও কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা সাধনা করে।
চ. শাসন ব্যবস্থার ঐক্য। এ উপাদানটি একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে একটি সম্মিলিত শাসন ব্যবস্থার যোগসূত্রে আবদ্ধ করে এবং ভিন্ন রাষ্ট্রর নাগরিকদের সাথে তাদের ব্যবধানের সীমা চিহ্নিত করে।
প্রাচীনতম যুগ থেকে শুরু করে আজকের বিংশ শতাদ্বীর আলোকোজ্জ্বল যুগ পর্যন্ত যতো ধরনের জাতীয়তার উপাদান অনুসন্ধান কারা হোক না কেন, সবগুলোর ভেতরে এই কয়টি উপাদানই যাওয়া যাবে।
আজ থেকে দুই তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীক, রোমক, ইসরাইলী, ইরানী, প্রভৃতি জাতীয়তা এই ভিত্তিগুলোর ওপরই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর আজকের জার্মান, ইটালীয়, ফরাসী, ইংরেজ, মার্কিন, রুশ ও জাপানী প্রভৃতি জাতীতাও এসব ভিত্তির ওপরই দাঁড়িয়ে আছে।
একথা ষোল আনা সত্য যে, বিশ্বের বহু সংখ্যক জাতীয়তা নির্মাণের এই ভিত্তিগুলো খুবই বলিষ্ঠভাবে জাতিগুলোকে সংগঠিত ও সংঘবদ্ধ করেছে। তবে সেই সাথে এই সত্যও অস্বীকার করা যায়না যে, এ ধরনের জাতীয়তা মানবজাতির জন্য এক ভায়াবহ বিপদ ডেকে এনেছে। এসব জাতীয়তা মানব জগতকে শত শত হাজার হাজার অংশে বিভক্ত করে দিয়েছে। আর এই বিভক্তিও এমন চরম যে, একটি অংশেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া যায় বটে, কিন্তু অন্য অংশে পরিবর্তিত করা যায়না। একটি বংশধর অপর বংশধরে পরিণত হতে পারেনা, একটি ভূমি বা দেশ অন্য ভূমি ও দেশে পরিণত হতে পারেনা, একটি ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী অন্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীতে পরিবর্তিত হতে পারেনা। এক বর্ণের মানুষ অন্য বর্ণের মানুষে রূপান্তরিত হতে পারেনা, একটি জাতির অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অবিকল অন্য জাতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আশা আকাংখায় পরিণত হতে পারেনা এবং একটি রাষ্ট্র কখনো অন্য রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারেনা। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, এসব ভিত্তির ওপর যেসব জাতীয়তা নির্মত হয়, তাদের ভেতরে পারস্পরিক সমঝোতা ও আপোষরফার কোনো পথই খুঁজে পাওয়া যায়না। জাতীয় আভিজাত্যবোধ ও জাত্যভিমানের কারণে তারা একে অপরের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দিতা ও পরস্পরকে প্রতিরোধের এক চিরস্থায়ী দ্বন্দসংঘাতে লিপ্ত হয় এবং একে অপরকে পদপিষ্ট করার চেষ্টা চালায়। তারা পরস্পরে লড়াই করতে করতে ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর পুনরায় একই উপাদানে নতুন জাতীয়তা গড়ে ওঠে এবং একই ধরনের দ্বন্দসংঘাতে জড়িয়ে পড়াই হয় তার শেষ পরিণতি। এই জাতীয়তা পৃথিবীতে ফেৎনাফাসাদ, অরাজকতা, অশান্তি ও পাপাচারের উৎস, আল্লাহ্র সবচেয়ে বড় অভিশাপ এবং মানুষকে ধ্বংস করার কাজে শয়তানের সবচেয়ে অব্যর্থ হাতিয়ার।
জাহেলী বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধ
এ ধরনের জাতীয়তার স্বাভাবিক দাবী হলো, তা মানুষের ভেতরে জাহেলী বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধ সৃষ্টি করে। এক জাতিকে অপর জাতির সাথে বিরোধ ও শত্রুতা পোষণে এটি শুধু এজন্য প্ররোচিত করে যে, তারা ভিন্ন জাতি। সত্য, সততা ও ন্যায়ের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকেনা। এক ব্যক্তির চামড়া কালো শুধু এ কারণেই সে সাদা চামড়াওয়ালার চোখ তুচ্ছ বিবেচিত হয়। এক ব্যক্তি এশিয়ার অধিবাসী- শুধুমাত্র এজন্যই সে ফিরিংগীদের তাচ্ছিল্য, অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হয়। আইনষ্টাইনের ন্যায় বিজ্ঞানী শুধুমাত্র ইহুদী হওয়ার কারণে জার্মানদের বিদ্বেষ ও অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হন। শুধুমাত্র কৃষ্ণকায় নিগ্রো হওয়ার কারণে একজন ইউরোপীয়কে শাস্তি দেয়ার অপরাধে তাশকেদীর রাজ্য ছিনিয়ে নেয়াকে সম্পূর্ণ বৈধ সাব্যস্ত করা হয়। ১. {তাশকেদী বসুয়ানা ল্যান্ডের বামিংভাটু গোত্রের গোত্রপতি। একজন ইউরোপীয় অপরাধীকে বেত্রদন্ড প্রদান তার এতা গুরতর অপরাধ বিবেচিত হয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্য তাকে তার রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করে দেয়। অথচ স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে এই ফিরিংগী লোকটির দুঃখজনক আচরণের কথা স্বয়ং হাই কমিশনারও স্বীকার করতেন। পরে বেচারা তাশকেদীকে শুধুমাত্র এই বলে অঙ্গীকার কারার পর রাজত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয় যে, কোনো ইউরোপীয় ব্যক্তি জড়িত এমন কোনো মামলার নিষ্পত্তি তিনি করবেননা। অথচ সে অংগীকারনামায় ইউরোপীয়দেরকে স্থানীয় লোকদের জানমাল ও সন্ত্রমে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত রাখতে পারে এমন কোনো ধারা ছিলোনা।}
আমেরিকার সুসভ্য নাগরিকদের জন্য নিগ্রোদেরকে ধরে ধরে জ্যান্ত জ্বালিয়ে দেয়া সম্পূর্ণ বৈধ হয়ে যায় শুধু এজন্য যে, তারা নিগ্রো। নিগ্রোদেরকে শ্বেতাংগদের বাড়ীঘরে থাকতে না দেয়া, সড়কের ওপর দিয়ে চলতে না দেয়া এমনকি তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত করা মার্কিনীদের জন্য বৈধ হয়ে যায়। একজন ফরাসী নাগরিক ও একজন জার্মান নাগরিকের পরস্পরকে ঘৃণা করার জন্য এটাই যথেষ্ট বিবেচিত হয় যে, তাদের একজন ফরাসী আর অপরজন জার্মান। তারা এজন্য পরস্পরকে শুধু ঘৃণা করেই ক্ষান্ত হয়না বরং একজনের যাবতীয় সদগুণ অপরজনের চোখে শুধুই দোষ মনে হয়। সীমান্ত প্রদেশের স্বাধীনচেতা আফগানরা আফগান বলেই ইংরেজরা তাদের ওপর বোমাবর্ষন করা আর দামেস্কের অধিবাসীরা আরব বলেই ফরাসীরা তাদেরকে পাইকারী হত্যা করা সম্পূর্ণ ন্যায়সংগত মনে করে। মোট কথা এই জাতিগত বৈষম্য এমন এক বস্তু যা মানুষকে ন্যায়নীতি ও ইনসাফের ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ বানিয়ে দেয়। এর কারণে বিশ্বখ্যাত নৈতিকতা ও সৌজন্যের সূলনীতিগুলিও জাতীয়তার রূপ ধারণ করে কোথাও যুলূম, কোথাও সুবিচার, কোথাও সত্য, কোথাও মিথ্যা, কোথাও সৌজন্যে এবং কোথাও অসৌজন্যে পরিণত হয়।
মানুষের জন্য এর চেয়ে অযৌক্তিক মানসিকতা আর কি হতে পারে যে, সে একজনস অযোগ্য ও অসৎ লোককে শুধু এজন্য একজন যোগ্য ও সৎ লোকের চেয়ে অগ্রগণ্য মনে করবে যে, প্রথমজন এক বংশে এবং দ্বিতীয়জন ভিন্ন বংশে জন্মেছে? প্রথমজন সাদা এবং দ্বিতীয়জন কালো? প্রথমজন একটি পাহাড়ের পশ্চিমে জন্মেছে এবং দ্বিতীয়জন তার পূর্বে? প্রথমজন এক ভাষায় কথা বলে এবং দ্বিতীয়জন অন্য ভাষায়? প্রথমজন এক সাম্রাজ্যের অধিকারী এবং দ্বিতীয়জন অপর সাম্রাজ্যের? চামড়ার রং কি আত্মার পরিচ্ছন্নতা নোংরামিকে পাল্টে দিকে পারে? বিবেক কি একথা বিশ্বাস করে যে, পাহাড় ও সমুদ্রের সাথে চরিত্র ও মানবিক গুণাবলীর কোনো সম্পর্ক আছে? প্রাচ্যে যা সত্য, পাশ্চাত্যে গিয়ে তা মিথ্যা হয়ে যাবে এটা কি কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ মেনে নিতে পারে? সততা, ন্যায়নীতি, ভদ্রতা ও মানসিক সদগুণবলীকে ধমনীতে প্রবহমান রক্ত, সুখের উচ্চারিত ভাষা ও জন্মস্থানের মাটির মানদন্ডে যাচাই করা উচিত, এমন ধারণা কি কোনো সুস্থ মনে স্থান পেতে পারে? নিশ্চয়ই বিবেক এসব প্রশ্নের নেতিবাচক জবাবই দেবে। কিন্তু বর্ণ, বংশ, জন্মস্থান ও অন্যান্য বৈষম্যের প্রবক্তার অত্যন্ত ধৃষ্টতার সাথে জবাব দিয়ে থাকে যে, হাঁ, ব্যাপারটা এ রকমই।
জাতীয়তার উপাদান সমূহের পর্যালোচনা
কিছুক্ষণের জন্য উপরোক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা স্থাগিত রাখুর। একটি বিশাল জনগোষ্ঠীর সকল সদস্যের সাধ্যে সমভাবে বিরাজমান যতগুলো বৈশিষ্ট্য জাতীয়তার ভিত্তি রচনা করে, আগে সেগুলোর নিজস্ব সত্তা নিয়ে চিন্তা করুন এবং ভাবুন, স্বতন্ত্রভাবে এসব বৈশিষ্টোর কোনো যৌক্তিক ভিত্তি আছে কি, না এগুলো নিছক কাল্পনিক মরিচিকার মতো?
প্রথমে ধরা যাক, প্রজাতিক বা বংশীয় অংশীদারিত্ব ও সমতার কথা। এটাতো নিছক রক্তের ঐক্য। মাতা ও পিতার বীর্য হলো এর সূচনাবিন্দু। এ দ্বারা রক্তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে কিছু সংখ্যক মানুষের মধ্যে। তারপর এর বৃত্ত আরো সম্প্রসারিত হয়ে সৃষ্টি হয় পরিবার গোত্র ও বংশধরের। এই সর্বশেষ সীমা অর্থাৎ বংশধর পর্যন্ত পৌছতে পৌছতে মানুষ তার বংশধরের। প্রতিষ্ঠাতা পিতা থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এতো দূরে সরে যায় যে, ঐ পিতার উত্তর পুরুষ হিসেবে তার নাম নিতান্তই গৌণ ও তাৎপর্যহীন হয়ে যায়। তাথাকথিত বংশধরের এই বিশাল নদীতে বহিরাগত রক্তের অনেক উপনদীও শাখানদী এসে মিলিত হয়। ফলে কোনো জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ একথা দাবী করতে পারেনা যে, এই নদী যে উৎস থেকে বেরিয়েছিলো, তার সেই আসল পানিই এতে প্রবাহিত। এতো ভেজালের মিশ্রর সত্তেও যদি রক্তের সম অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে মানুষ একটি “বশধর” কে নিজের জন্য ঐক্যের বন্ধন হিসেবে মেনে নিতে পারে, তাহলে যে রক্তের বন্ধন সমগ্র সানবজাতিকে তাদের আদিপিতা ও আদিমাতার সাথে সংযুক্ত করে তাকেই ঐক্যের বন্ধন হিসেবে মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? সকল মানুষকে একই ব্যশধর এবং একই মূলসুত্রের সাথে সম্মন্ধযুক্ত করলে ক্ষতি কি? যেসকল ব্যক্তিকে আজকাল বিভিন্ন ব্যশধর ও বিভিন্ন প্রজন্মের প্রতিষ্ঠাতা মনে কারা হয়, তাদের সকলেরই বংশপরস্পরা উপরে গিয়ে কোথাও না কোথাও একই ধারায় মিলিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত একথা না মেনে উপায় থাকেনা যে, তারা সবাই একই উৎস থেকে উদ্ভুত। তাহলে আর্য অনার্য নামে এই বিভক্তির যৌক্তিকতা কোথায়?
ভৌগলিক তথা জন্মভূমিভিত্তিক ঐক্যের ব্যাপারটা এর চেয়েও বেশী কাল্পনিক। মানুষের প্রকৃত জন্মস্থান তো কিছুতেই এক বর্গ গজের চেয়ে বেশী নয়। এতা ক্ষুদ্র আয়তনের ভুমিকে যদি সে নিজের জন্মভূমি বলে স্থির করে, তাহলে সে হয়তো কোনো দেশকেই নিজের জন্মভূমি বলতে পারবেনা। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ভূখন্ডের চারপাশে সে শত শত বা হাজার মাইল পর্যন্ত সীমারেখা এঁকে নেয় এবং বলে যে, ঐ পর্যন্ত আমার মাতৃভূমি, ঐ সীমারেখার বাইরে যা কিছু আছে তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, এটা শুধু তার দৃষ্টির সংকীর্ণতা। নচেত সমগ্র পৃথিবীকে নিজের মাতৃভূমি বলে দাবী করতে তাকে কেউ বাধা দিতে পারেনা। যে যুক্তির ভিত্তিতে এক বর্গগজ জায়গার মাতৃভূমি হাজার হাজার বর্গগজ পর্যন্ত সম্প্রসারিত হতে পারে। সেই একই যুক্তির বলে তা গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে পারে। মানুষ যদি নিজের দৃষ্টিভংগীকে সংকুচিত না করে তাহলে সে বুঝতে পারে যে, এই সমুদ্র, পাহাড়, নদী ইত্যাদি যাকে সে নিছক নিজের খেয়ালের বশে সীমান্তরেখা সাব্যস্ত করতঃ তার ভিত্তিহেত এক ভূখন্ড ও অপর ভূখেন্ডের মধ্যে পার্থাক্য করে তা সবই একই প্রথিবীর অংশ। তাহলে কিসের ভিত্তিতে সে পাহাড় নদী ও সমুদ্রকে এই অধিকার দিলো যে, তারা তাকে একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ডে বন্দী করে রেখে দেক? সে কেন বলেনা যে, আমি পৃথিবীর অধিবাসী, গোটা পৃথিবী আমার মাতৃভূমি ও স্বদেশ এবং সারা বিশ্বে যতো মানুষ বাস করে সবাই আমার স্বদেশবাসী? কেন সে দাবী করেনা যে গোটা পৃথিবীতে আমার সেই জন্মগত অধিকার রয়েছে, যা রয়েছে আমার এই এক বর্গগজ জন্মভূমিতে?
ভাষাগত অংশীদারিত্বের ফায়দা শুধু এতোটুকু যে, যারা একই ভাষায় কথা বলে তাদের পারস্পরিক সমঝোতা ও ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ বেশী। এতে পরস্পরের মধ্যে অজানা অচেনার ভাবটা অনেকাংশে কেটে যায় এবং সমভাষীরা নিজেদের মাঝে অধিকতর ঘনিষ্ঠতা অনুভব করে। কিন্তু একাধিক ব্যক্তির মনোভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম এক রকম হলেই যে খোদ্ মনোভাবটাও একই রকম হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। একই মনোভাব দশটা বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে, আর সেই দশটা ভাষায় মনোভাব ব্যক্তকারীদের একই মনোভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যাওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে দশটা রকমারি মনোভাব একই ভাষায় প্রকাশ করা যায় এবং এটাও বিচিত্র নয় যে, একই ভাষাভষীর সেইসব রকমারি ধ্যান ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন করে পরস্পরের বিরোধী হয়ে যেতে পারে। সুতরাং যে মাতমতের ঐক্য জাতীয়তার প্রাণ তা ভাষাগত ঐক্যের মুখাপেক্ষী নয়। অনুরূপভাবে একই ভাষাভাষীদের একই মতামত ও চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া জরুরী নয়। এরপর আমাদের যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মখীন হতে হয় তা এই যে, মানুষের মানুষ্যত্ব এবং তার ব্যক্তিগত ভালো বা মন্দে তার ভাষার অবদান বা প্রভাব কতোটুকু? এক জার্মানকে শুধু জার্মান ভাষাভাষী হওয়ার কারণেই কি একজন ফরাসী ভাষাভাষীর ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে? না তা কখনো নয়। দেখতে হবে তার ব্যক্তিসত্তা কি ধরনের দোষ বা গুণে ভূষিত? শুধু ভাষা দেখলে চলবেনা। বড় জোর এতোটুকু বলা যেতে পারে যে, একটা দেশের প্রশারনিক কাজকর্ম এবং সাধারণ কায়কারবার চালাতে সেই দেশের ভাষা জানা আছে এমন লোকই বেশী উপকারী ও সফল প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু মানবতার বিভজন ও জাতীয় বৈষম্যের জন্য এটা কোনো সঠিক ভিত্তি নয়।
এরপর আসে বর্ণের প্রসংগ। মানব সমাজে বর্ণভিত্তিক ব্যবধান ও বৈষম্য সবচেয়ে অর্থহীন ও বাজে জিনিস। বর্ণতো নেহায়েত শরীরের একটা গুণ বা অবস্থার নাম। কিন্তু মানুষ শুধু তার শরীরের কারণে সম্মানের পাত্র নয় বরং তার আত্মাও বিবেবের বদৌলতে। এই আত্মা ও বিবেকের কোনো রং নেই। সুতরাং মানুষে মানুষে সাদা, কালো লাল ও হলুদের বৈষম্যের অর্থ কি? আমসরাতো কালো ও সাদা গাভীর দুধে পার্থাক্য করিনা। কেননা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে দুধ, গাভীর রং নয়। কিন্তু আমাদের বিবেকবুদ্ধি এতোই বিকারগ্রস্ত ও মতিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, আমরা মানুষের চারিত্রিক ও মানসিক গুণাগুণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে তার বর্ণের দিকে বেশী মনোযোগী হয়ে পড়েছি। অর্থনৈতিক স্বার্থের অংশীদারিত্ব আসলে মানুষের স্বার্থপরতার এক অবৈধ সন্তান। এটা আল্লাহ্র সৃষ্টি করা জিনিস নয়। মানবশিশু মায়ের পেট থেকেই কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা নিয়ে ভুমিষ্ঠ হয়ে থাকে। পৃথিবীতে এসে সে চেষ্টা সাধনার এক বিস্তৃত ময়দান লাভ করে এবং জীবনের অসংখ্য উপায় উপকরণ তাকে স্বাগত জানায়। কিন্তু সে নিজের জীবিকার দুয়ার উম্মুক্ত হওয়াতেই শুধু খুশী থাকতে চায়না বরং সেই সাথে অন্যের দুয়ার রুদ্ধ হোক তাও কামনা করে। এই স্বার্থপরতায় কোনো বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্তির ফলে যে ঐক্য গড়ে ওঠে তা তাদেরকে একজাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করে। আপাতঃ দৃষ্টিতে তারা মনে করে যে, তার অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার একটা বৃত্ত বানিয়ে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থকে নিরাপদ করেছে। কিন্তু যখন এ ধরনের অনেকগুলো গোষ্ঠী নিজেদের চারপাশে অনুরূপ বৃত্ত বানিয়ে নেয়, তখন মানুষ নিজ হাতেই নিজের জীবন অতিষ্ঠ করে তোলো। তার নিজের স্বার্থপরতা তার পায়ে বেড়ি এবং হাতে কড়া পরিয়ে দেয়। অন্যদের জন্য জীবিকার দুয়ার রুদ্ধ করার চেষ্টা করতে গিয়ে সে নিজেই নিজের জীকিকার চাবিকাঠি হারিয়ে বসে। আজ আমাদের চোখের সামনে এ দৃশ্য বিদ্যমান যে, ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানের সাম্রাজ্যগুলো কিভাবে তাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে। তারা এখন বুঝতেই পারছেনা যে, যেসব অর্থনৈতিক দুর্গ তারা নিজেদের নিরাপত্তার সর্বোত্তম উপায় মনে করে নির্মান করেছিলো তা কিভাবে ভেংগে চুরমার করা যায়। এরপরও কি আমরা বুঝতে পারবোনা যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য বৃত্ত গড়ে তোলা এবং তার ভিত্তিতে জাতীয় বৈষম্য সৃষ্টি করা একটা নির্বোধসুলভ কাজ? আল্লাহ্র বিশাল পৃথিবীতে মানুষকে আপন প্রতিপালকের অনুগ্রহ অন্বেষণ করার স্বাধীনতা দেয়ায় দোষোর কি আছে?
শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত মতৈক্য মূলত একটা দৃর্বল ও ক্ষণস্থয়ী জিনিস। এর ভিত্তিতে কোনো স্থয়ী জাতীয়তার পত্তন কখনো সম্বব নয়। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদেরকে তার চিরস্থয়ী আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে একটি জাতিতে পরিণত করার চিন্তা কখনো সাফল্যের মুখ দেখেনি। রাষ্ট্র যতোক্ষণ পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী থাকে তাতেক্ষণ নাগরিকরা তার আইনের বাঁধনে বাঁধা থাকে। এই বাঁধন যখনই ঢিলা হবে অমনি তা খন্ডবিখন্ড হয়ে যাবে। মোগল সম্রাজ্যে কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ভরতের বিভিন্ন অঞ্চলকে নিজস্ব পৃথক পৃথক জাতিসত্তা গড়ে তুলতে কোনো কিছুই আর বাধা দিতে পারেনি। ওসমানী সাম্রাজ্যের একই পরিণতি ঘটেছিলো। শেষ যুগে তুর্কী যুবকদের সংগঠন “ইয়ং তুর্ক” উসমানী জাতীয়তার প্রাসাদ নির্মাণে অনেক চেষ্টা চালিয়েছিলো। কিন্তু একটিা ঠেলা লাগতেই গোটা প্রাসাদ হুড়মুড় করে ধ্বসে পড়লো। অষ্ট্রিয়া ও হাংগেরীর ঘটনা সাম্প্রতিকতম উদাহরণ। এছাড়াও ইতিহাস থেকে আরো অনেক উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। সেসব উদাহরণ দেখার পরও যারা রাজনৈতিক জাতীয়তা গড়া সম্মব মনে করে তারা শুধু তাদের কল্পনার নৈপুণ্যের জন্য অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।
উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মানব সমাজে এভাবে যতো বিভাজন করা হয়েছে, তার কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি নেই। এগুলো কেবল বস্তুগত ও আবেগ নির্ভর বিভজন। দৃষ্টিভংগীকে কিছুমাত্র প্রসারিত করলেই এসব বিভাজনের প্রতিটি বৃত্ত ভেংগে যায়। অজ্ঞতা ও মুর্খতার অন্ধকার, দৃষ্টির সীমাবদ্ধতা ও অন্তরের সংকীর্ণতার ওপর এসব বিভাজনের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। জ্ঞানের আলো যতো ছাড়াতে থাকে, অন্তর্দৃষ্টি যতো লক্ষ্যভেদী হয়, হৃদয়ে যতো বেশী উদারতা ও প্রশস্ততার উদ্ভব হয় ততোই এসব বস্তুগত ও আবেগ নির্ভর পর্দা সরে যেতে থেকে। অবশেষে বর্ণবাদ ও প্রজানম্নবাদকে মানবতার জন্য এবং স্বাদেশিকতাবাদকে আন্তর্জাতিকতার জন্য স্থান খালি করে দিতে হয়। বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্রের মধ্য দিয়ে মানবতার ঐক্য নামক মূল সত্যটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে। আল্লাহ্র পৃথিবীতে আল্লাহ্র সকল বান্দার অর্থনৈতিক কামনা বাসনা একই হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাবলী কেবল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নামক সূর্যর ছায়া মাত্র, যা ঐ সুর্যর গতিবিধি অনুসারে চলাফেরা করে এবং বাড়ে কমে।
ইসলামের প্রশস্ত দৃষ্টি ভংগী
উপরে আমি যেসব কথা বলেছি, অবিকল ওটাই ইসলামের বক্তব্য। ইসলাম মানুষে মানুষে কোনো বস্তুগত ও আবেগ নির্ভর ভেদাভেদ ও বৈষম্য স্বীকার করেনা। সে বলে, সকল মানুষ একই উৎস থেকে উদগতঃ
“আল্লাহ্ তোমাদেরকে একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় থেকে অসংখ্য নারী ও পুরুষ [বিশ্বময়] ছড়িয়ে দিয়েছেন।” [সূরা আননিসাঃ ১]
ইসলাম বলে, তোমাদের মধ্যে জন্মস্থান, মৃত্যুস্থান ও মাতৃভূমির পার্থক্য কোনো মৌলিক বিষয় নয়। আসলে তোমরা সবাই একই প্রাণ থেকে সুষ্টি করেছেন। তারপর প্রত্যেকেরই একটা অবস্থান স্থল ও সমাধিস্থাল হবে।” [সূরা আল আনয়ামঃ ৯৮]
এরপর সে বংশ ও গোত্রের পার্থক্যের তাৎপর্যও এভাবে ব্যাখ্যা করেছেঃ
“ওহে মানবমন্ডলীঃ আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে ও গোত্রে গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পারো। কিন্তু আসলে তোমাদের মধ্যে অধিকতর সম্মানিত ব্যক্তি তো সেই-ই, যে অধিকতর পরহেজগার।” [সূরা আল হুজরাতঃ ১৩]
অর্থাৎ এতো যে জাতি ও গোত্রের বিভিন্নতা, তা পরস্পরের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ, গর্ব ও দ্বন্দ সংঘাতের জন্য নয়, বরং পারস্পরিক পরিচয়ের সুবিধার জন্য। এই বিভিন্নতায় তোমরা মানবজাতির উৎপত্তির উৎস যে এক ও অভিন্ন সে কথা ভুলে যেওনা। তোমাদের মধ্যে যদি সত্যি সত্যি কোনো পার্থক্য ও ভেদাভেদ থেকে থাকে, তাবে তা চরিত্র ও কর্মের সততা ও অসততার ভিত্তিতে হয়ে থাকে।
এরপর বলা হয়েছে, এইসব রকমারি দল ও গোষ্ঠীগত বিভেদ আল্লাহ্র আযাব স্বরূপ। এ দ্বারা তোমাদেরকে পারস্পরিক শত্রুতার যন্ত্রণা উপভোগ করানো হয়ঃ
“নয়তো তিনি তোমাদেরকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরস্পরের শক্তি ও পতিপত্তির স্বাদ উপভোগ করাবেন।” [সূরা আল আনয়ামঃ ৬৫]
এই দলাদলিকে ইসলাম একটা অপরাধ বলে আখ্যায়িত করেছে এবং বলেছে যে, ফেরাউন এই অপরাধের কারণেই অভিশপ্ত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলোঃ
“ফেরাউন পৃথিবীতে অহংকার করলো এবং দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করলো।” { ফেরাউন মিষরের অধিবাসীদেরেকে কিবর্তী ও অকিবর্তী গোষ্ঠীতে বিভক্ত করে এবং উভয় গোষ্ঠীর সাথে বৈষম্যপূর্ণ আচরণ করে যে ঐতিহাসিক অপরাধ সংঘটিত করে তার প্রতি ইংগিত।}[সূরা ক্কাসাসঃ ৪১]
ইসলাম আরো বলেছে যে, পৃথিবী আল্লাহ্র। তিনি মানবজাতিকে এখানে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন, এখানকার সকল জিনিসকে মানুষের অনুগত ও বশীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ কোনো একটা ভূখন্ডের গোলাম হয়ে থাকতে বাধ্য নয়। এই বিশাল পৃথিবী তার জন্য উম্মুক্ত। এক জায়গা তার জন্য সংকীর্ণ ও অনাবাসযোগ্য হলে অন্যত্র যেতে পারে। সে যেখানেই যাবে, আল্লাহ্র প্রদত্ত সম্পদরাজি বিদ্যমান দেখতে পাবেঃ
“[আদম সুষ্টির সময় আল্লাহ্ বললেন] আমি পৃথিবীতে একজন পতিনিধি নিযুক্ত করতে যচ্ছি।” [সূরা আলবাকারাঃ ৩০]
“তোমরা কি দেখতে পাওনা যে, পৃথিবীতে বিরাজমান সকল জিনিসকে আল্লাহ্ তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন?” [সূরা হাজ্জঃ ৬৫]
“আল্লাহ্র পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিলোনা, যে তোমরা তার অভ্যন্তরে হিজরত করতে?” [সূরা আননিসাঃ ১০০]
আপনি সমগ্র কুরআন পড়ে যান। এতে একটি শদ্বও আপনি বর্ণ, বংশ ও ভৌগলিক আঞ্চলিকতা বা স্বাদেশিকতার সমর্থনে পাবেনা না। তার দাওয়াত গোটা মানবজাতিকে মম্বোধন করে উচ্চারিত হয়েছে। সারা পৃথিবীর মানব জাতিকে সে সততা ও কল্যাণের দিকে ডাকে। এক্ষেত্রে কোনো জাতি ও ভূখন্ডেরি ভেদাভেদ নেই। সে কোনো ভূখন্ডের সাথে যদি বিশেষ সম্পর্ক গড়ে থাকে তবে শুধু মক্কার সাথে গড়েছে।
“মক্কার স্থায়ী অধিবাসী এবং বাহিরাগত মুসলমান সবাই সমান মর্যাদার অধিকারী।” {এ তারণেই মুসলিম ফিকাহবিদদের একটা দল মক্কার মাটিতে কারো মালিকানা অধিকার স্বীকার করেননি। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু মক্কাবাসীকে ঘরের দরজা পর্যন্ত বন্ধ করতে নিষেধ করতেন, যাতে হাজীরা যে ঘরে ইচ্ছা উঠতে পারে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয মক্কায় ঘরবাড়ী ভাড়া করতে নিষেধ করতেন এবং মক্কার শাসকর্তাকে চিঠি লিখেছিলেন, তিনি যেনো লোকদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করেন। কোনো কোনো ফকীহ্র মতে নিজ খরচে ঘর বানালে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মক্কা পবিত্র, জায়গার ওপর সবার অধিকার রয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মক্কা পবিত্র, এর খলি জায়গা বিক্রি করা ও ঘর ভাড়া দেয়া। জায়েয নয়। অন্য হাদীসে বলেন, মক্কায় যেখানে যে ব্যক্তি প্রথম পৌছবে, সেখানে তারই অধিকার। ইসলাম যে জায়গাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে, এ হচ্ছে তার অবস্থা।}[ সূরা হজ্জঃ ২৫]
আর যে মোশরেকরা সেখানকার আসল অধিবাসী তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ওরা নাপাক ওদেরকে বহিস্কার করো।
“মোশরেকরা অপবিত্র। কাজেই এ বছরের পর তারা যেনো মসজিদুল হারামের ধারে কাছেও ঘোষণার পর ইসলামে দেশ ও অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হয়ে যায়। একজন মুসলামান অনায়াসে ঘোষণা করতে পারে যে “প্রতিটি দেশ আমাদের দেশ, কেননা তা আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র দেশ।”
বিদ্বেষ ও ইসলামের সাথে শত্রুতা
ইসলামে অভ্যুদয়কালে এই বর্ণ, বংশ ও মাতৃভূমি সংক্রা্ন্ত বিভেদ, বিদ্বেষ ও আভিজাত্যবোধই ছিলো তার পথের সবচেয়ে বড় বাঁধা।
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজ গোত্র এই আভিজাত্য ও কৌলিন্য ফলানোর প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে অগ্রগামী ছিলো। গোত্রসমূহের গৌরব গাথা এবং ব্যক্তিগত ও বংশীয় শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা তাদের ইসলাম গ্রহণের পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তারা বলতো, এই কুরআন যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই এসে থাকে তবে তা মক্কা বা তায়েফের কোনো মান্যগণ্য ব্যক্তির কাছেই আসতোঃ
“তারা বলেঃ এই কুরআন দুই জনপদের কোনো নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির কাছেই নাযিল হলো না কেন? [সূার যুখরুফঃ ৩১]
আবু জাহেল মনে করতো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবূয়্যতের দাবী করে নিজের গোত্রের জন্য আরো একটি গৌরব বৃদ্ধি করতে চান। সে বলতোঃ
“আমাদের আর বনু আবদে মানাফের সাথে বসকিছুতেই প্রতিযোগিতা হতো। ঘোড় দৌড়ে, গণভোজনের আয়োজনে ও দান দক্ষিণায় তাদের সাথে আমরা সমান ছিলাম। এখন তারা বলছে, আমাদের এক ব্যক্তির কাছে ওহি আসা শুরু হয়েছে। খোদার কছম, আমরাতো মুহাম্মদকে কখনো নবী মানবোনা।”
এটা আবু জাহেলেরই বক্তব্য ছিলোনা; বরং কোরেশ বংশীয় সকল মোশরেকদের দৃষ্টিতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীতে দীনে এই একটাই ‘খুত’ ছিলো যেঃ
“মুহাম্মদের ধর্ম কোরেশ বংশকে তার বংশীয় আভিজাত্য ও দেশীয় গৌরব থেকে বঞ্চিত করবে এবং তার আরবীয় আভিকাত্য বিনষ্ট করবে। তার দৃষ্টিতে ছোট বড় সব সমান এবং সে নিজের ভৃত্যের সাথে একসাথে বসে আহার করে। সে আরবের সম্ভ্রান্ত লোকরেদ মর্যাদা বোঝেনা, হাবশীদের সাথেও সে মিলে মিশে চলে। সাদা কালো সবাইকে সে একাকার করে ফেলেছে এবং সম্মানিত লোকদের সম্মান হানি করেছে।”
এ কারণে কোরেশ বংশের সকল গোত্র বনু হাশেম গোত্রের ওপর ক্ষুব্ধ হয়। আর বনু হাশেমও এই গোত্রীয় আভিজাত্যবোধের ভিত্তিতেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্র্রতি সমর্থন জানায় অথচ তাদের অধিকাংশই মুসলামন ছিলোনা। ‘শিয়াবে আবু তালেব’ নামক গীরিবর্তে বনু হাশেমকে এ কারণেই অবরুদ্ধ করে রাখা হয় এবং সমগ্র কোরেশ বংশ তাদেরকে বয়কট করে। যেসব মুসলামানের গোত্র দুর্বল ছিলো, তারা ভয়াবহ নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আবিসিনিয়ার হিজরত করতে বাধ্য হয়। আর যাদের গোত্র শক্তিশালী ছিলো, তার ইসলামের পক্ষাবলম্বনের জন্য নয় বরং গোত্রীয় শক্তির কারণে কোরেশ বংশের অত্যাচার থেকে কিছুটা নিরাপদ থাকে।
আরবের ইয়াহুদীরা বনী ঈসরাইলী নবীদের ভবিষ্যদ্বানীরি আলোকে বহুদিন যাবত একজন নবীর অপেক্ষায় ছিলো। তাদেরই প্রচারিত ভবিষ্যদ্বনীর ফল ছিলো এইযে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত প্রকাশ পাওয়ার পর মদীনার বহুসংখ্যক অধিবাসী ইসলাম গ্রহণ করে। অথচ খোদ্ ইয়াহুদীরা যে কারণে তাঁর প্রতি ঈমান আনা থেকে বিরত থাকে সেটি ছিলো এই বংশীয় আভিজাত্যবোধ। তাদের আপত্তি ছিলো এইযে, নবী যখনে এলেনই, তখন তিনি ইয়াহুদীদের মধ্য থেকে না এসে ইসমাইলের বংশধরের মধ্য থেকে এলেন কেন? এই বিদ্বেষ তাদেরকে এতো বেসামাল করে দেয় যে, তারা একত্ববাদীদের ছেড়ে মোশরেকদের সহযোগী হয়ে গেলো।
খৃষ্টানদের অবস্থাও ছিলো তদ্রুপ। তারাও একজন নবীর আগমনের অপেক্ষয় ছিলো। কিন্তু তাদের ধারণা ছিলো, তিনি সিরিয়ার খৃষ্টানদের মধ্য থেকে আবির্ভুত হবেন। আরবের কোনো নবীকে মেনে নিতে তারা প্রস্তুত ছিলোনা। হিরাক্লিয়াসের কাছে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বার্তা পৌঁছালো, তখন সে কোরেশ বণিকদের বললোঃ
“আমি জানতাম যে একজন নবীর আবির্ভাব আসন্ন হয়ে উঠিছে, কিন্তু তিনি যে তোমাদের মধ্য থেকে আবির্ভুত হবেনা এমনটি আশা করিনি।”
মিশরের মুফাওকিসের কাছে যখন ইসলামের দাওয়াত গেলো, তখন সে বললোঃ
“এখনো একজন নবী আসতে বাকী আছে, তাতো আমি জানি, তবে আমার আশা ছিলো যে, তিনি সিরিয়ায় আসবেন।”
অনারব বিশ্বেও এই জাত্যাভিমান তীব্রভাবে বিদ্যামান ছিলো। ইরানের শাহ খসরু পারভেজের কাছে যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহান দাওয়াতী চিঠি পৌঁছলো, তখন কোন্ কারণে সে আক্রোশে ফেটে পড়লো? সে কারণ ছিলো এটাই যে, “একটি গোলাম জাতির এক ব্যক্তির কিনা এতো স্পর্ধা যে, সে আযমের বাদশাকে এভাবে সম্বোধন করলো।” সে আরব জাতিকে নিকৃষ্টি জাতি মনে করতো। তাদেরকে সে নিজের অধীন মনে করাতো। এমন একটি জতির মধ্যে সত্যের দিকে আহবানকরী কোনো মানুষ জন্ম নিতে পারে তা সে ভাবতেও পারতোনা।
ইসলামের চরম শত্রু ইয়াহুদীদের কাছে ইসলামের প্রসার ঠেকানোর সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার ছিলো মুসলমানদের মধ্যে গোত্রীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার অপকৌশল। এ কারণেই মদীনার মোনাফেক তথা ভন্ড ও কপট মুসলমানদের সাথে তাদের গোপন যোগসাজশ ছিলো। একবার তার বুগাস যুদ্ধের প্রসংগ তুলে দুটো আনসার গোত্র আওস ও খাজরাজের মধ্যে বিদ্বেষের এমন আগুন জ্বালালো যে, উভয় পক্ষের তরবারী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। এই ঘটনা উপলক্ষে এ আয়াত নাযিল হয়ঃ
“হে মুমিনগণ! তোমরা যদি আহলে কিতাবের একটি গোষ্ঠীর কথামত চলো, তাহলে তারা তোমাদেরকে ঈমান থেকে কুফরির দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।” [সূরা আল ইমরান: ১০০]
এই একই বংশগত ও ভূখন্ডগত বিদ্বষের কারণে মদীনায় কোরেশী নবীর শাসন চলতে দেখে এবং আনসারদের খেজুরের বাগানে ও ফলের বাগানে মোহাজিরদের বিচরণ করতে দেখে মদীনার মোনাফিকরা তেলে বেগুণে জ্বলতে থাকতো। মোনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উপাই বলতো, “এই দরিদ্র কোরেশীরা আমাদের এখানে এসে আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছে। এদের উপমাহ হলো কুকুরকে খাইয়ে দাইয়ে মোটা তাজা বানানোর মতো যাতে কুকুর তার মালিককেকই ছিড়ে ভূঁড়ে খেতে পারে।”
সে আনসারদের বলতো: “তোমরা ওদেরকে মাথায় চড়িয়েছো। নিজেদের দেশে আশ্রয় দিয়েচো, নিজেদের সম্পদের ভাগ দিয়েছো। আল্লাহর কছম, আজ যদি তোমরা তাদের সাথে সহযোগিতা বন্ধ করো,তাহলে দেখবে ওরা ঘুরে বেড়াবে।” তার এসব উক্তির জবাব কুরআনে এভাবে দেয়া হয়েছে:
“এরাইতো সেইসব লোক যারা বলে, রাসূলুল্লাহর সংগীদের জন্যে অর্থ ব্যয় করোনা, যাতে তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। অথচ আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদের একমাত্র মালিক আল্লাহ্। কিন্তু মুনাফেকরা তা বোঝে না। তারা বলে, আমরা যদি [রণাংগন থেকে] মদীনায় ফিরে যাই তাহলে প্রতাপশালীরা দুর্বলদেরকে সেখান থেকে বহিষ্কার করবে। অথচ প্রতাপ ও প্রতিপত্তি মূলতঃ আল্লাহর, তার রসূলের এবং মুমিনদের। কিন্তু মোনাফেকরা তা জানেনা।” [সূরা মুনাফিকূন: ৭-৮]
এই স্বজাত্যবোধের অন্ধ আবেগই আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার ওপর অপবাদ আরোপ প্ররোচিত করে এবং এই আবেগের বশেই খাজরাজ গোত্রের সমর্থনে আল্লাহ ও রসূলের এই কট্টর দুশমন নিজের কৃতকর্মের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যায়।
গোষ্ঠীবাদ ও জাত্যাবিমানের বিরুদ্ধে ইসলামের জিহাদ
উপরোক্ত বিবরণ থেকে একথা ভালোভাবেই জানা গেছে যে, কুফরী ও শিরকের জাহেলিয়াতের পর ইসলামী দাওয়াত বিস্তারের সবচেয়ে বড় বাধা ও সবচেয়ে কট্টর দুশমন যদি কিছু থেকে থাকে তবে তা এই বংশ পূজা ও স্বাদেশিকতার শয়তান। আর এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুফরী ও শিরকের পরে যে জিনিসটার উচ্ছেদের জন্য সর্বাধিক চেষ্টা সাধনা করেছেন তা ছিলো জাহেলিয়াতের তৈরী এই জাত্যাভিমান। আপনি হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থাবলী পড়ে দেখলে বুঝতে পারবেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে রক্ত, মাটি, বর্ণ ও ভাষা এবং ইতর ও কুলীণের ভেদাভেদ নির্মূল করেছিলেন। কিভাবে মানুষে মানুষে বিরাজমান অস্বাভাবিক বৈষম্যের প্রাচীরগুলো ভেংগে চুরমার করেছিলেন এবং মানুষ হিসাবে সকল আদম সন্তানকে সমানাধিকার প্রদান করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা ছিলো:
“যে ব্যক্তি জাত্যাভিমান ও গোষ্ঠীবাদের জন্য প্রাণ দিলো, সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জাত্যাভিমানের প্রতি আহবান জানালো সে আমার দলভুক্ত নয়। যে ব্যীক্ত জাত্যাভিমান নিয়ে লড়াই করলো সে আমার দলভুক্ত নয়।”
“ধর্মপরায়ণতা ও খোদাভীতি ছাড়া আর কোনো জিনিসের ভিত্তিতে একজন অপর জনের ওপর অগ্রাধিকারের যোগ্য নয়। সকল মানুষ আদম আলাইহিস সালামের সন্তান এবং আদম আলাইহিস সালাম ছিলেন মাটির তৈরী।”
প্রজন্মবাদ, স্বাদেশিকতাবাদ, ভাষা ও বর্ণের বৈষম্য তিনি এই বলে নিশ্চিহ্ন করেন:
“অনারবদের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো অগ্রাধিকার বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তোমরা সবাই আদম আলাইহিস সালামের সন্তান।”
“কোন অনারবের ওপর আরবের, আরবের ওপর অনারবের, কালোর ওপর সাদার এবং সাদার ওপর কালোর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তবে শুধমাত্র সততা ও খোদাভীতির শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে।”
“শোনো ও আনুগত্য করো, এমনকি যদি তোমাদের আমীর এমন একজন নিগ্রো দাসকেও নিয়োগ করা হয়, যারমাথাটা কিশমিশের মতো কদাকার, তবুও।” [উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশ আরবের অভিজাত সরদার ও নেতাদের উদ্দেশ্যে জারী করা হয়েছিলো যে, তোমাদের আমীর কোনো নিগ্রো মুসলমানহলেও তাকেমেনে চলো। কোনো জাতীয়তাবাদী কি একথা কল্পনাও করতে পারে?]
মক্কা বিজয়ের পর যখন তরবাররির শক্তির সামনে কোরেশী সরদারদের গর্বিত মস্তক অবনমিত হলো, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে গোষণা করলেন:
“শুনে রাখো, কৌলীন্য ও আভিজাত্যের যেকোনো পুঁজি এবং রক্ত ও সম্পদের যেকোনো দাবী আমার পায়ের নিচে দাবিয়ে দিলাম।”
“হে কোরেশ: আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জাহেলিয়াতের জাত্যাভিমান এবং বাপ দাদার গৌরব গাথা নির্মল করে দিয়েছেন।
“ওহে মানব মন্ডলী! তোমরা সকলে আদম থেকে এসেছো আর আদমের জন্ম হয়েছে মাটি থেকে। বংশ নিয়ে গৌরবের কোনো অবকাশ নেই। কোনো অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। যে ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে সৎ ও খোদাভীরু, সেই সবচেয়ে বেশী সম্মানের পাত্র।”
আল্লাহর ইবাদাতেরপর তিনি আল্লাহর সামনে তিনটে জিনিসের সাক্ষ্য দিতেন। প্রথমতঃ “আল্লাহর কোনো শরীক নেই,” অতঃপর এই মর্মে সাক্ষ্য দিতেনযে, “মুহাম্মাদ সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লঅম আল্লাহর বান্দা ওরাসূল।” অতঃপর তৃতীয় যে বিষয়টির সাক্ষ্য দিতেন তাহলো এই যে, “আল্লাহর বান্দারা সবাই ভাই ভাই।”
ইসলামী জাতীয়তাবাদ ভিত্তি
জাহেলিয়াতের যে কয়টি সংকীর্ণ বস্তুগত, আবেগ প্রসূত ও কাল্পনিক ভিত্তির ওপর দুনিয়ার বিভিন্ন জাতীয়তার প্রাসাদ গড়ে উঠেছিলো, আল্লাহ ও তাঁর রসূল সেগুলিকেক নিশ্চিহ্ন করে দেন। মানুষ নিজের চরম অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণে বর্ণ, বংশ, জন্মভূমি, ভাষা অর্থনীতি ও রাজনীতির যেসব অযৌক্তিক ভেদাভেদ ও সৈষম্যের ভিত্তিতে মানব সমাজকে বিভক্ত করে রেখিছিলো ইসলাম সেগুলোর মূলোৎপাটিত করে এবং মানবতার ক্ষেত্রে সকল মানুষকে পরস্পরের সমমর্যাদা সম্পন্ন বলে ঘোষণা করে।
এই ভাংগার পাশাপাশি সে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত ভিত্তিতে একটি নতুন জাতীয়তা গড়ার কাজও সম্পন্ন করে। এ জাতীয়তার ভিত্তিও এক ধরনের বৈষম্যের ওপর স্থাপিত হয়েছিলো। তবে সেটা বস্তুগত ও ভৌতিক বৈষম্য নয় বরং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভেদাভেদ। সে মানুষের সামনে একটি স্বভাবসিদ্ধ সত্য পেশ করে যার নাম “ইসলাম।” সে আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্য, মনের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা এবং আমলেরসততা ও পরহেজগারীর প্রতি সকলকে দাওয়াত দেয়। তারপর জানিয়ে দেয় যে, এই দাওয়াতকে যে ব্যক্তি গ্রহণ করবে সে একটা জাতির অন্তর্ভুক্ত হবে আর যে ব্যক্তি প্রত্যাখ্যান করবে, সে একটা ভিন্ন জাতির সদস্যরূপে পরিগণিত হবে। এ দুই জাতির একটি ইসলামী জাতি এবং এর সকল ব্যক্তি মিলে একটা উম্মাত গঠিত হয়। পবিত্র কুরআনে এই উম্মাহকে মধ্যমপন্থী ও ভারসাম্যপূর্ণ উম্মাহ্ বলা হয়েছে।
“আমি এইভাবে তোমাদের সকলকে মধ্যমপন্থী উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত বানিয়ে দিয়েছি।
আর একটি জাতি কুফরি ও ভ্রষ্টতার জাতি হিসেব পরিচিত এবং এর অনুসারীরা নিজেদের মধ্যে তীব্র মতভেদ থাকা সত্ত্বেও একই গোষ্ঠী।
“আল্লাহর সত্য অস্বীকারকারীদের সুপথে পরিচালিত করেন না।”
উপরোক্ত দুটি জাতির মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি বর্ণ ও বংশ নয় বরং বিশ্বাস ও কাজ। এমনকি একই পিতার দুইছেলে ইসলাম ও কুফরীর বিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং সম্পূর্ণ অচেনা দুই ব্যক্তি ইসলামে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।
উক্ত জাতি দুটির মধ্যে পার্থক্যের ভিত্তি জন্মভূমির বিভিন্নতা নয়। এখানে পার্থক্য ও বিভেদ-বৈষম্যের ভিত্তি হলো হক ও বাতিল, যার কোন নির্দিষ্ট দেশ বা জন্মভূমি নেই। একই শহর, একই মহল্লা, এমনকি একই ঘরের দুই ব্যক্তির জাতীয়তা ইসলাম ও কুফরীর বিভিন্নতার কারণে বিভিন্ন হয়ে যেতে পারে। একজন নিগ্রো ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ হবার কারণ একজন মক্কাবাসীর স্বজাতিভুক্ত হয়ে যেতে পারে।
বর্ণের বিভিন্নতাও এখানে জাতিগত বিভেদের কারণ নয়। এখানে চেহারার বর্ণ কেমন তার কোনো গুরুত্ব ও মূল্য নেই। বরং গুরুত্ব হলো আত্মার রংয়ের এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ রং:
“আল্লাহর রং ধারণ করো। তার রংয়ের চেয়ে ভালো আর কার রং হবে?”
ইসলামের কারণে একজন শ্বেতাংগ ও একজন কালো মানুষ একই জাতিভুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং কুফরীর কারণে দু’জন সাদা মানুষেরও পৃথক পৃথক জাতীয়তা হওয়া সম্ভব।
ভাষার পার্থক্যও ইসলাম ও কুফরীর মধ্যে বিরোধের কারণ ঘটায়না। এক্ষেত্রে মুখের ভাষা নয়, মনের ভাষায় বিবেচ্য বিষয়। মনের ভাষা সারা পৃথিবীতেই প্রচলিত এবং সকলেই তা বোঝে। এ হিসেবে একজন আরব ও একজন আফ্রিকানের ভাষা একই হতে পারে। পক্ষান্তরে দু’জন আরবের ভাষা দু’রকম হতে পারে।
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্নতাও ইসলাম ও কুফরীর বিরোধে কোনো গুরুত্ব রাখেনা। এখানে বিতর্কের বিষয় টাকা নয়, ঈমানী সম্পদ। বিতর্কের বিষয় মানুষের রাজত্ব নয়, আল্লাহর সাম্রাজ্য। যারা আল্লাহর কর্তৃত্বের অনুগত এবং তাঁর কাছে নিজেদের জীবন বিক্রিয় করে দিয়েছে, তারা সবাই এক জাতিভুক্ত, চাই তারা ভারতের অধিবাসী হোক কিংবা তুর্কিস্তানের। আর যারা আল্লাহর কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা ওড়ায় এবং শয়তানের সাথে জান ও মালের ব্যাপারে আপোষ রফা করে তারা ভিন্ন জাতির লেক। তারা কোন্ রাষ্ট্রের নাগরিক এবং কোন্ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীন, তা এখানে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়।
এভাবে ইসলাম জাতীয়তার যে বৃত্ত একেঁছে, তা কোনো বস্তুগত বা ইন্দ্রিয় গোচর বৃত্ত নয়, বরং সম্পূর্ণ বুদ্ধিবৃত্তিক বৃত্ত। একই পরিবারের দুই ব্যক্তি এই বৃত্তে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে আবার পাশ্চাত্যের একজন ও প্রাচ্যের একজনের ভেতরে মিলিত হতে পারে। কবির ভাষায়:
এখানে ভালোবাসার সাথে রক্তের নেই কোনো সম্পর্ক
রোম, সিরিয়অ বা সেমিটিকের নেই কোনো ভেদাভেদ
এ নক্ষত্র প্রাচ্যেরও নয়, নয় পাশ্চাত্যের
এর না আছে অস্তাচল না সীমানায় উত্তর না দক্ষিণ।
এ বৃত্তকে যে জিনিস ঘিরে রেখেছে তা হচ্ছে কালেমা “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ।” এই কালেমাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে শত্রুতা ও বন্ধুতা। এই কালেমার স্বীকৃতি মিলনের পথ উন্মুক্ত করে আর অস্বীকৃতি নিয়ে যায় বিচ্ছেদের পথে। এ কালেমা যাদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে, তাদেরকে রক্তের সম্পর্কও একত্রিত করতে পারেনা, মাটির সম্পর্কও নয় এবং ভাষা, বর্ণ, খাদ্য কিংবা সরকারের অংশীদারিত্বও নয়। আর এই কালেমা যাদেরকে একত্রিত করেছে, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করার ক্ষমতা কারো নেই। কোনো নদনদী, পাহড় পর্বত, সমুদ্র, ভাষা, বংশ, বর্ণ এবং সম্পদ ও ভূমির বিরোধ ও বিভিন্নতার এ অধিকার ও ক্ষমতা নেই যে, ইসলামের অভ্যন্তরে বিভেদের রেখা এঁকে দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ বৈষম্য বা পার্থক্যের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক মুসলমান, চাই সে চীনের অধিবাসী হোক কিংবা মরক্কোর, সাদা হোক কিংবা কালো, হিন্দী বলুক বা আরবী, সেমিটিক হোক কিংবা আর্য, এক রাষ্ট্রের নাগরিক হোক কিংবা অন্য রাষ্ট্রের, সর্বাবস্থায় সে মুসলিলম উম্মাহর সদস্য, ইসলামী সমাজের সদস্য, ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক, ইসলামী সেনাবাহিনীর সৈনিক এবং ইসলামী আইনের সংরক্ষণ সুবিধার অধিকারী। ইসলামী শরীয়ত একটি বিধিও এমন নেই, যা ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন, সামাজিক আচার আচরণ, অর্থনীতি, রাজনীতি মোটকথা জীবনের কোনো একটি দিকেও জাতীয়তা, ভাষা বা জন্মভূমির ভিত্তিতে এক মুসলমানকে অপর মুসলমানের চেয়ে কম বা বেশী অধিকার দেয়।
ইসলামের মিলন ও বিচ্ছেদের নীতি
এরূপ ভুল ধারণা যেনো কারো মনে না জন্মে যে, ইসলাম যাবতীয় বৈষয়িক, সামাজিক ও মানবিক সুসম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করে দিয়েছে। কখ্খনো নয়। বরঞ্চ সে মুসলমানদের আত্মীয়তার বন্ধন অব্যাহ রাখা ও মজবুদ করার নির্দেশ দিয়েছে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করতে নিষেধ করেছে। মাতাপিতার আনুগত্য ও ফরমাবদরদারীর তাগিদ দিয়েছে। রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার ক্ষেত্রে সম্পত্তির উত্তরাধিকার চালু করেছে। দান সদকা ও বদান্যতায় আত্মীয় স্বজনকে অনাত্মীয়দের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। নিজের পরিবার পরিজন, ঘরদোর ও ধনসম্পদকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। যালেমের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলেছে এবং এ ধরনের লড়ইতে নিহত ব্যক্তিকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে। জীবনের সকল ব্যাপারে জাতিধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষের প্রতি সমবেদনা, সদাচর ও স্নেহমমতা প্রদর্শনের শিক্ষা দিয়েছে। তার কোনো বিধি বিধানের এমন ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই যে, ইসলাম স্বদেশ, স্বজাতির সেবা ও প্রতিরক্ষায় অবদান রাখতে নিষেধ করে, কিংবা অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথে আপোষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে বাধা দেয়।
[উল্লেখযোগ্য যে, অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের দুটো দিক রয়েছে। একটি দিক হলো, মানুষ হিসেবে আমরা ও তারা সমান। দ্বিতীয দিক এই যে, ইসলাম ও কুফরীর বিভিন্নতা আমাদেকে তাদের থেকে আলাদা করে দিয়েছ। প্রথম বিষয়টির বিচারেআমরা তাদের সাথে সহানুভূতি, উাদারতা, বদান্যতা ও সৌজন্যমূলক যাবতীয় সদাচার অব্যাহত রাখবো। কেননা এটা মানবতার দাবী। আর যদি তারা ইসলামের ও মুসলমানদের সক্রিয় দুশমন না হয়, তবে আমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব, আপোষ ওসহাবস্থানও করবো। যৌথ কল্যাণমূলক কাজে আমরা তাদেরসাথে সহযোগিতাও করতে দ্বিধা করবো না। কিন্তু কোনো বস্তুগত বা দুনিয়াবী, সামাজিক ও মানবিক যৌথ ও সম্মিলিত কর্মকাণ্ড আমাদেরকে তাদের সাথে এমনভাবে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে ফেলতে পারবে না যে, আমরাও তারা এক জাতিতে পরিণত হবো এবং ইসলামী জাতীয়তা পরিত্যাগ করে কোনো সম্মিলিত ভারতীয়, চৈনিক বা মিশরীয় জাতীয়তা গ্রহণ করবো। কেননা আমাদের সম্পর্কের দ্বিতীয় দিকটি এধরনের একত্রীকরণের বাধা দেয়। বস্তুতঃ কাফের ও মুসলমানদের মিলিত এক জাতিতে পরিণত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।]
এগুলো হলো এসব বস্তুগত ও পার্থিক সম্পর্কের বৈধ ও স্বাভাবিক সুবিধা। কিন্তু যে জিনিসটি জাতীয়তার ব্যাপারে ইসলাম ও কুফরীর নীতিকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দিয়েছে তা হলো, অন্যরা এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে আলাদা আলাদা জাতীয়তা তৈরী করে নিয়েছে, কিন্তু ইসাম এগুলিকৈ জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেনি। সে ঈমানের বন্ধনকে এ সকল সম্পর্কের ঊর্ধ্বে স্থান দেয় এবং প্রয়োজন হলে এসব সম্পর্কের প্রত্যেকটিকে ঈমানী সম্পর্কের জন্য বিসর্জন দেয়ার দাবী জানায়। তারা কথা হলো:
“তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাঁর সাথীদের মধ্যে অনুকরণীয় আদর্শ ছিলো। তারা তাদের জাতিকে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ্কে ছাড়া অন্য যাদের পূজা করো তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে বর্জন করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার সৃষ্টি হয়ে গেছে- যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনো।” [সূরা আল মুমতাহিনা: ৪]
সে আরো বলে!
“তোমাদের বাপ ও ভাইয়ের যদি ঈমানের চেয়ে কুফরীকে বেশী ভালোবাসে তবে তাদেরকেও প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করোনা। যারা তাঁদেরকে প্রিয়জন হিসেবে গ্রহণ করবে, তারা যালেম হিসেবে গণ্য হবে।” [সূরা আততাওবা: ২৩]
ইসলাম আরো বলেছে:
“তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান সন্ততীর মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু আছে [ইসলামের দৃষ্টিতে] কাজেই তাদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো।” [সূরা আত্তাগাবুন: ১৪]
সে বলে, যদি তোমাদের ধর্ম ও মাতৃভূমির মধ্যে বিরোধ বেঁধে যায়, তবে ধর্মের খাতিরে মাতৃভূমি ত্যাগ করে চলে যাও। যে ব্যক্তি দেশপ্রেমকে ধর্মপ্রেমের খাতিরে বিসর্জন দিয়ে হিজরত করেনা, সে মোনাফেক। তার সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই।
“যতক্ষণ তারা হিজরত না করে ততক্ষণ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করোনা।” [সূরা আননিসা: ৮৯]
এভাবে ইসলাম ও কুফরীর বিভেদের কারণে ঘনিষ্ঠতম রক্ত সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। শুধুমাত্র ইসলামের বিরোধী হওয়ার কারণে মাতা পিতা ভাইবোন ছেলে মেয়ে সবাই পার হয়ে যায়। আল্লাহর দুশমন হওয়ার কারণে একই বংশোদ্ভূত গোত্রকেও পরিত্যাগ করা হয়। ইসলাম ও কুফরীর সংঘাত চালু থাকার কারণে নিজের জন্মভূমিকেও পরিত্যাগ করা হয়। মোটকথা, দুনিয়ার সকল জিনিসের ওপর ইসলামকে কোনো কিছুর জন্যে বিসর্জন দেয়া যায়না। অপরদিকটিও লক্ষ করুন। যাদের ভেতরে রক্তের সম্পর্কও নেই, যাদের জন্মভূমিও এক নয়, ভাষাও এক নয় এবং যাদের সাথে বর্ণেরও মিল নেই, তাদেরকেও ইসলাম ভাই ভাই বানিয়ে দেয়। সকল মুসলমানকে সম্বোধন করে কুরআন বলে:
“তোমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরে রাখো। পরস্পরে বিভেদ বিচ্ছেদে ও কোন্দলে লিপ্ত হয়োনা। তোমাদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো যে, তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের হৃদয়ে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্র ও সম্প্রীতির সৃষ্টি করে দিলেন এবং তোমরা তাঁর অনুগ্রহে [ইসলামের বদৌলতে] পরস্পরের ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা [পারস্পরিক বিদ্বেষের দরুন] আগুন ভর্তি গহবরে কিনারে দাঁড়িয়েছিলে। আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে উদ্ধার করেছেন।” [সূরা আল ইমরান: ১০৩]
সকল অমুসলিম সম্পর্কে বলা হয়েছে:
“তারা যদি কুফরী থেকে তওবা করে, নামায পড়ে ও যাকাত দেয়, তবে তারা তোমাদের দীনি ভাই।”
আর মুসলমানদের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এভাবে:
“মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল। আর যারা তা সাথী তারা কাফিরদের সামনে অবিচল এবং পরস্পরের প্রতি দয়ার্দ্র।” [সূরা আল ফাতাহ: ২৯]
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:
“লোকেরা যতক্ষণ এই মর্মে সাক্ষ্য না দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রসুল, যতক্ষণ তারা আমাদের কিবলার দিকে মুখ না ফেরাবে, আমাদের যবেহ করা জন্তু না খাবে এবং আমাদের মতো নামায না পড়বে, ততক্ষণ তাদের সাথে যুদ্ধ করতে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখনই তারা এসব কাজ করবে, আমাদের ওপর তাদের রক্ত ও ধনসম্পদ নিষিদ্ধ হয়ে যাবে, তবে হক ও ইনসাফের খাতিরে যদি তা হালাল করা হয় তাহলে ভিন্ন কথা। এরপর তাদের অধিকার ও কর্তব্য অন্যসকল মুসলমানদের অধিকার ও কর্তব্যের মতোই।” [আবুদাউদ]
শুধু যে অধিকার ও কর্তব্যে সকল মুসলমান সমান তাই নয়, বরং তাতে কোনো পার্থক্য ও ভেদাভেদরও অবকাশ নেই। বরঞ্চ সেই সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন:
“মুসলমানের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক একটা প্রাচীরের বিভিন্ন অংশের মতো। প্রতিটি অংশ অপর অংশ থেকে শক্তি অর্জন করে।”[মিশকাত]
তিনি আরো বলেছেন:
“পারস্পরিক মমত্ব, সহানুভূতি ও দয়া দাক্ষিণ্যের দিক দিয়ে মুসলমানদের অবস্থা একটি একক দেহের মতো। দেহের একটি অংগ ব্যথা পেলে যেমন সমস্ত শরীরটারই নিদ্রা ও সুখশান্তি বিনষ্ট হয়ে যায়, তাদের অবস্থাও ঠিক তেমনি।” [মিশকাত]
মুসলিম জাতির এই দেহকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “জামায়াত” নামে আখ্যায়িত করেছেন এবং এই জামায়অত সম্পর্কে তিনি বলেছেন:
“জামায়াতের ওপর আল্লাহর হাত রয়েছে। যে ব্যক্তি জামায়অত থেকে বিচ্ছিন্ন হবে সে আগুনে যাবে।”
“যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামায়াত থেকে দূরে সরে গেলো সে নিজের গলা থেকে ইসলামের রজ্জু যেন খুলে ফেললো।”
শুধু এখানেই শেষ নয়। তিনি এ কথাও বলেছেন:
“যে ব্যক্তি তোমাদের জামায়াতকে খন্ড বিখন্ড করতে চেষ্টা করবে তাকে হত্যা করো।”
তিনি আরো বলেছেন:
“যে ব্যক্তি এই উম্মতের বন্ধনকে ছিন্নভিন্ন করতে উদ্যত হয়, তরবারী দিয়ে তাকে আঘাত করো তা সে যাই হোক না কেন।”
ইসলামী জাতীয়তা কিভাবে তৈরী হলো?
শুধুমাত্র ইসলামের ভিত্তিতে সংগঠিত এই জামায়াত বা দলের ভেতরে রক্ত, মাটি, ভাষা ও বর্ণের কোনো ভেদাভেদ ছিলোনা। এখানে ইরামেন সামলমা ছিলেন। তাঁকে কেউ পিতৃ পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন আমি ইসলামের ছেলে সালমান। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সম্পর্কে বলতেন, “সালমান আমাদের তথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বাযানকে ইয়অমানের এবং তাঁর ছেলেকে সানার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। এই জামায়াতে আবিসিনিয়ার অধিবাসী বিলালও ছিলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সম্পর্কে বলতেন: “বিলাল আমাদের মনিবের ভৃত্য এবং আমাদেন মনিব।” রোমের অধিবাসী সোহায়েবও ছিলেন এই জামায়াতের সদস্য। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাকে নিজের জায়গায় নামাযের ইমামতিতে দাঁড় করিয়েছিলেন। হযরত আবু হুযায়ফার গোলাম সালেমও এই সংগঠনের ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ওমর রাদিযাল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের ইন্তিকালের সময় বলেছিলেন যে, সালেম জীবিত থাকলে আমি তৃতীয় খলিফা হিসেবে তাকেই মনোনীত করতাম। এই জামায়াতে যায়েদ বিন হারেসা নামক এক গোলামও ছিলেন, যাঁর সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ ফুফাতো বেন যয়নব রাদিয়াল্লাহু তায়ালঅ আনহাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত যায়েদের ছেলে উসামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ছিলেন এই জামায়াতের আর এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উসামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে যে সেনাবাহিনীর সেনাপতি নিয়োগ করেছিলেন, তাতে সৈনিক হিসেবে শরীক হয়েছিলেন হযরত আবুবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহের মতো মর্যাদাবান সাহাবীগণ। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার নিজের ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে বলেছিলেন, “উসামার পিতা তোমার পিতার চেয়ে উত্তম এবং উসাম স্বয়ং তোমার চেয়ে উত্তম।”
মুহাজেরদের আদর্শ চরিত্র
রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে পরিচালিত এই মহান সংগঠন বংশ, জন্মভূমি, ভাষা ও বর্ণ ইত্যদি নামে যেসব মূর্তির পূজা আদিম জাহেলিয়াত থেকে শুরু হয়ে আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগেও অব্যাহত রয়েছে, সেগুলিকে ইসলামের কুড়াল দিয়ে ভেংগে গুড়িয়ে দেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং নিজের জন্মভূীম মক্কা ছেড়ে নিজের সংগী সাথীদের নিয়ে মদীনায় হিজরত করেন। এর দ্বারা একথা বুঝায়না যে, নিজ মাতৃভূমির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক ভালোবাসা থাকে, তা তাঁর ও মুহাজেরদের ছিলোনা। মক্কা থেকে বিদায় হওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন! “হে মক্কা, পৃথিবীতে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় স্থান। কিন্তু উপায় কি, তোমার অধিবাসীরা আমাকে এখানে থাকতে দিলোনা।” হযরত বিলাল যখন মদীনায় গিয়ে অসুস্থ হলেন, তখন মক্কার প্রতিটি জিনিসের কথা স্মরণ করেন। তাঁর আবৃত্তি করা কবিতার নিম্ন লিখিত লাইন কয়টি আজও প্রসিদ্ধ:
“হায়, যদি জানতে পারতাম, আর কোনোদিন ফাখ্ নামক জায়গায় রাত কাটাতে পারবো কিনা, যেখানে আমার পাশে সুগন্ধীযুক্ত আযখার ঘাষ এবং বাবুনার চারাগাছগুলো শোভা পাবে। আর আমি কোনোদিন মাজাতার [জায়গার নাম] ঘাটেও উপস্থিত হতে পারবো কিনা, যেখান থেকে শামা নামক পাহাড় ও তোফায়েল নামক জায়গা দেখা যাবে।”
কিন্তু তথাপি তাঁদের দেশপ্রেম তাদেরকে ইসলামের খাতিরে দেশত্যাগে বিরত রাখতে পারেনি। [“দেশপ্রেম ঈমানের অংগ” এইমর্মে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বানোয়অট হাদীস বর্ণিত আছে। আসলে এধরনের কোনো বিশুদ্ধ হাদীস রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত নেই।]
আনসারদের দৃষ্টান্ত
অপরদিকে মদীনার অধিবাসীরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং মুহাজেরদেরকে সাদরে গ্রহণ করলো। তাঁরা তাঁদের জানমাল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করে দিলো। এ কারণেই হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, “মদীনা কুরআন দ্বারা বিজিত হয়েছে।” রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসার ও মুহাজেরগণকে পরস্পরের ভাই বলে ঘোষণা করলে তাঁরা এমন ভাই ভাই হলেন যে, দীর্ঘদিন যাবত তারা একে অপরের উত্তরাধিকার পেতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করলেন:
“রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা উত্তরাধিকার লাভের ব্যাপারে পরস্পরের অধিকতর হকদার।”
এই আয়াত নাযিল করে এই উত্তরাধিকার বন্ধ করে দেন। আনসারগণ নিজেদের ক্ষেত ও বাগান পর্যন্ত অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে আপন মুহাজের ভাইদেরকে প্রদান করেন। এমনকি যখন ইহুদী গোত্র দ্বারা বনুনাযীরের ভূসম্পত্তিসমূহ হস্তগত হলো, তখন তাঁরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, “এসব জমিও আমাদের মুহাজের ভাইদের দিয়ে দিন।” এই ত্যাগ ও কুরবানীর প্রশংসা করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন:
“তারা স্বয়ং অভাবী হওয়া সত্ত্বেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।”
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এবং হযরত সা’দ বিন রবীয়া আনসারীর মধ্যে যখন দীনী ভ্রাতৃত্বের চুক্তি সম্পাদন করা হলো, তখন হযরত সা’দ তার দীনী ভাইদের জন্য সম্পত্তির অর্ধেক দিলেন এবং নিজের স্ত্রীদের মধ্য থেকে একজনকে তালাক দিয়ে তার সাথে বিয়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে গেলেন। রিসালাত যুগের পর যখন মুহাজিরগণ একের পর এক খিলাফতের পদ অলংকৃত করতে লাগলেন, তখন কোনো মদীনাবাসী একথা বলেনি যে, তোমরা বহিরাগতরা কোন্ অধিকারে আমাদের দেশ শাসন করছো? এমনকি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং দ্বিতীয় খলীফা ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু যখন মদীনার আশপাশে মুহাজেরদেরকে ভূসম্পত্তি বরাদ্দ করেন। তখনও কোনো আনসারী টু শব্দটিও করেনি।
ইসলামী সম্পর্কের জন্য পার্থিব সম্পর্কের কুরবানী
বদর যুদ্ধে ও ওহুদ যুদ্ধে মক্তা থেকে আগত মুহাজিরগণ ইসলামের জন্য আপন আত্মীয় স্বজনের সাথে যুদ্ধ করেন। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের ছেলে আব্দুর রহমানের ওপর তরবারী উত্তোলন করেন। হুযায়ফা নিজের পিতা আবু হুযায়ফাকে আক্রমণ করেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু নিজের মামাকে হত্যা করেন। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস, চাচাতো ভাই আকীল ও জামাতা আবুল আ’স বদরে যুদ্ধবন্দী হন এবং তাদেরকে সাধারণ কয়েদীদের মতো রাখা হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুতো সকল বন্দীকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রত্যেক মুসলমান নিজ নিজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে নিজ হাতে হত্যা করুক- এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
মক্কা বিজয়ের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন এলাকার লোকদেরকে নিয়ে নিজ মাতৃভূমির ওপর হামলা চালান এবং বহিরাগতদের হাতে কতিপয় মক্কাবাসীকে হত্যা করান। কোনো ব্যক্তি নিজ গোত্র ও নিজ মাতৃভূমির ওপর অপর গোত্রের লোকজন দিয়ে আক্রমণ করাবে, আর তাও কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রাপ্য ভূমি সহায় সম্পদ উদ্ধারের উদ্দেশ্যে নয় বরং নিছক একটি সত্যের কলেমা ও আদর্শের খাতিরে। এটা তৎকালীন আরব জনগণের কাছে একেবারেই অভাবনীয় ব্যাপার ছিলো। যখন কুরাইশ ও অন্যান্য গোত্রের গুন্ডাপান্ডারা মারা যেতে লাগলো, তখন আবু সুফিয়ান মিনতি জানালো যে, “হে রসূল! কুরাইশ বংশের তরুণ প্রজন্ম নিহত হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আজকের পর আর কুরাইশ বংশের নাম নিশানা থাকবেনা।” এ কথা শুনে দয়াল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৎক্ষণাত মক্কাবাসীকে নিরাপত্তা দান করলেন। আনসারগণ ভাবলেন, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের গোত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন। তাদের কেউ কেউ বললো: “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো মানুষই। নিজের গোষ্ঠী গোত্রের প্রতি মায়ামমতা তো দেখাবেনই।” এসব কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলো। তিনি আনসারদেরকে সমবেত করে বললেন! “নিজ গোত্রের ভালোবাসা আমাকে কখনো আকৃষট করেনি। আমি আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হিজরত করে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। এখন আমার বাঁচা মরা সবই তোমাদের সাথে হবে।” রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার বলা এই কথাগুলো অক্ষরে অক্ষরে সত্য করে দেখালেন। যে কারণে তিনি হিজরত করেছিলেন, মক্কা বিজয়ের পর সে কারণ আর অবশিষ্ট ছিলোনা। কিন্তু তবুও তিনি মক্কায় থেকে যাননি, এ দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো প্রতিশোধমূলক মনোভাব বা মাতৃভূমি পুনরুদ্ধারের আবেগ নিয়ে মক্কার ওপর আক্রমণ চালাননি, বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো শুধুমাত্র আল্লাহর কালেমাকে তথা তাঁর দীনকে বিজয়ী করা।
এরপর যখন হাওয়াযেন ও সাকীফ গোত্রদ্বয়ের জমি ও সহায়সম্পদ মুসলমানদের দখলে এলো, তখন পুনরায় সেই একই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলো। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গনীমত হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদের বেশীর ভাগ কুরাইশ বংশের নওমুসলিমদেরকে দিলেন। আনসারদের কতক তরুণ মনে করলেন, এসব কিছু নিজ গোত্রের লোকদেরকে খুশী করার জন্য করা হচ্ছে। তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে বললন! “আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাফ করুন। তিনি কুরাইশদেরকে দান করেন আর আমাদেরকে বঞ্চিত করেন। অথচ এখনো আমাদের তরবারী থেকে তাদের রক্ত ঝরছে।” একথা জানতে পেরে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাদেরকে ডেকে একত্রিত কররেণ এবং বললেন:
“আমি তাদেরকে এজন্য বেশী দিচ্ছি যে, তারা নতুন নতুন ইসলাম গ্রহণ করেছে। শুধু তাদের মনকে প্রীত করাই আমার উদ্দেশ্য। তোমরা কি এতে খুশী নও যে, এরা দুনিয়ার সম্পদ নিয়ে যাক, আর তোমরা আল্লাহর রসূলকে নিয়ে যাও?”
বনুল মোস্তালিক যুদ্ধে গিফারী গোত্রের জনৈক মুসলিম এবং আওফী গোত্রের অপর এক মুসলিম যুবকের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেলো। উত্তেজনার এক পর্যায়ে গিফারী আওফীকে থাপ্পর মেরে বসলো। এতে আওফী আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকলো, আর গিফারী ডাকলো মোহাজেরদেকে। দু’পক্ষের মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্শের আশংকা দেখা দিল। রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে উভয়পক্ষকে ডেকে বললেন, “তোমরা এ কি ধরনের জাহেলী ধাঁচের ডাকাডাকিতে লিপ্ত হয়ে গেলে?” সাহাবীরা বললেন, “জনৈক মোহাজর জনৈক আনসারীকে প্রহার করেছে।” রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তাই বলে জাহেলিয়অতের রীতি অনুসারে গোষ্ঠী গোত্রের নাম ধরে ডাকাডাকি করোনা। এটা বড়ই ঘৃণ্য রীতি।”
এই যুদ্ধে মদীনার নামকরা জাতীয়তাবাদী নেতা আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইও অংশ গ্রহণ করেছিলো। সে যখন শুনলো, মুহাজের পক্ষের লোক আনসার পক্ষের লোককে মেরেছে, তখন সে আনসার পক্ষকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বললো! “এই মোহাজেররা আমাদের দেশে এসে আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। এখন আমাদের সামনেই মাথা তুলছে। ওরা প্রবাদবাক্যের সেই কুকুরের মতো, যাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাতাজা বানানো হয়েছিলো যাতে সে তার মনিবকেই ছিড়েভুরে খেতে পারে। খোদার কছম, মদীনায় ফিরে যাওয়ার পর আমাদের মধ্যে যারা প্রভাবশালী, তারা দুর্বলদেরকে ওখান থেকে বের করে দেবে।” তারপর সে আনসারদেরকে বললো: “তোমাদের কি এমন ঠেকা পড়েছিলো যে ওদের নিজেদের দেশে আশ্রয় দিলে এবং নিজেদের ধনসম্পদ তাদেরকে বন্টন করে দিলে? আল্লাহর কছম, তোমরা যদি আজ ওদের সাহায্য সহযোগিতা বন্ধ করে দাও, তবে ওরা শুধু বাতাস খেয়ে বেড়াবে।” এসব কথা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে গেলে তিনি তার পুত্র হযরত আব্দুল্লাহকে জানালেন, তোমার বাবা এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। হযরত আব্দুল্লাহ তাঁর পিতাকে এতোই ভালোবাসতেন, তিনি গর্ব করে বলতেন, খাজরাজ গোত্রে কোনো ছেলে তার বাবাকে তাঁর মতো ভালোবাসেনা। কিন্তু এই ঘটনা শুনে তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, “হে আল্লাহর রসূল! আপনি আদেশ দেনতো এক্ষুনি ওর মাথা কেটে আনি।” রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: না। তথাপি যুদ্ধ থেকে মদীনায় ফির এসে হযরত আব্দুল্লাহ নিজের পিতার সামনে খোলা তলোয়ার নিয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত তোমাকে মদীনায় ঢুকতে দেবোনা। তুমি বলেছো, প্রভাবশালীরা দুর্বলদেরকে মদীনা থেকে বের করে দেবে। এখন তুমি জানতে পারবে, যাবতীয় প্রতাব ও মানসম্মান শুধু আল্লাহ ও তাঁর রসূলের।” এই পরিস্থিতিতে ইবনে উবাই এই বলে চেচাঁমেচি শুরু করে দিলো যে, “ওহে খাজরাজ গোত্র! দেখো, আমার ছেলে আমাকে বাড়ীতে ঢুকতে দিচ্ছেনা।”সাধারণ মুসলমানরা এসে হযরত আব্দুল্লাহকে অনেক বুঝালেন। কিন্তু তিনি বললে: “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি ছাড়া সে মদীনার ছায়ার নিচেও আশ্রয় নিতে পারবেনা।” অবশেষে লোকেরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে হাজির হয়ে ঘটনার কথা জানালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: “তোমরা আব্দুল্লাহকে বলো সে যেনো তার বাবাকে বাড়ীতে ঢুকতে দেয়।” আব্দুল্লাহ এ আদেশ শুনে তরবারী রেখে দিয়ে বললেন,! “রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আদেশ দিয়েছেন তখন সে যেতে পারে।” [এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ তাফসীরে ইবনে জারীরে (২৮শ খণ্ড, ৬৬-৭০ পৃঃ) দেখুন।]
বনু কাইনুকা নামক ইহুদী গোত্রের ওপর যখন হামলা করা হলো, তখন হযরত উবাদা ইবনুস সামিতকে তাদের ব্যাপারে শালিশ মানা হলো। তিনি সমগ্র ইহুদী গোত্রটিকে মদীনা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিলেন। বনু কাইনুকা গোত্র হযরত উবাদার গোত্র খাজরাজের মিত্র ছিলো। কিন্তু তিনি এই সম্পর্কের কোনো তোয়াক্কা করলেননা। অনুরূপভাবে বনু কুরাইযার ব্যাপারে হযরত সা’দ বিন মায়া’যকে শালিশ মানা হয়। আওস গোত্রের সরদার সা’দ বিন মায়া’য আদেশ দিলেন, বনু কুরায়যার সকল পুরুষকে হত্যা, সকল নারী ও শিশুকে যুদ্ধবন্দী এবং তাদের সমস্ত ধনসম্পদ গনীমত হিসেবে বাজেয়াপ্ত করা হোক। এক্ষেত্রে বনু কুরায়াযা ও আওস গোতের মধ্যে যে দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রীর সম্পর্ক ছিলো, তার প্রতি তিনি কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করলেননা। অথচ তৎকালীন আরব সমাজে মৈত্রীর গুরুত্ব কিরূপ ছিলো তা সবার জানা। তাছাড়া ইহুদী গোত্র বনু কুরায়াযা মদীনায় শত শত বছর যাবত আনসারদের প্রতিবেশীও ছিলো।
ইসলামী জাতীয়তাবাদ আসল প্রাণশক্তি
উল্লিখিত উদাহরণসমূহ থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে জানা যাচ্ছে যে, ইসলামী জাতীয়তা বিনির্মাণে বংশ,বর্ণ, ভাষা ও বাসভূমির আদৌ কোনো অবদান নেই। যে নির্মাতা এই প্রাসাদের নির্মাণকার্য সম্পন্ন করেছেন, তার চিন্তা ও পরিকল্পনা সারা দুনিয়ার চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন ও অভিনব। তিনি সমগ্র মনুষ্যজগতের কাঁচা মালের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং যেখানে যেখানে উত্তম ও মজবুত মালমশলা পেয়েছেন সেখান থেকে তা বাছাই করে নিয়েছেন। এসব বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে যে জিনিস দ্বারা পরস্পরের সাথে গেঁথে পাকাপোক্ত করেছেন তা হচ্ছে আমলে সালেহ ত থা সৎকর্ম ও নির্মল চরিত্ররূপী মজবুত চুন। এভাবে তিনি এমন এক বিশ্বজোড়া জাতীয়তাবার প্রাসাদ তৈরী করলেন, যাসমগ্র পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত। এই সুবিশাল প্রাসাদকে স্থায়ীভাবে টিকিয়ে রাখতে হলে বর্ণ, বংশ, উৎপত্তির উৎস ও বাসস্থান নির্বিশেষে এর সকল অংশকে নিজ নিজ পৃথক উৎপত্তির উৎসগুলোকে ভুলে গয়ে একটি মাত্র উৎসকে মনে রাখতে হবে। নিজেদের পৃথক পৃথক বর্ণকে ভুলে গিয়ে একটি মাত্র রং-এ রঞ্চিত হতে হবে এবং নিজেদের আলাদা আবাসভূমিকে ভুলে গিয়ে একটি মাত্র সত্যের আবাসে প্রবেশ করতে হবে। এই আদর্শিক ঐক্যই এই শীষা ঢালা গাঁথুনির প্রাণ। এই ঐক্য যদি ভেংগে যায়, ইসলামী আদর্শিক জাতির অংশগুলোর মধ্যে যদি নিজেদের উৎপত্তি স্থলগুলোর বিভিন্নতা, প্রজাতিক ও বংশীয় ধারার বিভিন্নতা, নিজ নিজ আবাস ও জন্মস্থানের বিভিন্নতা, নিজেদের দেহের বর্ণ ও আকৃতির বিভিন্নতা এবং নিজেদের পার্থিব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি জাগে, তাহলে এই প্রাসাদের দেয়ালে ফাটল ধরবে, এর ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যাবে এবং এর সকল অংশ ছিন্ন ভিন্ন ও খান খান হয়ে ধ্বসে পড়বে। একটি সাম্রাজ্যে যেমন একাধিক সাম্রাজ্য বা একটি রাষ্ট্রে একাধিক রাষ্ট্র হওয়া সম্ভব নয়, তেমনি একটি জাতীয়তার মধ্যে কয়েকটি জাতীয়তার সৃষ্টি সম্ভব নয়। ইসলামী জাতীয়তার মধ্যে কয়েকটি জাতীয়তার সৃষ্টি সম্ভব নয়। ইসলামী জাতীয়তার অভ্যন্তরে বর্ণ, বংশ, ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক আলাদা আলাদা জাতীয়তার সমাবেশ একেবারেই অসম্ভব। এই দুই ধরনের জাতীয়তার যে কোনো একটিই টিকেক থাকতে সক্ষম। আল্লামা ইকবালের ভাষায়:
“বর্ণ, বংশ, ভাষা ও বাসভূমি ইত্যাদি ভিত্তিক জাতীয়তার পোশাক ইসলামী জাতীয়তার জন্য কাফন স্বরূপ।” সুতরাং যে ব্যক্তি মুসলমান আছে এবং মুসলমান থাকতে চায়, তাকে ইসলামী জাতীয়তা ছাড়া অন্যসব জাতীয়তার চেতনা প্রত্যাখ্যান এবং মাটি ও রক্তের সম্পর্কগুলোকে ছিন্ন করতেই হবে। এসব সম্পর্ককে যে বহাল রাখতে চায়, তার সম্পর্কে আমরা এটাই বুঝবো যে, তার হৃদয়ে ও অন্তরাত্মায় ইসলাম প্রবেশ করেনি। তার মনমগজে এখনো জাহেলিয়াত আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। আজ হোক কাল হোক, ইসলামকে সে বর্জন করবে এবং ইসলামও তাকে বর্জন করবেঃ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অন্তিম উপদেশ
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন জীবনের শেষভঅগে যে জিনিসটি সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী আশংকায় ভুগতেন, তা ছিলো, মুসলমানদের ভেতরে জাহেলিয়াতসুলভ গোষ্ঠীপ্রীতি তথা ভাষা, বর্ণ, বংশ ও ভূমি ভিত্তিক বিভেদ বৈষম্য ও আভিজাত্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে কিনা এবং তার কারণে ইসলামী জাতীয়তার বিশ্বজোড়া প্রাসাদ ভেংগে খান খান হয়ে যায় কিনা? এ আশংকাবোধ করেই তিনি বারবার বলতেন:
“আমার পরে তোমরা আবার যেনো কুফরীতে লিপ্ত হ’য়ে পরস্পরে মারামারি কাটাকাটি শুরু না করে দাও।” [বুখারী]
জীবনের শেষ বিদায় হজ্জ্বে গিয়ে স্বীয় আরাফাতের ভাষণে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে তিনি বলেন:
“শুনে নাও, জাহেলিয়াতের সকল জিনিস আজ আমার দুই পায়ের তলায় দলিত। অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তোমরা সবাই আদম সন্তান এবং আদম ছিলেন মাটির তৈরী। মুসলমান মুসলমানের ভাই এবং সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। জাহেলিয়াতের সকল দাবী রহিত করা হলো। এখন তোমাদের জান মাল ও সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের জন্য ঠিক তেমনি হারাম, যেমন আজকের দিন এই মাস এবং তোমাদর এই শহর হারাম।”
এরপর তিনি মীনাতে গিয়ে আরো জোর দিয়ে এই ভাষণের পুনরাবৃত্তি করেন এবং এই কথাটা সংযোজন করেন!
“দেখো, আমার পরে তোমরা গোমরাহীতে প্রত্যাবর্তন করে পরস্পরকে হত্যা করতে লেগে যেওনা। অচিরেই তোমরা আপন প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে এবং তোমাদের কাছে তোমাদের কাজের হিসাব চাওয়া হবে। শোনো কোনো নাককাটা হাবশীকেও যদি তোমাদের আমীর বানিয়ে দেয়া হয় এবং সে তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালিত করে, তবে তার কথা শুনো এবং আনুগত্য করো।”
একথা বলার পর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আমি তোমাদেরকে আল্লাহর বিধান দিয়েছি?” সমবেত জনতা বললো: হাঁ, হে রসূল! তখন তিনি বললেন! “হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো।” জনতাকে বললেন, “যারা উপস্থিত হয়েছে, তারা অনুপস্থিতদের কাছে আমার এ বাণী পৌঁছে দিও।” [বুখারী, মুসলিম, সীরাতে ইবনে হিশাম]
হজ্জ থেকে ফিরে ওহদের শহীদদের গোরস্তানে গেলেন এবং সমবেত মুসলমানদের বললেন:
আমি এ আশংকা করিনা যে, আমার পরে তোমরা পৌত্তলিকতায় লিপ্ত হবে, কেবল এই ভয় পাই যে, তোমরা দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে যাও কিনা এবং পরস্পরে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হও কিনা। এরূপ করলে তোমরা ধ্বংস হ’য়ে যাবে যেমন পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে।
ইসলামের জন্য সবচেয়ে মারাত্মক বিপদ
যে মারাত্মক বিপদটি সম্পর্কে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশংকা বোধ করেছিলেন, তা বাস্তবিক পক্ষেই দেখা দিয়েছিলো এবং তা যেমন ধ্বংসাত্মক হবে বলে তিনি পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন, তেমনি ধ্বংসাত্মকও প্রমাণিত হয়েছিলো। প্রথম শতাব্দী থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর যে বিপর্যয়ই এসেছে, এর কারণেই এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাই ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের মাত্র কয়েক বছর পরই হাশেমী ও উমাভী গোষ্ঠীবাদের ভয়াবহ সংঘাতময় পুনরুত্থান ঘটলো এবং তা ইসলামের আসল রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও অবকাঠামোকে চিরদিনের জন্য বিদ্ধস্ত করে দিলো। তারপর পুনরায় আরবীয়, অনারবীয় এবং তুর্কী আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আকারে আবির্ভূত হলো এবং তা ইসলামের রাজনৈতিক ঐককে ধ্বংস করে দিলো। এরপর বিভিন্ন দেশে যেসব মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলোর ধ্বংসের মূলেও এই একই বিভ্রান্তিকর মতবাদ সক্রিয় ছিলো। সাম্প্রতিককালে সবচেয়ে বড় দুটো মুসলিম সাম্রাজ্য ছিলো ভারতে ও তুরস্কে। এই দুটো সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করেছিলো ভৌগলিক, বংশীয়, বর্ণগত ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ। ভারতে মোগল ও ভারতীযদের পারস্পরিক বিদ্বেষ এবং তুরস্কে তুর্কী, আরব ও কুর্দী কোন্দল সাম্রাজ্যের পতন ঘটায়।
ইসলামের সমগ্র ইতিহাস পড়ে দেখুন। যেখানেই কোনো শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য আপনি দেখবেন, তার ভিত্তি বর্ণ বংশ নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতির রক্তের ওপর গড়ে উঠেছে। সেসব সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা, সেনাপতি, লেখক, সৈনিক, সবই ছিলো বিবিধ অঞ্চল ও বিবিধ ভাষা, বংশ ও বর্ণের মানুষ। আপনি দেখতে পাবেন ইরাকের মানুষ আফ্রিকায়, সিরিয়ার মানুষ ইরানে এবং আফগানিস্তানের মানুষ ভারতে অবিকল সেই ধরনের সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা নিয়ে মুসলিম সরকার সমূহের প্রাণপন সেবায় নিয়োজিত, যা নিয়ে তারা নিজ দেশের সরকারের সেবা করতো। মুসলিম সাম্রাজ্য ও রাষ্ট্রসমূহ কখনো নিজের জনশক্তি সংগ্রহে কোনো একটি দেশ বা একটি প্রজাতির ওপর নির্ভরশীল থাকতোনা। সকল জায়গা থেকে দক্ষ হাত ও প্রতিভাধর মস্তিষ্ক মুসিলম শাসকদের কাছে সমবেত হতো। তারা প্রত্যেক মুসলিম দেশকে নিজেদের দেশ মনে করতো। কিন্তু যখন স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বজাতিপ্রীতি ও গোষ্ঠীবিদ্বেষের ন্যায় বিপজ্জনক প্রবণতা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো এবং মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের উদার ভ্রাতৃত্ববোধের পরিবরেত বর্ণ বংশ ও ভূমিকেন্দ্রিক বৈষম্য ও সংকীর্ণতার উদ্ভব ঘটলো তখন পরস্পরকে ঘৃণা ও হিংসা করা শুরু হলো। দলাদলি, কোন্দল ও ষড়যনেত্রর প্রসার ঘটলো এবং যে শক্তি ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে ব্যয়িত হতো তা পরস্পরের বিরুদ্ধে ব্যয়িত হতে লাগলো। এক পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের বিস্তার ঘটলো এবং মুসলিম শক্তিগুলো পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হ’য়ে গেলো।
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ
পাশ্চাত্যের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে সকল দেশের মুসলমানরা আজ বংশীয়, ভৌগলিক, ভাষাভিত্তিক ও বর্ণভিত্তিক জাতীয়তাবাদের আওয়ায তুলছে। আরবরা তাদের আরবীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করছে। মিশরীয়দের মনে পড়ছে তাদের ফেরাউনদের কথা। তুর্কীরা তাদের তুর্কী ঐতিহ্য নিয়ে এতো মেটে উঠেছে যে, চেংগীজ ও হালাকু খানের সাথে নিজেদের যোগসূত্র স্থাপন করছে। ইরানীরা ইরানী হওয়ার আবেগে বলে বেড়াচ্ছে যে, আমাদের আসল জাতীয় হিরো তো ছিলো রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ার। কিন্তু আরব সাম্রাজ্যবাদ জোর করে হোসেন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুকে আমাদের হিরো বানিয়ে দিয়েছে। ভারতেও এমন মুসলমান জন্ম নিচ্ছে, যারা ভারতীয জাতীয়তাবাদের সাথে নিজেদের সংযোগ ঘটাতে তৎপর। এখানে এমন মুসলমানও আছে যারা যমযমের পানির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে গংগার পানির ভক্ত হতে চায়। এমন লোকও রয়েছে, যারা ভীম ও অর্জুনকে নিজেদের জাতীয় হিরো বানাতে ইচ্ছুক। এখানে এমন মুসলমানও রয়েছে যারা ভুলেও মক্তা মদীনাকে মনে করেনা, কিন্তু তক্ষশীলা, মহেনজোদারো ও হরপ্পার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে রাত দিন ব্যাকুল থাকে। কিন্তু এসব কিছু শুধু এজন্য হচ্ছে যে, এইসব মূর্খ লোকেরা নিজেদের সভ্যতাতেও চেনেনি। পাশ্চাত্য সভ্যতাকেও চেনেনি। উভয় সভ্যতার নিগুঢ় তত্ত্ব ও তথ্য তাদের চোখের আড়ালে রয়েছে। তারা নিছক বাহ্যদর্শী। বহিরাচরণে যে রেখাগুলো তাদের চোখে অধিকতর দর্শনীয় ও চমকপ্রদ মনে হয়, তার ওপরই তারা লুটিয়ে পড়তে থাকে। তারা একেবারেই জানেনা যে, পাশ্চাত্য জাতীয়তার জন্য যা অমৃত, ইসলামী জাতীযতাতর জন্য তা বিষতুল্য। পাশ্চাত্য জগতে বংশ, বর্ণ, ভাষা ও জন্মভূমিভিত্তিক জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত। তাই ভিন্ন গোত্র, ভিন্ন বংশ ও ভিন্ন ভাষার মানুষকে এড়িয়ে চলতে প্রত্যেকেই বাধ্য, চাই সে মানুষটি তার সীমান্ত থেকে মাত্র একমাইল দূরত্বেই অবস্থান করুক না কেনো। সেখানে এক জাতির মানুষ অন্য জাতির নিষ্ঠাবান সদস্য হতে পারে না। কোনো জাতি কোনো ভিন্ন জাতির লোকের ওপর আস্থা রাখতে পারেনা যে, সে নিজ জাতির স্বার্থের চেয়ে তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেবে। কিন্তু ইসলামী জাতীযতার ব্যাপারে ঠিক এর বিপরীত। এখানে জাতীযতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে জন্মভূমি ও বংশের পরিবর্তে বিশ্বাস ও কাজের তথা চরিত্রের ওপর। সারা দুনিয়ার মুসলমানরা পরস্পরের সহযোগী ও সুখ দুঃখের অংশীদার- তার জাতিগত পরিচয় যাই হোক না কেন। একজন ভারতীয় মুসলমান ভারতের যেমন বিশ্বস্ত নাগরিক, তেমনি মিশরেরও বিশ্বস্ত নাগরিত হতে পারে। একজন আফগান খোদ আফগানিস্তানের জন্য যেরূপ জীবনপণ যুদ্ধ করতে পারে, সিরিয়ার প্রতিরক্ষার জন্যও তদ্রুপ যুদ্ধ করতে পারে। তাই এক দেশের মুসলমানের সাথে আরেক দেশের মুসলমানের কোনো ভৌগলিক ও প্রজাতিক ভেদ বৈষম্যের কোনো কারণ নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি ও প্রজাতিক ভেদ বৈষম্যের কোনো কারণ নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি পাশ্চাত্যের মূলনীতির একেবারেই বিপরীত। ওখানে যা সবলতার উপকরণ, এখানে তা দুর্বলতার উপকরণ। এখানে যা জীবনী শক্তির উজ্জীবক, ওখানে তা প্রাণবিনাশী হলাহল। আল্লামা ইকবালের ভাষায়:
“পাশ্চাত্য জাতিগুলোর সাথে নিজের জাতির তুলনা করোনা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে গড়া এ জাতির গঠন প্রণালীটাই ভিন্ন রকমের। বংশ ও দেশের ওপর পাশ্চাত্যের জাতীযতা নির্ভরশীল, কিন্তু তোমার জাতীয়তা ধর্মের শক্তিতেই শক্তিমান।”
অনেকে এরূপ ভুল ধারণায় লিপ্ত আছে যে, ভৌগলিক বা বংশীয় জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হওয়ার পরও ইসলামী জাতীয়তার বন্ধন মুসলমানদের মধ্যে অটুট থাকতে পারে। এজন্য এই উভয় প্রকারের জাতীয়তা পাশাপাশি চলবে বলে তারা আত্মপ্রতারণায় লিপ্ত। তাদের ধারণা, দুটো একসাথে চলতে থাকলে একটি অন্যটি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবেনা, অধিকন্তু আমরা উভয়টির সুফল লাভ করবো। কিন্তু এ ধারণা নিছক অজ্ঞতা ও অপ্রতুল চিন্তার ফসল। আল্লাহ যেমন এক বুকেট দুটো হৃদয় স্থান করেননি। তদ্রুপ তিনি একই হৃদয়ে এক সাথে দুটো জাতীয়তার পরস্পর বিরোধী ও পরস্পর সংঘর্ষমুখর আবেগকে একত্রিত করার অবকাশও রাখেননি। জাতীয়তার অনুভূতির অনিবার্য ফল আপন পরের বিভেদ ও বৈষম্য। ইসলামী জাতীয়তার চেতনার স্বতস্ফূর্ত দাবী এই যে, মুসলমানকে আপন ও অমুসলিমকে পর মনে করা হবে। আর দেশভিত্তিক বা বংশভিত্তিক জাতীয়তার অনুভূতির স্বাভাবিক দাবী হলো, আপনি স্বদেশী ও স্বগোত্রীয়কে আপন এবং বিদেশী ও ভিন্ন গোত্রের বা বংশের লোককে পর মনে করবেন। এমতাবস্থায় এই দুটো অনুভূতি বা চেতনা কিভাবে একই জায়গায় এক সাথে সমবেত হতে পারে, তা কোনো বুদ্ধিমান ব্যাখ্যা করুক তো দেখি। এটা কিভাবে সম্ভব যে আপনি অমুসলিম স্বাদেশীকে আপনও ভাববেন, পরও ভাববেন আর বিদেশী মুসলমানকে এড়িয়েও চলবেন আবার তার ঘনিষ্ঠও হবেন? এই দুটো কি আদৌ একত্রিত হতে পারে? এরূপ বিপরীতমুখী চিন্তার অধিকারীদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা, আপনাদের মধ্যে একজনও কি সুস্থমনা লোক নেই?
সুতরাং একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, মুসলমানদের মধ্যে ভারতীয়, তুর্কী, আফগান, আরব, ইরানী ইত্যাদি হওয়ার অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার অর্থই হবে ইসলামী জাতীয়তার অনুভূতি ধ্বংস হওয়া এবং ইসলামী ঐক্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাওয়া। এটা শুধু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নয় বরং বহুবার এর বাস্তব দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হয়েছে। মুসলমানদের মধ্যে যখনই ভূীম বা দেশভিত্তিক কিংবা বংশভিত্তিক বৈষম্য ও বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়ে উঠোছে, তখনই মুসলমানের হাতে মুসলমান গলাকাটা অবধারিত হয়ে উঠেছে এবং “আমার পরে তোমরা কুফরির দিকে প্রত্যাবর্তন করে একে অপরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়োনা” রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই শংকা সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কাজেই জন্মভূমি বা দেশমাতৃকা কেন্দ্রিক জাতীয়তার প্রবক্তারা যদি এ জিনিসটির প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেই চান, তাহলে তাদের জন্য এটাই উত্তম হবে যে, তারা যেনো নিজেদেরকে ও বিশ্ববাসীকে ধোকা না দেন। বরং যাই করেন একথা জেনে শুনেই যেনো করেন যে, জন্মভূমি কেন্দ্রিক জাতীয়তার দাওয়াত আর যাই হোক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত নয়, বরং তার সম্পূর্ণ বিপরীত।
২. ইসলামী জাতীয়তার প্রকৃত তাৎপর্য
সাম্প্রতিকাকালে মুসলমানদের সমাজের জন্য ‘কওম’ বা জাতি শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আমাদের সামষ্টিক অবস্থাকে প্রকাশ করার জন্য সাধারণভাবে এই পরিভাষাটি কার্যত চালু হয়ে গেছে। কিন্তু এটা একটা বাস্তবতা যে, কুরআনও হাদীসে মুসলমানদের জন্য ‘কওম’ শব্দটি [অথবা জাতি বা নেশন বুঝাবার মতো আর কোনো শব্দকে] পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। তবে এ কথাও সত্য যে, কোনো মহল এ পরিস্থিতি থেকে নিজেদের অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা করেছে। যাই হোক, এই পরিভাষাটিতে এমন কি অসুবিধা রয়েছে, যার জন্য ইসলামে এটিকে গ্রহন করা হয়নি এবং কুরআন ও হাদীসে এর বিকল্প কোন্ কোন্ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা আমি সংক্ষেপে আলোচনা করবো। এটা নিছক কোনো তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, বরং এর দ্বারা আমাদের জীবনটাকে যে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছি, এমন কিছু ধ্যানধারণা স্পষ্ট হবে।
“কওম” শব্দটি এবং তার সমার্থক ইংরেজী শব্দ “নেশন” [Nation] বা জাতি মূলতঃ জাহেলিয়াতের ধ্যানধারণা থেকে উৎপন্ন অনৈসলামিক পরিভাষা। জাহেলী সমাজ ব্যবস্থার ধারক বাহক ও প্রতিষ্ঠাতাগণ “কওমিয়াত” বা [Nationality] বা জাতীয়তাকে কখনো খাঁটি সাংস্কৃতিক ভিত্তিক [Cultural Basis] ওপর দাঁড় করায়নি। প্রাচীন জাহেলিয়াতের যুগেও নয়, আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগেও নয়। তাদের মনমগজে বংশীয় ও ঐতিহ্যগত বন্ধনপ্রীতি এমনভাবে বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিলো যে, তারা জাতীয়তার ধারণাকে কখনো প্রজাতিক যোগসূত্র ও প্রাচীন ঐতিহ্য থেকে মুক্ত করতে পারেনি। প্রাচীন আরবে যেমন ‘কওম’ শব্দটি দ্বারা সাধারণত একটি বংশধর বা একটি গোত্রকে বুঝানে হতো, তেমনি আজও “নেশন’ Nation শব্দটি দ্বারা যে মনোভাব প্রকাশ করা হয় তাতে একক প্রজন্ম বা Common Descent এর ধারণা অনিবার্যভাবেই অন্তর্ভুক্ত থাকে। আর এ জিনিসটা যেহেতু মৌলিকভাবে ইসলামী জাতীয়তার ধারণার পরিপন্থী, তাই কুরআনে “কওম” এবং তার সমার্থক অন্যান্য আরবী শব্দকে মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরিভাষা হিসেবে প্রয়োগ করা হয়নি। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, যে মানবগোষ্ঠীর ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মূলে বর্ণ, বংশ, দেশ এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসের আদৌ কোনো হাত ছিলোনা, যে দলকে শুধুমাত্র একটি আদর্শ ও জীবনবিধানের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ করা হয়েছিলো এবং যার সূচনাই হয়েছিলো হিজরত, বংশীয় বন্ধন ও অন্যান্য পার্থিব সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্য দিয়ে, তার জন্য এমন শব্দ কিভাবে বা ব্যবহৃত হবে?
কুরআনে যে শব্দ মুসলমানদের সামষ্টিক সত্তার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, তাহলে “হিযব” বা দল। ‘কওম’ বা জাতির উৎপত্তি হয় জন্মসূত্রে ও বংশধর থেকে। কিন্তু দল গটিত হয় আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে। এদিক দিয়ে মুসলমানরা আসলে জাতি নয় বরং একটি দল। কেননা তাদেরকে শুধু এ কারণে সারা পৃথিবী থেকে স্বতন্ত্রভাবে পরস্পরের সাথে সংঘবদ্ধ করা হয়েছে যে, তারা একটা নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুসারী। আর এই নীতি ও আদর্শে যারা বিশ্বাসী ও অনুসারী নয়, তারা তাদের সাথে ঘনিষ্ঠতম পার্থিব আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তারা তাদের আপনজন নয় এবং তাদের সাথে কোনো মিল নেই। কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবীর গোটা মানব বসতির মাত্র দুটো দলই বিরাজ করে! একটি আল্লাহর দল হিযবুল্লাহ, অপরটি শয়তানের দল হিযবুশ শয়তান। শয়তানের দলে নীতি ও আদর্শের প্রশ্নে যতোই পারস্পরিক বিরোধ থাকুক না কেন, কুরআন তাদের সকলকে একই দলভুক্ত মনে করে। কেননা তাদের চিন্তা ও কাজের ধরন আর যাই হোক ইসলাম নয় এবং খুঁটিনাটি মতভেদ সত্তেও তারা সকলেই শয়তানের আনুগত্যের ব্যাপারে একমত। কুরআন ব লে:
“শয়তান তাদের ওপর বিজয়ী হয়ে গেছে। তাই সে তাদেরকে আল্লাহর সম্পর্কে গাফেল ও উদাসীন করে দিয়েছে। তারা শয়তানের দল। জেনে রেখো, শয়তানের দল শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবেই।” [সূরা আল মুজাদালা : ১৯]
পক্ষান্তরে আল্লাহর দলের লোকেরা যখন আল্লাহর শেখানো চিন্তা ও কর্মের বিধান মেনে নিতে সম্মত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখন তারা প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী রজ্জুতে পরস্পরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আল্লাহর দলভুক্ত হয়েছে এবং এই নয়া দলে প্রবেশ করা মাত্রই শয়তানের সাথে তাদের যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, চাই তারা জন্মগতভাবে যেকোনো বংশোদ্ভূত, যেকোনো দেশের অধিবাসী, যেকোনো ভাষাভাষী এবং যেকোনো ইতিহাস ঐতিহ্যের ধারক হোক না কেন, এসব ব্যাপারে তাদের পরস্পরে যতো বিভেধ পার্থক্য থাকুক না কেন, এমনকি তাদের বাপ দাদাদের মধ্যে চরম শত্রুতা থেকে থাকুক না কেন।
একজনের আল্লাহর দলভুক্ত হওয়া আর অপর জনের শয়তানের দলভুক্ত হওয়া যে দলগত ও আদর্শগত বিভেদ ঘটে, তা পিতা পুত্রের সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এমনকি পিতার উত্তরাধিকার থেকেও পুত্র বঞ্চিত হয়। হাদীসে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে:
“দুই ধর্মের অনুসারী পরস্পরের উত্তরাধিকারী হয়না।”
দলের তথা আদর্শের এই বিভিন্নতা স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমনকি মতভেদ হওয়া মাত্রই উভয়ের মেলামেশা হারাম হয়ে যায়। এর কারণ শুধু এই যে, উভয়ের জীবন যাপনের পথ আলাদা হয়ে গেছে। কুরআনে বলা হয়েছে:
“স্ত্রীরাও স্বামীদের জন্য হালাল নয়, স্বামীরাও স্ত্রীদের জন্য হালাল নয়।” [সূরা মুমতাহিনা: ১০]
দলের এই বিভিন্নতা একই পরিবারের এবং একই বংশের বা গোত্রের লোকদের মধ্যে পুরোপুরি সামাজিক বয়কটের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেয়। এমনকি আল্লাহর দলভুক্ত লোকের পক্ষে নিজের গোত্র ও বংশের মধ্যে যারা শয়তানের দলভুক্ত তাদের সাথে বিয়েশাদী করাও হারাম হয়ে যায়। কুরআন বলেছে:
“মুশরিক মহিলারা যতক্ষণ ঈমান না আনে তাদেরকে বিয়ে করোনা। মুমিন দাসী মুশরিক স্বাধীন মহিলার চেয়ে ভালো, চাই সে তোমাদের কাছে যতোই ভালো লাগুক না কেন। আর তোমাদের মেয়েদের মুশরিক পুরুষের সাথে বিয়ে দিওনা যতক্ষণ তারা ঈমান না আনে। মুমিন গোলাম মুশরিক স্বাধীন পুরুষের চেয়ে ভালো, সে তোমাদের কাছে যতই পছন্দনীয় হোক না কেন।” [সূরা আল বাকারা: ২২১]
দলের এই বিভিন্নতা ভৌগলিক ও বংশীয় সম্পর্ক শুধু ছিন্নই করেনা বরং উভয়ের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সৃষ্টি করে দেয় এবং এই দ্বন্দ আল্লাহ্র দল বহির্ভূতরা এই দলের আদর্শ ও নীতি মেনে না নেয়া পর্যন্ত বহাল থাকে। কুরআন বলে:
“ইবরাহীম ও তার সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের [জন্মসূত্রীয়] জাতিকে বলেছিলো, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসব উপাস্যকে পূজা করে থাকো তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি এবং আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরদিনের জন্য শত্রুতা বিরাজ করছে যতক্ষণ না তোমর এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। তবে ইবরাহীম যে তার কাফের পিতাকে বলেছিলো, ‘আমি তোমার ক্ষমার জন্য দোয়া করবো’, এতে কোনো আদর্শ নেই।” [সূরা মুহতাহিনা: ৪]
“ইবরাহীম যে নিজের পিতার গুনাহ মাফের জন্য দোয়া করেছিলো তা ছিলো পিতাকে ইতিপূর্বে দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি পূরণের জন্য। কিন্তু যখনই তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে তার পিতা আল্লাহর দুশমন, তখন সে ঐ দোয়া থেকে ফিরে এলো।” [সূরা আততাওবা: ১১৪]
দলের এই বিভিন্নতা একই পরিবারের লোকদের মধ্যে এবং ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে দেয়। এমন কি বাপ, ভাই কিংবা ছেলেও যদি শয়তানের দলভুক্ত হয়, তাহলে আল্লাহর দলভুক্তরা তার সাথে প্রীতি ভালোবাসা রাখলে আপন দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে বিবেচনা করা হবে। কুরআনে বলা হয়েছে:
“তুমি এমন কখনো পবেনা যে, কোনো দল আল্লাহ্ ও আখেরাতের ওপর ঈমানও পোষণ করে আবার আল্লাহ্ ও তার রাসূলের দুশমনদের সাথে সন্ধুত্বও রাখে, চাই তারা তাদের বাপ, ছেলে, ভাই কিংবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনই হোক না কেন। ….. এরাই আল্লাহর দলের লোক এবং জেনে রেখো, আল্লাহ্র দলই শেষ পর্যন্ত কল্যাণ লাভ করবে।” [সূরা মুজাদালা: ২২]
আল কুরআন মুসলমানদের জন্য অন্য যে শব্দটি ব্যবহার করেছে তা হলো ‘উম্মাহ’ এবং এটিও ‘দল’ বা ‘হিযব’ এরই সমর্থক। হাদীসেও এ শব্দের ব্যবহার হয়েছে। উম্মাহ্সেই দল বা সংঘকে বলে যা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সংঘটিত হয়েছে। যারা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে সমভাবে অংশীদার তাদেরকেও উম্মাহ বলা হয়ে থাকে। যেমন কোনো বিশেষ যুগের লোকদের ‘উম্মাহ’ বলা হয়। কোনো বিশেষ দেশের অধিবাসী এবং কোনো একটি প্রজন্মকেও উম্মাহ বলা হয়ে থাকে। মুসলমানদের যে বিষয়ে সম অংশীদারিত্বের জন্য উম্মাহ্ বলা হয়, তা কোনো প্রজন্ম, মাতৃভূমি বা অর্থনৈতিক লক্ষ্য নয় বরং তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তাদের দলের নীতি ও আদর্শ। কুরআন বলছে:
“তোমরা সেই শ্রেষ্ঠতম উম্মাহ, যাদেরকে মানবজাতির কল্যাণের জন্য তৈরী করা হয়েছে তোমরা সৎ কাজের আদেশ দিবে, অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখচে।” [সূরা আলে ইমরান: ১১০]
“এভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মাহ্ বানিয়েছি, যেনো তোমরা মানবজাতির তত্ত্বাবধায়ক হও এবং রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়।” [সূরা আল বাকারা: ১৪৩]
উপরোক্ত আয়অতগুলো নিয়ে ভাবুনস। “মধ্যপন্থী উম্মাহ্” দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, “মুসলমান” একটা আন্তর্জাতিক দলের [International Party] নাম। পৃথিবীর সকল জাতির মধ্য থেকে সেই লোকগুলোকে বেছে বের করে এই দল গঠন করা হয়েছে, যারা একটা বিশেষ আদর্শ ও নীতিমালা মেনে চলতে, একটা বিশেষ কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে এবং একটা নির্দিষ্ট মিশন বা ব্রত সম্পন্ন করতে প্রস্তুত। যেহেতু এই লোকগুলো সকল জাতির মধ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে এবং একটা দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর অন্য কোনো জাতির সাথে তাদের সম্পর্ক নেই, তাই তারা মাঝখানের উম্মাহ্। কিন্তু প্রত্যেক জাতির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সকল জাতির সাথে তাদের অন্য একটা সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং সেটি হলো, তাদেরকে দুনিয়াতে আল্লাহর আইন চালু করতে হবে। “তোমরা মানবজাতির তত্ত্বাবধায়কঃ কথাটা দ্বারা বুঝা হচ্ছে যে, মুসলমানরা আল্লাহর দুনিয়াতে আল্লাহর নিযুক্ত রক্ষী বা পাহারাদার। “মানব জাতির কল্যাণের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে” কথাটার স্পষ্ট বক্তব্য হলো, মুসলমানদের মিশন সারা পৃথিবী জোড়া মিশন। এই মিশনের সংক্ষিপ্ত সার হলো, আল্লাহর দলের নেতা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তায়ালা চিন্তা ও কর্মের যে বিধান দিয়েছিলেন, তাকে সকল মানসিক, নৈতিক ও বস্তুতগত শক্তি প্রয়োগ করে দুনিয়াতে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তার মোকাবিলায় অন্যসকল নীতি, আদর্শ ও বিধানকে পর্যুদস্থ ও পরাভূত করতে হবে। এই হলো সেই কাজ যা সম্পাদনের জন্য মুসলমানদের একটি উম্মাহ্ হিসেবে গঠন করা হয়েছে।
তৃতীয় যে পরিভাষাটি মুসলমানদের সামষ্টিক অবস্থা ও পদমর্যাদাকে বুঝানোর জন্য প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে, তাহলো “জামায়াত”। এটি ‘হিযব’ শব্দটির মতো দল বা পার্টির সমার্থক। বহু হাদীস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইচ্ছাকৃত ভাবেই ‘কওম’ বা শা’য়াব [জাতি] বা অনুরূপ অর্থবোধক শব্দগুলো প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং তার পরিবর্তে ‘জামায়াত’ শব্দটাই পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তিনি কখনো বলেননি যে, “সর্বদা ‘কওমের’ সাথে থাকো” বা “আল্লাহর হাত কওমের ওপর থাকে।” বরং এ ধরনের প্রতিটি কথায় তিনি ‘জামায়াত’ শব্দটিই ব্যবহার করেছেন। এর একমাত্র কারণ হলো, মুসলমানদের সংঘবদ্ধতা বা সমাজবদ্ধতার ধরনটি বুঝতে “কওম” [বা জাতির] তুলনায় ‘জামায়াত’ ‘হিযব’ এবং ‘উম্মাহ’ [তথা পার্টি বা দলই] অধিকতর উপযোগী। ‘কওম’ শব্দটা সাধারণভাবে যেসব অর্থে ব্যবহৃত হ’য়ে থাকে, সে অনুসারে কোনো ব্যক্তি যেকোনো আদর্শ, বা নীতির অনুসারী হোক না কেন, সর্বাবস্থায় একটা কওম বা জাতির অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যদি সে সেই কওমে বা জাতিতে জন্ম নিয়ে থাকে এবং নিজের নাম, জীবন যাপন প্রণালী ও সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে সেই কওম বা জাতির সাথে সংযুক্ত থাকে। কিন্তু জামায়াত, হিযব বা পার্টি এই শব্দগুলোর অর্থ পর্যালোনা করলে বুঝা যায়, শুধুমাত্র নীতি বা আদর্শই পার্টিতে বা দলে শামিল থাকেনা থাকার আসল মাপকাঠি। আপনি একটা দলের নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হওয়ার পর কখনো সেই দলে থাকতে পারেননা। ঐ দলের নামও ব্যবহার করতে পারেননা। তার প্রতিনিধিও হতে পারেননা, তার স্বার্থের তদারককারী হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করতে পারেননা। সে দলের লোকদের সাথে আপনার কোনো সহযোগিতার সম্পর্কও থাকতে পারেনা। আপনি যদি বলেন, দলের নীতি ও আদর্শের সাথে আমি তো একমত নই, তবে আমার মাতাপিতা এ দলের সদস্য ছিলেন এবং আমার নামের সাথে এই দলের সদস্যদের নামের মিল আছে। তাই আমার ও দলের সদস্যদের সমান অধিকার থাকা উচিত। তাহলে আপনার এই যুক্তি এতটা হাস্রকর হবে যে, শ্রোতারা হয়তো আপনার মাথা ঠিক আছে নাকি খারাপ হয়ে গেছে, তা নিয়েই সংশয়ে পড়ে যাবে। কিন্তু দলের অর্থকে জাতির অর্থ দ্বারা পাল্টে ফেলুন। এরপর এসব কথা আর আবোল তাবোল মনে হবেনা এসব কথা বলার অবকাশ সৃষ্টি হবে।
ইসাম তার আন্তর্জাতিক দলের সদস্যদের মধ্যে সংহতি ও একাত্মতা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচরণে সমতা ও সামঞ্জস্য সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে একক সমাজে পরিণত করার আদেশ দিয়েছিলো যে, নিজেদের মধ্যেই বিয়েশাদী করো। সেই সাথে তাদের সন্তানদে জন্য শিক্ষাদীক্ষার এমন ব্যবস্থা নির্দেশ করেছিলো যে, তারা আপনা আপনি দলের নীতি ও আদর্শের অনুসারী হয়ে গড়ে উঠবে। প্রচারের পাশাপাশি বংশধর বৃদ্ধির মাধ্যমেও দলের শক্তি বাড়তে থাকবে। এখান থেকেই এ দলের জাতিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পরবর্তীতে এক সাথে সমাজবদ্ধ জীবন যাপন, প্রজাতিক সম্পর্ক ও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ও ঐতিহ্য এই জাতীয়তাকে আরো শক্তিশালী করেছে।
এ পর্যন্ত যা কিছু হয়েছে ঠিকই হয়েছে। [একটি আদর্শবাদী দল স্বাভাবিক সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিকশিত হয়ে জাতিতেও রূপান্তরিত হয়েছে এতে দোষের কিছু ছিলোনা।] কিন্তু ক্রমে ক্রমে মুসলমানরা এই সত্যটিই ভুলে যেতে থাকলো যে তারা আসলে একটা আদর্শবাদী দল এবং দল হিসেবেই তাদের জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এই ভ্রান্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে পেতে এতোদূর গড়ালো যে, দলীয় ভাবধারা জাতীযতার ভাবধারায় একেবারেই বিলীন হয়ে গেলো। এ পর্যায়ে এসে মুসলমান শুধুই একটা জাতিতে পর্যবসিত হলো, অবিকল তদ্রুপ একটি জাতি, যেমন জার্মানরা, জাপানীরা ও ইংরেজরা এক একটা জাতি। তারা ভুলে গেছে যে, যে নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে ইসলাম তাদেরকে একটা উম্মাহ্ বানিয়েছিলো, সেই নীতি ও আদর্শই আসল জিনিস। যে দায়িত্ব বা মিশন সম্পাদনের জন্য ইসলাম তার অনুসারীদেরকে একটা দল বা পার্টি হিসেবে সংগঠিত করেছিলো, সেই দায়িত্ব ও মিশনই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এই সত্যকে ভুলে গিয়ে তারা অমুসলিম জাতিগুলোর কাছ থেকে জাতীয়তার জাহেলী ধারণা গ্রহণ করেছে। এটি এমন মৌলিক ভ্রান্তি এবং এর কুফল এতো ব্যাপক বিস্তৃত যে, এ ভ্রান্তি দূর না করা পর্যন্ত ইসলামের পুনরুজ্জীবনে এক কদমও অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়।
একটি দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, সাহায্য ও সহযোগিতা যাই হয়, ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে হয়না বরং শুধুমাত্র একই নীতি ও আদর্শের বিশ্বাস ও আনুগত্যের কারণে হয়ে থাকে। দলের কোনো সদস্য যদি দলীয় আদর্শ ও মূলনতি লংঘন করে, তাহলে দলের অন্যরে ওপর তাকে সাহায্য করাতো কর্তব্য থাকেইনা, উপরন্তু দলের এ ধরনের বিশ্বাসঘাতকসুলভ বিদ্রোহাত্মক কর্মমাণ্ড থেকে তাকে নিষেদ করাই কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। নিষেধ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে দলীয় কার্যবিধি অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এরপরও যদি না মানে তবে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা উচিত। দুনিয়ায় এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে যে, যেব্যক্তি দলীয় নীতি ও আদর্শের মারাত্মক বিরুদ্ধাচরণ করে তাকে হত্যাও করা হয়। [একারণেই ইসলামে মুরতাদ বা ধর্মত্যাগীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়ে থাকে। রুশ সমাজতন্ত্রীরাও সমাজতন্ত্র ত্যাগীদেরকে এই শাস্তিই দিতো। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন: “ইসলামে মুরতাদের শাস্তি” রচনা মাওলানা আবুল আ’লা মওদুদী। -সম্পাদক] কিন্তু মুসলমানদের অবস্থাটা একটু দেখুন যে, নিজেদেরকে আদর্শবাদী দলের পরিবর্তে জাতি অর্থাৎ জন্মসুত্রে সংঘঠিত মানবগোষ্ঠী মনে করে কি সাংঘাতিক বিভ্রান্তিতে লিপ্ত হ’য়ে গেছে। তাদের কোনো ব্যক্তি যখন নিজের স্বার্থে অনৈসলামিক রীতিনীতি অনুসারে কাজ করে তখন অন্য মুসলমানরা তাকে সাহায্য করবে বলে আশা করে। আর সাহায্য না করলে ক্ষোভ প্রকাশ করে যে, দেখো মুসলমান মুসলমানের কাজে আসেনা। যারা সুপারিশ করে তারা এরূপ ভাষায় করে যে, একজন মুসলমান ভাই এর কল্যাণ হবে, তোমরা তার সাহায্য করো। যারা সাহায্য করে তারা তাদের এই কাজকে ইসলামী সমমর্মিতা নামে অভিহিত করে। প্রত্যেকের মুখে ইসলামী সহমর্মিতা, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব, ইসলামের ধর্মীয় সম্পর্ক ইত্যাদি শব্দ মুহুর্মুহু উচ্চারিত হয়। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলাম বিরোধী কাজ করার জন্য ইসলামেরই বরাত দেয়া এবং তার নামে সহানুভূতি চাওয়া ও সহানুভূতি করা এক নিদারুণ বেহুদা ব্যাপার। যে ইসলামের নাম নিয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড চলে, তা যদি যথার্থই মুসলমানদের মধ্যে জীবিত থাকতো, তাহলে ইসলামী উম্মাহর কোনো ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করছে, একথা জানা মাত্রই তারা তার বিরুদ্ধে দুর্জয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং তাকে তওবা করিয়ে তবে ছাড়তো। কারো সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা, একটি জীবন্ত ইসলামী সমাজে তো কোনো ব্যক্তি ইসলাম বিরোধী কোনো তৎপরতার নামও মুখে আনতে পারেনা। কিন্তু আমাদের সমাজে রাতদিন এসব হচ্ছে। এর একমাত্র কারণ হলো, আমাদের মধ্য জাহেলী জাতীয়তার ধারণা জন্মে গেছে। যে জিনিসকে আপনার ইসলামী ভ্রাতৃত্ব বলছেন, তা আসলে অমুসলিমদের কাছ থেকে ধার করা জাহেলী জাতীয়তার বন্ধন।
এই জাহেলিয়াতের একটা কৃতিত্ব এই যে, তা মুসলিম জনগনের মধ্যে “জাতীয় স্বার্থ” সংক্রান্ত এক আজব ধারণার জন্ম দিয়েছে। এ জিনিসটাকে তারা নিঃসংকোচে “ইসলামী স্বার্থ”ও বলে থাকে। এই তথাকথিত জাতীয় স্বার্থ বা ইসলামী স্বার্থ কি জিনিস? সেটি শুধু এই যে, যারা “মুসলমান” নামে পরিচিত, তাদের কল্যাণ হোক, তাদের হাতে বিপুল ধনসম্পদ আসুক, তাদের মান ইজ্জত ও প্রভাপ্রতিপত্তি বাড়ুক, তাদের হাতে ক্ষমতা আসুক, এক কথায়, কোনো না কোনোভাবে তাদের জাগতিক সমৃদ্ধি লাভ হোক। এইসব স্বার্থ ও কল্যাণ ইসলামী আদর্শ ও ইসলামী মূলনীতির আনুগত্যের পথে না বিরোধিতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হলো সেটা তাদের কাছে কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। জন্মসূত্রের মুসলমান বা বংশগত মুসলমানদের আমরা সর্বাবস্থায় মুসলমান বলি, চাই তাদের চিন্তাচেতনা ও কাজকর্মে কোথাও ইসলামী গুণাবলী খুঁজেও না পাওয়া যাক। এর অর্থ হলো, আমাদের কাছে মুসলমান আত্মার নাম নয়, শুধু দেহের নাম। ইসলামের গুণ ও ভাবধারা আছে কিনা, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করেও কাউকে মুসলমান বলা যায়। এই ভ্রান্তধারণার বদৌলতে যে দেহগুলোকে আমরা মুসলমান নাম দিয়ে রেখেছি, তাদের সরকারকে ইসলামী সরকার, তাদের উন্নতিকে ইসলামের উন্নতি বা প্রগতি এবং তাদের স্বার্থকে ইসলামী স্বার্থ নামে আখ্যায়িত করে চলেছি, চাই সেই সরকার এবং সেই উন্নতি প্রগতি ও স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে ইসলামের পরিচন্থি হোক না কেন। জার্মান জাতীয়তা যেমন কোনো নীতি বা আদর্শের নাম নয়, নিছক একটি জাতীয়তার নাম এবং একজন জার্মান জাতীয়তাবাদী যেমন জার্মানদের উত্থান ও শ্রেষ্ঠত্ব চায়, চাই যে পন্থায়ই হোক না কন, তেমনিভাবে আমরা “মুসলমানত্ব” কেও নিরেট আপন জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি চায়, তা সে উন্নতি ও সমৃদ্ধি নীতিগতভাবে বা কার্যত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা অনুসরণের মাধ্যমেই হোক না কেন। এটা কি জাহেলিয়াত নয়? আসলে মুসলমান যে পৃথিবীতে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে একটা বিশেষ মতবাদ ও বাস্তব কর্মসূচী নিয়ে কর্মরত একটি আন্তর্জাতিক দলের নাম, তা কি আমরা একেবারেই ভুলে যাইনি? সেই আদর্শ ও কর্মসূচীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার পর কেবল নিজের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক মর্যাদায় যারা অন্য কোনো আদর্শ ও কর্মসূচী অনুসারে কাজ করে, তাদের কাজকে কিভাবে “ইসলামী” বলা যায়? একথা কে কবে শুনেছে যে, যে ব্যক্তি পুঁজিবাদী নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করে, তাকে সমাজতন্ত্রী বলা হয়? কেউ কি পুঁজিবাদী সরকারকে সমাজতন্ত্রী সরকার বলে? ফ্যাসিবাদী প্রশাসনকে কি কেউ গণতান্ত্রিক প্রশাসন বলে? কেউ যদি এ ধরনের পরিভাষাগুলোর অপপ্রয়েঅগ করে, তবে আপনি হয়তো তাকে বেকুফ বা মুর্খ বলতে কিছুমাত্র সংকোচবোধ করবেননা। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই, ইসলাম ও মুসলমান পরিভাষাটি দুটির শোচনীয় অপপ্রয়োগ হচ্ছে। অথচ এতে কেউ মুর্খতা বা জাহেলিয়াতের গন্ধও অনুভব করেনা।
মুসলিম শব্দটা আপনা থেকেই প্রকাশ করছে যে, এটা কোনো জাতিবাচক নাম নয় বরং গুণবাচক নাম। এর অর্থ ইসলামের অনুসারী ছাড়া আর কিছু হতেই পারেনা। মানুষের যে বিশেষ মানসিক, নৈতিক ও বাস্তব গুণকে “ইসলাম” বলা হয়, মুসলমান শব্দটি সেই গুণকেই প্রকাশ করে। সুতরাং হিন্দু, জাপানী বা চৈনিক শব্দ যেমন একজন হিন্দু, জাপানী ও চৈনিস ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, মুসলমান শব্দটাকে টিক সেভাবে কোনো মুসলমান ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়না। মুসলমান নামধারী কোনো ব্যক্তি যখনই ইসলামী নীতি ও আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়, অমনি তার কাছ থেকে মুসলমানত্ব আপনা আপনি চলে যায়। এরপর সে যাই করুক, নিজের ব্যক্তিগত মর্যাদায় করে। ইসলামের নাম ব্যবহার করার কোনো অধিকার তার থাকেনা। অনুরূপভাবে “মুসলমানের স্বার্থ”, “মুসলমানের উন্নতি ও সমৃদ্ধি,” “মুসলিম সরকার ও রাষ্ট্র” “মুসলিম মন্ত্রীসভা” “মুসলিম সংগঠন” এবং এ ধরনের শব্দগুলো শুধু সেই ক্ষেত্রেই বলা যায়, যেখানে এই জিনিসগুলো অর্থাৎ স্বার্থ, উন্নতি, সরকার, রাষ্ট্র ইত্যাদি ইসলামী নীতি ও আদর্শের অনুসারী হবে এবং ইসলাম যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে এসেছে তার সফলতার অনুকূল হবে। তা না হলে এর কোনো একটির সাথেও মুসলমান বা মুসলিম শব্দ ব্যবহার করা সংগত নয়। [মুসলমানদের স্বার্থ ও কল্যঅণ মূলতঃ কোনো অন্যায় ব্যাপার নয়। কিন্তু যে জিনিস ইসলামের পরিপন্থী তাতে মুসলমানদের কোনো স্বার্থ ও কল্যাণ থাকতেই পারেনা। এজন্য সবকিছুকে ইসলামের কষ্টিপাথরে পরখ করেই জেনে নিতে হবে কোন্টি মুসলমানদের জন্য হিতকর কোন্টি ক্ষতিকর। [সংকলক] সেক্ষেত্রে এসব জিনিসের আর যে নাম খুশী রখা যেতে পারে, কিন্তু মুসলমান বা মুসলিম নাম কখনো রাখা যেতে পারেনা। কেননা ইসলামের গুণ বা বৈশিষ্ট্য বাদ দিয়ে মুসলিম বা ইসলাম আদৌ কোনো জিনিসই নয়। সমাজতন্ত্রকে বাদ দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা জাতি যখন সমাজতন্ত্রী হতে পারেনা, সমাজতনত্র ছাড়া কোনো স্বার্থকে যখন সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ, কোনো সরকার বা সংগঠনকে সমাজতান্ত্রিক সরকার ও সংগঠন এবং কোনো উন্নতিকে সমাজতন্ত্রীদের উন্নতি বলা চলেনা, তখন একমাত্র মুসলমানদের সম্পর্কে এমন ধারণা কেন পোষণ করা হয় যে, ইসলামী গুণবৈশিষ্ট্য থাক বা না থাক, মুসলমান কোনো ব্যক্তি বা জাতিগত নাম হতে পারে এবং যে কোনো জিনিসকে ইসলাম বল যেতে পারে?
বস্তুতঃ এই ভ্রান্ত ধারণা আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃকি ও ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের ধ্যানধারণা ও আচরণকে মৌলিকভাবে ভ্রান্ত বানিয়ে দিয়েছে। যেসব রাজ্য ও রাষ্ট্র অনৈসলামিক নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছিলো, তাদেরকে আমরা “ইসলামী রাষ্ট্র” বলি শুধু এজন্য যে, তার শাসক মুসলমান ছিলো্ কর্ডোভা, বাগদাদ, দিল্লী ও কায়রোর বিলাসবহুল দরবারে যে লাস্যময় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিলো, আমরা তাকে “ইসলামী সংস্কৃতি” নামে আখ্যায়িত করে থাকি। অথচ ইসলামের সাথে তার দূরতম সম্পর্কও নেই।’ আপনাকে যখন ইসলামী সভ্যতা কথা জিজ্ঞেস করা হয়, আপনি চটকরে আগ্রার তাজমহলের দিকে অংগুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দেন, যেনো ওটিই ইসলামী সভ্যতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অথচ একটি মৃতদেহ সমাহিত করার জন্য বহু একর জমি স্থায়ীভাবে বরাদ্দ করেতার ওপর কোটি কোটি টাকার সৌধ নির্মাণ করা আদৌ কোনো ইসলামী সভ্যতাই নয়। ইসলামী ইতিহাসের গৌরবময় স্মৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে আপনি আব্বাসী, সালজুকী ও মোগলদের কীর্তিগাথা তুলে ধরেন। অথচ সত্যিকার ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এসব কীর্তির বেশীরভাগ সোনালী অক্ষরে নয় বরং কালো কালি দিয়ে অপরাধের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার যোগ্য। আমরা মুসলমান রাজা মহারাজাদের ইতিহাসের নাম দিয়ে রেখেছি “ইসলামের ইতিহাস।” ভাবখানা এই যে, ঐ রাজাদের নামই যেনো ইসলাম। কোথায় ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং তার নীতি ও আদর্শের আলোকে আমরা আমাদের অতীত ইতিহাসের সমালোচনা ও পর্যালোচনা করবো এবং পূর্ণ ইনসাফের সাথে ও সততার সাথে ইসলামী আন্দোনগুলোকে অনৈসলামিক আন্দোলন থেকে আলাদা করে দেখবো এবং দেখাবো, তার পরিবর্তে অতীতের মুসলিম শাসকদের চরিত্র ও শাসন পদ্ধতির সমর্থন করাকেই আমরা ইসলামের ইতিহাসের সেবা বলে মনে করছি। আমাদের দৃষ্টিভংগীতে বক্রতা ও বিবৃতির সৃষ্টি হয়েছে শুধু এজন্য যে, আমরা মুসলমানদের সবকিছুকেই “ইসলাম” বিবেচনা করি, আর আমাদের ধারণা হলো, একজন মুসলিম নামধারী ব্যক্তি যদি অনৈসলামিক পন্থায়ও কাজ করে, তবে তার কাজকে মুসলমানের কাজ বলা যেতে পারে।
এই বক্র দৃষ্টিভংগীই আমরা আমাদের জাতীয় রাজনীতিতেও অবলম্বন করে রেখেছি। ইসলামের নীতি ও আদর্শ এবং তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা একটি জাতিকে “মুসলিম জাতি” বলে বিবেনা করি এবং সেই জাতির নামে, তার পক্ষ হতে তার বা তার জন্য যে কোনো ব্যক্তি এবং যে কোনো গোষ্ঠীকে যা ইচ্ছে তাই করতে অনুমতি দিয়ে থাকি। “মুসলিম জাতি”র সাথে সম্পর্ক রাখে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে আমরা মুসলমানদের প্রতিনিধি বা নেতা মেনে নিয়ে থাকি, চাই সে বেচারার ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই না থাক। একটা দলের অনুসারী হলে কিছুমাত্র উপকার পাবো বলে আমাদের ধারণা হলেই ব্যাস, আর কথা নেই, দলটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যতোই বিপরীত হোক না কেন, আমরা সে দলটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। মুসলমানদের জন্য কোনো মতে একবেলা খাবারের সংস্থাতন হয়ে গেলেই আমরা খুশী হয়ে যাই, চাই ইসলামের দৃষ্টিতে তা হারাম উপায়ে সংগৃহীত খাবারই হোক না কেন। কোনো অঞ্চলে কোনো মুসলমান ব্যক্তি ক্ষমতাসীন হয়েছে শুনলে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়, চাই সে একজন অমুসলিমের মতোই অনৈসলামিক উদ্দেশ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করতে থাকুক না কেন। আমরা এমন বহু জিনিসকে প্রায়ই ইসলামী স্বার্থ বলে থাকি, যা আসলেই ইসলাম বিরোধী। ইসলামী আদর্শ ও মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এমন প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে আমরা সর্বস্ব শক্তি ব্যয় করেথাকি এবং ইসলামেরসাথে আদৌ সংগতিপূর্ণ নয় এমনসব কাজে আমাদের অর্থ ও জাতীয় সম্পদের অপচয় করে থাকি। এসব কিছুই আমাদের একটিমাত্র মৌলিক ভুলের কুফল। সে ভুলটি হলো, আমরা নিজেদেরকে নিছক “জন্মসূত্রে গড়ে ওঠা একটা জাতি” ভেবে নিয়েছি আর এই সত্যটি ভুলে বসে আছি যে, আমরা আসলে একটা “আন্তর্জাতিক আদর্শবাদী দল” যার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং একমাত্র লক্ষ্য হলো এ দলের নীতি ও আদর্শকে পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন বানানো। আমরা যতক্ষণ নিজেদেরকে জন্মসূত্রে গঠিত একটি জাতির পরিবর্তে আদর্শবাদী দল ভাবতে না পারবো এবং এ ধারণাকে একটি জীবন্ত ধারণায় পরিণত না করবো, ততদিন কোনো ব্যাপারেই আমাদের ভূমিকা সঠিক ও নির্ভুল হবেনা।
সংযোজন
উপরোক্ত প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকে এই মর্মে সংশয় প্রকাশ করেন যে, “ইসলামী দলকে” “জাতি”র পরিবর্তে “পার্টি” বা “দল” বলার কারণে এমন আশংকা দেখা দিয়েছে যে, তা কোনো দেশ ও জাতীযতার অংশে পরিণত হয়ে যেতে পারে। একটি জাতির মধ্যে যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলের স্বতন্ত্র নীতি ও আদর্শ থাকলেও সবকয়টি দল তাদের সেই বৃহত্তর সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত থাকে, যাকে “জাতি” বলা হয়। অনুরূপ ভাবে, মুসলমানরা যদি একটা দল বা পার্টি হয়ে থাকে, তবে তাও স্বীয় মাতৃভূমি তথা দেশের বসবাসরত জাতির একটা অংশ হয়ে যেতে পারে।
যেহেতু দল বা পার্টি শব্দটাকে সাধারণভাবে মানুষ রাজনৈতিক দল অর্থে গ্রহণ করে থাকে, এজন্য উপরোক্ত ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এটা এর প্রকৃত অর্থ নয়, বরং একটা বিশেষ অর্থে প্রায়শঃ ব্যবহৃত হওয়ার কারণে সৃষ্টি হয়েছে। এ শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো, একটা বিশেষ আকীদা, আদর্শ, মতবাদ ও উদ্দেশ্যের ওপর ঐক্যবদ্ধ জনসমষ্টির নামই হলো জামায়াত তথা দল বা পার্টি। এই অর্থেই কুরআন “হিযব” এবং “উম্মাহ” শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছে। এই অর্থে হাদীসে “জামায়াত” শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং “পার্টি” বলতেও এটাই বুঝায়।
এই জামায়াত বা দল আবার দু’ধরনের হয়ে থাকে। একটি হলো, যার সামনে একটা জাতি বা দেশের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক কর্মকৌশলের একটা বিশেষ মতবাদ ও কর্মসূচী থাকে। এ ধরনের জামায়াত নিরেট রাজনৈতিক দল হয়ে থাকে। এ ধরনের দল যে জাতির অভ্যন্তরে গঠিত হয়, সে জাতিরই অংশ হয়ে কাজ করতে পারে এবং করেও থাকে।
দ্বিতীয় ধরনের দল হলো, যা একটি সামগ্রিক মতবাদ এবং একটা বিশ্বআদর্শ [World Idea] নিয়ে আবির্ভূত হয়। এধরনের দলের কাছে জাতি বা দেশ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতির জন্য একটা বিশ্বজোড়া নীতি থাকে। এদল গোটা জীবনকে এক নতুন ধাঁচে গড়ে তুলতে চায়। এদল স্বীয় মতাদর্শ ও মূলনীতি, আকীদা বিশ্বাস ও চিন্তাধারা এবং নৈতিকতার নীতিমালা থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত আচরণ ও সামাজিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি পর্যন্ত প্রতিটি জিনিসকে নিজস্ব ধাঁচে তৈরী করতে চায়। এদল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক সংস্কৃতি ও বিশিষ্ট এক সভ্যতা [Civilization] গড়ে তুলতে উৎুক। এ দৗ মূলতঃ একটি দল বা জামায়াতই বটে। তবে এটি এমন দল হয়না যা কোনো জাতির অংশ হ’য়ে কাজ করতে পারে। এ দলের অবস্থান সীমিত বলয়ের জাতীয়তার ঊর্ধ্বে। এ দলের লক্ষ্যই হ’য়ে থাকে এই যে, যেসকল বংশীয় ও ঐতিহ্যগত আভিজাত্যবোধের ওপর পৃথিবীতে নানা রকমের জাতীয়তা গড়ে ওঠে, তার বিলোপ সাধন করতে হবে। সুতরাং সে কেমন করে এ ধরনের জাতীয়তার অঙ্গীভূত হতে পারে? এদল বর্ণ, বংশ ও ইতিহাসভিত্তিক জাতীযতার পরিবর্তে একটা বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শবাদী জাতীয়তা [Rational Nationlality] গড়ে তোলে, স্থবির জাতীয়তার পরিবর্তে বর্ধিষ্ণু ও সম্প্রসারণশীল জাতীয়তা [Expanding Nationality] গড়ে তোলে। এদল নিজে এমন একটি জাতীয়তার রূপ ধারণ করে, যা বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর গোটা মানব গোষ্ঠীকে আপন বলয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। কিন্তু একটি জাতীয়তায় পরিণত হওয়া পরও প্রকৃত পক্ষে তা একটা জামায়াত বা দলই হয়ে থাকে। কেননা তাতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া জন্মগত সদস্য হওয়ার ওপর নির্ভরশীল নয় বরং যে মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে দলটি গঠিত হয়েছে, তার অনুসারী হওয়ার ওপর নির্ভরশীল।
মুসলমান আসলে এই দ্বিতীয় প্রকারের দলের নাম। এটি সেই ধরনের দল নয়, যা কোনো জাতির অভ্যন্তরে হয়ে থাকে। এটি এমন দল যার আবির্ভাব ঘটে একটা আলাদা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য এবং ছোট ছোট জাতীয়তাগুলো সংকীর্ণ বৃত্ত ভেংগে দিয়ে একটি বিরাট ও বিশাল বিশ্বজোড়া জাতীয়তা [World Nationality] গঠন করতে চায়। এই দল বা জামায়াতকে “জাতি” বলা নিঃসন্দেহে শুদ্ধ হবে। কেননা সে নিজেকে পৃথিবীর বর্ণ, বংশ ও ইতিহাসভিত্তিক জাতীয়হতাগুলোর কোনো একটিরও সাথে সংযুক্ত করতে প্রস্তুত হয়না বরং নিজস্ব জীবন দর্শন ও সমাজ দর্শন [Social Philolsophy] অনুসারে নিজের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে তৈরী করে। কিন্তু আরেক হিসেবে সে “জাতি” হওয়া সত্ত্বেও বাস্তবিকপক্ষে তা “দলই” থেকে যায়। কেননা নিছক কাকতহালীয় জন্মসূত্র [Mere accident of birth] কোনো ব্যক্তিকে তার সদস্য বানাতে সক্ষম নয় যতক্ষণ সে তার আদর্শে বিশ্বাসী ও অনুসারী না হয়। অনুরূপভাবে কোনো ব্যক্তির অন্য কোনো জাতিতে জন্মগ্রহণ তার নিজ জাতি থেকে বেরিয়ে এই জাতিতে প্রবেশ করার অন্তরায় নয়। যদি সে এই জাতির আদর্শকে মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে। সুতরং আমি যা বলেছি, তার মর্মার্থ হলো, মুসলিম জাতির জাতীয়তা তার একটি দল বা জামায়াত হওয়ার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। জামায়াত বা দলগত সত্তাই তার মূল আর জাতিগত সত্তা ডালপালা স্বরূপ। তার দলগত সত্তাকে যদি তার থেকে আলাদা করা হয় এবং সে নিছক একটা জাতি হিসেবে অবশিষ্ট থাকে তাহলে সেটা হবে পতন ও বিলুপ্তি।
প্রকৃত ব্যাপার হলো, মানবীয় সমাজ ও সংগঠনের ইতিহাসে ইসলামী জামায়াত একটা বিরল ও অভিনব সংগঠন। ইসলামের পূর্বে বৌদ্ধ ধর্ম ও খৃষ্টধর্ম জাতীয়তাসমূহের সীমান্ত অতিক্রম করে সমগ্র মানব জাতিকে সম্বোধন করেছে এবং একটা মতবাদ ও আদর্শের ভিত্তিতে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব গড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই উভয় মতাদর্শের কাছে কয়েকটা নৈতিক মূলনীতি ছাড়া এমন কোনো সামাজিক ও সামষ্টিক দর্শন ছিলোন, যার ভিত্তিতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনো সামগ্রিক অবকাঠামো গড়া যেতো। তাই এই দুটি মতাদর্শ কোনো বিশ্বজোড়া জাতীয়তা গড়তে পারেনি, কেবল একধরনের ভ্রাতৃত্ব [Brotherhood] বানিয়েই ক্ষান্ত থেকেছে। ইসলামের পর পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উদ্ভব ঘটে, যা নিজের আহ্বানকে আন্তর্জাতিক আহ্বানে পরিণত কতে চেয়েছিলো। কিন্তু জন্মের প্রথম দিন থেকেই তার ঘাড়ে জাতীয়তাবাদের ভূত চড়াও হলো। তাই সেও বিশ্বজোড়া জাতীয়তা গড়তে সক্ষম হলোনা। এবার মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এগিয়ে এসেছে। সে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয়তার বৃত্ত ভেংগে দিয়ে এক বিশ্বজোড়া সভ্যতা গড়তে ইচ্ছুক। কিন্তু যেহেতু এখনো তার পরিকল্পিত নয়া সভ্যতা পুরোপুরি আবির্ভূত হয়নি, তাই মার্কসবাদও এখনো বিশ্বজোড়া জাতীয়তায় রূপান্তরিত হতে পারেনি। [সত্যি বলতে কি, মার্কসবাদের ভেতরেও জাতীয়তাবাদের বীজ ঢুকে গেছে। ষ্ট্যালিন ও তার দলের কর্মকাণ্ডে রুশ জাতীযতাবাদের ভাবধারা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রুশ সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যে, এমনকি ১৯৩৬ সালের নতুন সংবিধানেও জায়গায় জায়গায় “ফাদার ল্যান্ড” [পিতৃভূমি] এর উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলামের দিকে লক্ষ্য করুন এর সর্বত্র “দারুল ইসলাম” শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ফাদারল্যান্ড বা মাদারল্যান্ডের নয়।] এখন পর্যন্ত ময়দানে শুধু ইসলামই একমাত্র নীতি ও আদর্শ, যা বংশীয় ও ঐতিহাসকি জাতীয়তাসমূহের বৃত্ত ভেংগে সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে একটা বিশ্বজোড়া জাতীয়তা গঠন করে। কাজেই যারা ইসলামের প্রাণশক্তি সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত নয় তাদের জন্য এটা বুঝা দুরূহ হয়ে পড়ে যে, একই সামষ্টিক কাঠামো কেমন করে একই সময়ে জাতি এবং দল দুটোই হতে পারে? দুনিয়ার যতোগুলো জাতি তাদের পরিচিত, তাদের মধ্যে কোনোটাই এমন নয়, যার সদস্যরা জন্মসূত্রে সদস্য হয়না বরং তাদেরকে সেচ্ছায় সদস্য হতে হ য়। তারা দেখতে পায় যে, যেব্যক্তি জন্মসূত্রে ইটালীয়, সে ব্যক্তি ইটালীয় জাতীয়তার সদস্য। আর যে ব্যক্তি জন্মসূত্রে ইটালীয় নয়, সে কোনোভাবেই ইটালীয় হতে পারে না। তারা এমন কোনো জাতীয়তাকে চেনেনা যার ভেতরে মানুষ আদর্শ ও আকিদার ভিত্তিতে প্রবেশ করে এবং আদর্শ ও আকিদা বদলে গেলে তা থেকে বেরিয়ে যায়। তাদের মতে, এ বৈশিষ্ট্য কোনো জাতির নয়, দলের হতে পারে। কিন্তু তারা যখন দেখে যে, এই অভিনব দল নিজস্ব আলাদা সভ্যতা ও সংস্কৃতি তৈরী করে, নিজের স্বতন্ত্র জাতীয়তার দাবী করে এবং কোথাও স্থানীয় জাতীযতহার সাথে নিজেকে সংযুক্ত করতে রাজী হয়না, তখন ব্যাপারটা তাদের কাছে এক দুর্বোধ্য রহস্যে পরিণত হয়।
অমুসলিমদের মতো মুসলমানরাও একই দুর্বোধ্যতার সম্মুখীন হচ্ছে। যুগ যুগ কাল ধরে অনৈসলামিক শিক্ষালাভ ও অনৈসলামিক পরিবেশে জীবন যাপন করতে থাকায় তাদের মধ্যে “ঐতিহাসিক জাতীয়তা” তথা জন্মগত ও বংশগত জাতীয়তার ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। তারা ভুলে গেছে যে, মুসলমানরা প্রকৃতপক্ষে এমন একটি দল, যা পৃথিবীতে একটা বিশ্বজোড়া বিপ্লব সংঘটনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলো। যার জীবনের উদ্দেশ্য ছিলো নিজের আদর্শকে সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়া। এবং যার সংকল্প ছিলো পৃথিবীর তাবত ভ্রান্ত সামষ্টিক ব্যবস্থাকে ভেংগে দিয়ে নিজস্ব সমাজ দর্শনের ভিত্তিতে একটা সামষ্টিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসব কথা ভুলে গিয়ে তারা নিজেদেরকে কেবল অন্যান্য জাতিসমূহের মতো একটা জাতি মনে করে নিয়েছে। এখন তাদের সভাসমিতি ও বৈঠকাদিতে এবং তাদের পত্রপত্রিকা ও বইপুস্তকে কোথাও তাদের সামষ্টিক জীবনের এই মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো আলোচনা হয়না, যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য তাদেকে সারা দুনিয়ার জাতিগুলোর মধ্য থেকে বাছাই করে একটা উম্মাহ বা আন্তর্জাতিক জাতিতে পরিণত করেছিলো। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পরিবর্তে যে জিনিস এখন তাদের মনোযোগের একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু, তাহচ্ছে “মুসলমানদের স্বার্থে।” মুসলমান বলতে মুসলিম মাতাপিতার ঔরসজাত সন্তান এবং স্বার্থ বলতে এইসব বংশানুক্রমিক মুসলমানের বৈষয়িক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বুঝানো হয়। এই স্বার্থের মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৈতৃক উত্তরাধিকার হিসেবে পাওয়া সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও অন্তর্ভুক্ত। এই স্বার্থের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য যে কৌশলই লাভজনক ও কার্যকর মনে হয়, সেদিকেই তারা দিকবিদিক জ্ঞানশুন্য হ’য়ে ছুটে, ঠিক যেমন মুসোলিনী ইটালীয়দের স্বার্থের অনুকূল যেকোনো কর্মপন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত হয়ে যেতো। কোনো আদর্শ ও নৈতিকতার তোয়াক্কা এরাও করেনা, মুসোলিনীও করতোনা। সে বলতো, ইটালীয়দে জন্য যেটাই কল্যাণকর সেটাই ভালো ও ন্যায়সঙ্গত। এই মনোভাবকেই আমি মুসলমানদের অধোপতন বলে থাকি। আর এই অধোপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যই আমি মুসলমানদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দেয়া জরুরীমনে করছি যে, আপনারা বংশানুক্রমিক ও ঐতিহাসিক জাতিগুলোর মতো একটা জাতি নন, বরং প্রকৃতপক্ষে একটি জামায়াত এবং নিজেদের মধ্যে জামায়াতী চেতনা [Party sense] জাগিয়ে তোলার মধ্যেই আপনাদের মুক্তি।
এই জামায়াতী চেতনা হারানো তথা আত্মভোলা হওয়ার কুফল এতো বেশী যে, তা গুণে শেষ করা কঠিন। আজকের মুসলমানরা প্রত্যেক পথপ্রদর্শকের পেছনে ছুটতে এবং প্রত্যেক মতবাদ ও আদর্শের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। অথচ এটা ভেবেও দেখেনা যে, ঐ নেতা ও আদর্শ ইসলামী বিধান ও ইসলামী আদর্শের কতো বিপরীত। এটা শুধু জামায়াতী চেতনাহীনতা ও আত্মবিস্মৃতির কারণেই সম্ভব হচ্ছে। মুসলমান জাতীয়তাবাদী হতেও কুণ্ঠিত হয়না, ফ্যাসিবাদী হতেও সংকোচবোধ করেনা এবং কমিউনিষ্ট হতেও কিছুমাত্র ইতস্ত করেনা। পাশ্চাত্যের রকমারি সামাজিক দর্শন এবং ইন্দ্রিয়াতীত চিন্তাধারা ও তাত্ত্বিক মতবাদসমূহের মধ্য থেকে প্রায় প্রত্যেকটিরই অনুসারী মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যাবে। পৃথিবীতে এমন কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পাওয়া যাবেনা, যার সাথে কোনো না কোনো মুসলমান শরীক হয়নি। মজার ব্যাপার হলো, তারা সবাই নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে, মুসলমান মনে করে এবং অন্যদের কাছ থেকেও মুসলমান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এইসব রকমারি পথে উদভ্রান্তের মতো বিচরণকারীদের কারো একথা মনে পড়েনা যে, “মুসলমান: জন্মসূত্রে পাওয়া কোনো খেতাব বা উপাধি নয়, বরং ইসলামের বাসতব অনুসারী হওয়ার গুণবাচক নাম। যে ব্যক্তি ইসলামের পরিবর্তে অন্য কোনো মতবাদের অনুসারী হয় তাকে মুসলমান বলা এই শব্দটির একেবারেই অপপ্রয়োগের শামিল। মুসলিম কমিউনিস্ট, মুসলিম জাতীয়তাবাদী এবং এই ধরনের অন্যান্য পরিভাষা “কমিউনিস্ট মহাজন” ও “বৌদ্ধ কসাই” প্রভৃতি পরিভাষার মতোই স্ববিরোধী পরিভাষা।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি