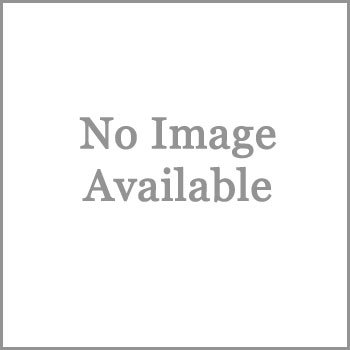ইস্তিমদাদে রূহানী
কবর যিয়ারত সম্পর্কে উপরোক্ত বিস্তারিত আলোচনা পাঠ করার পর কারো মনেই সন্দেহ থাকতে পারেনা যে, কবরস্থানে গিয়ে তাদের জন্য দো’আ করা ছাড়া আর কোনো কাজ করা। কবরস্থ লোকদের নিকট নিজেদের কোনো মনোবেদনা জানাতে চেষ্টা করা, কোনো প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদের সাহায্য প্রার্থনা করা কিংবা তাদের কাছ হতে রূহানী ফায়েয হাসিল করতে চেষ্টা করা সম্পূর্ণ শিরক। মূলত এ সেই কাজ, যা মূলত মুশরিকরা করে তাদের মনগড়া দেব-দেবী ও মাবুদদের নিকট। এ পর্যায়ে তাফসীর জামেউত তাফসীর এর সূরা ফাতির এর তাফসীর থেকে একটা ঘটনা উল্লেখ করা একান্তই জরুরী। ঘটনাটি হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী ইমাম আবু হানীফা(রহ) থেকে বর্ণনা করেছেন।
ঘটনাটি এরূপঃ ইমাম আবু হানীফা দেখলেন, এক ব্যক্তি নেক লোকদের কবরস্থানে উপস্থিত হয়ে সালাম করছে, তাদের সম্বোধন করে বলছেঃ হে কবরবাসীরা! তোমাদের কি কোনো খবর আছে? তোমাদের আছে কোনো ক্ষমতা? আমি তো তোমাদের কাছে কয়েক মাস ধরে আসছি, তোমাদের ডাকাডাকি করছি। তোমাদের নিকট আমার জন্য কোনো প্রার্থনা ছিলনা, ছিল শুধু দো’আর প্রার্থনা। কিন্তু তোমরা কি কিছু টের পেয়েছ, না একেবারে গাফিল হয়ে পড়ছো?
এ কথা ইমাম আবু হানীফা(রহ) শুনতে পেলেন। তিনি লোকটিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেনঃ কবরস্থ লোকেরা কি তোমার ডাকের কোনো জবাব দিল? লোকটি বললঃ না, কোনো জবাবই পাইনি। তখন ইমাম আবু হানীফা(রহ) বললেনঃ বড় দুঃখ, বড় লজ্জার বিষয়! তোমার দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক। তুমি এমন সব দেহকে লক্ষ্য করে কথা বলছো যারা কোনো জবাবই দিতে পারেনা, যাদের কোনো কিছুই করার ক্ষমতা নেই, (এমন কি) কোনো আওয়াজও তারা শুনতে পায়না। অতঃপর তিনি পড়লেন সূরা ফাতির এর 22 নং আয়াত।–তুমি শোনাতে পারবেনা তাদের, যারা কবরে রয়েছে।
ইমাম আবু হানীফার(রহ) এই উক্তি প্রমাণ করে যে, তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, অলী ও নেক লোকদের কবরে গিয়ে তাদের সম্বোধন করে কথা বলা বা কিছুর জন্য প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। দ্বিতীয়-মৃত ব্যক্তি শুনেওনা, জবাবও দিতে পারেনা। ভক্তদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা, নিঃসন্তানকে সন্তান দান করা বা চাকুরী-ব্যবসা ইত্যাদিতে উন্নতি দান করার কোনো সাধ্যই তাদের নেই- থাকতে পারেনা। ইমামা আবু হানীফা(রহ) এর এই মতে কুরআনের ঘোষণার যথার্থ প্রতিফলন ঘটেছে। ইয়াহুদি খ্রীস্টান মুশরিকার হযরত ঈসা, হযরত উজাইর ও ফেরেশতাদের ডাকতো। তাদের নিকট সাহায্য চাইতো বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য। এই প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা’আলা ঘোষণা করলেনঃ আরবী(*********)
-না, ওরা তোমাদের বিপদ দূর করতে এবং তোমাদের জন্য আসা বিপদকে অন্য দিকে সরিয়ে দিতে কস্মিনকালেও পারবেনা।
এই পর্যায়ে কুরআন মজীদের একটি আয়াত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ [٤٦:٥]
- যে লোক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে সে কিয়ামত পর্য্ন্তও তার ডাকের জবাব দিবেনা, তার চাইতে অধিক গুমরাহ আর কে হতে পারে? ওরা তো তাদের দো’আ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। (আহকাফঃ5)
এ পর্যায়ে সঠিক মাসআলা জানার জন্য সর্বপ্রথম দেখতে হবে কুরআন মজীদে স্বয়ং নবী করীম(স) এর কি মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। নবী করীমের যে মর্যাদা কুরআনে ঘোষিত হয়েছে- এ পর্যায়ে আকীদা ঠিক রাখার জন্য সুন্নাতের সঠিক জ্ঞান অর্জনের জন্য- তাই হবে ভিত্তি। কুরআনের পাঠক মাত্রই জানেন, কুরআন মজীদে স্বয়ং রাসূলের জবানীতে তাঁর নিজের মর্যাদা নানা স্থানে ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ের একটি আয়াত হচ্ছে এইঃ
قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [٧:١٨٨]
-বলো হে নবী! আমি আমার নিজের জন্য কোনো কল্যাণের ওপর কর্তৃত্বশালী নই, না কোনো ক্ষতির ওপর। তবে শুধু তা-ই এর বাইরে, যা আল্লাহ চাইবেন। আর আমি যদি গায়েব জানতাম, তাহলে আমি নিশ্চয়ই অনেক বেশি বেশি কল্যাণ লাভ করে নিতাম এবং আমাকে কোনো দুঃখ বা কষ্টই স্পর্শ করতে পারতোনা। আমি তো শুধু ভয় প্রদর্শনকারী, শুধু সংবাদদাতা ঈমানদার লোকদের জন্য।(আল আরাফঃ188)
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী লিখেছেনঃ এ আয়াত থেকে বোঝা গেল যে, নবী করীম(স) সে গায়েবের জ্ঞান জানেননা, যা ফায়দা লাভ ও ক্ষতির প্রতিরোধের জন্য অনুকূল। কেননা তার সাথে এবং দ্বীনী হুকুম আহকাম ও শরীয়তের বিধানের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এ জন্যে এ ধরনের গায়েবী জ্ঞান নবী করীম(স) জানেননা। আর এ জ্ঞান না জানা তাঁর নব্যুয়তের মহান মর্যাদার পক্ষে কিছুমাত্র ক্ষতিকর বা দোষের নয়।
এ পর্যায়ে গায়েবী ইলম যে রাসূলের নেই, তা একটি বাস্তব ঘটনা থেকেও প্রমাণিত হয়। হযরত আয়েশা(রা) বলেনঃ লোকেরা খেজুর গাছের স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মিলন ঘটাত। নবী করীম(স) বলেনঃ এ কাজ যদি তোমরা না কর তবে ভালোই হয়। কিন্তু পরবর্তী ফসল কালে তারা এ কাজ না করার দরুণ খেজুরের ফসল ভালো হলোনা। এ কথা শুনে নবী করীম(স) বললেনঃ ‘তোমাদের এসব বৈষয়িক ব্যাপার তোমরাই ভালো জানো।’ অপর বর্ণনায় কথাটি এভাবে বলা হয়েছেঃ ‘দেখ, ব্যাপার যদি তোমাদের বৈষয়িক সংক্রান্ত হয়, তবে তা তোমাদের ব্যাপার। আর যদি দ্বীন সংক্রান্ত হয়, তাহলে তা আমার আওতাভুক্ত।’
হানাফী মাযহাব সমর্থিত আকীদায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, নবী করীম(স) গায়েব জানতেন-এরূপ আকীদা যদি কেউ পোষণ করে, তবে সে হবে স্পষ্ট কাফির। কেননা এরূপ আকীদা কুরআনের(পূর্বোক্ত এবং) এ আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আয়াতটি হলোঃ
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ
–বলো, আসমান-জমিনের কেউ-ই গায়েব জানেনা এক আল্লাহ ছাড়া।
অর্থাৎ যা কিছু মানুষের অনুভূতি আর জ্ঞানের আওতার মধ্যের ব্যাপার নয় তা আসমান-জমিনের সমস্ত সৃষ্টিলোকের মধ্যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই জানেনা, জানতে পারেনা।
হযরত আয়েশা(রা) বলেনঃ আরবী(********)
-যে লোক ধারণা করবে যে, মুহাম্মদ(স) লোকদের সে সব বৈষয়িক বিষয়ে জানেন বা খবর দেন, যা কাল ঘটবে, তবে সে আল্লাহর প্রতি একটি অতি বড় মিথ্যা আরোপ করে দিলো।
গায়েব জানা সম্পর্কিত এ সব অকাট্য ও সুস্পষ্ট দলীলসমূহের ভিত্তিতে বলা যায়, নবী করীম(স)-ই যখন গায়েব জানতেননা, তখন কোনো পীর-অলী-দরবেশ এর পক্ষে গায়েব জানার কোনো প্রশ্নই উঠতে পারেনা। যদি কেউ তা মনে করে, তবে তা হবে আকীদার ক্ষেত্রে এক মহা শিরক, কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট ঘোষণাবলীর সম্পূর্ণ খেলাফ এবং সুন্নাতী আকীদার বিপরীত এক সুস্পষ্ট বিদয়াত।
অলৌকিক ক্রিয়া কান্ড ঘটানোর বিদয়াত
বিশ্বলোকের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। এ সবের ওপর কর্তৃত্বও চলে একমাত্র আল্লাহরই। তিনি ছাড়া এ দুনিয়ায় অপর কারো কিছু করার ক্ষমতা নেই। মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় শুধু ততটুকুই করতে পারে, যা করার অবকাশ রেখেছেন আল্লাহ তা‘আলা। সে অবকাশও অসীম নয়, অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে আল্লাহ যাকে যা করার ক্ষমতা দান করেন, সে তা ততটুকুই করতে পারে যতটুকু করার অনুমতি আল্লাহ দান করেন। এ কারণে বলা যায়, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের এ ধরনের কিছু কিছু কাজ করার অনুমতি দেন কখনো কখনো, যে ধরনের কাজকে আমরা ‘অলৌকিক কাজ’ বলে থাকি। এর কতগুলো কাজ এমন যেগুলো নবী রাসূলগণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়। এগুলোকেই ইসলামী পরিভাষায় বলে ‘মুজিযা’। নবী রাসূলগণের মুজিযা সত্য। নবীর নব্যুয়তী সত্যতা প্রমাণের জন্য তা হয় অকাট্য দলীল। কিন্তু এ ‘মুজিযা’ অনুষ্ঠিত হয় সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের জন্য, কোনো কোনো বিশেষ ফায়দা পৌঁছাবার জন্য এবং তা হয় স্বয়ং আল্লাহর কুদরতে ও ইচ্ছায়, নবী-রাসূলের ইচ্ছায় নয়। তা করার ক্ষমতা নবী-রাসূলের নিজস্ব নয়, কেবল মাত্র আল্লাহরই দেয়া ক্ষমতা।
আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য নবী ও রাসূলগণকে যেমন মুজিযা ও অকাট্য প্রমাণাদি দিয়েছেন তাঁদের নব্যুয়তের অকাট্যতার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে, তেমনি হযরত ঈসা(আ) কেও বহু অস্বাভাবিক কর্মকান্ড ঘটানোর শক্তি দান করেছিলেন। কিন্তু খ্রিস্টানরা সেসব নিদর্শন দেখে মনে করে নিয়েছে যে, এসব করার ক্ষমতা স্বয়ং হযরত ঈসা(আ) এর নিজস্ব এবং এই ক্ষমতা ও শক্তি ঠিক আল্লাহর ক্ষমতা ও শক্তি। এই কারণে সেই মূর্খরা মনে করে নিয়েছে যে-মহান আল্লাহই বুঝি হযরত ঈসার মধ্যে লীন হয়ে গেছেন। এক্ষণে আল্লাহ ও ঈসা অভিন্ন সত্তায় পরিণত, আল্লাহ ঈসা একাকার।(নাউজুবিল্লাহ)। আর এ-ই হচ্ছে খ্রিস্টানদের শিরকী আকীদা গ্রহণের মূলতত্ত্ব।
মুসলমানদের মধ্যে অলী-আল্লাহ নামে পরিচিত ব্যক্তিদের সম্পর্কেও ভক্তির আতিশয্যে- চরম মূর্খতার কারণে- মনে করেছে যে, আল্লাহ বুঝি তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গেছেন; কিংবা তারা আল্লাহ হয়ে গেছেন (নাউজুবিল্লাহ) বলেইতো তারা অসাধ্য সাধন করতে ও অস্বাভাবিক-অলৌকিক ঘটনাবলী ঘটাবার ক্ষমতার অধিকারী হয়ে বসেছেন। এও ঠিক শিরকে নিমজ্জিত খ্রিস্টানদের মতো চরম মূর্খতারই পরিণতি। খ্রিস্টানরা যেমন বুঝেনি যে, হযরত ঈসা(আ) এর যা কিছু ক্ষমতা, তা নবী হিসেবেই আল্লাহর দেয়া, তার নিজের কিছুই নয়, তেমনি মুসলমানদের মাঝে এই মূর্খ লোকেরাও বুঝেনা- বুঝতে প্রস্তুতই নয় যে, তারা যাদেরকে অলী-আল্লাহ বলে মনে করে প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহর অলী নাও হতে পারে। আর হলেও অলৌকিক কিছু করার, আল্লাহর চলমান ও সদা কার্য্কর স্বাভাবিক নিয়ম বিধান দর-বদল করার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই। ওরাও ঠিক এই কারণেই খ্রিস্টানদের মতোই চরম শিরকের মধ্যে ডুবে আছে।
কিন্তু নবী-রাসূল ছাড়া অন্য মানুষের দ্বারা যদি অস্বাভাবিক কর্মকান্ড হয় তবে তা তিন প্রকারের হতে পারে।
এক. তা দ্বারা যদি কোনে দ্বীনী ফায়দা হয়, তবে তা নেক আমলসমূহের মধ্যে গণ্য।
দুই. যদি তা থেকে কোনো বৈধ ব্যাপার ঘটে, তবে তা আল্লাহর দেয়া এক বৈষয়িক নেয়ামত। সে জন্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উচিত আল্লাহর শোকর করা।
তিন. অস্বাভাবিক ঘটনা যদি এমন কিছু ঘটে বা হারামের পর্যায়ে পড়ে যায়, তবে তা হবে আল্লাহর আযাবের কারণ। তার ফলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ফেটে পড়ে।
মনে রাখতে হবে, অস্বাভাবিক ঘটনা যেমন দুনিয়ার নেক বান্দাদের কেন্দ্র করে সংঘটিত হয় তেমনি সংঘটিত হতে পারে অন্যান্য বান্দাদের কেন্দ্র করেও। অতএব তা যেমন দ্বীনের দৃষ্টিতে ভালোও নয়, তেমনি মন্দও নয়। কিন্তু এমনও হয়, যা না ভালো, না মন্দ।
নেক লোকদেরকে কেন্দ্র করলে তেমন কোনো ঘটনা ঘটলে তা যেমন তার নিজের গৌরবের কোনো বিষয় নয়, তেমনি তা-ই নয় তার বুজুর্গীর কোনো প্রমাণ। আর যাকে কেন্দ্র করেই এমন কিছু ঘটবে, তাকেই যে অলৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে করতে হবে, মনে করতে হবে তাকে আল্লাহর প্রিয় বান্দা, তার কোনো দলীলই কুরআন হাদীসের খুঁজে পাওয়া যায়না। কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে কে আল্লাহর অলী, কে তাঁর প্রিয় ব্যক্তি, নিম্নোক্ত আয়াত থেকে জানতে পারা যায়। আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ
أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [١٠:٦٢]
الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ [١٠:٦٣]
–জেনে রেখো, আল্লাহর অলী লোকদের কোনো ভয় নেই, নেই তাদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ। এরা সেই লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে। (ইউনূসঃ62-63)
হযরত আবু হুরায়রা(রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম(স) হাদীসে কুদসী বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহর এ কথাটি বলেছেনঃ আরবী(**********)
-যে লোক আমার অলীর সঙ্গে শত্রুতা করবে, সে আমার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দেয়। বান্দার ওপর আমি যেসব ফরয ধার্য্ করে দিয়েছি কেবল সেগুলো আদায় করেই আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে- এ-ই আমার নিকট অধিক প্রিয়। নফল কাজ করেও বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে থাকে। শেষ পর্য্ন্ত আমি তাকে ভালোবাসতে শুরু করি। আর আমি যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসতে শুরু করি, তখন আমি তার সেই কান হয়ে যাই যা দ্বারা সে শুনে, সেই চোখ হয়ে যায় যা দ্বারা দেখে, সেই হাত হয়ে যাই যা দ্বারা সে ধরে, সেই পা হয়ে যাই যা দ্বারা সে চলে। অতএব সে আমার দ্বারাই শুনে, আমার দ্বারাই দেখে, আমার দ্বারাই ধরে, আমার দ্বারাই চলে।
কুরআনের আয়াত এবং হাদীস থেকে প্রমাণিত হলো যে, অলী-আল্লাহ সেই হয় এবং তাঁকেই বলা যায়, যে মুমিন হবে এবং মুত্তাকী হবে। ঈমান ও তাকওয়া হওয়ার মানে পূর্ণ ঈমান এবং নির্ভূল নির্ভেজাল তাকওয়া। আর হাদীস থেকে জানা গেল যে, সে হবে আল্লাহর আরোপিত ফরযসমূহের যথাযথ পালনকারী। কিন্তু সেই সঙ্গে তার যে কারামত হতে হবে এমন কথা না কুরআনে আছে, না হাদীসে। কুরআনের উক্ত আয়াতের পরবর্তী কথায় এই কারামতের কথা নেই। যা আছে তা হলো এইঃ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ
-তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে এবং পরকালের।
بُشْرىবা সুসংবাদ বলতে মূলত বোঝায় এমন খবর যা শুনলে মুখমন্ডলে আনন্দের চিহ্ন ফুটে ওঠে। এ থেকেই হচ্ছে বাশারাত মানে সুসংবাদ। আর যে সংবাদ দিলে এরূপ আনন্দ লাভ হয় তাকেও بُشْرى বলা হয়। আর এর সঠিক তাৎপর্য্ এইঃ তাদের জন্যে সুসংবাদ তারা দুনিয়ায় থাকতেও এবং পরকালে চলে গেলেও। অর্থাৎ নগদ ও বাকী উভয় ধরনই।
আল্লামা আলুসী লিখেছেনঃ বহু সংখ্যক হাদীসের বর্ণনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুরআনের এ بُشْرى শব্দের অর্থ হচ্ছে দুনিয়ার জীবনে ভাল ও শুভ স্বপ্ন, যা নব্যুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।
রাসূল(সা) এর নিজের কথা থেকেই এ তাফসীর জানা গেছে অকাট্যভাবে। আর পরকালের ব্যাপারে তা হচ্ছেঃ মুমিনকে মৃত্যুর মুহুর্তে সুসংবাদ দেয়া হবে যে, আল্লাহ তোমাকে এবং তোমাকে যারা তোমার কবর পর্য্ন্ত বহন করে নেবেন, তাদের মাফ করে দিয়েছেন।
আর হযরত আবু হুরায়রা(রা) এর বর্ণনা থেকেও জানা যায়, যার মানে হচ্ছে বেহেশত।
আর আতা থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ দুনিয়ায় হচ্ছে এই যে,بُشْرى ফেরেশতারা মৃত্যুর সময় তাদের নিকট রহমত নিয়ে আসবেন। আর পরকালীন হচ্ছে এই যে, بُشْرى তখন ফেরেশতাগণ এ সব মুসলমানের নিকট তাদের সাফল্য ও সম্মান মর্যাদার সুসংবাদ বহন করে নিয়ে আসবেন। তারা তাদের মুখমন্ডলকে উজ্জল দেখতে পাবেন এবং তাদের ডান হাতে তাদের আমলনামা দেয়া হবে, তারা তা পড়বে ইত্যাদি পর্যায়ের সুসংবাদ।
তাহলে অলী-আল্লাহদের যে কোনো কারামত লাভ হবে, যা নিয়ে এখনকার সত্য পীরেরা এবং মিথ্যা পীরেরা দাবি করছে এবং অন্ধ অজ্ঞ মুরীদদের এসব আজগুবী কথাবার্তা বলে সাচ্চা পীর আর ভন্ড পীরের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করে তোলা হচ্ছে।
অলী-আল্লাহদের প্রতি এসব দান বাস্তবিকই আল্লাহর অতি বড় অনুগ্রহ। কিন্তু সে অনুগ্রহ ব্যক্তিগতভাবে তাদের জন্য। কেউ তা লাভ করে থাকলে তার উচিত আল্লাহর শোকর আদায় করা। কিন্তু তার প্রচারণার মারফতে পীর-মুরীদী ব্যবসা চালানোর লিল্লাহিয়াতের কোনো প্রমাণ মিলে কি? আকায়িদের কিতাবে যে কারামতের কথা বলা হয়েছে তা হলো এগুলো। কারামত মানে সম্মান মর্যাদা; আর এগুলোও আল্লাহর পক্ষ হতে দেয়া সম্মান মর্যাদা এবং কুরআন হাদীসের ঘোষণায় প্রমাণিত এসব কারামতকে কোনো মুসলমান অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু এখানে যে কারামতের কথা বলা হচ্ছে তা এসব নয়। তা হলো কোনো পীর বা অলী আল্লাহ কোনো অঘটন ঘটিয়েছে, কোনো অস্বাভাবিক কাজ করে মুরীদদের তাক লাগিয়ে দিয়েছে, কে শূণ্যে উড়ে গেছে, কে পানির ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে সমুদ্র পার হয়েছে, কে জেলখানায় বন্দী থাকা অবস্থায়ও প্রতিদিন কাবায় গিয়ে নামায পড়েছে, এসব প্রচারণার মানে কি? এসব যে একেবারে ফাঁকা বুলি, কেবল অজ্ঞ মূর্খদের জন্যই তা বলা হয়, তাদের মধ্যেই তা প্রচার করা হয়, এটা যে কোনো সুস্থ বুদ্ধির মানুষই স্বীকার করবেন।
মোটকথা, অলী আল্লাহ হলেই যে তার কারামত বা অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা থাকতে হবে, কারো ‘কারামত’ থাকলেই যে সে অলী আল্লাহ বলে গণ্য হবে আর কারামত না হলে অলী আল্লাহ মনে করা যাবেনা, সব কথাই ভিত্তিহীন। কুরআন হাদীসের এসব কথার কোনোই দলীল নেই।
মূর্খ পীরেরা ততোধিক মূর্খ মুরীদদের সামনে নিজেদের যে সব কারামত জাহির করে, প্রকাশ করে যেসব অলৌকিক(?) কান্ড কারখানা কিংবা মৃত্যুর পরও তারা অলৌকিকভাবে দুনিয়ার ব্যবস্থাপনার এবং সামাজিক কাজকর্মে কোনোরূপ ‘তাসাররূপ করে বা করতে পারে কিংবা শায়খদের রূহ হাযির হয়, দুনিয়ার অবস্থা জানে বা শুনে ইত্যাদি বলে যে দাবি করা হচ্ছে, সেগুলো সুস্পষ্টভাবে কুফরি বা শিরকী কথাবার্তা ছাড়া আর কি হতে পারে। এ ক্ষমতা স্বয়ং রাসূলকেও দেয়া হয়নি। এ পর্যায়ে কয়েকটি দলীলের উল্লেখ করা যাচ্ছে।
মুল্লা আলী আল কারী লিখেছেনঃ হানাফী ইমামগণ স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ নবী করীম(স) গায়েব জানেন-এরূপ আকীদা যে রাখে, সে কাফির। কেননা এরূপ আকীদা আল্লাহর ঘোষণা ‘আল্লাহ ছাড়া আসমান জমিনের কেউ ই গায়েব জানেনা’ এর বিপরীত।( قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ আয়াতের অর্থ হলোঃ যে সব বিষয়ে মানুষের অনুভূতি শক্তি ও বিদ্যাবুদ্ধির বাইরে অবস্থিত গায়েব, তা আসমান-জমিনের গোটা সৃষ্টিলোকের মধ্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ই জানেনা। ইমাম ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি সমগ্র সৃষ্টিলোকের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে যেন বলে দেন যে, আসমান-জমিনের অধিবাসীদের মধ্যে কেউ-ই গায়েব জানেননা-জানেন কেবলমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। অতঃপর লিখেছেনঃ আল্লাহর কথা-‘আল্লাহ ছাড়া’ পূর্ব কথা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে আলাদা করা হয়েছে। তার মানে হলো এই যে, গায়েব আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেনা। কেননা এ ব্যাপারে তিনি এক ও একক, এ ব্যাপারে তাঁর কেউই শরীক নেই।)
এমনিভাবে যে লোক বিশ্বাস করবে যে, মৃত লোকেরা দুনিয়ার ব্যাপারে ‘তাসাররুফ’ করে (নিজেদের ইচ্ছেমতো কোনো ঘটনা ঘটানো ও কার্য্ সম্পাদন করে), আল্লাহ ছাড়া এরূপ আকীদা রাখা কুফরী।
বিবাহে যে লোক আল্লাহর রাসূল(স)-কে সাক্ষী বানায়ঃ তাকে হানাফী ফিকাহ এর কিতাবে কাফির বলা হয়েছে। কেননা সে এ কাজ রাসূলে করীমকে ‘আলিমুল গায়েব’ মনে করেই করেছে।
কবরস্থানে যে শিরক বিদয়াত অনুষ্ঠিত হয়, তার বিরুদ্ধে মুজাদ্দেদি আল ফেসানী জিহাদ করেছেন আজীবন। এ পর্যায়ে তিনি যা লিখেছেন, তা এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ রোগ শোক দূর করার ব্যাপারে মূর্তি দেব-দেবী ও বাতিল মা’বুদের নিকট সাহায্য চাওয়া, যা জাহিল মুসলমানদের মধ্যে রেওয়াজ পেয়ে গেছে-একেবারেই শিরক ও গোমরাহী। নির্মিত ও অনির্মিত পাথরের নিকট নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য দো’আ করা মহান আল্লাহকে স্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করার সমান এবং একেবারেই কুফরী। আল্লাহ তা‘আলা কোনো কোনো গোমরাহ লোকদের অবস্থান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, ‘তারা নিজের ব্যাপারসমূহকে তাগুতী শক্তির নিকট পেশ করতে ইচ্ছে করে, অথচ আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যে, এসব তাগুতী শক্তিকে অস্বীকার করতে হবে। আর শয়তান তাদের বিভ্রান্ত করে গোমরাহীর মধ্যে নিক্ষেপ করতে চায়।
অনেক মেয়েলোক চরম অজ্ঞতাবশত এ ধরনের সাহায্য্ প্রার্থনায় লিপ্ত হয়। কতক অলীক নামের কাছে রোগ শোক ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি চায়। তাতে মুশরিকদের রসম-রেওয়াজ জড়িত। খুব কম মেয়েলোকই এই সূক্ষ্ম শিরক হতে রক্ষা পেয়েছে, আর এতদসংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদিতে শরিক হয়নি। অবশ্য আল্লাহ যাকে বাঁচিয়েছেন, সেই বেঁচেছে।
বর্তমানকালে অলী-আল্লাহ বলে কথিত লোকদের কবরে যা কিছু ঘটছে, ঘটছে বিশেষ পীরের বিশেষ মুরীদরা জীবিত পীরের দরবারে বা মৃত পীরের কবরে গিয়ে যা কিছু করছে, তার কাছ থেকে রূহানী ফায়েজ হাসিল করছে, বিপদে আপদে সাহায্য প্রার্থনা করছে, তা যে সম্পূর্ণরূপে শিরকী কাজ এবং মুসলিম সমাজে তা যে শিরকের বিদয়াত মুজাদ্দিদে আলফেসানীর কথার পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। অথচ বড়ই আফসোস, তাঁরই পরবর্তীকালে মুরীদ ও তস্য মুরীদরা আজ ঠিক সেই সব কাজই করেছে এবং তা সত্বেও নিজেদের ‘আহলে সুন্নাত আল জামায়াত’ হওয়ার দাবি করছে। মুজাদ্দিদে আলফেসানীর উপরোক্ত যুক্তিপূর্ণ কথার আলোকে এদেরকে ‘আহলে সুন্নাত না বলে বরং বলা যায় আহলে সুন্নাত আল বিদয়াত। মুজাদ্দিদে আলফেসানী(রহ) এ ধরনের কাজকে স্পষ্ট ভাষায় শিরকী কাজ এবং এই লোকদেরকে মুশরিক বলে অভিহিত করেছেন। কেননা একাজ কেবল মুশরিকদের দ্বারাই সম্ভব। মুশরিক লোকেরা এ ধরনের কাজ করে বলেইতো তারা মুশরিক। এ ধরনের কাজ না করলেতো তারা নিশ্চয়ই মুশরিক হতোনা। তাহলে এক শ্রেণীর মুসলিম বা পীর আলিম নামধারী লোকেরা যদি এরূপ কাজ করে, তবে তা কোনো শিরকী কাজ হবেনা এবং তারাই বা আল্লাহর দরবারে ‘মুশরিক’ রূপে নিন্দিত হবেনা কেন? দীর্ঘ আলোচনার শেষ পর্যায়ে এ কালের পীর-মুরীদ ও ‘অলী-আল্লাহ’ বলে কথিত লোকদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী(রহ) এর নসীহত, যা তিনি করেছিলেন তদানীন্তন বিদয়াতী পীরদের প্রতি-তা হলোঃ
-একালের তাসাউফপন্থীরা যদি ইনসাফ করে এবং ইসলামের দূর্বল অবস্থা ও মিথ্যার ব্যাপক রূপ লক্ষ্য করে তাহলে তাদের উচিত সুন্নাতের বাইরে তাদের পীরদের পায়রুবী না করা। আর মনগড়া বিষয়গুলোকে নিজেদের পীরদের আমল করতে দেখার দোহাই দিয়ে অনুসরণ না করা।
বস্তুত নবী করীম(স) এর অনুসরণ করে চলা নিঃসন্দেহে মুক্তির বাহন, ভালো ও মঙ্গলময় ফলের উৎস। সুন্নাতের বাইরের বিষয়গুলোকে অন্ধভাবে মেনে চলার মধ্যে বিপদের ওপর বিপদ রয়েছে।
তাবিজ তুমার ও কবর বাঁধার বিদয়াত
আমাদের সমাজে সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের মাঝে তাবিজ কবজ এবং এক শ্রেণীর বড় লোকদের মাঝে, বিশেষ করে বিদেশ সফরকালে ‘ইমামে জামেন’ বাঁধার একটি ব্যাপক রেওয়াজ রয়েছে দেখা যায়। এ সব লোক ইসলামের মৌলিক আদর্শের বড় একটা ধার ধারেনা, বুঝেও না তেমন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিপদে পড়লে বা বিপদ দেখা দিলে অথবা বিপদের আশংকা করলে হাতে, গলায় তাবিজ কবজ ও ‘ইমামে জামেন’ না বেঁধে তারা পারেনা। এরা মনে করে, এতে করে বিপদ কেটে যাবে কিংবা বিপদ আসতেই পারবেনা। কিন্তু কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এসব যে ইসলামের তওহীদী আকীদার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং মুসলমানদের মাঝে এটা যে একটা সম্পূর্ণ বিদয়াত ও শিরকী কাজ, সে কথা তারা ভেবে দেখবারও অবকাশ পায়না। একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, মূলত দোষ এ লোকদের নয়, এক শ্রেণীর আলিম বেশ ধারী মোল্লা মৌলবীরাই সাধারণ মানুষের মাঝে এ জিনিসের প্রচলন করেছে এবং এতে করে তারা দু পয়সা রোজগার করে খাচ্ছে। তারা অজ্ঞ মূর্খ লোকদের মনে তওহীদী আকীদার কোনো ধারণা সৃষ্টি করতেই চেষ্টা করেনি। বরং তার বিপরীতে এ ধারণা দিয়েছে যে, বিপদ কেটে যাবে। বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। অর্থাৎ তওহীদী আকীদার পরিবর্তে স্পষ্ট শিরকী আকীদাই তাদের মন মগজে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এক আল্লাহর ওপর সর্বাবস্থায় নির্ভর করার, আল্লাহর নিকট বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দো’আ করার কথা না শিখিয়ে তাদের পরিচালিত করা হয়েছে সুস্পষ্ট শিরকের পথে। এতে করে মুসলিম সমাজে তাবিজ কবজ ও ইমামে জামেন বাঁধার রেওয়াজ দিয়ে এক সুস্পষ্ট বিদয়াতকেই চালু করা হয়েছে মুসলমানদের মধ্যে।
অথচ যে কোনো আলিম কুরআনের দিকে তাকালে দেখতে পেত, কুরআন মুসলমানদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে ওজস্বিনী ভাষায় ঘোষণা করেছেঃ
وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ
–মুমিন-মুসলমানেরা কেবল আল্লাহরই রহমত পাওয়ার আশা করে এবং কেবল তারই আজাববে ভয় করে। (বনী ঈসরাইলঃ৫৭)।
অন্য কথায় তারা আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট, কোনো জিনিসের নিকট একবিন্দু সাহায্য, শান্তি ও নিরাপত্তা পেতে চায়না। তাদের মন কোনো অবস্থাতেই অন্য কারো দিকে, কিছুর দিকে আশান্বিত হয়না। অপর কারো ক্ষতির একবিন্দু ভয়ও তাদের মনে জাগেনা। তারা যেমন কোনো মৃত্যু ও অনুপস্থিত ব্যক্তি বা কোনো প্রাণহীন জিনিসের আশ্রয় নেয়না – না কোনো ফায়দা লাভের আশায়, না কোনো বিপদ বা ক্ষতি দূর করার উদ্দেশ্যে। বস্তুত এই তওহীদী আকীদা এবং এই হচ্ছে তওহীদবাদী মুমিনের পরিচয়।
কিন্তু তাবিজ-তুমার-কবজ বাঁধা এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা কুরআন মজীদের নিম্নোক্ত আয়াতের স্পষ্ট বিরোধী। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেনঃ
قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ
–বলো হে নবী! তোমরা কি লক্ষ্য করছো তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাকে তাকে ডাকো, আল্লাহ যদি আমাকে কোনো ক্ষতি করতে চান তাহলে কি তারা তা রোধ বা দূর করতে পারবে? কিংবা আল্লাহ যদি আমাকে কোনো রহমত দিতে চান তাহলে কি তারা আল্লাহর এ রহমতকে বাধা দিতে পারবে? (আঝ ঝুমার ৩৮)।
ক্ষতি বা রহমত দেয়ার একমাত্র নিরংকুশ মালিক এক আল্লাহই, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ নয়। আল্লাহ চাইলে ক্ষতি করে দেবেন, সে ক্ষতি থেকে সে বাঁচতে পারবেনা। অনুরূপভাবে আল্লাহ যদি কাউকে রহমত দান করতে চান, তাহলে সে রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবেনা, কেউ তাকে রহমত থেকে বঞ্চিত করতে পারবেনা। যার জন্য রহমত নির্দিষ্ট, সে রহমত অন্য কাউকেও দিতে পারবেনা কেউ। অবস্থা যখন এই, তখন বুদ্ধিমান লোকেরা কেন আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো ব্যক্তি, শক্তি বা জিনিসের কাছে কিছু পেতে চাইবে, পেতে চাইবে তার দয়া সাহায্য, পেতে চাইবে বিপদ হতে তার কাছে নিষ্কৃতি? আমাদের দেশে তাবিজ কবজ, ইমামে জামেন কি এ ধরনের জিনিস নয়? হাদীসে তো এসব সম্পর্কে স্পষ্ট নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যে কোনো আলিম এ হাদীস দেখতে পারেন। দেখলে বুঝতে পারবেন যে, হাদীসের দৃষ্টিতেই এসব শিরকী কাজ। এখানে আমরা কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করছি।
আরবী(***********)
-হযরত ইমরান ইবনে হুসায়ন (রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম(স) এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন, সে পিত্তরসের রোগ থেকে বাঁচার জন্য একটি আংটি হাতে পড়ে রেখেছে। তিনি অসন্তোষের সুরে জিজ্ঞেস করলেন, ‘ওটা কি পরেছ? বললো, রোগ হতে উদ্ধার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এটা পড়েছি। রাসূল(স) বললেন, ওটা খুলে ফেল। কেননা ওটা তোমার হাতে পরা থাকলে তোমার বিপদ বাড়িয়ে দেবে- কমাবেনা একটুও। আর এটা রাখা অবস্থায় যদি তুমি মরে যাও, তাহলে তুমি কখনোই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।
হযরত উকবা ইবনে আমের(রা) হতে বর্ণিত, নবী করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ আরবী(******)
-যে ব্যক্তি কোনো তাবিজ তুমার ঝুলাবে, আল্লাহ তাকে কোনো ফায়দা দেবেননা। আর যে কোনো কবজ ঝুলাবে, আল্লাহ তার বিপদ দূর করবেননা কখনো (কোনো শান্তি পাবেনা সে)।
অপর বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ আরবী(********)
-যে লোক কোনো তাবিজ কবজ বাঁধবে, সে শিরক করলো।
পরপর উল্লেখ করা এ তিনটি হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, কোনো ক্ষতি লোকসান বিপদ হতে উদ্ধার পাবার জন্য কিংবা কোনো স্বার্থ উদ্দেশ্য লাভের আশায় তাবিজ কবয বাঁধা সুস্পষ্ট শিরক। ঈমানের বুনিয়াদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ কালেমা বান্দার নিকট যে ইখলাস দাবি করে, এ কাজ তার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা যে লোক সত্যিকার ইখলাস সম্পন্ন মুমিন সে তো কারো নিকট হতে ফায়দা পাওয়ার বা কারো লোকসান থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনকে উন্মুখ করবেনা। অতএব এসব ত্যাগ না করলে পূর্ণ তওহীদের দাবি পূরণ হতে পারেনা। এটা ছোট শিরক বলে অনেকেই এর গুনাহ এর মারাত্মকতা লক্ষ্য করেনা, বরং উপেক্ষা করে। কিন্তু আসলে এ ছোট শিরক হলেও অত্যন্ত সাংঘাতিক। হাদীসের থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, নবী করীমের জীবদ্দশায় কোনো সাহাবীর নিকট এর মারাত্মক রূপ অস্পষ্ট বা অজানা ছিল। তা হলে বর্তমান কালের কম ইলমের ও দূর্বল ঈমানের লোকদের নিকট তা গোপন থাকায় আশ্চর্য্যের কি আছে- বিশেষত যখন চারিদিকে শিরক ও বিদয়াত ব্যাপকভাবে ছেয়ে গেছে।
হযরত হুযায়ফা(রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন সে জ্বরের তীব্রতার কারণে তাবিজ স্বরূপ একটি সুতা হাতে বেঁধে রেখেছে। তখন তিনি তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেনঃ ‘তারা অধিকাংশ লোকই আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি, বরং তারা মুশরিক।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ(রা) শিরক ও বিদয়াতের বিরুদ্ধে বড় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে গেছেন। যখন যেখানেই যে বিদয়াত বা শিরক দেখেছেন, তারই বিরুদ্ধে তিনি দ্রুত প্রতিবাদের আওয়াজ তুলেছেন, ক্ষিপ্র কার্য্কর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। একদা তিনি ঘরের মধ্যে গিয়ে তার স্ত্রীর গলায় একটা তাগা ঝুলতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করায় স্ত্রী জবাবে বললেনঃ এটা অমুক অসুখের টোটকা চিকিৎসার জন্য গলায় বেঁধেছি। তিনি সেটি ধরে এত শক্তভাবে টান দিলেন যে, সেটা ছিঁড়ে গেল। নতুবা তাঁর স্ত্রীই উপুড় হয়ে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেতেন। চরিত্রের দৃঢ়তার জন্যই শুধু তিনি তা করেননি বরং শিরক বিদয়াতের বিরুদ্ধে দ্বীনি দায়িত্ব পালনের জন্যই করেছিলেন।
জাহিলিয়াত যুগে ‘যাতে আনওয়াত’ নামে একটি বৃক্ষ ছিল, সেখানে কুরাইশ ও সমস্ত আরব প্রতি বছর একবার একত্রিত হতো এবং তাদের তরবারী সেই বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে দিত, তারই নিকট জন্তু জবাই করবো এবং একদিন তথায় সকলে অবস্থান করতো।
মক্কা বিজয়ের পর মক্কার নবদীক্ষিত মুসলমান ও মদীনা থেকে আগত সাহাবী সমভিব্যাহারে নবী করীম(স) হুনায়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে সে বৃক্ষটি দেখতে পেয়েই মক্কার নবদীক্ষিত মুসলিমগণ পার্শ্ব থেকে বলে উঠলোঃ হে রাসূল(স)! আমাদের জন্যও একটি ‘যাতে আনওয়াত’ বানিয়ে দিন, যেমন ওদের জন্য ‘যাতে আনওয়াত’ রয়েছে। এই কথা শুনেই নবী করীম(স) বললেনঃ আল্লাহু আকবার, তোমরাতো সে রকম কথাই বলছো যেমন মূসার সঙ্গীরা বলেছিল-ওদের যেমন পূজ্য দেবতা রয়েছে আমাদের জন্যও অনুরূপ দেবতা বানিয়ে দাও হে মূসা!
অর্থাৎ তাদের ঐ কথা যেমন ইসলামের তওহীদী আকীদার পরিপন্থী ছিল, আজকের তোমাদের এই কথাও তেমনি তওহীদী ঈমানের বিপরীত। কেননা ওদের কথার মতো এদের কথাও মুশরিকদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। ফলে তা একটি অতি বড় শিরকী কথা। ওদের মতো ‘যাতে আনওয়াত’ বানিয়ে তার সাথে তরবারী ঝুলানো, তার নিকট জন্তু যবাই করা এবং সেখানে একদিন অবস্থান করা এক আল্লাহর সাথে আর একজন ইলাহ বানানো সমতুল্য গণ্য হওয়ায় রাসূলে করীম(স) ওদের কথা প্রত্যাখ্যান করলেন। (তিরমিযী, মুসনাদের আহমদ, ইবনে জরীর ও ইবনে ইসহাকে ফীসীরাতে নবী)।
এ ঐতিহাসিক কথা যদি সত্যি হয়(কে বলবে তা সত্যি নয়) তাহলে একালের মুসলিমরা যে বড় বড় নামকরা অলী-পীর-গাওসের(?) কবরের নিকট অবস্থান করছে, তার নিকট দো’আ করছে, তাকে ডাকছে এবং তার দো’আ চাচ্ছে, তা পরিষ্কার শিরক ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য হবেনা কেন?
দু’টি কাজের মধ্যে শিরক হওয়ার দিক দিয়ে পূর্ণ মিল রয়েছে। এই ঘটনার প্রেক্ষিতেই ইমাম মালিকের ছাত্র আবু বকর তাতুশী লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা যেখানেই এ ধরনের বৃক্ষ দেখতে পাবে, যাতে কেন্দ্র করে জনতা একত্রিত হয়, বৃক্ষটির প্রতি সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে, রোগ ও বিপদে মুক্তি চায় তার নিকট এবং বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে ওরস করে-সেই বৃক্ষটিকে অবিলম্বে কেটে ফেলবে এবং শিরকের এই আড্ডাখানা ভেঙ্গে নির্মূল করে ফেলবে।
এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, হযরত হুযায়ফার দৃষ্টিতে জ্বর ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ তুমার বাঁধা পরিষ্কার শিরক। এটা ছোট শিরক হলেও সাহাবায়ে কিরাম তার প্রতিবাদে এমন সব আয়াত দলীল পেশ করতেন, যা বড় শিরকের প্রতিবাদে নাযিল হয়েছে। কেননা ছোট হলেও সেটা যে শিরক তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ জন্যে নবী করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(*****)
-তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচাইতে ভয় করি ছোট ছোট শিরককে।
অতএব শিরক যত ছোটই হোকনা কেন, আসলে তা আদৌ ছোট নয়। বরং সাহাবীদের দৃষ্টিতে ছোট শিরকও ছিল কবীরা গুনাহর চাইতেও বড় কঠিন।
কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহের দৃষ্টিতে আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত তাবিজ-তুমার-কবজ- ইমামে জামেন বাঁধার রেওয়াজটি সম্পর্কে চিন্তা করলে দুঃখে কলিজা ফেটে যায়। কেবল জাহিল লোকরাই যদি এসব করতো, তাহলে কোনো কথা ছিলনা। কিন্তু বড় বড় আলিম নামধারী লোকদেরও এই শিরকে নিমজ্জিত দেখতে পাচ্ছি। রাষ্ট্রপ্রধানের বিদেশ গমনকালে বিমানবন্দরে বিদায়কালে যখন একজন আলিম নামধারী ব্যক্তি ঘটা করে তাঁর হাতে ইমামে জামেন বেঁধে দেন, যখন বিদেশে বিবাহিতা মেয়ে রুখসত করার সময় মা কন্যার হাতে ইমামে জামেন বাঁধে এবং তার খবর খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ করা হয়, তখন তওহীদে বিশ্বাসী মানুষের মস্তক লজ্জায় ও দুঃখে নত না হয়ে পারেনা।
আমাদের গ্রা্ম্য মূর্খ সমাজে দেখা যায়, সদ্যজাত সন্তানের গলায় হাতে রাজ্যের বাজে জিনিস বেঁধে দেয়া হয়। বড়ইর আটি, তামার পয়সা, মোল্লার দেয়া তাবিজের ঢোল, নানা গাছ গাছড়ার পাতা বা শিকড়ের টুকরা ঝুলিযে দেয়া হয়। হাটা চলা করতে পারে-এমন ছেলে মেয়ের পায়ে মল, ঝুনঝুনি পরিয়ে দেয়া হয়- পুকুরের দিকে যেতে লাগলে টের পাওয়া যাবে, পানিতে পড়ে মরা থেকে তাকে বাঁচানো যাবে এই আশায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, যার মৃত্যু শিশুকালে নির্ধারিত থাকে তাকে এসব আবর্জনার বোঝা রক্ষা করতে পারেনা। মল বা ঝুনঝুনি পরা ছেলেমেয়েও পানিতে ডুবে মারা যায়। কেননা মৃত্যু এগুলোর ওপর নির্ভরশীল নয়। বস্তুত মানুষের ক্ষেত্রে এসবের শিরক হওয়া এবং সব রেওয়াজের বিদয়াত হওয়ার কোনোই সন্দেহ নেই। নবী করীম(স) যেমন এসব ব্যাপারে স্পষ্ট উক্তি করেছেন, নিষেধ বাণী উচ্চারণ করেছেন, তেমনি কার্য্তও তিনি জাহিলিয়াতের জামানায় প্রচলিত এসব রীতির প্রতিবাদ করেছেন। এমন কি তিনি জন্তু জানোয়ারের গলায়ও এসব বাঁধতে নিষেধ করেছেন, বাঁধা থাকলে তা ছিঁড়ে ফেলেছেন।
জাহিলিয়াতের জমানায় একটি রেওয়াজ ছিল, ভালো ভালো উটকে লোকদের নজরের দোষ থেকে বাঁচার জন্য উটের গলায় নানা তাবিজ-তুমার বাঁধা হতো। হযরত আবু বুশাইর-কুরাইশ ইবনে উবাইদ বলেন, একবার বিদেশ যাত্রাকালে তিনি রাসূল(স) এর সঙ্গী ছিলেন। নবী করীম(স) যাত্রার পূর্বেই একজন লোক পাঠিয়ে দিলেন এই বলেঃ আরবী(*****)
-কোনো উটের গলায় যেন এ ধরনের কোনো সূতা বাঁধা না থাকে, থাকলে তা যেন ছিঁড়ে ফেলা হয়।
ইমাম আহমদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন, নবী করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(****)
-তাবিজ-তুমার ও নির্ভরতার জিনিসগুলো ব্যবহার স্পষ্ট শিরক।
এ আলোচনার শেষভাগে একটি সন্দেহের অপনোদন প্রয়োজন। পূর্বের আলোচনা পাঠে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ বানালেও কি শিরক হবে? এর সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, সলফে সালেহীনদের মধ্যে কেউ কেউ কুরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ কবয বানানো জায়েয বলেছেন। কিন্তু কেউ কেউ এ কাজকেও হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। হযরত ইবনে মাসঊদ(রা) এই শেষের লোকদের মধ্যে অন্যতম। ফিকহবিদদের মধ্যে কাতাদাহ, শাবী, সাঈদ ইবনে জোবাইর ও এক বড় দল বলেছেনঃ তাবিজ তুমার ব্যবহার মাকরূহ(তাহরীম)। মুমিন মাত্রই কর্তব্য এগুলো পরিহার করা, আল্লাহর প্রতি ঈমান দৃঢ় রেখে তাঁর ওপর নির্ভর ও ভরসা করা এবং এই জ্ঞান সহকারে যে, তার কোনো ফায়দা দেয়না, তা ত্যাগ করলে কোনো ক্ষতি হবেনা।
আমার মনে হয়, এসব কাজের পিছনে যে মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা থাকে, তা চিন্তা করলে সবাই স্বীকার করবেন, এসব কাজ হারাম ও তওহীদ বিরোধী না হয়ে পারেনা- তা কুরআনের আয়াত দ্বারা বানানো হলেও নয়। কেননা একজন যখন বিপদে পড়ার আশংকায় এসব কাজ করবে, তার মনের লক্ষ্য আল্লাহ হতে অ-আল্লাহ জিনিসের দিকে কেন্দ্রীভূত হবে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে সে এই জিনিসের ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করবে। আর তওহীদরে দৃষ্টিতে এটাই শিরক। দ্বিতীয়ত এ কাজে কুরআনের আয়াত ব্যবহৃত হলে, তা যে কুরআনের সঠিক ব্যবহার নয়, কুরআন যে তাবিজ হয়ে থাকার জন্য দুনিয়াতে আসেনি, কুরআনের উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে তাকে অন্য কাজে ব্যবহার করা হয়, তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে? এত কুরআনের প্রকাশ্য অপমান, কুরআনের অপব্যবহার, কুরআনের এও এক প্রকার তাহরীফ-ব্যবহারিক তাহরীফ(বিকৃতি সাধন), কুরআনের অভিজ্ঞ তওহীদ বিশ্বাসী মানুষের নিকট তা কিছু মাত্র অস্পষ্ট নয়। তাই এ কাজ যত শীঘ্রই বন্ধ হবে মানুষ তা ত্যাগ করে খলীস তওহীদবাদী তওহীদপন্থী হয়ে উঠবে, ততই মঙ্গল। অন্তত সমাজের আলিমদের যে এজন্য বিশেষ তৎপর হওয়া উচিত এবং এসব জিনিসকে একটুও প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়, তা আমি জোর গলায় বলতে চাই।
অবশ্য এ থেকে একথা প্রমাণ হয়না যে, কোনো আকস্মিক বিপদে কুরআনের আয়াত পড়ে আল্লাহর রহমত চাওয়া যাবেনা কিংবা বিপদগ্রস্ত লোকের ওপর আল্লাহর শিফা লাভের জন্য ফুঁ দেয়া যাবেনা। তা যে করা যাবে, তা হাদীস থেকেই প্রমাণিত এবং বহু সংখ্যক ফিকহবিদও সে মত জাহির করেছেন।
মিলাদ অনুষ্ঠান বিদয়াত
মুসলমান সমাজে বহু দিন থেকেই মিলাদ পাঠ ও মিলাদের মজলিস অনুষ্ঠানের রেওয়াজ চলে আসছে।সাধারণভাবে মুসলমানরা একে বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করে এবং খুব আন্তরিকতা সহকারে তা পালন করে। কিন্তু কোনো এক সময় মুহুর্তের জন্যও বোধ হয় মুসলমানরা- মুসলিম সমাজের শিক্ষিত সচেতন জনতা-ভেবে দেখতেও রাজি হয়না যে, এ কাজ ইসলামী শরীয়ত মোতাবিক কিনা, সেই সুন্নাত মোতাবিক কিনা, যা মুসলমানেরা লাভ করেছে হযরত মুহাম্মদ(স) এর নিকট থেকে তাঁর প্রতি ঈমান আনার কারণে। এমন কি এ দেশের আলিম সমাজেও সমাজের এ আবহমান কাল হতে চলে আসা রেওয়াজের স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। কখনো তাকিয়ে দেখেনা-আমরা সুন্নাত মোতাবিক কাজ করছি, না বিদয়াত করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা এ গ্রন্থে বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে।
এ কথা সবাই জানেন ও স্বীকার করেন যে, প্রচলিত মিলাদের কোনো রেওয়াজ রাসূলে করীম(স) এর জীবনে ছিলনা, ছিল না সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও পরবর্তীকালের মুজাহিদদের সময়ে। এ মিলাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো এই যে, নবী করীম(স) এর প্রায় দুইশ বছর পরে এমন এক বাদশা এর প্রচলন করে, যাকে ইতিহাসে একজন ফাসিক ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জামে আজহারের শিক্ষক ডঃ আহমাদ শারবাকী লিখেছেন-চতূর্থ হিজরীতে ফাহিমীয় শাসকরা মিসরে এর প্রচলন করেন। একথাও বলা হয় যে, শায়খ উমর ইবনে মুহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি ইরাকের মুসল শহরে এর প্রচলন করেছেন। পরে আল মুজাফফর আবু সাঈদ বাদশাহ ইরাকের এরকেল শহরে মীলাদ চালু করেন। ইবনে দাহইয়া এ বিষয়ে একখানা কিতাব লিখে তাকে দেন। বাদশাহ তাকে এক হাজার দীনার পুরস্কার দেন।
এ পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বর্তমানে মিলাদ সুন্নাতের ব্যবস্থা নয়, সুন্নাত মোতাবিক ব্যবস্থাও এটি নয়। বরং তা সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত।
এর বিদয়াত হওয়ার সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলীল হচ্ছে এই যে, এই কাজ রাসূলে করীম(স) এর জমানায় ছিলনা, রাসূলের পরে খুলাফায়ে রাশেদুন তথা সাহাবায়ে কিরামের যুগেও তা একটি সওয়াবের কাজরূপে চালু হয়নি। এমন কি তার পরবর্তী যুগেও তাবেয়ী মুজতাহিদদের সময়েও এর প্রচলন হতে দেখা যায়নি। আর এ ইসলামী যুগে যে কাজ একটি ইবাদত বা সওয়াবের কাজ হিসেবে প্রচলিত হয়নি, পরবর্তীকালের কোনো লোকের পক্ষে তেমন কোনো কাজকে সওয়াবের কাজরূপে চালু করা সম্ভব হতে পারেনা, সে অধিকারও কাউকে দেয়া হয়নি।
একে তো ইসলামের জায়েয নাজায়েয, সওয়াব-গুনাহ এবং আল্লাহ রাসূলের সন্তোষ অসন্তোষের বিধি ব্যবস্থা কেবলমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতেই প্রমাণিত হবে। কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে প্রমাণিত নয় অথচ তাকে বড় সওয়াবের কাজ বলে মনে করা হবে, তার কোনো অবকাশই ইসলামে নেই। প্রকৃতপক্ষে এরূপ কাজই বিদয়াত। আর যে কাজ মূলতই বিদয়াত, সে কাজ কোনোরূপ সওয়াব হওয়ার আশা করাই বাতুলতা মাত্র। রাসূলে করী(স) কয়যুগের কল্যাণময়তার সাক্ষ্য দিয়েছেন নিজে এই বলেঃ আরবী(******)
-অতীব কল্যাণময় ইসলামী যুগ হলো আমার এই যুগ, তারপর পরবর্তীকালের লোকদের যুগ এবং তারপরে তৎপরবতীকালের লোকদের যুগ।
এ তিনটি যুগের কোনো এক যুগেই অর্থাৎ রাসূলের নিজের সাহাবীদের এবং তাবেয়ীদের যুগে মিলাদের এ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ মুসলিম সমাজে চালু হয়নি, হয়েছে তারও বহু পরে। কাজেই এ কাজে কোনো প্রকৃত কল্যাণ আছে বলে মনে করাই একটি বড় বিদয়াত। বিশেষত কয়েকটি বিশেষ কারণে মিলাদের এ অনুষ্ঠান মুসলমানদের আকীদা ও দ্বীনের দিক দিয়ে খুবই মারাত্মক হয়ে উঠে। কারণ কয়টি সংক্ষেপে এইঃ
(ক) এ অনুষ্ঠানে নবী করীম (স) এর জন্ম বৃত্তান্ত যেভাবে আলোচিত হয় বা আরবী উর্দূ বা বাংলা উচ্চারণে পঠিত হয়, তা মূলতই ঘৃণার্হ। অথচ ঠিক এই সময়েই নবী করীম(স) মজলিসে স্বশরীরে উপস্থিত হন বলে লোকদের আকীদা রয়েছে। কিন্তু সব বিশেষজ্ঞদের মতেই এ ধরনের আকীদা সুস্পষ্ট কুফরী। কুরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণায় এবং ফিকাহর দৃঢ় সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এরূপ আকীদার হারাম হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়েছে।
নবী করীম(স) দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে চলে গেছেন। তাঁর পক্ষে দুনিয়ায় ফিরে আসার আকীদা পোষণ করা শিরক। এ কাজ কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। আল আল্লাহর কুদরতের কাজ কোনো বান্দার জন্য ধারণা করা পরিষ্কার শিরক। এ পর্যায়ে ফতোয়ায়ে বাজ্জাজিয়ার কথা আবার উল্লেখ করা যেতে পারে।
তাতে লেখা হয়েছেঃ আরবী (******)
-হানাফী মাযহাবে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, নবী করীম (স) গায়েবের ইলম জানেন- এরূপ আকীদা যে রাখবে, সে কাফির হয়ে যাবে। কেননা এরূপ আকীদা আল্লাহর ঘোষণার সম্পূর্ণ বিপরীত। আল্লাহ ইরশাদ করেছেনঃ
قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۚ
-বল, আসমান জমিনে যারাই রয়েছে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউই গায়েব জানেনা।
যদি কেউ বিবাহের অনুষ্ঠানে বলে যে, আমার এ বিবাহের সাক্ষী হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল, তবে সে কাফির হয়ে যাবে বলে ফিকহর কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা সেতো রাসূল(স) কে আলীমুল গায়েব বলে বিশ্বাস করলো।
(খ) মিলাদ মাহফিল শিরনি মিঠাই বন্টনকে একান্ত জরুরী মনে করা হয়। আর মিলাদ মাহফিল এর অনুষ্ঠানকে ওয়াজিব এর পর্যায়ে গণ্য করা হয়। এভাবে কোনো নাজায়েয কাজকে ওয়াজিব বা জরুরী মনে করা হলে তা মাকরূহ হয়ে যাবে। ফিকহর কিতাবে বলা হয়েছেঃ যে মুবাহ কাজই ওয়াজিব গণ্য হবে, তা মাকরূহ হবে(আর মাকরূহ মানে মাকরূহ তাহরীম)।
(গ) নির্দিষ্ট দিন ও তারিখে মিলাদ করাকে জরুরী মনে করা হয়। অথচ শরীয়তে যখন কোনো তারিখকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়নি এ কাজের জন্য, তখন এরূপ করাতো শরীয়তের বিধানের ওপর নিজেদের থেকে বৃদ্ধি করার শামিল।
হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছেঃ আরবী(******)
-রাত্রিসমূহের মধ্যে কেবল জুম‘আর রাত্রিকেই তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য এবং দিনসমূহের মধ্যে কেবল শুক্রবারের দিনটিকেই নফল রোযার জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে নিওনা।
অতএব নফল রোযার জন্যই যখন কোনো রাত বা দিন নিজেদের থেকে নির্দিষ্ট করে নিতে রাসূলে করীম(স) সুস্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন, তখন মিলাদের জন্যই বা নিজেদের থেকে এ নির্ধারণ কেমন করে জায়েয হতে পারে!
(ঘ) মিলাদ মজলিসের সাজ সজ্জার জন্য খুব আলো বাতির ব্যবস্থা করা হয়, মোমবাতি আর আগরবাতির ধুম পড়ে যায়। এসব নিতান্তই বেহুদা কাজ। আর একাজে যে পয়সা খরচ করা হয়, তাও বেহুদা খরচ। এ কাজ নিষিদ্ধ, এর ওপরই আরোপিত হয় আল্লাহর ঘোষণাঃ
-বেহুদা অর্থ খরচ করোনা। কেননা বেহুদা খরচকারী শয়তানের ভাই।
এসব করা হয় যে অনুষ্ঠানে, যাতে করে আল্লাহর কালামের স্পষ্ট বিরোধিতা করা হয়, তা করে সওয়াব হতে পারে বলে মনে কার কি নিতান্ত আহাম্মকী নয়?
মওলানা রশীদ আহমদ গংগুহী মিলাদ সংক্রান্ত এক সওয়ালে জবাবে লিখেছেনঃ প্রচলিত ধরনের মিলাদ অনুষ্ঠান বিদয়াত ও মাকরূহ।
এ জবাবকে সমকালীন বহু গণ্যমান্য আলিম ‘সহীহ’ বলে সমর্থন করেছেন এবং ফতোয়ার দস্তখতও দিয়েছেন। মওলানা গংগুহী অন্যত্র লিখেছেনঃ শরীয়তে যা বিনা শর্তে রয়েছে, তাকে শর্তাধীন করা এবং যা শর্তাধীন রয়েছে তাকে শর্তমুক্ত করাই হলো বিদয়াত। যেমন মিলাদের মজলিস অনুষ্ঠান করা। আসলে আল্লাহর যিকির কিংবা রাসূলের জীবন চরিত বর্ণনা ও আলোচনা করা শরীয়তে মুস্তাহাব ও জায়েয। কিন্তু ঠিক সেই উদ্দেশ্যেই কোনো মজলিস অনুষ্ঠান করা বিদয়াত ও হারাম। আল্লাহ ও রাসূলের কথা বলা তো মুস্তাহাব; কিন্তু বিশেষভাবে মিলাদের আলোচনার শর্ত করা বিদয়াত।
ইমাম আল্লামা ইবনুল হাজ্জ লিখেছেনঃ
তারা যে সব বিদয়াত রচনা করে নিয়েছে, তন্মধ্যে একটি তাদের এই আকীদা যে, তারা এ পর্যায়ে যা কিছু করছে তাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং আল্লাহর নির্দেশাবলীর বহিঃপ্রকাশ। আর তা হচ্ছে এই যে, রবিউল আউয়াল মাসে তারা মিলাদের অনুষ্ঠান করে, যাতে কয়েক প্রকারের বিদয়াতের অনুষ্ঠান করে, হারাম কাজ করে। এমন কি, এতদূর বলেছেন যে, এসব মিলাদেরই কারণে সৃষ্ট বিপর্য্য়। তাতে কোনোরূপ সুর গান হোক আর মিলাদের নিয়্যত করা হয়, লোকদের সেজন্য দাওয়াত দেয়া হয়, উপরোল্লিখিত কোনো দোষের কাজ যদি তাতে নাও থাকে তবু শুধু এ কাজের নিয়্যত করার কারণেও তা বিদয়াতই হবে। কেননা মূলতই এ জিনিস দ্বীন ইসলামে অতিরিক্ত বৃদ্ধি। অতীতকালের নেক ও দ্বীনদার লোকদের আমল এরূপ ছিলনা অথচ তাদের অনুসরণ করাই উত্তম। তারা কেউ মিলাদের নিয়্যত করেছেন বলে কোনোই উল্লেখ নেই? আমরাতো তাঁদেরই অনুসরণ করি। কাজেই তাঁদের কাজের যতদূর সুযোগ-সুবিধ ও ক্ষেত্র বিশালতা ছিল, আমাদেরও তো ঠিক ততোদূরই থাকবে।
মওলানা আবদূর রহমান আল মাগরিবী আল হানাফী(রহ) তাঁর ফতোয়ায় লিখেছেনঃ মিলাদ অনুষ্ঠান করা বিদয়াত। নবী করীম(স) খুলাফায়ে রাশেদীন এবং ইমামগণ তা করেনওনি, করতে বলেনওনি। ‘শরীয়াতুল ইলাহিয়া গ্রণ্থেও এমনিই লেখা হয়েছে।
মাওলানা নাসিরুদ্দীন আল আওদী শাফেয়ী এক প্রশ্নের জবাবে এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ
মিলাদ পাঠের অনুষ্ঠান করা যাবেনা। কেনা সলফে সালেহীন কেউই এ কাজ করেছেন বলে বর্ণিত হয়নি। বরং তিন যুগ(তাবেয়ী পরবর্তী যুগ)পরে এক খারাপ জমানার লোকেরা এ কাজ নতুন করে উদ্ভাবন করেছে। যে কাজ সলফে সালেহীন করেননি, তাই আমরা পরবর্তী লোকদের অনুসরণ করতে পারিনা। কেননা সলফে সালেহীন এর অনুসরণই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এ বিদয়াতী কাজ করার প্রয়োজন কোথায়?
হাম্বলী মাযহাবের শায়খ শরফুদ্দীন(রহ) বলেছেনঃ দেশের এই শাসকমন্ডলী প্রতি বছর নবী করীম(স) এর মিলাদের যে উৎসব অনুষ্ঠান করে, তাকে খুব খারাপ ধরনের বাড়াবাড়ি ছাড়াও তা মূলতই একটা বিদয়াতী কাজ। নফসের খায়েশের অনুসরণ করে তারাই এ কাজ নতুন করে উদ্ভাবন করেছে। তারা জানেনা নবী করীম(স) কি করতে আদেশ করেছেন, আর কি করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তিনিই শরীয়তের বাহক ও প্রবর্তক।
কাযী শিহাবুদ্দীন(রহ) এক প্রশ্নের জবাবে লিখেছেনঃ
না, তা করা যাবেনা। কেননা তা বিদয়াত। আর সব বিদয়াতই সুস্পষ্ট গোমরাহী। সব গোমরাহীরই পরিণাম জাহান্নাম। জাহিল লোকেরা রবিউল আউয়াল মাসে প্রত্যেক বছরের শুরুতে যা কিছু করে, তা শরীয়তের কোনো জিনিসই নয়। আর নবী করীমের জন্মের কথা উল্লেখ করার সময় তারা যে দাঁড়ায়, মনে করে নবী করীমের রূহ তাশরীফ এনেছে এবং উপস্থিত আছে, এ এক বাতিল ধারণা মাত্র। এ আকীদা পরিষ্কার শিরক। ইমামগণ এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করছেন।
শামী চরিত গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেনঃ রাসূল(স) এর প্রেমিকদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে যে, তারা যখন নবী করীম(স) এর জন্ম বৃত্তান্ত শুনতে পায় তখন তারা তাঁর তাজীমের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। অথচ এই দাঁড়ানো বিদয়াত, এর কোনো ভিত্তি নেই।
মওলানা ফজলুল্লাহ জৌনপুরী বলেনঃ নবী করীমের ভূমিষ্ট হওয়ার কাহিনী শুনবার সময় সাধারণ মানুষ যে কিয়াম করে, তার কোনো দলীল নেই; বরং তা মাকরূহ।
কাযী নসিরউদ্দীন গুজরাটি লিখেছেনঃ কোনো কোনো জাহিল পীর এমন বহু বিদয়াত চালু করেছেন, যার সমর্থনে কোনো হাদীস বা কোনো নীতি কুরআন-সুন্নাতে পাওয়া যায়না। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রাসূলে করীমের জন্ম বৃত্তান্ত বলার সময় দাঁড়ানো।
মুজাদ্দিদে আলফেসানী শায়খ আহমদ শরহিন্দী লিখেছেনঃ ইনসাফের দৃষ্টিতে বিচার করে দেখুন। মনে করুন নবী করীম(স) যদি এ সময়ে বর্তমান থাকতেন, দুনিয়ায় জীবিত থাকতেন আর এ ধরনের মজলিস অনুষ্ঠান হতে দেখতেন, তবে কি তিনি এতে রাজি হতেন, এ অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন? এটাই নিশ্চিত যে, তিনি কিছুতেই এ কাজকে পছন্দ করতেননা। বরং এ কাজের প্রতিবাদই করতেন।
এসব মজলিস সম্পর্কে কুরআন মজীদের এ আয়াতটি বিশেষভাবে
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ۗ
প্রযোজ্যঃ –আল্লাহ তোমাদের প্রতি এই নির্দেশ জারি করেছেন, তোমরা যখন আল্লাহর আয়াতকে অমান্য করা হচ্ছে শুনতে পাও এবং তার ঠাট্টা বিদ্রুপ হতে দেখতে পাও, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবেন-যতক্ষণ না তারা অন্য কাজে মনোযোগী হয়ে পড়ে। অন্যথায় সে সময় তোমরাও তাদেরই মতো গুনাহগার হবে। (আন নিসাঃ140)
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতবী ও মুহীউস সুন্নাহ ইমাম বগভী লিখেছেনঃ যহহাক হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বলেছেন যে, এ আয়াতের আওতায় পড়ে গেছে দ্বীন ইসলামের নতুন উদ্ভাবিত সব কাজ এবং কিয়ামত পর্য্ন্ত যা কিছু বিদয়াত রচনা করা হবে তা সবই।
আয়াতের শেষাংশঃ
إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا [٤:١٤٠]
–নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিক ও কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্রিত করবেন, বিদয়াতী ও কাফির উভয়ের জন্য অত্যন্ত কঠোর সতর্কবাণী।
এ পর্যায়ে আমার শেষ কথা হলো, নবী করীম(স) দুনিয়ার মুসলমানদের আদর্শ, সর্বাধিক প্রিয়, আল্লাহর হেদায়াত ও রহমত লাভের একমাত্র মাধ্যম। এ জন্যে রাসূলে করীমের জীবনী, তাঁর চরিত্র ও কর্মাদর্শই এ অন্ধকার দুনিয়ায় একমাত্র মুক্তির আলোকস্তম্ভ। তাই সব মানুষের জন্য বারে বারে তা আলোচনা করতে হবে, পড়তে হবে, জানতে হবে, অন্যদের সামনে বিস্তারিতভাবে তা তুলেও ধরতে হবে, বাস্তব জীবনের কদমে কদমে তাঁকেই অনুসরণ করে চলতে হবে, তাঁকেই মানতে হবে, ভালোবাসতে হবে, তারই কাছ থেকে চলার পথের সন্ধান ও নির্দেশ লাভ করতে হবে। এছাড়া মুসলমানের কোনোই উপায় নেই, থাকতে পারেনা। কুরআন হাদীসে রাসূল(স) সম্পর্কে যেসব বুনিয়াদী হেদায়াত দেয়া হয়েছে, তার সারকথা এ-ই। কিন্তু রাসূলে করীম(স) কে পূজা করা চলবেনা। তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণা রাখা যাবেনা, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে কেবল আল্লাহর সম্পর্কেই রাখা যেতে পারে।
রাসূলে করীমের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানদার ব্যক্তির ইসলামের পথে চলার সবচেয়ে বড় পাথেয়। সে ভালোবাসা নিশ্চয়ই এত মাত্রাতিরিক্ত হবেনা, যা কেবল আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত। রাসূল(স) কে সে মর্যাদা, সে গুরুত্ব এবং সে ভালোবাসাই দিতে হবে, যা দিতে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এবং রাসূল(স) যা করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন।
এ পর্যায়ে আল্লাহর সবচেয়ে বড় হেদায়াত হচ্ছে রাসূলে করীম(স) কে অনুসরণ করা।
আয়াত হলোঃ
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٣:٣١]
-বলে দাও হে নবী! তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে তোমরা হে মুসলমানরা! আমার অনুসরণ করে চলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন, তিনি তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও দয়াবান।(আল ইমরানঃ ৩১)
এ আয়াতের মূল কথা হলো আল্লাহকে ভালোবাসলে নবীর অনুসরণ করতে হবে। নবীর অনুসরণ করলে আল্লাহর ভালোবাসা ও ক্ষমা লাভই হচ্ছে বান্দার সবচেয়ে বেশি-সবচেয়ে বড় কাম্য। আর তা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে রাসূলে করীম(স) এর সার্বিক অনুসরণ।
রাসূল(স) এর প্রতি উম্মতের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে দুরূদ পাঠ। কুরআন মজীদের আয়াতে বলা হয়েছেঃ আরবী(*******)
-নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি দুরূদ পাঠান। হে মুমিন লোকেরা! তোমরাও নবীর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাও।
নবীর প্রতি দুরূদ পাঠানো একটি মহৎ কাজ, একটি অতি সওয়াবের কাজ। আল্লাহ নিজে যে নবীর প্রতি দুরূদ পাঠান, পাঠান ফেরেশতাগণ, সে নবীর প্রতি দুরূদ পাঠানো যে কত বড় মুবারক কাজ, কত বেশি সওয়াব পাওয়া যাবে এ থেকে; তার ব্যাখ্যা করে শেষ করা সম্ভব নয়।
এছাড়া নবীর প্রতি উম্মতের আর কি করণীয় থাকতে পারে? নবীর জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা এবং নবীর জননীর প্রসব বেদনাকালীন ঘটনাবলীর উল্লেখ যে সওয়াব হবে এ কথা কে বললো? কেমন করে তা জানা গেল? আর এই যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে ‘ইয়া নবী সালাম আলাইকা’ ‘ইয়া হাবীব সালাম আলাইকা’ বলতে হবে আর এতে বড় সওয়াব হবে বলে মনে করা হচ্ছে, এ কথা তো কুরআন হাদীস থেকে প্রমাণিত নয়। অনেকের মতে এসব কাজ হিন্দুদের এক ধরনের পূজা অনুষ্ঠানের মতোই ব্যাপার। আর ইবাদত পর্যায়ের কোনো কাজেই অন্য ধর্মাবলম্বীর সাথে সাদৃশ্য হওয়া মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বর্জনীয়। কেননা নবী করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(******)
-যে লোক অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য রক্ষা করে চলবে, কিয়ামতের দিন সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে।
মিলাদ মাহফীলে নবী করীমের ‘রূহ’ হাযির হয়, এ কথা যদি তর্কের খাতিরেও মেনে নেয়া হয়, তবু প্রশ্ন এই যে, তখন সে কথা মনে করে মজলিসে সবাইকে দাঁড়াতে হবে কেন? রাসূলের জীবদ্দশায়ও কি সাহাবীগণ রাসূলের আগমনে তাজীমের জন্য দাঁড়াতেন এবং এ দাঁড়ানোয় রাসূলে করীম(স) খুশি হতেন কিংবা তিনি দাঁড়িয়ে কি তাঁর তাজীম করতে বলেছেন কোনোদিন? এ পর্যায়ে আমরা সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত জিনিস দেখতে পাই। মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হয়েছে যে, আনাস(রা) সাহাবীদের সম্পর্কে বলেনঃ আরবী(********)
-সাহাবীদের নিকট রাসূলে করীম(স) সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন রাসূলকে উপস্থিত দেখতে পেতেন, তাঁরা তাঁর জন্যে দাঁড়াতেননা। কেননা তাঁরা জানতেন যে, তাঁর তাজীমের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানোকে তিনি অপছন্দ করেন।
আবু মাজলাজ বলেনঃ হযরত মুআবিয়া(রা) এমন একটি ঘরে প্রবেশ করলেন, যেখানে হযরত ইবনে আমের ও ইবনে যুবায়র উপস্থিত ছিলেন। মুআবিয়ার আগমনে ইবনে আমের দাঁড়ালেন কিন্তু ইবনে যুবায়র বসে থাকলেন। তখন মুআবিয়া(রা) তাঁকে বললেনঃ আরবী(******)
-তুমি বসো। কেননা আমি রাসূলে করীমের(স) নিকট শুনেছি তিনি বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার সম্মানার্থে লোকেরা দাঁড়াক-এটা চায় এবং এতে খুশী হয়, সে যেন জাহান্নামে নিজের ঘর বানিয়ে নেয়।
নবী করীম(স) নিজে মোটেই পছন্দ করতেননা, চাইতেননা যে তাঁর তাজীমের জন্য লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। তার প্রমাণ হযরত আবু ইমামের বর্ণনা। তিনি বলেনঃ আরবী(******)
-নবী করীম(স) লাঠির ওপর ভর দিয়ে আমাদের সামনে আসলেন। তখন আমরা তার তাজীমের জন্য দাঁড়িয়ে গেলাম। নবী করীম(স) বললেনঃ অমুসলিম লোকেরা যেমন পরস্পরের তাজীমের জন্য দাঁড়ায়, তোমরা তেমনি করে দাঁড়াবেনা।
রাসূলে করীমের(স) এ কথাটিকে কেউ কেউ তাঁর স্বভাবজনিত বিনয় বলে অভিহিত করতে পারেন। বলতে পারেন, রাসূলে করীম(স) বিনয়বশত তাঁর তাজীমার্থে কাউকে দাঁড়াতে বলেননি বা দাঁড়ালেও নিষেধ করেছেন। তাই বলে আমরা কি দাঁড়িয়ে তাঁর প্রতি সম্মান দেখাব না?
এরূপ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্ যে কতো ভয়াবহতা এ লোকেরা বুঝতে পারেনা। তাঁর মানে এই হয়ে যে, তিনি নিষেধ করেছেন কৃত্রিমভাবে, আসলে দাঁড়ানটাকেই তিনি পছন্দ করতেন, দাঁড়ালে তিনি খুশি হতেন, তাতে সওয়াবও হয়। অথচ প্রশ্ন এই যে, যে যে কাজ করলে মুসলমানরা সওয়াবও পেতে পারে কিংবা তাদের তাজীমার্থে দাঁড়ালে যদি সওয়াবই হতো বা তা যদি নবীর প্রতি মুসলমানদের কর্তব্যই ছিল, তবে এভাবে নিষেধ করার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। তিনি অকপটে তা বলতে পারতেন, যেমন বলেছেন তাঁর জন্য দুরূদ পড়তে, তাঁকে অনুসরণ করতে, এ ব্যাপারে কৃত্রিমতার কোনোই প্রয়োজন ছিলনা। আর নবীর পক্ষে কৃত্রিমতা করা সম্ভব বা কৃত্রিমতা করেছেন বলে মনে করা- দ্বীনের মূলের ওপরই কুঠারাঘাত। কোনো ঈমানদার লোকের পক্ষেই এরূপ ধারণা করা সম্ভবপর নয়।
মনে রাখা আবশ্যক- রাসূলে করীমের রূহ মিলাদে হাযির হয় মনে করে তাঁর তাজীমার্থে দাঁড়ানোর ব্যাপারটিই এখানে আমাদের আলোচ্য। নতুবা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিদের আগমনে সাময়িকভাবে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রসন্নচিত্তে সংবর্ধনা জানানো এবং তাঁকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার জন্য দাঁড়ানো এ থেকে ভিন্ন কথা। সহীহ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত সায়াদ ইবনে মুয়ায (রা) যখন তাঁর জন্তুযানে চড়ে আসছিলেন, তখন খোদ নবী করীম(স) আনসারদের নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ তোমরা তোমাদের নেতার প্রতি সম্মানা প্রদর্শনার্থে দাঁড়াও। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোনো মর্যাদাবান ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখানো নাজায়েয নয়। বরং জমহুর আলিমগণ তা মুস্তাহাব বলেছেন। এ পর্যায়ে কোনো নিষেধ পাওয়া যায়নি।
খোদ নবী করীম(স) স্নেহের আতিশয্যে তদীয় দুহিতা হযরত ফাতিমা(রা) এর জন্যও দাঁড়িয়েছেন। এই দাঁড়ান নিষিদ্ধ নয়। বরং নিষিদ্ধ হচ্ছে সেই দাঁড়ানো, যে সম্পর্কে রাসূলে করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(********)
-যে লোক পছন্দ করবে যে লোকেরা তার প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য দাঁড়াক, সে যেন তার আসন জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।
কোনো প্রকৃত ঈমানদারই তা পছন্দ করতে এবং দাঁড়িয়ে তাকে সম্মান দেখালে নিশ্চয়ই খুশি হতে পারেনা। অতএব কোনো নেতা বা ব্যক্তি খুশি হবে-এ জন্য দাঁড়ানো সম্পূর্ণ হারাম।
এ বিস্তারিত আলোচনার দৃষ্টিতে বর্তমানে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক মিলাদ মাহফিল এবং প্রতি বছর অতীব ধুম-ধামের সহিত ১২ই রবিউল আওয়ালের ‘ফাতিহা-ই-দোয়াজদহম’ নামের অনুষ্ঠান জাতীয় উৎসবরূপে পালন করা যে সুস্পষ্ট বিদয়াত, তাতে কোনোই সন্দেহ থাকতে পারেনা। সাহাবী, তাবেয়ীন ও তাবে তাবেয়ীন এর যুগে এর কোনো একটিরও কোনো দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারেনা। কুরআন হাদীস থেকেও এর অনুকূলে কোনো দলীল পেশ করা সম্ভব নয়। কাজেই এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আল্লাহর কোনো সওয়াব পাওয়ার আশা করাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এগুলোকে জাতীয় অনুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পালন করার, পালন করে রাসূলের প্রতি একটা বড় দায়িত্ব পালন করা হলো বলে আত্মশ্লাঘা লাভ করা কিংবা এসবের মাধ্যমে নিজেদেরকে রাসূলের বড় অনুসারীরূপে জাহির করে জনগণকে ধোঁকা দেয়া শুধু বিদয়াতই নয়, বিদয়াত অপেক্ষাও অধিক বড় ধৃষ্টতা, সন্দেহ নেই।
কদমবুসির বিদয়াত
বর্তমানকালের পীর ও আলিমদের দরবারে কদমবুসির বড় ছড়াছড়ি দেখা যায়। মুরীদ হলেই পীরের কদমবুসি করতে হয়, মাদ্রাসার ছাত্র হলেই ওস্তাদ হুযুরের কদমবুসি করতে বাধ্য। তা না করলে না মুরীদ ফায়েজ পেতে পারে পীরের, না ছাত্র ওস্তাদের কাছ হতে লাভ করতে পারে ইলম। বরং উভয় দরবারেই সে বেয়াদব বলে দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ‘বড় কুরআনের (?) দলীল পেশ করে বলা হয়ঃ আরবী(*******)
-বেয়াদব লোক আল্লাহর অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হয়ে যায়।
কদমবুসি করলে আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয় কিনা- তা আল্লাহই জানেন। কিন্তু এ ধরনের মুরীদ আর ছাত্র যে পীর ও ওস্তাদের স্নেহ দৃষ্টি থেকে মাহরুম হয়ে যায় তা বাস্তব সত্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, এই কদমবুসি করা কি সত্যই শরীয়ত মোতাবিক কাজ? এ জিনিস মুসলিম সমাজে কোথ্থেকে এসে প্রবেশ করলো? এর ফলাফলই বা কি?
সাহাবায়ে কিরামের সামনে নবী করীম(স) এর যে সম্মান ও মর্যাদা এবং নবী করীম(স) কে সাহাবায়ে কিরাম যতদূর ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, তার তুলনা অন্য কোথাও হতে পারেনা এবং সেই রকম সম্মান শ্রদ্ধা অন্য কাউকেই কেউ দিতে পারেনা। কিন্তু সেই সাহাবীগণ বাহ্যত নবী করীমের প্রতি কিরূপ সম্মান দেখাতেন? এ পর্যায়ে হাদীসে শুধু এতটুকুরই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, সাহাবীদের কেউ কেউ নবী করীমের হাতে ও কপালে হালকা ভাবে চুমু দিয়েছেন। এই চুমু’য় ভক্তির চাইতে ভালোবাসাই প্রকাশ পেতো সমধিক। তাঁদের কেউ কোনোদিন রাসূলে করীমের পা হাত দিয়ে স্পর্শ করে সে হাত দ্বারা মুখমন্ডল মুছে দেয়ার যে কদমবুসি, তা করেছেন বলে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যাবেনা হাদীসের বা জীবন চরিতের কিতাবে।
এ পর্যায়ে হাদীসে শুধু এতটুকুই উল্লেখ পাওয়া যায় যে, কোনো কোনো সাহাবী ভালোবাসার আতিশয্যে কখনো কখনো নবী করীম(স) এর হাত পা চুম্বন করেছেন। কিন্তু নির্বিশেষে সব সাহাবীর মধ্যে এ জিনিসের কোনো প্রচলন ছিলনা। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন এর যুগেও মুসলিম সমাজে এর কোনো রেওয়াজ দেখা যায়নি। এ কদমবুসির কোনো নাম নিশানাই পাওয়া যায়না ইসলামের এ সোনালী যুগের ইতিহাসে। তাহলে এ কাজটি যে ইজমা ও মুতাওয়াতির ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত তা অনস্বীকার্য্।
তা ছাড়া ইসলামী শরীয়তের একটি মূলনীতি হলো, কোনো মুবাহ বা সুন্নাত মোতাবিক কাজও যদি আকীদা বা আমলের ক্ষেত্রে খারাবী পয়দার কারণ হয়ে পড়ে, তাহলে তা করার পরিবর্তে বরং না করাই ওয়াজিব। এ কারণেই হযরত ওমর ফারূক(রা) সে গাছটি কেটে ফেলেছিলেন, যার পাদদেশে বসে নবী করীম(স) ঐতিহাসিক ‘বায়’আতে রেজওয়ান’ গ্রহণ করেছিলেন। কেননা তাঁর সময়কার লোকেরা এ গাছের নিকট সমবেত হওয়াকে সুন্নাতী কাজ বলে মনে করতো এবং তার নিকট রীতিমত হাজিরা দেওয়াকে একান্ত জরুরী ও সওয়াবের কাজ বলে মনে করতে শুরু করেছিল। অথচ এ জামানা ছিল ইসলামের উজ্জ্বলতম যুগ। এ জন্যে ইলমে ফিকহর মূলনীতি দাঁড়িয়েছেঃ যে মুবাহ কাজ ওয়াজিবের পর্যায়ে পৌছে যায়, তা করা মাকরূহ।
তা ছাড়া কদমবুসি করার সময় মানুষ ঠিক সে অবস্থায় পৌছে যায় , যে অবস্থায় পৌছে নামাযের রুকু ও সেজদার সময়ে, আর ইচ্ছে করে কারো জন্য এরূপ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।
কাযী ইয়াজ লিখেছেনঃ (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে)সেজদা করা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি রুকূর ধরনে কারো সামনে মাথা নত করাও নিষিদ্ধ।
আল মুজাদ্দিদে আল ফেসানী(রহ) লিখেছেনঃ কারো সামনে মাথা নত করা কূফরীর কাছাকাছি।
আর ফিকাহবিদদের মত হলোঃ রাজা বাদশাহ বা অন্য কারো জন্য মাথা নোয়ানো মাকরূহ। আর মাকরূহ মানে মাকরূহ তাহরীম।
এ সব কথা থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, পীর, ওস্তাদ বা অন্য কোনো মুরুব্বী- তিনি যেই হোননা কেন, তার যে কদমবুসি করতে হবে ইসলামী শরীয়তে তার কোনো নিয়ম নেই। আর এ কাজ রাসূলে করীমের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী-অতি বড় বিদয়াত।
কদমবুসি সম্পর্কে আর একটি কথা হলো, এর রেওয়াজ কেবল পাক ভারতের আলিম ও পীরের দরবারেই দেখা যায়। অন্যান্য মুসলিম সমাজে এর নাম নিশানাও নেই। এ কারণে এ কথা সহজেই মনে করা যেতে পারে যে, কদমবুসির এ কাজটি এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজ থেকে মুসলিম সমাজে এসে তা মুসলমানী রূপ পরিগ্রহ করেছে। মুসলিম সমাজের বর্তমান কদমবুসি ছিল আসলে ‘ব্রাক্ষ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত’। এখনো তা দেখা যায় এখানে সেখানে। যজমান ব্রাক্ষ্মণের সামনে আসলেই ব্রাক্ষ্মণ তার বাঁ পায়ের বুড়ো অঙ্গুলী উঁচু করে ধরবে, আর যজমান তার কপাল সে অঙ্গুলির অগ্রভাগে স্থাপন করবে। অতঃপর যখন ইচ্ছা ব্রাক্ষ্মণ তার পা টেনে নেবে। ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্মে এ রীতি আদিম। কেননা ব্রাক্ষ্মণ্য ধর্ম দর্শনে ব্রাক্ষ্মণরাই মানুষ আর অন্যান্যরা ব্রাক্ষ্মণের দাসানুদাস। অতএব ব্রাক্ষ্মণের পদপ্রান্তে প্রণিপাত করাই তাদের কর্তব্য।
পরবর্তীকালে এ দেশের হিন্দুরা মুসলমান হয়ে এ হিন্দুয়ানী ব্রাক্ষ্মণ্য প্রথাকেই- এ ‘পদপ্রান্তে প্রণিপাতকে’ই ‘মুসলমান’ বানিয়ে কদমবুসিতে পরিণত করে দিয়েছে। এক কথায় সম্পূর্ণ হিন্দুয়ানী ব্রাক্ষ্মণ্য প্রথাকে মুসলিম সমাজে-বিশেষ করে পীর সাহেবান ও আলিম ওস্তাদ সাহেবানের দরবারে বড় সওয়াবের কাজ হিসেবে চালু করে দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু এর কুফল, যা মুসলিম সমাজে প্রতিফলিত হয়েছে, তওহীদের দৃষ্টিতে তা খুবই ভয়াবহ। পীর মুরীদী আর ওস্তাদ শাগরিদীর পরিবেশে এ কদমবুসি রীতিমত শিরকী ভাবধারা বিস্তার করে দিয়েছে। মুরীদ আর ছাত্র মনে করে এ কাজ অপরিহার্য্। অন্যথায় হুজুরের নেক নজর পাওয়া যাবেনা, হুজুর খুশি হবেননা। দ্বিতীয়ত, হুজুর তো এমন উঁচু মর্যাদার যে, তিনি যা-ই বলবেন, অথবা যাতে তাঁর দিল খুশি হবে, তাই করা তাঁর কর্তব্য। তার উপর টু শব্দ করাও চরম বেয়াদবী। আর তাতে আল্লাহ বেজার হবেন। অথচ ইসলামের তওহিদী আকীদায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহর এবং বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে রাসূল(স) ছাড়া এ মর্যাদা আর কারোই হতে পারেনা।
অপরদিকে ‘হযরত পীর কেবলা’ ও ওস্তাদ হুযুরের মনে এ বাসনা স্পষ্টত মনে থাকে- তারা তো ফেরেশতা নয়, মানুষই-যে, মুরীদ বা ছাত্র আমার কদমবুসি করবেই। অনেক হুজুরকে এমনভাবে প্রস্তুত হয়েই আসন গ্রহণ করতে দেখা যায় যে, মুরীদ বা ছাত্রের পক্ষে পায়ে হাত দিতে যেন কোনো অসুবিধা না হয়। বরং অনায়াসেই যেন একাজ সম্পাদিত হতে পারে। তাই বলে তাঁরা মুখে কাউকে কদমবুসি করতে বলেন, এমন নয়; বরং তাঁরা নিষেধই করে থাকেন। আর সে নিষেধ বাণীটা উচ্চারিত হয় কদমবুসির কাজটা যথারীতি সম্পন্ন হয়ে যাবার পর, তার আগে নয়। আর সে নিষেধও ঠিক আদেশেরই অনুরূপ।
সবচেয়ে বড় কথা, কদমবুসির যে রূপটি তা সেজদার মতোই। আল্লামা শামী তাঁর সময়কার অবস্থা অনুযায়ী এ ধরনের কাজকে ‘সেজদা’ বলেই অভিহিত করেছেন।
তিনি লিখেছেনঃ এমনিভাবে লোকেরা যে আলিম ও বড় লোকদের জমিনবুসি করে, এ কাজ সম্পূর্ণ হারাম। আর যে একাজ করে এবং যে তাতে রাজি থাকে- খুশি হয়, উভয়ই গোনাহগার হয়। কেননা একাজ ঠিক মূর্তি পূজা সদৃশ্য।
দেওবন্দের মুফতী মাওলানা রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী-ও এরূপই ফতোয়া দিয়েছেন। (আহসানুল ফতোয়া দ্রষ্টব্য)।
বস্তুত কুরআন হাদীসে কদমবুসির কোনো উল্লেখ নেই, ইসলামী তাহযীব ও তমদ্দুনের ক্ষেত্রে এর কোনো স্থান নেই। এর পরিবর্তে কুরআন-হাদীসে সালাম দেয়ার ও মুসাফাহা করার উল্লেখ এবং সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।
কুরআন মজীদে সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا [٤:٨٦]
- তোমাদেরকে যখন কোনো প্রকার সম্ভাষণে সম্ভাষিত করা হবে, তখন তোমরা তার অপেক্ষা উত্তম সম্ভাষণে সম্ভাষিত করো অথবা ততোটুকুই ফিরিয়ে দাও। মনে রেখো, আল্লাহ সর্ব বিষয়ে নিশ্চিত হিসাব গ্রহণকারী। (আন নিসাঃ৪৬)
এ থেকে সুস্পষ্ট বোঝা গেল, মুসলমানদের পরস্পরের যখন দেখা সাক্ষাত হবে, তখন পরস্পরের সম্ভাষণের আদান প্রদান করবে। এ সম্ভাষণ মৌখিক হতে হবে এবং এ সম্ভাষণের ব্যাপারে পরস্পরে ঐকান্তিক নিষ্ঠা পোষণ করতে হবে এবং কোনোরূপ কৃপণতা পোষণ করা চলবেনা। বরং প্রত্যেককে অপরের তুলনায় উত্তম সম্ভাষণ দানে প্রস্তুত থাকতে হবে অকুন্ঠিতভাবে। আয়াতের শেষ অংশ এ সম্ভাষণের গুরুত্ব এবং তা যথারীতি আদান প্রদানের জন্য সতর্কতা অবলম্বন করার নির্দেশ দিচ্ছে।
হাদীসে নবী করীম(স) বারবার নানাভাবে পারস্পরিক সালাম আদান প্রদানের জন্য তাগিদ দিয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা(রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ
আরবী(********)
-আমার প্রাণ যে আল্লাহর মুষ্টিবদ্ধ তাঁর কসম করে বলছিঃ তোমরা জান্নাতে যেতে পারবেনা, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান আনবে, আর তোমরা ঈমান আনতে পারবেনা যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। অতঃপর বললেনঃ আমি কি তোমাদের এমন একটা কাজের পথ দেখাব, যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? তা হলো এই যে, তোমরা তোমাদের পরস্পরের মাঝে সালাম দেয়ার প্রচলনকে চালু করবে।
নবী করীম(স) হিজরত করে মদীনায় উপস্থিত হলে মদীনার মুসলমানগণে তাঁকে সাদর সম্বর্ধনা জানিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম এ সম্বর্ধনার বিবরণ দান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ আরবী(************)
-নবী করীম(স) যখন মদীনায় উপস্থিত হলেন, তখন জনগণ তাকে সম্বর্ধনা করার উদ্দেশ্যে দ্রুততা সহকারে এগিয়ে এল। যারা এই সময় সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন। …এই সময় আমি যে কথা তাঁকে যে কথা সর্বপ্রথম বলতে শুনেছিলাম তা হলোঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি সালাম আদান প্রদান করো।
কুরআনের আয়াত থেকে পারস্পরিক সম্ভাষণের যে হেদায়াত পাওয়া যায়, সে সম্ভাষণ যে কি এবং কিভাবে, কি কথা দিয়ে তা করতে হবে, তার সঠিক সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় এ হাদীস থেকে। অতএব নতুন সাক্ষাতকালে একজন মুসলমানের অপর মুসলমানের প্রতি প্রথম জরুরী কর্তব্য হচ্ছে সালাম দেয়া, বলা আসসালামু আলাইকুম। আর অপর পক্ষ জবাবে বলবেঃ ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। বুখারী শরীফের একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত আদম(আ) সৃষ্ট হওয়ার পরই আল্লাহর নির্দেশক্রমে ফেরেশতাদের সাথে এই সালামের আদান প্রদান করেছিলেন।
শেষোক্ত হাদীস থেকে একজন নবাগত মহাসম্মানিত মেহমানকে সম্বর্ধনা জানাবার সঠিক নিয়ম সম্পর্কে সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ জানতে পারা যায়। এই পর্যায়ে অপর হাদীস থেকে জানা যায়, এ সালাম করার সময় কি ধরনের আচরণ অবলম্বন করা উচিত এবং কি ধরনের অনুচিত।
এই পর্যায়ে যত হাদীসই বর্ণিত হয়েছে, তা সব সামনে রেখে চিন্তা করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ‘সালাম’ মুখে উচ্চারণ করার-কথার মাধ্যমে বলে দেবার ব্যাপার। এজন্যে কোনোরূপ অঙ্গভঙ্গি করা জরুরী নয়, তা হাদীস থেকেও প্রমাণিত নয়।
দ্বিতীয় যে কাজ নবাগত মুসলিমের সাথে করার কথা হাদীস থেকে সুন্নাত বলে প্রমাণিত, তা হলো মুসাফাহা করা। বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, হযরত কাব ইবনে মালিক(রা) বলেনঃ আরবী(******)
-আমি মসজিদে নববীতে প্রবেশ করলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম সেখানে নবী করীম(স) রয়েছেন। আমাকে দেখেই তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ দাঁড়িয়ে আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসলেন। আমার সাথে মুসাফাহা করলেন এবং আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে গেলেন।
বুখারীর অপর হাদীস থেকে জানা যায়, তাবেয়ী কাতাদাহ হযরত আনাস(রা) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আরবী(********)
-নবী করীমের(স) সাহাবীদের পরস্পর মুসাফাহা করার রীতি বহুল প্রচলিত ছিল কি? হযরত আনাস(রা) জবাবে বললেন, হ্যা, তা চালু ছিল।
আবদুল্লাহ হিশাম বলেন, আমরা নবী করীমের সঙ্গে ছিলাম। আর তিনি হযরত উমরের হাত ধরে ছিলেন।
এ পর্যায়ের হাদীস থেকে নবাগতের সাথে সালামের পর মুসাফাহার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় এবং তা রাসূলে করীম(স) এর সাহাবীদের সমাজে পুরা মাত্রায় চালু ছিল বলে অকাট্যভাবে জানা যায়।
এই সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে বর্ণিত একটি হাদীস সর্বাধিক স্পষ্টভাষী। হযরত আনাস ইবনে মালিক(রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলে করীম(স) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ আরবী(*******)
-ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমাদের একজন তার ভাই বা বন্ধুর সাথে যখন সাক্ষাত করে, তখন কি সে তার জন্য মাথা নুইয়ে দিবে? রাসূল(স) বললেনঃ না। জিজ্ঞেস করলো, তবে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে ও তার মুখমন্ডলে চুমু খাবে? রাসূল(স) বললেনঃ না। জিজ্ঞেস করলোঃ তবে কি তার হাত ধরে মুসাফাহা করবে? রাসূল(স) বললেনঃ হ্যা।
এ হাদীস সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী বলেছেন-‘মুসাফাহা’ হাতে হাত ধরা ও পরস্পরের জন্য দো‘আ করা ‘আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের মাফ করে দিন’-বলবে।
এর ফযীলত বর্ণনা সম্পর্কে রাসূলে করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ আরবী(********)
-দু’জন মুসলমান পরস্পরের সাক্ষাতকালে যদি মুসাফাহা করে, তাহলে দু’খানি হাত বিচ্ছিন্ন করার আগেই সে দুজনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়।
হাদীসে তৃতীয় যে জিনিসের উল্লেখ পাওয়া যায়, তা হচ্ছে ‘মুয়ানাকা’-কোলাকুলি। তিরমিযী শরীফে এ সম্পর্কে যে একমাত্র হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাহলো হযরত আয়েশা(রা) বলেনঃ
আরবী(********)
-যায়দ ইবনে হারিসা [রাসূল(স) এর পালিত পুত্র] মদীনায় উপস্থিত হলো। তখন নবী করীম(স) আমার ঘরে এলেন। যায়দ তাঁর সাথে দেখা করার জন্য এলো এবং দরজায় ধাক্কা দিলো। নবী করীম(স) তার কাছে উঠে গেলেন এবং তিনি তার সাথে গলাগলি করলেন, একজন আরেকজন এর গলা জড়িয়ে ধরলেন এবং তাকে স্নেহের চুম্বন দিলেন।
এ পর্যায়ে আরো কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে আল্লামা আহমাদুল বান্না লিখেছেনঃ এসব হাদীস প্রমাণ করে যে, মুয়ানাকা(গলাগলি বা কোলাকুলি)শরীয়তে জায়েয। বিশেষ করে যে আসবে তার সাথে।
নবী করীম(স) এর সাহাবীদের তরীকা ছিলো এই যে, যখন তাঁরা পরস্পরের সাথে দেখা করতেন, পরস্পরের মুসাফাহা করতেন। আর যখন বিদেশ সফর করে ফিরে আসতেন, তখন তাঁরা পরস্পরে গলাগলি করতেন।
এ আলোচনা থেকে জানা গেল, ইসলামের সুন্নাত হচ্ছে এই যে, দু’জন মুসলমান যখন পরস্পর সাক্ষাত করবে তখন সালাম করবে, মুসাফাহা করবে এবং গলাগলিও করবে-বিশেষ করে বিদেশাগত ব্যক্তির সাথে। এসব কয়টি কথাই সুস্পষ্ট হাদীস থেকে প্রমাণিত। রাসূলে করীম(স) তাই করেছেন, সাহাবাদের সমাজে এই ছিল স্থায়ী রীতি, বস্তুত এই হচ্ছে সুন্নাত। কিন্তু এই কদমবুসি এল কোথ্থেকে? কে কদমবুসি করতে বলেছে? কে তা রেওয়াজ করেছে ইসলামী সমাজে? কুরআন নয়, হাদীস নয়, রাসূল নয়, রাসূলের গড়া সমাজ নয়। অতএব এটি বিদয়াত ও মুশরিকী রীতি হওয়ার কোনোই সন্দেহ নেই। অথচ আমাদের সমাজের তথাকথিত পীরবাদি আহলে সুন্নাত(?) দের সমাজে কদমবুসি একটি অপরিহার্য্ রীতি। আর তা হবেই না বা কেন? এখানে ইসলাম ও সুন্নাত কুরআন, হাদীস, রাসূল ও সাহাবাদের আমল থেকে গ্রহণ করা হয়না, গ্রহণ করা হয় মরহুম বা বর্তমান পীর সাহেবানদের কাছ থেকে। আর এ ধরনের পীর মুরীদী যেহেতু বেদান্তবাদী ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী থেকে গৃহীত, তাই কদমবুসির ব্রাক্ষ্মণ্য রীতিও এখানে চালু হতে বাধ্য। কেউ যদি বলেন যে, ওস্তাদ, পীর ও মুরুব্বীদের তাজীম করার জন্যই এ রীতি চালু করা হয়েছে, তাহলে বলবো-ওস্তাদ, পীর ও মুরুব্বীদের তাজীমের তরীকা সুন্নাত থেকে যা প্রমাণিত তাই দিয়ে তাজীম করতে হবে। নিজেদের মনগড়া একটা রীতিকে চালু করার বিশেষ করে তাতে যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে ভয়ানক খারাবী থাকে-কারো অধিকার থাকতে পারেনা। করলে তাই তো হবে বিদয়াত। যারা চলতি প্রথার দোহাই দিয়ে শরীয়তের বাইরের জিনিসকে শরীয়তসম্মত বলে চালু করতে চাইবে, তারাইতো বিদয়াতী। আল্লাহ এই বিদয়াতীদের প্রভাব থেকে বাঁচান ঈমানদার ও তওহীদবাদী মুসলিম সমাজকে।
কদমবুসি পর্যায়ে আলোচনার শেষভাগে একটি কথার উল্লেখ করে তার জবাব না দিলে এ দীর্ঘ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কোনো কোনো পীরের অনুমোদনক্রমে প্রকাশিত তাসাউফ সংক্রান্ত কদমবুসি- বিশেষ করে পীর ওস্তাদের কদমবুসি-করা জায়েয বলে ফতোয়া দেয়া হয়েছে। এ ফতোয়ার দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে দুটো হাদীস। একটি হাদীস তিরমিযী থেকে, অপরটি আবু দাঊদ থেকে। প্রথম হাদীসটিতে দু’জন ইয়াহুদীর কথা বলা হয়েছেঃ তারা রাসূলে করীমের নিকট দ্বীন ইসলামের ব্যাখ্যা শ্রবণ করে। অতঃপর তারা রাসূলে করীমের দু’হাত ও দু’পা চুম্বন করলো এবং বললোঃ আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি নবী।
এ সম্পর্কে আমাদের প্রথম কথা হলো, ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে উত্তম বিশুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন বটে, কিন্তু ইমাম নাসায়ী হাদীস সম্পর্কে বলেছেন-অগ্রাহ্য হাদীস। আর মুনযেরী বলেছেন, হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে সালেমার কারণেই যয়ীফ। কেননা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে তাঁর দোষ বের করা হয়েছে। তাছাড়া হাদীসের সুস্পষ্ট কথা হলো-হাত ও পা চু্ম্বনের কাজটি দু’জন ইয়াহুদী করেছে। ইয়াহুদীদের কাজ মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় হতে পারেনা। আবু দাউদ বর্ণিত অপর হাদীসে ঊমামাত ইবনে শরীক(রা) এর কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ আরবী(******)
-আবু দাউদে উদ্ধৃত হাদীসে রাসূলে করীম(স) এর হাত বা পা নয়, কটিদেশ চুম্বনের কথা বলা হয়েছে। (হযরত উসাইদ ইবনে উজাইর(রা) হতে হাদীসটি বর্ণিত। একজন আনসারের কথায় রাসূলে করীম(স) তাঁর পরিহিত জামা পিছনের দিক দিয়ে তুলে ধরলে তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করলেন এবং তার কটিদেশে চুম্বন করতে লাগলেন।)
দ্বিতীয় কথা, এ পর্যায়ের সব কটি হাদীসকে একত্রিত করে বিচার করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, এসবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সব হাদীসে একই রকম নয়। কোনোটিতে শুধু দু’হাত চুম্বনের কথা বলা হয়েছে, কোনোটিতে এক হাত, এক পা চুম্বনের কথা বলা হয়েছে। এমন কি হযরত ইবনে উমর(রা) হতে বর্ণিত হাদীসে শুধু হাত চুম্বনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছেঃ আরবী(*******)
-অতঃপর আমরা তাঁর হাত চুম্বন করলাম। তিনি বললেনঃ এবং আবু লুকাবা ও কাব ইবনে মালিক এবং তাঁর দু’জন সঙ্গীও নবী করীম(স) এর হাত চুম্বন করলেন, যখন আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করলেন। এ কথা আবরাহীও উল্লেখ করেছেন।
ইবনে উমার বর্ণিত এ হাদীসটি ইমাম বুখারী ‘আদাবুল মুফরাদ’ নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত বুরাইদা ইবনে বর্ণিত একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, জনৈক বুদ্ধু লোক রাসূলের মস্তক ও দু’পা চুম্বনের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূলে করীম(স) তাকে অনুমতি দেন। আবদুর রহমান ইবনে রুজাইন বলেছেন, সালেমা ইবনুল আকওয়া তাঁর উটের হাতের মতো হাত বের করলেন, আমরা তা চুম্বন করলাম। সাবিত হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আনাসের হাত চুম্বন করলেন। আর হযরত ‘আলী নাকি’ হযরত আব্বাসের হাত ও পা চুম্বন করেছিলেন।
এভাবে বর্ণিত হাদীসসমূহ হতে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়না। মূলত হাত পা দু’টোই চুম্বন করার কথা ঠিক, না শুধু হাত চুম্বনের কথাই ঠিক। কাজেই এসব হাদীসের ভিত্তিতে কদমবুসি করা জায়েয কিছুতেই বলা যায়না। আবু মালিক আল আশযায়ী বলেনঃ আমি আবু আওফ(রা) কে বললাম, আপনি যে হাত দিয়ে রাসূলের বায়’আত করেছেন, তা বের করুন। তিনি সে হাত বের করেন। অতঃপর আমরা তা চুম্বন করি।
এ ধরনের হাদীস হতে কোনো আবিদ জাহিদ ব্যক্তির হাত ভক্তিভরে চুম্বন করা জায়েয প্রমাণিত হয় বটে; কিন্তু কদমবুসি প্রমাণিত হয়না। ইমাম নববীও এ মত প্রকাশ করেছেন।
আরো কথা হলো, কোনো নওমুসলিম যদি ভক্তি শ্রদ্ধায় ভারাক্রান্ত হয়ে রাসূলে করীমের হাত ও পা উভয়ই চুম্বন করে থাকেন, তবে তার ভিত্তিতে আজকের পীর ওস্তাদেরা ভক্ত মুরীদ ও ছাত্রদের দ্বারা নিজেদের হাত পা চুম্বন করাতে পারেননা। তাঁরা কি নিজেদের রাসূলের মর্যাদাভিষিক্ত মনে করে নিয়েছেন?
বস্তুত কদমবুসির বর্তমান রেওয়াজ রাসূলের সুন্নাতের বিপরীত; মানবতার পক্ষে চরম অবমাননাকর। অনতিবিলম্বে এ প্রথা বন্ধ হওয়া বাঞ্চনীয়।
সমাজে নারীদের প্রাধান্যও বিদয়াত
ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত, কুরআন দ্বারা ঘোষিত এবং রাসূলে করীম(স) দ্বারা বাস্তবায়িত। তাতে নারীদের নারী হিসেবে মর্যাদা ও অধিকার পুরোপুরি স্বীকৃত। কিন্তু নারীদের মর্যাদা পুরুষের ওপরে নয়, নীচে-প্রথম নয়, দ্বিতীয়- নিরংকুশ নয়, শর্তাধীন।
এ পর্যায়ে কুরআনের ঘোষণাঃ
الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
–পুরুষগণ নারীদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ কতক মানুষকে অপর কতক মানুষের ওপর অধিক মর্যাদা দিয়েছেন এই নিয়মের ভিত্তিতে এবং এজন্যও যে, পুরুষরাই তাদের ধন সম্পদ নারীদের জন্য ব্যয় করে।(আন নিসাঃ৩৪)।
নারীদের তুলনায় পুরুষদের মর্যাদা অধিক হওয়ার একটি কারণ স্বাভাবিক গুণ-বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ত্ব। আর দ্বিতীয়, পরিবার পরিচালনা ও আর্থিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নারীদের তুলনায় পুরুষরাই দায়ী-তারাই তা করে থাকে। এটাই পারিবারিক জীবনে ক্ষুদ্র সংকীর্ণ পরিসরে এবং বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুতা ও শৃঙ্খলা বিধানের জন্য কার্য্কর নিয়ম। এর ব্যতিক্রম হলে সামাজিক শৃঙ্খলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে বাধ্য। তাই রাসূলে করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(********)
-আমার পরে আমার উম্মতের জন্য সর্বাধিক ক্ষতিকর ফিতনা পুরুষদের ওপর আসতে পারে নারীদের প্রাধান্যের কারণে।
নারী প্রাধান্যের কারণেই বহু সমাজ ও রাষ্ট্র বিপর্য্স্ত হয়েছে; ইতিহাসই তার অকাট্য প্রমাণ।
হযরত আবু বকর(রা) নবী করীম(স) এর এ কথাটি বর্ণনা করেছেনঃ যে জনসমষ্টি তাদের সামষ্টিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ও কর্তৃত্ব কোনো নারীকে অর্পণ করবে, তারা কখনোই কোনো কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা।
আরও বর্ণিত হয়েছেঃ আরবী(***********)
-পুরুষই যখন নারীদের আনুগত্য করতে থাকে, মনে করো তখনই পুরুষরা ধ্বংসের মধ্যে পড়ে গেছে।
এ কথার সত্যতা যেমন বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজের অবস্থা প্রমাণ করে, তেমনি আমাদের এতদ্দেশীয় সমাজ ও পরিবারে অবস্থা থেকেও তার সত্যতা প্রমাণিত হয়। নারীকে যদি নৌকার হাল ধরতে দেয়া হয়, ড্রাইভারকে বসিয়ে যে ড্রাইভিং জানেনা বা যোগ্যতা নেই তাকে মোটর চালনা করতে দিয়ে যে অবস্থা দেখা দেয়, স্বাভাবিক নারী প্রাধান্যের পরিণতিও তা-ই হবে। এটা সুন্নাতে রাসূলের পরিপন্থী। (এটাই সাধারণ সত্য। ব্যতিক্রম থাকা অসম্ভব নয়)।
পোশাক পরিচ্ছদ এর বিদয়াত
আমাদের দেশে বর্তমানে ‘সুন্নাতী লেবাস’ বলে এক ধরনের বিশেষ কাটিং ও বিশেষ পরিমাণের লম্বা কোর্তা পরিধান করা হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে যে, এই হচ্ছে সুন্নাতী পোষাক। আর এ সুন্নাতী পোষাক যে না পরবে সে ফাসিক বলে বিবেচিত হবে এবং এমন লোক যদি আলিম হয়, তাহলে তার পিছনে নামায পড়া জায়েয হবেনা। এ কারণে সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোক-আলিম ও পীরগণ এ ধরনের কোর্তা পরাকেই সুন্নাত মনে করেন, ‘সুন্নাতী পোশাক’ বলেই তারা এর প্রচারও করেন। শুধু নিজেরাই তা পরিধান করেননা, তাঁদের ছাত্র ও মুরীদানকেও অনুরূপ কাটিং ও লম্বা মাপের কল্লিদার কোর্তা পরিধান করতে বাধ্য করে থাকেন।
কিন্তু প্রশ্ন এই যে, সুন্নাতী পোশাক বলতে কি বোঝায়, কোনো বিশেষ কাটিং বা বিশেষ লম্বা মাপের জামা পরা কি সত্যিই সুন্নাত? সে সুন্নাত কোন দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হলো? কুরআন থেকে? হাদীস থেকে? কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বিষয়টিকে বুঝতে চেষ্টা করবো।
পোশাক কি রকম হতে হবে সে সম্পর্কে কুরআন মজীদে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আয়াত হলো এই।
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ [٧:٢٦]
-হে আদম সন্তান! নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক(পরিধানের বিধান)নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। আর তাকওয়ার পোশাক, তা-ই কল্যাণময়। এ হচ্ছে আল্লাহর আয়াতসমূহের অন্যতম; এবং বলা হচ্ছে এই আশায় যে, তারা নসীহত কবুল করবে।(আল আরাফঃ২৬)
এ আয়াত থেকে কয়েকটি মৌলিক কথা জানতে পারা যায়। প্রথম এই যে, পোশাক মানুষের জন্য আল্লাহ তা‘আলার এক বিশেষ দান। অতএব পোশাক সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। সে পোশাক কি রকমের হতে হবে; সে বিষয়ে এ আয়াত থেকে দু’টো কথা জানতে পারা যায়।
একটি হলো, পোশাক এমন হতে হবে যা অবশ্যই মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে। যে পোশাক মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করেনা, তা মানুষের পোশাক হতে পারেনা। আর দ্বিতীয় কথা হলো, সে পোশাককে ‘ভূষণ’ হতে হবে।(رِيش শব্দের মানে হলো উজ্জ্বল্য, চাকচিক্য, শোভাবর্ধক। আভিধানিকদের মতে رِيش শব্দের আসল অর্থ হলো পাখির পালক যা চাকচিক্যময় ও শোভাবর্ধক হয়ে থাকে। আর মানুষের পোশাকও যেহেতু পাখির পক্ষ ও পালকের মতোই, এ কারণে মানুষের পোশাক বাহ্যত কেমন হবে তা বোঝাতে رِيش শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।) পোশাক পরলে যেন দেখতে মানুষকে ভালো দেখায়, বদসুরত যেন না হয়, সেদিকে খেয়াল করতে হবে। বস্তুত পোশাকই মানুষের সৌন্দর্য্ বৃদ্ধি করে, পোশাকের মাধ্যমে মানুষের সৌন্দর্য্ বোধ, ভদ্রতা, শালীনতা ও রুচি-সুস্থতা প্রমাণিত হয়। আর পোশাক যদি সে রকম না হয়, তা হলে আল্লাহর দেয়া এক সুন্দর ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা হবে, হবে আল্লাহর নাশোকরী।(নতুন পোশাক পরে যে দো‘আটি পড়তে রাসূলে করীম(স) বলেছেন তা হলোঃ ‘প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিয়েছেন, যা দ্বারা আমি লজ্জাস্থান আবৃত করি এবং আমার জীবনে শোভা ও সৌন্দর্য্ লাভ করি।’ এ দো‘আতে ও সেই ছতার ঢাকা এবং প্রশংসা লাভের লক্ষ্যের কথাই বলা হয়েছে, পোশাক পড়ার মূলে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। এ ঠিক কুরআনের আয়াতেরই ব্যাখ্যা যেন।)
এর সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ভূষণ ও শোভার ব্যাপারে মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল এবং স্থান, কাল ও মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে রুচির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। অতএব কুরআনের মতে পোশাকের ধরণ ও কাটিং পরিবর্তনশীল। কোনো ধরাবাঁধা কাটিং এর পোশাক ইসলামী পোশাক বলে অভিহিত হতে পারেনা।
এ আয়াতের তৃতীয় কথা হলোঃ তাকওয়ার লেবাস। তাকওয়ার লেবাস কাকে বলে এ বিষয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কাতাদাহ বলেছেন, ‘লেবাসুত-তাকওয়া’ বলে এখানে ঈমান বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দুটি পরিচয়সহ পোশাক পরতে হবে, কিন্তু এ ব্যাপারে সর্বাধিক কল্যাণময় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ঈমানকে তাজা রাখা, সঠিকরূপে বহাল রাখা। হাসান বসরী এর মানে বলেছেনঃ লজ্জা, লজ্জাশীলতা, শালীনতা। কেননা, এই লজ্জাশীলতা ও শালীনতাই মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। ইবনে আব্বাস(রা) বলেছেন- তা হলো, নেক আমল। ওসমান ইবনে আফফান(রা) বলেছেন, তা হলো নৈতিক পবিত্রতা।
আর আয়াতের মানে হলোঃ তাকওয়ার পোশাক ভালো-কল্যাণময়, যদি তা গ্রহণ করা হয় আল্লাহর সৃষ্ট পোশাক ও সৌন্দর্য্ ব্যবস্থা থেকে।
মোটকথা, পোশাককে প্রথমে লজ্জাস্থান আবরণকারী হতে হবে। এজন্যে নারী ও পুরুষের পোশাকে মৌলিকভাবে পার্থক্য হতে বাধ্য এ কারণে যে, পুরুষের লজ্জাস্থান এবং নারীদেহের লজ্জাস্থানের পরিধির দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তা অবশ্যই ভূষণ বা শোভাবর্ধক ও সৌন্দর্য্ প্রকাশক হতে হবে। যে পোশাক মানুষের আকার-আকৃতিকে কিম্ভূতকিমাকার বা বীভৎস করে দেয়, চেহারা বিকৃত করে দেয়, সে পোশাক কুরআন সমর্থিত পোশাক নয়, কোনো মুসলমানের পক্ষেই তা ব্যবহারযোগ্য হতে পারেনা।
এই পর্যায়ে কুরআন মজীদ থেকে দ্বিতীয় যে আয়াতটি উদ্ধৃত করা যায় তা হলো এইঃ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
-বলো হে নবী! আল্লাহর সৌন্দর্য্- যা তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বের করেছেন- তা কে হারাম করে দিলো? (আল আরাফঃ৩২)
‘আল্লাহর সৌন্দর্য্’ মানে মানুষের জন্য আল্লাহর সৃষ্টি করে দেয়া সৌন্দর্যের সামগ্রী, আর তা হলো্ পোশাক ও অন্যান্য সৌন্দর্যের উপাদান, সৌন্দর্য্ বৃদ্ধিকারী জিনিসপত্র। অর্থাৎ পোশাক ও সৌন্দর্য্ বৃদ্ধিকারী দ্রব্যাদি তো আল্লাহরই সৃষ্টি এবং তিনি তা সৃষ্টি করেছেন তাঁর বান্দাদের জন্য। তিনি তা ভোগ ব্যবহার করার জন্যই বানিয়েছেন, মূলগতভাবেই তা সকলের জন্য জায়েয। এ জায়েয জিনিসকে কে হারাম করে দিতে পারে? আল্লাহর সৃষ্টি জিনিসকে হারাম করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আর তিনিই একে হালাল করে দিয়েছেন-শুধু একে হালাল-ই করে দেননি, তা গ্রহণ ও ব্যবহার করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি এই বলেঃ
আরবী(*******)
-তোমাদের সৌন্দর্য্ বৃদ্ধিকারী জিনিস- পোশাক- তোমরা তা গ্রহণ করো প্রতি নামাযের সময়।
এ আয়াতেও সেই পোশাক গ্রহণের কথাই বলা হয়েছে যা হবে জিনাত, শোভামন্ডিত, সৌন্দর্য্ বৃদ্ধিকারী। অতএব পোশাক গ্রহণের ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী মূলগতভাবে তিনটি জিনিসের দিকেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবেঃ প্রথমত লজ্জাস্থান আবরণকারী, দ্বিতীয় ভূষণ, শোভাবর্ধনকারী এবং তৃতীয় সে পোশাক শালীনতাপূর্ণ হতে হবে, লজ্জাশীলতার অনুভূতির প্রতীক হতে হবে, নির্লজ্জতাব্যঞ্জক হবে না তা।
কুরআন মজীদে পোশাক সম্পর্কে যে হেদায়াত পাওয়া যায়, তা এই। এছাড়া কুরআন থেকে পোশাক পর্যায়ে আর কিছু জানা যায়না। কুরআন থেকে যা জানা গেল, তাতে কিন্তু পোশাকের কাটিং, ধরন, আকার ও পরিমাণ দৈর্ঘ্য প্রস্থ সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি।
অতঃপর দেখতে হবে, এ বিষয়ে হাদীস থেকে কি জানা যায়। সর্বপ্রথম বুখারী শরীফের ‘কিতাবুল লিবাস’ এ উদ্ধৃত হাদীস লক্ষ্যণীয়। নবী করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(********)
-তোমরা খাও, পান করো, পোশাক পরো এবং দান-খয়রাত করো। (আর এসব কাজ করবে দুটো শর্তে) না বেহুদা খরচ করবে, না অহংকারের দরুণ করবে।
খাওয়া, পান করা, পোশাক পর এবং দান খয়রাত করা সম্পর্কে রাসূলে করীমের এ নির্দেশ। এ কাজ অবাধ ও উন্মুক্ত-কেবলমাত্র দুটো শর্তের অধীন। একটি হলো, এর কোনোটিই বেহুদা বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনকারী হবেনা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে অহংকারের বশবর্তী হয়ে একাজগুলো করবেনা। বাঞ্চনীয় নয় এমন এমন পরিমাণ অতিরিক্ত ব্যয় করাই হলো ‘ইসরাফ’। আর অহংকার করা, খুব বেশী দামী পোশাক এবং বাহদুরী ও বড়মানুষী প্রকাশ হয় যে পোশাকে তা নিষিদ্ধ। আর পোশাক পর্যায়ে আমাদের জন্য হেদায়াত এই যে, প্রথম বেহুদা খরচ হয় যে পোশাকে, যে ধরনের যে পরিমাপের পোশাক, তা পরিধান করা সুন্নাতের খেলাফ। পোশাককে অবশ্যই এ থেকে মুক্ত হতে হবে। আর দ্বিতীয়ত গৌরব অহংকারবশত কোনো পোশাক পরা এবং যে ধরনের, যে আকারের ও যে পরিমাপের পোশাক পরলে গৌরব-অহংকার, বড় মানুষী ও বাহাদুরী প্রকাশ পায়, যা মানুষকে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট করে দেয়, তা পরা যাবেনা। তা পরলে হবে সুন্নাতের বিপরীত কাজ। অতএব ব্যয় বাহুল্য ও অহংকার বিবর্জিত যে কোনো আকারের, প্রকারের ধরনের, কাটিং এর এবং পরিমাপের পোশাকই সুন্নাত অনুমোদিত পোশাক। সুন্নাতী লেবাস তাই, যা হবে এরূপ। হযরত ইবনে আব্বাস(রা) বলেছেনঃ আরবী(*****)
-তুমি খাও, যা-ই চাও, তুমি পরো যাই তোমার ইচ্ছা, যতক্ষণ পর্য্ন্ত দুটো জিনিস থেকে তুমি ভুলে থাকবেঃ ব্যয় বাহুল্য বেহুদা খরচ ও গর্ব অহংকার প্রকাশক বস্ত্র।
অর্থাৎ এ দুটো বিকার থেকে মুক্ত যে কোনো পোশাকই হাদীস মোতাবিক পোশাক এবং তা পরা সম্পূর্ণ জায়েয। আকার, ধরন, কাটিং ও লম্বা খাটোর ব্যাপারে হাদীস কোনো বিশেষ নির্দেশ দেয়নি, আরোপ করেনি কোনো বাধ্যবাধকতা।
বুখারী শরীফেই এরপর যে হাদীসটি উদ্ধৃত হয়েছে, তা হলো এইঃ
আরবী(*********)
-নবী করীম(স) বলেছেনঃ আল্লাহ এমন কোনো ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেননা, সে আল্লাহর রহমত থেকে হবে বঞ্চিত।
মনে রাখতে হবে, এ হাদীস থেকে জামা কাপড়ের আকার, কাটিং বা দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো হেদায়াত পাওয়া যাচ্ছেনা। শুধু মানসিক ব্যাপারেই নির্দেশ করা হয়েছে। কাপড় পরার বাহ্যিক ধরণ কি হবে, কি না হবে তা-ই বলা হয়েছে। আর অহংকারের ভাব নিয়ে যাই করা হবে, যেভাবেই অহংকার প্রকাশ পাবে, তা-ই নিষিদ্ধ হবে।
অতঃপর বুখারী শরীফের সব কয়টি হাদীসই আপনি পড়ে যান, কোনো একটি হাদীসেও পোশাক সম্পর্কে বিশেষ কোনো কাটিং বা পরিমাপ গ্রহণের নির্দেশ পাবেননা। তবে হাদীস থেকে এ কথা জানা যায় যে, নবী করীমের কোর্তার আস্তিন বা হাত ছিল খুবই সংকীর্ণ। তা থেকে এখানকার চুরিদার আস্তিনের জামা পরা জায়েয প্রমাণিত হয়। নবী করীম(স) যে কামীস পরতেন তা কতখানি লম্বা ছিল? একটি হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, তা খুব লম্বা ছিলনা। হাদীসটির ভাষা এইঃ আরবী(*********)
-নবী করীমের কামীস সাধারণত সূতীর কাপড় দিয়ে তৈরী হতো এবং তার ঝুল খুব কম হতো ও আস্তিন চুরিদার হতো।
এ থেকে অকাট্যভাবে জানা গেল যে, যারা বলে বেড়ায় যে, নবী করীম(স) অর্ধেক নলা পর্য্ন্ত ঝুল কোর্তা পরেছেন, তারা বানানো মিথ্যা কথা বলেছেন। সত্য কথা হলো তিনি লুংগী পরলে খাটো কোর্তা পরিধান করতেন।
তিরমিযী শরীফে পোশাক পর্যায়ে যে হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যে ও প্রথম হাদীস হলো এইঃ
আরবী(*******)
-নবী করীম(স)বলেছেনঃ আমার উম্মতের পুরুষ লোকদের জন্য রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে, আর মেয়েদের জন্য হালাল করা হয়েছে।
অর্থাৎ পুরুষদের জন্য রেশমী পোশাক হারাম।
এছাড়া মুসনাদে আহমদ এর একটি হাদীস থেকে পরিধেয় বস্ত্রের ঝুল কতখানি হওয়া উচিত সে বিষয়ে একটা সুস্পষ্ট ধারণা মেলে। হযরত আবু হুরায়রা(রা) বর্ণনা করেনঃ আরবী(*********)
-ঈমানদার লোকদের ইজার পায়ের দুই নলার মাঝ বরাবর ঝুলতে পারে। এর নীচে যেতে পারে পায়ের গিরা ওপর পর্য্ন্ত। এর নীচে গেলে তা হবে জাহান্নামে যাওয়ার কাজ।
হাদীসে ইজার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে পরিধেয় বস্ত্র, যা কোমরের নীচের দিক ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হয়। তা লুঙ্গি হতে পারে, পাজামা হতে পারে, হতে পারে আজকালকার পোশাক প্যান্ট বা অন্য কিছু। এগুলো ঝুল হাঁটু হতে গিরা পর্য্ন্তকার মাঝ বরাবর ‘নিসফে সাক’ পর্য্ন্ত হতে পারে। ‘নিসফে সাক’ এর নীচে পায়ের গীরা পর্য্ন্ত ও ঝুলতে পারে; কিন্তু এর নীচে গেলে তা জায়েয হতে পারেনা।
নবী করীম(স) এর এ পর্যায়ের হাদীসসমূহকে ভিত্তি করে হযরত ইবনে উমর(রা) বলেনঃ আরবী(*******)
-রাসূলে করীম(স) ইজারকে পায়ের গীরার নীচে ঝুলবার ব্যাপারে যে আযাবের কথা বলেছেন, তা-ই তিনি বলেছেন কামীস এর ব্যাপারেও।
‘কামীস’ হলো গাত্রাবরণ, শরীরের ঊর্ধ্বভাগ ঢাকার জন্য যাই পরিধান করা হয়, তাই কামীস তার কাটিং বা ধরন যাই হোকনা কেন। তা এখনকার পাঞ্জাবী, শার্ট, কোর্ট বা কল্লিদার জামা-যে কোনোটাই হতে পারে। তার কাটিং কি হবে, সে বিষয়ে হাদীস কিছুই বলছেনা। বলছে শুধু এ কথা যে, তা যেনো এতদূর লম্বা না হয় যে, তদ্দারা পায়ের গিরাও ঢেকে যায়। হযরত ইবনে উমরের কথা থেকে স্পষ্ট জানা গেল যে, পায়ের গিরার নিচে ইজার বা কামীস যাই ঝুলবে, তাই হারাম হবে। মনে রাখতে হবে যে, তদানীন্তন আরব সমাজে সাধারণত একখানা কাপড় দিয়ে শরীরের ওপরভাগ হতে হাটুর নীচের ভাগ পর্য্ন্ত ঢেকে ফেলত। এমনকি বর্তমানেও আরবদের পোশাক এরকমই। নীচে ছোটো-খাটো একটা পরে, আর তার ওপর দিয়ে পায়ের গিরা পর্য্ন্ত লম্বা একটা জামা পরে-এই হলো এখনকার আরবদের সাধারণ পোশাক। এর কোনোটিকেই যে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের গিরা ঢেকে ফেলা যাবেনা তাই বলা হচ্ছে এইসব হাদীসে। বস্তুত ‘নিসফে সাক’ বলতে কোনো কিছুর উল্লেখ বা থাকলে তা হলো এই।
কিন্তু একটা লুঙ্গি বা পাজামা পরা সত্ত্বেও ‘নিসফে সাক’-নলার মাঝ বরাবর পর্য্ন্ত একটি কোর্তাও ওপর থেকে ঝুলে পড়তে হবে এবং এরূপ কোর্তা পরা সুন্নাত হবে-একথা কোথ্থেকে জানা গেল? কুরআন থেকে নয়, হাদীস থেকেও নয়। আর কুরআনও হাদীস থেকে যা প্রমাণিত নয়, তা ফিকাহর কিতাব থেকেও প্রমাণিত হতে পারেনা। বর্তমান আরবদের রেওয়াজ থেকেও তা প্রমাণিত নয়। অতএব বর্তমানে এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবানদের ‘সুন্নাতি লেবাস’ বলে চালিয়ে দেয়া ‘নলার অর্ধেক পর্য্ন্ত’ লম্বা কল্লিদার কোর্তা শরীয়তের মূল দলীল থেকে প্রমাণিত জিনিস নয়। এ হলো সম্পূর্ণ মনগড়া এক জিনিস। আর শরীয়তের সুন্নাত রূপে প্রমাণিত নয়- এমন একটি পোশাককে ‘সুন্নাতি লেবাস’ বলে চালিয়ে দেয়া এক অতি বড় বিদয়াত(এ দেশের এক শ্রেণীর আলিম ও পীর সাহেবান যে পাজামা বা লুঙ্গির ওপর কল্লিদার নিসফে সাফ কোর্তা পরেন, তাকে ‘সুন্নাতী লেবাস’ বলা একটা মনগড়া কথা। এ পোশাককে বড়জোর এতদ্দেশীয় পরহেযগার আলিম ও পীর সাহেবানদের পছন্দনীয় পোশাক-লিবালুস ওলামা-বলা যেতে পারে মাত্র)। তা বিদয়াত এজন্যেও যে, তাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খরচ হয়। আর বেহুদা খরচ থেকে দূরে থাকা পোশাকের ব্যাপারে প্রথম শর্ত। বর্তমানে এই বিদয়াত চালু হয়ে রয়েছে সমাজের একশ্রেণীর জনগণের মাঝে। তারা মনে করছে ‘সুন্নাতী পোশাক পরছি আমরা; রাসূলের পায়বরী করছি আমরা, সে কথা এই লোকদের খেয়ালেই আসেনা। বস্তুত এ চরম অন্ধত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।
আমার এ দলীলভিত্তিক আলোচনায় এ পোশাকের প্রতি কোনো বিদ্বেষ প্রচার করা হয়নি, তা পরতে নিষেধও করা হয়নি। আমার বক্তব্য শুধু এতটুকু যে, শুধুমাত্র এ ধরনের পোশাককেই ‘সুন্নাতী পোশাক’ বলাটাই বিদয়াত। এ পোশাক শুধু পরাকে আমি বিদয়াত বলিনি- বিদয়াত বলতেও চাইনা।
স্বপ্নের ফয়সালা মেনে নেয়ার বিদয়াত
পীর সাহেবদের দরবারের সবচাইতে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এখানে সব সময় স্বপ্নের রাজত্ব কায়েম হয়ে থাকে। কে কত বেশি এবং ভালো স্বপ্ন দেখতে পারে, মুরীদ-মুসাহিবদের মাঝে তা নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা চলে। ফলে তাদের কেউ কেউ যে বানানো স্বপ্নও না বলে, এমন কথা জোর করে বলা যায়না। কেননা যে যত ভালো স্বপ্ন দেখবে এবং স্বপ্নযোগে হুজুর কিবলার বেলায়েত ও উচ্চ মর্যাদা প্রমাণ করতে পারবে, হুজুরের দোয়া ফায়েজ এবং স্নেহাশীষ সেই পাবে সবচাইতে বেশি। কাজেই এ দরবারে স্বপ্ন দেখতেই হবে;-স্বপ্ন না দেখে কোনো উপায় আছে? এ দরবারের লোকেরা চোখ বুঝলেই স্বপ্ন দেখতে পায়, স্বপ্ন যেন এদের জন্য এমন পাগল হয়ে বসে থাকে যে, যে কোনো সময়ই তা এদের চোখের সামনে ভেসে ওঠার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখে অনেক সময় এবং তা হুজুর কিবলাকে খুশি করার জন্য সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দরবারে পেশ করে। শুধু তা-ই নয়, শরীয়তের দৃষ্টিতে ভালো-মন্দ জায়েয নাজায়েয সম্পর্কেও এখানে স্বপ্ন দ্বারাই ফয়সালা গ্রহণ করা হয়। একজন হয়তো বললোঃ আমি অমুক হুজুরকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি এই কাজটি করতে নিষেধ করেছেন; অমনি সে কাজটি পরিত্যাগ করা হলো। কিংবা তিনি অমুক কাজ করতে বলেছেন। অতএব সঙ্গে সঙ্গে সে কাজ করতে শুরু করা হলো।
কেউ বললোঃ আমি নবী করীম(স)কে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে এ কাজটি করতে আদেশ করেছেন, আর অমনি সে কাজ করতে শুরু করে দেয়া হলো। কিংবা কোনো কাজ করতে নিষেধ করেছেন বলে তা বন্ধ করা হলো। এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা যে কি, সে দিকে আদৌ তাকিয়েও দেখা হয়না; শরীয়ত কি বলে সে কথা জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন তারা বোধ করেনা।
এভাবে স্বপ্নের ওপর নির্ভরতা, স্বপ্ন দ্বারা পরিচালিত হওয়া, স্বপ্নের ভিত্তিতে কোনো কাজ করা বা না করা পীর-পূজকদের নীতি, কোনো শরীয়তপন্থীর এ নীতি নয়। কেননা সাধারণ মানুষের স্বপ্ন-সত্যিকারভাবে যদি কেউ দেখেই –কোনো শরীয়তের বিধান হতে পারেনা। স্বপ্ন সত্য হতে পারে। কোনো স্বপ্ন যদি কেউ সত্যিই দেখে থাকে তবে তা থেকে সে নিজে কোনো আগাম সুখবর লাভ করবে, না হয় কোনো বিষয়ে সতর্কাবলম্বনের ইঙ্গিত পাবে। সে জন্যে তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। কিন্তু এ স্বপ্ন দ্বারা ফরয-ওয়াজিব, হালাল হারাম ও জায়েয নাজায়েয কিংবা করণীয় কি, না করণীয় কি, তা প্রমাণিত হতে পারেনা। স্বপ্ন থেকে শরীয়তের অনুকূল কোনো কথা জানতে পারলে সে তো ভালোই; কিন্তু শরীয়তের বিপরীতে যদি কিছু জানা যায় তবে তা কিছুতেই অনুসরণ করা যাবেনা। করা যাবেনা এজন্য যে, শরীয়তের বিপরীত কারো কোনো হুকুম দেয়ার অধিকার নেই, স্বপ্নের কি দাম থাকতে পারে শরীয়তের মুকাবিলায়?
অবশ্য স্বপ্ন ইসলামের দৃষ্টিতে একেবারে ফেলবার বিষয় নয়- এ কথা ঠিক। স্বপ্নযোগে নবী করীম(স) এর দর্শন লাভ করা যায়, তাও হাদীস থেকে প্রমাণিত। কিন্তু প্রথম কথা হলো, স্বপ্নযোগে শয়তান যদি নবী করীমের নিজের বেশ নয়- যে কোনো একটি বেশ ধারণ করে তাকেই ‘নবী করীম’ বলে জাহির করে, তবে স্বপ্ন দ্রষ্টা কি করে বুঝতে পারবে যে এ প্রকৃত রাসূল নয়?
এ পর্যায়ে রাসূলে(স) এর হাদীসের ভাষা ও তাতে ব্যবহৃত শব্দগুলো লক্ষণীয়। হযরত আবদুল্লাহ(রা) নবী করীম(স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ আরবী(*******)
-যে লোক স্বপ্নযোগে আমাকে দেখলো, সে ঠিক আমাকেই দেখলো। কেননা শয়তান আমার রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারেনা। (তিরমিযী)।
শয়তান রাসূলের রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারবেনা-বলে যদি কেউ স্বপ্নযোগে রাসূলে করীম(স)কে দেখল, তবে বিশ্বাস করতে হবে যে, সে ঠিক রাসূলকেই দেখেছে, অন্য কাউকে নয়-হাদীসের শব্দ ও ভাষা থেকে একথাই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কিন্তু এ শব্দ ও ভাষার ভিত্তিতেই দু’টো দিক এমন থেকে যায়-যার স্পষ্ট মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন। একটি হলো রাসূলে করীম(স) বলেছেনঃ যে লোক আমাকে দেখল, সে আমাকেই দেখল, কিন্তু যদি কেউ অন্য কাউকে দেখে এবং তার মনে ভ্রম হয় শয়তান ভ্রম জাগিয়ে দেয় যে, ইনি রাসূল(স) তাহলে কি হবে? এরূপ হওয়ার অবকাশ কি এ হাদীসের ভাষা থেকে বের হয়না?
দ্বিতীয় রাসূলে করীম(স) বলেছেনঃ শয়তান আমার রূপ ও প্রতিকৃতি ধারণ করতে পারেনা, কিন্তু শয়তান যদি অন্য কারো রূপ প্রতিকৃতি ধারণ করে স্বপ্ন দ্রষ্টার মনে এই ভ্রম জাগিয়ে দেয় যে, ইনি রাসূলে করীম তাহলে কি হবে?
এরূপ হওয়া সম্ভব কিনা এ হাদীসের স্পষ্ট ভাষার পরিপ্রেক্ষিতে? আমার মনে হয়, হাদীসে এই দুটো সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে দেয়নি। এখানে এ সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই কথা বলা হচ্ছে। আল মাজেরী ও কাযী ইয়াজ প্রমুখ হাদীস বিশারদ এ হাদীসের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। (তিরমিযীর শরাহ‘তুহফাতুল আল ওয়াযী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।
কাজেই স্বপ্ন দেখলেই তদনুযায়ী কাজ করতে হবে, ইসলামে এমন কথা অচল। আর দ্বিতীয় কথা হলো, নবী করীম(স) এর যা কিছু বলবার ছিল তা তো তাঁর জীবিত থাকাকালে সম্পূর্ণই বলে দিয়ে গেছেন, তাঁর জীবদ্দশয়াইতো দ্বীন পূর্ণতা লাভ করেছে। এখন নতুন করে তাঁর কিছুই বলবার থাকতে পারেনা। হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয বলে দেয়া নবীর দায়িত্ব। আর নবীর এ দায়িত্ব নবীর জীবন পর্য্ন্তই সীমাবদ্ধ। নবীর জীবন শেষ হয়ে যাওয়ার পর এ পর্যায়ের কোনো দায়িত্বই থাকতে পারেনা তাঁর ওপর। আর শেষ নবীতো তাঁর জীবদ্দশাতেই ‘খাতামুন্নাবীয়ীন’ ছিলেন। নবীর জীবন শেষ হয়ে গেছে, তার পূর্বেই নব্যুয়তের দায়িত্ব পূর্ণরূপে পালিত হয়ে গেছে। অতঃপর স্বপ্নযোগে শরীয়তের কোনো নতুন বিধান দেয়ার প্রয়োজনই নেই। তাই স্বপ্নযোগে নবী করীম(স) কে দেখলেও এবং তার নিকট হতে কোনো নির্দেশ পেলেও তা পালন করার কোনো দায়িত্ব স্বপ্নদ্রষ্টারও নেই, নেই উম্মতের কোনো লোকেরও। দ্বীন ইসলাম পরিপূর্ণ। এখন বিশ্ব মানবের জন্য তা-ই একমাত্র চূড়ান্ত বিধান। সবকিছু তা থেকেই জানতে হবে, তা থেকেই গ্রহণ করতে হবে, চলতে হবে তাকে অনুসরণ করেই।
শরীয়তে স্বপ্নের যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকেই প্রমাণিত। এ পর্যায়ে দুটো হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে। একটি হযরত আবু হুরায়রা(রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আরবী(********)
-নবী করীম(স) বলেছেন, নব্যুয়তের কোনো কিছুই বাকী নেই- সবই শেষ হয়ে গেছে। এখন আছে শুধু-‘সুসংবাদ দাতাসমূহ’। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন-সুসংবাদ দাতাসমূহ বলতে কি বোঝায়? নবী করীম (স) বললেনঃ তা হলো ভালো স্বপ্ন।
দ্বিতীয় হাদীস হলো হযরত আনাস(রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেনঃ আরবী(********)
-ভালো স্বপ্ন নব্যুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের একভাগ মাত্র।
প্রথম হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, ভালো স্বপ্ন বান্দার জন্য সুসংবাদ লাভের একটি মাধ্যম মাত্র। আর দ্বিতীয় হাদীস থেকে জানা যায় যে, নব্যুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ মর্যাদার অধিকারী হলো এই ‘শুভ স্বপ্ন’। তা হলে বাকি পঁয়তাল্লিশ ভাগ কি? তা হলো নব্যুয়তের মাধ্যমে লব্ধ কুরআন ও সুন্নাত।[এ হাদীসে শুভ স্বপ্নকে নব্যুয়তের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ বলা হয়েছে। মুসলিম শরীফে হযরত আবু হুরায়রা(রা) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছেঃ ‘শুভ স্বপ্ন’ নব্যুয়তের পঁয়তাল্লিশ ভাগের এক ভাগ, ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে সত্তর ভাগের এক ভাগ। কাজেই এসব কথা কোনো নির্দিষ্ট জিনিস নয়। দ্বিতীয়, শুভ স্বপ্নকে নব্যুয়তের অংশ বলার মানে এ নয় যে, শুভ স্বপ্নও বুঝি ঠিক নব্যুয়তের মতোই নির্ভূল বিধানকারী জিনিস। এখানে নব্যুয়তের সঙ্গে শুভ স্বপ্নের শুধু সাদৃশ্য দেখানোর জন্যই এ কথা বলা হয়েছে। অন্যথায় শুভ স্বপ্ন কখনো নব্যুয়তের সমান হতে পারেনা।(জুরকানী লিখিত মুয়াত্তার শরাহ, চতূর্থ খন্ড. ৩৫১ পৃ.)]
অতএব এই কুরআন ও সুন্নাহই হলো দ্বীনের আসল ও মূল ভিত্তি। তা-ই বাস্তব জিনিস, তার মুকাবিলায় স্বপ্নকে পেশ করা কল্পনা বিলাসী লোকদেরই কাজ। যারা বাস্তব জীবনের ব্যাপারগুলোকে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে ইচ্ছুক, তাদের কর্তব্য হলো স্বপ্নের পেছনে না ছুটে কুরআন ও সুন্নাহকে ভিত্তি ধরে অগ্রসর হওয়া। যারা কুরআন-হাদীসের বাস্তব বিধানকে ভিত্তি করে কাজ করেনা, তা থেকে গ্রহণ করেনা জীবন পথের নির্দেশ ও ফয়সালা; বরং যারা স্বপ্নের ভিত্তিতেই সব বিষয়ে ফয়সালা গ্রহণ করে, তারা আসলেই ঈমানদার নয়, ঈমানদার নয় আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতের প্রতি। অতএব তারা বিদয়াতপন্থী, বিদয়াতী লোক।
বিদয়াত প্রতিরোধ ও সুন্নাতের প্রতিষ্ঠা
সুন্নাত ও বিদয়াতের এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শই হচ্ছে এবং এরই বিপরীতকে বলা হয় বিদয়াত। সুন্নাত হচ্ছে ‘উসওয়ায়ে হাসান’-নিখুঁত, উৎকৃষ্টতম ও উন্নততর আদর্শ; যা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার প্রত্যেকটি মানুষের জন্যিই একান্তভাবে অনুসরণীয়। বস্তুত ইসলামী আদর্শবাদী যে, সে এই আদর্শকে মনে মগজে ও কাজে কর্মে পুরোপুরিভাবে গ্রহণ ও অনুসরণ করে চলে। আর সেই হচ্ছে প্রকৃত মুসলিম।
পক্ষান্তরে ইসলামের বিপরীত চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব রীতিনীতি যাই গ্রহণ করা হবে, তাই বিদয়াত। তাই সে জাহিলিয়াত, যা খতম করার জন্য দুনিয়ায় এসেছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ(স)। তিনি নিজে তাঁর নব্যুয়তের জীবন-ব্যাপি অবিশ্রান্ত সাধনার ফলে একদিকে যেমন জাহিলিয়াতের বুনিয়াদ চূর্ণ করেছিলেন এবং বিদয়াতের পথ রুদ্ধ করেছেন চিরতরে অপরদিকে তেমনি করেছেন সুন্নাতের পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সাহাবীদের সমাজকেও তিনি এ আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন পুরো মাত্রায়। তিনি নিজে এ পর্যায়ে এত অসংখ্য ও মহামূল্য হেদায়েত দিয়ে গেছেন, যার বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তিনি একান্তভাবে কামনা করেছিলেন তাঁর তৈরী সমাজ যেন কোনো অবস্থায় বিদয়াতের প্রশ্রয় না দেয়, বিচ্যূত না হয় সুন্নাতের আলোকো্জ্জ্বল আদর্শ রাজপথ থেকে। শুধু তাই নয়, তাঁর তৈরি সমাজ যেন প্রতিনিয়ত বিদয়াতের প্রতিরোধে এবং সুন্নাতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে ব্যতিব্যস্ত ও আত্মনিয়োজিত থাকে- এই ছিল তাঁর ঐকান্তিক কামনা। তাঁর এ পর্যায়ের বাণীসমূহের মধ্য থেকে কিছু কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি।
নবী করীম(স) হযরত বিলাল ইবনে হারীস(রা) কে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেনঃ আরবী(*****)
-জেনে রেখো, যে লোক আমার পরে আমার কোনো সুন্নাতকে যা মরে গেছে তা পুনরুজ্জীবিত করবে, তার জন্য নির্দিষ্ট রয়েছে সেই পরিমাণ সওয়াব ও প্রতিফল, যা পাবে সে, যে তদনুযায়ী আমল করেছে। কিন্তু যারা তদনুযায়ী আমল করবে তাদের প্রতিফল থেকে বিন্দুমাত্র সওয়াব হ্রাসপ্রাপ্ত হবেনা। পক্ষান্তরে যে লোক কোনো গোমরাহীপূর্ণ বিদয়াতের উদ্ভাবন ও প্রচলন করবে, যার প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কিছুমাত্র রাজি নন-তার গুনাহ হবে সেই পরিমাণ, যতখানি গুনাহ হবে তার, যে তদনুযায়ী আমল করবে।কিন্তু তাদের গোনাহ হতে কিছুমাত্র হ্রাস করা হবেনা।
এ পর্যায়ে তাঁর আর একটি হাদীস হলো এই। হযরত আনাস (রা) কে লক্ষ্য করে তিনি বলেছিলেনঃ আরবী(*********)
-হে প্রিয় পুত্র! তুমি যদি পারো সকাল সন্ধ্যা সর্বক্ষণই কারো প্রতি মনে কোনো ক্লেদ রাখিবেনা, তবে অবশ্যই তা করবে। হে প্রিয় পুত্র! এ হচ্ছে আমার উপস্থাপিত সুন্নাতের অন্যতম। আর যে লোক আমার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করলো, সে আমাকে ভালোবাসল, আর যে আমাকে ভালোবাসল, সে পরকালে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে।
প্রথমোক্ত হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলে করীমের উপস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত সুন্নাতও কোনো এক সময় মরে যেতে পারে, পরিত্যক্ত হতে পারে মুসলিম সমাজ কর্তৃক, তা তিনি ভালো করেই জানতেন এবং বুঝতেন। কিন্তু সে সুন্নাত চিরদিনের তরেই মৃত হয়ে থাকবে ও মিটে যাবে, কোনোদিনই তা পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবেনা- তা তিনি ভাবতেও পারেননি। এই কারণেই তিনি তাঁর তৈরি করা উম্মাতকে মরে যাওয়া সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন সাধনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন এ হাদীসসমূহের মাধ্যমে। অনুরূপ কোনো সুন্নাতও যখন মরে যেতে পারে, তখন অবশ্যই তাঁর গড়া উম্মাতের মাঝে বিদয়াতের উদ্ভাবন ও অনুপ্রবেশও ঘটতে পারে, এ কথাও তিনি বুঝতেন স্পষ্টভাবে। এ কারণেই তিনি বিদয়াত উদ্ভাবন ও প্রচলন করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সাবধান করে গেছেন তাঁর উম্মতকে।
শেষোক্ত হাদীসে প্রথমে নবী করীম(স) এর একটি বিশেষ সুন্নাতের বিশ্লেষণ দেয়া হয়েছে। সুন্নাতটি হলো মুসলিম সমাজের কোনো লোকের মনেই অপর লোকের বিরুদ্ধে কোনোরূপ হিংসা বা বিদ্বেষের স্থান না দেয়া। এ হিংসা বিদ্বেষ যে বড় মারাত্মক ঈমান ও আমলের পক্ষে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলার দৃষ্টিতে, এ হাদীসাংশ থেকে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নবী করীম(স) বলেছেন যে, এরূপ পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে কাল যাপন করাই আমার আদর্শ, আমার সুন্নাত। কোনো সময় যদি সমাজ, সমাজের ব্যক্তিগণ-এ অতি উন্নত সুন্নাত পালনের গুণ হারিয়ে ফেলে, তাহলে তা হবে সামগ্রিকভাবে জাতির লোকদের আদর্শ বিচ্যূতি। আর মুসলমানদের আদর্শ বিচ্যূতি রাসূল(স) এর নিকট কিছুতেই মনোঃপুত হতে পারেনা। তাই তিনি ছোট্ট ধরনের এ সুন্নাতকে উপলক্ষ করে সমগ্র মুসলিম উম্মাতকে এক মহামূল্য নীতি বাণী শুনিয়েছেন। তা হলো এই যে, যে আমার কোনো সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলবে, অ-চালু সুন্নাতকে চালু করবে, সে-ই রাসূলকে ভালোবাসল। অন্য কথায়, যে লোক রাসূলকে ভালোবাসে তার পক্ষেই রাসূলের সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা-পুনরুজ্জীবনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হতে পারে, অন্য কারো পক্ষে নয়। শুধু তাই নয়, রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণের অকৃত্রিমতা ও নিষ্ঠা সে-ই প্রমাণ করতে পারল। যে লোক তার সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করার কোনো চেষ্টা করলোনা, তার মনে রাসূলের প্রতি একবিন্দু পরিমাণ ভালোবাসা যে আছে, তার কোনো প্রমাণ-ই থাকতে পারেনা। তা দাবি করারও তার কোনো অধিকার নেই। অথচ রাসূলের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা পোষণ করা ঈমানের মৌল শর্ত। অতএব যারাই রাসূলের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে, তারাই ভালোবাসে রাসূলের সুন্নাতকে এবং যারাই রাসূলের সুন্নাতকে ভালোবাসে তারা যেমন তাঁর সুন্নাতকে উপক্ষা করতে পারেনা, পারেনা সে সুন্নাতের মরে যাওয়া মিটে যাওয়াকে বরদাশত করতে, পারেনা তার মিটে যাওয়ার পর নির্বাক, নিশ্চুপ এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে। রাসূলের প্রতি ঈমান ও ভালোবাসাই তাকে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য এবং বিদয়াতকে প্রতিরোধ করার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ করবে, নিশ্চিন্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে দেবেনা এক বিন্দু সময়ের তরেও। নবীর প্রতি এরূপ গভীর ভালোবাসা এবং নবীর সুন্নাতের এরূপ অকৃত্রিম মমত্ব বোধ মুমিন মাত্রেরই দিলে বর্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন এ মুমিনদের সমন্বয়ে গড়া এক জনসমষ্টির, যারা ঈমানী শক্তিতে হবে বলীয়ান, সুন্নাতের ব্যাপারে হবে ক্ষমাহীন এবং বিদয়াত প্রতিরোধে অনমনীয়। নবী করীম(স) এমনি এক সুসংবদ্ধ জনসমষ্টি গড়ে গিয়েছিলেন। যতদিন এ জনসমষ্টি দুনিয়ায় ছিল ততোদিন পর্য্ন্ত মুসলিম সমাজে কোনো বিদয়াত প্রবেশ করতে পারেনি, পারেনি কোনো সুন্নাত পরিত্যক্ত হতে। কিন্তু উত্তরকালে ইতিহাসে এমন এক অধ্যায় আসে, যখন মুসলিম সমাজে বিদয়াত প্রবেশ করে এবং সুন্নাত হয় পরিত্যক্ত। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো পর্যায়েই এমন দেখা যায়নি, যখন মুসলিম সমাজে বিদয়াতের প্রতিবাদ এবং সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টানুবর্তী লোকের অভাব ঘটেছে। অতীতে সুন্নাত ও বিদয়াতের মাঝে প্রচন্ড দ্বন্দ্ব ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করছে। কখনো বিদয়াতপন্থীরা বাহ্যত জয়ী হয়েছে, আর কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সুন্নাত প্রতিষ্ঠাকামীরা। এ জয় পরাজয়ও এক শাশ্বত সত্য। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম সমাজে বিদয়াতের প্রভাব প্রচন্ডরূপে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, বিদয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এখানে অবাধে। প্রতিবাদ হচ্ছেনা তা নয়; কিন্তু বিদয়াত যে প্রচন্ড শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আসছে, প্রতিবাদ হচ্ছে তার তুলনায় অত্যন্ত ক্ষীণ কন্ঠে, অসংবদ্ধভাবে প্রায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে। অথচ প্রয়োজন সুসংবদ্ধ এক প্রবল প্রতিরোধের। শুধু নেতিবাচক প্রতিরোধই নয়, প্রয়োজন হচ্ছে ইতিবাচকভাবে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার এক সামগ্রিক ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টার। এরূপ এক সর্বাত্মক ও পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টাই এখন মুসলিম সমাজকে রক্ষা করতে পারে বিদয়াতের এ সয়লাবের স্রোত থেকে। অন্যথায় এ সমাজ বিদয়াতের স্রোতে ভেসে যেতে পারে রসাতলে। তাই আজ ‘সুন্নাত ও বিদয়াত’ পর্যায়ে এ দীর্ঘ আলোচনা সমাজের সামনে উপস্থাপিত করা হলো। বিদয়াত প্রতিরুদ্ধ হোক, প্রতিরুদ্ধ হোক কেবল আংশিক বিদয়াত নয়, বিদয়াতের কতকগুলো ছোটোখাট অনুষ্ঠান নয়, প্রতিরুদ্ধ হোক সম্পূর্ণরূপে সর্বাত্মকভাবে, মূলোৎপাটিত হোক বিদয়াতের এ সর্বগ্রাসী বিষবৃক্ষ। আর সে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হোক সুন্নাত। কেবল পোশাকী সুন্নাত নয়, প্রকৃত সুন্নাত, সম্পূর্ণ সুন্নাত। সেই সুন্নাত, যা দুনিয়ায় রেখে গেছেন সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ(স) চিরদিনের তরে। বিশ্বমানবতার জন্য এই হচ্ছে আমার একমাত্র কামনা, অন্তরের একান্ত বাসনা। এ দাওয়াতই আমি আজ পেশ করছি সাধারণভাবে সব মুসলমানের সামনে, বিশেষ করে আলিম সমাজের সামনে এবং আরো বিশেষভাবে ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী যু্ব সমাজের সামনে।
সুন্নাত ও বিদয়াত সম্পর্কে এ দীর্ঘ আলোচনায় দলীল ও প্রমাণের ভিত্তিতে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কুরআন ও সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো কাজ বা বিষয়, ব্যাপার, নিয়ম-প্রথা ও পদ্ধতিকে ধর্মের নামে নেক আমল ও সওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়াই হলো বিদয়াত- যে সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাত থেকে কোনো সনদ পেশ করা যাবেনা, যার কোনো নজীর পাওয়া যাবেনা খোলাফায়ে রাশেদীন এর আমলে।
বস্তুত নিজস্বভাবে শরীয়ত রচনা এবং আল্লাহর কুদরত ও উলুহিয়াতে অন্যকে শরীক মনে করা, ও শরীক বলে মেনে নেয়াই হচ্ছে বিদয়াত। আর আল্লাহর শরীক বানানো বা শরীক আছে মনে করা যে কত বড় গুনাহ তা কারোই অজানা নয়। এ পর্যায়ে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখযোগ্য। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেনঃ
আরবী(*****)
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ [٤٢:٢١]
- তাদের এমন শরীক আছে নাকি, যারা তাদের জন্য দ্বীনের শরীয়ত রচনা করে এমন সব বিষয়ে যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? চূড়ান্ত ফয়সালার কথা যদি আগেই সিদ্ধান্ত করে না নেয়া হতো, তাহলে আজই তাদের ব্যাপারে চূড়ান্ত করে দেয়া হতো। আর জালিমদের জন্য কঠিন পীড়াদায়ক আযাব রয়েছে। (আশ শূরাঃ২১)।
এ আয়াতের অর্থ হলোঃ আল্লাহর শরীয়তকে যারা যথেষ্ট মনে করেনা, অন্যদের রচিত আইন ও শরীয়ত মনে করা যারা জরুরী মনে করে এবং আল্লাহর দেয়া শরীয়তের বাইরে-তার বিপরীত-মানুষের মনগড়া শরীয়ত ও আইনকে যারা আল্লাহর অনুমোদিত সওয়াবের কাজ বলে বিশ্বাস করে তারা জালিম। আর এ জালিমদের জন্যই কঠিন আযাব নির্দিষ্ট।
আল্লাহর শরীয়তের বাইরে মানুষের মনগড়া শরীয়ত ও আইন পালন করাই হলো বিদয়াত। আর এ আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী এ বিদয়াত হলো শিরক। কেননা আসলে তো আল্লাহর শরীক কেউ নেই, কিছু নেই। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বানানো শরীয়ত বা আইন পালন করতে মানুষ বাধ্য নয়। অতএব আল্লাহর শরীয়তের দলীল ছাড়া যারাই ফতোয়া দেয়, মাসআলা বানায়, রসম ও তরীকার প্রচলন করে, তারাই বিদয়াতের শিরকে নিমজ্জিত হয়।
বিদয়াত পালনে শুধু আল্লাহরই সাথে শিরক করা হয়না, রাসূলে করীম(স) এর রিসালাতেও শিরক করা হয়। কেননা আল্লাহর নাযিল করা শরীয়ত রাসূলই পেশ করে গেছেন পুরোমাত্রায়-রাসূল পাঠাবার উদ্দেশ্যও তাই। আল্লাহর দ্বীন কি, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূলেই নির্দেশ করে গেছেন।
রাসূলের দ্বারাই আদেশ-নিষেধ, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয, সওয়াব-আয়াবের সীমা নির্ধারিত হয়েছে। এরূপ অবস্থায় অপর কেউ যদি রাসূলের শরীয়তের বাইরে কোনো জিনিসকে শরীয়তের জিনিস বলে পেশ করে এবং যে তা মেনে নেয়, সে যুগপৎভাবে আল্লাহর সাথেও শিরক করে, শিরক বানায় রাসূলের সাথেও। সে তো রাসূলের দায়িত্ব ও মর্যাদা নিজের দখলে করে নিতে চায় কিংবা রাসূল ছাড়া এ মর্যাদা অন্য কাউকে দিতে চায়। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ দ্বীনে সে নতুন আচার রীতি প্রবেশ করিয়ে দিয়ে নিজেই নবীর স্থান দখল করে, যদিও মুখে তারা দাবি করেনা। আর রাসূলে করীম হযরত মুহাম্মদ(স) এর পর আর কেউ নবী হবেনা, হতে পারেনা, এ কথা তো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদারই অন্তর্ভূক্ত।
সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ বর্ণিত একটি হাদীসের কথা এখানে উল্লেখ করতে হচ্ছেঃ
-হাশরের ময়দানে রাসূলে করীম(স) তাঁর উম্মতকে পেয়ালা ভরে ভরে ‘হাওযে কাওসার’ এর পানি পান করাবেন। লোকেরা একদিক থেকে আসতে থাকবে ও পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে অপর দিকে সরে যেতে থাকবে। তখন নবী বলেনঃ আমার ও তাদের মাঝে এক প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে। তারা আমার নিকট পোঁছতে পারবেনা। আমি আল্লাহর নিকট দাবি করে বলবো-হে আল্লাহ! এরা তো আমার উম্মত, এদের আসতে বাঁধা দেয়া হলো কেন? তখন আল্লাহ তা‘আলা জবাব দেবেনঃ এই লোকেরা তোমার মৃত্যুর পর কি কি বিদয়াত উদ্ভাবন করছে তা তুমি জাননা। বলা হবেঃ এরা তো তোমার পেশ করা দ্বীনকে বদলে দিয়েছে, বিকৃত করেছে। (এজন্য বিদয়াতীরা-‘হাউযে কাওসার’ এ কখনো হাযির হতে পারবেনা)। নবী করীম(স) বলেনঃ তখন আমি তাদের লক্ষ্য করে বলবো-দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও।
বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের মর্মান্তিক পরিণতির কথা এ সহীহ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা গেল। এমতাবস্থায় বিদয়াতকে সর্বতোভাবে পরিহার করে চলা এবং সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে একে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য চেষ্টা করা যে ঈমানদার মুসলমানদের কত বড় কর্তব্য তা বলাই বাহুল্য। আর এজন্য সঠিক কর্মনীতি হচ্ছে এই যে, বিদয়াত মুক্ত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ প্রচার করে জনমত গঠন করতে হবে এবং জনমতের জোরে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে। অতঃপর এই ইসলামী রাষ্ট্র শক্তিকে পুরোপুরি প্র্রয়োগ করতে হবে জীবনে ও সমাজে অবশিষ্ট বিদয়াতের শেষ চিহ্নকেও মুছে ফেলবার কাজে। এ পন্থায় কাজ করলে বিদয়াতও মিটবে এবং সুন্নাত ও প্রতিষ্ঠিত হবে। বস্তুত এই হচ্ছে ইসলামের কর্মনীতি।
সর্বশেষ আমি ইমাম গাযযালীর একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করে এ গ্রন্থের সমাপ্তি ঘোষণা করতে চাই। তিনি বলেছেনঃ আরবী(*******)
-বিদয়াত যত রকমেরই হোক, সবগুলোরই দ্বার রুদ্ধ করতে হবে আর বিদয়াতীদের মুখের ওপর নিক্ষেপ করতে হবে তাদের বিদয়াতসমূহ-তারা তাকে যতোই বরহক বলে বিশ্বাস করুকনা কেন!
– সমাপ্ত –
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি