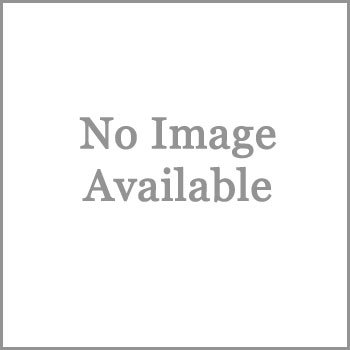আইন পালনের শিরক-এর বিদয়াত
ইসলামের তওহীদী আকীদায় আল্লাহর একত্ব ও অনন্যতা স্বীকৃত যেমন বিশ্বসৃষ্টি, লালন-পালন, রিযিকদান এবং দো‘আ ও ইবাদত পাওয়ার অধিকার প্রভৃতির ক্ষেত্রে। অনুরূপভাবে মানুষের বাস্তব জীবনের সর্বস্তরে ও সর্বক্ষেত্রে নিরংকুশভাবে আনুগত্য করে চলতে হবে এক আল্লাহকেই। মানুষের নিকট এই আনুগত্য পাওয়ার একমাত্র অধিকার হচ্ছে আল্লাহ তা‘আলার, আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই এই অধিকার নেই, যেমন সমগ্র বিশ্বলোক-বিশ্বলোকের অনু-পরমাণু পর্য্ন্ত আনুগত্য করে চলছে একমাত্র আল্লাহর। পরন্তু নিখিল জগতের সবকিছুর ওপর যেমন আইন বিধান চলে একমাত্র আল্লাহর, তেমনি মানুষের জীবনেও সর্বদিকে ও বিভাগে আইন জারি করার নিরংকুশ অধিকারও একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর সৃষ্ট এই মানুষের ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই আইন জারি করার নেই। মানুষও পারেনা আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন মেনে নিতে ও পালন করতে। করলে তা হবে সম্পূর্ণরূপে অনধিকারচর্চা, অন্যায় এবং অত্যাচার; তা হবে সুস্পষ্টরূপে শিরক।
বস্তুত মানুষের জন্য আইন বিধান তিনিই রচনা করবেন, মানুষ তার জীবনের সকল দিক ও বিভাগে কেবল তাঁরই দেয়া আইন পালন করে চলবে। তাঁর দেয়া আইন বিধানের বিপরীত কোনো কাজ কিছুতেই করবেনা। কেননা মানুষের ওপর হুকুম করার, অন্য কথায়-আইন দেয়ার ও জারি করার অধিকারতো আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই, থাকতে পারেনা। এ বিষয়ে মূল কথা হলো; আপনি কাকে এই অধিকার দিচ্ছেন যে, সে আপনার জন্যে আইন তৈয়ার করবে, আর আপনি তা পালন করবেন, করতে প্রস্তুত হবেন আর কাকে এই অধিকার আপনি দিচ্ছেননা।
যদি আপনি একমাত্র আল্লাহকে এই অধিকার দেন, তাহলে আল্লাহর তওহীদ বিশ্বাস পূর্ণ হলো, আর যদি ওপর কাউকে, কোনো ব্যক্তিকে, কোনো প্রতিষ্ঠানকে –এই অধিকার দেন বা অধিকার আছে বলে মনে করেন, তা হলে প্রকৃতপক্ষে সে-ই হলো আপনার আল্লাহ, আর আপনি তার বান্দা-দাস। কিন্তু এই শেষোক্ত অবস্থা নিঃসন্দেহে শিরক এর অবস্থা। একথাই ঘোষিত হয়েছে কুরআন মজীদে নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে।
সূরা আল-আনআমের আয়াতে রাসূলে করীমের জবানীতে বলা হয়েছেঃ
مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ [٦:٥٧]
-তোমরা যে জন্যে খুব তাড়াহুড়া করছো তা তো আমার কাছে নেই। সব ব্যাপারে ফয়সালা ও হুকুম করার অধিকার কারোই নেই-একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। তিনিই সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই সর্বোত্তম ফয়সালা দানকারী।
সূরা ইউসূফের আয়াত হলোঃ
আরবী(*********)
-হুকুমদানের-আইন বিধান রচনার চূড়ান্ত অধিকার কারোরই নেই এক আল্লাহ ছাড়া। সেই আল্লাহ-ই ফরমান দিয়েছেন যে, হে মানুষ তোমরা কারোরই দাসত্ব করবেনা, করবে কেবলমাত্র সেই আল্লাহর।
এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ নির্দেশদান, হস্তক্ষেপকরণ, ইচ্ছা করা ও মালিকানা বা নিরংকুশ কর্তৃত্ব এই সব কিছুই একমাত্র আল্লাহর জন্য। তিনি তাঁর বান্দাদের চূড়ান্তভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই ইবাদাত-বন্দেগী বা দাসত্ব করবেনা।
উপরোক্ত এ আয়াতে একদিকে বলা হয়েছে হুকুম দানের কথা, অপরদিকে দাসত্বের কথা। যার হুকুম পালন করা হয়, কার্য্ত দাসত্ব তাঁরই করা হয়। আর কারো হুকুম আইন, আদেশ নিষেধ, হালাল হারাম পালন করা, মেনে নেয়া ও অনুসরণ করাই হচ্ছে শরীয়তের পরিভাষায় ইবাদত। কাজেই এ ব্যাপারে আল্লাহকেই একমাত্র আইনদাতা বলে মেনে নেয়া তওহীদেরই আকীদা ও আমল। আর এই দিক দিয়ে অপর কাউকে এ অধিকার দিলে তা হবে সুস্পষ্ট শিরক।
নিম্নোক্ত আয়াত ও ঠিক এ কথাই ঘোষণা করেছে।
مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا [١٨:٢٦]
-লোকদের জন্য এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ‘অলী’ নেই এবং তিনি তাঁর হুকুম রচনা ও জারি করার ক্ষেত্রে কাউকেই শরীক করেননা।
এখানে ‘অলী’ শব্দটি ঠিক ‘আদেশদাতা’ ‘আইন-বিধানদাতা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো ‘অলী’ নেই-এর মানে আল্লাহ ছাড়া আদেশদাতা, আইন বিধানদাতা ও প্রভুত্ব কর্তৃত্বসম্পন্ন আর কেউ নেই, কেউ হতে পারেনা। এ কথাই এ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। আর এ কথাকে অধিক চূড়ান্ত করে বলা হয়েছে আয়াতের শেষাংশে এই বলে যে, তাঁর হুকুমের ক্ষেত্রে তিনি কাউকেই শরীক করেননা। অর্থাৎ আইন-বিধানদাতা হিসেবে আল্লাহ এক, একক ও অনন্য। তিনি আর কাউকেই নিজস্বভাবে মানুষের ওপর হুকুম দানের ও আইন জারী করার অধিকার দেননি। সেই সঙ্গে মানুষকেও অধিকার দেয়া হয়নি আর কাউকে হুকুমদাতা বলে মেনে নেয়ার এবং আর কারো দেয়া আইন পালন করার। মানুষ যদি কাউকে এরূপ অধিকার দেয়, তবে আল্লাহর সাথে শিরক করা হয়। তা হবে অনধিকার চর্চা। কেননা আল্লাহর সৃষ্টির ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই এই অধিকার তিনি নিজে দেননি; এখন আল্লাহর সৃষ্টির ওপর অপর কারো হুকুমদানের এবং হুকুমদাতা বলে মেনে নেয়ার কার অধিকার থাকতে পারে? আল্লাহ তো শিরক এর গুনাহ কখনো মাফ করেননা। অন্যান্য গুনাহ্র কথা স্বতন্ত্র।
ইরশাদ হয়েছেঃ
إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ
-আল্লাহর সাথে শিরক হলে তিনি তা মাফ করেননা। এছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করে দেন। (আন-নিসাঃ116)
বস্তুত ইসলামের তওহীদী আকীদায় এ-ই হচ্ছে সুন্নাত। কুরআন মজীদের ত্রিশ পারা কালাম এই আকীদারই বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। নবী করীম(স) এই আকীদাই প্রচার করেছেন, এই আকীদার ভিত্তিতেই তিনি চালিয়েছেন তাঁর সমগ্র দাওয়াতী ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। তখনকার সময়ের লোকেরা এই কথাই বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর প্রচারিত আকীদা থেকে এবং আকীদা গ্রহণ করেই তাঁরা মুসলমান হয়েছিলেন। এক কথায় এই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা এবং এরই ভিত্তিতে নবী করীম(স) গড়ে তুলেছিলেন পূর্ণাঙ্গ সমাজ ও রাষ্ট্র।
এক আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ
আরবী(********)
-হুকুম আইন-বিধান রচনা ও জারী করার অধিকার কেবলমাত্র মহান আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট।
আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীকে লক্ষ্য করে হুকুম দিয়েছেন-
إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا [٧٦:٢٣]
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا [٧٦:٢٤]
-নিশ্চয়ই আমরা কুরআন নাযিল করেছি। অতএব আল্লাহর হুকুম পালনের মধ্যেই সবর করে থাকো, তা বাদ দিয়ে কোনো গুনাহগার কিংবা কাফির ব্যক্তির আনুগত্য করোনা, তার দেয়া হুকুম মেনো না।
কুরআন নাযিল করার কথা বলার পরই আল্লাহর হুকুম পালনে সবর করতে বলার তাৎপর্য্ এই যে, কুরআনই হলো আল্লাহর হুকুমপূর্ণ কিতাব। এ কিতাব মেনে চললেই আল্লাহর হুকুম মান্য করা হবে। আর তা পালনে সবর করার অর্থ আল্লাহর হুকুম পালন করেই ক্ষান্ত থাকা, তাছাড়া আর কারো হুকুম পালন না করা।
নবী করীম(স) নিজের ভাষায় বলেছেন-
আরবী(*******)
-সৃষ্টির আনুগত্য করতে গিয়ে আল্লাহর নাফরমানী করার অধিকার নেই কারো।
তার মানে, আনুগত্য মৌলিকভাবে কেবল আল্লাহরই প্রাপ্য মানুষের কাছে। মানুষ কেবল তাঁরই আনুগত্য করতে আদিষ্ট। কিন্তু যদি কোনো ক্ষেত্রে অন্য কারো আনুগত্য করতে হয়, অন্য কারো আইন বিধান পালন করার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে কি করা যাবে? রাসূলের এই কথাটুকুতে তারই জবাব রয়েছে। এখন এর তাৎপর্য্ হলো এই যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারে কেবলমাত্র একটি শর্তে আর সেই শর্ত হলো এই যে, অন্য কারো আনুগত্য করা হলে তাতে যেন আনুগত হওয়ার আসল ও মৌল অধিকার আল্লাহর নাফরমানী হয়ে না যায়। যদি তা হয় তাহলে কিছুতেই অন্য কারো আনুগত্য করা যেতে পারেনা।
ইলমে ফিকাহ্ও এই কথাই আমাদের সামনে পেশ করে নানা কথায়, নানা ভাষায়। উসুলুল ফিকহর কিতাব ‘নুরুল আনোয়ার’ এ লিখিত হয়েছেঃ
তওজীহ কিতাবের বিশ্লেষণ থেকে যা জানা যায়, তা হলো এই যে, প্রত্যেকটি হুকুমের জন্য (১) হুকুমদাতা, (২)যার প্রতি হুকুম দেয়া হয় এবং (৩) যে বিষয়ে হুকুম দেয়া হলো এই তিনটি জিনিস জরুরী। অতএব হুকুমদাতা হচ্ছে এক আল্লাহ, হুকুম দেয়া হয়েছে শরীয়ত পালনে বাধ্য মানুষকে এবং হুকুম দেয়া হয়েছে শরীয়ত পালনের।
‘তাওজীহ’ কিতাবে আরো স্পষ্ট করে কথাটি বলা হয়েছে এভাবেঃ
কিতাবের দ্বিতীয় পর্যায়ে আলোচনা হবে হুকুম সম্পর্কে। হুকুম এর জন্য হুকুমদাতা আবশ্যক, আর হুকুমদাতা হচ্ছে আল্লাহতা‘আলা, মানুষের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক নয়।
বলা হয়েছেঃ হুকুম কেবল আল্লাহর ই হতে পারে। এ ব্যাপারে সব ইমামই সম্পূর্ণ একমত।
কুরআন, হাদীস ও ইজমা-ইসলামী শরীয়তের এই তিনটি বুনিয়াদী দলীল থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয়। তা হচ্ছে এই যে, হুকুম দেয়ার অধিকার আল্লাহ ছাড়া আর কারোই নেই। আল্লাহর তওহীদে বিশ্বাসী লো্ক এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেই হুকুমদাতা, বিধান-দাতা ও জায়েয-নাজায়েয নির্ধারণকারী হিসেবে মানতে পারেনা। মানলে তা হবে শিরক। রাসূলে করীমের পরে খোলাফায়ে রাশেদীন এর আমলেও মুসলমানদের এই ছিল আকীদা এবং এই ছিল তাঁদের আমল।
হযরত উমর ফারূক(রা) হযরত আবু মূসা আশ‘আরীর নিকট ইসলামী শাসন কার্য্ পরিচালনা সম্পর্কিত পলিসি নির্ধারণকারী এক চিঠিতে লিখেছিলেনঃ
শরীয়ত ভিত্তিক বিচার ব্যবস্থা কায়েম করা এক অকাট্য দ্বীনি ফরয এবং অনুসরণযোগ্য এক সুন্নাত।
কিন্তু উত্তরকালে মুসলিম সমাজে তওহীদের এই মৌলিক ভাবধারা-যাকে আমাদের ভাষায় বলতে পারি তওহীদ আকীকার রাজনৈতিক তাৎপর্য্-স্তিমিত হয়ে আসে। শেষ পর্য্ন্ত এমন একদিনও আসে, যখন মুসলমানরা দ্বীন ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন জিনিস বলে মনে করতে শুরু করে এবং এই মনোভাবের ফলে ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের কর্তৃত্ব মেনে নেয়। কেবল আল্লাহর হুকুমই নয়, সেই সঙ্গে ধর্ম নেতা তথা পীর সাহেবের হুকুম পালন করাও দরকারী বলে মনে করে। জীবনের বৃহত্তম দিক-রাজনীতি, সমাজনীতি ও অর্থনৈতিক কাজকর্মকে ইসলামের আওতার বাইরে বলে মনে করে। সেখানে মেনে নেয়া হয় রাজনীতিকও শাসকদের বিধান। নামাযের ইমামতি ধার্মিক লোকই করবে বলে গুরুত্ব দেয়া হয়, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ফাসিক-ফাজির তথা ইসলামের দুশমনদের নেতৃত্ব স্বীকার করে নিতেও এতটুকু দ্বিধাবোধ করা হয়না-একে ইসলামের বিপরীত কাজ বলে মনে করা হয়না। শুধু তাই নয়, ব্যক্তি জীবনে যারা ধর্মকে খুব গুরুত্ব সহকারে পালন করে –পালন করা দরকার বলে মনে করে, তারাই যখন রাজনীতি করতে নামে, তখন সেখানে করে চরম গায়র ইসলামী রাজনীতি, চরম শরীয়ত বিরোধী সামাজিকতা এবং সুস্পষ্ট হারাম উপায়ে ব্যবসা বাণিজ্য ও লেনদেন। কেননা এসব ক্ষেত্রে তারা আল্লাহকে হুকুম দেয়ার অধিকার দিতে রাজি হয়না, আল্লাহর হুকুম মেনে চলতে হবে এক্ষেত্রে তা মনে করতে পারেনা। ধর্ম ও রাজনীতি কিংবা ধর্ম ও অর্থনীতি ইত্যাদিকে বিচ্ছিন্ন পরস্পর সম্পর্কহীন মনে করাই হলো আধুনিক সেকিউলারিজম এর মূল কথা এবং ইসলামের তওহীদী আকীদার সামাজিক-রাজনৈতিক দিকে এই হলো এক মারাত্মক বিদয়াত। এই পর্যায়ে এসে সমাজের ধার্মিক লোকেরা আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পীর ধরা ফরয বলে প্রচার করে। আর অপর শ্রেণীর লোকেরা রাজতন্ত্র, বাদশাহী ও ডিকটেটরী শাসন ব্যবস্থা পর্য্ন্ত ইসলাম সম্মত মনে করতে শুরু করে। ফাসিক-ফাজির নেতা, রাজা-বাদশাহ ও ডিকটেটরকে বাস্তব জীবনে আইন শাসনের ক্ষেত্রে ঠিক আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দেয়। তারা এজন্যে রাসূলের হাদীস ‘সুলতানরা আল্লাহর ছায়া সদৃশ’ প্রচার করে। রাজা-বাদশাহ ও ফাসিক ফাজির নেতৃবৃন্দকে মানব সমাজের ওপর আল্লাহর সমান মাননীয় করে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মুসলমানদের বাস্তব আনুগত্যের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিক দিয়ে আলিম ও পীরকে এবং জাগতিক ব্যাপারে রাজা-বাদশাহ, রাজনৈতিক নেতা ও ডিকটেটরকে আল্লাহর সমতুল্য করে ফেলেছে। আল্লাহ যেমন জনগণের ওপর নিজস্ব আইন বিধান জারী করেন, তেমনি ধর্মনেতা বা পীর-বুযুর্গ এবং রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদেরও নিজেদের মর্জিমত আইন বিধান জারী করার অধিকার আছে বলে মনে করেছে। ইসলামী ধর্ম ব্যবস্থায় এবং বৈষয়িক রাজনীতির ক্ষেত্রে এমনিভাবে এক মহা বিদয়াতের অনুপ্রবেশ সম্ভব হয়েছে। আর তারই ফলে আল্লাহর তওহীদী ধর্মে ধর্মনেতার তথা পীর-বুজুর্গ লোকদের এবং রাজনীতি ও সমাজ সংস্থায় রাজনীতিবিদদের নিরংকুশ কর্তৃত্ব স্বীকার করে শিরক এর এক অতি বড় বিদয়াত দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। পরবর্তীকালে ক্রমশ এমন একদিন এসে পড়ে, যখন রাজা-বাদশাহ ও রাষ্ট্রকর্তাদের রচিত আইন বিধান পালন করাকে আল্লাহর আইন পালনের মতোই কর্তব্য এবং পীরের হুকুম মানা আল্লাহর হুকুম পালনের সমান কর্তব্য বলে মনে করতে থাকে। আর তাদের নাফরমানীকে আল্লাহর নাফরমানীর মতোই গুনাহের কাজ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে।(ঠিক এ কারণে এক সঙ্গে দু’জন ইমাম-রাষ্ট্রপ্রধান মেনে নেয়াও জায়েয নয়। একজন ধর্মীয় ইমাম-পীর ও একজন রাষ্ট্রীয় ইমাম-বাদশাহ বা ডিকটেটর মেনে নেয়া শরীয়তবিরোধী।)
অথচ শরীয়তের নির্দেশ মুতাবিক তাদের কর্তব্য ছিল এক ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম করা এবং সেজন্য ইসলামী আদর্শবাদী ইমাম তথা রাষ্ট্রচালক নিয়োগ করা। কুরআনের আয়াত ‘আমি পৃথিবীতে খলীফা বানাব’-এর ভিত্তিতে ইমাম কুরতবী লিখেছেনঃ
ইমাম ও খলীফা নিয়োগ কর্তব্য – যার কথা শোনা হবে ও আনুগত্য করা হবে, যেন জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় ও খলীফার আইন আদেশ পুরোপুরি জারী হয়-এ পর্যায়ে উপরোক্ত আয়াতই মূল দলীল। ইমাম ও মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই। অতএব এ কাজ যে ওয়াজিব তা প্রমাণিত হলো। প্রমাণিত হলো যে, এরূপ একজন ইমাম বা খলীফা নিয়োগ করা সেই দ্বীন ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ, যে দ্বীন হলো মুসলমানদের সামাজিক ও সামগ্রিক জীবনের ভিত্তি।
আল্লাহর হুকুম ও আইন ছাড়া অন্য কারো আইন পালন করা যে শিরক, পূর্বের আলোচনায় শরীয়তের অকাট্য দলীলের ভিত্তিতে তা প্রমাণিত হয়েছে।
কিন্তু আলিম নামধারী এমন কিছু লোক রয়েছে, যারা জাহিল পীরদের ফেরেবে পড়ে কেবল আল্লাহকেই একমাত্র আইন বিধানদাতা বলে মানতে রাজি নয়। কেননা হুকুম আইনদাতা রূপে কেবল আল্লাহকেই যদি মানতে হয়, তাহলে ‘হুযুর কিবলা’র স্থান হবে কোথায়? অতএব আল্লাহর সঙ্গে ‘হুযুর কিবলাকে’ও হুকুম দেয়ার অধিকারী মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই। এ জন্যে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা শিরক-‘ইসলামের তওহীদী’ আকীদাসম্মত এই কথার জবাবে নেহায়েত মূর্খের মতই বলতে শুরু করেঃ
“পাঠকগণ! একটু চিন্তা করুন-স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে, রাজনৈতিক, সামাজিক, বিভিন্ন সমিতি, কমিটি ও সংস্থায়, নৌকা, স্টীমার, বাস, ট্রেন ইত্যাদি পরিচালনায় ও যাতায়াত প্রভৃতি অসংখ্য পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে কি মানুষের গড়া কোনো আইন মেনে চলতে হয়না? জ্বি হ্যা, তাতো নিশ্চয়ই হয়; তাতে আর সন্দেহ কি? তাহলে কি আল্লাহকে একমাত্র হুকুমদাতা বলে মানতে হবে? আমাদের পূর্বোক্ত দীর্ঘ আলোচনার আলোকে চিন্তা করলে আলিম নামধারী ব্যক্তির উপরোক্ত কথা যে কতখানি হাস্যকর তা যে কোনো লোকই বুঝতে পারেন। একেতো তিনি নিজেই বলছেনঃ ‘পার্থিব ও বৈষয়িক ব্যাপারে মানুষের গড়া আইন পালন করতে হয়।’ নিতান্ত বৈষয়িক ব্যাপারেও আল্লাহ ও রাসূলের কোনো বিধান বা আদর্শ নেই, সেসব ক্ষেত্রে আর কারো হুকুম মানা যাবেনা- একথা আপনাকে কে বলেছে? এখানে মূল কথা হচ্ছে মানুষের জীবনকে বৈষয়িক ও ধর্মীয়-এ দু’ভাগে ভাগ করাই আপনার মারাত্মক ভুল। ইসলামে এ বিভাগকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছে। অতএব কেবল জাগতিক ব্যাপারেই নয়, নিছক ধর্মীয় ব্যাপার বলে আপনি যাকে মনে করছেন, তাতেও আল্লাহ ছাড়া অন্যের হুকুম পালন করা যেতে পারে; কিন্তু বিনাশর্তে নয়, একটি বিশেষ শর্তের ভিত্তিতে। তাহলো প্রথমতো সে হুকুম আল্লাহর হুকুম মুতাবিক হবে। আর দ্বিতীয়ত আল্লাহর হুকুমের বিপরীত কিছু হবেনা-এ শর্তের ভিত্তিতে যে কোন ক্ষেত্রে যে কারোরই হুকুম পালন করা যেতে পারে। কেননা তা মূলত আল্লাহরই হুকুম। কিন্তু জনাব, হুযুর কিবলার হুকুমকে যে আল্লাহর হুকুমের মতোই বিনাশর্তে নির্বিচারে মানবেন, তা চলবেনা, তাহলে সুস্পষ্ট শিরক হবে এবং আপনি সেই শিরকের অতল সমুদ্রে হাবুডুবু খেতে থাকবেন।
রাজনীতি না করার বিদয়াত
রাজনীতিকে পরিত্যাগ করে, তার সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক না রেখে চলা আর এক প্রকারের বড় বিদয়াত, যা বর্তমান মুসলিম সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোকদের গ্রাস করে আছে। এ লোকদের দৃষ্টিতে রাজনীতি সম্পূর্ণ ও মূলগতভাবেই দুনিয়াদারীর ব্যাপার। দুনিয়াদার লোকেরাই রাজনীতি করে। আর যারাই রাজনীতি করে তাদের দুনিয়াদার হওয়ার একমাত্র প্রমাণই এই যে, তারা রাজনীতি করে। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়, তারা বলে বেড়ায়ঃ ‘আমি রাজনীতি করিনা’ কিংবা ‘রাজনীতি অনেকদিন করেছি, এখন আর করিনা’ আবার কেউ কেউ বলেঃ ‘আমরা ধার্মিক লোক, রাজনীতির সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক্ নেই।’
এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি যে বিদয়াত, তার কারণ এই যে, তা স্বয়ং রাসূলে করীম(স) এর আদর্শ, কর্মনীতি ও আকীদার সম্পূ্র্ণ বিপরীত। রাসূলে করীম(স) এর নব্যুয়তের জিন্দেগীটি অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, তিনি রাজনীতি করেছেন, রাষ্ট্রের সাথে তাঁর কাজের সংঘর্ষ হয়েছে এবং শেষ পর্য্ন্ত তিনি সকল বাতিল রাষ্ট্র ও গায়র ইসলামী রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে পুরোপুরি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করেছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন ইসলামী আদর্শের রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। রাসূলের জীবদ্দশায় ও তাঁর পরে এ রাজনীতি সাহাবায়ে কিরাম করেছেন, রাষ্ট্র চালিয়েছেন এবং রাষ্ট্র সংক্রান্ত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনরাও রাজনীতি করেছেন।
রাজনীতির কথা কুরআন মজীদে রয়েছে, রয়েছে হাদীসে, আছে এ দুয়ের ভিত্তিতে তৈরী ফিকাহ শাস্ত্রের মাসলা-মাসায়েলে। কাজেই রাজনীতি করা সুন্নাত। ইসলামী আদর্শের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।
রাজনীতি সুন্নাত, ইসলামী আদর্শ মোতাবিক-শুধু তাই নয়, তা হচ্ছে ইসলামের মূল কথা। দুনিয়ায় নবী প্রেরণের মূলেও রয়েছে জমিনের বুকে আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করা। নবীগণ দুনিয়ায় এ কাজ করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে, জীবন ও প্রাণ দিয়ে আর আধুনিক ভাষায় এ-ই হচ্ছে রাজনীতি।
আল্লাহর নিকট মানুষের জন্য মনোনীত জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম, অন্য কিছু নয়। এই হচ্ছে আল্লাহর ঘোষণাঃ
ইন্নাল্লাজিনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম।
এর অর্থও তাই। আর এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করে মানব সমাজে আল্লাহর বিধান মোতাবিক ইনসাফ কায়েম করার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাঠিয়েছেন আম্বিয়ায়ে কিরামকে।
আল্লাহ্ নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۖ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
-নিশ্চয়ই আমরা নবী রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে। তাদের সঙ্গে নাযিল করেছি কিতাব ও ইনসাফের মানদন্ড যেন লোকেরা হক ও ইনসাফ সহকারে বসবাস করতে পারে। আর দিয়েছি ‘লৌহ’। এর মধ্যে রয়েছে বিপুল ও প্রচন্ড শক্তি এবং জনগণের জন্য অপূর্ব কল্যাণ।
এ আয়াত থেকে যে মূল কথাটি জানা যাচ্ছে তা হলো, দুনিয়ার মানুষ সুষ্ঠু ও নির্ভূল ইনসাফের ভিত্তিতে জীবন যাপন করা সুযোগ লাভ করুক-এ উদ্দেশ্যে আল্লাহতা‘আলা নবী রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন। নবী-রাসূলগণ যাতে করে দুনিয়ায় সঠিক ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করতে সক্ষম হন, তার জন্যে রাসূলগণকে আল্লাহর নিকট হতে প্রধানত দুটি জিনিস দেয়া হয়েছে বৈশিষ্ট্য ও আল্লাহর সরাসরি প্রেরণের নিদর্শন হিসেবে। তার একটি হলো-মোজেযা-অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ, যা লোকদের সামনে নবী-রাসূলগণের নব্যুয়ত ও রিসালাতকে সত্য বলে প্রমাণ করে দেয়। আর দ্বিতীয় হচ্ছে আল্লাহর কালাম-আসমানী কিতাব, যা নাযিল করা হয়েছে মানুষের জীবন যাপনের বাস্তব বিধান হিসেবে।
এছাড়া আরো দু’টি জিনিস দেয়া হয়েছে। একটি হলো ‘মীযান’ মানে মানদন্ড, মাপকাঠি; যার সাহায্যে ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ ও সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করা যায়। আল্লামা ইবনে কাসীর এ আয়াতের তাফসীরে ‘মীযান’ শব্দের ব্যাখ্যা হিসেবে লিখেছেনঃ ‘মীযান’ মানে মুজাহিদ এবং কাতাদার মতে ‘সুবিচার ও নিরপেক্ষ ইনসাফ’। আর তা হচ্ছে এমন এক সত্য যা সুস্থ, অনাবিল ও দৃঢ় জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক হতে প্রমাণিত। আর দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে আল হাদীদ। ‘হাদীদ’ মানে চলতি কথায় ‘লৌহ’। আর এর শাব্দিক অর্থ ইমাম রাগেবের ভাষায় ধারালো, তীক্ষ্ম, শক্তভাবে প্রভাব বিস্তারকারী জিনিস। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এসব বিভিন্ন অর্থেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।
অতএব এর অর্থ আমরা বুঝতে পারি, প্রথমত লৌহ ধাত, দ্বিতীয়ত এক শক্ত শাণিত ও অমোঘ প্রভাব বিস্তারকারী ও ক্ষমতা প্রয়োগকারী জিনিস। আর নবী রাসূলের প্রসঙ্গে এর অর্থ অনায়াসেই বুঝতে পারিঃ ‘জবরদস্ত শক্তি’। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Coercive Power বা অন্য কথায় ‘রাষ্ট্রশক্তি’।
নবী-রাসূলগণ আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে তীব্র তীক্ষ্ম শক্তিসম্পন্ন ও অমোঘ কার্য্কর রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করতেন, তারই সাহায্যে লৌহ নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে সমস্ত অন্যায় ও জুলুমের পথ বন্ধ করতেন, আর নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের ওপর নিরপেক্ষ ইনসাফ কায়েম করতেন। কাজেই নবী-রাসূলগণকে যে ইনসাফ কায়েমের উদ্দেশ্যে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিল, খতমে নব্যুয়তের পর সে ইনসাফ কায়েম করা এবং তারই জন্য তীব্র শক্তি প্রভাবশালী রাষ্ট্রশক্তি প্রতিষ্টিত করা নবীর উম্মতের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আর এ শক্তি অর্জন করতে চেষ্টা করা, এ শক্তি অর্জন করে তার সাহায্যে ইনসাফ কায়েম করাকেই আধুনিক ভাষায় বলা হয় রাজনীতি। এ কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে রাসূলে করীম(স) এ বাণীতেঃ
নিশ্চয়ই আল্লাহতা‘আলা রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে এমন অনেক কাজই সম্পন্ন করেন, যা কুরআন দ্বারা তিনি করাননা।(কোনো কোনো মনীষীর মতে এ কথাটি হযরত উসমান(রা) এর, হযরত মুহাম্মদ(স) এর নয়। সেটা হতেও পারে, তিনি কথাটি রাসূলের নিকটই শুনেছিলেন হয়তো। আর তা না হলেও সাহাবীদের কথারও গুরুত্ব অনস্বীকার্য্। তাও হাদীস হিসেবে গণ্য। সাহাবীগণ রাসূলে করীম(স) এর নিকট হতেই দ্বীন সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান লাভ করেছিলেন।)
তার মানে আল্লাহর চরম লক্ষ্য হাসিলের জন্য কুরআনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শক্তি অপরিহার্য্। কুরআনকে কার্য্কর করার উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ না করলে কুরআন আপন শক্তির বলে মানব সমাজে কার্য্কর হতে পারবেনা।
এছাড়া কুরআন মজীদে নির্দেশ রয়েছেঃ
شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۖ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ [٤٢:١٣]
-আল্লাহতা‘আলা তোমাদের দ্বীনের জন্য সে পন্থাই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন যার হুকুম তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, আর অহীর সাহায্যে – হে মোহাম্মদ-এখন তোমার দিকে পাঠিয়েছি, আর যার হেদায়াত আমরা ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে দিয়েছি এই তাগিদ করে যে, কায়েম করো এই দ্বীনকে এবং এ ব্যাপারে তোমরা বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্নপন্থী হয়ে যেওনা। হে নবী, তুমি যে জিনিসের দাওয়াত দিচ্ছ তা মুশরিকদের নিকট বড়ই দুঃসহ ও অসহ্য হয়ে উঠেছে। আল্লাহ যাকে চান যাচাই করে আপনার বানিয়ে নেন এবং তাঁর নিজের দিকে যাওয়ার ও পৌছার পথ তাকেই দেখান, যে তাঁর দিকে রুজু হবে। (আশ শুরাঃ13)।
এ আয়াত স্পষ্ট বলছে যে, হযরত নূহ(আ) হতে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ(স) কেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর দেয়া এ দ্বীনকে পুরোপুরি কায়েম করো। হযরত মুহাম্মদ(স) সব বাতিল আদর্শে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা চূর্ণ করে এ দ্বীনকে কায়েম করার এবং দ্বীনের ভিত্তিতে সমাজ, জীবন ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে গড়ে তোলারই দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখনকার সময়ের লোকদের মধ্যে। আর এ জিনিসই ছিল মুশরিকদের জন্য বড় দুৎসহ। দ্বীন কায়েমের দাওয়াত ও চেষ্টা মুশরিকদের পক্ষে সহ্য করা এ জন্য দুঃসহ ছিল যে, তার ফলে মানুষের জীবন থেকে শিরকের নাম নিশানা পর্য্নত মুছে যাবে। আর শিরকই যদি না থাকলো, তাহলে তো মুশরিকদের অস্তিত্বই নিঃশেষ হয়ে গেল। তার আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এখানে দ্বীনকে কায়েম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, দেয়া হয়েছে রাসূলে করীমের নবুয়্যতী জিন্দেগীর প্রথম দিকেই। দ্বীনকে শুধু প্রচার করার নির্দেশ কোরআন মজীদে কোথাও নেই। আর দ্বীন কায়েমের মানে হলো মানুষের মন, জীবন, আকীদা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক পলিসি ও ব্যবস্থাকে দ্বীনের ভিত্তিতে গড়ে তোলা এবং আল্লাহর দেয়া আইন বিধানকে বাস্তবভাবে জারী ও কার্য্কর করা, তারই ভিত্তিতে শাসন, বিচার, শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে পূর্ণমাত্রায় রূপায়িত করা।
(কুরআন মজীদে আল্লাহ নির্ধারিত ফৌজদারী আইনকে বলা হয়েছে ‘আল্লাহর দ্বীন’। সূরা আন-নূর এ যিনাকারী পুরুষ ও নারীকে শরীয়তী দন্ড হিসেবে কোড়া মারার নির্দেশ দেয়ার পর বলা হয়েছেঃ আল্লাহর দ্বীন জারী ও কার্য্কর করার ব্যাপারে সে দুজনের প্রতি দয়া ও মায়া যেন তোমাদেরকে পেয়ে না বসে, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাকো। এ আয়াতে কোড়া মারা ফৌজদারী আইনকে ‘আল্লাহর দ্বীন’ বলা হয়েছে।)
অতএব দ্বীন কায়েম করা, কায়েম করার চেষ্টা করা হযরত মুহাম্মদ(স) এর প্রতি ঈমানদার মুসলমানের মাত্রেরই দ্বীনি ফরয, যেমন ফরয নামায কায়েম করা, যাকাত দেয়া ইত্যাদি। হাদীসেও দ্বীন কায়েম করার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়।
একটি হাদীসে নবী করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ কেউ যদি তার যিনার অপরাধ আমাদের সামনে প্রকাশ করে দেয় তাহলে আমরা তার ওপর আল্লাহর কিতাব কায়েম করে দেবো।
‘আল্লাহর কিতাব কায়েম করে দেব’ কথার অর্থ আল্লাহর কিতাবে লিখিত যিনার শাস্তি তার ওপর কার্য্কর করে দেবো, তাকে সেই শাস্তি দেবো, যা আল্লাহর কিতাবে লিখিত রয়েছে। এখানে আল্লাহর কিতাব কায়েম করার মানে হলো আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী আইন জারী করা। অনুরূপভাবে দ্বীন কায়েম করার মানে হলো দ্বীন অনুযায়ী পূর্ণ জীবন পূণর্গঠিত করা। রাসূলে করীম(স) এ নির্দেশ পেয়েছিলেন তাঁর নব্যুয়তের প্রাথমিক পর্যায়েই। পূর্বোক্ত আয়াতটি হলো সূরা আশ শুরার। আর তা মক্কা শরীফেই অবতীর্ণ হয়েছিলো। উক্ত সূরায় পূর্বোদ্ধুত আয়াতের একটু পূর্বেই রয়েছে এ আয়াতটিঃ
وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ [٤٢:٧]
-এমনিভাবে হে মুহাম্মদ! তোমার প্রতি আরবী ভাষার কিতাব এ কুরআনকে ওহী করে পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি এ কিতাবের মাধ্যমে মক্কাবাসী ও তার আশেপাশের লোকদের ভয় দেখাবে, ভয় দেখাবে একত্রিত হওয়ার সেই দিনটি সম্পর্কে, যে দিনের উপস্থিতির ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই।
এ আয়াতে নবী করীম(স) কে ভয় দেখাবার কাজ করতে বলা হয়েছে আর তারই ভিত্তিতে পরবর্তীতে দেয়া হয়েছে দ্বীন কায়েমের নির্দেশ। তার মানে দ্বীন কায়েম করা বা সেজন্য চেষ্টা করা পরকালের প্রতি ঈমানের অপরিহার্য্ দাবি। তা করা না হলে সে দিন আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। আর এ-ই ছিল নবী করীম(স) এর নব্যুয়তের প্রাথমিক পর্যায়ের দাওয়াত ও সাধনা। এ ছিলে সে জিহাদ, যার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল নবী করীম(স) কে মক্কার জীবনেই এ আয়াতেঃ
فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا [٢٥:٥٢]
- হে নবী কাফির লোকদের আনুগত্য স্বীকার করবেনা কখনো এবং কিছুতেই। বরং কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী কাফিরদের সাথে পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে ও সর্বাত্মকভাবে জিহাদ করবে।
কাফিরদের আনুগত্য স্বীকার না করার-তা অস্বীকার ও অমান্য করার এবং এ বাতিলপন্থীদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করে তাদের ক্ষমতাচ্যূত করার সাধনাই ছিল প্রথম দিন থেকে বিশ্বনবীর সাধনা।(এ পর্যায়ে আল্লামা ইবনূল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ যেদিন প্রথম তাঁকে নবী রূপে নিয়োগ করলেন, সেদিনই আল্লাহ তাঁকে জিহাদ করার নির্দেশ দিলেন।
আর কোরআনের পূর্বোক্ত আয়াত সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ এ সূরাটি মক্কায়ই অবতীর্ণ। এতে আল্লাহতা‘আলা রাসূলকে কাফির (এবং মুনাফিকদের) সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন।)
আর আজকের ভাষায় এই হচ্ছে দ্বীন কায়েমের রাজনীতি। নবীর এ সাধনারই বাস্তব ফল পাওয়া গেছে হিজরতের পরে মদীনা কেন্দ্রিক ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থারূপে।
এ দৃষ্টিতে তাঁদের কথা ভুল প্রমাণিত হয় যারা বলে বেড়ান যে, ‘নবী করীম(স) দ্বীন কায়েম করার-ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার- কোনো দাওয়াত দেননি বা সেজন্য কোনো চেষ্টা করেননি।’ মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রতো ছিল আল্লাহর দান মাত্র। অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার দাওয়াত সব নবীরই মৌলিক দাওয়াত ছিলো, সর্বশেষ নবীর সাধনাও ছিল তারই জন্য।
একথা আজকের দিনে কেবল কোরআন হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণেই জানা যাচ্ছে তা নয়; খোদ সাহাবীগণ একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন যে, রাসূলে করীম(স) কে দ্বীন কায়েমের এ মহান উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) ছিলেন এ কাজের জন্যেই তাঁর সঙ্গী ও সাথী। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কথা পূর্বেই উদ্বৃত হয়েছে।
তিনি সাহাবীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ আল্লাহতা‘আলা তাঁদের বাছাই করে মনোনীত করে মনোনীত করে নিয়েছেন তাঁর নবীর সঙ্গী সাথী হওয়ার জন্য এবং তাঁর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে।
এখানে দুটো কথা বলা হয়েছে। প্রথম কথাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কিরামের ফযীলত ও মর্যাদা-শ্রেষ্টত্বের একমাত্র ভিত্তি হলো রাসূলে করীমের সোহবত লাভ করা, তাঁর সঙ্গী ও সাথী হওয়া। তাঁরা কি কাজে রাসূল(স) এর সঙ্গী ও সাথী ছিলেন? সকলেই জানেন, রাসূলে করীমের(স) রিসালাতের মূল দায়িত্ব পালনের ব্যাপারেই তাঁরা ছিলেন রাসূলের সঙ্গী ও সাথী। আর এ এত বড় মর্যাদা ও শ্রেষ্টত্বের ব্যাপার যে-ঈমান, আমল ও তাকওয়া-তাহরাতের উচ্চতম মর্যাদাও এর সমতুল্য হতে পারেনা।
আর দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যেই রাসূলের সাহাবীদেরকে মনোনীত করেছেন। সাহাবীদের ব্যাপারে এ হলো আল্লাহর দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। আর এ উদ্দেশ্য প্রথম উদ্দেশ্যেরই পরিপূরক। বরং বলা যায়, তাঁদের নবীর সঙ্গী ও সাথী বানিয়ে দেবার মূল লক্ষ্যই ছিলো আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা। একথা থেকে স্বয়ং নবী করীম(স) এর আগমনের উদ্দেশ্যও স্পষ্টভাবে বোঝা গেল। জানা গেল যে, নবীর জীবন লক্ষ্য ও ছিল আল্লাহর দ্বীন কায়েম করা এবং সাহাবীদের উদ্দেশ্যও ছিল তা-ই। নবীর আগমন, লক্ষ্য ও সাহাবীদের জীবন উদ্দেশ্য দু’রকমের ছিল কিংবা পরস্পর বিপরীত ছিলো-তার ধারণাও করা যায়না। যে মহান উদ্দেশ্যে আল্লাহতা‘আলা সাহাবায়ে কিরাম(রা)-কে নবী করীম(স) এর সঙ্গী ও সাথী বানিয়ে দিয়েছেন, তা হলো আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করা আর এ কারণেই নবী করীম(স) এর ইন্তিকালের সঙ্গে সঙ্গে সাহাবীদের এ দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। বরং তা ছিল তাঁদের জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্য্ন্ত শাশ্বত কর্তব্য। এ থেকে এ কথাও বোঝা গেল যে, আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে সাহাবীদের বাছাই ও মনোনীত করেছিলেন, তা কেবল মদীনাতেই মনোনীত ছিলনা, করণীয় ছিল মক্কায়ও। বরং মক্কী জীবন থেকেই যারা রাসূলে করীম(স) এর সাহাবী হয়েছিলেন, সাহাবীদের মধ্যে তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা ছিল সর্বাধিক। এ থেকে একথাও অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, নবী করীম(স) ও সাহাবীদের জীবন উদ্দেশ্য মক্কী জীবনেও তাই ছিলো, যা ছিল মাদানী পর্যায়ে। মদীনায় গিয়ে যেমন কোনো নতুন লক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি, তেমনি মদীনায় যাওয়ার পর মক্কী পর্যায়ের লক্ষ্য ও বদলে যায়নি। এমন হয়নি যে, নবী করীম(স) সাহাবায়ে কিরাম মক্কায় এক ধরনের উদ্দেশ্যে কাজ করেছিলেন আর মদীনায় গিয়ে ভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। অতএব গোটা মুসলিম উম্মতের উদ্দেশ্য ও দায়িত্ব তা-ই ছিলো যা ছিলো স্বয়ং রাসূলে করীম(স) ও সাহাবায়ে কিরামের। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করা, শুধু ‘দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে কওম ও হুকুমাতকে রাহমুনায়ী’ করে এ কর্তব্য পালন হতে পারেনা। বরং সেজন্য প্রত্যক্ষভাবে দ্বীন কায়েমের রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়া ইসলামে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য।(এখানে মনে করতে হবে যে, যারা শুধু কলেমার তাবলীগ করেন এবং বলেন, আমরা নবীর মক্কী পর্যায়ের কাজ করছি, তারা কিন্তু মোটেই সত্যি কথা বলছেননা। বরং নবীর মক্কী পর্যাযের কাজকে এরূপ বিকৃতরূপে পেশ করে তারা বড় অপরাধ করছেন। মক্কী পর্যায়ে রাসূল(স)ইসলামী রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার যে আদর্শ পেশ করেছেন, মাদানী পর্যায়ে তা-ই কায়েম করেছেন। কাজেই তাঁর কাজ এক অখন্ড ও অবিভাজ্য আদর্শ, তাকে দু’ভাগে বিভক্ত করা যায়না। বিভক্ত করা হলে তা নিঃসন্দেহে বিদয়াত হবে।)
এ যদি রাজনীতি হয়ে থাকে, তবে এ রাজনীতি তো দ্বীন-ইসলামের হাড়মজ্জার সাথে মিশ্রিত, ইসলামের মূলের সাথে সম্পৃক্ত। সব নবী এ দ্বীনই নিয়ে এসেছিলেন এবং সব নবীর প্রতি এ রাজনীতি করারই নির্দেশ ছিল আল্লাহর তরফ থেকে। আজ যাঁরা এ রাজনীতিকে ক্ষমতার লোভ বলে দোষারোপ ও ঘৃণা প্রকাশ করছেন, তাঁরা বুঝতে পারেননা যে, এ দোষারোপ কার্য্ত রাসূলে করীম(স) এর ওপরই বর্তায়। বর্তায় মহান আদর্শ স্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের ওপর, বর্তে দুনিয়ার মুজাদ্দিদীন ও ইসলামের মুজাহিদীনের ওপর। এ রাজনীতি ছাড়া দ্বীন, কোনোভাবেই দ্বীন ইসলাম নয়, সে দ্বীন নয়, যা নিয়ে এসেছিলেন আখেরী নবী। এ রাজনীতি পরিহার করে চলা এবং একে ‘ক্ষমতার লোভ’ বলে ঘৃণা করা ও গালাগালি করাই হলো এক অতি বড় বিদয়াত। এ বিদয়াত খতম করা না হলে ইসলাম রক্ষা পেতে পারেনা। এহেন রাজনীতিকে অস্বীকার করা, তাকে পাশ কাটিয়ে চলা এবং ‘‘দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে জনগণ ও সরকারকে শুধু রাহমুনায়ী করা কিংবা রাজনীতির ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থেকে ধর্মের কিছু অংশ প্রচার করাকে যে নিঃসন্দেহে কুরআন হাদীসের মূল ঘোষণা তথা ইসলামের প্রাণ শক্তিকেই অস্বীকার করার শামিল, তা কে অস্বীকার করতে পারে?”
নবী করীম(স) এর প্রতি ঈমান এনেই আমরা মুসলিম হতে পেরেছি। তিনিই আমাদের একমাত্র আদর্শ। আর তাঁর সাহাবী সে আদর্শানুসারী লোকদের প্রথম কাফেলা, আমাদেরও অগ্রপথিক? তাঁরা কি রাজনীতি চর্চা করেছেন? না তাঁরা দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে থেকে শুধু রাহনুমায়ী-ই(?) করে গেছেন, না নিজেরাই রাজনীতির মাঝদরিয়ায় ঝাঁপ দিয়ে মানুষকে গায়রুল্লাহর গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর বন্দেগীর পথে নিয়ে গেছেন? যে কেউ রাসূলের জীবন কাহিনী ও সাহাবীদের দিন রাতের ব্যস্ততার কথা জানেন, তাঁদের মনে এ ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা থাকতে পারেনা। তাঁরা নিঃসন্দেহে জানেন, রাসূল করীম(স) ও সাহাবায়ে কিরাম রাষ্ট্রশক্তি অর্জন করেছেন, তাঁর সাহায্যে ইসলামী জীবন বিধানকে বাস্তবায়িত করেছেন, অন্যায় ও জুলুমের প্রতিরোধ করেছেন এবং ন্যায় এর প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই আল্লাহর দ্বীনকে কায়েম করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিধান মোতাবিক ও রাসূলের দেখানো পথে ও নিয়মে যে রাজনীতি, সে রাজনীতি করা প্রকৃতই সুন্নাহ এবং তা বাদ দিয়ে চলা, আর এ রাজনীতিকে বাদ দিয়ে চলার রাজনীতেকে সুন্নাত বা ‘ইসলামের রীতি’ বলে বিশ্বাস করা সুস্পষ্টভাবে বিদয়াত। এ বিদয়াত ইসলামকে এক বৈরাগ্যবাদী ধর্মে পরিণত করেছে। শুধু তা-ই নয়, মুসলিমদের উপর ফাসিক ফাজিরদের কর্তৃত্ব, জুলুম ও শোষণ চলার স্থায়ী ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বস্তুত নবী করীম(স) যদি এদের মতো নীতি অনুসরণ করতেন, যদি তদানীন্তন আরব সমাজের প্রধান আবু জেহেল ও আবু লাহাব এর প্রতি তাদের শুধু ‘রাহনুমায়ী’ করার নীতিই গ্রহণ করতেন, তাহলে মুশরিক কাফিরদের তরফ হতে এত বিরুদ্ধতা হতোনা, রাসূলকে হিজরত করতে, জিহাদে দাঁত ভাঙতে ও সাহাবীদের শহীদ হতে হতোনা কখনো। বরং তাঁরা এ ধরনের নীতি গ্রহণ করে লাখ লাখ টাকা পেতে পারতেন, যেমন একালের এক শ্রেণীর আলিম ও পীরেরা পাচ্ছে এ যুগের আবু জেহেল ও আবু লাহাব এর কাছ থেকে। আর তা-ই যদি তাঁরা করতেন, তাহলে এ যুগে ইসলামের কোনো অস্তিত্বই থাকতোনা, হতো না ইসলামের কোনো ইতিহাস- কোনো গৌরবোজ্জ্বল জীবন্ত কাহিনী।
প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের রাজনীতি করা ইমাম মুজতাহিদগণের মতে এবং ফিকাহ ও আকাঈদের দৃষ্টিতেও ঈমানেরই তাগিদ-একান্তই কর্তব্য।
আল্লামা মুল্লা আলী আল কারী ইমাম আবু হানীফা(রহ) এর ইসলামী আকায়েদ এর বড় ব্যাখ্যাতা। তিনি লিখেছেনঃ ইমাম-ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালক-নিয়োগ করা যে ওয়াজিব, এ বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞই সম্পূর্ণ একমত।
ইমাম নিয়োগের কাজ যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে গিয়ে তিনি আরো লিখেছেনঃ সাহাবায়ে কিরামও ইমাম নিয়োগকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এমন কি নবী করীম(স) কে দাফনের পূর্বেই ইমাম নিয়োগের কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। কিন্তু কেন? তার কারণ এই যে, মুসলমানদের জন্য একজন ইমাম-রাষ্ট্রচালক-একান্তই আবশ্যক, যে তাদের আইনসমূহ কার্যকর করবে, হদ্দসমূহ কায়েম করবে, তাঁদের ফাঁক ও ফাটলসমূহ বন্ধ করবে, তাদের সৈন্যদের সদা প্রস্তুত ও সজ্জিত করে রাখবে, তাদের সম্মান ও সময় সংরক্ষণ করবে, তাদের বিদ্রোহী আক্রমণকারীদের শক্তিবলে দমন করবে, ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের শাসন করবে, জুম’আ, হজ্জ ও ঈদ কায়েম রাখবে, অভিভাবকহীন ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা করবে, গনীমতের মাল ও জাতীয় সম্পদ বন্টন করবে এবং এ ধরনের আরও শরীয়ত মোতাবিক যে সব কাজ করা জরুরী তা সুসম্পন্ন করবে। (শরহে ফিকাহ আকবর)
এই পর্যায়ে সর্বশেষ ও অত্যন্ত জরুরী কথা হলো, ‘রাজনীতি না করা বিদয়াত’ পর্যায়ে এখানে যা কিছু বলা হয়েছে, তা শুধু দ্বীন কায়েমের রাজনীতি না করা সম্পর্কে কিন্তু রাজনীতির নামের দ্বীন ইসলাম পরিপন্থী মতাদর্শ কায়েমের রাজনীতি, তা না করা নয়, তা করাই একালের একটি অতি বড় বিদয়াত। বড়ই দুঃখ ও লজ্জার বিষয়, মুসলমানরা এ ইসলামী পরিচিত ধারণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠী, দল জামা‘আত বর্তমানে সাধারণভাবে যে রাজনীতি করছে, তা দ্বীন কায়েমের রাজনীতি নয়; এবং দ্বীন ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, সমাজতন্ত্র বা পুঁজিবাদ কায়েম করার রাজনীতি করছে-তা সম্পূর্ণ বিদয়াত, হারাম। মুসলমান বা ইসলাম পরিচিতি দিয়ে কুফর কায়েম করার রাজনীতি করা কুরআনের ভাষায় চরম মুনাফিকী, তা আল্লাহর এই প্রশ্নের সম্মুখীনঃ আরবী(****)
-হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা মুখে কেন বলো সেই কথা যা কাজে তোমরা করছোনা?
যা করছো না তাই বলছো, অতএব যা বলছো তা করছো না-নিজেদের নাম ও পরিচিতির আলোকে যা তোমাদের করা উচিত, তা করছো না, যা করা উচিত নয় তা করছো। তোমাদের নাম ও পরিচিতি দেখে লোকেরা তোমাদের নিকট যে রাজনীতি আশা করে স্বাভাবিকভাবে তোমরা সে রাজনীতি করছো না, করছো যা তা হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, সমাজতন্ত্রী বা পুঁজিবাদ রাজনীতি। ফলে তোমাদের গোটা অস্তিত্বই একটা প্রচন্ড মুনাফিকী হয়ে দাঁড়িয়েছে। তোমরা হচ্ছো মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজ।
তোমাদের এই রাজনীতি স্পষ্ট বিদয়াত, তা অবিলম্বে পরিহার করে সরাসরি আল্লাহর দ্বীন কায়েমের রাজনীতি করা তোমাদের কর্তব্য। তোমাদের নাম ও পরিচিত ঐকান্তিক দাবিও তাই। গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম করার কথা বলা সুস্পষ্ট বিদয়াত। কেননা গণতন্ত্র কুফরি মতবাদ। কুফর দ্বারা ইসলাম কায়েম হতে পারেনা। ইসলাম সরাসরি আল্লাহর বন্দেগী কবুলের দাওয়াতের মাধ্যমেই কায়েম হতে পারে, এছাড়া মধ্যমপন্থা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়, অতএব তা ত্যাগ করতে হবে।
আল্লাহর নৈকট্য লাভে অসীলা’র বিদয়াত
কুরআন ও হাদীসে যে সর্বাত্মক তওহীদী আকীদা পেশ করেছে, তদানুযায়ী একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই হলেন সমগ্র বিশ্বলোকের নিরংকুশ অধিকারী কর্তা ও পরিচালক। মানুষ কেবল এক আল্লাহরই বন্দেগী দাসত্ব ও আনুগত্য করবে, জীবনের সমগ্র ক্ষেত্রে এক আল্লাহরই দেয়া আইন বিধান পালন করে চলবে এবং এই সব ব্যাপারেই একমাত্র অনুসরণ করবে আল্লাহর রাসূলের। হেদায়াত লাভ করবে রাসূলের নিকট থেকে। তিনি যে পথ, পন্থা ও উপায় এবং কর্মনীতি উপস্থাপিত করেছেন, মানুষ তাদের সমগ্র কাজ সেই অনুযায়ীই সম্পন্ন করবে। কোনো কিছু চাইতে হলে কেবল তাঁরই নিকট চাইবে এবং কোনো কিছু পাওয়ার আশা করলেও কেবল তাঁরই নিকট হতে আশা করবে।
কুরআন মজীদে উদাত্ত ভাষায় বলা হয়েছেঃ
قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٣:٣١]
- তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস, তবে তোমরা আমার(নবীর) অনুসরণ করে চলো। তা হলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গোনাহ খাতা মাফ করে দেবেন।
এই আয়াত অনুসারে আল্লাহকে ভালোবাসার, আল্লাহর বন্দেগী করার ইচ্ছা বান্দার মনে জাগাবার অনিবার্য্ ফলশ্রুতি যেমন রাসূলের অনুসরণ করা; তেমনি বাস্তব ক্ষেত্রে রাসূলের অনুসরণ করা ছাড়া আল্লাহকে ভালোবাসার কোনো দাবিই অর্থবহ হতে পারেনা। উপরন্তু আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে রাসূলের অনুসরণ।
আল্লামা আলুসী এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করে তাঁর প্রতি ভালোবাসা দেখাল এবং তাঁর নবীর অনুসরণ করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করলো, আল্লাহ তার জন্য ক্ষমাশীল ও দয়াবান।
রাসূলে করীম(স) কে মুসলমানদের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে পেশ করা হয়েছে কোরআন মজীদে।
ইরশাদ হয়েছেঃ
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا [٣٣:٢١]
-নিশ্চিতই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের চরিত্রে উত্তম অনুসরণীয় নমুনা ও আদর্শ রয়েছে। তাদের জন্য তা ফলপ্রসূ হবে যারা আল্লাহকে পেতে চায়, পরকালে মুক্তি চায় এবং আল্লাহকে খুব বেশি স্মরণ করে।
এ আয়াত অনুযায়ীও যে লোক আল্লাহকে পেতে চায়, পরকালের মুক্তি চায় এবং আল্লাহর জিকির করে বেশি বেশি করে, তার জন্য বাস্তব অনুসরণযোগ্য আদর্শ চরিত্র হচ্ছে রাসূলে করীম(স)। যে লোক তাঁকে অনুসরণ করবে সর্বোতভাবে, সে যেমন আল্লাহকে পাবে, পাবে পরকালীন মুক্তি, তেমনি তাঁর আল্লাহ জিকির বাস্তবরূপ লাভ করবে নবীর অনুসরণের মাধ্যমে, তারই মাঝে তা রূপায়িত ও প্রতিফলিত হয়ে উঠবে।
কুরআনের এসব উদাত্ত ঘোষণা অনুযায়ী মানুষ মানতে বাধ্য একমাত্র আল্লাহকে এবং অনুসরণ করতে বাধ্য একমাত্র রাসূলে করীম(স) কে। বস্তুত ইসলামের তওহীদী আকীকা অনুযায়ী আল্লাহকে পাওয়ার উপায় রাসূলের বাস্তব অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নেই। রাসূলের জামানায়, সাহাবীদের সময়ে এবং তাবেই ও তাবে তাবেয়ীনের সময়েও এই ছিল ইসলামী সমাজের বাস্তবরূপ। আল্লাহকে পাওয়ার এছাড়া অন্য কোনো পথই তাঁদের জানা ছিলনা, তাঁরা অন্য কোনো উপায়ই গ্রহণ করতেননা। কিন্তু পরবর্তীকালে মানুষের ওপর চেপে বসে পীরত্বের বিদয়াত। সমাজে এক শ্রেণীর লোক পীর হয়ে বসে এবং দাবি করে যে, তারা আল্লাহর নিকট বান্দাদের পৌছার অসীলা বা মাধ্যম। তাদের গ্রহণ করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে আর তাদেরকে গ্রহণ না করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবেনা (নাউজুবিল্লাহ)।
অথচ কুরআন থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহকে পাওয়ার জন্য রাসূলের অনুসরণে শরীয়ত পালন ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাধ্যমের কোনো অবকাশই নেই, তার কোনো প্রয়োজনই নেই। বান্দার দো‘আ আল্লাহর নিকট সরাসরি পৌছে যায়, আল্লাহ সরাসরিভাবে বান্দার দো‘আ কবুল করে থাকেন, সে জন্য তিনি কোনো মাধ্যম গ্রহণ করতে বলেননি, দো‘আ কবুল হওয়ার জন্য তিনি কোনো মাধ্যম গ্রহণের শর্তও আরোপ করেননি। বরং এ পর্যায়ের যাবতীয় বিভ্রান্তি ও ভুল আকীদা দূর করে দিয়ে তিনি স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ [٢:١٨٦]
-হে নবী! আমার বান্দা যদি তোমার নিকট আমার বিষয়ে জিজ্ঞেস করে, তবে বলে দাও আমি অতি নিকটে, কোনো দো‘আকারী যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার দো‘আ র জবাব দিই-দো‘আ কবুল করি। অতএব আমারই নিকট জবাব পেতে চাওয়া তাদের কর্তব্য এবং আমার প্রতিই তাদের ঈমান রাখা উচিত। তাহলে সম্ভবত তারা সঠিক পথে চলতে পারবে।
আল্লাহ-ই সব দো‘আ প্রার্থনাকারীর দো‘আ কবুল করেন, কেবল তাঁরই নিকট দো‘আ করে তাঁরই নিকট থেকে তাঁর জবাব পেতে চেষ্টা করা উচিত, এ কথাই বলা হয়েছে উক্ত আয়াতে। আল্লাহর নিকট কোনো মাধ্যম ছাড়া পৌছা যায়না বলে বিদয়াতীরা যে ধারণা সৃষ্টি করেছে তার মূলোৎপাটন করা হয়েছে এ আয়াতে। “দো‘আ কারীর দো‘আ আমিই কবুল করি” বলে আল্লাহ তা‘আলা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর নিকট দো‘আ করতে এবং দো‘আ কবুল করাতে কোনো অসীলার প্রয়োজন নেই। সঠিকভাবে আল্লাহর নিকট দো‘আ করতে পারলে আল্লাহ সরাসরিভাবেই তা কবুল করে থাকেন। “আমারই জবাব পেতে চাওয়া কর্তব্য” বলে আল্লাহ বুঝিয়ে দিলেন যে, যে লোক দো‘আ করবে তার মনে এ দো‘আ কবুলের জন্য বিশেষ আগ্রহ, উৎসাহ ও আবেগ থাকা বাঞ্চনীয়। এ জিনিস অপরের দ্বারা হয়না, অসীলা কিছুই করতে পারেনা। আর ‘‘আমার প্রতিই ঈমান রাখা উচিত” বাক্য দ্বারা বলে দিলেন যে, আমার এই ঘোষণাকে মনে রেখে আল্লাহকে আপনার অতি নিকটে বলে বিশ্বাস করা কর্তব্য। কোনো মাধ্যমের ধোঁকায় পড়ে গিয়ে সরাসরি আল্লাহর নিকট দো‘আ করার পরিবর্তে কোনো মাধ্যমের আশ্রয় গ্রহণের বিভ্রান্তিতে পড়া উচিত নয়। আয়াতের শেষ শব্দেও এ পথকেই সত্যিকার বিদয়াতের পথ বলে ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের একমাত্র উপায় হলো, আল্লাহর নিকট কাতরভাবে দো‘আ করা ও এই বিশ্বাস মনে রাখা যে, আল্লাহ-ই আমার দো‘আ কবুল করবেন।
অপর এক আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা আরো জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেনঃ
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ [٤٠:٦٠]
- তোমাদের আল্লাহ বলেছেনঃ তোমরা আমাকেই ডাকো, আমারই নিকট দো‘আ করো, আমিই তোমাদের জবাব দেবো-দো‘আ কবুল করবো। যে সব লোক আমার ইবাদত করার ব্যাপারে অহংকার করবে, তাদের সকলকে জাহান্নামে একত্রিত করা হবে। (আল মোমেনঃ60)
এখানেও আল্লাহকে সরাসরি ডাকার-সরাসরিভাবে আল্লাহর নিকট দো‘আ করার নির্দেশ। আর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে এই দো‘আ কেই আল্লাহর ইবাদত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ যারা সরাসরিভাবে আল্লাহর নিকট দো‘আ করেনা, অসীলা ধরে অগ্রসর হতে চায়, তারা একান্তভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে প্রস্তুত নয়, তারা যে জাহান্নামে যাবে তাতে আর কোনোই সন্দেহ থাকতে পারেনা। মক্কার কাফিরদের তো এই অপরাধই ছিলো যে, যার জন্য তারা জাহান্নামী হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।
কোরআন মজীদের এসব আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য, নিজেদের দো‘আ কবুল করবার জন্যে এবং ইসলামী শরীয়ত মোতাবিক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করবার জন্য কোনো ‘অসীলার’ আদৌ কোনো প্রয়োজন নেই এবং আল্লাহর নিকট তা পছন্দনীয়ও নয়। বরং আল্লাহতো চান বান্দা সরাসরিভাবে তাঁরই দিকে রুজু হোক, তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করুক; তাঁর পরিবর্তে অন্য কারো নিকট দরবারে কপাল লুটানো ত্যাগ করুক। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম সমাজে ইসলামেরই দোহাই দিয়ে প্রবর্তন করা হয়েছে ‘অসীলা’। অসীলা ছাড়া আল্লাহকে পাওয়ার নাকি আর কোনো উপায়-ই নেই-এমন প্রচারণা চালানো হয়েছে। ইসলামের তওহীদী ব্যবস্থায় এই ‘অসীলা’র প্রচলন এক অতি বড় বিদয়াত এবং এ বিদয়াত তওহীদবাদিদের কঠিন শিরক-এ নিমজ্জিত করে ছেড়েছে। বিদয়াতীদের দরবার থেকে ফতোয়া জারি করা হয়েছেঃ আল্লাহ প্রাপ্তির জন্য অথবা আল্লাহপাকের অনুগ্রহ লাভের উদ্দেশ্যে অসীলা অবলম্বন করা কেবলমাত্র জায়েজই নয়; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফরয ও ওয়াজিবও বটে।
বস্তুত যা কুরআন থেকে প্রমাণিত নয়, যা রাসূলের কথা, কাজ ও অনুমোদন দ্বারা প্রমাণিত নয়-তাকে ফরয, ওয়াজিব বলাই হলো বিদয়াত। উপরোল্লিখিত অংশ এই বিদয়াতেরই সপক্ষে এক বিশেষ ফতোয়া। এই বিদয়াত এখন জনগণের একাংশকে গ্রাস করে রয়েছে। তাদের মধ্যে কারো ধারণাঃ “আমরা নামায রোজা করিনা; কেননা আমরা পীরকে ধান দিয়ে থাকি”। (নাউজুবিল্লাহ)
তার মানে পীরকে ধান দিলে পীর তো খুশি হবে। আর পীর খুশি হলে আল্লাহও খুশি হবেন। তাহলে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করার আর প্রয়োজন কি? আল্লাহকে পাওয়ার জন্য পীরকে ধান দেয়া-ভেট দেয়াই –নাকি যথেষ্ট।
আবার অন্য কিছু লোকের ধারণা যে, পীর সাহেব যে বেহেশতে যাবেনই একথা তো নিশ্চিত-যেন তারা আল্লাহর কাছ থেকে জানতে পেরেছে যে, পীর সাহেব একজন বেহেশতী হয়েই আছেন। অথচ এ ধারণা চরম বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা যাকে এরূপ মর্যাদা দিয়ে তার হাত হাত রাখা হচ্ছে, তার পক্ষে অন্যদের বেহেশতে নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, সে নিজেই যে বেহেশতে যাবে তারও কোনোই ঠিক ঠিকানা নেই।
অসীলাবাদীরা তাদের মতের সমর্থনে কোরআনের একটি আয়াতের অংশও পেশ করে থাকেঃ সে আয়াতাংশ হচ্ছে-
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
-হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় করো আল্লাহকে এবং তাঁর নিকট অসীলার সন্ধান করো।
আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহকে ভয় করে তাঁর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে। কিন্তু কুরআনের আয়াতের মূল প্রতিপাদ্য কথার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করা হয়েছে এভাবে এ আয়াতকে ব্যবহার করে। প্রথম কথা, অসীলাবাদীরা এ আয়াতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেনি, আয়াতটির শুধু একটি অংশকে নিজেদের কথা প্রমাণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। অথচ পূর্ণ আয়াতের অর্থ হয় এক, আর আয়াতের একটি অংশ পেশ করে নিজেদের মতলব মতো সম্পূর্ণ ভিন্ন কথাও বলতে চেষ্টা করা যেতে পারে। এখানে ঠিক তাই হয়েছে।
সম্পূর্ণ আয়াতটি এইঃ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٥:٣٥]
-হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নিকট অসীলার সন্ধান করো এবং জিহাদ করো তাঁর পথে। সম্ভবত তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পারবে। (আল মায়েদাঃ35)
প্রখসে প্রমাণ করতে হবে-‘অসীলা’ শব্দের অর্থ কি, কুরআনের এ আয়াতে কোন্ অর্থে ‘অসীলা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। তারপরই এ আয়াতের যথার্থ বক্তব্য বুঝতে পারা যাবে। আমরা তাই দেখছি, কুরআন মজীদে এই ‘অসীলা’ শব্দটি এ আয়াত ছাড়া আরো একটি আয়াতে-মোট দুই জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।
অপর আয়াতটি হলো এইঃ
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا [١٧:٥٦]
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا [١٧:٥٧]
-বলো! তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদের মা’বুদ বলে মনে করো, তাদের একবার ডাকো, তারা তোমাদের থেকে বিপদ ও কষ্ট দূর করতে কিংবা তা বদলে দেবার কোনো ক্ষমতা রাখেনা। এই লোকেরা যাদের ডাকে, তারাই তাদের পরোয়ারদিগারের নিকট নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী, তাঁর রহমতের তারা আশা করে, তাঁর আযাবকে তারা ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব ভয় করার যোগ্য।
(বনী ঈসরাইলঃ 56-57)
এ দু জায়গায় যে ‘অসীলা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ কি? কুরআন মজীদের শব্দ ব্যাখ্যাকারী লেখক সর্বজনমান্য মনীষী আল্লামা রাগেব ইসফাহানী এ শব্দের অর্থ লিখেছেন এভাবেঃ অসীলা মানে কোনো জিনিসের নিকট আগ্রহ সহকারে পৌছা। এর মধ্যে আগ্রহের ভাব বলে তা অসীলা বা পৌছা অপেক্ষা একটু বিশেষ অর্থজ্ঞাপক।
তিনি তাঁর খতীব নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ ‘অসীলা’ বিশেষ্য অর্থাৎ নৈকট্য, নিকটবর্তী হওয়া, নৈকট্য লাভের উপায় অর্থাৎ আনুগত্য।
আল্লামা কুরতবী তাফসীরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ‘অসীলা’ শব্দের অর্থ হলো নৈকট্য। আর এ অর্থই বর্ণিত হয়েছে আবু অয়েল, হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, আতা, সুদ্দী, ইবনে যায়দ ও আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর প্রমূখ তাবেয়ী ও কুরআনবিদ মনীষীদের কাছ হতে।
তিনি আরো লিখেছেনঃ অসীলা হলো এমন নৈকট্য যার দরুণ কারো কাছে কোনো কিছু চাওয়া বাঞ্চনীয় নয়। চাওয়া যেতে পারে আল্লাহর নিকট, কাজেই এ নৈকট্যও আল্লাহরই হতে হবে।
ইমাম সুয়ূতী প্রথমোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ অসীলা হচ্ছে সেই আনুগত্য-ইবাদাত, যা তোমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী করে দেয়।
মওলানা আবদূর রশীদ নোমানী ‘লাগাতুল কুরআন’ এ লিখেছেনঃ শব্দটি সম্পর্কে দু’ধরনের মত রয়েছে। খতীব ও ইমাম রাযীর মতে এর অর্থ নৈকট্য লাভের উপায়। আর ইমাম সুয়ূতী এর দু’প্রকারের অর্থ করেছেন। একটি হলো-নৈকট্যের উপায় মানে ইবাদাত আর অপরটি হলো খোদ নৈকট্য যা ইবাদাত এর সাহায্যে লাভ করা যায়।
ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ ‘অসীলা’ মানে নৈকট্য, যা সন্ধান করা উচিত।
আবু ওয়ায়েল, হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী, ইবনে যায়দ প্রমুখ মনীষী এই মতই প্রকাশ করেছেন এবং হযরত ইবনে আব্বাস, আতা ও আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর হতেও একই মত বর্ণিত হয়েছে।
তাফসীরে ফতহুল বয়ানেও এই কথাই বলা হয়েছে। তাতে লেখা হয়েছেঃ অসীলা জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদা, যা রাসূলের জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট।
বুখারী শরীফে হযরত জাবির হতে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম(স) বলেছেনঃ আযান শুনে যে লোক বলবে-হে আল্লাহ! এই পূর্ণ দাওয়াতের ও কায়েম করা নামাযের রব্ব তুমি মুহাম্মাদ কে ‘অসীলা’ দান করো, মর্যাদা দান করো এবং তাঁকে সেই মাকামে মাহমুদে পাঠাও, যার ওয়াদা তুমি তাঁকে করেছ, কিয়ামাতের দিন এই লোকের শাফায়াত অনিবার্য্ হবে।
মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নবী করীম(স) কে বলতে শুনেছেনঃ তোমরা মুয়াযযিনের আযান শুনতে পেলে সে যা যা বলে তোমরাও তাই বলতে থাকে। পরে আমার প্রতি দুরুদ পাঠ করো। বস্তুত যে লোক আমার প্রতি এক দুরুদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশ দুরুদ পাঠাবেন।
অতঃপর তোমরা আমার জন্য অসীলার সওয়াল করো। কেননা এ হচ্ছে জান্নাতের একটি বিশেষ মঞ্জিল।
‘ফতহুল বয়ান’ গ্রন্থে অসীলা শব্দের প্রথম অর্থের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছেঃ এ কথা সুস্পষ্ট যে-অসীলা-যার মানে নৈকট্য-তাকওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, তাকওয়া ছাড়াও এমন সব গুনাবলী যার সাহায্যে বান্দাগণ তাদের আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা বোঝায়। কেউ কেউ বলেছেন-অসীলা অর্থ প্রেম-ভালোবাসা অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা পোষণ করো। কিন্তু প্রথম অর্থই উত্তম।
আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর তাফসীরে প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় যা লিখেছেন তার তরজমা এইঃ আল্লাহ তা‘আলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর প্রতি তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর তাঁকওয়াকে যদি তাঁর আনুগত্যের সংগে মিলিয়ে দেয়া যায় তাহলে তার অর্থ হবে হারাম কাজ হতে বিরত থাকা এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ ত্যাগ করা। আর তারপরই বলেছেন-তাঁর নিকট অসীলা সন্ধান করো।
অতঃপর লিখেছেনঃ সুফিয়ান সওরী তালহা থেকে, তালহা আতা থেকে এবং আতা ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এই ‘অসীলা’ মানে নৈকট্য।
আবু ওয়ায়েল, হাসান, মুজাহিদ, কাতাদাহ, সুদ্দী, ইবনে যায়দ, আবদুল্লাহ ইবনে কাসীর প্রমুখ প্রখ্যাত প্রাচীন মনীষীগণও এই মতই প্রকাশ করেছেন এবং কাতাদাহ্ এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবেঃ
অর্থাৎ তাঁর দিকে তোমরা নৈকট্য লাভ করো, তাঁর আনুগত্য করো এবং যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন তা করো।
তারপরই আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ ইলমে কুরআনের এই ইমামগণ ‘অসীলা’ শব্দের অর্থ যা কিছু বলেছেন, সে বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।
তিনি ‘অসীলা’ শব্দের আরো দুটো অর্থ লিখেছেন।
একটি হলোঃ অসীলাতা, যার সাহায্যে মূল লক্ষ্যে পৌছা যায়।
আর দ্বিতীয়ঃ অসীলা জান্নাতের এক উচ্চতর মঞ্জিলের নামও। আর তা হচ্ছে রাসূলে করীম(স) এর মরতবা।
অসীলার এই অর্থের সমর্থনে ইমাম ইবনে কাসীর বহু সংখ্যক হাদীস উদ্বৃত করেছেন। হযরত আলী(রা) বর্ণিত এই পর্যায়ের একটি হাদীসের ভাষা হলোঃ জান্নাতে একটি বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থান আছে যাকে বলা হয় ‘অসীলা’। তোমরা যখন আল্লাহর নিকট কিছু চাইবে তখন তোমরা আমার জন্য অসীলার প্রার্থনা করবে।
আর এ আয়াতের শেষাংশের তাফসীরে লিখেছেনঃ
আল্লাহ যখন হারাম কাজ ত্যাগ করার ও ইবাদাত আনুগত্যের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দিলেন, তখন সীরাতাল মুস্তাকিম-বহির্ভূত কাফির মুশরিক শত্রু বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন।
ইমাম বায়জাবী এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেনঃ
অর্থাৎ সন্ধান করো সেই জিনিস যার সাহায্যে তোমরা তাঁর সওয়াব এবং তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারো। আর তা হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজ করা এবং নাফরমানীমূলক কাজ ত্যাগ করা।
আল্লামা যামাখশারী লিখেছেনঃ অসীলা হচ্ছে এমন জিনিস, যার দ্বারা কোনোরূপ নৈকট্য লাভ করা যায় বা এমন কোনো কাজ কিংবা অন্য কিছু। পরে তা ব্যবহার করা হয়েছে সে জিনিস বোঝাবার জন্য, যা দ্বারা আল্লাহ তা‘আলা পর্য্ন্ত পৌছানো যায়। তা হচ্ছে ইবাদাত ও আনুগত্যের কাজ করা এবং নাফরমানী ত্যাগ করা। আল্লামা আবুস সয়ুদও এ আয়াতের তাফসীরে একই কথা বলেছেন নিজস্ব ভাষায়।
তাতে অসীলা সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ ‘অসীলা’ তা, যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়-আল্লাহ পর্যন্ত পৌছা যায়। আর তা হচ্ছে ইবাদাত আনুগত্যের কাজ করা এবং নাফরমানী ত্যাগ করা।
তিনি আরো লিখেছেনঃ আয়াতের এরূপ অর্থও করা হয়েছে-প্রথম বাক্যে আল্লাহকে ভয় করো বলে গুনাহ ও নাফরমানী ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় বাক্যে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো বলে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর যে লোকই নাফরমানীর কাজ ত্যাগ করবে এবং মনের পক্ষে দুঃসহজনক কাজ সম্পন্ন করবে তার কিছু না কিছু কষ্ট ও শ্রম অবশ্যই হবে। তাই এ দু’টি আদেশের পরপর আল্লাহর আদেশ হলো-আল্লাহর পথে জিহাদ করো আল্লাহর প্রকাশ্য ও শক্ত দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে।
আল্লামা সাইয়েদ মাহমুদ আলুসীও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় অনেক কথা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করেছেন। তিনি সূরা আল মায়েদার উপরোল্লিখিত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এবং তালাশ করো-সন্ধান করো তোমাদের নিজেদের জন্য তাঁর সওয়াব এবং তাঁর নৈকট্য।
আর ‘অসীলা’র অর্থ লিখেছেনঃ অসীলা তা, যার সাহায্যে পৌছা যায় এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়, তা হলো ইবাদত বন্দেগীর কাজ করা ও নাফরমানীর কাজ ত্যাগ করা।
আল্লামা ইবনে জরীর তারাবী লিখেছেনঃ আল্লাহর নিকট আমল সহকারে নৈকট্য পেতে চাও, যা তাঁর সন্তোষের কারণ হবে, ‘অসীলা’, ‘ফাযীলা’ ওজনের শব্দে। যেমন কেউ বলে, ‘আমি তার নিকটবর্তী হলাম’ এতে তাওয়াসসূল ‘তাকাররূব’ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ‘তাওয়াসালতু ইলাইহি’ মানে আমি তার নিকটবর্তী হলাম।
তিনি আরো লিখেছেনঃ আমরা যেমন বলেছি, শব্দের ব্যাখ্যাকার ও তাৎপর্য্ বিদগণ এ অর্থই গ্রহণ করেছেন। বাশশার ও সুফিয়ান আবু ওয়েল থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসীলাতা’ বলে আমলের নৈকট্য লাভের হুকুম করা হয়েছে। সুফিয়ান, আবু তালহা, আতা প্রমুখও এ ব্যাপারে অর্থ করেছেন নৈকট্য। কাতাদাহ থেকে বর্ণিতঃ তিনি এ আয়াতের তরজমা করেছেন এভাবেঃ ‘আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর পছন্দমতো কাজ করে আল্লাহর নিকটবর্তী হও।’ হুযায়ফা থেকে বর্ণিত, মাশীদ আবু নজীহ বলেছেন যে, মুজাহিদ ‘ওয়াবতাগু ইলাইহিল অসীলাতা’র অর্থ করেছেন নৈকট্য।
আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ আল্লাহর নিকট ‘অসীলা’ তালাশ করো অর্থ-আমলের সাহায্যে আল্লাহর নৈকট্য তালাশ করো।
আল্লামা আলুসী বলেছেনঃ ইবনুল আনবারী ইবনে আব্বাসের কথা উদ্বৃত করে বলেছেন-অসীলা মানে প্রয়োজন, আবশ্যকতা।
এ অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের অর্থ হবেঃ তোমরা আল্লামুখী হয়ে তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে চাও। কেননা আসমান জমিনের সব চাবিই তাঁর হস্তে এবং আর কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হয়ে তোমরা প্রয়োজন পূরণ করতে চেওনা।
‘অসীলা’ শব্দের এ অর্থটি বলা যায় নতুন। অর্থাৎ অপর কোনো মুফাসসীর তা উল্লেখ করেননি। তবু বলা যায়- মূল আরবী অভিধান, সব সাহাবী, তাবেয়ী এবং প্রামাণ্য সব কয়খানি তাফসীরই ‘অসীলা’ শব্দের অর্থ এই হতে পারে, অন্য কিছু নয়। অন্য কিছু অর্থ করা হলে তা হবে পরবর্তীকালের লোকদের মনগড়া। মূল কোরআন হাদীস ও আরবী ভাষার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। এ আয়াতের ভিত্তিতে জানা গেল যে, এ আয়াতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ‘অসীলা’ সন্ধানের যে নির্দেশ আল্লাহ তা‘আলা দিয়েছেন, তার মানে হলো আল্লাহরই আনুগত্য করা, কেবল তাঁরই ইবাদত বন্দেগী করা এবং তাঁর নাফরমানী না করা। কিংবা নিজেদের প্রয়োজন কেবল আল্লাহর নৈকট্যের থেকে পূরণ করতে চাওয়া অন্য কারো নিকট থেকে নয়। অপর কাউকে অসীলা বা মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারেনা, করা হলে তা হবে শিরক আর বিদয়াত। এই শিরক এর পথ চিরতরে বন্ধ করার জন্যই আল্লাহর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আয়াতকেই পেশ করা হচ্ছে অসীলার শিরককে সুষ্ঠু-জায়েয-ওয়াজিব-ফরয প্রমাণ করার কুমতলবে। আর এই পর্যায়ে ‘হেসনে হাসীন’ ‘আল-মুহান্নাদ’ আর ‘শেফাউস-সেকাম’ ধরনের কিতাবাদিতে লিখিত কথা পেশ করে তওহীদের এই চিরন্তন শাশ্বত আকীদাকে বিকৃত ও বিনষ্ট করতে চেষ্টা করা হচ্ছে।
কুরআনের যে দুটো আয়াতে এ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সমস্ত মুফাসসির এ সম্পর্কে একমত যে, উভয় জায়গায়ই এ শব্দের এ অর্থই লক্ষ্যভূত হয়েছে, অন্য কোনো অর্থ নয়। আর বিস্তারিত আলোচনার দৃষ্টিতে গোটা আয়াতের অর্থ হলোঃ ‘হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, ভয় করো আল্লাহর নৈকট্য বা নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করো এবং এ জন্যই আল্লাহর পথে জিহাদ করো।’ (ইমাম কুরতবী, ইমাম ইবনে কাসীর, ইমাম শাওকানী প্রমূখ তাঁদের তাফসীরসমূহে এই একই কথা বলেছেন যার বাংলা তরজমা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে)।
আর হাদীসে ব্যবহৃত ‘অসীলা’ শব্দের অর্থ আল্লাহর এক বিশেষ মঞ্জিল। শরীয়তে এ অর্থকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এখন দেখতে হবে, আল্লাহর নিকট অসীলা বানানোর শরীয়তসম্মত পন্থা ও পদ্ধতি কি? এ পর্যায়ে কয়েকটি জিনিস পেশ করা হচ্ছে।
প্রথমতঃ আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অসীলা গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে কুরআন হাদীসসম্মত। আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ
-আল্লাহর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম। অতএব তোমরা সে নাম ধরে ধরে তাঁকে ডাকো।(আল আরাফ 180)।
হাদীসে বর্ণিত রয়েছে, আবদুল্লাহ তাঁর পিতা বরিদা(রা) হতে বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম(স) এক ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত ভাষায় দোআ করতে শুনতে পেলেন।
-হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি এ দিক দিয়ে যে, তুমিই আল্লাহ, তুমি ছাড়া কেউ মাবুদ নেই, তুমি পরমুখাপেক্ষীহীন, যিনি নিজে পয়দা হননি, জন্মও দেননি এবং কেউ তাঁর সমান সমকক্ষ নেই।
তখন নবী করীম(স) বললেন-এ লোকটি আল্লাহর নিকট তাঁর এমন বিরাট মহান নাম নিয়ে দো‘আ করল যে, এভাবে কিছু প্রার্থনা করলে নিশ্চয়ই কিছু দেয়া হবে, আর দোআ করা হলে তা অবশ্যই কবুল করা হবে।
হযরত আনাস ইবনে মালিক(রা) ও হযরত আয়েশা(রা) হতে বর্ণিত হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়।
দ্বিতীয়ঃ নেক আমলের অসীলা। এ পর্যায়েও কুরআন হাদীসের দলীল বর্তমান। কুরআনের দলীল হচ্ছে সে দুটো আয়াত যাতে অসীলা শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কেননা দুটো আয়াতেই ‘অসীলা’ শব্দের মানে ‘নৈকট্য’ হওয়া সম্পর্কে সমস্ত মুফাসসিরের ইজমা রয়েছে। এ পর্যায়ের তৃতীয় দলীল হচ্ছে সূরা ফাতিহার আয়াত إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُকেবল তোমারই বন্দেগী করি, কেবল তোমারই নিকট সাহায্য চাই হে আল্লাহ! এতে সাহায্য প্রার্থনা এর পূর্বে ইবাদত এর উল্লেখ করাই হয়েছে প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির অসীলা বানানোর জন্য।
হাদীসে এর দলীল হলো বুখারী শরীফে উল্লিখিত সেই কাহিনী, যাতে বলা হয়েছে –তিনজন লোক বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পর্বত গুহায় আশ্রয় নেয়। অমনি এক বিরাট শিলাখন্ড এসে পর্বতগুহীর মুখ বন্ধ করে দেয়। মুক্তির কোনো পথ নেই মনে করে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের নেক আমলের উল্লেখ করে আল্লাহর নিকট মুক্তির প্রার্থনা করতে লাগলো। পরে তাদের দোআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় এবং তারা মুক্তি লাভ করে। নবী করীম (স) এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন প্রশংসাচ্ছলে এবং গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে।
এ হাদীস সম্পর্কে বলা যায়ঃ জুম’আর দিন যখন সূর্য্ যথেষ্ট পশ্চিমে ঢলে পড়বে, তখন দু’রাকাআত নামায পড়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করো। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, জুম‘আর নামায পড়লেও আল্লাহর নৈকট্য লাভ হয়।
হাদীসে আরো বলা হয়েছেঃ এ কাহিনী থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের আমলকে অসীলা বানাতে পারে; কিন্তু অপরের-নবী ও অলী-আল্লাহদের আমলের অসীলা গ্রহণের কোনো প্রমাণ এতে নেই।
বিশেষত বান্দার নিজের নেক আমলকে অসীলা বানিয়ে আল্লাহর নিকট দোআ করলে তাতে বান্দা আল্লাহর আরো নিকটতর হয়। আর এ কাজ কুরআন ও ইজমা উভয় দলীল মতেই শরীয়তসম্মত। এতে ব্যক্তির নফস পবিত্র হয় এবং আল্লাহর সন্তোষ লাভের যোগ্য হয়ে গড়ে ওঠে।
তৃতীয়ঃ নবী করীম(স)কে তাঁর নব্যুয়ত ও রিসালাতের ব্যাপারে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে ‘অসীলা’ বানান। তিনি যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন, তার প্রতি ঈমান এনে তাকে অসীলা ধরা। নবীর আদেশ নিষেধ মান্য করা এবং তাঁর সাহায্য করাকে অসীলা বানানো। তাঁর সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করা, তাঁর দাওয়াতকে জারী রাখা, সে বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করা প্রভৃতিও অসীলা হতে পারে। এসব জিনিসকে অসীলা বানানো মূল দ্বীনের মুতাবিক কাজ। কেননা এ অসীলা বানানো ঠিক নেক আমলকে অসীলা বানানোর অন্তর্ভূক্ত।
চতূর্থঃ নবীর জীবদ্দশায় তাঁর দো’আকে অসীলা বানানো, দো’আর কাজে তাঁকে শরীক করা, তাঁকে দিয়ে আল্লাহর নিকট দো’আ করানো এবং তাঁর ইন্তেকালের পরে সময়ের যে কোনো নেক লোকের দ্বারা দো’আ করানো বা দো’আয় তাঁকে শরীক করা এবং তাঁর দো’আকে অসীলা মনে করা।
হাদীসে এর দলীল এই যে, হযরত উমর(রা) একবার দূর্ভিক্ষের সময় হযরত আব্বাস(রা)কে অসীলাস্বরূপ শামিল করে দো’আ করেছিলেন এই বলেঃ
হে আল্লাহ, আমার পূর্বে আামাদের নবীকে তোমার নিকট অসীলা বানাতাম। তখন তুমি আমাদের পানি দিয়ে সিক্ত করেছিলে। এখন আমরা তোমার নিকট দো’আ কবুল হবার জন্য তাঁর চাচাকে অসীলা বানাচ্ছি। অতএব তুমি আমাদের পানি দিয়ে সিক্ত করে দাও।
এখানে সুস্পষ্ট যে, এতদুপলক্ষে যে সামষ্টিক দো’আ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে হযরত আব্বাসই দো’আকারীদের মধ্যে শরীক ও শামিল ছিলেন। তাঁকে দো’আয় অসীলা বানিয়েছিলেন, কেননা সাহাবীগণের মধ্যে তিনিই ছিলেন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর মর্যাদা ছিল সকলের ওপর। হযরত মুআবিয়া(রা) ও তাঁর সঙ্গীরা ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল জকরীকে অসীলা বানিয়েছিলেন তাঁর নেক আমল ও তাকওয়া পরহেযগারীর জন্য। তাঁদের সকলের পক্ষে রওযায়ে পাকে যাওয়া ও রাসূল(সা) কে অসীলা বানানো কঠিন ছিলনা কিন্তু বানাননি। কাজেই এরূপ দো’আর কোনো দোষ হতে পারেনা তওহীদী সুন্নাতের দৃষ্টিতে, তা হতে পারেনা কোনো বিদয়াত। আরো কথা এই যে, নবী করীম(স) এর ইন্তিকালের পরে সাহাবায়ে কিরাম স্বয়ং রাসূল(স) কে দো’আর ক্ষেত্রে অসীলা বানাননি। কেননা মৃত লোককে সে নবীই হোননা কেন অসীলা বানানোকে তাঁরা বিদয়াত ও শিরক মনে করতেন। হযরত উমরের দো’আয় রাসূলে করীম(স) কে অসীলা না বানিয়ে অসীলা বানানো হয়েছিল তাঁর চাচা আব্বাসকে-যিনি জীবিত থেকে দো’আয় উপস্থিত ছিলেন। আর তাঁকে অসীলা বানানো থেকেই এ কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। এ দো’আয় বড় বড় সাহাবীগণও উপস্থিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা কেউই এর প্রতিবাদ করেননি। তখনো যদি রাসূলকে অসীলা বানানো জায়েয হতো, তাহলে অন্যান্য সাহাবীরা তাঁকে তা-ই করতে বলতেন। কিন্তু তা কেউই বলেননি; বরং এ দো’আয় তাঁরা সকলেই শরীক হয়েছেন। আর রাসূলকেই যদি মৃত্যুর পর অসীলা বানানো বিদয়াত হয়ে থাকে, তাহলে অলী আল্লাহ কথিত মরে যাওয়া লোকদের কাউকে অসীলা বানানো তো একশ বার বিদয়াত হবে। কেননা মরে যাওয়ার পরও কাউকে বিশেষ ক্ষেত্রে দো’আয় অসীলা বানানোর মানে এই যে, তার সম্পর্কে ধারণা করা হচ্ছে যে, সে মরে গিয়েও এতদূর ক্ষমতা রাখে যে, সে বিপদগ্রস্ত লোকদের উদ্ধার করতে পারে বা উদ্ধার কাজে আল্লাহর সাথে শরীক হতে পারে। আর এরূপ আকীদাই তওহীদী শরীয়তের দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট শিরক।
হাদীসে বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন কঠিন দূর্ভিক্ষের সময় রাসূলে করীম(স) কে লক্ষ্য করে বলেছিলঃ আরবী (******)
-হে আল্লাহর রাসূল, ধন-মাল ধ্বংস হয়ে গেছে; পরিবার-পরিজন অভুক্ত হয়ে আছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য দো’আ করুন।
আল্লাহর কুরআন মজীদেও এর দলীল রয়েছে। আল্লাহ নিজেই ইরশাদ করেছেনঃ
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا [٤:٦٤]
-তারা যখন নিজেদের উপর জুলুম করেছিল তখন যদি তারা হে নবী! তোমার নিকট আসত এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো আর রাসূলও তাদের জন্যে ক্ষমা চাইতো, তাহলে নিশ্চয়ই তারা আ্লাহকে তওবা কবুলকারী ও দয়াবান হিসেবে পেত।(আন নিসাঃ৬৪)
এ আয়াতে লোকদের জন্য রাসূলের ক্ষমা চাওয়ার পূর্বে তাদের নিজেদের ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। তার অর্থ, তারা নিজেরা ক্ষমা না চাইলে তাদের জন্য রাসূলের ক্ষমা চাওয়ার কোনো মূল্য আল্লাহর নিকট নেই।
এ ধরনের অসীলা গ্রহণের ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই, থাকতে পারেনা। কিন্তু নবী করীম(স) এর মৃত্যুর পর তাঁর ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর নৈকট্যের জন্য অসীলা বানানো স্পষ্ট বিদয়াত।
পঞ্চমঃ আল্লাহর নিকট তাঁর নেক বান্দাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেখিয়ে দো’আ করা। যেমন হাদীসে হযরত আয়েশা(রা) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ আরবী(******)
-হে আমাদের আল্লাহ, যিনি জীবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের রব্ব।
এরূপ দো’আ করা জায়েয মনে করা হলেও অনেকেই এটাকে নাজায়েয বলেছেন।
ষষ্ঠঃ নবী করীম(স)এর প্রতি দুরূদ পাঠানোকে অসীলা বানানো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা(রা) হতে বর্ণিত হয়েছে-নবী করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(*******)
-আল্লাহর নিকট যার কোনো প্রয়োজন দেখা দিবে কিংবা কোনো মানুষের নিকট, সে যেন খুব ভালো করে অযূ করে এবং দু’রাকাআত নামায পড়ে, আল্লাহর ভালো প্রশংসা করে এবং নবীর প্রতি দুরূদ পাঠ করে, তারপর বলে আল্লাহ ধৈর্য্শীল ও অনুগ্রহ সম্পন্ন, তিনি ছাড়া কেউই মা‘বুদ নেই।
মোট কথা আল্লাহর নিকট দো’আ করার এসবই হলো ইসলাম ও সুন্নাত মোতাবিক নিয়ম। এছাড়া অন্য কোনো নিয়মে ও পন্থায় দো’আ করা ঈমানদার লোকদের পক্ষে জায়েয নয়।
সপ্তমঃ এরূপ দো’আ করাঃ
হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট তোমার অমুক নেক বান্দার দোহাই দিচ্ছি বা তার সম্মানের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট দো’আ করছি।
কিন্তু এ ধরনের দো’আ শরীয়তে আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। ইজ্জ ইবনে আবদুস সালাম ও তাঁর অনুসারীদের মতে কেবল নবীর নামেই এরূপ দোহাই দেয়া জায়েয হতে পারে, অন্য কারো নামে জায়েয নয়। হাম্বলী মাযহাবে এরূপ দো’আ করা মাকরূহ তাহরীম। ‘কুদূরী’ প্রমুখ হানাফী মাযহাবের ফকীহগণ ইমাম আবু ইউসুফ হতে বর্ণনা করেছেনঃ
ইমাম আবু হানীফা(রা)বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট, আল্লাহর নামে ছাড়া অন্য কারো দোহাই দিয়ে দো’আ করা কারো পক্ষেই উচিত হতে পারেনা।
‘হে আল্লাহ, তোমার আরশের মর্যাদা বন্ধনের দোহাই দিয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করি; অমুকের দোহাইতে দো’আ করি; তোমার নবী ও রাসূলগণের দোহাই দিয়ে দো’আ করি বা তোমার মহান ঘরের দোহাই দিয়ে দো’আ করি’, এরূপ বলে দো’আ করাকেও আমি মাকরূহ মনে করি।
ইমাম আবু হানীফা(রহ) হতে তাতারখানিয়া এবং তাঁর থেকে কিতাবে আল আলায়ী উদ্ধৃত করে বলেছেনঃ আল্লাহু সুবহানাহুর নিকট তাঁর নিজের দোহাই ছাড়া অপর কারো দোহাই দিয়ে(অসীলা বানিয়ে)দো’আ করা কিছুতেই উচিত নয়।
ইমাম বদলজী বলেছেনঃ আল্লাহর নিকট আল্লাহ ছাড়া অপর কারো অসীলায় দো’আ করা মাকরূহ। আর ‘হে আল্লাহ তোমার নিকট তোমার ফেরেশতা ও নবীগণের অসীলায় প্রার্থনা করি’ বলবেনা কখনো।
হানাফী মাযহাবের সব কিতাবেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী-রাসূল ও অলী-পীর বা আল্লাহর ঘর ইত্যাদিকে অসীলা করে দো’আ করা মাকরূহে তাহরীম। আর জাহান্নামের আযাবের দিক দিয়ে মাকরূহে তাহরীম হারামের সমান্।
আল্লাহর নিকট অপর কারো দোহাই দিয়ে দো’আ করা বা অপর কাউকে অসীলা বানানো হারাম কেন? হারাম এজন্য যে- মাখলুকের মধ্যে কারোই কোনো হক্ নেই সৃষ্টিকর্তার ওপর। তাই এই দোহাই চলতে পারেনা। দোহাই দিলে বা কাউকে অসীলা বানালে তা হবে অর্থহীন।কাজেই মুসলিম সমাজে এরূপ করা সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত।
মক্কার কাফির মুশরিকগণ যে সব মূর্তি দেব-দেবী উপাসনা করতো আল্লাহ আছেন-তিনি এক ও একক-একথা জানা থাকা এবং তার স্বীকৃত দেয়া সত্ত্বেও। তাদেরও তো মূল লক্ষ্য সেগুলোর পূজা-উপাসনা ইবাদত ছিলনা, মূল লক্ষ্য ছিল একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভ, আল্লাহর নিকট ঘনিষ্ট হওয়া, উচ্চতর মর্যাদা পাওয়া। মূর্তি ও দেব-দেবীর পূজা-উপাসনাকে তারা সেই লক্ষ্যে পৌছার মাধ্যমে বা অসীলা রূপেইতো গ্রহণ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের এ কাজকে আল্লাহ শিরক বলেছেন, তাদেরকে হেদায়াতবঞ্চিত ও মিথ্যাবাদী কাফির বলে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটিতে সে কথাই বলা হয়েছেঃ
أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ [٣٩:٣]
(আঝ ঝুমারঃ৩)
-জেনে রাখো, আল্লাহর জন্য তো খালিস অবিমিশ্র আনুগত্য হতে হবে। আর যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করে এই বিশ্বাস পোষণের দাবি নিয়ে যে, আমরা তো আসলে ওদের ইবাদত করিনা- ওদের প্রতি যা কিছু করি, তা তো এই উদ্দেশ্যে যে, ওরাই আমাদেরকে আল্লাহর অতি ঘনিষ্ট নৈকট্যে পৌছে দেবে(তাদের এই কথা অসত্য, অযথার্থ) আল্লাহই তাদের পারস্পরিক মত-পার্থক্যের ব্যাপারাদির চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিবেন। মনে রেখো আল্লাহ কখনোই মিথ্যাবাদী চরম মাত্রার কাফিরকে হেদায়াত দেননা।
এ আয়াতের আলোকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে, সেকালের আরব জনগণ আল্লাহকে পাওয়ার, তাঁর নৈকট্য অর্জনের লক্ষৌ মূর্তি ও দেব-দেবীর প্রতি যে আচরণ করতো, আজকের দিনের সে প্রকৃতির লোক আল্লাহর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে পীর-দরবেশদের প্রতি ঠিক সেই আচরণই গ্রহণ করেছে। এ দু’টির মধ্যে মৌলিক কোনেই পার্থক্য নেই। তাহলে আরবদের সেই কাজ যদি শিরক গণ্য হয়ে থাকে এবং তাদের মৌলিক দাবিকে আল্লাহ অসত্য ধরে নিয়ে তাদের স্পষ্ট ভাষায় মিথ্যাবাদী বলে থাকেন। তাহলে আজকের দিনের এই অসীলা গ্রহণকারী লোকেরা আল্লাহর নিকট মিথাবাদী আখ্যায়িত হবেনা কেন? আর তাদেরকে যদি কেবল এজন্যই কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, তাহলে আজকের দিনের এইসব বড় বড় অসীলা গ্রহণকারী লোকেরা ‘কাফির’ বলে অভিহিত হবেনা কেন?
আল্লাহর নিকটি কি সেকাল ও একাল এবং আরব ও এদেশের লোকদের মধ্যে কোনোরূপ পার্থক্য বা তারতম্য আছে?
অত্যন্ত খারাপ কথা, যা তারা বলছে বা মনে করছে।
পীর-মুরীদীর বিদয়াত
ইসলামের সুন্নাতের আদর্শে আর একটি মারাত্মক ধরনের বিদয়াত দেখা দিয়েছে- তা হলো পীর-মুরীদী। পীর-মুরীদীর যে ‘সিলসিলা’ বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত। এ জিনিস রাসূলে করীম(স) এর যুগে ছিলনা, তিনি পীর-মুরীদী করেননি কখনো। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর আর না ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরীদ। সাহাবায়ে কিরামও এ পীর-মুরীদী করেননি কখনো। তাঁদের কেউই কারো পীর ছিলেননা এবং কেউ ছিলেননা তাঁদের মুরীদ। তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীন এর যুগেও এ পীর-মুরীদীর নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়না।
শুধু তা-ই নয়। কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরীদীর কোনো দলীলের সন্ধান পাওয়া যাবেনা। অথচ বর্তমানে এক শ্রেণীর পীর নামের কথিত জাহেল লোক ও তাদের ততোধিক জাহেল মুরীদ এ পীর-মুরীদীকে দ্বীন ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অজ্ঞা মূর্খ লোকদের মুরীদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। যদিও তাতে কোনো মূলধন বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়নি এবং বিপুল লাভজনক ব্যবসায়ে সঞ্চিত মূলধনে কোনো আয়করও দিতে হয়না। আর সঞ্চিত নগদ বিপুল অর্থের যাকাতও দেয়া হয়না কখনো।
শরীয়ত মারিফাত
এ পর্যায়ে সবচেয়ে মৌলিক বিদয়াত হলো শরীয়ত ও তরীকতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র জিনিস মনে করা। এতোদূর পতন ঘটেছে যে, শরীয়তকে ‘ইলমে জাহের’ এবং ‘তরিকত’ বা ‘মারেফত’ কে ইলমে বাতেন বলে অভিহিত করে দ্বীন-ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল তরীকতপন্থী লোক বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই হলো তরীকত বা মারিফত, আর এ-ই হাকীকত। এ হাকীকত কেউ যদি লাভ করতে পারলো, তাহলে তাকে শরীয়ত পালন করতে হয়না, সে তো আল্লাহকে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শরীয়তের আলিম এক আর মারিফত বা তরীকতের আলিম অন্য। এই তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। ধারণা প্রচার করা হয় যে, কেউ যদি শরীয়তের আলিম হয় আর সে তরীয়তের ইলম না জানে-কোনো পীরের নিকট মুরীদ না হয়-তবে সে ফাসিক।
তাসাউফকে বলা হয় সাধারণত মারিফাত। প্রখ্যাত অলী-আল্লাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী এ মারিফাত এর মূল্যহীনতা আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেনঃ
মারিফাতের তুলনায় ইলম অনেক উন্নত, সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ নিজে ইলম এর নামে অভিহিত হয়েছেন, মারিফাতের নামে নয়। আর তিনি বলেছেন-যারা ইলম লাভ করেছেন, তাদেরই উচ্চ মর্যাদা। এছাড়া তিনি যখন নবী করীম(স) কে সম্বোধন করলেন, সম্বোধন করলেন সর্বোত্তম, অধিকতর ব্যাপক কল্যাণময় ও পূর্ণাঙ্গ এক গুণ উল্লেখ করে।
আর বলেছেনঃ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ
-‘তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনোই মা’বুদ নেই’।
কিংবাঃ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ
-অতঃপর জানবে যে, এ লোকেরা নিজেদের কামনা বাসনাকে অনুসরণ করে চলেছে। আর যারাই নিজেদের কামনা বাসনাকে অনুসরণ করে চলে, তাদের চাইতে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে।
পীর-মুরীদী সম্পর্কে এ আয়াত খুবই প্রযোজ্য। কিন্তু ‘মারিফাত হাসিল করো’ একথা কোথাও বলেননি। কেননা মানুষ একটা জিনিসকে চিনতে পারে; কিন্তু তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হয়না । আর যখন সে জিনিস সম্পর্কে ইলম হলো, সম্যকভাবে সে সম্পর্কে জানতে পারলো, তখন তাকে চিনতেও পারলো।
হযরত জুনাইদের একথার সারমর্ম হলো এই যে, মারিফাতের চাইতে ‘ইলম’ বড়। অতএব আল্লাহর মারিফাত নয়, আল্লাহ সম্পর্কে ইলম হাসিল করতে হবে। ‘ইলম’ হাসিল হলেই ‘মারিফাত’ লাভ হতে পারে। আর যার ইলম নেই, সে মারিফাতও পেতে পারেনা। এ ইলম-এর একমাত্র উৎস হলো আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের হাদীস। কুরআন-হাদীসের মাধ্যমেই রাসূলকে জানতে হবে এবং আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার ফলেই মানুষ পারে আল্লাহকে জানতে ও চিনতে-অন্য কোনো উপায়ে নয়।
কিন্তু তাসাউফবাদীরা এ মারিফাতকে কেন্দ্র করে গোলকধাঁধার এক প্রাসাদ রচনা করেছে। তাদের মতে মারিফাত বা ইলমে বাতেন এক সুসংবদ্ধ ও সুশৃংখলিত কর্মপন্থা, ইসলামী শরীয়ত থেকে তা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জিনিস। তাদের মতে রাসূলে করীম(স) তাঁর এই মারিফাত কোনো কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর অনেককে দেননি। তারা আরো মনে করেন, ইলমে বাতেন হযরত আলী(রা) হতে হাসান বসরী পর্য্ন্ত পৌছেছে। আর তাঁরই থেকে সীনায় সীনায় এ জিনিস চলে এসেছে এ কালের পীরদের পর্য্ন্ত।
এ সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা রাসূলে করীম(স) এ জিনিস কাউকেই শিখিয়ে যাননি, যা এখনকার পীর তার মুরীদদের শিখিয়ে থাকে। তিনি এরূপ করতে কাউকে বলেও যাননি। কোনো দরকারী ইলম তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে শিখিয়ে যাবেন আর অন্য সাহাবীদেরকে বঞ্চিত করবেন-এরূপ তরা নবী করীমের নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাছাড়া হাসান বসরী(র) হযরত আলী(রা) এর সাক্ষাৎ পাননি, তাঁর নিকট থেকে মারিফাত এর শিক্ষা লাভ করা ও খিলাফত এর ‘খিরকা’ লাভ করাতো দূরের কথা।
আল্লামা মুল্লা আলী আল কারী আল্লামা ইবনে হাযার আল আসকালানীর উদ্বৃতি দিয়ে লিখেছেনঃ
-সূফী ও মারিফাতপন্থীরা যেসব তরীকা ও নিয়ম-নীতি প্রমাণ করতে চায়, প্রমাণ হওয়ার মতো কোন জিনিসই নয়। সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোনো প্রকার হাদীসেই এ কথা বলা হয়নি যে, নবী করীম(স) তাঁর কোনো সাহাবীকে তাসাউফপন্থীদের প্রচলিত ধরনের খিলাফতের ‘খিরকা’(বিশেষ ধরনের জামা বা পোষাক)পড়িয়ে দিয়েছেন। সেসব করতে তিনি কাউকে হুকুমও করেননি। এ নিয়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয় তা সবই সুস্পষ্টরূপে বাতিল। তাছাড়া হযরত আলী(রা) হাসান বসরীকে ‘খিরকা’ পরিয়েছেন(মারিফাতের খিলাফত দিয়েছেন) বলে যে দাবি করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া মিথ্যা কথা। কেননা হাদীসের ইমামগণ প্রমাণ করতে পারেননি যে, হাসান বসরী হযরত আলীর নিকট হতে কিছু শুনেছেন-তাঁকে হযরত আলীর ‘খিরকা’ পরিয়ে দেয়াতো দূরের কথা।
মুল্লা আলী কারী আরও লিখেছেনঃ
-এমনিভাবে তাসাউফপন্থীদের মধ্যে মুরীদকে তালকীন করা-রূহানী ফায়েজ দেয়ার যে ব্যাপারটি চালু করেছে, তাকে হাসান বসরীর সূত্রে হযরত আলীর সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়ারও শরীয়তে কোনোই ভিত্তি নেই।
বস্তুত তাসাউফপন্থী লোকদের এ একটি অমূলক ধারণামাত্র। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী এ সম্পর্কে লিখেছেনঃ
-সূফী বা তাসাউফপন্থীদের কথা যে, এসব তরীকতের সিলসিলা হযরত আলী (রা) পর্য্ন্ত পৌছে গেছে-এর জবাব এই যে, এটি পীর মুরীদের মুখে ধ্বনিত ও প্রসিদ্ধ একটি কথা। কিন্তু অনুসন্ধান করে জানা গেছে যে, এ কথার মূলে কোনোই ভিত্তি ও সত্য নেই।
এ পর্যায়ে তিনি আরো লিখেছেন যে, প্রসিদ্ধ দু রকমের হয়ে থাকে। এক রকমের প্রসিদ্ধ কথা যা সকল জ্ঞানী মনীষীদের নিকটই প্রসিদ্ধ। আর এক প্রকারের প্রসিদ্ধ কথা হলো, যা কেবল মাত্র একদল লোকের নিকট প্রসিদ্ধ। হযরত আলীর নিকট হতে মারিফাতের ইলম শুরু এ কথাটা কেবল এই সূফী পীরদের নিকটই প্রসিদ্ধ; অন্য কারোরই এ কথা জানা নেই। আসলে এ কথাটাই বাতিল। কিংবা বলা যায়, একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। শেষের জমানার লোকেরা এটাকে রচনা করেছে ও কবুল করেছে। আর এ ধরনের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। মারিফাতের যেসব তরীকা, মুরাকাবা-মুশাহিদা ও যিকির এখনকার পীরেরা তাদের মুরীদদের শিখিয়ে থাকে তা যে রাসূলে করীম(স) বা সাহাবায়ে কিরামের জামানায় ছিলনা, শাহ দেহলভী সে কথাও ঘোষণা করেছেন।
তিনি বলেছেনঃ
-জ্ঞাতব্য বিষয় হচ্ছে, সূফী পীরদের তাসাউফের রীতিনীতি সাহাবা ও তাবেয়ীদের যুগে ছিলনা। উপায় উপার্জন ত্যাগ করা, তালিযুক্ত পোশাক পরা, বিয়ে ঘর সংসার না করা ও খানকার মধ্যে বসে থাকা সেকালে প্রচলিত ছিলনা।
মারিফাত পন্থীদের বিশ্বাস, মারিফাতের এ কর্মপন্থা পুরোপুরি অনুসরণ করে চললেই পথিক-সালেক-নিগূঢ় তত্ত্ব (হাকীকত) কে জানতে পারে। আর শেষ পর্য্ন্ত এ মারিফাত এই তত্ত্ব লাভ করে যে, বাহ্য দৃশ্যমান এ জিনিসগুলো নির্ধারণ হিসেবে যদিও আল্লাহ হতে ভিন্ন জিনিস; কিন্তু মূল ব্যাপারের দৃষ্টিতে তা-ই হলো মূল আল্লাহ। আল্লাহ ও বাহ্যিক জিনিসগুলো মধ্যে যে পার্থক্য মনে হচ্ছে, তা হলো আমাদের ভ্রম। অর্থাৎ বাইরে দৃশ্যমান বর্তমান জিনিসের বৈচিত্র ও বিপুলতা সৃষ্টির ধোঁকা বা মায়া। অন্য কথায় বলা চলে, এ কর্মপন্থা অনুসরণ করলে মানুষ শেষ পর্য্ন্ত দৃষ্টি বিভ্রম হতে মুক্তি পেতে পারে। আর তখন মনে হয়, এক আল্লাহকে-ই এই বিপুলতার রূপে দেখতে পাচ্ছি। এ লোকদের মতে এ-ই হচ্ছে তওহীদের মারিফাত।
কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, এসব তত্ত্বকথাই হচ্ছে বেদ-উপনিষদের দর্শন-বেদান্তবাদ। আর এ দর্শনের সঠিক পরিচয় হলো অদ্বৈতবাদ। মানে, আল্লাহ ও জগত কিংবা স্রষ্টা ও সৃষ্টি আসলে এক ও অভিন্ন। যা স্রষ্টি তাই স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি। অদ্বৈতবাদী আদর্শের এই হলো গোড়ার কথা। আর তা-ই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব, যা বর্তমান পীর-মুরীদী ধারায় ইসলামের মারিফাত নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং এ যে সুস্পষ্ট শিরক তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই।
বস্তুত ইসলাম এক সর্বাত্বক দ্বীন। এতে এক ব্যক্তির মন হৃদয় অন্তর একান্তভাবে আল্লাহর জন্য খালিস করে দেয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের সর্বদিক ও বিভাগ, সব কাজ ও বিষয় সম্পর্কেই বিস্তারিত বিধান দেয়া হয়েছে। তাতে শরীয়ত ও তরীকত কোনো বিচ্ছিন্ন,স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিপরীত জিনিস নয়। যেমন দুই বিপরীত জিনিস নয় ব্যক্তির দেহ ও মন। দেহ ও মনের সমন্বয়েই যেমন মানুষ, তেমনি শরীয়ত-তরীকত বা মারিফত সবই একই জিনিসের এদিক ওদিক- বাহির ও ভিতর এবং একই কুরআন হাদীস হতে উৎসারিত।
কুরআন থেকেই পাওয়া যায় আল্লাহর সঠিক ও সার্বিক পরিচয়, তাঁর জাত ও সিফাত সম্পর্কিত নাম এবং তাঁর কুদরতের বিচিত্র বর্ণনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে। কুরআন থেকেই জানা যায় আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার, তাঁর বন্দেগী কবুল করার এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করার শরীয়তী বিধান। এগুলোর নিগুঢ় তত্ত্ব, মাহাত্ম্য ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্ যখন মানুষের মর্মমূলে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনি তা হয় তরীকত বা মারিফাত। মানুষ যখন শরীয়ত মোতাবিক আমল করে, তখন হয় শরীয়তের আমল। আর এই আমল যদি ইখলাস, আল্লাহর ভয় ও আল্লাহ ভালোবাসায় সিক্ত ও সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, আল্লাহকে সব সময় হাজির নাজির অনুভব করতে পারে, তখনি তা হয় মারিফাত বা তরীকত। ইলম ও আমলের মাঝে যদ্দিন দ্বন্ধ থাকবে মনে, ততোদিন তা হবে শরীয়ত পর্যায়ের ব্যাপার। আর যখন এ দ্বন্ধে মন অন্তর মুতমায়িন হবে, পুরোপুরিভাবে আত্মসমর্পণ করবে আমলের নিকট, আমলময় হয়ে উঠবে জীবন, তখন তরীকত বা মারিফাত অর্জিত হলো বলা যাবে। শায়খ আবদুল মুহাদ্দিসে দেহলভী লিখেছেনঃ “হাকীকতকে শরীয়ত থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে করে নিওনা।” আসলে হাকীকত শরীয়তেরই আসল জাওহার ও মূল প্রাণবস্তু। আর শরীয়ত হচ্ছে হাকীকতেরই বাহ্য রূপ ও অবয়ব।
শরীয়ত হচ্ছে এই যে, আল্লাহ ও রাসূলে করীম(স) যা কিছু বলেছেন তা বিশ্বাস করতে হবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর ‘হাকীকত’ হচ্ছে এই যে যেসব বিষয়ে ইয়াকীন রয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাসটা যেন সর্বাধিক দৃঢ় ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।
শায়খ মহি উদ্দিন আবদুল কাদির জিলানি কুদ্দেশা সিররুহুশ বলেছেনঃ ‘যে হাকীকত শরীয়ত প্রত্যাখ্যান করবে, তাই ‘জান্দাকা’-“দ্বীন বিরোধিতা”- এ বাক্যের অর্থ হলো, কেউ যদি এমন কাশফ লাভ করে, যা দ্বীন ও শরীয়ত মোতাবিক নয়, আর সে যদি তাকেই নিজের আকীদা বানিয়ে নেয়, তাহলে সে কাফির ও জিন্দীক হয়ে যাবে।
আবু সালমান দুররানী বলেনঃ “অনেক সময় সলুক-পথের ‘অজুদ’ ও শোকর এর কোনো তত্ত্ব পূর্ণ সৌন্দর্য্ মন্ডিত হয়ে আমার সামনে এসে উপস্থিত হয়; কিন্তু আমি তা কবুল করিনা। আমি বলি দুজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য স্বাক্ষী তোমার সত্যতা ও যথার্থতা সম্পর্কে যতক্ষণ না সাক্ষ্য দেবে, ততক্ষণ আমি তোমাকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারিনে। আর এ দুজন বিশ্বস্ত সাক্ষী কে?…তাহলো আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাত।”(শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী, মকতুব নং ১৩)
বস্তুত এ দুয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই, নেই কোনো বিরোধ বা দ্বন্ধ, নেই কোনোরূপ দ্বৈততা। বরং সত্য কথা এই যে, এখানে তরীকত বা মারিফাতের যে পরিচয় দেয়া হলো, তা-ই হলো প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলাম। এই অখন্ড ইসলামই আল্লাহ তা‘আলা নাযিল করেছেন, কুরআন এই দ্বীন ইসলামই পেশ করেছে, নবী করীম(স) তাঁর জীবন, চরিত্র, আমল ও যাবতীয় কাজের মাধ্যমে এই অবিচ্ছিন্ন দ্বীনকেই দুনিয়ার সামনে উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন এবং সম্পূর্ণ জিনিসেরই নাম হলো কুরআনের ভাষায় শরীয়ত। কাজেই না এ শরীয়তকে অস্বীকার করতে পারে কোনো মুসলমান না এ তরীকত বা মারিফাতকে। তাসাউফের বিশেষজ্ঞ মনীষীদের মতে তাসাউফ হলোঃ উত্তম চরিত্রই তাসাউফ। কিন্তু উত্তরকালে শরীয়ত ও তরীকত দুটি বিচ্ছিন্ন জিনিস হয়ে গিয়ে দুই বিপরীত ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। শরীয়ততো কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে অবিকৃত অপরিবর্তিত রয়েছে-থাকবে চিরদিন, কিন্তু তরীকত আর মারিফাতের নামে যে অলিখিত ও ‘সীনা-বা- সীনা’ চলে আসা স্বতন্ত্র জিনিসটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, তাতে উত্তম নির্মল চরিত্রের কোনো গুরুত্বই থাকলোনা; তাতে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠল নানাবিধ শিরকের আবর্জনা। আর এ ক্ষেত্রে এ-ই হলো বিদয়াত।
মারিফাত বা তরীকত শরীয়ত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারায় বইতে লাগলো, তখন তাতে এসে জমলো এমন সব জিনিস যা শরীয়ত তথা কুরআন ও সুন্নাত থেকে গৃহীত নয়। তাতে শামিল হলো গ্রীক দর্শন, প্রাচীন মিশরীয় দর্শন এবং ভারতীয় বেদান্ত দর্শন। এ সবের সমন্বয়ে মারিফাত বা তরীকতের এই স্বতন্ত্র ইলম গড়ে উঠল; যার নাম রাখা হলো ‘ইলমে তাসাউফ’ বা শুধু তাসাউফ। অথচ পূর্বে কোনো যুগেই এই নামে কোনো ইলম ইসলামে ছিলনা, তাই মুসলমানরা জানতো না যে, ইসলামে শরীয়ত ও মারিফাতের দ্বৈততার ধারণা অতি বড় বিদয়াত। যেমন অতি বড় বিদয়াত হচ্ছে ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে দুই বিচ্ছিন্ন জিনিস মনে করা। ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন ও পারস্পরিক সম্পর্কহীন করে রাজনীতির ক্ষেত্রে ফাসিক-কাফির-জালিম লোকদের কর্তৃত্ব কায়েম করা হয়েছে। আর দ্বীনকে সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে শুধু নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাতের মধ্যে। অনুরূপভাবে শরীয়ত ও তরীকতকে বিচ্ছিন্ন করে সৃষ্টি হয়েছে এক শ্রেণীর জাহিল পীর। মুসলিম সমাজে চলছে পীরবাদ নামে এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মুশরিকী প্রতিষ্ঠান। এ পীরবাদ চিরদিনই ফাসিক-ফাজির-জালিম শাসকদের- রাজা বাদশাহদের – আশ্রয়ে লালিত পালিত ও শাখায় পাতায় সুশোভিত হয়েছে। সাধারণত পীরেরা চিরদিনই এ ধরনের শাসকদের সমর্থন দিয়েছে। তারা কোনো দিনই জালিম ফাসিক শাসকদের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করেনি। বরং সব সময়ই “আল্লাহ আপ কা হায়াত দারাজ করে” বলে দুহাত তুলে তাদের জন্য দো’আ করেছে।
তাসাউফের গতি ইসলামের বিপরীত দিকে
ইসলামী আধ্যাত্মবাদের মূল উৎস যদিও শুরুতে কুরআন ও সুন্নাতই ছিল; কিন্তু উত্তরকালে বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে গিয়ে তা তাসাউফের নাম ধারণ করে এবং তার আদর্শ ও লক্ষ্য কুরআন সুন্নাতের আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। দু’টোর তুলনামূলক অধ্যয়নে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তাসাউফের আদর্শের ক্ষেত্রে এসে ইসলামের কোনো কোনো মৌল আদর্শ ও লক্ষ্য ম্লান এবং উপেক্ষিত হয়ে পড়েছে, আর কোনো কোনো খুঁটিনাটি বিষয় মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব লাভ করেছে। কোনো কোনো ভাবধারা তাসাউফে এসে অধিক তীব্র ও প্রকট এবং কোনো কোনোটি অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও কম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে। কোনো কোনো ইসলামী ধারণা তাসাউফের ক্ষেত্রে এসে সম্পূর্ণ নতুন অর্থ ধারণ করেছে। আর কোনো কোনোটির অর্থ ও তাৎপর্যে আংশিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। আবার ইসলামের অনেকগুলো জরুরী দিককে তাসাউফ সম্পূর্ণ উপেক্ষাই করেছে এবং কোনো কোনো দিক দিয়ে বাইরের অনেক জিনিসই শামিল হয়ে পড়েছে তাসাউফের মধ্যে।
এখানে এসব বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার অবকাশ না থাকলেও সংক্ষেপে বিষয়টি ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করছি-যেন কেউ ধারণা না করে বসেন যে, তাসাউফের প্রতি শত্রুতা পোষণের কারণেই এসব কথা বলা হচ্ছে। কেননা তা আদৌ সত্য নয়। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত পেশ করা হচ্ছে।
ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে ‘আমল’ ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তাসাউফে এসে তার ক্ষেত্র হয়ে যায় একেবারে সংকীর্ণ, সীমাবদ্ধ। মানুষের সামাজিক জীবন, সামাজিক ব্যবস্থা, প্রয়োজন জটিলতার সুষ্ঠ ও কার্য্কর সমাধান বের করা ইসলামের লক্ষ্য; কিন্তু এসব জিনিসের প্রতি তাসাউফপন্থীদের কোনো আগ্রহ ও কৌতুহলই নেই। এসব জিনিস তাদের তৎপরতার সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত। ইসলামের প্রাথমিককালে ‘ফিকির’, ‘জযবা’ ও ‘আমল’- এ তিনটির মাঝে পরস্পর গভীর সম্পর্ক ও পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষিত ছিল; কিন্তু তাসাউফপন্থীরা আবেগ ও কলবী-কাইফীয়াতের উপর এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করে যে, তদ্দরুণ আমল- বিশেষ করে চিন্তা বা ফিকির এর গুরুত্ব কম হয়ে গেছে বা আদৌ থাকেণি। আল্লাহর ভালোবাসা দ্বীন ইসলামের মৌল ভাবধারা। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ভালবাসা ‘আমল’ থেকে বিচ্ছিন্ন ও আলাদা কোনো জিনিস ছিলনা, তেমন কিছু হওয়ারও স্বীকৃতি পায়নি কোনো দিন বরং আল্লাহর ভালোবাসা ছিল এমন এক প্রাণ উদ্দীপক ভাবধারা, যা সেসব আমলের মধ্যেই প্রবাহিত ও সঞ্চারিত হয়েছিল, যা জমিনের বুকে আল্লাহর খলীফা হওয়ার কারণে বাস্তবায়িত করা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্ ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তাসাউফপন্থীদের আদর্শ ও লক্ষ্য আমল-এর ক্ষেত্রে কেবল সংকীর্ণই হয়ে যায়নি, ‘আমলে’র সাথে ‘মুহাব্বাত’ জোরদার করনের জন্য তাসাউফপন্থীরা নানা উপায় অবলম্বন করেছে। যেমনঃ গানের আসর এবং সঙ্গীত চর্চা ইত্যাদির দ্বারা ঈমান মজবুত হয় বলে মনে করা হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক যুকে ‘আল্লাহর মুহাব্বত’ মানুষের দ্বারা এই কাজ করিয়েছিল-তাসাউফপন্থীরা এর প্রমাণ দিতে পারবে কি?
‘যিকির’ কেও এখানে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মাথা নিচু করে বসে মুখে ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ কিংবা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কলেমা নিম্নস্বরে বা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করাকেই যিকির বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং তা করলেই আল্লাহর যিকির করার কর্তব্য আদায় হয়ে গেল বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু এ যে কতো সংকীর্ণ ধারণা এবং ইসলামী আদর্শের একটি মৌল বিষয়কে বিকৃত করা, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। কুরআন মজীদে আল্লাহর যিকির করার স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সূরা আল বাকারায় বলা হয়েছেঃ
فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ [٢:١٥٢]
- তোমরা আমায় স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো, তোমরা আমার শোকর করো, আমার অকৃতজ্ঞতা করো না।
আল্লামা রাগেব ইফসানী ‘যিকির’ শব্দের অর্থ লিখেছেনঃ
*******
যিকির হচ্ছে মনের এমন একটা অবস্থা যা দ্বারা মানুষ যে জ্ঞান সংরক্ষণ করতে চায় তা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়। ইয়াদ রাখা বা স্মরণে রাখা বা সংরক্ষণ যেমন, এ-ও তেমনি।
অপর অর্থে বলা হয়েছে ‘যিকির’ অর্থ মনে কোনো জিনিসের উপস্থিতি। তিনি আরও লিখেছেন-‘যিকির’ দু’ভাবে সম্ভব-একটি অন্তরের যিকির, অপরটি মুখের যিকির। তার ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করা ও ভুলে না গিয়ে স্মরণে রাখা, সবসময় স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখা, সংরক্ষণ করা, এই উভয় অবস্থায়ই যিকির শব্দটি প্রযোজ্য।
আল্লামা কুরতবী লিখেছেনঃ কোনো জিনিস সম্পর্কে দিলের সদা সচেতন ও অবহিত হওয়া, সে বিষয়ে মনের জাগৃতি।
আর আয়াতটির তরজমা করেছেনঃ
তোমরা আমার আনুগত্য করে আমাকে স্মরণে রাখো। তাহলে আমি তোমাদের স্মরণ রাখবো সওয়াব দিয়ে, গুনাহ মাফ করে।
অন্য কথায় যিকির হচ্ছে আল্লাহকে স্মরণ রেখে তাঁর ইবাদত করা, আনুগত্য ও হুকুম পালন করা মনের আগ্রহ সহকারে।
অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ[٨:٢]
–প্রকৃত মুমিন তারাই, আল্লাহর উল্লেখ বা স্মরণ হলেই যাদের দিল কেঁপে উঠে।
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ অতএব হে মুমিনেরা-আল্লাহর নির্ধারিত ফরযসমূহ যথাযথভাবে পালন করো।
পরে এ তাফসীরকার লিখেছেনঃ মুমিনের-আল্লাহর যিকির হলেই যার দিল কেঁপে উঠে-কর্তব্য হচ্ছে সে আল্লাহকে ভয় করবে এবং তার আদেশসমূহ পালন করবে ও নিষেধসমূহ তরক করে চলবে।
এ আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, আল্লাহর যিকির করতে বলার অর্থ আল্লাহর ইবাদত করা, সর্বক্ষণ তাঁকে মেনে চলা, তাঁকেই নিজের একমাত্র মা’বুদ মনে করা এবং নিজেকে মনে করা একমাত্র তাঁরই দাস এবং এ বিষয়ে কখনোই গাফিল হয়ে না যাওয়া, সব সময়ই আল্লাহকে স্মরণ রাখা, কোনো সময়ই তাঁকে ভুলে না যাওয়া।
তাছাড়া কুরআনের ঘোষণা অনুযায়ী ‘যিকির’ ই একমাত্র করণীয় কাজ নয়। সেই সঙ্গে ‘ফিকির’ ও অপরিহার্য্। এই যিকির ও ফিকির-উভয়ের গুরুত্ব ও সার্বক্ষণিকতা বোঝাতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেনঃ
الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ[٣:١٩١]
-যারাই আল্লাহর যিকির করে দাঁড়ানো, বসা ও পার্শ্ব নির্ভর শয়ন অবস্থায় এবং নভোমন্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা ভাবনা গবেষণা করে (বস্তুত তারাই বুদ্ধিমান লোক।)
(আল ইমরানঃ১৯১)
আয়াতটিতে আল্লাহর যিকির করতে বলা হয়েছে বসা, দাঁড়ানো ও শয়ন অবস্থায় অর্থাৎ সর্বাবস্থায়। কেননা এই তিনটি অবস্থার মধ্যে যে কোনো একটি অবস্থায়ই মানুষ থাকে। কোনো সময়ই এই তিনটির একটি ভিন্ন অন্য কোনো অবস্থায়ই তার হয়না, হয় সে বসে আছে, নয় দাঁড়িয়ে আছে কিংবা শুয়ে আছে। অতএব সর্বাবস্থায়ই আল্লাহর যিকির করতে হবে। অর্থাৎ স্মরণে রাখতে হবে, কোনো অবস্থায়ই আল্লাহকে ভুলে যাওয়া চলবেনা।
দ্বিতীয়ত, আয়াতটিতে শুধু যিকির এ কথাই বলা হয়নি, সেই সঙ্গে ফিকির এর কথাও বলা হয়েছে। আর ইমাম রাগেব এর ভাষায় ফিকির বলতে বোঝায়ঃ কোনো বিষয়ে জানবার জন্য নিয়োজিত শক্তি। বলা হয়েছে এ শব্দটির আসল অর্থ-বিষয়াদি ঘর্ষণ করা তার নিগুঢ় তত্ত্ব ও গভীর সত্য জানবার উদ্দেশ্য।
এক কথায় নিছকই যিকির আল্লাহর কাম্য নয়, বুদ্ধিমান লোকেরও কর্ম নয়। সেই সঙ্গে ফিকিরও আবশ্যক। ফিকিরবিহীন যিকির নির্বোধ লোকদের কাজ। আর ‘যিকির’ বিহীন ‘ফিকির’ হচ্ছে নাস্তিক ও আল্লাহদ্রোহী লোকদের কাজ।
কিন্তু আজকালকার ‘তাসাউফে’ শুধু যিকির আছে, ‘ফিকির’ নেই। যিকির এর সঙ্গে ফিকির করলে প্রচলিত ভাষায় তা আর তাসাউফ হলোনা। কোনো পীরের মুরীদ তা করতে চাইলে তার মুরীদগিরীই চলে যাবে, শুধু তাই নয়, এ যিকিরকেও তথায় খুবই ভালো অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে ও নির্দিষ্ট সময়ে চোখ বন্ধ করে মুখে ‘আল্লাহ’ ‘আল্লাহ’ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে দেয়া হয়েছে, চলে সেই নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে অন্যান্য সময়েও। এবং সেই বিশাল প্রক্রিয়ার বাইরে জীবনের বিশাল ক্ষেত্রে কোথাও তাদের জীবনে আল্লাহর যিকির এর কোনো লক্ষণ দেখা যায়না। ‘যিকির’ এর এই প্রক্রিয়া ও সময় নির্ধারণ ইসলামের এক মারাত্মক বিদয়াত। এই ‘বিদয়াত’ ইসলামকে সর্বাত্মক বিপ্লবী আদর্শ হতে না দিয়ে একটা যোগ সাধনার বৈরাগ্য ধর্মে পরিণত করে রেখেছে।
মৌখিক যিকিরও যিকির বটে যদি তার সাথে অন্তরের যিকির যুক্ত হয়। তাই ইমাম কুরতবী লিখেছেনঃ মৌখিক যিকিরকেও যিকির বলা হয়েছে, কেননা তা অন্তরের যিকির এর নিদর্শন।
অর্থাৎ অন্তরের যিকিরের যিকিরই মৌলিক যিকির এর রূপ লাভ করে। কিন্তু তাসাউফে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের যিকির প্রবর্তিত। সেখানে অন্তরের যিকির এর কোনো স্থান নেই। অন্তরের যিকির এর যে লক্ষ্য, তা এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। এখানে মৌখিক যিকিরই প্রধানত মুখ্য। তার আঘাতে কলব সাফ করা ও ছয় লতীফা জারি করাই যে যিকির এর মূল উদ্দেশ্য। তাই বলা হয় সে যিকির কুরআনের বলা যিকির হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর জিনিস। যার কোনো দলীল কুরআন হাদীসে নেই। লতীফাও একটি বিদয়াতী ধারণা মাত্র। কুরআন হাদীসে তা স্বীকৃত নয়, তা থেকে পাওয়া যায়নি।
অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ আরবী(*******)
-হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আল্লাহকে খুব বেশি বেশি স্মরণ করো।
আল্লামা কুরতবী এর তাফসীরে লিখেছেনঃ আয়াতটিতে যে যিকির করার নির্দেশ, তার অর্থ দিল দিয়ে এমনভাবে যিকির করা, যা সর্বাবস্থায় ও স্থায়ীভাবে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কোনো সময়ই তা হারিয়ে ফেলবেনা বা ভুলে যাবেনা।
এই পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতটিও প্রণিদানযোগ্যঃ
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ
-আল্লাহর দিকে উথ্থিত হয় সব পাক পবিত্র কথাবার্তা। আর নেক আমলই তাকে উথ্থিত করে। (আল ফাতিরঃ১০)
অর্থাৎ ভালো ভালো ও পবিত্র কথা-তওহীদ বিশ্বাস, আল্লাহর যিকির, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি সবই আল্লাহর নিকট পৌঁছায়, তবে তা পোঁছিয়ে দেয় নেক আমল। নেক আমলবিহীন শুধু কথা, শুধু যিকির বা তওহীদ বিশ্বাস অর্থহীন। তা আল্লাহর নিকট কবুল হবেনা।
এই কারণে, হাদীসে যিকির এর বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে বটে; কিন্তু সেই সঙ্গে তার বাস্তব রূপ কি হলে তা আল্লাহর যিকির হয় বা আল্লাহর যিকির এর বাস্তব পন্থা কি, তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দেয়া হয়েছে।
নবী করীম(স) বলেছেনঃ আরবী(*******)
-যে লোক আল্লাহর আনুগত্য করলো, সেই আল্লাহর যিকির করলো, যদিও তার(নফল) নামায রোযা ও কল্যাণময় কাজ খুব কমই হলো।
অর্থাৎ আল্লাহর যিকির এর সঠিক বাস্তবরূপ হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য করা, তাঁর হুকুম আহকাম পালন করা। কেননা আল্লাহর হুকুম পালন করলে আল্লাহর যিকির স্বতঃই হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ স্মরণে না থাকলে আল্লাহর হুকুম পালন সম্ভব হতে পারেনা। অতএব আল্লাহর ‘যিকির’ বিশেষ একটা ধরনে ও নির্দিষ্ট সময় ও সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই হচ্ছে বিদয়াত। তাসাউফে তথা পীর মুরীদীতে এই বিদয়াতই মূল উপজীব্য। এরূপ যিকির এর অনুষ্ঠান করেই পীরেরা বোকা লোকদের ভেড়া বানিয়ে রাখে এবং হাদীয়া-তোহফা আকারে ঘোষণা করে। বস্তুত যিকির এর এই ধরন হিন্দু বৈরাগ্যবাদী ও বৈষ্ঞবদের মধ্যেই প্রচলিত। পীরদের এই পদ্ধতিটি হিন্দু বৈরাগ্যবাদী হতে গৃহীত হয়েছে বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবেনা।
বৈরাগ্যবাদের বিরুদ্ধে কুরআন মজীদ চিরকালই সোচ্চার। নবী করীম(স) সারা জীবনের সাধনা দিয়ে এর বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন, মানুষের বৈরাগ্যবাদী ঝোঁক ও প্রবণতাকে দূর করেছেন। কিন্তু তাসাউফ এ জিনিসটিকে শক্তিশালী করে তুলেছে, তাসাউফের প্রধান হোতাদের মধ্যে বৈষয়িক স্বাদ আস্বাদন ও সামাজিক সম্পর্ক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে এক প্রবল নেতিবাচক ভাবধারা বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায়। অথচ ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে এ জিনিস ছিলনা। রাসূলের জামানায় সাহাবীদের মাঝে এমন ভাবধারা কখনো দেখা দিলে নবী করীম(স) কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ করেছেন। কুরআন হাদীসে ‘তাজকিয়া’র ব্যাপারে যিকির ই ইলাহী-আল্লাহর যিকির এর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই একমাত্র উপায় ছিলনা। যিকিরে ইলাহীর সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক উপায় ও উপকরণ ছিল, যা মুসলমানদের তাজকীয়ায়ে নফস হাসিলের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হতো। এ পর্যায়ে ‘জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ’-র কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুত ‘তাজকীয়ায়ে নফস’ সবর, তাওয়াক্কুল, আল্লাহর নিকট আত্মসমর্প্ণ, আল্লাহর ব্যবস্থায় রাজি হওয়া প্রভৃতি অতি উঁচুদরের মহান গুণাবলী অর্জনের জন্য জিহাদের গুরুত্ব সর্বাধিক। কুরআন ও হাদীসে তাকে এ মর্যাদাই দেয়া হয়েছে।(বিশেষভাবে কুরআন মজীদের সূরা আল-বাকার ১৫২, ১৫৩ ও ১৫৪ আয়াত এবং সূরা আহযাব এর ২২ ও ২৩ আয়াত দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাসাউফপন্থীগণ জিহাদ পরিহার করেছে, জিহাদের প্রাণান্তকর ময়দান ত্যাগ করেছে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব শয়তান লোকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে খানকার নিরাপদ আশ্রয়ে যিকিরে ইলাহী ও মুরাকাবা মুশাহাদায় মশগুল হয়ে রয়েছে। আর এ কাজকেই তাজকীয়ায়ে নফসের একমাত্র উপায় রূপে নিজেরাও গ্রহণ করেছে, অন্যান্য মানুষকেও তা করতে দাওয়াত দিয়েছে। এরই ফলে যিকির এর নতুন নতুন পন্থা ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।
মুরাকাবা-মুশাহাদার সম্পূর্ণ নতুন পরিভাষা ও অভিনব পন্থা ও পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার কোনো নাম নিশানা রাসূলে করীম(স) ও সাহাবায়ে কিরামের আমলে ছিলনা।
তাসাউফপন্থীদের মুজাহিদা নফসের খায়েশের বিরুদ্ধে এক প্রবল ও নিরবিচ্ছিন্ন যুদ্ধবিশেষ। কিন্তু আল্লাহর দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সাথে এর দূরতম সম্পর্কও নেই। তাসাউফপন্ধীরা এ পর্যায়ে একটি হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করে। তা হচ্ছেঃ আরবী(*********)
-আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদে ফিরে এলাম। লোকেরা জিজ্ঞেস করলোঃ বড় জিহাদ কি? বললেনঃ দিল বা নফসের সাথে জিহাদ করা।
এ কথাটিকে রাসূলের কথা বা হাদীস হিসেবেই প্রচার করা হয়। আর এর ওপর নির্ভর করে তাসাউফপন্থীরা প্রথমে দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বা তাদের মোকাবিলা করার তুলনায় নিজের নফসের সাথে মুজাহিদা করাকে উত্তম ও বড় জিহাদরূপে গ্রহণ করে। পরে এটাকেই একমাত্র কাজরূপে নির্ধারণ করে নেয়। আর দ্বীনের শত্রুদের সাথে জিহাদ করাকে দুনিয়াদারী বা রাজনীতি ইত্যাদি বলে সম্পূর্ণ বর্জন করে। কিন্তু আসলে এ একটা মস্ত বড় ধোঁকা। উপরোক্ত কথাটি সম্পর্কে হাদীস বিশারদ ও বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম ইবনে হাযার আসকালানী বলেছেন-ওটা হাদীস নয়। বরং খুবই প্রসিদ্ধ একটি কথা, লোকদের মুখে মুখে উচ্চারিত। কিন্তু আসলে ওটি ইবরাহীম ইবনে আইলার কথা, রাসূলের হাদীস নয়।
উক্ত কথাটি বায়হাকী ও খতীব বাগদাদী কর্তৃক উদ্ধৃত হয়েছে বটে; কিন্তু তা অত্যন্ত দূর্বল সনদের। তাই এর উপর ভিত্তি করে ইসলামের এত বড় একটা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়না। এ কারণে আল্লাহর দুশমনদের মোকাবিলায় যুদ্ধ ও সংগ্রামে দৃঢ়তা মজবুতী ও অচল অটল হয়ে থাকার যে সবর কুরআন মজীদে যার উচ্চ মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে তাসাউফপন্থীদের নিকট এর কোনোই গুরুত্ব নেই। ‘তাওয়াক্কুল’ ও অন্যান্য দ্বীনী ফযীলতপূর্ণ কাজ-কর্মের অবস্থা তা-ই ঘটেছে।
জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের ক্ষেত্রে তাসাউফপন্থীরা যে পরিবর্তন সূচিত করেছেন তা কি করে জায়েয হতে পারে? এ একটি কঠিন প্রশ্ন তাঁদের তরফ থেকে এর জবাব দিতে চেষ্টা করা হয়েছে বটে; কিন্তু সে জবাব কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে অগ্রাহ্য এবং অর্থহীন। তাঁরা নিজেদের আমলে বৈধতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ‘ইস্তিখাব’ ও ‘ইখতিয়ার’-‘ছাঁটাই বাচাই ও গ্রহণের’ নীতি অবলম্বন করেছেন। যেমন নবী করীমের সহস্র লক্ষ্য সাহাবীদের মধ্য থেকে কেবলমাত্র সুফ্ফাবাসী সাহাবীদেরকে নিজেদের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁদের জীবনের সাথে তারা তাদের সামগ্রিক আদর্শের মিল দেখতে পেয়েছিল। আর অন্যান্য সাহাবীদের জীবনের সেসব খুঁটিনাটি দিকগুলোই উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন যেগুলো থেকে তাদের মনে ভাবধারার সমর্থন পাওয়া যায়। হযরত জুনাইদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলঃ ‘তাসাউফ’ কি? তিনি বললেন ‘তাসাউফ’ এর ভিত্তি আটটি জিনিসের ওপর স্থাপিত। এ আটটি জিনিস স্বতন্ত্রভাবে আটজন নবী পয়গম্বরের জীবনে স্পষ্ট প্রতিভাত। তা হলোঃ হযরত ইবরাহীমের বদান্যতা, দানশীলতা, মেহমানদারী, হযরত ঈসমাইলের আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা ও আত্মসমর্পণ, হযরত ইয়াকুবের সবর, হযরত যাকারিয়ার ইশারাত, হযরত ইয়াহিয়ার অপরিচিত, হযরত ঈসার দেশ সফর, হযরত মূসার খিরকা পরিধান এবং হযরত মুহাম্মদ(স) এর ফাকর-দারিদ্র্য।
সহজেই বুঝতে পারা যায়, এক-একজন নবীর বিরাট বিশাল ও সম্পূর্ণ জীবনের বিপুল গুণরাশির মধ্যে আলাদা করে একটি মাত্র গুণকেই ‘আদর্শ’ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে, যদিও তা করার অনুমতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দেননি। আল্লাহ তা‘আলা তো সম্পূর্ণ ও সামগ্রিকভাবেই হযরত মুহাম্মদ(স) কে আদর্শরূপে গ্রহণ করার-তার একটি মাত্র গুণ নয়-সবগুলো গুণই ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।
বলেছেনঃ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
-তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের সত্তায় অতীব উত্তম অনুসরণযোগ্য আদর্শ রয়েছে।(আল আহযাবঃ21)
আর রাসূলে করীম(স) নিজেই ঘোষণা করেছেনঃ আরবী(*******)
-আমি যে দ্বীন নিয়ে এসেছি তোমাদের মন ও মানসিকতা যতক্ষণে তার সম্পূর্ণ অধীন না হবে, ততক্ষণে তোমাদের কেউ-ই ঈমানদার হতে পারবেনা।
তার অর্থ রাসূলের একটি কথা বা একটি নীতিই নয়, তাঁর নিকট হতে পাওয়া সম্পূর্ণ দ্বীন-পুরোপুরি আদর্শই গ্রহণ করতে হবে।
‘খুলাফায়ে রাশেদুন’ এর ক্ষেত্রেও তাঁদের এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে। তারা তাদের জীবনের জুহদ, সাখাওয়াত ও রিয়াজত পর্যায়ে ভাবধারা সমূহকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তাদের জিহাদী কার্য্ক্রম ও কর্মতৎপরতাকে এরা সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চেয়েছে। অথচ তাঁদের সমগ্র জীবনই অতিবাহিত হয়েছে বাতিল শক্তির সাথে লড়াই সংগ্রাম, ইসলামী সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সাধনা, সমাজে শরীয়তের আইন জারি ও কার্য্কর করা, ইনসাফ কায়েম করা ও আল্লাহর দুশমনদের মস্তক চূর্ণ করার কাজের মধ্য দিয়ে। কিন্তু বর্তমান তাসাউফপন্থীদের নিকট তাঁদের এসব মহান গুণের কোনোই গুরুত্ব নেই। এরই ফলে মুসলিম সমাজ আজ বৈরাগ্যবাদের স্রোতে ভেসে গিয়ে জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রাণ-মনের শক্তি প্রতিভা হারিয়ে ফেলেছে, হয়েছে সর্বহারা।
ইলমে শরীয়ত ও ইলমে মারিফাত দুটি আলাদা জিনিস হওয়ার দাবির সমর্থনে একটি হাদীসও পেশ করা হয়। হাদীসটি মিশকাত শরীফে এভাবে উদ্বৃত হয়েছেঃ আরবী(******)
-হাসান বসরী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ ইলম দু’প্রকার। একটি ইলম কলবের অভ্যন্তরে প্রতিফলিত। আর এ-ই হচ্ছে সত্যিকার কল্যাণকর ইলম। আর একটি ইলম শুধু মুখে মুখে বলা। আর তা-ই হচ্ছে মানুষের উপর আল্লাহর অকাট্য দলীল।
কিন্তু এটা এ পর্যায়ের কোনো দলীলই হতে পারেনা। কেননা একেতা এটা রাসূলের কথা নয়, কথা নয় কোনো সাহাবীর। এটি হচ্ছে হাসান বসরীর কথা এবং তিনি তাবেয়ী মাত্র।
দ্বিতীয়ত, এখানে যে ইলমের কথা বলা হচ্ছে, তা আসলে দুটি স্বতন্ত্র ইলম নয়। একটি ইলমেরই দুটি দিক-বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ। এর একটি অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। যেটিকে মুখে ইলম বলা হয়েছে, তা-ই হলো কুরআন ও সুন্নাতের ইলম; তা মুখে পড়ে শিখতে হয়। আর এই পড়ার যে প্রতিফলন ঘটে অন্তরের ওপর, তা-ই হলো ‘ইলমুন ফিল কালব’-দিলের ইলম। কাজেই এই দুয়ের মাঝে কোনো দ্বৈততা নেই এবং তা ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হাসিল করা যায়না; বরং একই কুরআন হাদীস থেকেই তা শিখতে হবে। প্রদীপ জ্বালালে তা একটি হয় আগুন ও অপরটি সেই আগুনেরই আলো ও তাপ। এই আলোর তাপকে কি আগুন থেকে আলাদা করা যায়? এ-ও তেমনি। আবু তালীব মক্কী উপরোক্ত কথাটির ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ
-এ দুটিই মৌলিক ইলম। একটি অপরটি ছাড়া নয় যেমন ঈমান ও ইসলাম। আর এ দু’টো পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত, ঠিক যেমন দেহ ও মন। একটি অপরটি হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা।
‘ইলমে বাতেন’ বা ‘বাতেনীইলম বলেও কোনো জিনিস ইসলামে স্বীকৃত নয়। যদিও এ ইলম এর অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য আর একটি হাদীস ‘মুসাললাল’ বর্ণনা করা হয়।
তা এরূপঃ হাসান বসরী(রা) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত হুযায়ফা(রা) হতে বর্ণনা করেছেনঃ হযরত হুযায়ফা বলেনঃ আমি নবী করীম(স) কে জিজ্ঞেস করলাম-ইলমে বাতেন কি? রাসূল(স) বললেন-আমি এ বিষয়ে জীবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন; আল্লাহ বলেছেনঃ ইলমে বাতেন হলো আমার ও আমার বন্ধু প্রিয়জন, আমার অলী ও আমার খাঁটি দোস্তদার লোকদের মধ্যবর্তী এক বিশেষ জিনিস, আমি তা তাদের কলবের ভিতরে আমানত রেখে দিই, তা আমার কোনো নিকটবর্তী ফেরেশতাও জানতে পারেনা, জানতে পারেনা কোনো নবী-রাসূলও।
কিন্তু হায় আফসোস! এটা কোনো হাদীসই নয়। ফাতহুল বারীর গ্রন্থকার ইমাম ইবনুল হাযার আসকালানী এটাকে হাদীস বলে মানতে রাজি হননি।
তিনি বলেছেনঃ এ কথাটি মনগড়াভাবে রচিত, রাসূল(স) এর কথা নয়। হাসান বসরী হযরত হুযায়ফার সন্ধান লাভ করেননি। তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করার কোনো সুযোগই তাঁর হয়নি।
কাজেই এখানে হযরত হুযাইফা(রা) হতে হাদীসটি হাসান বসরী বর্ণনা করেছেন বলে যা বলা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, নবী করীম(স) ও পরবর্তী ইসলামের স্বর্ণযুগের অনেক পরে ‘ইলমে বাতেন’ নামে পীর মুরীদী ব্যবসা এসব মিথ্যা কথাবার্তা ব্যাপক রচনা ও হাদীস নামে প্রচার করা হয়েছে। আসলে এ হলো বাতেনীয়া ফিরকার আকীদা। তারাই শরীয়তকে বাতেনী ও জাহেরী এ দু’ভাগে ভাগ করেছে। আর বাতেনীয়া ফিরকা সুন্নাত আল জামায়াতের মধ্যে গণ্য নয়। এ এক বাতিল ফিরকা। তারা নব্যুয়ত ও শরীয়তকে মানতোনা। সব হারাম জিনিসকে তারা হালাল মনে করতো।
বস্তুত কুরআন সুন্নাত থেকে বিচ্ছিন্ন এ মারিফাত মানুষকে ইসলামের তওহীদী ঈমান থেকে সরিয়ে নিয়ে বেদান্তবাদী শিরক এর মহাপংকে ডুবিয়ে দেয়। আর তা-ই ঘটেছে বর্তমানকালের অনেক পীরবাদী ও তথাকথিত তাসাউফপন্থীদের জীবন। অতএব ইসলামে এ তাসাউফের কোনো স্থান থাকতে পারেনা।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি