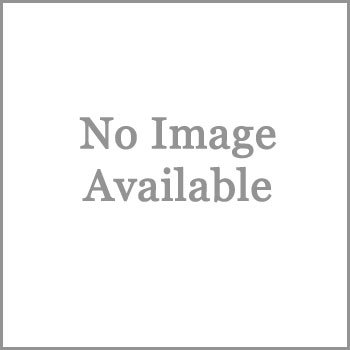কিয়াস ও ইজতিহাস কি বিদয়াত?
ইসলামী শরীয়তের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন ও হাদীস। এ দুটোকে ভিত্তি করেই ইসলামী জিন্দেগীর নিত্য নতুন প্রয়োজনীয় বিষয়ে শরীয়তের রায় জানতে হবে, দিতে হবে নিত্য নতুন উদ্ভূত সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান। তাই ইসলামী শরীয়তে কিয়াস ও ইজতিহাদ শরীয়তের অন্যতম উৎসরূপে পরিগণিত, এ দুয়ের সাহায্যেই ইসলাম সকল কালের, সকল মানুষের জন্য পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হওয়ার সামর্থ্য ও যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়ে থাকে, দিতে পারে মুসলিম জীবন বিধানের সকল পর্যায়ে ও সকল প্রকার অবস্থায় নির্ভূল পথ-নির্দেশ। তা-ই এ দুটো বিদয়াত নয়। বিদয়াত নয় এ জন্য যে, এ দুটো ইসলামী ব্যবস্থায় কিছুমাত্র নতুন জিনিস নয়। স্বয়ং রাসূলে করীম(স) ও খুলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক এ দুটো পূর্ণমাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে ইসলামী আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে।
আল্লামা আলুসী লিখেছেনঃ কিয়াস ও ইজতিহাস দ্বীন পূর্ণ হওয়ার কিছুমাত্র বিপরীত নয়। কেননা দ্বীন পূর্ণ হওয়ার অর্থ হচ্ছেঃ দ্বীন নিজস্ব দিক দিয়ে এবং তার আনুষঙ্গিক জরুরী বিষয়ে পূর্ণ পরিণত ও চূড়ান্ত। এখন তা হতেই প্রয়োজনীয় আইন কানুন ও নিয়মনীতি বের করা হবে। আকায়েদের মূলনীতি নির্ধারণ করা হবে, শরীয়তের মূলনীতি ও ইজতিহাদের কায়দা কানুন উদ্ভাবিত হবে। তার কোনোটাই কুরআন তথা দ্বীনের পূর্ণ হওয়ার বিপরীত হবেনা।
মুজাদ্দেদী আলফেসানী শায়খ আহমদ সরহিন্দী বলেছেনঃ কিয়াস ও ইজতিহাদকে কোনো দিক দিয়েই বিদয়াত মনে করা যেতে পারেনা। কেননা এ দুটো মূল কুরআন হাদীসের দলীলই প্রকাশ করে, কোনো নতুন অতিরিক্ত জিনিস দ্বীনের ভিতরে প্রমাণ করেনা।
বস্তুত কিয়াস ও ইজতিহাদ রূপায়িত হয় ইজমার মাধ্যমে। ইজমাও দ্বীন ইসলামের নবোদ্ভাবিত কোনো জিনিস নয় এবং তদ্দারা কোনো নতুন ইসলামের মূল বিধানের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোনো মতও প্রমাণিত হয়না। তাই ইজমাও বিদয়াত নয়-ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কোনো ফায়সালাও বিদয়াত বলে গণ্য হতে পারেনা। ইজমার ভিত্তি স্পষ্টভাবে হাদীসেই স্বীকৃত।
হযরত ইবনে মাসউদ(রা) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ
- আরবী (*******)
- মুসলিম সমাজ সামগ্রিকভাবে শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সিদ্ধান্ত করবে তা আল্লাহর নিকটও ভালোও উত্তমরূপে গৃহীত হবে এবং সে মুসলিমরাই যাকে খারাপ ও জঘন্য মনে করবে, তাই খারাপ ও জঘন্য বলে গণ্য হবে আল্লাহর নিকট। (ইবনে নযীম এ হাদীসটিকে ইবনে মাসউদের কথা বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তবুও ইজমার সমর্থনে এ একটি দলীলরূপে গণ্য। কেননা সাহাবীর কথাও শরীয়তের দলীল)।
আহলে সুন্নাত ও আহলে বিদয়াত
সুন্নাত ও বিদয়াত সম্পর্কে এ আলোচনার পর বিবেচ্য বিষয় হলো, কে আহলে সুন্নাত আর কে আহলে বিদয়াত?
আহলে সুন্নাত কে- মানে, সুন্নাতের অনুসারী কারা? কারা সুন্নাতকে অবলম্বন করে চলছে এবং জীবনধারাকে সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখছে। আর আহলে বিদয়াত কে-মানে কারা সুন্নাতের অনুসারী নয়, কারা বিদয়াতপন্থী? কারা বিদয়াতী?
এ প্রশ্নেরও আলোচনা আবশ্যক। কেননা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, বেশ কিছু লোক চরম বিদয়াতী কাজ করেও জীবনের বিভিন্ন দিকে সুন্নাতের বরখেলাপ কাজ করেও একমাত্র নিজেদেরকেই ‘আহলে সুন্নাত’ বলে দাবি করছে। আর তাদের বিদয়াতসমূহকে যারা সমর্থন করেনা, যারা শক্তভাবে সুন্নাতের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে চাচ্ছে, সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে জীবনে ও সমাজে তাদেরকে তারা বিদয়াতী (ফিতরাতপন্থী) বলে ফতোয়া দিচ্ছে। কাজেই দলীল ভিত্তিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠা দরকার যে, সত্যিকারভাবে কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে কে আহলে সুন্নাত আর কে আহলে বিদয়াত এবং সেই সঙ্গে আহলে সুন্নাতেরই বা স্থান কোথায় এবং কোথায় স্থান আহলে বিদয়াতের।
আহলে সুন্নাত কারা, এ কথার জবাবে আল্লামা আবদুর রহমান ইবনুল জাওজীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নবী করীম(স) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরামের আদর্শে অনুসারীরাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আহলে সুন্নাত। কেননা তাঁরাই সুন্নাতের আদর্শকে বাস্তবভাবে অনুসরণ করে চলেছে, যে সুন্নাতে কোনরূপ নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়নি। এ জন্যে যে, নতুন জিনিস উদ্ভাবিত হয়েছে-বিদয়াত সৃষ্টি হয়েছেতো রাসূলে করীম(স) ও সাহাবায়ে কিরামের পরবর্তীযুগে।
তিনি আরো বলেছেনঃ পূর্বোক্ত আলোচনা হতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আহলে সুন্নাত হলো সুন্নাতের অনুসারী লোকেরা। আর আহলে বিদয়াত হলো তারা, যারা এমন কিছু জিনিস বের করেছে, যা পূর্বে ছিলনা এবং যার কোন সনদও নেই।
অর্থাৎ সুন্নাত যারা কার্যত পালন করে, তাতে কোনোরূপ হ্রাস করেনা, বৃদ্ধিও করেনা, যেমন রাসূল ও সাহাবায়ে কিরাম করেছেন, বলেছেন ও চলেছেন হুবহু তেমন-ই পালন করে, তারাইতো অভিহিত হতে পারে আহলে সুন্নাত বলে। আর যারা তাতে কোনোরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি করে, মনগড়া অনেক কিছু ধর্মের মধ্যে শামিল করে নেয়, ধর্মীয় কাজ বলে চালিয়ে দেয়, তারা ‘আহলে সুন্নাত’ হতে পারেনা। তারাতো সম্পূর্ণরূপে ‘আহলে বিদয়াত’-বিদয়াতপন্থী।
বস্তুত সাহাবায়ে কিরামের যুগে কোনো বিদয়াত ছিলনা। তাঁরাতো খালেস সুন্নাতের উপর আমল করেছেন; আমল করেছেন ব্যক্তি জীবনে, অনুসরণ করে চলেছেন সমষ্টিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে। শুধু তা-ই নয়, কোথাও কোনো বিদয়াত দেখা দিলে তাঁরা পূর্ণ শক্তিতে সে বিদয়াতের প্রতিরোধ করেছেন। তাঁরা নবী করীম(স) এর ঘোষণার উপর খাঁটি বলে উত্তীর্ণ হয়েছেন। নবী করীম(স) বলেছেনঃ
আরবী (************)
-আমার সাহাবীগণ আমার উম্মতের উপর আমানতদার। আর আমার সাহাবীরা যখন চলে যাবে, তখন আমার উম্মতের উপর সেই অবস্থা ফিরে আসবে, যার ওয়াদা তাদের জন্য করা হয়েছে।
সুন্নাত প্রতিষ্ঠা ও বিদয়াত প্রতিরোধের দায়িত্ব
এ ছিল রাসূলে করীম(স) এর আগাম সাবধান বাণী। তাঁর উম্মতের উপর যেসব আদর্শিক বিপদ ও সংঘাত আসতে পারে বলে রাসূলে করীম(স)মনে করেছেন, সেগুলোর উল্লেখ করে তিনি আগেই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যেন উম্মতের জনগণ সে বিষয়ে হুঁশিয়ার হয়ে থাকে এবং নিজেদের ঈমান-আকীদায় এবং আমলে ও আখলাকে সে ধরনের কোনো জিনিস-ই প্রবেশ করতে না পারে। এ পর্যায়ের আর একটি হাদীস হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) কর্তৃক বর্ণিত।
রাসূলে করীম(স) বলেছেনঃ আরবী (*********)
- আমার পূর্বে প্রেরিত প্রত্যেক নবীর-ই তাঁর উম্মতের মধ্য থেকে হাওয়ারীগণ হয়েছে এবং এমন সব সঙ্গী সাথী ও হয়েছে, যারা সে নবীর সুন্নাত গ্রহণ ও ধারণ করেছেন। আর তাঁর আদেশ ও নির্দেশ যথাযথভাবে পালন করেছেন। পরে সে উম্মতের অধিকারী হয়েছে এমন সব লোক, যারা বলতো এমন সব কথা যা তারা করতোনা এবং করতো এমন সব কাজ, যা করতে তাদের আদৌ আদেশ করা হয়নি। এরূপ অবস্থায় এ লোকদের বিরুদ্ধে যারা জিহাদ করবে নিজেদের শক্তি দ্বারা, তারা মুমিন আর যারা জিহাদ করবে নিজেদের মুখের ভাষা ও সাহিত্য দ্বারা তারাও মুমিন; আর যারা জিহাদ করবে দিল দ্বারা তারাও মুমিন। কিন্তু অতঃপর একবিন্দু ঈমাণের অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা যেতে পারেনা।
এ দীর্ঘ হাদীসে পরবর্তীকালে যেসব উত্তরাধিকারী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে, তারাই হচ্ছে আহলে বিদয়াত। কেননা তাদের কাজ ও কথায় মিলন নেই এবং করে এমন কাজ, যা করতে তাদের বলা হয়নি। অথচ ইসলামী শরীয়তে এমন কাজকে দ্বীন কাজ হিসেবে করার কাউকে-ই অনুমতি দেয়া যেতে পারেনা। তাহলে রাসূলের সুন্নাতের কোনো মূল্যই থাকবেনা কারো কাছে, থাকবেনা কোনো গুরুত্ব। এ জন্যে এদের বিরুদ্ধেই জিহাদ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব বিদয়াতীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিরই কর্তব্য। যে তা করবেনা, এ হাদীস অনুযায়ী তার মধ্যে ঈমানের লেশমাত্র নেই।
ইসলামের জিহাদ ঘোষণার নির্দেশ মূলত কূফর ও শিরকের বিরুদ্ধে। কিন্তু এখানে যে বিদয়াতের বিরুদ্ধে জিহাদ করার গুরুত্ব এত জোরালো ভাষায় বলা হলো, তার কারণ এই যে, বিদয়াত সুস্পষ্ট কুফর ও প্রকাশ্য শিরক না হলেও তা যে কুফর ও শিরক এ সূচনা, কুফর ও শিরক এর উৎসে বীজ, তাতে সন্দেহ নেই।
ইসলামী সমাজে একবার বিদয়াত দেখা দিলে ও ক্ষেত্র তৈরি করে নিতে পারলে অনতিবিলম্বে তা-ই যে আসল শিরক ও কুফর-এর দিকে টেনে নিয়ে যাবে তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এ কারণেই ইসলামী সমাজে কুফর ও শির্ক এর এই বীজকে অংকুরেই বিনষ্ট করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং এ জন্যেই বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করার ওপর ঈমানের নির্ভরশীর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। বস্তুত দ্বীন ইসলামে যে কাজ করতে বলা হয়নি সে কাজকে দ্বীনি কাজ মনে করে করাই হচ্ছে এক প্রকার কুফরী এবং এতেই নিহীত রয়েছে শিরক এর ভাবধারা। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত হাদীস কয়টিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
নবী করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ
আরবী (********)
- যে লোক আমার পরে মরে যাওয়া কোনো সুন্নাতকে পুনরুজ্জীবিত করবে, তার জন্যে সে পরিমাণ সওয়াব রয়েছে যে পরিমাণ সওয়াব সে সুন্নাত অনুযায়ী আমল করে পাও্য়া যাবে; কিন্তু আমলকারীর সওয়াবে বিন্দুমাত্র কম করা হবেনা। পক্ষান্তরে যে লোক কোনো গোমরাহীর বিদয়াতকে চালু করবে-যে বিদয়াতে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল মোটেই রাজি নহেন-তার গুনাহ হবে সে পরিমাণ, যে পরিমাণ গুনাহ তদনুযায়ী আমল করলে হবে; কিন্তু আমলকারীর গুনাহ হতে এক বিন্দু কম করা হবেনা।
এখানে মরে যাওয়া সুন্নাতকে পুণরায় চালু করার সওয়াব ও গোমরাহীর বিদয়াত প্রবর্তন করার গুনাহ সম্বন্ধে যা কিছু বলা হয়েছে, তা থেকে মুসলিম সমাজকে সুরক্ষিত রাখা এবং সমাজে সুন্নাতকে চালু ও প্রতিষ্ঠিত করা- তাকে মরে যেতে না দেয়া ও বিদয়াতকে কোনোক্রমেই চালু হতে না দেয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করাই এ হাদীসের মূল লক্ষ্য।
নবী করীম(স) বলেছেনঃ
আরবী (**********)
- দ্বীন ইসলাম শুরুতে যেমন অপরিচিত ও প্রভাবহীন ছিল, তেমনি অবস্থা পরেও দেখা যাবে। এই সময়কার এই অপরিচিত লোকদের জন্য সুসংবাদ। আর এই অপরিচিত লোক হচ্ছে তারা, যারা আমার পরে আমার সুন্নাতকে বিপর্যস্ত করার যাবতীয় কাজকে নির্মূল করে সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টিত হবে। (তিরমিযী)।
মুসলিম সমাজে যদি সাধারণভাবে সুন্নাত প্রতিষ্ঠিত না থাকে, বিদয়াত যদি মুসলিম সমাজকে গ্রাস করে ফেলে তাহলে প্রকৃত দ্বীন ইসলাম সেখানে এক অপরিচিত জিনিসে পরিণত হবে এবং প্রকৃত ইসলাম পালনকারী লোকগণ-যাও বা অবশিষ্ট থাকে- তারা সমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত ও প্রভাবহীন হয়ে পড়ে। সমাজের উপর মাতব্বরী ও কর্তৃত্ব হয় বিদয়াতী ও বিদয়াতপন্থী লোকদের। এরূপ অবস্থায় যারাই সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দ্বীনের দৃষ্টিতে সমাজকে সুস্থ করে গড়ে তুলতে চেষ্টিত হয়, তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহ্র রাসূলের তরফ হতে সুসংবাদ শুনান হয়েছে। কেননা তারা বাস্তবিক মজবুত ঈমানের ধারক।
বস্তুত সুন্নাত যখন সমাজে ম্লান ও স্তিমিত হয়ে আসে এবং বিদয়াতের জুলমাত পুঞ্জীভূত হয়ে গ্রাস করে ফেলে সমস্ত সমাজকে, তখন ঈমানদার লোকদের একমাত্র কাজ হলো বিদয়াতকে মিটিয়ে সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করা। কিন্তু তখনও যারা বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের সম্মান দেখায়, তারা ইসলামের সাথে করে চরম দুশমনি।
রাসূলে করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ
আরবী (********)
- যে লোক কোনো বিদয়াতী বা বিদয়াতপন্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলো, সে তো ইসলামকে ধ্বংস করায় সাহায্য করলো।
কেননা বিদয়াত পন্থী ব্যক্তির ভূমিকা ইসলামের বিপরীত। সে তো ইসলামকে নির্মূল করার ব্রতেই লেগে আছে নিরন্তর। আর এরূপ অবস্থায় তার প্রতি সম্মান দেখানো বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সে লোক বিদয়াতীর কাজকে সমর্থন করে এবং বিদয়াতকে পছন্দ করে। এতে করে বিদয়াতী ও বিদয়াতপন্থী ব্যক্তির মনে ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে অধিক সাহস ও হিম্মত হবে, সে হবে নির্ভীক, দুঃসাহসী। আর এ জন্যেই এ কাজ ইসলামকে ধ্বংস করার ব্যাপারে সাহায্য করে বলে রাসূলে করীম(স)ঘোষণা করেছেন।
হযরত ইবনে আব্বাস(রা) বলেন, নবী করীম(স) ইরশাদ করেছেনঃ
আরবী (********)
- আল্লাহর নিকট তিন শ্রেণীর লোক অত্যধিক ঘৃণ্য। এক. যারা হারাম শরীফে শরীয়তবিরোধী কাজ করে, দুই. ইসলামী আদর্শে যারা জাহিলিয়াতের নিয়ম-নীতি প্রথাকে চালু করতে ইচ্ছুক এবং তিন. যারা কোনো কারণ ব্যতীত-ই মুসলমানের রক্তপাত করতে উদ্ধত হয়। (বুখারী)।
হাদীসে বলা হয়েছে জাহিলিয়াতের সুন্নাত, নিয়ম-নীতি ও প্রথা। অর্থাৎ জাহিলিয়াতের সুন্নাত। আর তা সম্যকভাবেই ‘সুন্নাতে রাসূল’ এর বিপরীত জিনিস। এখন যে লোক ইসলামের সুন্নাতের মাঝে জাহিলিয়াতের সুন্নাত বা নিয়ম-নীতি প্রথাকে চালু করতে চায় ইসলামের অন্তর্ভূক্ত সুন্নাত হিসেবে, সে যে আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত ঘৃণ্য হবে, হবে আল্লাহ্র নিকট অত্যন্ত অভিশপ্ত তাতে আর কি সন্দেহ থাকতে পারে।
এ পর্যায়ে হযরত হাসান বসরী(র) বলেছেনঃ যে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই তাঁর নামে শপথ করে বলছি, অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও মাত্রা হ্রাস করার দুই সীমাতিরিক্ত প্রান্তিক নীতির মধ্যবর্তী নীতিই হচ্ছে তোমাদের সুন্নাতের নীতি, অতএব তোমরা তারই উপর ধৈর্য্ সহকারে অবিচল হয়ে থাক, আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করবেন। কেননা আহলে সুন্নাত-সুন্নাত অনুসারী লোকদের সংখ্যা চিরকালই কম ছিল অতীতে, পরবর্তীকালেও তাই থাকবে। এরা হচ্ছে তারা যারা কখনো বাড়াবাড়িকারীদের সঙ্গে যোগদান করেনি। বিদয়াতপন্থীদেরও সঙ্গী হয়নি তারা তাদের বিদয়াতের ব্যাপারে। বরং তারা সুন্নাতের উপর অটল হয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদ্দিন না আল্লাহ্র সাক্ষাতের জন্য তারা মৃত্যুবরণ করেছে। আল্লাহ চাইলে তোমরাও এমনিই হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেছেনঃ
লোকেরা যখনই কোনো বিদয়াতকে উদ্ভাবন করেছে, তখনই তারা এক একটি সুন্নাতকে মেরেছে। এভাবেই বিদয়াত জাগ্রত ও প্রচন্ড হয়ে পড়েছে, আর সুন্নাত মিটে গেছে।
এসব কয়টি হাদীসই মুসলমানদের সামনে একটা সুস্পষ্ট কর্মসূচী পেশ করেছে এবং তা হচ্ছে এই যে, মুসলমানরা যে দেশ ও যে অবস্থাতেই থাকুকনা কেন, তারা বিদয়াত ও বিদয়াতপন্থীদের বিরুদ্ধে দূর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং সুন্নাতকে তার আসল রূপে ও ভাবধারায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং রাখতে চেষ্টিত হবে। ‘সুন্নাত’ যদি বিলীন হয়ে যায় আর বিদয়াত যদি প্রবল হয়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে মুমিন ও মুসলিমের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।
সাহাবীদের জামা‘আতই আদর্শ
দুনিয়া ইসলামের এ সুন্নাতের আদর্শ লাভ করেছে শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ(স) এর কাছ থেকে। মুহাম্মদ(স)-ই এ সুন্নাতকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীরাও এ সুন্নাতেরই উপর অটল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সাহাবীদের পরে তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের যুগেও সুন্নাতই সমাজের ওপর জয়ী ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে মুসলিম মিল্লাতের নানাবিধ দূর্বলতা দেখা দেয়, দেখা দেয় নব নব বিদয়াত। সমাজের সাধারণ অবস্থা প্রচন্ডভাবে বদলে যায়। বিদয়াত জয়ী ও প্রকট হয়ে পড়ে এবং সুন্নাত হয় দূর্বল ও পরাজিত বরং লোকেরা বিদয়াতকেই সুন্নাত হিসেবে গ্রহণ করে এবং সুন্নাতকে বিদয়াতের ন্যায় পরিহার করে। সে আজ প্রায় বার তেরশ’ বছর আগের কথা। তারপর মুসলিম জীবন সুন্নাতের আদর্শ থেকে ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়তে থাকে এবং সুন্নাতের আদর্শের পরিবর্তে শিকড় গাড়তে থাকে বিদয়াত। আজকের মুসলমান তো এ দৃষ্টিতে বিদয়াত-অজগরের একেবারে উদর গহবরে আটকে গেছে। কিন্তু আজও তাদের সামনে আদর্শ ও অনুকরণীয় ও অনুসরণযোগ্য হচ্ছে রাসূলে করীম(স) ও তাঁর সাহাবায়ে কিরাম। তাঁদেরই অনুসরণ করে চলা উচিত সকল মুসলমানের। রাসূল ও সাহাবদের যুগে সুন্নাত বিশ্ব মুসলিমের নিকট চিরকালের তরে আঁধার সমুদ্রের আলোকস্তম্ভ। আজো সেখান থেকেই আলো গ্রহণ করতে হবে, পেতে হবে পথ-নির্দেশ। রাসূলে করীম(স) এমনি এক ভবিষ্যদ্বাণী করে বিভ্রান্ত মুসলিমের জন্য পথ-নির্দেশ করে গেছেন।
রাসূলের একটি হাদীসের শেষাংশ হচ্ছে এইঃ
আরবী (************)
-বনী-ইসরাঈলীরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল আর আমার উম্মত তিহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ফির্কা ছাড়া আর সব ফির্কা-ই জাহান্নামী হবে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেনঃ সে একটি ফির্কা কারা হে রাসূল (স)? তিনি বললেন, “তারা হচ্ছে সেই লোক যারা অনুসরণ করবে আমার ও আমার আসহাবদের আদর্শ”।
এ হাদীসকে ভিত্তি ধরে ইমাম তিরমিযী এবং ইমাম ইবনুল জাওজী যে কথাটি বলেছেন, তার মর্ম হলো এইঃ এ হাদীসে প্রমাণ রয়েছে যে, ‘এক জামা‘আত’ বলতে সাহাবাদের জামা‘আতকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ কোনো একজন সাহাবী নন, নবী করীম(স) এবং সামগ্রিকভাবে সাহাবীদের জামা‘আত যে সুন্নাতকে পালন করে গেছেন, পরিবর্তিত অবস্থায় এবং পতন যুগেও যারা সেই সুন্নাতকে অনুসরণ করবে, তারাই জান্নাতে যাওয়ার অধিকারী হবে। তারা হবে সেই লোক যারা আকীদা, কথা ও বাহ্যিক আমলের রীতি-নীতি সব-ই সাহাবীদের ইজমা থেকে গ্রহণ করবে।
আবুল আলীয় তাবেয়ী বলেছেনঃ মুসলিম সমাজ ফির্কায় ফির্কায় বিভক্ত হওয়ার পূর্বে যে অবস্থায় ছিল, তোমরা সেই অবস্থাকে শক্ত করে বজায় রাখতে ও বহাল করতে চেষ্টা করবে।
এ কথাটিতেও ঠিক সাহাবাদের যুগের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা সাহাবীদের যুগই ছিল এমন যুগ-যখন মুসলিম সমাজ ছিল ঐক্যবদ্ধ, অবিভক্ত।
আসেম বলেন, আবুল আলীয়ার এ নসীহতের কথা হাসানুল বসরীকে বলায় তিনি বলেনঃ আল্লাহ্র কসম, তোমাকে ঠিকই উপদেশ দিয়েছে এবং তোমাকে একান্তই সত্য কথা বলেছে।
ইমাম আওয়াজী বলেছেনঃ তোমরা নিজেকে সুন্নাতের ওপর অবিচল রাখো সুন্নাতে ধারক লোকেরা যেখানে দাঁড়িয়েছেন অর্থাৎ যে নীতি গ্রহণ করেছেন, তুমিও সে নীতিই গ্রহণ করো, তাঁরা যা বলেছেন, তুমি তাই বলবে, যা থেকে তাঁরা বিরত রয়েছেন, তুমিও তা থেকে বিরত থাকবে। আর তোমার পূর্ববর্তী নেককার লোক যে পথ ধরে চলে গেছেন, তুমিও সেই পথেই চলবেন। তাহলে তাঁরা যা করেছেন, তা-ই করার তওফীক তুমিও পাবে।
মনে রাখতে হবে, ইমাম আওজায়ী একজন তাবেয়ী এবং তিনি সলফে সালেহ বলতে বুঝিয়েছেন সাহাবীদের জামা‘আতকে। অতএব রাসূলের পরে সুন্নাতের আদর্শ সমাজ যেমন ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম, তেমনি রাসূলের পরে সাহাবায়ে কিরামই হতে পারেন সকল কালের, সকল মুসলিমের আদর্শ ও অনুসরণীয়। সলফে সালেহীন বলতে দুনিয়ার মুসলমানের নিকট তাঁরাই বরণীয়। কেননা তাঁদের আদর্শবাদিতা ও রাসূলের অনুসরণ গুণের কথা স্বয়ং আল্লাহ তা‘আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন কুরআন হাদীসে সাক্ষ্য দিয়েছেন স্বয়ং নবী করীম(স)। রাসূলের সত্য মাপকাঠিতে পুরোপুরিভাবে তাঁরাই উত্তীর্ণ হয়েছেন।
বস্তুত রাসূল(স) এর পরে সাহাবায়ে কিরাম ছাড়া মুসলমানদের নিকট আর কোনো ব্যক্তি কোনো কালের, কোনো দেশের কোনো বুযুর্গ ও(?) আদর্শ ও অনুসরণীয়রূপে গণ্য হতে পারে না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) কোনো ব্যক্তিকে আদর্শরূপে গ্রহণ করা সম্পর্কে বলেছেনঃ কারো যদি সুন্নাতকে ধারণ করতেই হয়, তাহলে তার উচিত এমন ব্যক্তির সুন্নাত ধারণ করা, যে মরে গেছে। কেননা যে লোক এখনো জীবিত সে যে ভবিষ্যতে ফিতনায় পড়বেনা, তার কোনো নিশ্চয়তাই নেই। আর মরে যাওয়া লোক হচ্ছেন মুহাম্মদ(স) এর সাহাবীগণ, যারা ছিলেন এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম লোক, যাঁদের দিল ছিল সর্বাধিক পূণ্যময়, গভীরতম জ্ঞানসম্পন্ন। কৃত্রিমতা ছিলনা তাঁদের মধ্যে। আল্লাহ তা‘আলা তাঁদের বাছাই করে নিয়েছিলেন তাঁর নবীর সাহাবী হওয়ার জন্যে এবং তাঁর দ্বীন কায়েম করবার জন্যে। অতএব তোমরা তাদের সঠিক মর্যাদা অনুধাবন করো-স্বীকার করো। তাঁদের পদাংক অনুসরণ করো। আর তাঁদের চরিত্র ও স্বভাবের যতদূর সম্ভব তোমরা ধারণ ও গ্রহণ করো। কেননা তাঁরা ছিলেন সঠিক ও সুদৃঢ় হেদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) এর মতো একজন সাহাবীরও এ এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ। এর তাৎপর্য্ এই যে, সাহাবায়ে কিরামই সর্বকালের লোকদের জন্য পরিপূর্ণ ও নিখুঁত নির্ভরযোগ্য আদর্শ। আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাকের দৃষ্টিতে তাঁরা সর্বোন্নত পর্যায়ে উন্নীত ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। কিন্তু এখানে বিশেষ কোনো ব্যক্তি সাহাবীর কথা বলা হয়নি, বলা হয়েছে সমষ্ঠিগতভাবে সাহাবীদের জামা‘আতের কথা। এই সাহাবীদের জামা‘আতই মুসলিমের নিকট অনুসরণীয়।
এ থেকে বোঝা গেল যে, রাসূলে করীম(স) ছাড়া মানব সমাজের কোনো এক ব্যক্তিকে-ই একান্তভাবে অনুসরণীয়রূপে গ্রহণ করা কিছুতেই কল্যাণকর হতে পারেনা, ইসলাম সে নির্দেশ দেয়নি কাউকেই-সে যে যুগের এবং যত বড় বুযুর্গ ও অলী-আল্লাহ্ই হোকনা কেন। শুধু তাই নয়, ইসলামে সে বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ বাণীও উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা) হতে বর্ণিত হয়েছেঃ কেউ যেন নিজের দ্বীনকে কোনো ব্যক্তির সাথে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে না দেয় যে, সে ঈমান আনলে সেও ঈমান আনবে আর সে কুফরী করলে সেও কুফরী করবে। যদি তোমরা কারো অনুসরণ করতে বাধ্য হও-ই, তাহলে তোমরা অনুসরণ করবে মরে যাওয়া লোকদের। কেননা জীবিত মানুষ জীবিত থাকা অবস্থায় ফিতনা হতে মুক্ত হতে পারেনা।
এখানেও মরে যাওয়া লোক বলতে বোঝায়, সাহাবীদের জামা‘আত, কোনো বিশেষ ব্যক্তি-সাহাবী নয়। একমাত্র রাসূলে করীম(স) ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়। এ হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের মতো একজন জলীলুল কদর সাহাবার কথা। তিনি যেমন ছিলেন প্রথম যুগের সাহাবী, তেমনি রাসূলের বিশেষ খাদেম। কাজেই সাধারণভাবে মুসলমানদের জন্য সঠিক নির্ভরযোগ্য কর্মনীতি এ-ই হতে পারে যে, তারা মেনে চলবে শুধু আল্লা্হকে, আল্লাহ্র রাসূলকে-কুরআন এবং হাদীসকে; আর এক কথায় সুন্নাতকে। এ ছাড়া কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতকে ব্যক্তিগত চাল-চলন, স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারকে কখনোই একমাত্র আদর্শরূপে আঁকড়ে ধরবেনা। কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের বিনা শর্তে আনুগত্য স্বীকার করবেনা। বিনা শর্তে আনুগত্য মানব সমাজে কেবলমাত্র রাসূলে করীম(স) কে করা যেতে পারে, করতে হবে, অন্য কারো নয়।
এ পর্যায়ে একটি বড় বিভ্রান্তির অপনোদন করা একান্তই আবশ্যক। বিভ্রান্তিটি হচ্ছে একটি প্রখ্যাত হাদীসকে কেন্দ্র করে।
হাদীসটি হলো এইঃ আরবী(**********)
-আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রপুঞ্জের মতোই উজ্জ্বল। এদের মধ্যে যার-ই তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে।
এই হাদীসের ভিত্তিতে কেউ কেউ বলতে চান যে, নিজেদের ইচ্ছেমতো যে কোনো একজন সাহাবীর অনুসরণ করলেই হেদায়াতের পথে চলা সম্ভব হবে। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করা যুক্তিযুক্ত হতে পারেনা। প্রথম কারণটি এই যে, এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে। একটি সূত্র হলোঃ আ‘মাশ থেকে আবু সুফিয়ান হতে, জাবির(রা) হতে। আর একটি হলো সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হতে, ইবনে আমর থেকে। আর তৃতীয় হলো হামযা আল-জজী থেকে, নাফে থেকে, ইবনে উমর থেকে। কিন্তু মুহাদ্দিসদের বিচারে এ সব সূত্রে কোনো হাদীস প্রমাণিত নয়। ইবনে আবদুল বার্র এর উদ্বৃতি দিয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেনঃ আমাদের নিকট সাঈদের পুত্র ইবরাহীম, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তাদের নিকট হামদ ইবনে আইয়ূব আস সামূত বর্ণনা করেছেন যে, আমাদের নিকট বাজ্জার বলেছেন যে, “আমার সাহাবীরা নক্ষত্রপুঞ্জের মতো, তাদের মধ্যে যার-ই তোমরা অনুসরণ করবে, হেদায়াত পাবে”। এই অর্থের যে হাদীসটি বর্ণনা করা হয় তা এমন একটি কথা, যা নবী করীম(স) হতেই সহীহ বলে প্রমাণিত হয়নি। (খতীব আল বাগদাদীর উদ্ধৃত হযরত ইবনুল খাত্তাব (রা) এর বর্ণনা থেকে এর বিপরীত কথা জানা যায়।)
হাদীস বিচারে সনদের গুরুত্ব হলো মৌলিক। আর সনদের বিচারে যে হাদীস সহীহ বলে প্রমাণিত নয়, তাকে শরীয়তের দলীল হিসেবে পেশ করার কোনো অধিকার কারোই থাকতে পারেনা।
সুন্নাত- কঠিন ও সহজ
আমরা যারা আহলি সুন্নাত হওয়ার দাবি করছি এবং মনে বেশ অহমিকা বোধ করছি এই ভেবে যে, আমরা কোনো গোমরাহ ফির্কার লোক নই; বরং নবী করীম(স)-এর প্রতিষ্ঠিত ও সুন্নাত অনুসরণকারী সমাজের লোক। কিন্তু আমাদের এই ধারণা কতখানি যথার্থ, তা আমাদের অবশ্যই গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।
আমরা আহলি সুন্নাত অর্থাৎ সুন্নাতের অনুসরণকারী। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা রাসূলে করীম(স) এর কোন সুন্নাতের অনুসরণকারী? কঠিন ও কষ্টের সুন্নাতের, নাকি সহজ, নরম ও মিষ্টি মিষ্টি সুন্নাতের।
অস্বীকার করার উপায় নেই যে, রাসূলে করীম(স) এর জীবনে ও চরিত্রে এ উভয় ধরনের সুন্নাতেরই সমাবেশ ঘটেছে। তিনি একজন মানুষ ছিলেন। তাই মানুষ হিসেবেই তাঁকে এমন অনেক কাজই করতে হয়েছে, যা এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য দরকার। যেমন খাওয়া, পরা, দাম্পত্য ও সাংসারিক জীবন যাপন। এ ক্ষেত্রে তিনি যে যে কাজ করেছেন শরীয়তের বিধান অনুযায়ী তা-ও সুন্নাত বটে। তবে তা খুবই সহজ, নরম ও মিষ্টি সুন্নাত। তা করতে কষ্টতো হয়-ই না; বরং অনেক আরাম ও সুখ পাওয়া যায়। যেমন, কদুর তরকারী খাওয়া, মিষ্টি খাওয়া, পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা, মিস্ওয়াক করা, আতর-সুগন্ধী ব্যবহার করা, বিয়ে করা, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ, লম্বা জামা-পাগড়ী বাঁধা, দাঁড়ি রাখা ইত্যাদি।
কিন্তু রাসূলে করীম(স) এর জীবনে আসল সুন্নাত সেইসব কঠিন ও কষ্টসাধ্য কাজ, যা তাঁকে সেই মুশরিক আল্লাহদ্রোহী সমাজে তওহীদি দাওয়াত প্রচার ও দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-প্রচেষ্টার সাথে করতে হয়েছে। এই পর্যায়ে তাঁকে ক্ষুধায় কাতর হতে, পেটে পাথর বাঁধতে ও দিন-রাত অবিশ্রান্তভাবে শারীরিক খাটুনী খাটতে হয়েছে। শত্রুদের জালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে, পায়ে কাঁটা লাগাতে এবং তায়েফে গিয়ে গুন্ডাদের নিক্ষিপ্ত পাথরে দেহ মুবারককে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তের ধারা প্রবাহে পরনের কাপড় সিক্ত করতে ও ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন হয়ে রাস্তার ধারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতে হয়েছে। এক সময় বনু হাশিম গোত্রের সাথে মক্কাবাসীদের নিঃসম্পর্ক ও বয়কট হয়ে আবু তালিব গুহায় ক্রমাগত তিনটি বছর অবস্থান করতে হয়েছে। সর্বশেষে পৈতৃক ঘর-বাড়ি ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করতে হয়েছে। কাফির শত্রু বাহিনীর মোকাবিলায় মোজাহিদদের সঙ্গে নিয়ে পূর্ণ পরাক্রম সহকারে যুদ্ধ করতে, দন্ত মুবারক শহীদ করতে ও খন্দক খুদতে হয়েছে।
রাসূলে করীম(স) এর এসব কাজও সুন্নাত এবং সে সুন্নাত অনুসরণ করাও উম্মতের জন্য একান্ত কর্তব্য। তবে এ সুন্নাত অত্যন্ত কঠিন, দুঃসাধ্য ও প্রাণান্তকর চেষ্টার সুন্নাত।
সহজেই প্রশ্ন জাগে, আমরা কি এই সুন্নাত পালন করছি? যদি না করে থাকি-করছি না যে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়- তাহলে রাসূলের সুন্নাত অনুসরণের যে দাবি আমরা করছি, তা কি সত্য বলে মনে করা যায়? বড়জোর এতটুকুই বলা চলে যে, হ্যাঁ, আমরা রাসূলের সুন্নাত অনুসরণ করছি বটে, তবে তা মিষ্টি, সহজ ও নরম নরম সুন্নাত। কিন্তু কঠিন, কষ্ট, প্রাণে ও ধন-সম্পদে আঘাত লাগে এমন কোনো সুন্নাত পালনের দিকে আমাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, তাও যে আমাদেরকে অবশ্য পালন করতে হবে, না করলে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট কঠিন জবাবদিহি করতে হবে, সেকথা স্মরণ করতেও যেন আমরা ভয় পাই।
বিদয়াতের পুঞ্জীভূত স্তূপ
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ(রা)এর পূর্বোক্ত কথাটি যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা মুসলমানদের সাহাবী পরবর্তী যুগের ইতিহাস অকাট্য ও নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে। উত্তরকালে মুসলিম সমাজে নানাবিধ বিদয়াত প্রচলিত হয়ে পড়ে, সুন্নাত ধীরে পরিত্যক্ত হয়-মন ও জীবন থেকে নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখনি সুন্নাতকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছে, তখনই এই ব্যক্তিগত অন্ধ অনুসরণের প্রবল বিদ্বেষ তার পথে প্রচন্ড বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।
বিশেষ ব্যক্তির নাম করে যে তার জীবদ্দশায় হয়তো বড় আলীম বা পীর, অলী আল্লাহ হওয়ার সূখ্যাতি পেয়ে গেছেন জনগণের মাঝে-তাঁর দোহাই দিয়ে বলা হয়েছেঃ অমুক বুজুর্গ বা অমুক পীর একথা বলে গেছেন, কাজেই এতে কোনো দোষ নেই। এভাবে ব্যক্তি ভিত্তিক সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায়ের বিচার ইসলামে এক সম্পূর্ণ নতুন জিনিস-সুস্পষ্ট বিদয়াত। অথচ ইসলামে নবী করীম(স) ছাড়া আর কোনো ব্যক্তির কথা অথবা কাজের দোহাই আদৌ সমর্থনীয় নয়। এভাবে মুসলিম সমাজে ধীরে ধীরে সুন্নাত-রাসূলে করীম(স) এর আদর্শ –তলিয়ে গিয়ে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে বিদয়াত-আবর্জনার স্তূপ। এ বিদয়াত যেমন দেখা দিয়েছে আকীদা বিশ্বাসে, চিন্তায়-মনে, তেমনি আমলে ও আখলাকে, বাস্তব জীবনের সর্বদিকে ও সর্বক্ষেত্রে। এ স্তুপ প্রায় আকাশছোঁয়া। এর একটা একটা করে গণনা করাও সাধ্যাতীত। অথচ এ বিদয়াতগুলো চিহ্নিত ও নির্ধারিত না হলে মুসলমানকে তা থেকে রক্ষা করার-বিদয়াতের স্তুপের তলা থেকে তাদের উদ্ধার করার আরে কোনোই উপায় নেই। তাই আমরা কতকগুলো বড় বড় বিদয়াত সম্পর্কে যথাসম্ভব সংক্ষেপে আলোচনা পেশ করবো। আমরা দেখাবঃ এক-একটি বিদয়াত কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করেছে ও শিকড় গেড়ে বসেছে এবং মূল ইসলামের দৃষ্টিতে তাদের কোথায়-কোন গোমরাহীর সুদূর প্রান্তে নিয়ে পৌছিয়েছে।
এ পর্যায়ের আলোচনার শেষভাগে আমরা ‘খলিফায়ে রাশিদ’ হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীযের সে বিখ্যাত ভাষণটির কথা উল্লেখ করবো, যা তিনি খলীফা নিযুক্ত হওয়ার পরই সমবেত লোকদের সামনে পেশ করেছিলেন।
ভাষণটি এইঃ জেনে রাখো, তোমাদের নবীর পর আর কোনো নবী-ই নেই, তোমাদের কিতাব(কুরআন মজীদ) এর পর আর কোনো কিতাব-ই নেই, তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট সুন্নাতের পর আর কোনো সুন্নাত নেই এবং তোমাদের এই উম্মতের পর আর কোনো (নবীর) উম্মত হবেনা। তোমরা জেনে রাখো, হালাল তা-ই, যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর রাসূলের জবানীতে হালাল করে দিয়েছেন এবং তা হালাল কিয়ামত পর্য্ন্ত। জেনে রাখো, হারাম কেবল তা-ই, যা আল্লাহ হারাম করেছেন তাঁর কিতাবে তাঁর রাসূলের জবানীতে, তা হারাম কিয়ামত পর্য্ন্ত। জেনে রাখবে, আমি বিদয়াতপন্থী বা নতুন কিছুর প্রবর্ত্ক নই। আমি শুধু দ্বীনের অনুসরণকারী মাত্র। জেনে রাখো, আমি চূড়ান্ত ফয়সালাকারী কেউ নই, আমি তো শুধু নির্বাহকারী। জেনে রাখবে, আমি ধন-ভান্ডার সঞ্চয়কারী নই বরং আমি সেখানেই তাই রাখব, যা যেখানে রাখার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। এ-ও জেনে রাখবে, আমি তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি নই; আমাকে তো তোমাদের উপর বোঝাস্বরূপ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে, আর শেষ কথা জেনে রাখবে, স্রষ্টার নাফরমানী করে কোনো সৃষ্টির আনুগত্য করা যাবেনা।
বস্তুত এ ভাষণটি ইসলামী আদর্শানুসারী রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ব্যক্তিরই উপযুক্ত ভাষণ। এ ভাষণের মূল বক্তব্য আমাদের এ আলোচনারও বক্তব্য।
বিদয়াত কত প্রকার?
বিদয়াত সম্পর্কে এ মৌলিক আলোচনার শেষ পর্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অবতারণা একান্ত আবশ্যক, তা হলো বিদয়াতের প্রকারভেদ সম্পর্কে। প্রশ্ন হলো, বিদয়াত কি সত্যিই কয়েকভাগে বিভক্ত?
সাধারণভাবে মুসলিম সমাজের প্রচলিত ধারণা হলো বিদয়াত দু’প্রকার। একটি হলো ‘বিদয়াতে হাসানা’ বা ‘ভালো বিদয়াত’ আর দ্বিতীয়টি হলো ‘বিদয়াতে সাইয়্যেয়া’ বা মন্দ বিদয়াত। কেউ কেউ দ্বিতীয়টির নাম দিয়েছেন ‘বিদয়াতে মুস্তাকবিহা’ বা ‘ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত’। কিন্তু বিদয়াতের এ বিভাগও বোধ হয় একটি অভিনব বিদয়াত। কেননা বিদয়াতকে ‘ভালো’ ও ‘মন্দ’ এ দু’ভাগে ভাগ করার ফলে বহু সংখ্যক ‘বিদয়াত’-ই ভালো বিদয়াত হওয়ার পারমিট নিয়ে ইসলামী আকীদা ও আমলের বিশাল ব্যবস্থায় অনুপ্রবেশ করেছে অগোচরে। ফলে তওহীদবাদীরাই আজ এমন সব কাজ অবলীলাক্রমে করে যাচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষেই তওহীদবিরোধী-যা সুস্পষ্টরূপে বিদয়াত এবং কোনো তওহীদবাদীর পক্ষেই তা এক মুহুর্তের তরেও বরদাশত করার যোগ্য নয়।
এ পর্যায়ে আল্লামা বদরুদ্দীন আইনীর মতো মনীষী ও বিদয়াতকে দু’প্রকারে বলে একটি সংজ্ঞা পেশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ বিদয়াত দু’প্রকার। বিদয়াত যদি কোনো শরীয়তসম্মত ভালো কাজের মধ্যে গণ্য হয়, তবে তা ‘বিদয়াতে হাসানা’-ভালো বিদয়াত। আর তা যদি শরীয়তের দৃষ্টিতে খারাপ ও জঘন্য কাজ হয়, তবে তা ‘বিদয়াতে মুস্তাকবিহা’ বা ‘ঘৃণ্য ও জঘন্য বিদয়াত’।
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ ‘বিদয়াত’ আসলে বলা হয় এমন নতুন উদ্ভাবিত কাজ ও কথাকে, পূর্ববর্তী সমাজে যার কোনো দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়না। আর শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাতের বিপরীত জিনিসকে বলা হয় বিদয়াত। অতএব তা অবশ্যই নিন্দনীয় হবে।
অর্থাৎ যা-ই সুন্নাতের বিপরীত তা-ই বিদয়াত। অতএব বিদয়াতের সব কিছুই নিন্দনীয়, পরিত্যাজ্য, তার মধ্যে কোনো দিকই প্রশংসনীয় বা ভালো হতে পারেনা। অন্য দিকে বিদয়াতকে দু’ভাগে ভাগ করে এক ভাগকে ভালো বিদয়াত বলে আখ্যায়িত করা এবং এক ভাগকে মন্দ বিদয়াত বলা একেবারেই অমূলক।
এ কথার যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য্। শরীয়তে যার কোনো না কোনো ভিত্তি বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, তা তো কোনোক্রমেই সুন্নাতের বিপরীত হতে পারেনা। যা-ই সুন্নাতের বিপরীত নয়, তা-ই বিদয়াত নয়। আর যার কোনো দৃষ্টান্তই ইসলামের সোনালী যুগে পাওয়া যায়না, শরীয়তে পাওয়া যায়না যার কোনো ভিত্তি তা কোনোক্রমেই শরীয়তসম্মত নয় বরং তা-ই সুন্নাতের বিপরীত; অতএব তা-ই বিদয়াত। এর কোনো দিকই ভালো প্রশংসনীয় বা গ্রহণযোগ্য নয়। এক কথায় বিদয়াতকে হাসানাহ্ ও সাইয়্যেয়া-ভালো ও মন্দ ভাগ করা অযৌক্তিক।
রাসূলের যুগে বিদয়াতের মধ্যে কোনো ভালো দিক পাওয়া যায়নি। সাহাবী ও তাবেয়ীনের যুগেও নয়, রাসূলের বাণীতেও বিদয়াতকে এভাবে ভাগ করা হয়নি।
তাহলে মুসলিম সমাজে বিদয়াতের এ বিভাগ কেমন করে প্রচলিত হলো? এর জবাব পাওয়া যাবে হযরত উমর ফারূকের(রা) একটি কথার বিস্তারিত ব্যাখ্যার মাধ্যমে। এ সম্পর্কে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। আবদুর রহমান ইবনে আবদুল কারী বলেনঃ আমি হযরত উমর(রা) এর সাথে রমজান মাসে মসজিদে গেলাম। সেখানে দেখলাম লোকেরা বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজ নিজ নামায পড়ছে। আবার কোথাও একজন লোক নামায পড়ছে, আর তার সঙ্গে পড়ছে কিছু লোক। তখন হযরত উমর(রা) বলেনঃ আমি মনে করছি, এসব লোককে একজন ভালো ক্বারীর পিছনে একত্রে নামায পড়তে দিলে খুবই ভালো হতো। পরে তিনি তাই করার ব্যবস্থা করেন এবং হযরত উবাই ইবনে কায়াবের ইমামতিতে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। এই সময় এক রাত্রে আবার উমর ফারূকের সাথে আমিও বের হলাম। তখন দেখলাম লোকেরা একজন ইমামের পেছনে জামা‘আতবদ্ধ হয়ে তারাবীহর নামায পড়ছেন। এ থেকে হযরত উমর(রা) বললেনঃ এতো খুব ভালো বিদয়াত।(এই হাদীসটি ঈমাম বুখারী প্রমূখ মুহাদ্দিস জামা‘আতের সাথে তারাবীহ নামায পড়ার পর্যায়েই তা উল্লেখ করেছেন। রমযান মাসে জামা‘আতের সাথে তারাবীহ পড়া যে জায়েজ এ হাদীসই তার দলীল।)
হাদীসের শেষভাগে উল্লেখিত হযরত উমর ফারূক(রা) এর কথাটিই হলো বিদয়াতকে দু’ভাগে ভাগ করার পক্ষে অনেকের যুক্তি। বাক্যটির শাব্দিক তরজমা হলো ‘এটা একটা উত্তম বিদয়াত’। আর একটি বিদয়াত যদি উত্তম হয়, তাহলে আপনা আপনি বোঝা যায় যে, আর একটি বিদয়াত অবশ্যই খারাপ হবে। তাহলে মনে করা যেতে পারে যে, কোনো কোনো বিদয়াত ভালো, আর কোনো কোনো বিদয়াত মন্দ। এই হলো এ ব্যাপারে মূল ইতিহাস। মনে হচ্ছে উত্তরকালে হাদীসের ব্যাখ্যা লিখতে গিয়েই লোকেরা বিদয়াতের এ দুটো ভাগকে তুলে ধরেছেন। এবং বুখারী থেকেই সাধারণ সমাজে এ কথাটি ছড়িয়ে পড়েছে ও লোকদের মনে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, যে কোনো বিদয়াতকে সমালোচনা করলে বা সে সম্পর্কে আপত্তি তোলা হলে, তাকে বিদয়াত বলে ত্যাগ করার দাবি জানানো হলে অমনি জবাব দেয়া হয়, ‘হ্যাঁ, বিদয়াততো বটে, তবে বিদয়াতে সাইয়্যেয়া নয়, বিদয়াতে হাসানাহ, অতএব ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।’ হয়তোবা এ বিদয়াতের হাসানাহ এর আবরণে সুন্নাতের সম্পূর্ণ খেলাপ এক মারাত্মক বিদয়াত-ই সুন্নাতের মধ্যে, সওয়াবের কাজের মধ্যে গণ্য হয়ে মুসলিম সমাজে দ্বীনি মর্যাদা পেয়ে গেল। বস্তুত বিদয়াতের মারাত্মক দিক-ই হচ্ছে এই। এ কারণে বাস্তবতার দৃষ্টিতে রাসূলের বাণী ‘সব বিদয়াত-ই গোমরাহী’- এ কথাটি অর্থহীন হয়ে যায়। কেনন সব বিদয়াত-ই যদি গোমরাহী হয়ে থাকে তাহলে কোনো বিদয়াতই হেদায়াত হতে পারেনা। কিন্তু বিদয়াতের ভাগ-বন্টনে তার বিপরীত কথাই প্রমাণিত হয়। তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, কোনো কোনো বিদয়াত ভালোও আছে।রাসূলের কথা ‘সব বিদয়াতই গোমরাহী’ এ কথাটি ঠিক নয় (নাউজুবিল্লাহে মিন জালিক)। রাসূলের কথার বিপরীত ব্যাখ্যা দানের মারাত্মক দৃষ্টতা এর চেয়ে আর কিছু হতে পারেনা।
আমার বক্তব্য এই যে, মূলত বিদয়াতকে হাসানাহ ও সাইয়্যেয়া এ দু’ভাগে ভাগ করাই ভুল। আর হযরত উমর ফারূক(রা) এর কথা দ্বারাও এ বিভাগ প্রমাণিত হয়না। কেননা উমর ফারূক(রা) এর কথার অর্থ মোটেই তা নয়, যা মনে করা হয়েছে। এ জন্যে যে, উমর ফারূক(রা) জামা‘আতের সাথে তারাবীহর নামাযকে সে অর্থে বিদয়াত বলেননি, যে অর্থে বিদয়াত সুন্নাতের বিপরীত। তা বলতেও পারেননা তিনি। হযরত উমরের চাইতে অধিক ভালো আর কে জানবেন যে, জামা‘আতের সাথে তারাবীহ এর নামায পড়া মোটেই বিদয়াত নয়। রাসূলের জামানায় তা পড়া হয়েছে। রাসূলে করীম(সা) তারাবীহ এর নামায দু’তিন রাত নিজেই ইমাম হয়ে পড়িয়েছেন- এ কথা সহীহ হাদীস হতেই প্রমাণিত।
হযরত আয়েশা(রা) বলেনঃ আরবী(*******)
-নবী করীম(স) মসজিদে নিজের নামায পড়ছিলেন। বহু লোক তাঁর সঙ্গে নামায পড়লো, দ্বিতীয় রাত্রেও সে রকম হলো। এতে করে এ নামাযে খুব বেশি সংখ্যক লোক শরীক হতে শুরু করলো। তৃতীয় বা চতূর্থ রাত্রে যখন জনগণ পূর্বানুরূপ একত্রিত হলো, তখন নবী করীম(স) ঘর হতে বের হলেননা। পরের দিন সকাল বেলা রাসূলে করীম(স) লোকদের বললেনঃ তোমরা যা করেছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমি নামাযের জন্য মসজিদে আসিনি শুধু একটি কারণে, তাহল এভাবে জামা‘আতবদ্ধ হয়ে (তারাবীহ) নামায পড়লে আমি ভয় পাচ্ছি, হয়ত তা তোমাদের ওপর ফরযই করে দেয়া হবে।
হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ ‘এ ছিল রমযান মাসের ব্যাপার।’
এ হাদীসে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, জামা‘আতের সাথে তারাবীহ নামায পড়াবার কাজ প্রথম করেন নবী করীম(স) নিজে। করেন পর পর তিন রাত্রি পর্য্ন্ত। তাঁর পিছনে লোকেরা নামাযে শরীক হয়; কিন্তু তিনি নিষেধ করেননা। পরে তিনি তা পড়ান বন্ধ করেন শুধু এ ভয়ে যে, এভাবে এক অফরয নামায রাসূলের ইমামতিতে পড়া হলে এ কাজটি আল্লাহ্র তরফ হতে ফরয করে দেয়া হতে পারে। কেননা তখনো ওহী নাযিল হচ্ছিল, শরীয়ত তৈরি হচ্ছিল। আর নবীর কাজতো সুন্নাত। তা বিদয়াত হবে কি করে? [নবী করীম(স) নিজে তারাবীহ নামাযে ইমামতি বন্ধ করলেও তা জামা‘আতের সাথে পড়া কিন্তু বন্ধ হলোনা। তারপরও তা চলছে, কিন্তু তিনি নিষেধ করেননি জানা সত্ত্বেও। হযরত আয়েশা(রা) বর্ণিত হাদীসই তার প্রমাণ। তিনি বলেনঃ তৃতীয় বা চতূর্থ রাত্রে তিনি যখন তারাবীহ নামাযের ইমামতি করতে এলেননা, তখন পরেরদিন সকাল বেলা তিনি সাহাবীদের লক্ষ্য করে বললেনঃ রাত্রি বেলা তোমরা যা করেছিলে(তারাবীহ নামায পড়ছিলে) তা আমি দেখেছি। কিন্তু কেবল মাত্র একটি ভয়ই তোমাদের সাথে যোগ দিতে আমাকে বিরত রেখেছে। তা হচ্ছে, জামা‘আতের সাথে তারাবীহ পড়া তোমাদের জন্য ফরয হয়ে যাওয়া।]
[নবী করীম(স) কোনো কাজ করতে ইচ্ছে করেও তা করেননি শুধু এ ভয়ে যে, তিনি নিয়মিত তা করলে লোকেরাও তা নিয়মিত করতে শুরু করবে। আর তা দেখে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের জন্য তা ফরয করে দিতে পারেন, এ কথা হযরত আয়েশা(রা) এর কথা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি বলেনঃ নবী করীম(স) কোনো কোনো কাজ করতে ভালবাসতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তা করতেননা শুধু এ ভয়ে যে, তিনি তা নিয়মিত করতে থাকলে লোকদের উপর তা ফরয হয়ে যেতে পারে।]
তাহলে হযরত উমর (রা) জামা‘আতের সাথে নামায পড়াকে বিদয়াত বললেন কেন? বলছেন বিদয়াতের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থে, পরিভাষা হিসেবে নয়। বিদয়াতের শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ যে ‘নতুন’ তা পূর্বেই বলা হয়েছে। আর একে নতুনও এ হিসেবে বলা হয়নি যে, এরূপ নামায ইতিপূর্বে কখনোই পড়া হয়নি; বরং বলা হয়েছে এ জন্যে যে, নবী করীম(স)এর সময়ে জামা‘আতের সাথে তারাবীহ নামায পড়া দু চার দিন পর বন্ধ হয়ে যায়, তার পর বহু বছর অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। হযরত আবু বকর(রা) এর খিলাফতের সময় এ নামায নতুন করে চালু করা যায়নি। এরপরা হযরত উমর ফারূক(রা) এর সময় এ নামায় পূণরায় চালু হয়। এ হিসেবে একে বিদয়াত বলা ভুল কিছু হয়নি এবং তাতে করে তা সে বিদয়াতও হয়ে যায়নি যা সুন্নাতে বিপরীত, যার কোনো দৃষ্টান্তই রাসূলের যুগে পাওয়া যায়না। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, তাহলে হযরত উমরের এ কথাটির সঠিক তাৎপর্য্ কি? মুহাদ্দিসদের মতে এর তাৎপর্য্ এইঃ জামা‘আতের সাথে নামায পড়া এক অতি উত্তম চমৎকার ব্যবস্থা যা রাসূলে করীম(স) হতে শুরু হয়েছিল এবং পরে হযরত আবু বকরের সময়ে লোকদের নানা জটিলতায় মশগুল হয়ে থাকার কারণে পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল।
মুল্লা আলী কারী হযরত উমর ফারূক(রা) এর এ কথাটুকুর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ
উমার ফারূক(রা) এ কাজকে বিদয়াত বলেছেন তার বাহ্যিক দিককে লক্ষ্য করে। কেননা নবী করীমের পর এ-ই প্রথমবার নতুনভাবে জামা‘আতের সাথে তারাবীহ্র নামায পড়া চালু হয়েছিল। নতুবা প্রকৃত ব্যাপারের দৃষ্টিতে জামা‘আতের সাথে এ নামায পড়া মোটেই বিদয়াত নয়।
এখানে ইমাম মালিক(রা) এর প্রখ্যাত কথাটি স্মরণীয়। তিনি বলেছেনঃ যে লোক ইসলামের কোনো বিদয়াতের সৃষ্টি করলো এবং তাকে খুবই ভালো মনে করলো, সে প্রকারান্তরে ঘোষণা করলো যে, হযরত মুহাম্মদ(স) রিসালাতের দায়িত্ব পালনে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তো বলেছেনঃ আমি আজ তোমাদের দ্বীনকে তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম। অতএব রাসূলের সময় যা দ্বীনভুক্ত ছিলনা, তা আজও দ্বীনভুক্ত নয়।
এ বিষয়ে আমার শেষ কথা হলো, বিদয়াতকে দু’ভাগে ভাগ করাও একটি বিদয়াত এবং বিদয়াতের এ বিভাগ এর দুয়ার-পথ দিয়ে অসংখ্যা মারত্মক বিদয়াত ইসলামের গৃহ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে দ্বীনি মর্যাদা লাভ করেছে। বড় সওয়াবের কাজ বলে সমাজের বুকে শিকড় মজবুত করে গেড়ে বসেছে। এ বিষবৃক্ষ যত তাড়াতাড়ি উৎপাটিত করা যায়, ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষে ততোই মঙ্গল।
বিদয়াত সমর্থনের পীর অলির দোহাই
বিদয়াতপন্থীরা সাধারণত নিজেদের উদ্ভাবিত কাজে সমর্থনে সূফীয়ায়ে কিয়াম ও মাশায়েখে তরীকতের দোহাই দিয়ে থাকে। তারা বড় বড় ও সুস্পষ্ট বিদয়াতী কাজকেও ‘বিদয়াত’ নয়-বড় সওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেয়। আর বলেঃ অমুক অলী-আল্লাহ, অমুক হযরত পীর কেবলা নিজে এ কাজ করেছেন এবং করতে বলেছেন। আর তাঁর মতো অলী-আল্লাহই যখন এ কাজ করেছেন, করতে বলে গেছেন, তাহলে তা বিদয়াত হতে পারেনা, তা অবশ্যই বড় সওয়াবের কাজ হবে। তা না হলে কি আর তিনি তা করতেন। অতএব তা সুন্নাত বলে ধরে নিতে হবে।
বিদয়াতের সমর্থনে এরূপ পীরের দোহাই দেয়ার ফলে সমাজে দু’ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। একটি প্রতিক্রিয়া এই যে, কোনটি সুন্নাত আর কোনটি বিদয়াত, কোনটি জায়েয আর কোনটি নাজায়েয তা সুনির্দিষ্টভাবে ও নিঃসন্দেহে জানবার জন্য না কুরআন দেখা হয়, না হাদীস, না সাহাবায়ে কিরামের আমল ও জীবন চরিত। কেবল দেখা হয়, অমুক হুজুর কিবলা এ কাজ করেছেন কিনা। তিনিই যদি করে থাকেন তাহলে তা করতে আর কোনো দ্বিধাবোধ করা হয়না। সেক্ষেত্রে এতটুকুও চিন্তা করা হয়না যে, যার বা যাদের দোহাই দেয়া হচ্ছে সে বা তারা কুরআন-হাদীস অনুযায়ী কাজ করছে কিনা; তারা শরীয়তের ভিত্তিতে এ কাজ করেছে নাকি নিজেদের ইচ্ছেমতো।
এরূপ কথাতো আরবের কাফির সমাজের লোকদের বলা কথার মতো। যখন তাদের নিকট প্রকৃত তওহীদী দ্বীনের দাওয়াত পেশ করা হয়েছিল, তখন তারা বলেছিলঃ আমরা আমাদের বাপদাদাকে একটি পন্থার সংঘবদ্ধ অনুসারীরূপে পেয়েছি। আমরা তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে চলতে চলতে হেদায়াত পেয়ে যাব।
অর্থাৎ তাদের নিকট হক না হকের একমাত্র দলীল ছিল পূর্বপুরুষের দোহাই। তাদের তারা অনুসরণ করতো এ কারণে নয় যে, তারা কোনো ভাল আদর্শ অনুসরণ করে গেছে; বরং এ জন্যে যে, তারা ছিল তাদের পূর্বপুরুষ। এক্ষেত্রেও তাই দেখা যায়ঃ বিদয়াত কাজের সমর্থনে কেবল হুজুর কেবলার দোহাই। সে দোহাইর ভিত্তি শরীয়তের কোনো দলীল নয়, দলীল শুধু এই যে, সে তাদের ধারণা মতে একজন বড় অলী-আল্লাহ আর তার করা কাজ শরীয়তের প্রধান সনদ।
সেদিন আরবদের উপরোক্ত কথার জবাবে নবীগণের জবানীতে কুরআন মজীদে বলা হয়েছিলঃ
বলো! তোমরা তোমাদের বাপ দাদাকে যে নীতি অনুসারে পেয়েছ, তার অপেক্ষা অধিক উত্তম হেদায়াতের বিধান যদি আমি তোমাদের নিকট নিয়ে উপস্থিত হয়ে থাকি, তাহলেও কি তোমরা সে বাপ দাদাদেরই অনুসরণ করতে থাকবে?
অর্থাৎ এ এক আশ্চর্যের ব্যাপার যে, নীতি হিসেবে যেটা ভালো ও উত্তম বিবেচিত হবে, সেটা তারা অনুসরণ করতে রাজি নয়। এমন কি ভালো নীতি কোনটি তার বিচার বিবেচনা করতেও প্রস্তুত নয় তারা। সর্বোত্তম নীতি ও আদর্শ পেশ করা হলেও তারা যেমন পূর্বপুরুষদের অনুসরণ করতেই বদ্ধপরিকর ছিল, তেমনি এরাও শরীয়তের দলীলের ভিত্তিতে যদি কোনো কাজের বিদয়াত হওয়ার প্রমাণিতও হয় তবু তারা হুজুর কেবলার দোহাই দিয়ে সে বিদয়াতী কাজ-ই করতে থাকবে।
এর পরিণাম এই যে, মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে জনৈক অলী-আল্লাহ বা তথাকথিত পীরের আচার-আচরণের উপর নির্ভরশীল করে দেয়া হয়। সেখানে না আল্লাহ্র কথার কোনো দোহাই চলে, না রাসূলের কোনো কাজের বা কথার। আর কুরআন হাদীসের দৃষ্টিতে এ নীতি সুস্পষ্ট শিরক ও নিষিদ্ধ। এরূপ নীতিই গোমরাহীর মূল উৎস। এরূপ অবস্থায় মানুষ মানুষের অন্ধ অনুসারী হয়ে যায়; আর আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার পরিবর্তে বান্দা হয়ে যায় সেই মানুষেরই। আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার কোনো সুযোগই এদের জীবনে ঘটেনা।
অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে সত্যিকার মুমিন মুসলমানের ভূমিকা সম্পূর্ণরূপে বিবৃত হয়েছে কুরআনে, হাদীসে, ইতিহাসে। তাদের সমাজে দোহাই চলতো কেবল কুরআনের, হাদীসের। কোনো ব্যক্তির দোহাই দেয়া সে সমাজে শিরক রূপে গণ্য ছিল। সকল জটিল অবস্থাতেই শুধু এই কুরআন হাদীসেরই দোহাই দেয়া হতো এবং কুরআন হাদীসের কোনো দলীল তাদের সামনে পেশ করা হলে সব বিবাদ মুছে যেত, বিদ্রোহ দমন হতো, ঘুছে যেত সব মতপার্থক্য। তা-ই মেনে নিত তারা মাথা নত করে। তার বিপরীত আচরণ করতে তারা সাহস করতোনা, সে অধিকার কারো আছে বলেও মনে করতোনা তারা। রাসূলে করীমের ইন্তিকালের পরে খিলাফত পর্যায়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ হয়, হয় বাক-বিতন্ডা। কিন্তু যখনই তাঁদের সামনে রাসূলে করীম(স) এর একটি হাদীস পেশ করা হয় অমনি সবাই তা মেনে নিলেন। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর(রা) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সাহাবীদের মাঝে এ বিষয়ে মতভেদ হলো। এ পর্যায়ে কুরআনের দলীল পেশ করা হলে সবাই মেনে নিলেন যে, খলীফার গৃহীত এ নীতি যুক্তিসঙ্গত। ক্রীতদাস উসামা ইবনে যায়দের নেতৃত্বে বাহিনী প্রেরণ পর্যায়ে সাহাবীদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। হযরত আবু বকর(রা) বললেনঃ রাসূলে করীম(স) নিজে যে বাহিনী প্রেরণের সিদ্ধান্ত করে গেছেন, আমি তা প্রত্যাহার করতে পারবোনা।
এ সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা সবাই মেনে নিলেন। বস্তুত এ-ই হচ্ছে আদর্শ মুসলমানের ভূমিকা। আর মুসলমানদের জন্য চিরন্তন আদর্শ এ-ই হতে পারে, এ-ই হওয়া উচিত।
এর দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই দেখা দিয়েছে যে, জনসাধারণ মনে করতে শুরু করেছে যে, শরীয়ত ও মারিফাত (বা তরীকত) দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বতন্ত্র জিনিস। শরীয়তে যা নাজায়েজ, মারিফাত বা তরীকতের দৃষ্টিতে তাই জায়েয। কেননা একদিকে শরীয়তের দলীল দিয়ে বলা হচ্ছেঃ এটা বিদয়াত কিন্তু পীরের দোহাই দিয়ে সেটিকেই জায়েয করে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ফলে শরীয়ত আর মারিফাতের দুই পরস্পর বিধান হওয়ার ধারণা প্রকট হয়ে উঠে।
এরূপ ধারণা দ্বীন ইসলামের পক্ষে যে কতখানি মারাত্মক, তা বলে শেষ করা কঠিন। অতঃপর দ্বীন ও ঈমানের যে কোনো কল্যাণ নেই, তা স্পষ্ট বলা যায়। কেননা মানুষকে সব রকমের গোমরাহী থেকে বাঁচাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে শরীয়ত। এই শরীয়তের সুস্পষ্ট বিরোধিতাকেও যদি জায়েয মনে করা হয়, জায়েয বলে চালিয়ে দেয়া সম্ভব হয়, তাহলে গোমরাহীর সয়লাব যে সবকিছুকে রসাতলে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তা রোধ করতে পারবে কে?
তাই আমরা বলতে চাই, শরীয়তের ব্যাপারে রাসূল ও সাহাবাদের ছাড়া আর কারো দোহাই চলতে পারেনা। কুরআন, হাদীস ও ইজমায়ে সাহাবা ছাড়া স্বীকৃত হতে পারেনা অপর কোনো দলীল। কোনো মুসলমান-ই সে দোহাই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। নিলে তা ইসলাম হবেনা, হবে অন্য কিছু।
কয়েকটি বড় বড় বিদয়াত
সুন্নাত ও বিদয়াত সম্পর্কে নীতিগত আলোচনা এখানে শেষ করে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা কতকগুলো বড় বড় বিদয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করবো। এখানে বিদয়াত হিসেবে যে কয়টি বিষয়কে পেশ করা হচ্ছে, তার মানে কখনো এ নয় যে, কেবল এ কয়টিই বিদয়াত, এর বাইরে বা এছাড়া আর কোনো বিদয়াত নেই এবং এ কয়টি বিদয়াত উৎখাত হলেই সমস্ত বিদয়াত বুঝি শেষ হয়ে যাবে, আর সুন্নাতের সোনালী যুগের সূচনা হবে। না, তা নয়। বরং এর অর্থ এই যে, আমাদের মুসলিম সমাজে বর্তমানে যত বিদয়াতই প্রবেশ করেছে, তন্মধ্যে এগুলো হচ্ছে মৌলিক ও বড় বড় বিদয়াত। তবে এ-ই শেষ নয়। এ রকম আরো বিদয়াত রয়েছে যা আমাদের জীবনে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে। বিদয়াতের এ নীতিগত আলোচনার পর এখানকার আলোচনাকে মনে করা যেতে পারে দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ দৃষ্টান্তস্বরূপ এ কয়টি বিদয়াতের আলোচনা এখানে পেশ করা হলো, এ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এ ধরণের আরো অনেক বিদয়াত রয়েছে আমাদের জীবনে ও সমাজে। এর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোরও মূলোৎপাটন আবশ্যক।
তওহীদি আকীদায় শিরক এর বিদয়াত
একথা কেবল মুসলমানেরই নয়, দুনিয়ায় কারো অজানা থাকার কথা নয় যে, ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা হচ্ছে তওহীদ। ‘তওহীদ’ মানে আল্লাহ্র একত্ব। আল্লাহ্র এর একত্ব সার্বিক, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক। এ দৃষ্টিতে আল্লাহ শুধু সৃষ্টিকর্তাই নন তিনি একমাত্র পালনকর্তা, মালিক, রিযিকদাতা, রক্ষাকর্তা ও আইন বিধানদাতাও। অতএব মানুষ ভয় করবে কেবল আল্লাহ কে, ইবাদত বন্দেগী ও দাসত্ব করবে একমাত্র আল্লাহ্র। সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও লালন পালনকারী হিসেবে মানবে একমাত্র আল্লাহকে। এসব দিক দিয়ে তিনিই একমাত্র ‘ইলাহ’। তিনি ছাড়া কেউ ইলাহ নেই, কেউ ইলাহ নয় এবং কেউ ইলাহ হতে পারেনা এবং তিনিই একমাত্র রব, তিনি ছাড়া লালনপালনকারী ও ক্রমবিকাশদাতা, রক্ষাকর্তা ও প্রয়োজন পূরণকারী আর কেউ নেই। মাবুদ ও একমাত্র তিনি-ই। তিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদাত-বন্দেগী আনুগত্য পাবার অধিকারী নয়। অতএব মানুষের উপর আইন-বিধান কেবল আল্লাহরই চলবে। সংক্ষেপ কথায়ঃ রব্ব হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, একক, অনন্য; আর ইলাহ হওয়ার দিক দিয়েও তিনি এক, লা-শরীক। রবুবিয়তের দিক দিয়েও আল্লাহ এক, উলুহিয়াতের দিক দিয়েও তিনি এক। এর কোনো একটি দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই, জুড়ি কেউ নেই, সমতুল্য কেউ নেই।
শুধু এখানেই শেষ নয়। তিনি তাঁর যাত- মূল সত্তায় এক, অনন্য। তাঁর গুণাবলীতেও তিনি একক-শরীকহীন। মাখলুকাতের ওপর-অতএব মানুষের ওপর-হক বা অধিকার তাঁরই অপ্রতিদ্বন্ধী। এ হক-হকুকের দিক দিয়েও তাঁর শরীক কেউ নেই। এবং ক্ষমতা ইখতিয়ারও একমাত্র তাঁরই রয়েছে, সৃষ্টির ওপর, এই মানুষের ওপর। আর এসব ক্ষেত্রেও তাঁর শরীক কেউ নেই, কিছু নেই। কাউকেই তাঁর শরীক হওয়ার মর্যাদা দেয়া যেতে পারেনা।
ইসলামের এই তওহীদী আকীদা কুরআন হতে প্রমাণিত; প্রমাণিত হাদীস থেকেও। রাসূলে করীম(স) সর্বশেষ নবী ও রাসূল হিসেবে এই আকীদা-ই পেশ করেছেন বিশ্ববাসীর সামনে। দাওয়াত দিয়েছেন মৌলিক আকীদা হিসেবে এ তওহীদকে গ্রহণ করার। যারাই সেদিন ইসলাম কবুল করেছিলেন, তাঁরা সকলে ইসলামের এ ধারণার প্রতি ঈমান এনেই হয়েছিলেন মুসলমান। অতএব রাসূলের সাহাবীরাও ছিলেন এই আকীদায় বিশ্বাসী। এই ব্যাপারে তাঁরা কখনো দূর্বলতা দেখাননি, এক্ষেত্রে কারো সাথে তাঁরা রাজি হননি কোনোরূপ আপোস বা সমঝোতা করতে। অতএব, এ-ই হচ্ছে সুন্নাতের তওহীদী আকীদা। আকীদার সুন্নাত এ-ই।
কিন্তু ইসলামের এই সুন্নাতী আকীদায় কিংবা বলা যায়-আকীদার এই সুন্নাতে বর্তমানে দেখা দিয়েছে নানা শির্ক এর বিদয়াত। মুসলিম সমাজে আল্লাহকে এক ও অনন্য বলে সাধারণভাবে স্বীকার করা হয় বটে। কিন্তু কার্যত দেখা যায়, আল্লাহ্র উলুহিয়াতী তওহীদের প্রতি যদিও বিশ্বাস রয়েছে; কিন্তু তাঁর রবুবিয়াতের তওহীদ স্বীকার করা হচ্ছেনা। মুখে স্বীকার করা হলেও কার্য্ত অস্বীকারই করা হচ্ছে। রব্ব হিসেবে মেনে নেয়া হচ্ছে আরো অনেক শক্তিকে; মুখে নয়-বাস্তব কাজের ক্ষেত্রে। আর এ-ই হচ্ছে শির্ক। শব্দগত আকীদা হিসেবে যদিও আল্লাহকে-ই রিযিকদাতা, জীবনদাতা, মৃত্যুদাতা, সৃষ্টিকর্তা, প্রভাবশালী, কর্তৃত্বসম্পন্ন, বিশ্ব ব্যবস্থাপক এবং রব্ব বলে স্বীকার করা হয়, কিন্তু এ শ্রেণীর লোকেরাই মৃত ‘বুযুর্গ’ লোকদের নিকট প্রার্থনা করে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদেরই ভয় করে চলে, তাদেরই নিকট হতে কোনো কিছু পেতে আশা পোষণ করে। বিপদে পড়লে তাদের নিকটই নিষ্কৃতি চায়, উন্নতি তাদের নিকট থেকেই চায় লাভ করতে। মনে করেঃ এর অলৌকিকভাবে মানুষের দোয়া শুনতে ও কবুল করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, ফয়েজ করতে পারে। ভালো মন্দ করাতে ও ঘটাতে পারে। এই উদ্দেশ্যে তাদের সন্তোষ কামনা করে। আর তাদের সন্তোষ বিধানের জন্যেই তাদের উদ্দেশ্যে মানত করে, জন্তু জবাই করে, মরার পর তাঁদের কবরের উপর সিজদায় মাথা লুটিয়ে দেয়, নিজেদের ধন-সম্পদের একটা অংশ তাদের জন্য ব্যয় করা কর্তব্য মনে করে। আর এসব কারণেই দেখা যায়, এ শ্রেণীর লোকদের কবরকে নানাভাবে ইজ্জত ও তাজীম করা হচ্ছে, বহু অর্থ খরচ করে কবরের ওপর পাকা-পোখত কুব্বা নির্মাণ করা হচ্ছে। ধীরে ধীরে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর সফর করা হয়। এক নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে চারিদিক হতে ভক্তরা এসে জমায়েত হয়। ঠিক যেমন মুশরিক জাতিগুলো গমন করে তাদের জাতীয় তীর্থভূমে।
ইসলামের তওহীদী আকীদার দৃষ্টিতে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো নিকট-আর কাউকে সম্বোধন করে দো‘আ করা সুস্পষ্ট শিরক। ইসলামে তা স্পষ্ট ভাষায় নিষিদ্ধ। কুরআন মজীদে এ সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত তার অকাট্য প্রমাণ। কুরআনের কোনো কোনো আয়াতে মুশরিকদের লক্ষ্য করে, কোনো কোনো আয়াতে সাধারণভাবে এবং অনেক আয়াতে তওহীদবাদী মুসলিমদের লক্ষ্য করেই এই নিষেধ বাণী উচ্চারিত হয়েছে।
এ পর্যায়ে কুরআনের কয়েকটি আয়াত পেশ করা হচ্ছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ [٤٦:٥]
-আল্লাহকে বাদ দিয়ে(বা আল্লাহ ছাড়াও) যারা এমন সবকে ডাকে- দো‘আ করে, যারা তাদের জন্যে কিয়ামত পর্য্ন্তও জবাব দিতে পারবেনা আর তারা তাদের দো‘আ সম্পর্কে কিছুই জানেনা, এই শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অধিক গোমরাহ আর কে হতে পারে। (আল আহক্বাফ)
অপর এক আয়াতের ভাষা হলো এইঃ
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا [٧٢:١٨]
-সব মসজিদ-ই আল্লাহর। অতএব, আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেই ডাকবেনা। (জ্বীনঃ17)
এ আয়াতটিতে স্বয়ং রাসূলে করীম ও মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা ইবনে কাসীর লিখেছেনঃ আল্লাহ তাঁর বান্দাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, তারা যেন তাঁর ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাগুলোতে একমাত্র তাঁকেই ডাকে, তাঁরই একত্বকে প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং তাঁর সাথে অপর কাউকেই যেন ডাকা না হয়, তাঁর সাথে যেন কোনোরূপ শিরক করা না হয়।
একটি আয়াতে খোদ নবী করীম(স) কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছেঃ
তুমি আল্লাহর সাথে অপর কোনো ইলাহ্ কে একত্র করে ডেকোনা- একত্রিত করোনা। যদি তা করে, তাহলে তুমি আযাবপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে গণ্য হবে।
আয়াতে ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে স্বয়ং নবী করীম(স) কে। ‘তফসীরে ফতহুল বয়ান’ এ লেখা হয়েছেঃ আল্লাহতা‘আলা যখন কুরআনের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করলেন, প্রমাণ করে দিলেন যে, কুরআন তাঁর নিকট হতে অবতীর্ণ কিতাব, তখন তিনি তাঁর নবী মুহাম্মদ(স) কে নির্দেশ দিলেন এককভাবে কেবলমাত্র তাঁকেই ডাকবার, কেবল তাঁরই নিকট দো‘আ করার। আর আয়াতের শেষাংশের ব্যাখ্যা উক্ত তফসীরে লেখা হয়েছে এভাবেঃ
রাসূলে করীমকে বলা হয়েছে যে, যদি তুমি তাই করো, তাহলে তোমাকে আযাব দেয়া হবে। এখানে মুহাম্মদ(স) কে সম্বোধন করে একথা বলা হয়েছে। তিনি নিজে যদিও শিরকের গুনাহ হতে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ পবিত্র, তবুও তাঁকে লক্ষ্য করে একথা বলা হয়েছে তওহীদ সম্পর্কে মুমিন বান্দাগণকে উদ্বুদ্ধ করার ও সর্ব প্রকার শিরক-এর স্পর্শ হতে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে। তাহলে কথাটি এই দাঁড়াল যে, আল্লাহ বললেনঃ তুমি তো সৃষ্টিলোকের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত, আমার নিকট সবচাইতে মর্যাদাবান, সবচেয়ে বেশি প্রিয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তুমি যদি আমি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ আছে বলে বিশ্বাস করো, তাহলে আমি তোমাকেও আযাব দেবো। অতএব ভেবে দেখো, অন্যান্য বান্দারা এরূপ করলে তাদের পরিণতি কি হবে?
আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকেই ডাকা শির্ক, অন্য কারো নিকট দো‘আ করা শির্ক-অতএব সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত কয়টি থেকেও প্রমাণিত হয়।
وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ [١٠:١٠٦]
-আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডাকবেনা, যা তোমাকে কোনো উপকার দিতে পারেনা, তোমার কোনো ক্ষতি সাধনও করতে পারেনা। তুমিও যদি তা-ই করো, তাহলে তুমিও জালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।
সুরা মুমিন এর এ আয়াতটি এ পর্যায়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। দো‘আ সম্পর্কে ইতিবাচকভাবে পথনির্দেশ করেছে এ আয়াত।
আল্লাহতা‘আলাই ইরাশাদ করেছেনঃ
هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [٤٠:٦٥]
-তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া মাবুদ নেই। অতএব তোমরা ডাকো কেবল তাঁকেই একনিষ্ঠভাবে তাঁরই আনুগত্য সহকারে। আর সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, যিনি সারাজাহানের রব্ব।
আল্লাহকে জীবন্ত ও চিরঞ্জীব বলার মানে-ই হলো এই যে, তিনি ছাড়া আর যত মা‘বুদ-যাদের তোমরা মাবুদ বলে স্বীকার করো, বাস্তবভাবে যাদের তোমরা বন্দেগী ও দাসত্ব করো-তারা সবাই আসলে মৃত। জীবনের কোনো সন্ধানই সেখানে পাওয়া যাবেনা। আর যারা মৃত, জীবনহীন, তাদের ডাকার-তাদের নিকট কাতর স্বরে দো‘আর প্রার্থনা করার কি সার্থকতা থাকতে পারে। কেননা মৃতদের না দো‘আ শুনবার ক্ষমতা আছে, না শুনে তা কবুল করার ও দো‘আ অনুযায়ী কোনো কাজ করে দেবার আছে সামর্থ্য্। জীবন্ত ও চিরঞ্জীবতো একমাত্র আল্লাহ; তাঁর কোনো লয়, ক্ষয় বা কোনোরূপ অক্ষমতা নেই। অতএব কেবলমাত্র তাঁকেই ডাকা উচিত, তাঁরই নিকট দো‘আ ও প্রার্থনা করা বাঞ্চনীয়-সব সময়, সকল অবস্থায়। এর ব্যতিক্রম কিছু হতে পারেনা।
এ আয়াত থেকে আরো স্পষ্টভাবে জানা গেল যে, যিনি প্রকৃত ইলাহ, দো‘আ কেবল তাঁরই নিকট করা যেতে পারে এবং যাঁর নিকট দো‘আ করা হবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে বাস্তব আনুগত্য ও করতে হবে একমাত্র তাঁরই। আর দো‘আ কবুল হওয়ার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর জন্য সব তায়ীফ ও প্রশংসা উৎসর্গ করা। আন্তরিকভাবে আল্লাহর আনুগত্য বাস্তব জীবনে না করলে এবং মুখে অকৃত্রিমভাবে তাঁর প্রশংসা না করলে তাঁর নিকট দো‘আর করার কোনো অর্থ হয়না। তুমি যাঁর আনুগত্য করে চলতে রাজি নও, যার প্রশংসা ও শোকর তোমার মুখে ধ্বনিত হয়না, তাঁর নিকট তোমার দো‘আ করারও কোনো অধিকার থাকতে পারেনা। আর তিনিই বা সে দো‘আ কবুল করবেন কেন?
তাই সুরা আল আরাফে সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন আল্লাহতা‘আলাঃ
المُعتَدينَ ا يُحِبُّ ل إِنَّهُ وَخُفيَةً تَضَرُّعً رَبَّكُم ادعوا ۗ العٰلَمينَ رَبُّ اللَّهُ تَبارَكَ وَالأَمرُ الخَلقُ لَهُ أَلا
-সাবধান, মনে রেখ, সৃষ্টি তাঁরই, বিধানও তাঁরই চলবে। মহান বরকতওয়ালা আল্লাহতা‘আলা যিনি সারা জাহানের রব্ব। তোমরা ডাকো তোমাদের এই রব্বকে কাঁদ কাঁদ স্বরে, চুপে চুপে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।(আরাফঃ55)
এ আয়াত স্পষ্টভাবে আমাদের সামনে যে গভীর তত্ত্ব উদঘাটিত করে, তা হলো এই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ, অতএব দুনিয়া জাহানে আইন ও বিধান চলবে একমাত্র তাঁরই। এই সৃষ্টিকর্তা ও বিধানদাতা আল্লাহ বড় মহান, অসীম বরকতের মালিক। তোমাদের এই রব্বকেই তোমরা ডাকবে। ডাকবে কাঁদ কাঁদ স্বরে-বিনীত অবনত মস্তকে কাতর কন্ঠে। এবং ডাকবে গোপনে, অনুচ্চ স্বরে। আর শেষ কথাটি বলা হচ্ছে যে, যে লোক আল্লাহকেই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা বিধানদাতা বলে মানেনা, মানেনা বরকতওয়ালা মহান আল্লাহরূপে এবং তাঁরই নিকট যে লোক দো‘আর করেনা, বিপদে আপদে একমাত্র তাঁকেই ডাকেনা, তারাই সীমালংঘনকারী। আর সীমালংঘনকারীরা আল্লাহর ভালোবাসা পায়না।
কোনো কোনো মহল মনে করে যে, কুরআনে এসব আয়াতে যে ‘দো‘আ’ শব্দ উল্লিখিত হয়েছে, তার মানে হচ্ছে ইবাদত আর এ আয়াত কয়টির মানে হলোঃ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করোনা, তা করা শিরক। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট দো‘আ করা নিষিদ্ধ নয়, শিরক-ও নয়। কিন্তু এ কথা যে কতখানি ভুল ও প্রকৃত সত্যের বিপরীত, তা বলাই বাহুল্য। আসল কথা হলো, কুরআন মজীদের এসব আয়াতে যে দো‘আ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এর প্রকৃত অর্থঃ ধ্বনি দেয়া, আওয়াজ দেয়া এবং এমনভাবে কারো কাছে প্রার্থনা করা যার নিকট দো‘আ কবুল হতে বা প্রার্থিত জিনিস পাওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ বা সংশয় নেই। ইবাদত এ শব্দের প্রকৃত অর্থ নয়। তা হচ্ছে এর ‘মাজাজী’ বা পরোক্ষ অর্থ। আরবী অভিধানে বা শরীয়তে কোনো দিক দিয়েই এর অর্থ ‘ইবাদত’ নয়। আরবী ভাষার কোনো অভিধানেই এর অর্থ ইবাদত লেখা হয়নি। এমনকি জাহিলিয়াতের যুগের কোনো কবি-সাহিত্যিকের লেখায়ও এ শব্দের ব্যবহার এ অর্থে হতে দেখা যাবেনা। এখানে আমরা কয়েকটি আরবী প্রাচীণ ও প্রমাণিক অভিধান হতে কিছু উদ্বৃতি করছি।
আল জাওহীরি তাঁর অভিধানে লিখেছেনঃ
আরবী(*********)
আমি অমুক ব্যক্তিকে ডেকেছি, মানেঃ তার নাম করে আওয়াজ দিয়েছি, তাকে আহবান জানিয়েছি। তার জন্যে আল্লাহর নিকট দো‘আ করেছি। আর তার উপর বদদো‘আ করেছি। দাওয়াত মানে একবার ডাকা। আর দো‘আ হলো এক বচন শব্দ। এর বহুবচন দাওয়াত বা দো‘আসমূহ।
এখানে ‘দো‘আ’ শব্দের ভিন্ন রূপ ও প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। সবক্ষেত্রেই অর্থ হলো প্রার্থনা, ডাকা, আহবান করা।
আর আলকেমিস এ বলা হয়েছে-
দো‘আ মানে আল্লাহর দিকে নিষ্ঠাপূর্ণ আহবান , ঝোঁক প্রবণতা। তাঁকে ডাকো যেমন ডাকা দরকার। অপরের ওপর তাদের জন্য দাওয়াত অর্থাৎ দো‘আ তাদের থেকেই শুরু করা হবে। তাদের ডাকো, মানেঃ তাদের একত্রিত করো। নবী করীম(স) আল্লাহর (দিকে)আহবানকারী। মুয়াযযিনকেও আহবানকারী বলা হয়।
মোটকথা আরবী অভিধানের কোনো কিতাবেই দো‘আ মানে ইবাদত লিখিত হয়নি।
অবশ্য আল্লামা ইবনুল হাজার বলেছেনঃ দো‘আ শব্দটি ইবাদত অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু তা নিশ্চয়ই এ শব্দের প্রত্যক্ষ ও প্রকৃত অর্থ নয়, পরোক্ষ অর্থ হবে।
শায়খ আবুল কাশেম আল কুশাইরী লিখেছেনঃ কুরআনে দো‘আ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথাঃ ইবাদত, কাতর ফরিয়াদ, প্রার্থনা, কথা, আওয়াজ, ধ্বনি, প্রশংসা ইত্যাদি।
আল্লামা তাকীউদ্দীন আসসুবকী লিখেছেনঃ তা সত্ত্বেও এ আয়াতে ‘দো‘আ’ শব্দের বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করাই উত্তম।
কেননা দো‘আ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে যত আয়াতে তার কোথাও এমন কোনো কারণ দেখা যায়না, যার দরুণ শব্দটির আসল ও বাহ্যিক অর্থ গ্রহণের পরিবর্তে পরোক্ষ অর্থ গ্রহণ করা দরকারী হতে পারে। কুরআনের সব তাফসীরকারকই এই মত পোষণ করেছেন। কাজেই কুরআনের ব্যবহৃত ‘দো‘আ’ শব্দের ইবাদত অর্থ করা এবং এই সুযোগে আল্লাহ ছাড়া অন্য শক্তির নিকট দো‘আ করাকে জায়েয মনে করা চরম বাতুলতা এবং সুস্পষ্ট বিদয়াত ছাড়া আর কিছুই নয়।
কুরআনের আয়াতঃ
আরবী(********)
-ওয়ালা তাদয়ু মিন দুনিল্লাহী মালা ইয়ান ফায়ুকা ওয়ালা ইয়া দুররুকা ফায়ীন ফায়ালতা ফা ইন্নাকা ইজা লামিনাজ্জালিমীন।
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ
আয়াতের দো‘আ শব্দের অর্থ হলো উপকার পেতে চাওয়া, ক্ষতি থেকে বাঁচতে চাওয়া। আর আয়াতের অর্থ হলোঃ তুমি যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট উপকার বা ক্ষতির জন্য প্রার্থনায় মনোনিবেশ করো, তাহলে তুমি জুলুমকারী হবে। কেননা জুলুম বলা হয় কোনো জিনিসকে তার আসল জায়গা ছাড়া অন্য জায়গায় স্থাপন করা। আর আল্লাহ ছাড়া যখন কারোই কোনো ক্ষমতা নেই, তখন কোনো প্রকার ক্ষমতা চালানাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো প্রতি অর্পণ করা অন্য কারো ক্ষমতা চালাবার শক্তি আছে বলে মনে করা নিঃসন্দেহে জুলুম।
আর এই ‘দো‘আ’ শব্দের প্রকৃত অর্থ ‘ইবাদত’ না হলেও দো‘আ ও এক প্রকারের ইবাদত। অতএব তা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নিকট করা যেতে পারেনা।
তাহলে আল্লাহ ছাড়া নানাভাবে নানা শক্তি ব্যক্তির নিকট যে দো‘আ করা হয়, বিপদ মুক্তি ও দুনিয়ার উন্নতির জন্য প্রার্থনা করা হয়, নিরাময়তা চাওয়া হয়, সেগুলো কি হবে? সেগুলো যে সুস্পষ্ট শিরক হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং এ শিরক হচ্ছে ইসলামের তওহীদী সুন্নাতের এক মহা বিদয়াত। কেননা একজন যে অপরজনকে ডাকে, অপর একজনের নিকট দো‘আ করে এমন এক কাজের জন্যে, যা করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারোই নেই-থাকতে পারেনা। এভাবে ডাকার মানেই এই যে, সে তাকে অলৌকিক ক্ষমতার মালিক মনে করে, বিশ্বাস করে তার কিছু একটা করার ক্ষমতা আছে। তা মনে না করলে সে কিছুতেই তাকে ডাকত না, তার নিকট দো‘আর করতো না। ফলে তার মনে তার নিকট কেবল দো‘আ করেই ক্ষান্ত হয়না; শান্ত হয়না, বরং তার ইবাদত করতেও আগ্রহাণ্বিত হয়ে পড়ে। আর এরূপ হচ্ছে সুস্পষ্ট শিরক।
কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলোঃ
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٦:١٧]
-কোনো দুঃখ বা বিপদ যদি তোমাকে গ্রাস করে থাকে তা(আল্লাহর মর্জিতেই হয়েছে বলে মনে করতে হবে এবং তা)দূর করার কেউ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এমনিভাবে তুমি যদি কল্যাণ লাভ করে থাকো তবে তিনিই তো সর্বশক্তিমান। (আল আনআমঃ ১৫)
অর্থাৎ এ কল্যাণ দান করার ক্ষমতাও তাঁরই রয়েছে এবং তাঁরই অনুগ্রহে তুমি এ কল্যাণ লাভ করেছো। তিনি ছাড়া এ কল্যাণ তোমাকে আর কেউই দিতে পারেনি। কেননা অন্য কারোই কিছু করার ক্ষমতা নেই, সামর্থ্য নেই।
অপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ ۚ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [١٠:١٠٧]
-আল্লাহ যদি তোমাকে কোনো ক্ষতি বা বিপদ দেন, তবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ-ই দূর করতে পারবেনা। আর তিনিই যদি তোমার প্রতি কোনো কল্যাণ দান করতে ইচ্ছে করেন, তাহলে তাঁর এই কল্যাণ দানকে প্রত্যাহার করতে পারে এমন কেউ নেই। তবে তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান কল্যাণ দেন, তিনিই ক্ষমা দানকারী, করুণাময়। (ইউনূসঃ107)
এ আয়াত দুটো-এমনিভাবে কুরআনের আরো ভুরি ভুরি আয়াত এবং রাসূলে করীম(স) এর হাদীস স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ বিপদ দিতে পারেনা, কেউ সে বিপদ দূরও করতে সক্ষম নয় আল্লাহ ছাড়া। অনুরূপভাবে আল্লাহ ছাড়া কেউ কল্যাণ করতে পারেনা কারো। তিনি কারো কল্যাণ করতে চাইলে তা ফেরাতেও এবং সেই কল্যাণ হতে তাকে বঞ্চিত রাখতেও পারেনা কেউই। সব শক্তির একচ্ছত্র মালিকতো তিনিই। অতএব দো‘আ একমাত্র আল্লাহর নিকটই করা কর্তব্য। কর্তব্য সব রকমের বিপদ হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দো‘আ করা, কর্তব্য সব ধরণের কল্যাণ লাভের জন্য দো‘আ করা। এবং সেই দো‘আ হবে সরাসরি আল্লাহর নিকট, অন্য কারো অসীলা দিয়ে বা দোহাই দিয়ে নয়, অন্য কারো মাধ্যমেও নয়। তওহীদ বিশ্বাসের ঐকান্তিক দাবিও হলো এই। কেননা আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নিকট দো‘আ করার কোনো ফল নেই, নেই কোনো সার্থকতা।
আল্লাহতা‘আলা এই পর্যায়ে আরো স্পষ্ট ও বলিষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ
وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ [٣٥:١٣]
إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ[٣٥:١٤]
-আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা আর যার নিকটই দো‘আ করো, তাদের কেউ একবিন্দু জিনিসের মালিক নয়। তা সত্ত্বেও যদি তোমরা তাদেরই ডাকো- তাদের নিকটই দো‘আ করো, তবে তারা তো তোমাদের ডাকও শুনতে পারেনা। (আল ফাতীরঃ13-14)
তোমাদের দো‘আ আর যদি শুনতে পায়ও, তবু এ কথা চূড়ান্ত যে, তারা না দিবে তোমাদের ডাকের জবাব, না পারবে কবুল করতে তোমাদের দো‘আ।
বস্তুত দো‘আ যে কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই করতে হবে খালেসভাবে অপর কারো দোহাই দিয়ে নয়, কাউকে তাঁর নিকট অসীলা বানিয়ে নয়, একথা কুরআন মজীদে উদ্বৃত অসংখ্য দো‘আ থেকেও আমাদের শেখানো হয়েছে। কুরআনে উল্লেখীত যে কোনো দো‘আ-ই তার দলীল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআনের বিশেষ কয়েকটি দো‘আ উদ্বৃত করা হচ্ছে।
কুরআনের প্রথম সূরা আল ফাতিহায় উদ্বৃত হয়েছে এই দো‘আঃ
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [١:٦]
-হে আল্লাহ তুমিই আমাদের সরল সঠিক দৃঢ় পথ দেখাও-পরিচালিত করো সে পথে।
এরূপ দো‘আ করতে শেখানো হয়নিঃ হে আল্লাহ! অমুক পীরের অসীলায় আমাদের সরল সঠিক সুদৃঢ় পথ দেখাও।
সূরা আল বাকারা’র শেষ আয়াত কয়টিও আল্লাহর শিখিয়ে দেয়া দো‘আ। তাতে কোনো একটি কথা সরাসরিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট কিংবা কারো অসীলা ধরে আল্লাহর নিকট দো‘আ করার শিক্ষা দেয়া হয়নি। এই পর্যায়ে হযরত ইবরাহীম(আ) এর দো‘আ ও উল্লেখযোগ্য। কাবা ঘর নির্মাণের সময় তিনি এবং হযরত ঈসমাইল(আ) দো‘আ করেছিলেনঃ
رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ [٢:١٢٧
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ [٢:١٢٨]
-হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দো‘আ কবুল করো। তুমি সব-ই শোনো, সব-ই জানো। হে আমাদের আল্লাহ তুমি আমাদের দুজনকে মুসলিম-তোমার অনুগত বানাও। আর আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে এমন এক উম্মত জাগ্রত করো, যা হবে তোমার অনুগত। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের যাবতীয় ইবাদত বন্দেগীর-হজ্জ ও কুরবানীর নিয়ম-নীতি জানিয়ে দাও, আমাদের তওবা কবুল করো। কেননা তুমি তওবা কবুলকারী।
বস্তুত বান্দার মনে দুঃখ ও ব্যথা বেদনার কথা কেবল আল্লাহর নিকটই বলা যেতে পারে, বলতে হবে কেবলমাত্র তাঁরই সমীপে। কেননা সে দুঃখ বেদনার সৃষ্টিও যেমন হয়েছে আল্লাহর মঞ্জুরীতে, তা দূর করার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই রয়েছে। হযরত ইয়াকুব(আ) পুত্রহারা হয়ে তাঁর মর্মবেদনা পেশ করেছিলেন দুনিয়ার অপর কারো নিকট নয়, নয় কোনো পীর বা গদ্দীনশীনের নিকট; বলেছিলেন কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট।
তাঁর তখনকার কথা উদ্বৃত হয়েছে কুরআন মজীদে এ ভাষায়ঃ
আরবী(****)
-আমি আমার দুঃখ-বেদনা এবং চিন্তা-ভাবনার কথা কেবল আল্লাহর নিকটই প্রকাশ করছি, পেশ করছি।
হযরত মূসা(আ) এর দো‘আ ছিল নিম্নোক্ত ভাষায়ঃ
-আরবী (******)
-হে আল্লাহ! তোমার জন্যেই সব প্রশংসা, সব অভিযোগ তোমারই নিকট, কেবল তোমার নিকটই সাহায্য প্রার্থনা, কেবল তোমার নিকটই ফরিয়াদ। কেবল তোমার উপরই ভরসা। কেননা কোনো কিছু করার সামর্থ্য্ এবং ক্ষমতা ও শক্তি তুমি ছাড়া আর কারো নিকটই নাই।
আল্লাহ নিজেই হযরত জাকারিয়া এবং তাঁর স্ত্রীর প্রশংসা করে ইরশাদ করেছেনঃ
-আরবী (******)
-তারা ছিল সব কল্যাণময় কাজে উৎসাহী, প্রতিযোগী ও তৎপর। তারা কেবল আমাকে ডাকত-আমারই নিকট দো‘আ করতো আগ্রহ উৎসাহ এবং ভয় আতংক সহকারে। আসলে তারা সব সময় আমার জন্যেই ভীত হয়ে থাকত।
স্বয়ং আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ(স)-এর নীতিও ছিল তাই। কোনো ব্যতিক্রম ছিলনা এ থেকে। বদরের যুদ্ধে তাঁর সঙ্গী সাথীদের সংখ্যাল্পতা দেখে তিনি আল্লাহর দিকে মুখ করে দু’হাত তুলে দো‘আ করেছিলেনঃ
-আরবী (******)
-হে আল্লাহ! তুমি আমার কাছে যে ওয়াদা করেছ তা আজ পূর্ণ করো। হে আল্লাহ! ইসলামের ধারক এ মুষ্টিমেয় বাহিনীকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে যে দুনিয়ায় তোমার বন্দেগী করা হবেনা।
এর-ই পর আল্লাহর আয়াত নাযিল হলোঃ
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ [٨:٩]
-তোমরা যখন তোমাদের আল্লাহর নিকট-ই ফরিয়াদ করলে, তখন তিনি তোমাদের জবাব দিলেন, তোমাদের দো‘আ ও ফরিয়াদ কবুল করে নিলেন। এবং বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমি তোমাদের পর পর এক হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে সাহায্য করবো। (আনফালঃ 9)
এ আয়াত থেকে এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, ফরিয়াদ যদি একান্তভাবে আল্লাহর নিকট করা হয়, কোনো মাধ্যম, অসীলা আর ওয়াস্তা ছাড়াই, তাহলেই তিনি দো‘আ কবুল করেন, অন্যথায় তাঁর কোনো ঠেকা নেই কারো দো‘আ কবুল করার। কেউ তাঁকে সেজন্য বাধ্যও করতে পারেনা। দো‘আ কার কাছে করতে হবে সে কথা অধিক স্পষ্ট করে তোলবার জন্য নবী করীম(স) ঘোষণা করেছেনঃ তোমাদের প্রত্যেকেই যেন নিজের যাবতীয় প্রয়োজন কেবল আল্লাহর নিকট চায়। এমনকি কারো জুতার ফিতাও যদি ছিঁড়ে যায়, তবুও তাঁর নিকটই চাইবে। তিনি যদি না-ই দেন, তবে তা কেউ-ই দিতে পারবেনা।
আল্লাহর শিক্ষা ও রাসূলের শিক্ষাও এই যে, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত বিপদের কালে ফরিয়াদ করতে হবে একমাত্র আল্লাহর নিকট এবং তাতে অন্য কাউকে অসীলা ধরা কিংবা কারো দোহাই দেয়ার এই শিক্ষা-ইসলামের এই সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত। নবী-রাসূলগণই যদি নিজেদের সব ব্যাপারে কেবলমাত্র আল্লাহরই নিকট ফরিয়াদ করে থাকেন এবং এ ব্যাপারে আর কারো নিকট কোনো ইন্তেমদাদ(সাহায্য প্রার্থনা)না করে থাকেন, তাহলে আমরা সাধারণ মুসলমানরাই বা কেনো অন্য কারো প্রতি মুখাপেক্ষী হবো, নির্ভরশীল হবো, কেন অন্য কাউকে অসীলা ধরবো? অথচ এই নবী-রাসূলগণই তো আমাদের চিরন্তন আদর্শ। তাঁদের কাজও যেমন আমাদের কাছে অনুসরণীয় তেমনি অনুসরণীয় তাঁদের কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতিও। বিশেষত আল্লাহ এসব দো‘আ শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকেও অনুরূপ আল্লাহ মুখী হতে, কেবলমাত্র আল্লাহর নিকটই দো‘আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন।
অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যাচ্ছেনা যে, নবী করীমের(স) জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা বানিয়ে বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে আল্লাহর কাছে দো‘আ করেছেন তদানীন্তন মুসলমানেরা। হাদীসে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তা হলো রাসূলের জীবদ্দশায়, রাসূল নিজে একজন প্রার্থনাকারী হিসেবে লোকদের মাঝে উপস্থিত থাকা অবস্থায়। আর তা থেকে অতটুকুই প্রমাণিত হয়, রাসূলের জীবদ্দশায় তাঁকে অসীলা বানিয়ে দো‘আ করা জায়েয ছিল। কিন্তু রাসূলে করীমের ইন্তিকালের পর আর কোনো দিন সাহাবায়ে কিরাম তাঁকে দো‘আ প্রার্থনায় অসীলা বানাননি। ‘অসীলা’ বানানো হয়নি এমন কোনো ব্যক্তিকে যে মরে গেছে এবং যে নিজে দো‘আর অনুষ্ঠানে শরীক নেই। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদের আরো দু’টি আয়াত বিবেচ্য। সূরা সেজদায় আল্লাহ নেক বান্দাদের পরিচয় দান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ
تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ [٣٢:١٦]
-তাদের পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ সুখশয্যা হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই থাকে, তারা (তাদের আল্লাহর প্রতি) ভয় ও আশা পোষণ করেই ডাকতে থাকে তাদের আল্লাহকে। তদুপরি আমি তাদের যা দান করেছি তা থেকে (আমার পথে) ব্যয় করে।
এ আয়াতে ‘ইয়াদয়ুদা রাব্বাহুম খাওফান ওয়া তামআন’ বাক্যাংশ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আয়াতের প্রতি প্রকৃত যারা ঈমানদার তারা ভয় পায় কেবলমাত্র আল্লাহকে, আশা পোষণ করে একমাত্র আল্লাহর প্রতিই, যিনি তাদের রব্ব। বিপরীত অর্থে তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয়ও করেনা, কারো প্রতি কিছু আশাও পোষণ করেনা। আর ভয়ের কারণ হলেও তাঁরা ডাকে কেবল আল্লাহকে, আল্লাহর-ই নিকট দো‘আ প্রার্থনা করে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকটই প্রার্থনা করেনা। অনুরূপভাবে কোনো কিছু পাওয়ার আশাও করে কেবলমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে, সে জন্যেও দো‘আ করে তাঁরই নিকট। আল্লাহর নিকট ছাড়া আর কারো নিকট হতে কিছুই পাওয়ার আশা করেনা তারা এবং কোনো কিছু পাওয়ার প্রয়োজন হলে একমাত্র আল্লাহর নিকটই সেজন্য দো‘আ করে, প্রার্থনা করে।
তাছাড়া প্রথমাংশে বলা হয়েছে নামায পড়ার কথা, শেষাংশে বলা হয়েছে দো‘আ করার কথা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ দো‘আ ও নামায প্রকৃত অর্থের দিক দিয়ে একই জিনিস।
অর্থাৎ নামায যেমন আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্যে, কারো উদ্দেশ্যে পড়া হয়না, দো‘আ ও তেমনি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট করা যায়না।
আর একটি আয়াত হলোঃ
আরবী(*******)
-যে লোক আল্লাহর অনুগত-আল্লাহর-ই হুকুম পালনকারী, রাতের বেলা আল্লাহকে সেজদা করে, পরকালকে ভয় করে এবং কেবলমাত্র আল্লাহর রহমতেরই আশা করে, তার পরিণতি কি মুশরিক ব্যক্তিদের মতো হতে পারে?
তার মানে এসব গুণ যার আছে সে মুশরিক নয়, সে তওহীদবাদী। আর যার এসব গুণ নেই, নেই এর কোনো একটি গুণও, সে-ই মুশরিক হয়ে যাবে প্রকৃত ব্যাপারের দিক দিয়ে। যেমন কেউ যদি আল্লাহর অনুগত না হয়ে অনুগত হয় আল্লাহর সৃষ্ট কোনো শক্তির- যে লোক পরকালকে ভয় করেনা কিংবা যে লোক তার আল্লাহর রহমতের আশা করেনা বা আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো রহমত ও অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভের আশা পোঁষণ করে-কুরআনের এ আয়াতের ঘোষণা অনুযায়ী সে-ই মুশরিক হবে। অতএব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা কুরআনের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েয হতে পারেনা।
এ আলোচনার শেষ পর্যায়ে শায়খ আবদুল কাদের জিলানী(রহ) এর দু-তিনটি কথা এখানে প্রমাণ হিসেবে উদ্বৃত করা জরুরী মনে করছি। তিনি তাঁর গ্রন্থ…..এর শুরুতেই লিখেছেনঃ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য, যাঁর প্রশংসা সহকারে সব কিতাবই শুরু করা হয় এবং যাঁর জিকির করে সব কথা শুরু করতে হয়। তাঁরই প্রশংসার দৌলতে জান্নাতী লোকেরা জান্নাত পাবে, তিনিই এমন সত্তা যে তাঁর নাম উচ্চারণ করলে সব রোগ নিরাময় হয়, তাঁরই নামে সব চিন্তা দুঃখ ও বিপদ দূর হয়ে যায়। সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দকালে তাঁরই দরবারে কাতর কন্ঠে কাঁদ কাঁদ স্বরে দো‘আ করা হয়। তাঁর জাত-ই এমন যে, নানা বুলি ও নানা ভাষা হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত দো‘আ প্রার্থনাকারীর ডাক তিনি শুনেন, বিপদগ্রস্ত কাতর মানুষের দো‘আ তিনিই কবুল করেন।
তিনি তাঁর গ্রন্থ ‘ফাতাউল গায়েব’ এ লিখেছেনঃ আমাদের কান্না-কাটা, আমাদের দো‘আ এবং সব অবস্থায় আমাদের রুজু হতে হবে একমাত্র আল্লাহর-ই নিকট, যিনি আমাদের পরোয়ারদিগার, আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের রিযিকদাতা। তিনি খাওয়ান, তিনিই পান করান, তিনিই উপকার দেন, তিনিই মুহাফিজ, তিনিই নিগাহবান। আমাদের জীবন তাঁরই হাতে।
“অতএব তোমার প্রার্থনা হবে এবং নিজের প্রয়োজন পূরণের জন্য ডাকবে একমাত্র আল্লাহকেই, আল্লাহরই নিকটে, তিনি একাই তোমার দাতা, তিনি-ই তোমার লক্ষ্য হবেন।”
“যে লোক নিজেরই মতো কোনো মাখলুকের ওপর ভরসা করে, সে অভিশপ্ত।”
শায়খ জিলানী মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর পুত্র আবদুল ওহাব তাঁকে বললেনঃ “আমাকে এমন কিছু অসীয়ত করুন, আপনার পরে যা অনুসরণ করে আমি চলবো, আমল করবো”।
তখন তিনি বললেনঃ আল্লাহকে ভয় করে চলাই তোমাদের কর্তব্য; আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় করবেনা, আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কিছু চাইবেনা-কারো কাছ থেকে কিছু পাওয়ার আশা করবেনা। সব প্রয়োজনকেই এক আল্লাহর ওপরই সোপর্দ করে দেবে। সেই এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো নিকট কিছুমাত্র ভরসা করবেনা, নির্ভরতা গ্রহণ করবেনা। সব কিছু কেবল তাঁরই নিকট হতে পেতে চাইবে। আল্লাহ ছাড়া কারো প্রতি আস্থা স্থাপন করবেনা। তওহীদকেই ধারণ করবে, তওহীদকেই ধারণ করবে, তওহীদকেই ধারণ করবে। সকলেই এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।
এ পর্যায়ে শেষ কথা এই যে, দো‘আ কবুলকারী যদি কেবলমাত্র আল্লাহতা‘আলা ই হয়ে থাকেন, আর তিনি-ই যদি সরাসরি তাঁরই নিকট দো‘আ করতে বলে থাকেন, তাহলে অন্য কারো নিকট দো‘আ করা, দো‘আয় অন্য কাউকে অসীলা বানানো আল্লাহর ওপর খোদকারী ছাড়া আর কিছু নয়। যারা তা করতে বলে তারা শুধু বিদয়াতী-ই নয়, তারা সুস্পষ্টরূপে শিরক- এ লিপ্ত-শিরক প্রচারকারী তারা। ইসলামের তওহীদি আকীদায় শিরক-এর আমদানি করে।
বস্তুত ইসলামের ঐকান্তিক দাবি হলো, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে মা‘বুদ ও (অলৌকিকভাবে) প্রয়োজন পূরণকারী বলে মেনে নিতে সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করবে এবং কোনোরূপ শরীকদারী ছাড়াই একমাত্র আল্লাহ তা‘আলারই অনন্য মা‘বুদ হওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণ করবে। এই হচ্ছে প্রকৃত তওহীদী আকীদা এবং কালেমায়ে তাইয়্যেবার প্রথম অংশ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’ এর তাৎপর্য্। অতঃপর হযরত মুহাম্মদ(স) কে আল্লাহতা‘আলার রাসূল মানবে। অর্থাৎ জীবন যাপনে আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি, তা জানবার সর্বশেষ একমাত্র ব্যক্তি হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ(স)। তাই জীবন যাপনের অপরাপর নিয়ম ও পদ্ধতিকে-যা হযরত মুহাম্মদ(স) কর্তৃক প্রচারিত নয় তা-ও মেনে নিতে অস্বীকার করতে হবে। কলেমার দ্বিতীয় অংশের এই হচ্ছে তাৎপর্য্।
পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণও তাঁদের উম্মতদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহ যে উত্তরকালে তারা গোমরাহ হয়ে শিরকে নিমজ্জিত হয়েছে। এই পর্যায়ে হযরত মুহাম্মদ(স) কালেমার এই উভয় পর্যায়ে বৈপরীত্য শিরক ও বিদয়াতের গোমরাহীতে নিমজ্জিত হওয়ার ব্যাপারে খুব বেশি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কেননা তার কোনো একটি দিক দিয়েও শিরকে নিমজ্জিত হলে নিঃসন্দেহে জাহান্নামে যেতে হবে।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি