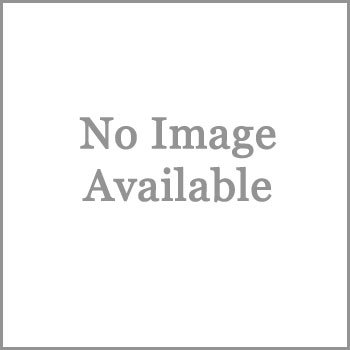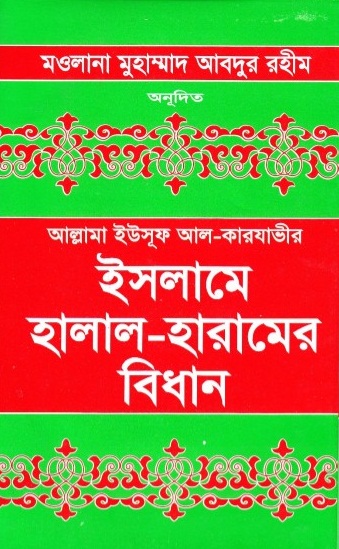চতুর্থ অধ্যায়
আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় অন্ধ অনুসরণ
পারস্পরিক কাজকর্ম ও লেনদেন
খেলা-তামাসা ও স্ফূর্তির অনুষ্ঠান
সামাজিক-সামষ্টিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ
অমুসলিমদের সাথে সম্পর্ক
আকীদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় অন্ধ অনুসরণ
সুস্থ সঠিক ও নির্ভুল আকীদা-বিশ্বাসই হচ্ছে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি। আর তওহীদ-সর্বতোভাবে আল্লাহ্ এক-একক ও অদ্বিতীয়- বিশ্বাসই হচ্ছে এ আকীদার নির্যাস এবং পূর্ণ দ্বীন ইসলামের প্রাণশক্তি। নির্ভুল আকীদা ও খালেস তওহীদের সংরক্ষণকেই ইসলাম তার শরীয়ত গঠনে ও শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে চরম লক্ষ্য হিসেবে সম্মুখে রেখেছে। সেই সাথে মূর্তি পূজারীরা যে জাহিলী আকীদা-বিশ্বাস ব্যাপকভাবে প্রচার করে রেখেছিল, তার বিরোধীতা ও মূলোৎপাটনও তাকে করতে হয়েছে। কেননা মুসলিম সমাজ-সামষ্টিকে শিরকের মলিনতা-কদর্যতা ও গুমরাহীর অবশিষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্যে এ কাজ একান্তই অপরিহার্য।
আল্লাহর সুন্নাতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা
ইসলাম তার অনুসারীদের মন-মগজে সর্বপ্রথম এ বিশ্বলোক সংক্রান্ত দর্শনকে সুদৃঢ় করেছে। ইসলাম ঘোষণা করেছে, মানুষ এ বিশ্বলোকের বিরাট ব্যবস্থার অধীন তার পৃথিবীর ওপর ও আকাশ মণ্ডলের নিচে জীবন যাপন করে। এ বিরাট বিশ্বলোক কোন ‘মগের মুল্লুক’ নয়, ছেলে-শিশুদের খেলনা নয়। তা হেদায়েতের বিধান ছাড়া চলছে না, ইচ্ছামত যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে না। তা কোন সৃষ্টির কামনা-বাসনা অনুযায়ীও চালিত হচ্ছে না। কেননা সৃষ্টির কামনা-বাসনা এক ও অভিন্ন নয়, পরস্পর সামঞ্জস্য সম্পন্ন নয় বরং পরস্পর সাংঘর্ষিক। তাও যে বিভ্রান্ত ও দিশেহারা তা-ও নিঃসন্দেহ। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
প্রকৃত মহাসত্য যদি তাদের কামনা বাসনা অনুসরণ করে চলত, তাহলে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা সবই ধ্বংস ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। (সূরা আল-মুমিনীনঃ ৭১)
বস্তুত এ বিশ্বলোক প্রাকৃতিক আইন ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্নাতের সুদৃঢ় বন্ধনে বন্দী। এ নিয়ম ও আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্নাতের কোন পরিবর্তন নেই, তাতে নেই কোনরূপ ব্যতিক্রম। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানেই এ কথা বলিষ্ঠ ঘোষিত হয়েছে। সূরা ফাতির-এ বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহর সুন্নাত- নিয়ম-কানুনে কোনরূপ পরিবর্তন বা ব্যতিক্রম দেখতে পাবে না।
কুরআন ও সুন্নাত মুসলমানকে শিক্ষা দিয়েছে যে, এসব প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনকে সম্মান করা- তার মর্যাদা রক্ষা করা কর্তব্য। কার্যকারণ প্রয়োগে ফলাফল লাভের জন্যে চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালাবে। কেননা আল্লাহ্ প্রতিটি কাজের মূলে ‘কারণ’ রেখেছেন এবং এ দুয়ের মধ্যে গভীর সম্পর্ক সংস্থাপন করে নিয়েছেন। ইবাদতগাহের পরিচালক, ধোঁকা প্রতারণার পেশাধারী ও ধর্ম-ব্যবসায়ীরা নিজেদের সার্থোদ্ধারের মতলবে যে সব কাল্পনিক গোপন কার্যকারণকে উপার্জন উপায়রূপে অবলম্বন করেছে, তার প্রতি কোন মুসলমানই একবিন্দু ভ্রুক্ষেপ করতে ও তার গুরুত্ব মেনে নিতে পারে না।
কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই
বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা) যখন দুনিয়ায় আগমন করলেন, তখন তিনি সমাজে ধোঁকাবাজদের দল-কে দল দেখতে পেলেন। তারা গণকদার বা জ্যোতিষী নামে পরিচিত ছিল। গায়েবের অতীত বা ভবিষ্যতে সঙ্ঘটিত বা ব্যাপারাদি জ্বিনদের মাধ্যমে জেনে নিতে পারে বলে দাবি করত। এ ধোঁকা-প্রতারণা কুরআন ও সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী বলে নবী করীম (সা) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি সকলকে আল্লাহর কালাম শোনালেনঃ ( আরবি******************)
আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীতে যারাই রয়েছে তারা কেউই ‘গায়ব’ জানে না, সব কিছু জানেন একমাত্র আল্লাহ্। (সূরা নামলঃ ৬৫)
অতএব ফেরেশতা, জ্বিন বা মানুষ কেউই ‘গায়ব’ জানতে পারে না।
রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর এ ঘোষণাও পাঠ করে শোনালেনঃ ( আরবি******************)
আমি (মুহাম্মাদ) যদি গায়ব জানতাম, তাহলে বেশি বেশি কল্যাণ ও মঙ্গল আমি নিজের জন্যে করে নিতাম এবং কোনরূপ খারাবী আমাকে স্পর্শ পর্যন্তও করতে পারত না। আমি তো শুধু প্রদর্শনকারী, সুসংবাদদাতা ঈমানদার লোকদের জন্যে।
হযরত সুলায়মানের খেদমতে নিয়োজিত জ্বিনদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা জানিয়ে দিলেনঃ ( আরবি******************)
ওরা যদি গায়ব জানতই, তাহলে তারা সেই অপমানকর আযাবে দীর্ঘদিন বন্দী হয়ে থাকত না। (সূরা সাবাঃ ১৪)
অতএব যে লোক প্রকৃত গায়ব জানার দাবি করে, সে আল্লাহ্, প্রকৃত ব্যাপারে এবং সমস্ত মানুষের ওপর সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট মিথ্যা আরোপ করে।
নবী করীম (সা)-এর কাছে বিভিন্ন প্রতিনিধি দল এসে উপস্থিত হয়েছিল। তাদের ধারণা ছিল, নবী করীম (সা)-ও বুঝি গায়ব জানার দাবি করেছেন। এ ব্যাপারে তারা নবী করীম (সা)-এর পরীক্ষাকরণের উদ্দেশ্যে হাতের মুঠির মধ্যে কিছু গোপন করে জিজ্ঞেস করলঃ ‘বলুন তো আমাদের মুঠোর মধ্যে কি আছ।’ নবী করীম (সা) তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলে দিলেনঃ ( আরবি******************)
আমি কোন গণকদার নই। জেনে রাখ, গণকদার, গণকদারী ও গণকদার গোষ্ঠী সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।
গণকদারকে বিশ্বাস করা কুফর
ইসলাম কেবল গণকদার ও ধোঁকাবাজ প্রতারকদের বিরুদ্ধে কথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি। যারা নিজেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত ধারণা সম্পন্ন হওয়ার দরুন তাদের কাছে যায়, জিজ্ঞস করে ও জানতে চায় এবং তাদের সত্য বলে বিশ্বাস করে, তাদেরকেও ইসলাম ওদের সঙ্গেই শরীক করে নিয়েছে এবং উভয় শ্রেণীর লোকদের অভিন্ন পরিণতির কথা ঘোষণা করেছে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক জ্যোতিষীর কাছে গেল, তাকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞেস করল এবং সে যা বলল তাতে তাকে সত্যবাদী বলে বিশ্বাস করে নিল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোন নামাযই কবুল হবে না।
অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক গণকদারের কাছে গেল এবং সে যা বলল, ততে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে হযরত মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ দ্বীনকে অবিশ্বাস করল- কাফির হয়ে গেল। (বাজ্জার)
তা এজন্যে যে, মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি নাযিল হয়েছে যে, গায়েব কেবলমাত্র আল্লাহই জানেন, মুহাম্মাদ (সা) গায়ব জানেন না, অন্যরা তো বটেই। কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
বল, আমি বলছি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডারসমূহ রয়েছে, আমি গায়বও জানি না, আমি তোমাদের একথাও বলছি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমি তো অনুসরণ করি শুধু তাই যা আমার কাছে ওহী হয়ে আসে।
মুসরমান যখন কুরআন মজীদ থেকে একথা স্পষ্ট ও অকাট্যভাবে জানতে পারল, তার পরও বিশ্বাস করল যে, কোন কোন সৃষ্টি- মানুষ বা জ্বিন্- তকদীরের নিগূঢ় রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম এবং তারা গয়বী জগতের জ্ঞানের অধিকারী, তাহলে তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর কাছে অবতীর্ণ দ্বীন-ইসলামকে সম্পূর্ণরূপেই অস্বীকার করল, তার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করল।
পাশার দ্বারা ভাগ্য জানতে চাওয়া
পূর্বোল্লেখিত যুক্তির ভিত্তিতেই ইসলাম পাশার সাহায্যে ভাগ্য জানতে চাওয়াকে সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে।
‘পাশা’ বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে, কতগুলো তীর। জাহিলিয়াতের যুগে আরবরা তার সাহায্যে ভাগ্য জানবার জন্যে চেষ্টা করত, সেজন্যে সেগুলোকে ব্যবহার করত। তার একটার উপর লেখা থাকত, ‘আমাকে আমার আল্লাহ্ নির্দেশ দিয়েছেন’। দ্বিতীয়টির ওপর লেখা থাকত, ‘আমাকে আমার আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন’। তৃতীয়টি থাকত সম্পূর্ণ খালি। তার ওপরু কিছুই লেখা থাকত না। তারা যখন বিদেশ যাত্রার ইচ্ছা করত কিংবা বিয়ে ইত্যাদি কাজের ইচ্ছা করত, তখন তারা মূর্তির ঘরে উপস্থিত হতো। আর তাতেই রক্ষিত থাকত এই তীরসমূহ। এখন তাদের ভাগ্যে কি লেখা আছে তা তারা জানতে চাইত। যদি প্রথম তীরটি- যাতে ‘আদেশ করেছেন’ লেখা রয়েছে- বের হতো, তাহলে তারা অগ্রসর হতো। আর যদি নিষেধ লেখা তীরটি বের হতো, তাহলে তারা প্রস্তাবিত কাজ থেকে বিরত থাকত। আর খালি তীরটি বের হলে তারা বারবার তীর বের করত- যেন সুস্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়।
আমাদের সমাজে জাহিলিয়াতের ঠিক এ ধরনটি প্রচলিত না থাকলেও এর সাথে সাদৃশ্য সম্পন্ন বেশ কিছু কাজ প্রচলিত রয়েছে। যেমন ‘রমন’ কড়ি, কিতাব খুলে ফাল লওয়া। তাসের পাতা বা পেয়ালা পড়া ইত্যাদি এ পর্যায়ে যা কিছু করা হয়, ইসলামে তা সবই সম্পূর্ণ হারাম।
আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের প্রতি যেসব খাদ্য হারাম করেছেন, তার উল্লেখের পর বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা তীরসমূহ দ্বারা ভাগ্য জানতে চাইবে, তা হারাম, তা আল্লাহর আইন লংঘনমূলক কাজ। (সূরা মায়িদাঃ ৩)
আর নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক গণকদারী করল কিংবা তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চেষ্টা করল অথবা খারাপ ‘ফাল’ লওয়ার দরুন বিদেশ সফর থেকে ফিরে গেল, সে উচ্চতর মর্যাদা লাভ করতে পারবে না কখনও। (বুখারী, মুসলিম)
যাদুবিদ্যা
আনুরূপভাবে ইসলাম যাদুবিদ্যা ও যাদুকরদের মুকাবিলা করেছে। যারা যাদুবিদ্যা শিখে, তাদের সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তারা এমন বিদ্যা শিখে যা তাদের ক্ষতি করে, কোন উপকার দেয় না।
নবী করীম (সা) যাদু কার্যকে ধ্বংসকারী কবীরা গুনাহর মধ্যে গণ্য করেছেন. তা ব্যক্তির পূর্বে জাতিকে ধ্বংস করে। পরকালের পূর্বে এ দুনিয়াই যাদুকররা চরমভাবে বিপর্যয়ের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা সাতটি ধ্বংসকারী কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবিগণ বললেনঃ হে রাসূল, সে সাতটি কি কি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা, যাদুবিদ্যা, আল্লাহ্ যে প্রাণী হত্যা করাকে হারাম করেছেন- ইনসাফের ভিত্তিতে হত্যা করা ছাড়া- সেই নর হত্যা, সুদ খাওয়া, ইয়াতীমের ধন-মাল ভক্ষণ-হরণ, যুদ্ধের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন এবং ঈমানদার অসতর্ক মহিলাদের সম্পর্কে মিথ্যা মিথ্যা ব্যভিচারের দোষারোপ করা। (বুখারী, মুসলিম)
কোন কোন ফিকাহবিদ যাদুবিদ্যা বা যাদুকার্যকে কুফরি বলেছেন, কিংবা বলেছেন, তা মানুষকে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। অপর কোন কোন ফিকাহবিদ এ মত দিয়েছেন যে, যাদুকরের দুষ্কৃতি থেকে সমাজকে পবিত্র রাখার জন্যে তাকে হত্যা করা ওয়াজিব।
কুরআন মজীদ আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যাদুকরদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাওয়ারঃ ( আরবি******************)
ফুঁ দিয়ে গিয়ে কসে বাঁধে যেসব নারী, তাদের দুষ্কৃতি ও ক্ষতি থেকে, হে আল্লাহ্ তোমার কাছে পানা চাই।
গিড়ের মধ্যে ফুঁ দেয়া যাদু করার একটা পদ্ধতি এবং এটা যাদুকরদের একটা বিশেষ ধরনের কাজ। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক গিড়েতে ফুঁ দিল, সে যাদু করল। আর যে যাদু করল সে শিরক করল।
গণদারদের কাছে যাওয়া এবং গায়বী ও রহস্যাবৃত বিষয়াদি জানতে চেষ্টা করাকে যেমন ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে, তেমনি যাদু বা যাদুকরদের কাছে কোন রোগের চিকিৎসার্থে বা কোন সমস্যার সমাধানের জন্যে আশ্রয় গ্রহণকেও সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। নবী করীম (সা) এ কাজ থেকে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্কতার কথা ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক গণকদারী করল বা যার জন্যে গণকদারী করা হলো, যে ফাল গ্রহণ করল কিংবা যার জন্যে ফাল গ্রহণ করা হলো কিংবা যে যাদুগিরি করল বা যার জন্যে যাদুগিরি করা হলো, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।
হযরত ইবনে মাসঊদ বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক কোন গণকদার বা যাদুকর কিংবা গায়বী কথা বলার লোকের কাছে গেল, তাকে জিজ্ঞেস করল এবং সে যা বলল তা সে সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মুহাম্মাদ (সা)-এর প্রতি অবতীর্ণ দ্বীন-ইসলামকে অস্বীকৃতি জানাল, তা অবিশ্বাস করল।
রাসূলে করীম (সা) আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মদ্যপায়ী, যাদু বিদ্যায় বিশ্বাসী ও রক্তসম্পর্ক ছিন্নকারী কখনই জান্নাতে যাবে না।
এসব হাদীসের আলোকে জানা গেল যে, কেবল যাদুকরের কাজই হারাম নয়, যাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী এবং গণকদার বলে তাকে যে সত্য মানে, তার এ কাজও সম্পূর্ণ হারাম।
যদি মূলত হারাম কাজের উদ্দেশ্যে এ যাদুবিদ্যা ব্যবহৃত হয়, যেমন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি, দৈহিক ক্ষতি সাধন প্রভৃতি তাহলে আরও কঠিন হারাম হয়ে দাড়ায়, আর যাদুকররা যে সাধারণত এসব কাজ করে তা সকলেই জানেন।
তাবীজ ব্যবহার
তাবীজ-তুমার ব্যবহারও এ পর্যায়েরই কাজ। তাতে এ বিশ্বাস মনে নিহিত থাকে যে, তাবীজ বাঁধলেই রোগ সেরে যাবে বা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল যুগেও এমন বহু লোকই রয়েছে যারা নিজেদের ঘরের দুয়ারে ঘোড়ার ‘জুতা’ বাঁধে। আজকের দুনিয়ায় এমন লোকেরও অভাব নেই যারা জনগণের মূর্খতা-অজ্ঞতার সুযোগে বৈষয়িক অর্থনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করার কাজে দিন-রাত ব্যস্ত। তারা তাদের জন্যে তাবীজ লিখে। এসব তাবীজে রেখা ও ধাঁধা অঙ্কিত থাকে। তারা তাদের সম্মুখে কিরা-কসম করে নিজেদের সত্যতা ও দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করে। মন্ত্র পড়ে তাবীজের ওপর ফুঁ দেয়। দাবি করে যে, তাবীজ-তুমার বাঁধলে জ্বিনের কুপ্রভাব পড়তে পারে না, ভূত-প্রেত, কুদৃষ্টি বা হিংসা-পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি কোন ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এসব ইসলাম সমর্থিত চিকিৎসা পদ্ধতি নয়।
রোগমুক্তি, রোগ প্রতিরোধ ও রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে ইসলাম পরিচিত পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করেছে। যারা সে সব পরিহার-প্রত্যাখ্যান করে গুমরাহীর পথ অবলম্বন করে তাদের তিরষ্কার করেছে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা রোগের চিকিৎসার্থে ঔষধ ব্যবহার কর। কেননা যিনি রোগ সৃষ্টি করেছেন, তিনি তার ঔষধও সৃষ্টি করেছেন। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের এ সব ঔষধের মধ্যে তিনটি জিনিস খুবই উপকারী। তা হচ্ছে, মধু পান করা, রক্ত চুসার ছুরি কিংবা আগুনে দাগাঁনো। (বুখারী, মুসলিম)
একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে, রাসূলে করীমের বিশেষ উপকারী এ তিনটি ঔষধই চিকিৎসা প্রক্রিয়ার আধুনিক কালের চিকিৎসা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। মুখে খাওয়া ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা, অস্ত্রোপাচারের সাহায্যে রোগমুক্তি এবং দাগানো পন্থায় রোগের নিরাময়তা অর্জন। বিদ্যুৎ তাপ বা ছ্যাঁকের চিকিৎসা এই তৃতীয় পর্যায়ের মধ্যে শামিল এবং তা অত্যাধুনিক পদ্ধতি। অতএব এ সব চিকিৎসাই বৈধ।
রোগ প্রতিরোধ বা চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তাবীজ বাঁধা কিংবা যাদু-মন্ত্র পাঠ সুস্পষ্ট মুর্খতা ও গুমরাহী এবং তা আল্লাহ্ প্রদত্ত সুন্নাত ও তওহীদী আকীদার পারিপন্থী। হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেনঃ দশ ব্যক্তি সমন্বয়ে সঠিক এক প্রতিনিধিদল নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হলো, তন্মধ্যে নয়জনের কাছ থেকে তিনি বায়’আত গ্রহণ করলেন, একজনের বায়’আত নিলেন না। তাদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেনঃ ( আরবি******************)
ও লোকটির বাহুতে তাবীজ বাঁধা রয়েছে। এ কথা শুনে লোকটি তাবীজ ছিঁড়ে ফেলল। পরে নবী করীম (সা) তারও বায়’আত গ্রহণ করলেন, এবং পরে বললেনঃ যে লোক তাবীজ বাঁধে সে শিরক করে। (আহমদ, হাকেম)
অপর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক তাবীজ বেঁধেছে, আল্লাহ্ তাকে সাফল্যমণ্ডিত করবেন না। আর যে লোক মাদুলী বাধল, আল্লাহ্ তাকে একবিন্দু শন্তি ও স্বস্তি দেবেন না। (আহমদ)
ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, নবী করীম (সা) এব ব্যক্তির বাহুতে পিতলের মাদুলি বা কবজ বাঁধা দেখতে পেলেন। বললেনঃ তোমার জন্যে আফসোস! তুমি ওটা কি বেঁধে রেখেছ? বললঃ এটা দুর্বলতা দূর করার উদ্দেশ্যে বেঁধেছি। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
ওটা তোমার দুর্বলতা অধিক বৃদ্ধি করবে, ওটা ফেলে দাও। নতুবা ওটা বাধা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তাহলে কস্মিনকালেও তুমি কল্যাণ পেতে পারবে না। (আহমদ, ইবনে হাব্বান)
এ সব শিক্ষা সাহাবিগণের ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে তাঁরা নিজেরাই এসব উপায়-উপকনণ ও বাতিল পন্থা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।
ঈসা ইবনে হামযা বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুকাইমের কাছে গেলাম তাঁর বিসর্প (Erysipelas- an inflammation of the skim with redness) রোগ হয়েছিল। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনি এ রোগের জন্যে কোন তাবীজ-কবজ বাঁধেন না কেন? জবাবে তিনি বললেনঃ
( আরবি******************) আমি তা থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই।
অপর বর্ণনায় তাঁর উক্তি এইঃ ( আরবি******************)
তার অপেক্ষা মৃত্যু অতি নিকটবর্তী যে লোক কিছু একটা ঝুলাবে, বাঁধবে, তাকে তারই ওপর ছেড়ে দেয়া হবে।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা) তাঁর স্ত্রীর কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন, তার গলায় কি যেন বাঁধা রয়েছে। তিনি তা টেনে ছিড়ে ফেললেন। পরে বললেনঃ ( আরবি******************)
আবদুল্লাহর বংশের লোকেরা শিরক করা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে, যে বিষয়ে আল্লাহ্ কোন দলিল নাযিল করেন নি।
পরে তিনি বললেন, আমি নবী করীম (সা)-কে বলতে শুনেছিঃ ( আরবি******************)
তাবীজ-তুমার, কবজ, তাওলা ইত্যাদি সব শিরক। লোকেরা জিজ্ঞেস করলঃ ‘তাওলা’ কাকে বলে? তিনি বললেন, তা এমন একটা তদবীর ও আমল যা মেয়ে-লোকেরা স্বামীদের বেশি ভালবাসা পাওয়ার জন্যে ব্যবহার করে।
সহজকথায় ‘তাওলা’-ও এক প্রকার যাদু।
আলিমদের মত হচ্ছে, যে সব তাবীজ আরবী ভাষায় লিখিত নয়, তাতে কি লিখিত রয়েছে তা জানা বোঝা যায় না- তাতে যাদুও থাকতে পারে, কুফরি কথাবার্তাও থাকতে পারে। তাই তা নিষিদ্ধ। কিন্তু যদি তার অর্থ ও মর্ম বোঝা যায় এবং তাতে আল্লাহর যিকির বা নাম উল্লেখ থাকে, তবে তা নিষিদ্ধ বা হারাম নয়। এরূপ অবস্থায় তাবীজ দো’আ পর্যায়ে গণ্য। চিকিৎসা নয়, ঔষধও নয়, আল্লাহর সাহায্যের আশা মাত্র। জাহিলিয়াতের যুগে ব্যবহৃত তাবীজে যাদু, শিরক বা রহস্যপূর্ণ কথাবার্তা থাকত, যার কোন অর্থ বোঝা যেত না। এ জন্যে তা হারাম ঘোষিত হয়েছিল।
হযরত ইবনে মাসউদ (রা) তাঁর স্ত্রীকে জাহিলিয়াতের এসব মন্তর ও তাবীজ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি জবাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করলেন। বললেনঃ আমি একদিন বাইরে বের হলাম, তখন অমুক ব্যক্তি আমাকে দেখে ফেলল। আমার দুই চোখ থেকে অশ্রু ধারা প্রবাহিত হতে শুরু করল।
পরে আমি মন্ত্র পড়লে চোখের পানি বন্ধ হয়ে গেল। মন্ত্র পড়া বন্ধ করলে আবার ফরফর বেগে পানি পড়তে শুরু করে। ইবনে মাসউদ বললেনঃ ( আরবি******************)
এ হচ্ছে শয়তান। তুমি যখন ওকে মেনে নাও, তখন সে তোমাকে ছেড়ে দেয়। আর তুমি যখন তার অবাধ্যতা কর তখন সে তার আঙ্গুলী দিয়ে তোমার চোখে খোঁচা দেয়। কিন্তু তুমি নবী করীম (সা) যা করতেন তাই যদি কর তাহলে তা তোমার জন্যে খুবই ভাল এবং সম্ভবত তুমি নিরাময়তাও লাভ করতে পারবে। তা হচ্ছে, নিজের চোখে পানি দাও এবং বল দো’আ। (ইবনে মাজাহ, আবূ দাউদ)
খারাপ লক্ষণ গ্রহণ
কোন কেন জিনিস থেকে খারাপ লক্ষণ গ্রহণ- তা কোন স্থান, কোন ব্যক্তি বা অন্য যে কোন জিনিস থেকেই হোক, তা ভিত্তিহীন কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। বহু আগের ও প্রাচীনতম কাল থেকেই তা মানব সমাজে চলে এসেছে এবং আরও বহুকাল অবধি হয়ত তা চলতেও থাকবে। বহু ব্যক্তি ও বহু মানব গোষ্ঠীকেই এর মধ্যে নিমজ্জিত দেখতে পাওয়া যায়। হযরত সালেহ্ নবীর সময়ের লোকেরা বলেছিলঃ ( আরবি******************)
আমাদের মতে তো তুমি এবং তোমার সঙ্গী সাথী খারাপ লক্ষণ বিশেষ।
ফিরাঊন ও তার লোকদের ওপর কোন বিপদ ঘনীভূত হয়ে এলেঃ ( আরবি******************)
তারা মূসা ও তাঁর সঙ্গীদের কুলক্ষণ মনে করতে শুরু করে দিত।
চরম গুমরাহীতে নিমজ্জিত বিপুল সংখ্যক কাফিরের ওপর সেকালে নবী-রাসূলগণের দাওয়াত অস্বীকার করার দরুন যখন কোন বিপদ আপতিত হতো, তখন তারা বলতঃ
( আরবি******************) আমরা তোমাদেরকে কুলক্ষণে মনে করি।
এর জবাবে নবী-রাসূলগণ বলতেনঃ
( আরবি******************)- তোমাদের কুলক্ষণ তো তোমাদের সঙ্গে লেগে আছে।
অর্থাৎ তোমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ তোমাদেরই সঙ্গী। আর তা হচ্ছে, তোমাদের কুফরি, আল্লাহর সাথে তোমাদের শত্রুতা এবং আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
খারাপ লক্ষণ গ্রহণে জাহিলিয়াতের যুগের আরবদের বিশ্বাস ছিল ভিন্নতর। কিন্তু ইসলাম এসে সেই সবকে বাতিল ঘোঘণা করে এবং তাদের চালিত করে সুদৃঢ় ও বিবেক বুদ্ধিসম্মত পথে।
নবী করীম (সা) কুলক্ষণ গ্রহণকে গণকদারী ও যাদুক্রিয়ার সাথে একই সুত্রে গেঁথেছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক নিজে কুলক্ষণ গ্রহণ করবে বা যার জন্যে কুলক্ষণ গ্রহণ করা হবে বা গণনা করা হবে কিংবা যাদু করবে যার জন্যে যাদু করা হবে সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (তিবরানী)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
রমল, পাখির উড়ানো কুলক্ষণ গ্রহণ ও পাথরকুচি নিক্ষেপ করে খারাপ লক্ষণ গ্রহণ- এ সবই কুসংস্কার বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত।
এ কুলক্ষণ গ্রহণ কোন জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর ভিত্তিশীল নয়। এর সাথে বাস্তবতারও কোন সম্পর্ক নেই। এটা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও মানসিক দুর্বলতার ফসল। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন-মানসিকতার দরুনই মানুষ লক্ষণ- তা কু হোক বা শুভদ্বারা চালিত হতে প্রস্তুত হয়ে থাক। নতুবা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে, কোন নির্দিষ্ট স্থানকে কিংবা গ্রহ-তারকার কোন কক্ষে প্রবেশ করাকে কুলক্ষণের প্রতীক মনে করার কি অর্থ থাকতে পারে? কোন পাখির আওয়াজ শুনলেই যাত্রা অশুভ হয়ে যাবে কিংবা চোখের পাতার কম্পনে ভাল বা মন্দ নিহিত থাকবে অথবা কোন বিশেষ শব্দ শুনলেই সমস্ত সংকল্প নড়বরে হয়ে যাবে, এমন কথার সাথে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।
আসলে মানুষের ভিতরে স্বভাবগতভাবে নিহিত দুর্বলতার দরুনই কোন কোন জিনিস থেকে ‘লক্ষণ’ গ্রহণ করে। অতএব বুদ্ধিমান সচেতন মানুষের কর্তব্য কোনরূপ দুর্বলতার কাছে মাথা নত না করা।
একটি মরফু হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তিনটি জিনিস এমন রয়েছে, যা থেকে খুব কম লোকই রক্ষা পেতে পারে। তা হচ্ছেঃ কুধারণা, কুলক্ষণ গ্রহণ এবং হিংসা। অতএব তোমার মনে যদি কুধারণা জাগে, তাহলে তুমি তাতে প্রত্যয় নিও না, কুলক্ষণ যদি তোমার মনে দ্বিধার সৃষ্টি করে, তাহলে মাঝপথ থেকে ফিরে যেও না। আর যদি হিংসার উদ্রেক হয়, তাহলে তুমি তেমনটা চাইবে না। (তিবরানী)
রাসূলের শেখানো এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হলে এ তিনটি মনের পটেই জেগে উঠা ভিত্তিহীন চিন্তা-কল্পনা ও শয়তানের ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না এবং বাস্তব কাজের ওপর তার কোন প্রভাব প্রতিফলিত হবে না। এরূপ অবস্থায় আল্লাহ্ তা’আলা এসব ক্ষমা করে দেবেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
কুলক্ষণ গ্রহণ শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ শিরক, কুলক্ষণ গ্রহণ শিরক।
ইবনে মাসউদ বলেছেনঃ আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুলক্ষণ সংক্রান্ত চিন্তার উদ্রেক হয় না। কিন্তু আল্লাহর ওপর নির্ভরতা গ্রহণ করলে এ ধরনের ভাবধারা সবই নিঃশেষ হয়ে যায়। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
জাহিলী অন্ধ অনুসরণের বিরুদ্ধে জিহাদ
ইসলাম যেভাবে জাহিলী আকীদা-বিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে,- কেননা এগুলো বিবেক-বুদ্ধি, নৈতিকতা ও সুস্থ আচার-আচরণের পরিপন্থী, অনুরূপভাবে জাহিলিয়াতের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছে। কেননা তা হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার-গৌরব ও গোত্রীয় আত্মাভিমানের ওপর ভিত্তিশীল।
বিদ্বেষমূলক ভাবধারা ইসলামের বিপরীত
এ পর্যায়ে ইসলাম সর্বপ্রথম বিদ্বেষমূলক ভাবধারার ওপর কুঠারাঘাত করেছে এবং তার সব রূপ ও ধরনকে মাটির তলায় দাফন করেছে। সেই সাথে বিদ্বেষাত্মক ভাবধারা সৃষ্টি ও তার দিকে জনগণকে আহ্বান করাকে হারাম ঘোষণা করেছে। নবী করীম (সা) উদার কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারার দিকে লোকদের আহ্বান জানায়, যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারার ওপর লড়াই করে এবং যে লোক বিদ্বেষাত্মক ভাবধারা নিয়ে মরে, তারা কেউই আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (আবূ দাঊদ)
অতএব ইসলামের দৃষ্টিতে চামড়ার বিশেষ বর্ণের কোন গুরুত্ব বা বিশেষত্ব নেই, লোকদের বিশেষ কোন জাতির প্রাধান্য স্বীকৃত নয়। পৃথিবীর কোন ভুখণ্ডেরও বিশেষত্ব নেই অপরাপর অংশের ওপর। কোন বর্ণের পক্ষেও অপর বর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা মুসলমানের জন্যে হালাল নয়। কোন জাতির ওপর অপর জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠারও কোন অধিাকর নেই। বিশেষ বিশেষ অঞ্চল বা রাজ্য-সম্রাজ্য সম্পর্কেও ইসলামের এ কথা। বর্ণে-বংশে-জাতিতে-অঞ্চলের পার্থক্যের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করতে ইসলাম আদৌ প্রস্তুত নয়। অতএব মুসলমান বর্ণ, জাতি বা দেশভিত্তিক হিংসা-বিদ্বেষের ভিত্তিতে কোন কাজ করতে পারে না। আর ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, জুলুম-ইনসাফ- সর্বাবস্থাই নিজ জাতির সমর্থন করে যাওয়াও কোন মুসলমানের কর্ম নয়। ওয়াসিলা ইবনে আসকা (রা) বলেনঃ ( আরবি******************)
আমি বললাম, ইয়া রাসূল, ‘আসবিয়াত’ কাকে বলে? জবাবে তিনি বললেনঃ তোমার জাতি জুলুমের ওপর হওয়া সত্ত্বেও তুমি তার সাহায্য-সহযোগিতা করবে, এটাই ‘আসবিয়াত’ (বিদ্বেষাত্মক ভাবধারা অপর জাতির বিরুদ্ধে।
আল্লাহ্ তা’আলার ঘোষণা হচ্ছেঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইনসাফ ও সুবিচারের জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহর সাক্ষ্যদাতা হয়ে- যদিও তা তোমাদের নিজেদের পিতামাতার ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেই হোক। (সূরা নিসাঃ ১৩৫)
( আরবি******************) কোন বিশেষ জাতির শত্রুতা যেন তোমাকে অবিচার করতে প্রবৃদ্ধ না করে।
নবী করীম (সা)-এর সুবিচার নীতি এ অর্থেই জাহিলিয়াতের যুগে সর্বত্র বিস্তীর্ণ ছিল, তা বাহ্যিক অর্থেই গৃহীত। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তুমি তোমার ভাইয়ের সাহায্য কর, সে জালিম হোক, কি মজলুম।
উত্তরকালে সাহাবীদের মধ্যে ইসলামী ঈমান যখন দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হলো তখন উপরিউক্ত কথাটির খারাপ অর্থ লোকদের সম্মুখে ভেসে উঠল এবং তদ্দরূন তাদের মনে আতঙ্ক ও বিস্ময় জেগে উঠল। তাঁরা প্রশ্ন করলেনঃ ( আরবি******************)
হে রাসূল! আপনার কথানুযায়ী আমার ভাই মজলুম হলে তাকে তো সাহায্য করতে পারি এবং এ পর্যায়ে আপনার কথার তাৎপর্য বুঝতে পারি। কিন্তু সে জালিম হলে তাকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি?- এ কথাটির অর্থ বুঝতে পারি নি। জবাবে তিনি বললেনঃ ( আরবি******************)
তুমি তাকে জুলুম থেকে বিরত রাখবে আর এটাই তাকে সাহায্য করতে বলার অর্থ।
এ থেকে আমরা স্পষ্ট জানতে পারি যে, মুসলিম সমাজে কোন আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি কিংবা কোন জাতীয়তার শ্রেষ্ঠত্বের দাবি চলতে পারে না। দেশ মাতৃকার দোহাই বা আঞ্চলিক কিংবা শ্রেণী-বংশ-বর্ণ ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার দোহাই ও আত্মম্ভরিতা জাহিলিয়াতের দাবি। এর সাথে ইসলাম, রাসূল বা আল্লাহর কিতাবের কোনই সম্পর্ক থাকতে পারে না।
বস্তুত ইসলাম তার আকীদা পরিপন্থী কোন বন্ধুতা-সংস্থা বা ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বাইরে কোন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক সমর্থন করে না। ঈমান ও কুফর ভিন্ন মানুষে-মানুষে পার্থক্য করার অপর কোন ভিত্তিকেও ইসলাম স্বীকার করে না। অতএব ইসলামের শত্রু- কাফির মুসরমানেরও শত্রু, সে তার স্বদেশী, স্বজাতীয় ও প্রতিবেশী হলেও। শুধু তা-ই নয়, তার আপন ভাই, পিতা, জননী যেই হোক, সেও তার আপন নয়, যদি ইসলামের দুশমন হয়। আল্লাহ্ তা’আলা এ কথাই বলেছেন নিম্নের এ আয়াতেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার জাতিকে আল্লাহ্ ও রাসূলের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব পোষণকারী রূপে পাবে না, তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভাই ও বংশীয় লোকই হোক না কেন। (সূরা মুজাদালাঃ ২২)
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের পিতৃস্থানীয় লোক ও ভাই সদৃশ লোকদের বন্ধু, পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করবে না, যদি তারা ঈমানের ওপর কুফরিকে অগ্রাধিকার দেয়। (সূরা আত্ তাওবাঃ ২৩)
বংশ ও বর্ণের কোন গৌরব নেই
বুখারী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, হযরত বিলাল হাবশী ও আবূ যর গিফারী (রা) দুজনেই প্রাথমিক কালের সাহাবী। দুজন পরস্পরের ওপর ক্রোধান্ধ হয়ে গালাগাল করতে শুরু করেন। ক্রোধের তীব্রতায় হযরত আবূ যর (রা) হযরত বিলাল (রা)-কে সম্বোধন করে বললেনঃ ( আরবি******************)- ‘হে কালোর পুত্র’। হযরত বিলাল নবী করীম (সা)-এর কাছে এ কথা বলে অভিযোগ করলেন। তিনি হযরত আবূ যরকে বললেনঃ ( আরবি******************)
তুমি ওর মাকে মন্দ বললে? দেখা যায় তোমার মধ্যে জাহিলিয়াতের স্বভাব-চরিত্র এখনও অবশিষ্ট কয়েছে।
হযরত আবূ যর (রা) থেকেই বর্ণিত, নবী করীম (সা) তাঁকে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তুমি নিজ সম্পর্কে ভেবে দেখ। লাল বা কালো বর্ণের লোকদের অপেক্ষা তুমি কোন অংশেই উত্তম ব্যক্তি নও। তুমি ওর ওপর কেবল মাত্র তাক্ওয়ার ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পার। (আহমদ)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে মাটি দিয়ে।
এ সবের সাহায্যে মুসলমানের বংশ বর্ণ পিতৃপুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার ভিত্তিতে গৌরব করা ও অন্যদের তুলনায় নিজেদের বড়ত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করাকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। কেননা এগুলোই হচ্ছে জাহিলিয়াতের উপকরণ। নিতান্ত লালসার দাসত্ব করতে গিয়েই মানুষ এ কাজ করতে পারে। কাজেই আমি অমুকের ছেলে, আমি অমুকের বংশধর আর তুমি অমুক হীন বংশের লোক, আমি শ্বেতকর্ণ, আর তুমি কৃষ্ণাঙ্গ, আমি আরব আর তুমি অনারব ইত্যাদি ধরনের বিদ্বেষাত্মক ও হিংসাত্মক কথাবার্তা পরস্পরে বলার কোন অবকাশ ইসলামে নেই।
বস্তুত সমস্ত মানুষ যখন এক ও অভিন্ন মূল থেকে উৎসারিত, তখন পরবর্তী লোকদের পক্ষে বংশ গোত্র বা রক্ত নিয়ে গৌরব করার ও অপরের তুলনায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানর কোন অর্থ হয় না, তার অধিকারও কারো থাকতে পারে না। বংশের কোন গুরুত্ব আছে যদি ধরেও নেয়া যায়, তবু তার বংশে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তির নিজের কি শ্রেষ্ঠত্ব থাকতে পারে বা তার কি অপরাধ মনে করা যেতে পারে? নবী করীম (সা) ওজস্বিনী কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের এসব বংশ নিয়ে অপরের ওপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পার না। কেননা তোমরা সমস্ত মানুষই আদমের সন্তান- বংশধর। দ্বীনদারী ও আল্লাহ্ ভীতি ছাড়া তোমাদের কারো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই অপর লোকদের ওপর। (আহমদ)
তিনি আরও বলেনঃ ( আরবি******************)
সমস্ত মানুষই তো আদম-হাওয়ার বংশধর। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তোমাদের বংশ বা আভিজাত্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন না। আসলে তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাবান সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহ্ ভীরু।
বাপ-দাদার বা বংশের উচ্চতা নিয়ে গৌরবকারী লোকদেরকে কঠোর ভাষায় সাবধান করে দিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ
হে লোকেরা! বাপ-দাদাদের নিয়ে গৌরব করা ত্যাগ কর-সেসব বাপ-দাদা যারা মরে জাহান্নামের কয়লা হয়ে গেছে। নতুবা তারা পোকা-মাকড়ের তুলনায়ও অধিক দীন ও লাঞ্ছিত হবে। আল্লাহ্ তা’আলা জাহিলিয়াতের আত্মম্ভরিতা ও বংশ গৌরব নির্মূল করে দিয়েছেন। এক্ষণে মানুষ হয় মুমিন মুত্তাকী হবে অথবা হবে পাপী দুশ্চরিত্র। সব মানুষই আদমের সন্তান। আর আদম মাটি থেকে সৃষ্ট। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, বায়হাকী)
এ হাদীসে বড় গুরুত্বপূর্ণ দিক্ষা রয়েছে তাদের জন্যে, যারা নিজেদের প্রাচীন বাপ-দাদা পূর্ববংশ, আবরী-আজমী জাহিলিয়াতের অগ্রনায়ক ফিরাউন ও কাইজার কিসরাকে নিয়ে গৌরব করে অথচ নবী করীমের ঘোষণার দৃষ্টিতে তারা জাহান্নামের কয়লা ছাড়া আর কিছুই নয়।
হুজ্জাতুল বিদা’র সময় হজ্জের মাসে সম্মানিত মক্কা নগরে লক্ষাধিক মুসলিম সমবেত হয়ে রাসূলে করীমের উদাত্ত ভাষণ শুনছিলেন। তিনি শুরুতেই ঘোষণা করলেনঃ ( আরবি******************)
হে জনগণ! তোমাদের আল্লাহ্ এক। কোন আরববাসীর কোন শ্রষ্ঠত্ব নেই কোন অনারবের ওপর, কোন অনারবের কোন শ্রেষ্টত্ব নেই কোন আরবের ওপর। লাল-ধলা বর্ণের লোকের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই কালো বর্ণের লোকের ওপর। কালো বর্ণের লোকেরও কোন শ্রেষ্ঠত্ব-বৈশিষ্ট্য নেই লাল-ধলা লোকদের ওপর তাকওয়া ছাড়া। আল্লাহর ঘোষণা হচ্ছে, তোমাদের মধ্যে সেই লোক আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান, যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ্-ভীতি সম্পন্ন। (বায়হাকী)
মৃতের জন্যে বিলাপ
ইসলাম জাহিলিয়াত যুগের যেসব আচার-আচরণের অনুকরণের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে তন্মধ্যে একটি হচ্ছে, মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জাহিলিয়াতের আচরণ।
মৃতের জন্যে বিলাপ করা, খুব বেশি দুঃখ ও মনোকষ্ট প্রকাশে বাড়াবাড়ি করা তার মধ্যে অন্যতম।
ইসলাম তার অনুসারীদের শিক্ষা দিয়েছে যে, মৃত্যু এক জগত থেকে আর এক জগতে যাত্রা করা বা স্থানান্তর গ্রহণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তা কোন চূড়ান্ত ধ্বংস, বিনাশ ও বিলুপ্তি নয়। উপরন্তু বিলাপ করলেই মৃত জীবন্ত হয়ে যাবে না। আল্লাহর ফয়সালা বদলে যাবে না অন্য কোন ফয়সালার দরুন। অতএব মুমিনের কর্তব্য হচ্ছে, প্রতিটি বিপদকে যেমন ধৈর্য সহকারে মুকাবিলা করতে হয়, মৃত্যুর ব্যাপারেও তারা তেমনি ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করবে। তা থেকে বরং সবক গ্রহণ করবে। মনে মনে এ আশা পোষণ করবে যে, আল্লাহর শিখান উক্তি বারবার বলবেঃ ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন- ‘আমরা আল্লাহরই জন্যে এবং আমরা তাঁরই কাছে ফিরে যাব।’
তাই জাহিলিয়াতের যুগে মৃতের জন্যে যে বিলাপ করা হতো, ইসলামে তা হারাম- পরিত্যাজ্য। রাসূলে করীম (সা) তা থেকে নিঃসম্পর্কতার কথা ঘোঘণা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক মৃতের জন্যে বিলাপ করতে গিয়ে নিজের মুখমণ্ডল আহত করে, পরনের কাপড় ছিন্নভিন্ন করে ও জাহিলিয়াতের ন্যায় চিৎকার আর্তনাদ করে, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়। (বায়হাকী)
মৃতের জন্যে শোক করতে গিয়ে মাতামী পোশাক পরা, অলংকারাদি পরিহার করা ও সাধারণ পরিধেয় ত্যাগ করা এবং আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন সাধন করা কোন মুসলমানের জন্যে হালাল বা জায়েয নয়। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর জন্যে যা করণীয়, তা অবশ্য করতে হবে। যেমন চার মাস দশদিন ইদ্দত পালন করা তার কর্তব্য। স্বামীর জন্যে স্ত্রীর এ বিধিবদ্ধ শোককাল এটা দাম্পত্য জীবন অবসানের কারণে কর্তব্য। তাদের দুজনের মধ্যে যে প্রেম-প্রীতির বন্ধন ছিল, স্বামীর মৃত্যুতে তা ছিন্ন হয়ে গেল বলে তার এতটুকু শোক প্রকাশ করা উচিত। তাতে সেই পবিত্র সম্পর্কের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কাজেই এ সময় তার কোন অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয়, যেন ইদ্দত যাপন কালে বিবাহেচ্ছু বহু লোকের দৃষ্টিতে আকর্ষণীয়া হয়ে না উঠে।
কিন্তু মৃত ব্যক্তি স্বামী ছাড়া অন্য কেউ হলে- যেমন পিতা, ভাই, পুত্র, মা ইত্যাদি তিন দিনের বেশিকাল শোক প্রকাশ করা স্ত্রীলোকদের জন্যে জায়েয নয়। যয়নব বিনতে আবূ সালমা থেকে বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে, তিনি নবী করীমের বেগম উম্মে হাবীবা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর পিতা আবূ সূফিয়ান ইবনে হারম মারা গেলে এবং যয়নব বিনতে জাহাশের ভাই মারা গেলে তাঁরা দুজনই সুগন্ধি ব্যবহার করলেন এবং বললেনঃ সুগন্ধি লাগাবার এখন কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে নরী আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী, তার পক্ষে মৃতের জন্যে তিন রাতের অধিক শোক করা জায়েয নয়। তবে স্বামীর জন্যে শোক করতে হবে চার মাস দশদিন পর্যন্ত। (বুখারী)
স্বামীর জন্যে এই শোক ওয়াজিব। এর প্রতি অবজ্ঞা দেখানো চলবে না। একজন মহিলা নবী করীমের খেদমতে হাযির হয়ে বলল, আমার মেয়ের স্বামী মরে গেছে। এখন কি আমি তার চোখে সুরমা লাগাতে পারি? নবী করীম (সা) বললেনঃ না, দুবার তিনবার এই একই জবাব দিলেন। এ কথা দ্বারা স্পষ্ট বোঝা গেল, স্বামী মরে গেলে স্ত্রীকে সৌন্দর্যের উপকরণাদি ও অলংকার ব্যবহার করা ইদ্দত কাল শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্যে হরাম।
তবে কোন রূপ অস্থিরতা প্রকাশ ছাড়া শুধু শোক বা দুঃখ করা এবং চিৎকার না করে কান্নাকাটি করা- এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার। এজন্যে কোন গুনাহ্ হবে না। হযরত উমর (রা) শুনতে পেলেন, খালিদ ইবনে ওয়ালীদের জন্যে মেয়েরা কান্নাকাটি করছে। তখন কোন কোন পুরুষ তাদের নিষেধ করার ইচ্ছা করল। তা দেখে হযরত উমর (রা) বললেনঃ ( আরবি******************)
ছেড়ে দাও ওদের। ওরা আবূ সুলায়মান- খালিদের জন্যে কান্নাকাটি করুক, যতক্ষণ না মাথায় মাটি তুলছে বা উচ্চস্বরে চিৎকার করছে।
পারস্পরিক কার্যাদি
আল্লাহ্ তা’আলা মানুষকে এমন প্রকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা পরস্পরের কাছে ঠেকা, পরস্পরের সাহায্যের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তির যা কিছু প্রয়োজন তা যোগাড় করা তার একার পক্ষে কখখনই সম্ভবপর হয় না। কেউ হয়ত কোন জিনিসের অধিকারী, যা অপর কারো প্রয়োজন পূরণ করে এবং কেউই হয়ত এমন জিনিসের মুখাপেক্ষী যা অপর কারো কাছে পাওয়া যায়। এ করণে আল্লাহ্ তা’আলা তাদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য ও মুনাফা বিনিময় করণের ব্যবস্থা মেনে চলার ভাবধারা জাগিয়ে দিলেন। এভাবেই মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ হয়ে থাকে এবং এ করেই মানব জীবন দৃঢ়তা লাভ করে। এ শুধু ব্যক্তিগণের পারস্পরিক ব্যাপারই নয়, জাতি ও রাষ্ট্রসমূহও পারস্পরিক কল্যাণ ও উৎপাদনের ফসল বিনিময় করে চলতে পারে।
নবী করীম (সা) যখন প্রেরিত হলেন তখন আরব সমাজে নানা প্রকারের ক্রয়-বিক্রয় ও পারস্পরিক লেন-দেন চলছিল। তখন ইসলামী শরীয়তের অনুকূল ব্যবস্থা ও কার্যাদি চালু রাখা হলো, তা জায়েয বলে ঘোষিত হলো, এবং যা যা শরীয়তের পরিপন্থী ছিল, তা সবই হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। এ নিষেধ কয়েক পর্যায়ে বিভক্ত। যেমন কোন গুনাহের কাজে, ধোঁকা-প্রতারণার কাজে, অধিক মূল্য ও মুনাফা লুণ্ঠনের কাজে এবং চুক্তির পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন এক পক্ষের ওপর জুলুম হওয়ার কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।
হারাম জিনিস বিক্রয় করা হারাম
ক. নিষিদ্ধ ও হারাম ঘোষিত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ও তা থেকে উপকার গ্রহণও হারাম এবং গুহান পর্যায়ের কাজ। এ কারণে তা ক্রয় বা বিক্রয় করা কিংবা তার ব্যবসা করা হারাম। শূকর, মদ্য, হারাম খাদ্য-পানীয়, মূর্তি, ক্রুশ, প্রতিকৃতি (Statue) প্রভৃতি এ পর্যায়ে গণ্য। এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা যদি জায়েয করে দেয়া হতো তাহলে গুনাহের এসব কাজ ব্যাপক প্রসারতা লাভ করত। জনগণকে সেই কাজে উদ্বুদ্ধ করা হতো, তা করার জন্যে সহজতার সৃষ্টি করা হতো, লোকদের তার কাছে নিয়ে যাওয়া হতো। সেজন্যে লোকদের উৎসাহিত করা হতো। কিন্তু যেহেতু এসব জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় ও তা অর্জন হারাম করে দেয়া হয়েছে। ফলে মানুষ এসব থেকে বেঁচে থাকতে পারে। এক্ষণে এসব জিনিসের দিকে লোকদের না দৃষ্টি পড়তে পারে, না তা স্মরণ করার কোন কারণ ঘটতে পারে। এসব জিনিসের সংস্পর্শ থেকেই মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাওয়া হয়েছে। এজন্যেই নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল মদ্য, মৃত জীব, শূকর ও মূর্তি বিক্রয় করা হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)
এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আল্লাহ্ যখন কোন জিনিস হারাম করেন তখন সে জিনিসের বিক্রয় মূল্যও হারাম করে দেন। (আহমদ, আবূ দাউদ)
ধোঁকাপূর্ণ বিক্রয় হারাম
খ. যে ধরনের বিক্রয়ে পণ্য অজ্ঞাত বা ধোকা হওয়ার কিংবা এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে ক্ষতি সাধনের সুযোগের কারণে পারস্পরিক ঝগড়া হওয়ার আশংকা থাকে, তা ‘কারণ বন্ধের’ নীতি অনুযায়ী নিষিদ্ধ। যেমন পুরুষ উষ্ট্রের পৃষ্ঠের যে জিনিস বা উষ্ট্রী গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে, তা বিক্রয় করা কিংবা উড়ন্ত পাখি বা পানির মধ্যে অবস্থিত মাছ অথবা এ ধরনের অজানা পণ্য ক্রয় ও বিক্রয় করা।
নবী করীম (সা)-এর সময়ে ক্ষেতের ফসল বা বাগানের ফল পাকার পূর্বেই বিক্রয় করে দেয়া হতো। বিক্রায় সাব্যস্ত হওয়ার পর অনেক সময় নৈসর্গিক কারণে ফল ধ্বংস হয়ে যেত, ফসল বিনষ্ট হতো, ফলে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়ার সৃষ্টি হতো। বিক্রয়কারী বলত, আমি তো বেঁচে দিয়েছে। ক্রেতা বলত, যে ফল বিক্রয় করেছ, সেই ফল-ই নেই। এ কারণে নবী করীম (সা) ফল-ফসল পাঁকার পূর্বে বিক্রয় করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে ফল কাটা সাব্যস্ত হলে তা জায়েয হতে পারে। শস্যের মঞ্জরী বা শিষ সাদা হওয়া ও বিপদমুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রয় করতেও নিষেধ করা হয়েছে। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা কি চিন্তা করেছ, আল্লাহই যখন ফল বন্ধ করে দিলেন, তখন তোমাদের ভাইর টাকা লওয়া তোমাদের জন্যে কিভাবে জায়েয হতে পারে?
অজ্ঞাত পণ্য মাত্রই যে ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ এমন কথা নয়। কোন কোন ব্যাপারে পণ্যের অনেকাংশ অজানা অন্ধকারে থেকে যায়। যেমন কেউ যদি কোন পাকা বাড়ি ক্রয় করে, তাহলে তার ভিত্তি ও প্রাচীরসমূহের ভিতরকার অবস্থা ক্রেতার অগোচরেই থেকে যায়। সে বিষয়ে কিছু জানা তার পক্ষে সম্ভবপর হয় না। কিন্তু তার অন্যান্য সবদিকই ক্রয়কারী ভাল করে দেখতে পারে। কাজেই যে জিনিস সম্পূর্ণরূপে অজানা, যার কারণে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ হতে পারে কিংবা যার মধ্যে বাতিল পন্থায় লোকদের মাল ভক্ষণ করার অবকাশ থাকে, তা-ই নিষিদ্ধ।
যদি কোন জিনিস সামান্যভাবে অজানা হয়, আর এ আংশিক অজানা জিনিসের ক্রয়-বিক্রয়ের রেওয়াজ থাকে, তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় যথা মূলা, গাজর, পিয়াজ প্রভৃতি কাকই ও ফুটি-তরমুজের ক্ষেত বিক্রয়। ইমাম মালিকের মতে প্রয়োজনের কারণে তা জায়েয। কেননা তাতে অজ্ঞানতার ক্ষেত্র খুব ব্যাপক নয়, অতি সাধারণ এবং সামান্য।
ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইমাম মালিকের নীতি অন্যান্যের নীতির তুলনায় উত্তম কেননা তাঁর নীতি সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যিবের মতের ওপর ভিত্তিশীল। আর ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত বিষয়াদিতে তিনি বড় ফিকাহবিদ বলে মান্য। ( আরবি******************)
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতও এরই কাছাকাছি।
দ্রব্যমূল্য লয়ে খেলা করা
ইসলাম বাজার ও দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক গতিতে চলতে দিতে ইচ্ছুক। হাট-বাজার স্বাভাবিকভাবে চলতে পারলেই দ্রব্যমূল্য আপনা থেকেই নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে, বাজারে পণ্য আমদানী ও তার চাহিদা অনুপাতে দ্রব্যমূল্যে উত্থান-পতন হতেই থাকে। আমরা নবী করীমের যুগে তাই দেখতে পাই। তখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা এসে বললঃ ইয়া রাসূল, আমাদের জন্যে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত করে দিন। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ্ তা’আলাই। তিনিই মূল্য বৃদ্ধি করেন, তিনি সস্তা করেন। রিযকদাতা তিনিই। আমি তো আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চাই এ অবস্থায় যে, কোনরূপ জুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে আমার ওপর দাবিদার কেউ থাকবে না। (আহমদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)
নবী করীম (সা) এ হাদীসের মাধ্যমে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কোনরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ চাপান জুলুম এবং সেই জুলুম থেকে মুক্ত ও পবিত্র থেকেই তিনি আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করতে চান।
কিন্তু বাজারদরের ওপর যদি অস্বাভাবিক অবস্থায় চাপ আসে, যেমন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মজুদকরণ শুরু হয়ে যায় এবং মজুদদাররা দ্রব্যমূল্য নিয়ে খেলা করতে শুরু করে, তাহলে সমষ্টির কল্যাণ স্বার্থে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দিতে হবে। তাতে অধিক মূল্য গ্রহণকারীর শোষণ থেকে জনগণকে বাঁচান সম্ভবপর হবে।
অতএব উপরিউক্ত হাদীসের অর্থ এই নয় যে, যে কোন পরিস্থিতিতেই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ জুলুম ও তা নিষিদ্ধ- লোকদের কষ্ট দূর করা বা সুস্পষ্ট জুলুম থেকে লোকদের বাঁচানর জন্যে হলেও। বরং ইসলামের বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, মূল্য নির্ধারণ দুরকমের হয়। এক প্রকারের মূল্য নির্ধারণে লোকদের ওপর জুলুম হয় এবং তা হারাম। আর এক অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ সুবিচার ও ন্যায়পরতার দাবি তা অবশ্যই জায়েয এবং জরুরী।
অতএব অন্যায়ভাবে লোকদের ওপর যদি এমন মূল্য চাপিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা রাজি নয়, কিন্তু মুবাহ জিনিস থেকে জনগণকে বিরত রাখা হয়, তাহলে তা হবে হারাম। পক্ষান্তরে লোকদের মধ্যে সুবিচার ও ইনসাফ কার্যকর করার উদ্দেশ্যে যদি মূল্য নির্ধারিত করে দেয়া হয়- প্রচলিত দামে (standardprice) বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয় কিংবা প্রচলিত বিনিময় মূল্যের অধিক গ্রহণ থেকে তাদের বিরত রাখা হয়, তাহলে তা করা শুধু জায়েযই নয়, ওয়াজিবও।
প্রথম অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রথমোক্ত হাদীসটি উদ্ধৃত। কাজেই লোকরা যখন প্রচলিত নিয়মে কোনরূপ জুলুম ও বাড়াবাড়ি ব্যতীতই দ্রব্য বিক্রয় করে ও পণ্যদ্রবের স্বল্পতার বা জনসংখ্যা বৃদ্ধির করণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহলে গোটা ব্যাপারটাই আল্লাহর উপর সোপর্দ করা কর্তব্য। এরূপ অবস্থায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় করতে বাধ্য করা অকারণ বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়।
আর দ্বিতীয় অবস্থায়- লোকদের প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ীরা যদি পণ্যদ্রব্য বিক্রয় না করে অথবা চলতি মূল্যের অধিক দাবি করে, এরূপ অবস্থায় প্রচলিত দামে দ্রব্য বিক্রয় করাও ওয়াজিব। এ সময় দ্রব্য মূল্য নির্ধারিত করে দেয়ার অর্থ, প্রচলিত দাম লোকদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দেয়া। এরূপ অবস্থায় দ্রব্যমূল্য নির্ধারণের অর্থ, আল্লাহ্ তা’আলা যে ন্যায়বিচারকে জরুরী ও বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন, তা মেনে চলতে ব্যবসায়ীদের বাধ্য করা।
( আরবি******************)
পণ্য মজুদকারী অভিশপ্ত
ইসলাম ক্রয়-বিক্রয় ও স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা (natural competition)-এর পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেও লোকেরা স্বার্থপরতার ও লোভের বশবর্তী হয়ে পরের ওপর টেক্কা দিয়ে নিজের ধন-সম্পদের পরিমাণ স্ফীত করতে থাকবে, তা কিছুতেই বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। খাদ্যপণ্য ও জনগণের সাধারণ ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ইত্যাদি সব ব্যাপারেই ইসলামের এ কঠোরতা। এ জন্যেই নবী রকীম (সা) পণ্য মজুদকরণের ব্যাপারে নানাভাবে কঠোর ও কঠিন ভাষায় নিষেধবাণী উচ্চারণ করেছেন। একটি হাদীসে তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক চল্লিশ রাত্রি কাল খাদ্যপণ্য মজুদ করে রাখল, সে আল্লাহ্ থেকে নিঃসম্পর্ক হয়ে গেল এবং আল্লাহও নিঃসম্পর্ক হয়ে গেলেন তার থেকে। (আহমদ, হাকেম)
নবী করীম (সা) আরও বলেছেনঃ - ( আরবি******************)
অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া কেউ পণ্য মজুদ করে রাখার কাজ করে না। (মুসলিম)
এ ‘অপরাধী’ কথাটি খুব সহজ অর্থে নয়। ‘যে-ই পণ্য মজুদ রাখার কাজ করে সে-ই অপরাধী’ কথাটি যথার্থ। কুরআন মজীদে ফিরাঊন, হামান প্রভৃতি বড় বড় কাফির ও খোদাদ্রোহীদের সম্পর্কে এ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
নিশ্চয়ই ফিরাঊন ও হামান ও সে দুজনার সৈন্য-সামন্ত বড় বড় অপরাধী ছিল।
পণ্য মজুদকারীর মনস্তত্ত্ব ও বীভৎস মনোভাবের ব্যাখ্যা দিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
পণ্য মজুদকারী ব্যক্তি অত্যন্ত খারাপ লোক হয়ে থাকে। সে যদি শুনতে পায় যে, পণ্যমূল্য কমে গেছে, তাহলে তার খুব খারাপ লাগে। আর যদি শুনতে পায় যে, মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা হলে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠে। (রাজিন)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
বাজারে পণ্য আমদানীকারক রিযক প্রাপ্ত হয়। আর পণ্য মজুদকারী হয়ে অভিশপ্ত।
তার কারণ হচ্ছে ব্যবসায়ীর মুনাফা লাভ দুইটির কোন একটি কারণে সম্ভবপর হয়। একটি হচ্ছে, সে পণ্যদ্রব্য মজুদ করে রাখবে অধিক মূল্যে বিক্রয় করার আশায় অর্থাৎ পণ্য আটক করে রাখলে বাজারে তার অভাব তীব্র হয়ে দেখা দেবে এবং লোকেরা খুবই ঠেকায় পড়ে যাবে। তখন তার যে মূল্যই দাবি করা হবে তা যত বেশি ও সীমালংঘনকারীই হোক না কেন। তাই দিয়েই লোকেরা তা ক্রয় করতে বাধ্য হবে।
আর দ্বিতীয় হচ্ছে, ব্যবসায়ী পণ্য বাজারে নিয়ে আসবে এবং অল্প স্বল্প মুনাফা নিয়েই তা বিক্রয় করে দেবে। পরে এ মূলধন দিয়ে সে আরও অন্যান্য পণ্য নিয়ে আসবে। তাতেও সে মুনাফা পাবে। এ ভাবে তার ব্যবসা চলতে থাকতে ও পণ্যদ্রব্য বেশি কাটতি ও বিক্রয় হওয়ার ফলে অল্প অল্প করে মুনাফা করতে থাকবে। মুনাফা লাভের এই নীতি ও পদ্ধতিই সমাজ সমষ্টির পক্ষে কল্যাণকর। এতে বরকত বাড়ে। আর নবী করীম (সা) যেমন বলেছেন, এই ব্যবসায়ীই রিযিক প্রাপ্ত হয়।
পণ্য মজুদকরণ ও পণ্যদ্রব্য নিয়ে খেলা করা যে কত বড় অপরাধ, তা রাসূলে করীমের অপর একটি বাণী থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। হযরত মাকার ইবনে ইয়ামার (রা) বর্ণনা করেছেন, তিনি যখন রোগাক্রান্ত হলেন তখন উমাইয়া প্রশাসক উবায়দুল্লাহ ইবনে জিয়াদ তাঁকে দেখতে এলেন। তাঁকে সম্বধন করে বললেন, হে মাকাল, আপনি কি জানেন, আমি কোন হারাম রক্তপাত করেছি? বললেন, আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি জানেন আমি মুসলমানদের পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন হস্তক্ষেপ করেছি? বললেনঃ তাও আমি জানি না। পরে মাকাল লোকদের বললেনঃ আমাকে বসিয়ে দাও। লোকেরা তাঁকে বসেয়ে দিলেন এবং বললেনঃ হে উবায়দুল্লাহ! শুনুন, আমি একটি হাদীস আপনাকে শোনাচ্ছি, যা রাসূলে করীমের কাছ থেকে আমি মাত্র এক-দুইবার শুনিনি। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মুসলিম জনগণের জন্যে পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য যদি কেউ কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা’আলার অধিকার রয়েছে তিনি কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের ওপর বসাবেন। (আহমদ, তাবারানী)
একথা শুনে উমাইয়া শাসক বললেনঃ আপনি কি নিজেই এই হাদীস রাসূলে করীম (সা)-এর মুখে শুনেছেন? বললেনঃ হ্যাঁ, এক-দুইবার নয়।
এসব হাদীস ও তার ইঙ্গিত-ইশারার ভিত্তিতে আলিমগণ এ মাসলা বের করেছেন যে, পণ্য মজুদকরণ দুটি শর্তে হারাম। একটি এইঃ
এমন এক স্থানে ও এমন সময় পণ্য মজুদ করা হবে যখন তার কারণে জনগণকে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।
আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে অধিক মূল্য হরণ, যার ফলে মুনাফার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে।
বাজারের স্বাধীনতায় কৃত্রিম হস্তক্ষেপ
পণ্য মজুদকরণের মতো আরও একটি কাজ করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন। আর তা হচ্ছে, শহরবাসীর গ্রামবাসীর কাছ থেকে মাল ক্রয় করে নেয়। তার রূপটা হচ্ছে, শহরের বাইরের লোক মাল নিয়ে শহরের বাজারে এল চলতি দামে বিক্রয় করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শহরের লোক বললঃ এ মাল আমার কাছে রেখে যাও, পরে বেশি দামে বিক্রয় করে তোমাকে মূল্য ফেরত দেব। এমতাবস্থায় গ্রাম থেকে আশা লোকই যদি নিজে মাল বিক্রয় করত তাহলে তা সস্তায় বিক্রয় হতো। তাতে সে নিজেও মুনাফা লাভ করত এবং অন্যরাও- শহরের ক্রেতারাও লাভবান হতো।
সেকালের সমাজে এরূপ ক্রয়-বিক্রয়ের খুব বেশি ও ব্যাপক প্রচলন ছিল। হযরত আনাম বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কোন শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রয় না করে- এ বিষয়ে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। সে লোক তার নিজের ভাই, পিতা বা মাতাই হোক-না-কেন।
এ থেকে জানা গেল ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আত্মীয়তার চাইতে সামষ্টিক কল্যাণের গুরুত্ব অনেক বেশি।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কোন শহরের লোক যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ্ তাদের কারোর দ্বারা কাউকে রিযক দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।
রাসূলে করীম (সা)-এর এই কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে ব্যবসা পর্যায়ে একটা বড় মূলনীতি লাভ করা যাচ্ছে। তা হচ্ছে, বাজারে পণ্য ও স্বাভাবিক পন্থার বিনিময় প্রণালীকে নিজস্বভাবে কাজ করার অবাধ সুযোগ দিতে হবে। এ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করা হলে স্বাভাবিক পন্থায়ই লোকেরা নিজের নিজের রিযক লাভ করতে সক্ষম হবে।
উপরিউক্ত হাদীসের সঠিক তাৎপর্য কি, তা হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ ( আরবি******************)
বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝখানে কোন দালাল থাকবে না। (বুখারী)
তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কেউ যখন তাকে মূল্য জানিয়ে দিল, তাকে উপদেশ দিল এবং বাজারের অবস্থার সাথে তাকে পরিচিত করল এবং তাতে কোন মজুরী গ্রহণ না করল, তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তার এ উপদেশ দান একান্তভাবে আল্লাহর জন্যে। এ উপদেশ দান দ্বীনের অংশ; বরং তা-ই সম্পূর্ণ ও সমগ্র দ্বীন। সহীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি******************) দ্বীনই হচ্ছে নসীহত বা নসীহতই হচ্ছে দ্বীন।
অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
তোমাদের কেউ উপদেশ চাইলে তার ভাইকে উপদেশ দেয়া তার কর্তব্য।
‘দালাল’ সাধারণতঃ তার মজুরী পাওয়ার জন্যেই লালায়িত হয়। আর এসব ব্যাপারে সে সাধারণ মানুষের কল্যাণের কথা প্রায়ই ভুলে যায়।
দালালী জায়েয
অন্যান্য কাজে দালালী করা হলে, তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তা একপ্রকার পথ-প্রদর্শন, ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং মাধ্যম হওয়ার ব্যাপার। তার দরুন উভয় পক্ষই উপকৃত হয়। উভয় পক্ষেরই নিজের নিজের কাজে অনেক অসুবিধা হয়ে যায়। বর্তমান কালে আমদানী রফতানী ব্যবসায়ে এবং খুচরা বা পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতার বড় প্রয়োজন দেখা দেয়। অতীতের যে কোন কালের বা যুগের তুলনায় একালে ও এযুগে এ প্রয়োজন তীব্রতর। আর তাতে দালালের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করার উপায় নেই।
তাই দালাল যদি তার নির্দিষ্ট মজুরী নগদ গ্রহণ করে কিংবা মুনাফা থেকে হার মতো কমিশন অথবা অন্য কোনভাবে উভয় পক্ষ সম্মত হয়ে নেয়, তবে তাতে কোন দোষ নেই। ইমাম বুখারী লিখেছেন- ইবনে সিরীন, আতা, ইবরাহীম, হাসান প্রমুখ প্রখ্যাত ফিকাহবিদ দালালীর মজুরী গ্রহণে কোন দোষ দেখতে পান নি। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ যদি একজন অপর জনকে বলে, ‘এ কাপড়টা বিক্রয় করে দাও। অতিরিক্ত যা পাওয়া যাবে তা তোমার’ তবে তা সম্পূর্ণ জায়েয। ইবনে সিরীন বলেছেনঃ এ জিনিসটি এ দামে বিক্রয় কর। আর বেশি যা পাবে, তা তোমার হবে কিংবা তা তুমি-আমি ভাগাভাগি করে নেব এবং এ ভিত্তিতে যদি তা বিক্রয় করে দেয়ার কাজ করা হয় তবে তাতে কোন দোষ নেই। এ দালালী ব্যবসা কমিশন এজেন্সী ধরনের কাজ সম্পূর্ণ জায়েয। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মুসলমান নিজেদের পারস্পরিক শর্ত মেনে চলতে বাধ্য। (বুখারী)
মুনাফাখোরি ও ধোঁকাবাজি হারাম
বাজার বা স্বাভাবিক দ্রব্যমূল্যের ওপর কৃত্রিমভাবে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করার সাথে সাথে নবী করীম (সা) মুনাফাখোরি ও ধোঁকাবাজি করতেও স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। হাদীসে এ কথাটি বোঝার জন্যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত ইবনে উমর (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ পণ্যের ন্যায্য মূল্যের অধিক বুলি দেয়া অথচ তুমি তা কিনবার ইচ্ছা পোষণ কর না। আর তুমি তা কর এ জন্যে যে, তোমার বুলি শুনে অন্য লোকেরা তোমার অনুসরণ করবে। সাধারণত অন্যদের ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যেই এরূপ করা হয়।
বেচা-কেনা কারবারটিকে মুনাফাখোরি থেকে এবং দ্রব্যমূল্যকে ধোঁকাবাজি থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে নবী করীম (সা) বাজারে মাল আসার পূর্বেই- বাইরে-বাইরে- ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন নতুবা মূল বাজারেই পণ্যদ্রব্যের আমদানী ব্যাহত হয়ে পড়বে। আর তার ফলে সঠিক মূল্যও নির্ধারিত হতে পারবে না। কেননা সঠিক মূল্য নির্ধারণ বাজারে পণ্যের আমদানী ও তার চাহিদা (demand) অনুপাত সম্ভবপর হয়। কিন্তু উপরিউক্ত অবস্থায় বিক্রেতা বাজারের দর-দাম কিছু জানতে পারে না। এ কারণেই নবী করীম (সা) বাজারে পণ্য পৌঁছার পর পূর্ববর্তী সওদা ভঙ্গ করার অধিকার বিক্রেতার আছে বলে ঘোষণা করেছেন। ( আরবি******************)
যে ধোঁকাবাজি করল সে আমাদের নয়
ইসলাম ধোঁকা-প্রতারণার সবল রূপ ও পন্থাকে হারাম করে দিয়েছে। তা ক্রয় বিক্রয় সম্পর্কেই হোক কিংবা অন্যান্য মানবীয় ব্যাপারেই মুসলমান সততা ও ন্যায়পরতা অবলম্বন করবে। ইসলামের দৃষ্টিতে সর্বপ্রকার বৈষয়িক কামাই-রোযগারের তুলনায় ‘দ্বীনের মধ্যে নসীহত’ অত্যধিক মুল্যবান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
ক্রেতা-বিক্রেতার কথাবার্তা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে না। ততক্ষণে তাদের (চুক্তি ভঙ্গ করার) ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা দুজনই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের দুজনের এই ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা দুজন মিথ্যার আশ্রয় নেয় ও দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নির্মূল হয়ে যাবে। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কোন পণ্য বিক্রয়ে পণ্যের দোষ-ত্রুটি বলে দেয়া না হলে হালাল হবে না কারো জন্যেই। আর যে তা জানে, কিন্তু জানা সত্ত্বেও যদি না বলে তবু তা তার জন্যে হালাল নয়। (হাকেম, বায়হাকী)
রাসূলে করীম (সা) বাজারে গিয়ে দেখলেন, এক ব্যক্তি শস্য বিক্রয় করছে। তা তাঁর খুব পছন্দ হলো। পরে তিনি স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন হাত ভিজে গেল। তখন তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ ‘হে শস্য ব্যবসায়ী, এসব কি,? সে বললঃ ‘বৃষ্টির পানিতে ভিজে গেছে।, তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
তাহলে তুমি এ ভিজা শস্যগুলো স্তুপের উপরিভাগে রাখলে না কেন, তাহলে ক্রেতারা তা দেখতে পেত?... এ তো ধোঁকা। আর যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (মুসলিম)
অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ নবী করীম (সা) অপর এক খাদ্য বিক্রেতার কাছে গেলেন। সে খুব ভাল পণ্য নিয়ে বসেছিল। তিনি তার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। দেখলেন খুব নিকৃষ্ট মানের খাদ্য নীচে রয়েছে। তখন তিনি তাকে বললেনঃ ( আরবি******************)
এ খাবার আলাদা বিক্রয় করবে এবং এ খাবার স্বতন্ত্রভাবে বিক্রয় করবে। জেনে রাখ, যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করবে, সে আমাদের মধ্যের কেউ নয়। (আহমদ)
আগের কালের মুসলমানরা এ নীতি অনুসরণ করে চলতেন। পণ্যদ্রব্যে যে দোষত্রুটি থাকত, তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতেন। তার কিছুই গোপন করতেন না। আর ক্রয় বিক্রয়ে সদা সত্য কথা বলতেন, মিথ্যার প্রশ্রয় দিতেন না। তাঁরা লোকদের কল্যাণ চাইতেন, কাউকে ধোঁকা দিতেন না।
প্রখ্যাত ফিকাহবিদ ইবনে সিরীন একটি ছাগী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে তিনি বললেন, ছাগীটির দোষ আছে তা তোমাকে বলে আমি দায়িত্ব মুক্ত হতে চাই। ওটি ঘাস পা দিয়ে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দেয়।
হাসান ইবনে সালেহ একটি ক্রীতদাসী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। তা ছিল মাত্র একবারের ঘটনা। কিন্তুতা সত্ত্বেও তাঁর ঈমানদার অন্তর তার উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারল না, যদিও তাতে মূল্য কম হওয়ার আশংকা ছিল।
বারবার কিরা-কসম করা
ধোঁকাবাজির সাথে মিথ্যামিথ্যি কিরা-কসম করা হলে এ কাজ অধিক মাত্রায় হারাম হয়ে দাঁড়ায়। নবী করীম (সা) ব্যবসায়ীদের কিরা-কসম করতে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মিথ্যা কিরা-কসম করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি******************)
কিরা-কসম দ্বারা পণ্য তো বিক্রয় করা যায়; কিন্ত বরকত পাওয়া যায় না।
বিক্রয়ে বেশি বেশি কিরা-কসম করা নবী করীমের আদৌ পছন্দ নয়। কেননা তাতে প্রথমতঃ চুক্তির পক্ষদ্বয়ের ধোঁকাবাজির মধ্যে পড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আর দ্বিতীয়তঃ তাতে আল্লাহর পবিত্র নামের ইজ্জত নষ্ট হওয়ারও ভয় আছে।
মাপে-ওজনে কম করা
পণ্য বিক্রয়ে পাত্র দ্বারা মাপায় বা পাল্লা দ্বারা ওজন করে কম দেয়াও এক প্রকারের ধোঁকাবাজি। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারটির ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং সূরা আল-আন’আম-এর শেষে দশটি উপদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আয়াতটি এইঃ ( আরবি******************)
তোমরা মাপার পাত্র ও ওজনের পাল্লা সুবিচার সহকারে পূর্ণ ভর্তি করে দাও। মানুষের সাধ্য-সামর্থ্যের অধিক আমরা কোন দায়িত্বই তার ওপর চাপিয়ে দিই না।
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আর তোমরা মাপার কাজ যখন করবে তখন পূর্ণ করে মাপবে। আর সুদৃঢ়-সঠিক দাঁড়ি-পাল্লার দ্বারা ওজন করবে। এ নীতি অতীব কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে খুবই ভাল ও উত্তম। (সূরা বনী-ইসরাঈলঃ ৩৫)
বলেছেনঃ ( আরবি******************)
মাপে ওজনে যারা কম করে তাদের জন্যে বড়ই দুঃখ। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি গ্রহণ করে। আর যখন তাদের মেপে বা ওজন জরে দেয়, তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সমস্ত মানুষ রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যাবে। (সূরা মুত্বাফফিফীনঃ১-৬)
মুসলিম মাত্রেরই কর্তব্য এ ক্ষেত্রে সাধ্যমত পূর্ণ সুবিচার নীতি ও ন্যায়পরতা অবলম্বন করা। কেননা পুরামাত্রার ও প্রকৃত সুবিচার ন্যায়পরতা হয়ত কল্পনা করা কঠিন। এ কারণেই পূর্ণমাত্রায় পরিমাপ করার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে কুরআন বলেছেঃ আমরা মানুষের সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজের দায়িত্ব কারো ওপর অর্পণ করি না।
যে সব জাতি তাদের পারস্পরিক কার্যাদি ও লেন-দেনে জুলুম করেছে, বিশেষভাবে পরিমাপে ও ওজনে সুবিচারনীতি লংঘন করেছে এবং লোকদের পণ্য বিক্রয়ে তাদের ঠকিয়েছে, তাদের কিসসা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা এসব জাতির কাছে নবী রাসূল পাঠিয়েছেন, তাঁরা তাদেরকে সংশোধন করতে ও সুবিচার নীতির দিক নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছেন, যেমন চেষ্টা করেছেন তাদের তওহীদে বিশ্বাসী বানাবার জন্যে।
এদের মধ্যে শুয়াইব নবীর লোকদের কথাও বলা হয়েছে। তিনি তাদের উচ্চস্বরে দাওয়াত দিয়েছেন, নাফরমানীর পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা পরিমাণ পূর্ণ কর এবং লোকদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ো না তোমরা। আর সুদৃঢ় পাল্লায় ওজন কর ও লোকদের দ্রব্যাদি কম দিও না এবং পৃথিবীতে সীমালংঘন করে বিপর্যয়কারী হইও না। (সূরা শূআরাঃ ১৮১-১৮৩)
মুসলিম সমাজের জন্যে এ নির্দেশ অবশ্য পালনীয়। তাদের জীবনে লোকদের সাথে সম্পর্কে ও সমস্ত পারস্পরিক কাজকর্মে এ নীতিই তাদের পালন করতে হবে। অতএব দুই রকমের পরিমাণ ও দুই ধরনের পাল্লায় ওজন করে বেচা-কেনা করা তাদের জন্যে জায়েয নয়। একটা নিজের জন্যে মানদণ্ড আর একটা অন্যান্য লোকদের জন্যে সাধারণ মানদণ্ড, তার নিজের জন্যে ও তার প্রিয়জনদের জন্যে এক রকমের আচরণ এবং অন্যান্য সাধারণ মানষের জন্যে ভিন্ন রকমের মানদণ্ড ইসলামে সম্পূর্ণ অচল। কেননা এরূপ হলে সে নিজের ও নিজের অনুসারীদের প্রাপ্য পুরামাত্রায় আদায় করবে, বেশিও নিয়ে বসবে। আর অপর লোকদের জন্যে কম দেবে এবং তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কিন্তু এর মতো অবিচার আর কিছু হতে পারে না।
চোরা মাল ক্রয়
ইসলাম অপরাধ ও অপরাধ প্রবণতার বিরুদ্ধে লড়াই ঘোষণা করেছে। অপরাধীদের সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছে। তাই যে মাল অপহৃত বা চুরি করে আনা হয়েছে কিংবা মালিকের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয়া হয়েছে তা শুনে ক্রয় করা মুসলমানের জন্যে জায়েয নয়, কেননা তা করা হলে অপহরণকারী, চোর ও ছিনতাইকারীকে তার কাজে সাহায্য করা হবে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ্ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল। (বায়হাকী)
চুরি করা মালের যদি দীর্ঘদিনও অতিবাহিত হয়, তাহলেও তার গুণাহ্ দূর হয়ে যায় না। কেননা ইসলামে সময়ের দীর্ঘতা হারামকে হালাল করে দেয় না। প্রকৃত মালিকের হক নাকচ করে না। মানব রচিত আইনেও এ নীতিই অবলম্বিত হয়েছে।
সুদ হারাম
ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুলধনের মুনাফা লাভ ইসলামে সম্পূর্ণ জায়েয। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমারা পরস্পরের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে না। তবে তোমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের সম্মতিতে ব্যবসায় হলে দোষ নেই।
যারা দুনিয়ায় ব্যবসায় লিপ্ত হয় এবং দুনিয়ায় দেশ-বিদেশে সফর করে, তাদের প্রশংসা করে কুরআনে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
আর অন্যান্য যারা পৃথিবীতে চলাফেরা করে ও আল্লাহর অনুগ্রহের সন্ধান করে বেড়ায়। (সূরা মুজাম্মিলঃ ২০)
কিন্তু সুদের পন্থায় ‘মুনাফা’ লাভ করার সবল পথকে ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ও হারাম করে দিয়েছে। তার পরিমাণ কম হোক, কি বেশি, ইসলামে তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে।
তার পরিমাণ কম হোক বেশি হোক- সবই হারাম। ইয়াহূদীদের এ সুদী কারবার করতে নিষেধ করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তা করেছে। এজন্যে তাদের ওপর ভর্ৎসনা করা হয়েছে। কুরআনের সর্বশেষ নাযিল হওয়া আয়াত সমূহের মধ্যে এ আয়াত একটিঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা ভয় কর আল্লাহকে এবং সুদের অবশিষ্টাংশ পরিহার কর যদি তোমরা ঈমানদার হও। আর তা যদি না-ই কর, তাহলে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও। আর তোমরা যদি তওবা কর, তাহলে তোমাদের মূলধন তোমরা ফেরত পেতে পার। তোমরা জুলুমও করবে না, তোমরা মজলুমও হবে না। (সূরা বাকারাঃ ২৭৮-২৭৯)
রাসূলে করীম (সা) সুদ ও সুদখোর, সুদী কারবারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। এ সুদের ফলে সমাজ জীবনের ওপর যে বিপদ ঘনীভূত হয়ে আসে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেনঃ ( আরবি******************)
সুদ ও ব্যভিচার যখন কোন দেশে-শহরে ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়, তখন তাদের ওপর আল্লাহর আযাব আসা অনিবার্য হয়ে পড়ে। (হাকাম)
আসমানী ধর্মসমূহের মধ্যে ইসলামে এটা কোন একক ঘোষণা নয়। ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থে পুরান নিয়ম-এ বলা হয়েছেঃ
তুমি যদি আমার প্রজাদের মধ্যে তোমার স্বজাতীয় কোন দীন-দুখীকে টাকা ধার দাও, তবে তাহার কাছে সুদ গ্রাহীর ন্যায় হইও না, তোমরা তাহার উপরে সুদ চাপাইবে না। (যাত্রা পুস্তক-২২ অধ্যায়, ২৫ স্তোত্র)
আর খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছেঃ
তোমরা আপন আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, তাহাদের ভাল করিও এবং কখনও নিরাশ না হইয়া ধার দিও, তাহা করিলে তোমাদের মহা পুরস্কার হইবে। (নূতন নিয়ম-লুক, ৩৫ স্তোত্র, ৬ অধ্যায়)
বড়ই দুঃখের বিষয় ‘পুরাতন নিয়ম’ গ্রন্থে পরিবর্তন করে সুদে টাকা না দেয়ার কথাকে কেবল ইয়াহূদী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ‘ভাই’ বলতে কেবল তাদেরই মনে করা হয়েছে এবং অপর লোকদের জন্যে সুদের ভিত্তিতে টাকা দেয়ার কারবার চালাবার অবাধ সুযোগ করে দেয়া হয়েছে।
সুদ হারামকরণের যৌক্তিকতা
ইসলাম সুদের ব্যাপারে খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছে এবং তাগিদী ভাষায় হারাম করে দিয়েছে। এতে করে সামগ্রিকভাবে মানুষের কল্যাণ সাধন করেছে। তাদের নৈতিকতা, সমাজ ও অর্থনীতেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে।
সুদ হারাম হওয়ার যৌক্তিকতা দেখান প্রসঙ্গে আলিমগণ কয়েকটি গুরুতর কারণের উল্লেখ করেছেন, আধুনিক বিশ্লেষণ ও চিন্তা-ভাবনার ফরে তা প্রকট হয়ে উঠেছে।
ইমাম রাযী তাঁর তাফসীরে এ পর্যায়ে যা লিখেছেন, তার উল্লেখকেই আমরা যথেষ্ট মনে করছি। তিনি লিখেছেনঃ
প্রথম কথা এই যে, সুদ লোকদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে কোনরূপ বিনিময় ব্যতিরেকেই। কেননা যে লোক একটি টাকা দুই টাকায় বিক্রয় করে, সে একটি টাকা অতিরিক্ত গ্রহণ করে; কিন্তু সেজন্যে তাকে কিছুই দিতে হয় না। আর মানুষের টাকা তো তাদের প্রয়োজন পুরণার্থেই লাগে। তার একটি বিশেষ ও বিরাট মর্যাদাও রয়েছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
মানুষের রক্তের যে মর্যাদা, মানুষের ধন-মালেরও ঠিক সেই মর্যাদা।
এ কারণে কোনরূপ বিনিময় না দিয়ে তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম হওয়াই বাঞ্ছনীয়।
দ্বিতীয়তঃ সুদের মাধ্যমে অর্থাগমের ওপর নির্ভরশীলতা মানুষকে শ্রম করে উপার্জন করা থেকে বিমুখ ও অনুৎসাহী বানিয়ে দেয়। সুদী করবার বা সুদ ভিত্তিক লগ্নির ফলে যখন অতিরিক্ত অর্থ পাওয়াই যাচ্ছে, তা নগদ হোক বা বাকী, তখন শ্রম করে, ব্যবসায় ও শিল্পোৎপাদনের খাটাখাটুনির কোন প্রয়োজন বোধই লোকদের মধ্যে জাগবে না এবং তার দরুন সামষ্টিক কল্যাণ ব্যবস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। আর ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কৃষি ও নির্মাণ প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন না হলে মানব-সাধারণের কোন কল্যাণের চিন্তা বা আশাই করা যায় না।
আমাদের মতে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে সুদ হারাম হওয়ার এ-ই হচ্ছে কারণ।
তৃতীয় কথা, সমাজের লোকদের মধ্যে প্রচলিত নিয়মে ঋণ দেয়া-নেয়ার ব্যবস্থা এর দরুন ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। কেননা সুদ যখন হারাম গণ্য করা হবে, তখন মানুষের মন এজন্যে প্রস্তুত হবে যে, তারা এক টাকা ঋণ বাবদ গ্রহণ করলে সেই এক টাকাই ফেরত দেবে। কিন্তু সুদ যদি হালাল বা প্রচলিত হয়, তাহলে প্রয়োজন মানুষকে এক টাকার পরিবর্তে দুই টাকা দিতে ও গ্রহণ করতে বাধ্য করবে। তার ফলে লোকদের পারস্পরিক সহৃদয়তা, কল্যাণ কামনা ও দয়া অনুগ্রহ বলতে কোন জিনিসের অস্তিত্বই থাকবে না।
আর এ হচ্ছে সুদ হারাম হওয়ার নৈতিক কারণ।
চতুর্থ, সাধারণত ঋণদাতা ধনী এবং ঋণগ্রহীতা দরিদ্র ব্যক্তি হয়ে থাকে। এক্ষণে সুদ-ভিত্তিক ঋণ-দান ব্যবস্থা চালু থাকলে ধনী ব্যক্তিকে গরীব দুর্বল ব্যক্তির কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণের অধিকারী বানিয়ে দেয়া হবে। কিন্ত মহান দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহমূলক ব্যবস্থায় তা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না।
এ হচ্ছে সামাজিক দৃষ্টিতে সুদ হারাম হওয়ার কারণ এবং তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, সুদ ব্যবস্থায় শক্তিমানের স্বার্থে দুর্বলকে শোষণ করার অবাধ সুযোগ ঘটে। তার ফলে ধনী আরও ধনী হয়ে যায় এবং গরীব আরও গরীবীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয় এবং সমাজের এক শ্রেণীর লোক দিন দিন মোটা হয়ে উঠে অন্যান্য বহু কয়টি শ্রেণীর লোককে পেশাষণ করে, শেষ করে। আর তার ফলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে উঠে। সমাজের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের আগুন জ্বালাতে থাকে দাঊ দাঊ করে। শেষ পর্যন্ত তার পরিণতি দেখা দেয় চরম ধ্বংস ও সামষ্টিক বিপর্যয়। আধুনিক কালের সমাজ ইতিহাস থেকেও এ কথার সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণিত। দেখা যায়, এ সুদ ও সুদখোর লোকেরাই রাজনীতির, রাষ্ট্র, প্রশাসন ও শান্তি নিরাপত্তার পক্ষে বিরাট হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সুদদাতা ও সুদী দলিলের লেখক
ধনী লোকেরাই সুদ খায় ও সুদের ভিত্তিতে ঋণ দেয়। সে ঋণী ব্যক্তিকে টাকা দেয়া, যেন মূলধনের ওপর সে বাড়তি টাকা ফেরত দেয়। এরূপ ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও যেমন অভিশপ্ত হয়ে থাকে, তেমনি জনগণের কাছেও। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে কেবল সুদখোররাই অপরাধী হয় না, যারা সুদ দেয়, সুদ খাওয়ায়, তারাও এই অপরাধে শরীক রয়েছে। সুদের দলিল যারা লেখে এবং তাতে যারা সাক্ষী হয়, তারাও কোন অংশে কম অপরাধী নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে সুদ খায়, সুদ খাওয়ায়, তার সাক্ষী হয় এবং তার দলিল লেখে, তাদের সকলেরই ওপর আল্লাহ্ তা’আলা অভিশাপ করেছেন। (মুসনাদে আহমদ, আবূদাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)
অবশ্য সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করার যদি তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে শুধু সুদখোরই গুনাহগার হবে। তবেঃ
১. যদি বাস্তবিকই তার প্রয়োজন থাকে। নিছক নিজের প্রয়োজন পূরণ বা উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপকতা বিধান তার লক্ষ্য হবে না। প্রয়োজনের অর্থ, মানুষ তা থেকে বাঁচতে চেয়েও বাঁচতে পারে না, নিজেকে ধ্বংস করতে প্রস্তুত হওয়া ছাড়া। যেমন খাদ্য, কাপড়, চিকিৎসা প্রভৃতি অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণের জন্যে এ সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে মানুষ বাধ্য হয়ে পড়ে অনেক সময়।
২. কেবলমাত্র নিজের প্রয়োজন পূরণ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ হবে। যথা দশ টাকার প্রয়োজন হলে সেখানে এগারো টাকা গ্রহণ করা হবে না।
৩. সুদ থেকে মুক্তি লাভের জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে হবে। এমন ঠেকায় পড়া ব্যক্তির সাহায্য করা মুসলিম জনগণের কর্তব্য। কিন্তু ঠেকায় পড়া ব্যক্তি যদি সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায়ই না পায়, তাহলে সে সুদ ভিত্তিক ঋণ গ্রহণ করতে পারে, তবে শর্ত হচ্ছে তার জন্যে তার মনে কামনা-বাসনা জাগতে পারবে না, সে ব্যাপারে সীমাও লংঘন করা চলবে না। এরূপ অবস্থা হলে হয়ত আল্লাহ্ তাকে মাপ করে দেবেন।
৪. আর ঠেকায় পড়ে এ কাজ করতে হলে অত্যন্ত ঘৃণা সহকারে এ কাজ করবে। তাতে সে সন্তুষ্ট থাকবে না, অসন্তোষ প্রকাশ করবে। যতদিন না আল্লাহ্ তার জন্যে অন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন, শুধু ততদিনই এ কাজ করা যাবে।
ঋণ লওয়া থেকে নবী পানা চাইতেন
মুসলমান মাত্রেই একথা জানা উচিত যে, ইসলাম জীবনে ভারসাম্য সৃষ্টি ও অর্থনীতিতে মধ্যম পন্থা অনুসরণ করার হেদায়েত দিয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা সীমালংঘন করো না। কেননা আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।
( আরবি******************) বেহুদা খরচ করো না। কেননা বেহুদা অর্থ ব্যয়কারী লোকেরা শয়তানের ভাই ও দোসর হয়ে থাকে। (সূরা বনী-ইসরাঈলঃ ২৬-২৭)
কুরআন মজীদ মুসলমানদের আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর দেয়া সম্পূর্ণ ধন-সম্পদই ব্যয় করে দিতে বলেনি, তা থেকে তার অংশ ব্যয় করার কথাই বলেছে। আর যে লোক নিজ উপার্জন থেকে কিছু অংশ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, সে সম্ভবত কখনই দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়বে না। এ মধ্যম ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বনের অনিবার্য দাবি এই যে, কোন মুসলমান ঋণ প্রহণ করতে কখনই বাধ্য হবে না। বিশেষ করে নবী করীম (সা) মুসলমানের ঋণ গ্রহণ করাকে কখনই পছন্দ করেন নি। কেননা স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির জন্যে ঋণ রাতের দুশ্চিন্তা ও দিনের বেলার লাঞ্ছনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নবী করীম (সা) সব সময় এ ঋণ গ্রহণ থেকে আল্লাহর কাছে পানা চেয়েছেন। তিনি এই দো’আ করতেনঃ ( আরবি******************)
হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই ঋণের বোঝা বৃদ্ধি ও রুদ্র রোষ থেকে।
বলতেনঃ ( আরবি******************)
আমি কুফরি ও ঋণ থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাই।
এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলঃ হে রাসূল! আপনার মতে কুফরি ও ঋণ কি সমান ব্যাপার? উত্তরে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ।
তিনি নামাযে প্রায়ই দো’আ পড়তেনঃ ( আরবি******************)
হে আল্লাহ্, আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে পানা চাই।
এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করা হলোঃ ( আরবি******************)
হে রাসূল! আপনি ঋণগ্রস্ততা থেকে খুব বেশি বেশি পানা চান কেন? উত্তরে তিনি বললেনঃ মানুষ যখন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন সে কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে এবং ওয়াদা করে তার খেলাফ করে। (নিসায়ী, হাকেম)
ঋণগ্রস্ততা নৈতিকতার দৃষ্টিতে যে কতখানি মারাত্মক তা এসব হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ ও দিনের মতো ভাস্বর হয়ে উঠে।
কোন মৃতের লাশ জানাযা পড়ার জন্যে নবী করীম (সা)-এর কাছে নিয়ে আসা হলে; যদি জানতে পারতেন যে, সে ঋণগ্রস্ত হয়ে মরেছে এবং তা শোধ করার মতো কিছুই রেখে যায়নি, তখন তিনি তার জানাযা নামায পড়তেন না। জানাযা না পড়ে তিনি লোকদের এই ঋণগ্রস্ততার মারাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চাইতেন মাত্র। উত্তরকালে রাসূলে করীম (সা)-এর হাতে যখন বিপুল গনীমতের মাল-সম্পদ জমা হলো, তখন তিনি তা থেকেই মৃতের ঋণ শোধ করার ব্যবস্থা করতেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
শহীদের সব গুনাহই মাফ হয়ে যায়। কিন্তু ঋণ ক্ষমা হয় না। (মুসলিম)
এসব কথার আলোকে বলতে হয়, মুসলমানের কখনও ঋণ গ্রহণ করা উচিত নয়। তবে নিতান্ত ও কঠিন ধরনের ঠেকায় পড়ে গেলে অন্য কথা। আর এ অবস্থায় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে তা শোধ করার মনোভাব প্রবল রাখতে হবে সব সময়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
যে লোক অন্যদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করল এবং তা আদায় করে দেয়ার মনোভাব রাখল, তার ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা আল্লাহ্ তা’আলা করে দেবেন। আর যে লোক ঋণ গ্রহণ করে তা না দেয়ার বা নষ্ট করার মনোভাব নিয়ে, আল্লাহও তাঁকে বিনষ্ট করবেন। (বুখারী)
বস্তুত মুসলমান যখন নেহায়েত ঠেকায় না পড়ে কখনও ঋণ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হতে পারে না, তখন তাকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে কি করে বাধ্য করা যেতে পারে?
বেশি মুল্যে বাকী ক্রয়
এখানে আরও একটি কথার ব্যাখ্যা হওয়া আবশ্যক মনে হচ্ছে। নগদ দামে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করা যেমন জায়েয, তেমনি পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বাকী মূল্যে ক্রয় করাও নাজায়েয নয়। তবে তাতে একটা মেয়াদ নিদিষ্ট থাকতে হবে। নবী করীম (সা) নিজে ইয়াহূদীর কাছ থেকে তাঁর ঘরের লোকদের জন্যে বাকীতে খাদ্যপণ্য ক্রয় করেছেন। তবে সেজন্যে তিনি তাঁর লৌহবর্ম বন্ধক রেখেছিলেন।
কিন্তু বিক্রেতা যদি নগদ মূল্য না দেয়া ও বাকীতে ক্রয়ের দরুন পণ্য মূল্য বেশি ধার্য করে- অনেক বড় বড় ব্যবসায়ী মূল্য বাড়িয়ে দিয়ে ও কিস্তিতে আদায় করার শর্তে পণ্য বিক্রয় করে থাকে- অনেক ফিকাহবিদই মনে করেন, এ ধরনের বিক্রয় হারাম। কেননা মূল্য আদায় করণে যে বিলম্ব করা হচ্ছে, তার বিনিময়েই বেশি মূল্য ধার্য করা হচ্ছে। আর তা এক ধরনের সুদই বটে। তবে সাধারণ আলিম ও ফিকাহবিদগণ এরূপ বিক্রয়কে জায়েয মনে করেন। তারা বলেন, ক্রয়-বিক্রয় মূলত তো হালাল এবং জায়েয। তা হারাম বলার পক্ষে কোন দলিলই পাওয়া যেতে পারে না। আর এরূপ ক্রয়-বিক্রয় সবদিক দিয়ে সুদী কারবারের মতোও নয়। তাঁরা মনে করেন, অনেক কয়টি দিকের দিকের বিবেচনায় বিক্রেতা বাকী মূল্যে বিক্রয় করে বলে পণ্যের অতিরিক্ত মূল্য ধার্য করতে পারে, তার সে অধিকার রয়েছে। তবে তা অবশ্যই সাংঘাতিকভাবে বেশি মূল্য হওয়া উচিত নয়, তাতে ক্রেতার ওপর জুলুম হওয়ার মতো কোন অবস্থাও সমর্থনীয় নয়। নতুবা তাও হারাম হবে।
ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ বাহ্যত এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েযই হবে। কেননা এ পর্যায়ের কতগুলো সাধারণ দলিল প্রমাণ রয়েছে। আর শাফেয়ী, হানাফী ও যায়দ ইবনে আলী প্রমুখ ফকিহর মতেও তা জায়েয। ( আরবি******************)
আগে মূল্য দেয়া ও পরে পণ্য গ্রহণ
নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্য অগ্রিম বিক্রেতাকে দেয়া ও নির্দেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার বিনিময়ে পণ্য গ্রহণকে ইসলামী পরিভাষায় ‘সিলম’ বিক্রয় বলা হয় এবং তা জায়েয। মদীনায় এর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কিন্তু নবী করীম (সা) এতে কতগুলো শর্ত আরোপ করেছেন, যা পালন করা হলে তাতে শরীয়তের সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা পায়।
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ নবী করীম (সা) মদীনায় উপস্থিত হলেন, যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, মদীনার লোকেরা মূল্য অগ্রিম দিচ্ছে যেন এক বছর বা দুই বছর পর তার বিনিময়ে ফসল লাভ করতে পারে।
তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি******************)
যে লোক অগ্রিম মূল্য দিয়ে কোন কিছু কিনবার সাব্যস্ত করবে, সে যেন তার ওজন, পরিমাণ ও সময় সব কিছুই নির্দিষ্ট করে নেয়।
এভাবে পরিমাণ, ওজন ও সময় পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকলে পারস্পরিক ঝগড়া ও গণ্ডগোল হওয়ার আশংকা থাকে না। ধোঁকাবাজি করার অবকাশও অনেকটা কম হয়ে যায়। বিশেষ গাছের ফলের অগ্রিম সওদা করা থেকে নবী করীম (সা) এ জন্যেই নিষেধ করেছেন। কেননা তাতে ধোঁকা ও ঠকবাজির ভয় রয়েছে। অনেক সময় নৈসর্গিক বিপদে পড়ার দরুন গাছে আদৌ ফলই ধরে না। তখন তা সাংঘাতিক অবস্থা দেখা দেয়।
এ পর্যায়ের কারবারের সঠিক পন্থা এ হতে পারে যে, বিশেষ গাছ বা বিশেষ জমির ফসলের শর্ত লাগানো উচিত নয়। কেবল ওজন ও পরিমাণ নির্ধারণ করে সওদা করা যেতে পারে। কিন্তু গাছ বা জমির মালিকের কাছ থেকে যদি অবৈধভাবে স্বার্থ উদ্ধার করা হয়। অর্থাৎ সে যদি এ সওদা করতে বাধ্য হয়, তাহলে তা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা।
শ্রম ও মূলধনের পারস্পরিক সহযোগিতা
কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি কৌশল অনুযায়ী মানুষকে স্বীয় অফুরন্ত নিয়ামতে ধন্য করেছেন। কত মানুষই এমন, যাদের মধ্যে জ্ঞান-প্রতিভা ও কর্মক্ষমতা অসীম, কিন্তু তাদের কাছে অর্থ নেই। পক্ষান্তরে বহু লোক এমনও রয়েছে, যাদের অর্থের কোন পরিমাপ সীমা নেই, কিন্তু যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে, যাদের কাছে ধন-সম্পদ রয়েছে, তারা তাদের ধন-সম্পদ কর্মক্ষমতা সম্পন্ন লোকদের হাতে সঁপে দেয় না কেন? তারা তা পেলে শ্রম মেহনত করে সেই ধন-সম্পদকে অধিক কল্যাণময় রাখতে পারে। আর ধনমালের অধিকারীরা নিজেদের ধনের বিনিময়ে বিপুল মুনাফার অংশীদারও হতে পারে।
এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলব, ইসলামী শরীয়ত মূলধন ও কর্মক্ষমতা অথবা মূলধন ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার পথে কোন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেনি। বরং ইনসাফ ও সুবিচারের ভিত্তিতে ও নির্ভুল সঠিক ব্যবস্থাপনার অধিন সহযোগিতার পন্থা উদ্ভাবন করেছে। অতএব ধনশালী ব্যক্তি যদি তার সঙ্গীর সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কোন মুনাফামূলক কারবার করতে চায় তাহলে এ অংশীদারিত্বের সমস্ত ফলাফলকে দায়িত্ব সহকারে তাকে তা গ্রতণ করতে হবে। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় তাকে বলা হয় ‘মুজারিবাত’ কিংবা ‘কিরাজ’। ফিকাহবিদগণ এ কাজে শর্ত আরোপ করেছেন যে, কারবারের উভয় পক্ষকেই লাভ বা লোকসান সব কিছুতেই শরীক হতে হবে এবং তার হার নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। তা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ, এক-তৃতীয়াংশ কিংবা এক-চতুর্থাংশ এক পক্ষের জন্যে হবে, আর অবশিষ্ট হবে অপর পক্ষের। মূল কারবার এভাবে ঠিক হয়ে যাওয়ার পর তাতে মুনাফা হলে চুক্তি অনুযায়ী তা পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বন্টন হবে। আর লোকসান হলে মুনাফা থেকে তা বাদ দিয়ে নিয়ে হার মতো ভাগ করে নিতে হবে। আর মুনাফার তুলনায় লোকসান যদি বেশি হয় তাহলে এ অতিরিক্ত লোকসান মূলধন থেকে নিয়ে নেয়া হবে। মূলধনের মালিককে লোকসানের অংশ তার মূলধন থেকে কেটে দেয়া কর্তব্য, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কেননা তার অংশীদারকেও শ্রম ও মেহনতের ক্ষতিটা মেনে নিতে হচ্ছে।
সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে এ-ই ইসলামের বিধান। মূলধনের মালিকের জন্যে মুনাফার সীমা নির্ধারণ ও তার নিরাপত্তা দেয়া- সে লাভ হোক, লোকসান হোক, তাকে মুনাফা দিয়ে যাওয়াই হবে, তা সুবিচার নীতি ও ইনসাফ ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাতে যোগ্যতা ও শ্রমের ওপর মূলধনকে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ও অকারণ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। উপরন্তু তা সেই জীবন পদ্ধতিরও বিরোধী যা মানুষের জন্যে যেমন মুনাফার ব্যবস্থা করে, তেমনি ক্ষতিকরও। শুধু তা-ই নয়, তদ্দরুন উপার্জনকে নিশ্চিতকরণের ঝোঁক-প্রবণতাকেও সমর্থন দেয়া হয়। তার জন্যে না শ্রম করার প্রয়োজন, না ক্ষতির ঝুঁকি মাথা পেতে নেয়ার কোন কারণ দেখা দেয়। ফলে তা প্রকৃতপক্ষে সুদ ও সুদী কারবারের মতোই হয়ে দাঁড়ায়।
নবী করীম (সা) এ রকম ভাগে জমি চাষ করতে দিতে নিষেধ করেছেন যে, জমির একটা নির্দিষ্ট অংশের ফসল এক পক্ষ পাবে আর অপর পক্ষ পাবে অপর নির্দিষ্ট অংশের ফসল। ফসলের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ওপরও ভাগ চাষ করতে নিষেধ করেছেন। কেননা এটা ঠিক সুদ বা জুয়ার মতোই ব্যাপার। হতে পারে যে, জমির সেই নির্দিষ্ট অংশে কোন ফসলই হলো না অথবা সেই নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক ফসলও হলো না। তাতে এক পক্ষের সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকে যাওয়ার অবস্থা হতে পারে। অথচ অপর পক্ষ পূর্ণভাবে লাভবান হয়ে যাবে। আর এ অবস্থা কোনক্রমেই ইনসাফপূর্ণ হতে পারে না।
মুজারিবাত ইসলামে জায়েয। কিন্তু সেজন্যে শর্ত এই যে, মূল বারবারের লাভ-লোকসানের দিক খেয়াল না রেখে এক পক্ষের জন্যে নিশ্চিত মুনাফার ব্যবস্থা থাকতে পারবে না। এ মতের ওপর ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সে শর্ত হলে ‘মুজারিবাত’ জায়েয হবে না ঠিক যে কারণে ‘মুজারিবাত’ জায়েয হয় না। পারস্পরিক জমি চাষের ব্যাপারটিও অনুরূপ কারণে নাজায়েয হয়ে যায়। ফিকাহবিদগণ বলেন, এক পক্ষ যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকাই মুনাফা লাভের শর্ত ধার্য করে, আর কারবারের ফলে অতটা পরিমাণ টাকাই মুনাফা হয়, তাহলে তার অর্থ হবে, সমস্ত মুনাফা এক পক্ষই পেয়ে গেল; বরং আদপেই মুনাফা না হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি বেশি মুনাফা পাওয়ার শর্তে কারবার করেছে সে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য হবে। ( আরবি******************)
উপরের বর্ণিত কারণটি ইসলামের মৌলিক ভাবধারার সাথে পুরা মাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুত ইসলামের সকল নীতি ও বিধানই সুদৃঢ়, সুস্পষ্ট ও নিরেট ইনসাফের ওপর ভিত্তিশীল।
মূলধনের পারস্পরিক অংশীদারিত্ব
ব্যক্তিগতভাবে নিজের মূলধন নিজের ইচ্ছামত কোন মুবাহ কাজে বিনিয়োগ করা ও তা থেকে মুনাফা লাভ করা, উপরন্ত কোন অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে মুজারিবাতের বিধান অনুযায়ী কারবার করার জন্যে দেয়া যেমন জায়েয, অনুরূপ মূলধন বিনিয়োগকারী লোকেরা একত্র ও পারস্পরিকভাবে সম্মত হয়ে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী ফার্ম বা সংস্থা গড়ে তোলা অথবা অন্য কোন কারবারে পারস্পরিক শরীকদারীর ভিত্তিতে কাজ করাও সম্পর্ণ জায়েয। কেননা অনেক ধরনের কারবার এমন হয়ে থাকে, যার জন্যে বহু সংখ্যক হস্তের বুদ্ধিমানের ও বিরাট পরিমাণ মূলধনের একত্র সমাবেশ একান্তই অপরিহার্য। আর তা পারস্পরিক সহযোগিতা ও শরীকদারীর মাধ্যমেই পূরণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা কল্যাণময় পুণ্যময় ও আল্লাহ্ ভীতির কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর।
আর যে কাজই ব্যক্তি বা সমাজ-সমষ্টির কল্যাণ সাধন বা অকল্যাণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে করা হবে, তা-ই কল্যাণময় এবং আল্লাহ্ ভীতির কাজ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে শর্ত এই যে, তা অবশ্যই ভাল নিয়্যত ও মন-মানসিকতা সহকারে সম্পন্ন করতে হবে।
পারস্পরিক শরীকদারীকে ইসলাম শুধু জায়েয ও সঙ্গত ঘোষণাই করেনি; বরং তাতেই বরকত নিহিত বলেছে। তাতে যেমন দুনিয়ায় আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার ওয়াদা রয়েছে, তেমনি পরকালেও তাতেই বিপুল সওয়াব পাওয়ার আশা। তবে তা জায়েয সীমার মধ্যে থেকে ও সুদ, ধোঁকা,প্রতারণা, জুলুম, লোভ-লালসা ও খিয়ানতকরণ থেকে সযত্নে দূরে থেকে শরীকদারীর কারবার করতে হবে। নবী করীম (সা) এরূপ শরীক ব্যবসায়ীদের সম্পর্কেই বলেছেনঃ ( আরবি******************)
শরীকদ্বয়ের প্রতি আল্লাহর সাহায্য থাকে, যতক্ষণ না তাতে একজন অপর জনের সাথে অবিশ্বাসের কাজ করবে। যদি একজন অপর জনের সাথে খিয়ানত করে, তহলে আল্লাহ্ সে সাহায্য তুলে নেন ও বন্ধ করে দেন।
রাসূলে করীম (সা) আল্লাহর কথা উদ্ধৃত করেছেন এ ভাষায়ঃ ( আরবি******************)
দুই শরীকী কারবারীদের মধ্যে আমি তৃতীয়, যতক্ষণ একজন অপরজনের খিয়ানত করবে না। যদি একজন অপর জনের খিয়ানত করে তাহলে আমি তাদের দুজনের মধ্য থেকে বের হয়ে যাই আর সেখানে শয়তান এসে যায়।
বীমা কোম্পানী
ব্যবসায়ের এক অতি আধুনিক রূপ হচ্ছে বীমা কোম্পানী। বীমা নানা রকমের হয়ে থাকে। জীবন-বীমা, দুর্ঘটনা বীমা, অগ্নি বীমা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এ ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের হুকুম কি, তা-ই আলোচ্য। ইসলামে কি এ ধরনের ব্যবসা চলতে দেয়া হবে? এ প্রশ্নের জবাবের পূর্বে বীমা কোম্পানীসমূহের প্রকৃতি জানতে হবে। বীমা যে করায় বীমা কোম্পানীর সাথে তার সম্পর্ক কি ধরনের হয়, তাও জানা আবশ্যক। অন্য কথায়, বীমাকারী কি কোম্পানীর মূল সংস্থায় একজন অংশীদার হিসেবে বিবেচিত? যদি তা-ই হয় তাহলে বীমাকারীকে মূল ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে সমানভাবে শরীক হতে হবে। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বীমায় বীমাকারীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বার্ষিক হিসাবে কোম্পানীকে দিয়ে দিতে হয়। যে ব্যবসায়ের বীমা করানো হয়েছে, তা যদি কোন দুর্ঘটনার শিকার না হয়, তাহলে সে ব্যবসায়ের মালিককে দেয়া সব টাকাই কোম্পানী নিয়ে নেবে ও হজম করে ফেলবে, তা থেকে কিছু ফেরত দেয়া হবে না। অবশ্য দুর্ঘটনা কবলিত হলে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করা হয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা শরীকদারী কারবার বা ব্যবসায়ের প্রতিকৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।
জীবন বীমার নিয়ম হচ্ছে, যদি দুই হাজার টাকার বীমা করানো হয় এবং প্রথম কিস্তি দিয়ে দেয়ার পর মৃত্য সঙ্ঘটিত হয়, তাহলে বীমাকারী ব্যক্তি পূর্ণ দুই হাজার টাকা পাওয়ার অধিকারী কিন্তু সে যদি মূল ব্যবসায়ের অংশীদারের মতো হতো, তাহলে দেয়া কিস্তির পরিমাণ টাকা ও সেই হারে মুনাফাটুকুই তার পাওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বীমাকারী যদি কোম্পানীর নিয়মাবলী লংঘন করে ও কিস্তি দিতে অক্ষম হয়, তাহলে দেয়া সব টাকা বা তার অংশ-বিশেষ থেকে বঞ্চিত থাকতে হবে। আর এ নিয়মটা যে অন্যায়, জুলুম ও অসত্য শর্ত, তা বলাই বাহুল্য।
আর উভয় পক্ষ যদি নিজ নিজ সম্মতিক্রমে এ শর্ত মেনে নেয় এবং এরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়- নিজ নিজ স্বার্থ ভাল করে বুঝে-শুনেই হোক-না কেন, তবু তা জায়েয হবে না। কেননা সুদখোর ও সুদ গ্রহীতারাও পারস্পরিক সম্মতিক্রমেই এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। জুয়া খেলে যারা, তাদেরও পারস্পরিক সম্মতি থাকে, তাতেই হারাম কখনই হালাল হয়ে যেতে পারে না। এ ধরনের সম্মতি গ্রহণযোগ্য নয়। এটা এমন নয় যে, এতে ধোঁকাবাজি ও সীমালংঘনের সামান্য অংশও নেই। এতে এক পক্ষের মুনাফা নিশ্চিত আর অন্য পক্ষের লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এসব ক্ষেত্রে আসল ভিত্তি হতে হবে সম্পূর্ণ নির্ভেজাল সুবিচার ও ন্যায়পরতা। সর্ব ব্যাপারেই তা এমনভাবে নিশ্চিত হতে হবে যে, না নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, না অন্যরা ক্ষতির মধ্যে পড়বে।
বীমা কোম্পানী কি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা
বীমাকারী ও বীমা কোম্পানীর মধ্যে সম্পর্ক অংশীদারী কারবারের মতো নয়। তাহলে সে সম্পর্কের রূপটা কি? তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের সম্পর্ক কি এটা? এসব প্রতিষ্ঠান কি পারস্পরিক সাহায্য সংস্থা যা দানকারীদের সহযোগিতা বা অংশীদারিত্বে চালান হয়? আর আর্থিক অংশীদারিত্ব হয় পরস্পরের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে?...তা যে নয়, তাতো সুস্পষ্ট।
পারস্পরিক সাহায্যের জন্যে নির্ভুল কর্মপন্থা গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বিপন্ন লোকদের সাহায্য করা তার লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং এ উদ্দেশ্যেই অর্থ জমা হওয়া উচিত। এজন্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবেঃ
১. ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদ ভ্রাতৃত্বের খাতিরে দান হিসেবে দেবে এবং এ ফাণ্ড থেকে কেবলমাত্র প্রয়োজন ক্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাহায্য করতে হবে।
২. ফণ্ড থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে কেবলমাত্র বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে হবে।
৩. কেউ যেন এ উদ্দেশ্যে দান না দেয় যে, দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হলে সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ লাভ করবে। বরং প্রতিষ্ঠানের ফাণ্ড থেকে সাধ্যমত একটা দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে, যেন তা দিয়ে সম্পূর্ণ বা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিপূরণ হয়ে যায়। ( আরবি******************)
৪. দান দানই। তা ফেরত নেয়া সম্পূর্ণ হারাম। কাজেই যখন কোন দুর্ঘটনা ঘটবে তখন তাতে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিচার বিবেচনা করতে হবে।
এ শর্তসমূহ কেবলমাত্র এমন কতিপয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের ওপরই প্রযোজ্য হতে পারে, যা ঠিক এ উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাতে ব্যক্তিরা দান হিসেবে নিজেদের মাসিক অংশ আদায় করে দেবে, তা ফেরত নেয়ার তাদের কোন অধিকার থাকবে না। এ শর্ত ধার্য থাকে না যে, বিপদকালে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তাদের পেয়ে যেতে হবে।
কিন্তু বীমা কোম্পানীসমূহ এবং বিশেষ করে জীবন বীমায় নিম্নোক্ত শর্তসমূহ আদৌ আরোপ করা হয় না। তার অবস্থা সম্পর্ণ স্বতন্ত্র।
১. বীমাকারীরা (policy Holdders) দান হিসেবে কিস্তি দেয় না। তার চিন্তাও তাদের মনে জাগে না।
২. বীমা কোম্পানীসমূহ নিজেদের মূলধন হারাম সুদী করবারে বিনিয়োগ করে মুনাফা কামাই করে। কিন্তু কোন মুসলমানই সুদী কারবারে শরীক হতে পারে না। এ ব্যাপারে সুবিধাবাদী ও কঠোরতাবাদী সকলেই একমত।
৩. বীমাকারী চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর সমস্ত কিস্তির টাকা ফেরত নিয়ে নেয়। সেই সাথে সে আরও অতিরিক্ত টাকা পেয়ে যায়। তা হলে এ অতিরিক্ত টাকা সুদ ছাড়া আর কি মনে করা যেতে পারে?
অনুরূপভাবে ধনী সামর্থবান ব্যক্তিকে অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তির তুলনায় বেশি টাকা দেয়াও পারস্পরিক সাহায্যমূলক ভাবধারার সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা দেখা যায়, অর্থশালী ব্যক্তি মোটা টাকার বীমা করায়। এ জন্যে মৃত্যু বা দুর্ঘটনা কালে তাকে সেই অনুপাতে অনেক বেশি টাকা দেয়া হয়। কিন্তু সাহায্য করার ভাবধারা টাকা দেয়া হবে।
৪. যে ব্যক্তি বীমার চুক্তি শেষ করতে ইচ্ছুক হয়, তাকে দিয়ে দেয়া অংশের টাকায় বড় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এরূপ ক্ষতি স্বীকার করার শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন বৈধ কারণ নেই।
পরিবর্তন ও সংশোধনী
এ সব সত্ত্বেও বর্তমানে প্রচলিত দুর্ঘটনা সংক্রান্ত বীমা ব্যবস্থার সংশোধন করে তাকে ইসলামী নিয়ম নীতির খুব কাছাকাছি নিয়ে আসা সম্ভবপর। আর তার জন্যে এ ব্যবস্থা নিতে হবে যে, বিনিময়ের শর্তের ভিত্তিতে দানসমূহ গ্রহণ করার নীতি অবলম্বন করতে হবে। বীমাকারী কোম্পানীকে আর্থিক সাহায্য দেবে এ শর্তে যে, দুর্ঘটনা ঘটলে কোম্পানী তাকে ক্ষতিপূরণ দেবে, তাতে তার সাহায্য হয়ে যাবে, বিপদের মাত্রা লাঘব হবে। কোন কোন ফিকহী মতে এরূপ চুক্তি জায়েয। বীমার ক্ষেত্রে যদি এরূপ পরিবর্তন ও সংশোধনী কার্যকর করে নেয়া হয় আর বীমা কোম্পানীসমূহের কার্যাদি সুদমুক্ত হয়, তাহলে তা জায়েয হবে বলে মনে করা যায়। কিন্তু জীবন-বীমার সমস্ত ব্যাপার শরীয়তের বিধান থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থিত।
ইসলামে বীমা পদ্ধতি
বীমা কোম্পানীসমূহ বর্তমানে ইসলামী বিধান অনুযায়ী চলছে না, তা আমরা দেখতে পেলাম। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মূল বীমা ব্যাপারটাই বুঝি ইসলামের পরিপন্থী। আসলে তা নায়। তার বর্তমান প্রচলিত নীতিগুলোই শুধু ইসলামের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ, এ হচ্ছে আসল কথা। তাতে যদি ইসলাম অনুকূল নিয়ম-নীতি অবলম্বন করা হয়, তাহলে তা ইসলামের দৃষ্টিতে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য হবে।
সত্যি কথা এই যে, ইসলামী জীবন-বিধান মুসলিম জনগণ ও ইসলামী রাষ্ট্রের অধীন বসবাসকারী লোকদের জন্যে সামষ্টিক ভরণ-পোষণ ব্যবস্থা বা সরকারী অর্থ ভাণ্ডার তথা বায়তুলমালের সাহায্যে বীমার নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর করেছে। ইসলামের বায়তুলমাল প্রকৃতপক্ষে জনগণের জন্যে বীমা কোম্পানিই বটে। যারাই তার অধীন বসবাস করবে তাদের সকলের জন্যেই তা কাজে আসবে।
দুর্ঘটনা ও বিপদ-আপদকালে ব্যক্তিদের সাহায্য সহযোগিতা করার দায়িত্ব ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেউ যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে সরকারী দায়িত্বশীলের কাছে নিজের সমস্যা পেশ করতে পারে। সরকার সেই অনুযায়ী তার ক্ষতিপূরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। মৃত্যুর পর অসহায় উত্তরাধিকারীদের জন্যেও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে।
নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
প্রত্যেকটি মুসলিমের সাথে আমার সম্পর্ক তার নিজের তুলনায়ও অনেক বেশি নিকটবর্তী। যে মুসলমান ধন-মাল রেখে যাবে তা তার উত্তরাধিকারীই পাবে। আর যে লোক ঋণ বা অক্ষম শিশু সন্তান রেখে যাবে সেই ঋণ শোধ ও শিশুদের লালন-পালনের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমার ওপরই বর্তিবে।
ইসলাম মুসলিম জনগণের জন্যে যে গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছে ফরয যাকাত ব্যয়ের জন্যে নির্দিষ্ট করা ক্ষেত্র ( আরবি******************) ঋণগ্রস্ত লোকগণ। পূর্বকালের কোন কোন তাফসীরকার এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যার ঘরবাড়ি সব পুড়ে গেছে কিংবা বন্যা-বাদল যার সব ধন-সম্পদ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সে-ই এ গারেমীন-এর মধ্যে গণ্য।
কৃষি জমিতে ফসল উৎপাদন
মুসলমান কৃষি জমির মালিকানা শরীয়ত মুতাবিক লাভ করলে সে জমি চাষ করে ফসল লভ করা বা গাছপালা লাগিয়ে ফল ফলাদি হাসিল করা তার একান্ত কর্তব্য হয়ে পড়ে। বিনা চাষে জমিকে বেকার ফেলে রাখা ইসলামে অবৈধ কাজ। কেননা তা করা হলে আল্লাহর দেয়া নিয়ামতের প্রতি অবজ্ঞা দেখানো হবে। ধন-সম্পত্তির অপচয়ও বলা যায় তাকে। অথচ নবী করীম (সা) ধন-সম্পত্তি বিনষ্ট করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। জমি মালিক জমি থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে নানাবিধ পন্থা ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে পারে।
জমি কাজে লাগাবার নানা উপায়
জমির মালিক নিজেই জমি চাষাবাদ করবে। গাছপালা লাগিয়ে তাতে পানি সেচ করার সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তার ফলে সে জমিতে ফসল ফলবে বা গাছ পালায় ফলন ধরবে। এটা বস্তুতই খুব পছন্দনীয় কাজ। যেসব মানুষ, পাখি ও জীবজন্তু এসব ক্ষেত বাগান থেকে উপকৃত হবে, তার সওয়াব সেই মালিকই পাবে। রাসূলে করীম (সা)-এর বড় বড় সাহাবী যে কৃষি ও বাগান রচনার কাজ করেছেন, তা তো সকলেই জানা কথা।
দ্বিতীয় পন্থা
জমি মালিক নিজ জমি চাষাবাদ করতে পারছে না। তখন সে নিজের জমি এমন ব্যক্তিকে ধার হিসেবে দিয়ে দেবে, যে নিজের যন্ত্রপাতি, শ্রমিক, বীজ ও জন্তু লাগিয়ে চাষাবাদের কাজ সম্পন্ন করবে। কিন্তু জমি মালিক নিজে তা থেকে কিছুই নেবে না। এভাবে ধারে জমিদান ইসলামে কাম্য ও প্রশংসিত। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
যার জমি আছে, সে নিজে তা চাষাবাদ করবে, নতুবা তার ভাইকে তা চাষাবাদের জন্যে দিয়ে দেবে।
হযরত জাবির (রা) বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমরা নবী করীম (সা)-এর যুগে ‘মুজাবিরাত’ নিয়মে জমি চাষাবাদ করতাম। ফলে আমরা কাটাই হওয়ার পর শীষের মধ্যে অবশিষ্ট দানাগুলো এখান-ওখান থেকে পেয়ে যেতাম। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ যার জমি আছে, সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে কিংবা তার ভাইকে বিনিময় ব্যতিরেকেই চাষ করতে দিয়ে দেয়। আর তা-ও না করলে তা ছেড়ে দেবে।
‘মুজাবিরাত’ অর্থ জমির একাংশের ভিত্তিতে তা চাষাবাদ করা।
কোন কোন লোক এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থের ভিত্তিতে বলেছেন, জমি দ্বারা উপকার গ্রহণের এ দুটি পন্থাই শরীয়তসম্মত, হয় নিজেই তা চাষ করবে নতুবা কোনরূপ মূল্য বা বিনিময় ছাড়াই কাউকে জমি চাষ করতে দিয়ে দেবে। আর তা হতে পারে এভাবে যে, জমি হবে তার, যে তার মালিক আর ফসল হবে তার, যে তার চাষাবাদ করবে।
( আরবি******************)
টাকা বা পয়সার বিনিময়ে জমি লাগিয়ে দেয়া ঠিক নয়। অন্য কোন প্রকান চুক্তিতেও জমি দেয়া যায় না। শুধু একটি উপায়ই আছে। হয় মালিক নিজে তা চাষাবাদ করবে, না হয় কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই অন্যকে তা দিয়ে দেবে।
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, এ সব হাদীসে জমি দিয়ে দিতে যে বলা হয়েছে, তার অর্থ এ নয় যে, দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। আসলে তা মুস্তাহাব মাত্র। এভাবে দিয়ে দেয়াটা বেশ পছন্দনীয় কাজ। আমার ইবনে দীনার থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ হযরত ইবনে আব্বাসের প্রখ্যাত ছাত্র তায়ূসকে জিজ্ঞেস করলামঃ আমি যদি ‘মজাবিরাত’ (জমি ভাগে চাষ) পরিহার করি, তাহলে কেমন হয়? জবাবে তায়ূস বললেনঃ সবচেয়ে বড় আলিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন যে, নবী করীম (সা) তা নিষেধ করেন নি। তিনি কথাটি বলেছেন এভাবেঃ ( আরবি******************)
তোমরা নিজের ভাইকে বিনিময় ছাড়াই জমি দিয়ে দেয়া তার কাছ থেকে ‘কর’ আদায় করার চেয়ে উত্তম। (বুখারী)
ভাগে জমি চাষ
তৃতীয় পন্থা হচ্ছে, যে লোক নিজের যন্ত্রপাতি বীজ ও জন্তু দ্বারা চাষের কাজ করবে, জমি মালিক তাকে জমি দেবে এ শর্তে যে, জমি ফসলের উভয়ের সম্মত পরিমাণ অংশ যেমন অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সে পাবে। জমি মালিক জমি চাষকারীকে বীজ যন্ত্রপাতি ও জন্তু দিলে তাও জায়েয হবে। এ পন্থায় জমি চাষাবাদে ব্যবস্থা করলে তাকে পারস্পরিক জমি চাষ, ভাগে জমি চাষ, মুখাবিরা, মুসাকাত ইত্যাদি বলা হয়।
নবী করীম (সা) নিজে খায়বরের জমি অর্ধেক ফসলের শর্তে চাষ করতে দিয়েছিলেন। (বুখারী, মুসলিম) এ ধরনের পারস্পরিক ‘চাষাবাদকে’ যে সব ফিকাহবিদ জায়েয মনে করেন, রাসূলে করীম (সা)-এর উপরিউক্ত কাজ তাঁদের দলিল। তাঁরা বলছেনঃ এ এক প্রখ্যাত সর্বজনপরিচিত ও সহীহ ব্যাপার। রাসূলে করীম (সা) জীবনভর মৃত্যু পর্যন্ত এ পন্থায় আমল করেছেন। তাঁর পরবর্তীকালের লোকেরাও তা-ই করেছেন। তার পরে খুলাফায়ে রাশেদুনও শেষ পর্যন্ত তাঁরই পদাংক অনুসরণ করেছেন। মদীনার এমন কোন ঘরই ছিল না, যে ঘরের লোকেরাও এ পন্থায় চাষাবাদের কাজ করেন নি। নবী করীম (সা)-এর বেগমরা এ নীতিরই অনুসরণ করেছেন। এ এমন একটা ব্যাপার যা নাকচ বা প্রত্যাহার করা যেতে পারে না। কেননা প্রত্যাহার বা নীতি বদল তো কেবলমাত্র নবী করীম (সা)-এর জীবদ্দশাতেই হতে পারত। কিন্তু যে কাজ তিনি মৃত্যু পর্যন্ত করলেন, তাঁর পর খলীফাগণও করলেন, সাহাবিগণ যে ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত ও সর্বসম্মতভাবে আমল করেছেন, একজনও যে নীতি বিরোধিতা বা প্রতিবাদ করেন নি, তা কি করে পরিত্যাক্ত ও নাকচ হয়ে যেতে পারে? আর রাসূলে করীম (সা)-এর জীবদ্দশায়ই যদি তা পরিত্যক্ত হয়ে থাকে, তাহলে তার পর তাঁর অনুসারী লোকেরা এ পন্থায় কি করে চাষাবাদ করলেন? এ বিষয়টি গোপন থাকলই বা কি করে যে, খুলাফায়ে রাশেদুন পর্যন্ত তা জানলেন না? অথচ খায়বারের ব্যাপারটি তো সর্বজনবিদিত। পরিত্যক্ত পওয়ার কথা যিনি বর্ণনা করেন তিনি-ই বা তখন কোথায় ছিলেন যে, তিনি কাউকে কিছু জানালেন না? ( আরবি******************)
ভুল নীতিতে পারস্পরিক চাষাবাদ
নবী করীম (সা)-এর সময়ে আর এক ধরনের চাষাবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু তাতে ধোঁকা, প্রতারণা ঠকবাজি ও অজ্ঞতার অবকাশ ছিল, যার দরুন পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদের সৃষ্টি হতো। এজন্যে নবী করীম (সা) চাষাবাদের এ পন্থাকে নিষেদ্ধ ঘোষণা করেন। দ্বিতীয়ত, ইসলাম সুস্পষ্ট ন্যায়পরতা ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে চায়; কিন্তু উপরিউক্ত পন্থায় চাষাবাদে সেই ন্যায়পরতা ও ইনসাফের পরিপন্থী কাজ হলেই তিনি তা নিষেধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
সে পন্থা ছিল এই যে, জমি মালিক চাষকারীর উপর এ শর্ত চাপিয়ে দিত যে, নির্দিষ্ট জমির এক-চতুর্থাংশ তার জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে ও তা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হবে। সমগ্র চাষের !ব্দর সে সেই নির্দিষ্ট জমিটুকুরই ফসল পাবে, তা যতটাই হোক। অথবা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল মাপা বা ওজন করা সে পাবে। আর অবশিষ্ট ফসল থাকবে একা চাষকারীর জন্যে, অথবা তা দুজসের মধ্যে আধা-আধি ভাগ করে দেয়া হবে।
কিন্তু নবী করীম (সা) দেখলেন যে, ন্যায়পরতা ও সুবিচারের দাবি হচ্ছে এই যে, সর্বমোট ফসলেই- তা কম হোক বেশি হোক, উভয় পক্ষকে শরীক হতে হবে। তাদের দুজনের একজনের জন্যে একটা পরিমাণ জমি বা ফসল পূর্বেই নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া ঠিক কাজ নয়। কেননা অনেক সময় জমির সেই অংশ হয়ত কোন ফসলই দিল না। তাহলে তো একজনই মাত্র যা পাওয়ার পেয়ে যাবে। আর অপর জন প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়ে থাকবে। কেননা নির্দিষ্ট খণ্ড জমিতে হয়ত কোন ফসলই ফললো না। তাহলে সে তো কিছুই পেল না অথচ অপর পক্ষ পুরোপুরি পেয়ে গেল। এরূপ অবস্থায় ইনসাফ পূর্ণ পন্থা এই হতে পারে যে, পারস্পরিক চুক্তি অনুযায়ী সমস্ত জমির সমস্ত ফসল থেকেই প্রত্যেক পক্ষ নিজ অংশ গ্রহণ করবে। যদি জমির ফসল বেশি হলো তাহলে তার ফায়দা উভয় পক্ষই পেলো। আর যদি কম হয় তাহলে উভয়ই কম কম করে পেয়ে গেল। আর যদি কোন ফসলই না হয়, সে বঞ্চনায়ও উভয় পক্ষই শরীক থাকবে। পক্ষদ্বয়ের জন্যে এ পন্থাই যে উত্তম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
হযরত রাফে ইবনে খদীজ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমাদের মধ্যে যাদের জমি ছিল তারা বেশির ভাগ পারস্পরিক চাষাবাদের নীতিতে কাজ করত। তারা জমি এ শর্তে কেরায়া দিত যে, তার এক কোণের জমির ফসল জমির মালিকের জন্যে নির্দিষ্ট করা হতো। কিন্তু অবস্থা এই হতো যে, জমির সেই নির্দিষ্ট অংশে কোন ফসল হতো না, হতো অপর ভাগে। আর কখনও জমির সেই নির্দিষ্ট অংশে ফসল হতো অপর অংশে হতো না। এই কারণে এ রূপ চাষাবাদের কাজ করতে আমাদের নিষেধ করে দেয়া হয়।
এই হযরত রাফে বলেছেনঃ ( আরবি******************)
নবী করীম (সা)-এর লোকেরা খালের কিনারে ও পানি প্রবাহের মুখের স্থানে ফল-ফসলের শর্তে চাষাবাদের চুক্তি করত কিংবা ফসল থেকে কিছু দেয়ার বিনিময়ে করত। পরে দেখা যেত এ অংশের ফসল নষ্ট হয়েছে, এ অংশের ফসল রক্ষা পেয়েছে অথবা এর বিপরীতটা হতো। আর লোকদের জন্যে এ পন্থা ভিন্ন জমি লাগানো আর কোন নিয়ম ছিল না। এ কারণে তা নিষেধ করা হয়। (মুসলিম)
নবী করীম (সা) জিজ্ঞেস করলেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের চাষের জমি-ক্ষেত লাগান-পরানের কাজ তোমরা কিভাবে কর?
লোকেরা বললঃ ( আরবি******************)
আমরা এক-চতুর্থাংশ এবং খেজুর ও গমের একটা পরিমাণের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষের চুক্তি করি।
এ কথা শুনে তিনি বললেনঃ তোমরা তা করবে না। এর অর্থ তখন একটা নির্দিষ্ট মাপের পরিমাণ ঠিক করে দিত, তারা তার ওপর থেকে নিয়ে নিত। পরে চাষকারীদের মধ্যে অবশিষ্ট ফসল ভাগ করা হতো। কেউ এক-চতুর্থাংশ কেউ চার ভাগের তিন ভাগ নিয়ে নিত।
এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, নবী করীম (সা) তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজে পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশেষভাবে উদগ্রীব থাকতেন। আর যে যে কারণে পারস্পরিক ঝগড়া-বিসম্বাদের সৃষ্টি হতে পারে বলে আশংকা করতেন, তিনি মুমিনদের সমাজ থেকে সেই সবকিছু দূর করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।
হযরত যায়দ ইবনে সাবিত (রা) বর্ণনা করেছেনঃ নবী করীম (সা)-এর সামনেই দুই ব্যক্তি জমি নিয়ে ঝগড়া করল। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি******************)
তোমাদের অবস্থা যদি এ-ই হয়ে থাকে, তাহলে তোমরা চাষ জমি ভাড়ায় দিও না।
অতএব প্রত্যেক জমি মালিকের উচিত তার সঙ্গী ও সাথীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও মর্যাদা দানকারী হওয়া। এজন্যে জমি মালিক যেন ফসলের বেশির ভাগই দাবি করে না বসে। পক্ষান্তরে চাষকারীও জমি মালিককে তার জমির দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না করে। এ প্রেক্ষিতে হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছেঃ ( আরবি******************)
পারস্পরিক ভিত্তিতে জমি চাষাবাদ করাকে নবী করীম (সা) হারাম করে দেন নি। বরং তিনি তো পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেককে অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ অবলম্বন করতে বলেছেন। (তিরমিযী)
এজন্যে তায়ূসকে যখন বলা হলো, হে আবূ আবদুর রহমান! এ ‘মুখাবিরা’ যদি ত্যাগ করি তাহলে তো ভাল হয়। কেননা লোকেরা মনে করে যে, নবী করীম (সা) তা করতে লোকদের নিষেধ করেছেন। তখন তিনি বলেছিলেনঃ
আমি তাদের সাহায্য করব, আমি তাদের দেব।
তারা নিজেদের জমি থেকে বেশি বেশি কামাই করার চিন্তিই করত না। যারা জমিতে শ্রম-মেহনত করে, তারা ক্ষুধায় কাতর হয়ে থাক, তা-ই তারা চাইত না। বরং তারা তাদের সাহায্য করত, তাদের দিত। আর বস্তুত এই হচ্ছে মুসলিম সমাজের বৈশিষ্ট্য।
অনেক সময় জমি মালিক জমিকে বেকার ফেলে রাখে। তাতে চাষাবাদও করে না, গাছ-পালাও লাগায় না। কিন্তু কোন চাষাবাদকারীকেও স্বল্প বিনিময়ে জমি দিতে প্রস্তুত হয় না। এ কারণে পযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজ তাঁর খিলাফতের বিভিন্ন দায়িত্বশীলদের নির্দেশ দিয়েছিলেনঃ এক-চতুর্থাংশ বা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ ফসলের বিনিময়ে লোকদের জমি চাষ করতে দাও, দশমাংশ পর্যন্তও দিতে বলেছিলেন এবং জমিকে অনাবাদী করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন।
নগদ টাকায় জমি লাগানো
চতুর্থ পন্থা এই হতে পারে যে, চাষাবাদকারীকে জমি চাষ করতে দেয়া হবে এ শর্তে যে, সে নগদ টাকায় মূল্য আদায় করবে।
বহু প্রখ্যাত ফিকাহবিদই এ পন্থাকে জায়েয বলেছেন। অবশ্য অপর কিছু সংখ্যক ফিকাহবিদ তা নিষেধ করেছেন। তাঁদের দলিল হচ্ছে নবী করীম (সা) জমি কেরায়ায় দিতে নিষেধ করেছেন- এটি সহীহ্ বর্ণনা। হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, হযরত রাফে ইবনে খদীজ, হযরত জাবির, আবূ সায়ীদ, আবূ হুরায়রা ও ইবনে উমর (রা) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা সকলেই বলেন যে, নবী করীম (সা) জমিকে কেরায়ায় লাগাতে অকাট্যভাবে নিষেধ করেছেন।
( আরবি******************)
জমি কেরায়া লাগানোর ভিন্নতর পন্থা ভাগে চাষ করানো। নবী করীম (সা) তাঁর জীবদ্দশায় খায়বর অধিবাসীদের সাথে এ চুক্তিই করেছেলেন এবং তার ওপর তিনি শেষ পর্যন্ত অবিচল রয়েছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদুনের আমলেও তার ব্যতিক্রম কিছু করা হয় নি।
এ পর্যায়ে ইসলামী আইনের ক্রমবিবর্তন যারা লক্ষ্য করেছেন, তাঁদের কাছে ইবনে হাজমের কথার যথার্থতা খুবই স্পষ্ট হয়ে থাকবে। তিনি লিখেছেন, নবী করীম (সা) যখন তাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁরা তাঁদের চাষের জমি কেরায়ায় লাগাতেন। রাফে ইবনে খদীজ (রা) থেকেও অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত হয়েছে। আর জমি কেরায়ায় লাগানোর ব্যাপারটা রাসূলে করীম (সা)-এর উপস্থিতির পূর্বেও যেমন চলত, তার পরও তাতে পরিবর্তন আসেনি। এ ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে পারেন না। এরপর হযরত জাবির, আবূ হুরায়রা, আবূ সায়ীদ, রাফে, যহীর (রা) ও বদর যুদ্ধে শরীক হওয়া সাহাবী এবং হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছেঃ ( আরবি******************)
নবী করীম (সা) জমি কেরায়া লাগাতে সার্বিকভাবে নিষেধ করেছেন।
এ হাদীসের দ্বারা পূর্বের মুবাহ নীতি যে বাতিল হয়ে গেল, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অতএব নগদ টাকায় জমি কেরায়া লাগানো যাঁরা জায়েয বলেন, তাঁরা ভুল কথা বলেন। তাঁদের কথা কখনই সহীহ প্রমাণিত হতে পারে না। তবে উৎপন্ন ফসলের নির্দিষ্ট অংশ দেয়ার বিনিময়ে তা কেরায়ায় লাগানো যায়েয হতে পারে। কেননা নবী করীম (সা) থেকে এবথা প্রমাণিত যে, তিনি কেরায়ায় জমি লাগাতে নিষেধ করার পর খায়বরে ফসলের ভাগের ভিত্তিতে জমি চাষ করে দেয়ার চুক্তি করেছিলেন এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অপরিবর্তীত ছিল। ( আরবি******************)
প্রাথমিককালের অনেক ফিকাহবিদই এ মত পোষণ করতেন। ইয়েমেনের প্রখ্যাত ফিকাহবিদ ও মহামান্য তাবেয়ী তায়ূস স্বর্ণ-রৌপ্যের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দেয়াকে মাকরূহ মনে করতেন। কিন্তু ফসল ভাগে দেয়ায়- তা এক তৃতীয়াংশ হোক বা চতুর্থাংশ- কোন দোষ মনে করতেন না। কেউ কেউ যখন এ বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করলেন এবং বললেন যে, নবী করীম (সা) জমি কেরায়া লাগাতে নিষেধ করেছেন, তখন তিনি বললেনঃ আমাদের কাছে হযরত মু’আয উপস্থিত হলেন- নবী করীম (সা)-ই তাঁকে ইয়েমেনে পাঠিয়েছিলেন, তখন তিনি এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি চাষ করতে দিয়েছিলেন। আর আজ পর্যন্ত তাই করে যাচ্ছি।
এ থেকে বোঝা যায়, তায়ূসের মতে নগদ মূল্যে জমি কেরায়া লাগানোই নিষেধ। তবে ফসল ভগের শর্তে জমি চাষ করতে দেয়ায় কোন অসুবিধা নেই।
মুহাম্মদ ইবনে সিরীন, কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক থেকেও এ কথাই জানা গেছে। তবে তাবেয়ীনের মধ্য থেকে কিছু লোক জমি যে-কোন ভাবে কেরায়ায় দেয়াকে নিষিদ্ধ বলে মনে করেন, তা নগত মূল্যেই হোক আর ফসল ভাগের ভিত্তিতেই হোক। কিন্তু এ মত খুব বলিষ্ঠ নয়। কেননা নবী করীম (সা) খূলাফায়ে রাশেদুন ও হযরত মু’আয (রা) নিজেরা ফসল ভাগের শর্তে জমি চাষাবাদ করেছেন, করিয়েছেন। তাতে এই পন্থার জায়েয হওয়ার কথা নিঃসন্দেহে জানা যায়। প্রাক্তন কালসমূহে মুসলমানদের জন্যে কার্যত এ নীতি অনুযায়ীই আইন প্রণয়ন করা হতো। তবে নগদ মূল্যের বিনিময়ে জমি কেরায়ায় দেয়া যে নিষেধ, তা হাদীস থেকেই প্রমাণিত। আর তা যে যুক্তিসঙ্গত, তাও নিঃসন্দেহ।
নগদ মূল্যে জমি লাগানো নিষিদ্ধ হওয়ার যৌক্তিকতা
ইসলামের মৌলনীতি ও আদর্শের দৃষ্টিতে চিন্তা-বিবেচনা করলে খালি জমি নগদ টাকার বিনিময়ে লাগানো নাজায়েয হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হবে।
ক. নবী করীম (সা) উৎপন্ন ফসলের একটা নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে জমি কেরায়া লাগাতে নিষেধ করেছেন। কেবলমাত্র ফসলের হারের ভিত্তিতে লাগানোটাই জায়েয অর্থাৎ উৎপাদনের তিন ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের একভাগের ভিত্তিতে জমি লাগানো যেতে পারে। শতকরা হারে (percentage) ভাগ ঠিক করলে খুবই ভাল হয় বলে আমরা মনে করি। তাহলে উৎপন্ন ফসলের অংশ লাভ করার ব্যাপারে উভয় পক্ষই সমানভাবে উপকৃত হবে। কোন বিপদের ফলে যদি ফসলের কোন ক্ষতি হয়, তাহলে সে ক্ষতিতেও দুই পক্ষ সমান হারে শরীক থাকবে। কিন্তু এক পক্ষের পাওনা যদি নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তাহলে সে তো ক্ষতি থেকে বেঁচে যাবে; কিন্তু অপর পক্ষের অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়ে যাওয়া একান্তই অবধারিত। তার ভাগে ঘাস শুকানো ছাড়া আর কিছু মিলবে না। এটা তো সুদ ও জুয়ার সাথে পুরোমাত্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাপার। এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য থাকে না।
এ দৃষ্টিতে যখন নগদ টাকায় জমি লাগানোর ব্যাপারটা বিবেচনা করা যায়, তাহলে তাতেও উপরি উল্লিখিত নিষিদ্ধ ধরনের পারস্পরিক চাষের মধ্যে কোন পার্থক্যই ধরা পড়ে না। জমি মালিক নগদে তার পাওনাটা নিশ্চিত রূপেই পেয়ে যায়। কিন্তু যে লোক এ টাকা দিয়ে চাষের জন্যে জমি নিল, সে তো নিজের শ্রম, যায়। কিন্তু যে লোক এ টাকা দিয়ে চাষের জন্যে জমি নিল, সে তো নিজের শ্রম, মেহনত ও মূলধন সবকিছুই কঠিন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়। সে জমি থেকে কিছু পাবে কি না, তার কোন নিশ্চয়তাই তার থাকে না। তাতে ফসল ফলবে কি না, তার কিছুই জানা নেই।
খ. উপরন্তু একজন যখন কোন জিনিস কেরায়ার ভিত্তিতে কাউকে দেয় সে তো তার মালিক। সে তার কেরায়া পাওয়ার অধিকারী হয় এ কারণে যে, সেই জিনিসটিকে ব্যবহার করে ফায়দা লাভের উপযুক্ত করে কেরায়ায় গ্রহণকারীর হাতে সোপর্দ করে দেয়। তা ব্যবহার করার দরুন তাতে যে অপচয় (Depercition) দেখা দেয় তার বিনিময় মূল্য পাওয়ার তার অধিকার রয়েছে। কিন্তু জমিকে কেরায়ায় লাগাতে কোনরূপ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয় না। জমিতে উৎপাদন শক্তি তো জমি মালিক সৃষ্টি করেন না, তা তো সম্পূর্ণ আল্লাহরই দান। দ্বিতীয়, চাষাবাদ করা হলে জমির কোন ‘অপচয়’ হয় না, যন্ত্রপাতির ন্যায় তাতে ময়লাও ধরে না, দালান-কোঠার ন্যায় তা পুরাতনও হয়ে যায় না।
গ. এও সত্য যে, কেউ যখন কোন বাড়ি কেরায়ায় গ্রহণ করে, তখন সে তাতে অবস্থান ও বসবাস করে, তা থেকে সরাসরি উপকৃত হয়। মাঝখানে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে না। এমনিভাবে কোন যন্ত্র ভারা করলেও ঠিক সেই আসল জিনিসটার দ্বারাই উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু জমি থেকে সরাসরি উপকার পাওয়া সম্ভব হয় না, আর তা থেকে উপকার লাভ নিশ্চিতও কিছু নয়। জমির ব্যাপারটা ভাড়াটে বাড়ির মতো নয়, তা থেকে ফায়দা লাভ এক অনিশ্চিত ব্যাপার। বরং জমি যখন কেরায়ায় গ্রহণ করে কেউ, তখন সে তা থেকে উপকৃত হওয়ার আশাতেই করে। আর এ আশায়ই সে তাতে শ্রম মেহনত করে, পয়সা ও সময় ব্যয় করে, তারপরও সে তা থেকে কখনও ফায়দা লাভ করে, কখনও তা করে না। কাজেই জমি ভাড়ায় গ্রহণকে বাড়ি ইত্যাদি কেরায়ায় লওয়ার মতো মনে করা ঠিক নয়।
ঘ. সহীহ্ হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ
ফল-ফলাদি পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে ক্ষেতে ও বাগানে থাকা অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করতে নবী করীম (সা) নিষেধ করেছেন। আর তার কারণ স্বরূপ বলেছেন, ‘তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ্ যদি ফল থেকে বঞ্চিত করে দেন, তাহলে তোমার ভাইয়ের কাছ থেকে নেয়া টাকা তোমার জন্যে হালাল হতে পরবে কেমন করে? ফলগুলো পাকতে শুরু করেছে, কিন্তু এখনও তা সুরক্ষিতভাবে পেয়ে যাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেননা তা কোন বিপদের কারণে নাও পাকতে পারে- এই যখন অবস্থা, তখন খালি জমি- যাতে কোদাল পর্যন্ত লাগান হয়নি, তাতে বীজও ফেলা হয়নি- কেরায়ায় দেয়া নিষিদ্ধ হবে না কেন? আসলে সঠিক ও ইনসাফপূর্ণ পন্থা হচ্ছে ফসলের হার ভাগের ভিত্তিতে পারস্পরিক চাষাবাদ। তাতে কাজের উভয় পক্ষই মুনাফা বা ফায়দায় সমানভাবে শরীক থাকে, ক্ষতি হলেও তা দুজনেরই ভাগে পড়ে।
( আরবি******************)
ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন, ফসলের হার ভাগের ভিত্তিতে জমি চাষ করানোই হচ্ছে ইসলামী শরীয়তের মৌলনীতি ও সুবিচার ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পন্থা। আর কেরায়ায় দেয়ার তুলনায় ফসল ভাগের ভিত্তিতে চুক্তি অধিকতর সুবিচার ও ন্যায়পরতা সম্পন্ন। কেননা এ পন্থাতেই উভয় পক্ষ লাভ ও লোকসান উভয়তেই শরীক থাকে। জমি কেরায়ায় দেয়ার ব্যাপারটি ভিন্নতর। তাতে জমি-মালিক কেরায়া তো পেয়ে যায়, কিন্তু কেরায়াদারের ভাগে কখনও ফসল উঠে আর কখনও তাকে তা থেকে বঞ্ছিত থাকতে হয়।
( আরবি******************)
ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম লিখেছেনঃ
যে ধরনের পারস্পরিক চাষাবাদ ইনসাফপূর্ণ, মুসলমানরা তদানুযায়ী রাসূলে করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদুনের আমল থেকেই কাজ করে আসছে। আবূ বকর-উমর- উসমান-আলী (রা)-এর বংশধররাও তাই করেছেন। বড় বড় সাহাবী সাটাকেই জায়েয মনে করতেন। হযরত ইবনে মাসউদ, উবাই ইবনে কা’ব, যায়দ ইবনে সাবিত প্রমূখ সাহাবী (রা) এ মতই পোষণ করতেন। মুহাদ্দিস-ফিকাহবিদ ইমাম আহমেদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক ইবনে বাহওয়াই, ইমাম বুখারী, দাঊদ ইবনে আলী, ইবনে খুজাইমা, আবূ বকর ইবনুল মুনযির, মুহাম্মদ ইবনে নছর মরোজী প্রমুখও এ মতকেই যথার্থ ঘোষণা করেছে। আর মুসলমানদের নামকরা ফিকাহবিদ লাইস ইবনে সা’দ ইবনে আবূ রাইলা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ইবনে ইমাম হাসান প্রমুখও এ মতই প্রকাশ করেছেন।
ইবনুল কাইয়্যেমের সময়ে কৃষিজীবীদের ওপর প্রশাসক ও সেনাবাহিনীর লোকদের পক্ষ থেকে যে জোর-জুলুম চালান হয়েছে, তিনি তার তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ এ প্রশাসক ও সৈন্যবাহিনীর লোকেরা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের দেয়া শরীয়তের বিধান অনুযায়ী চাষীদের সাথে ব্যবহার করত, তাহলে তারা সকলে উপর ও নিচ থেকে দেয়া আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামত লাভ করতে পারত। আসমান ও জমিনের বরকতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হতো। তারা জুলুম ও নির্যাতন করে যা পায়, এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করলে তাও তার চাইতে অনেক বেশি হতো। কিন্তু ওরা মূর্খ, ওরা জালিম। তাই জুলুম ও পাপ ভিন্ন ওদের করার আর কিছুই নেই। ফলে ওরা বরকত ও রিযকের প্রশস্ততা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর তার দরুন তাদের জন্যে পরকালীন আযাবই পুঞ্জীভূত হয়ে থাকল। দুনিয়ার কোন বরকত তাদের ভাগ্যে জুটবে না।
যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল এ পর্যায়ে কি বিধান দিয়েছেন এবং সাহাবিগণই বা কোন্ নীতি মেনে চলেছেন?
উত্তরে বলা যাবে, ঠিক যে পন্থা পারস্পরিক ইনসাফপূর্ণ, যাতে জমি মালিক ও চাষী সুবিচারের এক ও অভিন্ন মানে উত্তীর্ণ হতে পারে, প্রচলিত নিয়মে যেমন হয় তেমন বিশেষ এক পক্ষকে তার ভাগ্য সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেয়ে অপর পক্ষকে অনিশ্চয়তার ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয় না, তা-ই। দুনিয়ায় সাধারণভাবে প্রচলিত রসম-রেওয়াজ ভুইফোঁড় নীতিতে চলছে। তা-ই যত বিপর্যয় এনেছে পৃথিবীতে। জনগণকেও নিক্ষেপ করেছে কঠিন সংকটের মধ্যে। বৃষ্টি পড়া বন্ধ হয়েছে, বরকত উঠে গেছে। প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর অধিকাংশ লোক হারাম খেতে শুরু করেছে। আর হারাম খাদ্যে তাদের দেহে যে গোশত জমেছে, তার জন্যে তো জাহান্নামই উপযুক্ত স্থান।
এই ইনসাফপূর্ণ কৃষি ব্যবস্থাই ছিল মুসলিম জনগণের অনুসৃত নীতি। নবী করীম (সা)-এর যুগেও যেমন, তেমন খুলাফায়ে রাশেদুন ও তৎপরবর্তীকালেও। স্বয়ং নবী করীম (সা) খায়বরবাসীদের সাথে এ নীতির ভিত্তিতেই জমি চাষের চুক্তি করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাদের নির্বাসিত না করা পর্যন্ত তদানুযায়ী কাজ হয়েছে। তাতে কথা ছিল তারই জমি চাষাবাদ করবে নিজেদের খরচ, বীজও তারাই দেবে।
এ কারণে আলিমদের মতে বীজ চাষির দেয়া উচিত হলেও দুজনের যে কোন একজন দিলেও জায়েয হবে। হযরত উমর (রা) এভাবে চুক্তি করেছিলেন যে, তিনি বীজ দিলে অর্ধেক ফসল পাবেন। আর চাষকারী যদি তা দেয়, তবে সেও তাই পাবে অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশি।
পারস্পরিক জমি চাষ পর্যায়ে যত হাদীসের বর্ণনাই পাওয়া যায়, তাতে চাষকারী যে অর্ধেকের কম পাবে, তার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না; বরং তারও বেশি পাওয়ার কথা কোন কোন বর্ণনায় বলা হয়েছে।
এ প্রেক্ষিতে মন বলছে, চাষকারীর অংশ অর্ধেকের কম হওয়া উচিত নয়। নবী করীম (সা) ও খুলাফায়ে রাশেদুন খায়বারের ইয়াহূদীদের সাথে তাই করেছেন। অতএব ফসল বন্টনের সময় মানুষের (চাষকারীর) অংশের তুলনায় পাথরের- জমির- অংশ বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।
পশুপালনে শরীকানা
আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আর একটা কাজের প্রচলন রয়েছে তা হচ্ছে পশু-জন্তু পালনে শরীকী ব্যবস্থা। এক পক্ষ সম্পূর্ণ বা কতক মূলধন দেয় আর অপর পক্ষ দেখা-শোনার দায়িত্ব পালন করে। আর ফল বা মুনাফা দুজনে ভাগ করে নেয়।
এ সম্পর্কে শরীয়তের রায় জানার পূর্বে এ কাজের বিভিন্ন ধরন বিশ্লেষণ করা আবশ্যক।
১. একটি ধরন এই যে, নিছক ব্যবসায়ী উদ্দেশ্যে উভয় পক্ষ একত্রিত হবে। বাছুর মোটা করার উদ্দেশ্যে পালন বা গাভী-মহিষ থেকে দুগ্ধ লাভের উদ্দেশ্যে পালন।
এতে এক পক্ষ মূলধন দেয় আর অপর পক্ষ দেয় শ্রম ও দেখা-শোনার কাজের দায়িত্ব। পশুগুলোর খাদ্য পানীয় দিতে যা ব্যয় হবে তা দুজনই বহন করবে। আর তা বিক্রয় করা হলে যে মূল্য পাওয়া যাবে, তা থেকে খরচ বাদ দেয়া হবে। তার পরে যা মুনাফা দাঁড়াবে তা দুজনে নিজেদের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী বন্টন করে নেবে।
যদি এক পক্ষই সমস্ত খরচ বহনে বাধ্য হয়, আর তার বিনিময়ে সে কিছু না পায়, অথচ মুনাফা দুজনের মধ্যে সমান হারে ভাগ করা হয়, তবে তা ইনসাফপূর্ণ ব্যবসা হতে পারল না।
২. দ্বিতীয় ধরন এই হয় যে, এক পক্ষ মূল্য দেবে আর অপর পক্ষ খরচ ও দেখাশোনার দায়িত্ব বহন করবে। আর জন্তুর দুগ্ধ নিয়ে কিংবা চাষাবাদ বা পানি বহনের কাজে সে পশু ব্যবহার করে উপকৃত হবে।
হ্যাঁ, এরূপ করায় কোন দোষ নেই, যদি জন্তু আকারে বড় হয়, তার থেকে দুধ পাওয়া যায় কিংবা তার দ্বারা কাজ করানো যায়। একথা ঠিক যে, দ্বিতীয় পক্ষ যে খরচ পত্র বহন করে, তার সে সব ব্যয় বহনের তুলনায় দুগ্ধ ইত্যাদি পাওয়াটা সমান মনে হয় না, তাতে ক্ষতির আশংকাটাও থাকে, কিন্তু আমরা ভাল মনে করেই তা জায়েয বলেছি এবং ক্ষতির এ সামান্য আশংকাকে তেমন গুরুত্ব দিই নি। কেননা শরীয়ত এ ধরনের জিনিস সহ্য করে নিতে অসুবিধাবোধ করে না। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
বন্ধকী বাবদ রাখা জন্তুর খরচাদি বহনের বিনিময়ে তাতে সওয়ার হওয়া যায় এবং তার দুগ্ধও পান করা যেতে পারে। সওয়ারী যে করে ও দুগ্ধ যে পান করে খরচাদি তাকেই বহন করতে হবে। (বুখারী)
এ হাদীসে নবী করীম (সা) জন্তুর খাদ্য ইত্যাদি বাবদ খরচের সমান বিনিময় ধরেছেন সেটিকে সওয়ারী রূপে ব্যবহার করা ও সেটির দুগ্ধ পান করাকে।
জন্তুর জন্যে খরচাদি তার ওপর সওয়ার হওয়ার ও তার দুগ্ধ পান করার তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে, কমও হতে পারে। কিন্তু প্রচলনের দৃষ্টিতে যখন বন্ধকীর ক্ষেত্রে এ অবস্থাকে জায়েয মনে করা হয়েছে তখন জন্তু পালনের আলোচ্য শরীকী ব্যবসাকেও প্রয়োজনের দৃষ্টিতে জায়েয মনে করতে কোনরূপ দ্বিধা বোধ হয় না।
উপরিউদ্ধৃত হাদীস থেকে যে প্রতিপাদ্য আমরা বের করেছি তা একান্তভাবে এ গ্রন্থকারের মত। আল্লাহ্ এ মতটিকে নির্ভুল করুন।
কিন্তু ছোট বাছুর জাতীয় জন্তু পালনে- যাতে তার ওপর সওয়ার হওয়াও যায় না, তার দুগ্ধও পান করা যায় না- যদি এক পক্ষ মূল্য দেয় আর অপর পক্ষ খরচাদি বহন করে, তাহলে তা ইসলামের মৌলনীতির দৃষ্টিতে মুবাহ মনে করা যায় না। কেননা যে পক্ষকে খরচাদি বহন করতে হবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর অপর পক্ষ কেবল সুবিধা ও লাভই লাভ পাবে। অতএব তা যেমন ন্যায়ভিত্তিক নয়, তা সুস্পষ্ট অথচ ইসলাম সর্ব ব্যাপারে ইনসাফ ও ন্যায়পরতাকে কার্যকর দেখতে চায়। তবে খরচাদি বহনকারী পক্ষের ফায়দা পাওয়ার সময় হওয়া পর্যন্ত সমস্ত খরচ যদি উভয় পক্ষ পারস্পরিক বন্টনের মাধ্যমে বহন করে, তাহলে আমরা মনে করি, তা জায়েয হবে।
ক্রীড়া ও আনন্দ
ইসলাম বাস্তববাদী জীবন-বিধান। তা মানুষকে অবাস্তব কল্পনা বিলাস ও নানা চিন্তা ভাবনার কুঙঝটিকার পরিবেষ্টনে আবদ্ধ করে রাখতে ইচ্ছুক নয়। বরং এ বাস্তবতার পৃথিবীতে ঘটনা প্রবাহের আবর্তনের মধ্যে সুষ্ঠু রূপে বসবাস করার নীতে ও পদ্ধতিই ইসলাম মানুষকে শিক্ষা দেয়। তা মানুষকে নভোমণ্ডলে বিচরণকারী ফেরেশতা মনে করে কর্মবিধান তৈরী করেনি। খাদ্য-পানীয় গ্রহণকারী ও হাটে-বাজারে বিচরণকারী মানুষ মনে করেই তার জন্য বিধান দেয়া হয়েছে।
এ কারণে মানুষের প্রতিটি কথা ‘যিকির’ হবে, চুপ করে থাকলেও গভীর গবেষণায় নিমজ্জিত হতে হবে, কেবলমাত্র কুরআনের ধ্বনিই তাদের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে, সমস্ত অবসর কাল অতিবাহিত হবে মুসজিদে- এমন কথা কল্পনা করা যায় না, তার আশাও করা যায় না এবং ইসলাম মানুষের ওপর এ কর্তব্য চাপয়েও দেয়নি, এ বাধ্যবাধকতাও আরোপ করেনি। সত্যি কথা হচ্ছে, ইসলাম মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাবগত ভাবধারার ওপর পুরো মাত্রায় লক্ষ্য নিবদ্ধ রেখেছে। আল্লাহ্ তা’আলা মানুষকে সৃষ্টিই করেছেন এভাবে যে, পানাহার যেমন তার প্রকৃতির চাহিদা তেমনি আনন্দ-স্ফূর্তি ও সন্তুষ্ট-উৎফুল্লচিত্ত হয়ে থাকা এবং হাসি-তামাসা-খেলা ইত্যাদিও তার প্রকৃতিগত ভাবধারা হয়ে রয়েছে। এ সত্য কোন ক্রমেই অস্বীকার করা যায় না।
প্রতি মুহূর্তে একই অবস্থা থাকে না
কোন কোন সাহাবী আধ্যাত্মিকতার প্রাধান্য ও তাতে সর্বোচ্চ উন্নতি লাভের ফলে মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, সব সময় ইবাদতের মধ্যে ডুবে থাকাই তাদের কর্তব্য এবং বৈষয়িক স্বার্থ স্বাদ-আনন্দ পরিহার করে চলাই বাঞ্ছনীয়। ক্রীড়া আনন্দ স্ফূর্তিতে তাদের অংশ গ্রহণ করা উচিত নয়। সম্পূর্ণভাবে পরকালমুখী ও পরকালীন ধ্যান-ধারণা ও দায়-দায়িত্ব পরিপূরণে আত্মসমর্পিত হয়ে থাকা একান্তই আবশ্যক।
এ পর্যায়ে মহামান্য সাহাবী হযরত হিনজিলা উসাইদী (রা)-এর একটি কাহিনী উল্লেখ্য। তিনি রাসূলে করীম (সা)-এর বিশেষভাবে নিয়োগকৃত একজন লেখক ছিলেন। তিনি নিজের সম্পর্কে নিজেই বলেছেনঃ
হযরত আবূ বকর (রা) আমার সাথে সাক্ষাত করলেন। জিজ্ঞেস করলেনঃ কি অবস্থা হে হিনজিলা? বললামঃ হিনজিলা তো মুনাফিক হয়ে গেছে। তিনি বললেনঃ সুবহান-আল্লাহ্ বল কি? তখন আমি বললামঃ হ্যা, ব্যাপার তো তা-ই। আমরা যখন রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে বসা থাকি ও তিনি জান্নাত ও দোযখের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, তখন অবস্থা এমন হয়, যেন আমরা তা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু যখন সেই দরবারের বাইরে চলে আসি, তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও কায়কারবারে মন লাগিয়ে দিই; জান্নাত ও দোযখের কথা তখন অনেক খানিই ভুলে যাই। একথা শুনে হযরত আবূ বকরও বললেনঃ আল্লাহর নামে শপথ! আমার অবস্থাও তো ঠিক তদ্রুপ। হিনজিলা বলেনঃ অতঃপর আমরা দুজন- আমি ও আবূ বকর নবী করীমের খেদমতে উপস্থিত হলাম এবং বললামঃ ইয়া রাসূল! হিনজিলা তো মুনাফিক হয়ে গেছে! রাসূলে করীম (সা) বললেনঃ সে কি রকম? আমি বললামঃ ইয়া রাসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, আপনি জান্নাত জাহান্নামের কথা বলেন, তখন আমরা তা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই- এমন অবস্থা হয়। কিন্তু এখান থেকে যখন বের হয়ে যাই, তখন আমরা স্ত্রী-পুত্র-পরিজন ও কায়কারবার নিয়ে এত মশগুল হয়ে যাই যে, অনেক কিছুই আমরা ভুলে যাই।
এসব কথা শুনে নবী করীম (সা) ইরশাদ করলেনঃ ( আরবি******************)
যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর নামে শপথ, তোমরা আমার কাছে এবং যিকিরের মধ্যে যে অবস্থা ও ভাবধারা অনুভব কর, তার মধ্যে যদি তোমরা সব সময়ই থাকতে তাহলে ফেরেশতাগণ এসে তোমাদের বিছানায় ও পথেঘাটেই তোমাদের সাথে করমর্দন করত। কিন্তু হে হিনজিলা! সময়ে সময়ে পার্থক্য রয়েছে। সব সময় এক অবস্থায় থাকা যায় না- এই কথাটি তিনি পরপর তিনবার বললেন। (মুসলিম)
রাসূল তো মানুষ ছিলেন
রাসূলে করীম (সা) মানুষ ছিলেন এবং তাঁর উন্নত জীবন পূর্ণাঙ্গ ও সর্বোন্নত মানের মানব জীবনের জন্যে উজ্জ্বল ভাস্বর আদর্শ এবং অনুসরণীয়। তিনি নিবিড় একাকীত্বে নামায পড়তেন, দীর্ঘক্ষণ বিনয়-ভীতি, কান্নাকাটি করতেন। দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন বলে তাঁর পা দুখানি ফুলে উঠত। তিনি তো পুরোপুরি সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আল্লাহর দিক দিয়ে তাঁর এক বিন্দু ভয় ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মানবীয় জীবনই যাপন করছিলেন। আর সাধারণ মানুষের ন্যায় তিনি ভাল ও সুঘ্রাণ পছন্দ করতেন, হাসতেন, ঠাট্টা-মশকরা-রসিকতা করতেন, তা তাঁর মহান প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। কিন্তু তিনি সত্য বিরোধী কথা কখনই বলতেন না।
নবী করীম (সা) আনন্দ-স্ফূর্তি ও হাসি-খুশী থাকা খুব পছন্দ করতেন, কষ্ট ও দুঃখ অপছন্দ করতেন। তিনি সব খারাবী থেকে আল্লাহর কাছে পানা চাইতেন। বলতেনঃ ( আরবি******************)
হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে পানা চাই দুশ্চিন্তা ও দুঃখানুভূতি থেকে।
তিনি ঠাট্টা-মশকরাও করতেন। এক বৃদ্ধা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললঃ হে রাসূল! আপনি আল্লাহর কাছে দো’আ করুন- তিনি যেন আমাকে বেহেশতে দাখিল করেন। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ হে অমুকের মা, ব্যাপার হচ্ছে এই যে, বুড়া-বুড়ি লোক তো বেহেশতে যাবে না। একথা শুনে বৃদ্ধাটি কেঁপে উঠল ও কাঁদতে শুরু করে দিল। সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না মনে করে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। নবী করীম (সা) বৃদ্ধার এ অবস্থা দেখে ব্যাখ্যা করে বললেন যে, এর অর্থ হচ্ছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এ অবস্থায় বেহেশতে যাবে না। বরং আল্লাহ্ তাদের এক নবতর সৃষ্টিতে ধন্য করবেন এবং যৌবনদীপ্ত অবস্থায় তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে। তিনি তখন এই আয়াতটি পাঠ করে শোনালেনঃ ( আরবি******************)
আমরা তাদের, বিশেষভাবে নতুনতর সৃষ্টিদান করব, তাদের কুমারী বানিয়ে দেব। তারা নিজেদের স্বামীদের প্রেমিকা ও সমবয়স্ক হবে। (সূরা আল-ওয়াকীয়াঃ ৩৫-৩৮)
মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে
নবী করীমের পবিত্র হৃদয় ও মহান চরিত্রবান সাহাবিগণও হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করতেন। খেলা-তামাসায় যোগ দিতেন। তাঁরা নিজেদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন। মনকে আনন্দ দান করতেন, হৃদয়ে প্রশান্তি ও সুখানুভূতির ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন এবং তার মাধ্যমে নবতর উদ্যম ও কর্মক্ষমতা তৎপরতা লাভ করে নতুন ও তাজা হয়ে কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়তেন।
হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
দেহের ন্যায় মনও ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই এই ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরণের জন্যে আশ্চর্য ও বুদ্ধিমানের কথাবার্তা বল।
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি******************)
হৃদয়কে সময় অবসর মতো শান্তি সুখ-আনন্দ দান কর। কেননা হৃদয়ে অস্বস্তি তাকে অন্ধ বানিয়ে দেয়।
হযরত আবুদদারদা (রা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
আমি আমার মনকে বাতিলের সাথে কতকটা হাসি-মশকরা করার সুযোগ দিই, যেন তার দরুন সত্যের দুস্কর পথে চলার ব্যাপারে আমার সাহায্য হয়।
অতএব হাসি মশকরার কথাবার্তা বলায় হৃদয়ে যদি হালকা ভাব অর্জিত হয় তাহলে তাতে কোন দোষ নেই। মুবাহ্ ক্রীয়া খেলা দ্বারা যদি নিজের মন ও সঙ্গী-সাথীদের সান্তনা-প্রশান্তি লাভের ব্যবস্থা করা হয়, তাতেও কোন গুনাহ হবে না, যদি তা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে না পড়ে এবং সর্বক্ষণ কেবল তাতেই মগ্ন থাকার প্রবণতা সৃষ্টি না হয়। কেননা সেরূপ হলে তো সকাল-সন্ধ্যা তাতেই কাটাতে হবে ও তার ফলে দায়িত্বসমূহ পালনে অনীহা দেখা দেবে। এমনকি যেখানে গম্ভীরতা অবলম্বন জরুরী, সেখানেও হাসি-মশকরা শুরু করে দেবে। এ জন্যেই বলা হয়েছেঃ ( আরবি******************)
খাদ্যে যতটা লবণ দেয়ার প্রয়োজন, কথাবার্তায় ঠিক ততটা রসিকতা মিশ্রিত কর।
কেননা লোকদের সম্মান ও ইজ্জত-হুরমতের প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে তাদের কেবল বিদ্রুপ করা মুসলমানের কাজ হতে পারে না। এ জন্যে আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি******************)
হে ঈমানদার লোকেরা, লোকেরা যেন পরস্পরে বিদ্রুপ ও অপমানসূচক আচরণ না করে। কেননা হতে পারে সে তার চেয়েও অনেক ভাল। (সূরা হুজরাতঃ১১)
লোকদের হাসাবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা কথার আশ্রয় লওয়াও সমীচীন বা জায়েয নয়। এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি******************)
ধ্বংস তার, যে লোকদের হাসাবার জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার ধ্বংস, তার জন্যে ধ্বংস। (তিরমিযী)
জায়েয ধরনের খেলা
আনন্দ-স্ফূর্তি ও ক্রীড়ার বহু প্রকার ধরন ও পদ্ধতি এমন রয়েছে যা নবী করীম (সা) মুসলমানদের জন্যে জায়েয ঘোষণা করেছেন। মুসলমানরা এগুলোর সাহায্যে মনের বোঝা হালকা করতে পারে, স্ফূর্তি লাভ করতে পার। এসব ক্রীড়া মানুষকে ইবাদত ও কর্তব্য পালনে- এসব কাজে তৎপরতা সহকারে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এসব শরীর চর্চামূলক ক্রীড়ার সাহায্যে শক্তিবর্ধক ট্রেনিং লাভ করতে পারে। তার দরুন মানুষ জিহাদে অংশ গ্রহণের জন্যেও প্রস্তুত হতে পারে। নিম্নোদ্ধৃত ক্রীড়াসমূহ এ পর্যায়ের খেলাঃ
দৌড় প্রতিযোগিতা
সাহাবায়ে কিরাম দৌড়ে প্রতিযোগিতা করতেন। নবী করীম (সা) তা করার জন্যে তাদের অনুমতি দিয়েছিলেন। হযরত আলী (রা) দৌড় লাগানর কাজে খুব দ্রুত গতিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে।
স্বয়ং নবী করীম (সা) তাঁর মুহতারিমা বেগম হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে তাকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা)-কে শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। হযরত আয়েশা (রা) নিজেই বলেছেনঃ ( আরবি******************)
নবী করীম (সা) দৌড়ে আমার সাথে প্রতিযোগিতা করলেন। তখন আমি আগে বেরিয়ে গেলাম। পরে যখন আমার শরীর ভারী হয়ে গেল তখনও আমার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে আমাকে হারিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ এবার সেবারের বদলা নিলাম। (আহমদ, আবূ দাঊদ)
কুস্তি করা
নবী করীম (সা) রুকানা নামক এক নামকরা কুস্তিগীরের সাথে লড়েছিলেন। তাতে তিনি একাধিকবার তাকে আছাড় দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। (আবূ দাঊদ)
অপর এক বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ নবী করীম (সা) যাকে ধরাশায়ী করে দিয়েছেন তিনি ছিলেন নিরতিশয় বলিষ্ঠ। তিনি পর পর তিনবার তাকে ধুলিসাত করেন। ফিকাহবিদগণ এ সব হাদীসের ভিত্তিতে মত দিয়েছেন যে, দৌড়ে প্রতিযোগিতা করা সম্পূর্ণ জায়েয, পুরুষরা এক সাথে এ দৌড় দিতে পারে। পুরুষ ও মুহাররম মেয়েরা যৌথভাবে কিংবা স্বামী-স্ত্রীও একত্রে প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। দৌড়ে প্রতিযোগিতা ও কুস্তি করা মান-মর্যাদা, গাম্ভীর্য, জ্ঞান-গরিমা ও বয়োবৃদ্ধি কোনটারই পরিপন্থী নয়। কেননা নবী করীম (সা) যখন হযরত আয়েশা (রা)-এর সাথে দৌড়ে প্রতিযোগিতা করেছিলেন, তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশোর্ধ হয়েছিল।
তীর নিক্ষেপ
তীরন্দাজী ও বল্লম মারার খেলাও শরীয়াতসম্মত।
নবী করীম (সা) যখন সাহাবায়ে কিরামকে তীর নিক্ষেপণে মশগুল দেখতে পেতেন তখন তিনি তদের সর্বতোভাবে উৎসাহিত করতেন। বলতেনঃ ( আরবি******************)
তোমরা তীর মারো, আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি।
বস্তুত নবী করীম (সা)-এর দৃষ্টিতে তীর নিক্ষেপণ কেবলমাত্র একটা খেলা ও হাস্য-কৌতুকের ব্যাপারই ছিল না। তা ছিল একটি শক্তি- শক্তি অর্জন ও শক্তি প্রকাশ। আল্লাহ্ তা’আলাই তার নির্দেশ দিয়েছেনঃ
তোমরা শত্রুদের মুকাবিলার জন্য সাধ্যমত শক্তি অর্জন ও সংগ্রহ কর।
এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ
জেনে রাখো, তীরন্দাজী একটা শক্তি। তীর নিক্ষেপণ একটা শক্তি, তীর নিক্ষেপণ একটা শক্তি।
তিনি আরও বলেছেনঃ
তীরন্দাজী শিক্ষা লাভ করা তোমাদের কর্তব্য। কেননা তা তোমাদের জন্যে একটা উত্তম খেলাও।
তবে তিনি পালিত জন্তুকে তার লক্ষ্য বানাতে নিষেধ করেছেন। জাহিলিয়াতের যুগে আরবেরা তাই করত। হযরত ইবনে উমর (রা) কতিপয় লোককে তাই করতে দেখে বলেছিলেনঃ
নবী করীম (সা) কোন জীবিত প্রাণবন্ত জিনিসকে তীর নিক্ষেপণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণকারীর ওপর অভিশাপ করেছেন।
এ অভিশাপ বর্ষণের কারণ হল, এতে যেমন ধন-সম্পদের অপচয় হয়, তেমনি জীবনে কষ্ট দান করা হয়, নিজেকেও ধ্বংস করা হয়। বস্তুত জগতের কোন জীবন সত্তার ওপর কষ্ট দিয়ে নিজেদের আনন্দ-উৎসব অনুষ্ঠান করাটা মানুষের জন্যে কখনো শোভন হতে পারে না।
ঠিক এ কারণে নবী করীম (সা) জন্তুগুলোকে উত্তেজিত করে দিয়ে পারস্পরিক লড়াইয়ে লিপ্ত করতে স্পষ্ট ভাষায় নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)। তদানীন্তন আরবের লোকেরা দুটো ছাগল কিংবা দুটো বলদ (ষাড়)-কে পারস্পরিক লড়াইতে এমনভাবে লিপ্ত করে দিত যে, সে দুটো লড়াই করে করে ধ্বংস ও মৃত্যমুখে পতিত হয়ে যেত। আর তা দেখে তারা উল্লসিত হতো, অট্রহাসিতে ফেটে পড়ত। এ কাজ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ দর্শাতে গিয়ে বিশেষজ্ঞগণ বলেছেনঃ ( আরবি******************)
এ কাজে জন্তুগুলোকে মর্মান্তিকভাবে পীড়া ও কষ্ট দেয়া হয়। ওদের কঠিন দুরবস্থার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। উপরন্তু তা এক নিষ্ফল কর্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।
বল্লম চালানো
তীর নিক্ষেপণের ন্যায় বল্লাম চালানোও এক প্রকারের বৈধ খেলা। নবী করীম (সা) হাবশীদেরকে মসজিদের মধ্যে বল্লম চালানোর খেলা খেলবার অনুমতি দিয়েছিলেন। আর তাঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা) কে অনুমতি দিয়েছিলেন ঘরের মধ্যে থেকে তা দেখতে। তিনি তাদের উৎসাহ দানের জন্যে বলছিলেনঃ হে বনী আরফাদা, মারো, জোরে মারো, তোমার কাছেই রয়েছে তোমার প্রতিপক্ষ।
হযরত উমর (রা) কঠোর মেজাযের লোক ছিলেন বলে এ খেলা তাঁর ভাল লাগেনি। তিনি তাদের নিষেধ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু নবী (সা) তাঁকে বিরত রাখলেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেছেনঃ হাবশীরা নবী করীম (সা) এর সম্মুখেই বল্লম দিয়ে খেলছিল। এ সময় হযরত উমর উপস্থিত হলেন। তিনি এ খেলা থেকে ওদের বিরত রাখার ও নিষেধ করার উদ্দেশ্যে ওদের প্রতি পাথর কুচি নিক্ষেপ করলেন। নবী করীম (সা) বললেনঃ ওদের খেলতে দাও হে উমর।
নবী করীম (সা) তার পবিত্র মসজিদের মধ্যে এ খেলা খেলবার অনুমতি দিয়ে বিরাট উদারাতা ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এর ফলেই মসজিদে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই একত্রিত ও সমন্বিত হয়েছিল। যেন মুসলমানরা যখন খেলা করে, হাস্যরস করে তখন যেন মনে করে যে, এটা নিছক খেলাই নয়। এটা যেমন খেলা- চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম, তেমনি তা শরীর চর্চা ও ব্যায়াম অনুশীলনও বটে! এ হাদীসের আলোকে বিশেষজ্ঞগণ মত দিয়েছেন যেঃ ( আরবি*******************)
মসজিদ হচ্ছে মুসলিম সমাজের যাবতিয় কাজের কেন্দ্রস্থান। কাজেই যে যে কাজে দ্বীন ও দ্বীনদার লোকদের কল্যাণ নিহিত, তা তাতে করা নিঃসন্দেহে জায়েয।
এ প্রেক্ষিতে এ কালের মুসলমানদের ভেবে দেখা উচিত, তাদের মসজিদসমূহকে সে কালে কিভাবে জীবন ও শক্তির উৎস বানান হয়েছিল। আর বর্তমানে তো তা অকর্মাদের আলস্য কেন্দ্র বানিয়ে রাখা হয়েছে। তাতে না জীবনের স্পন্দন পাওয়া যায় , না কোন শক্তি লাভের উপায় আছে তা থেকে। উপরন্তু স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা ও মুয়ামিলাকরণ এবং এ ধরনের মুবাহ খেলা- তামাসার সাহায্যে মন-অন্তরকে উৎফুল্লকরণ পর্যায়ে রাসূলে করীমের পথ-নির্দেশও এ থেকে পাওয়া যায়। নবী করীমের বেগম আয়েশা (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমি দেখছিলাম, রাসূলে করীম (সা) তাঁর চাদর দ্বারা আমাকে আবৃত করছিলেন। আর আমি হাবশীদের দেখছিলাম তারা মসজিদে খেলা করছিল। দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। অতএব তোমরা খেলায় উৎসাহী ছোট বয়সের বালিকাদের খেলায় নিয়োজিত করতে পার। (বুখারী, মুসালিম)
তিনি আরও বলেছেনঃ আমি রাসূলে করীমের সামনে তাঁর ঘরে মেয়েদের সঙ্গে খেলতাম। আমার কতিপয় বান্ধবী ছিল, তারা আমার সাথে খেলত। রাসূলে করীম (সা) ঘরে এলেই ওরা আত্মগোপন করে বসত। তখন নবী করীম (সা) আমার সঙ্গে ওদের নিয়ে তামাসা করতেন। ফলে ওরা আমার সাথে খেলতে সাহস পেত। (বুখারী, মুসলিম)
ঘোড় সাওয়ারী
আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
ঘোড়া, খচ্চর, গাঁধা তোমাদের সওয়ারীর জন্যে বানিয়েছি এরং তা তোমাদের সৌন্দর্য বৃদ্বিকারকও। (সূরা নহলঃ ৮)
রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
ঘোড়াগুলোর ললাট কল্যাণে আবদ্ধ। (বুখারী)
তিনি আরও বলেছেনঃ তীর চালাও, ঘোড়া-সওয়ারী কর।
যে কাজে আল্লাহর যিকির নেই, তা নিতান্তই খেলা এবং নিরর্থক। চারটি কাজ তার ব্যতিক্রম। তা হচ্ছে, দুই লক্ষস্থলের মাঝে দৌড়ানো, ঘোড়া প্রশিক্ষণ, নিজ স্ত্রী-পরিজনের সাথে খেলা করা ও সাঁতার কাটা শেখানো। হযরত উমর (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের সন্তানদের সাঁতার কাটা ও তীর নিক্ষেপণ শিক্ষা দাও। ঘোড়ার পীঠে লস্ফ দিয়ে উঠে শক্ত হয়ে বসতেও তাদের অভ্যস্ত কর। (মুসলিম)
হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ নবী করীম (সা) ঘোড়ার দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। যেটি জিতেছে সেটিকে পুরস্কারও দিয়েছেন।
এ সব হচ্ছে দৌড় প্রতিযোগিতার সর্বাগ্রে চলে যাওয়ার জন্যে রাসূলে করীমের উৎসাহ দান পর্যায়ের কাজকর্ম। তা যেমন খেলা, তেমনি চর্চা এবং ব্যায়ামও।
হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেসা করা হলো, আপনার কি রাসূলে করীমের সময়ে বাজি ধরতেন? বললেন, হ্যা। তিনি নিজে ‘সারহা’ নামক ঘোড়ার ওপর বাজি ধরেছিলেন। সেটি সবার আগে চলে গিয়েছিল এবং তা দেখে তিনি খুবই আনন্দিত-উৎসাহিত হয়েছিলেন। ( আরবি*******************)
জায়েয ধরনের বাজি ধরার পদ্ধতি এই যে, তাতে অংশগ্রহণকারী পক্ষদ্বয়ের তরফ থেকে পুরস্কার ঘোষিত হবে না। তা অন্য কারো তরফ থেকে হবে কিংবা হবে মাত্র একটি পক্ষ থেকে। যদি উভয় পক্ষের তরফ থেকে হয়, বলা হয় যে জিতবে সে পুরস্কার পাবে, তাহলে তা জুয়া হবে। আর জুয়া তো নিষিদ্ধ। যেসব ঘোড়া জুয়া খেলায় ব্যবহৃত হয়, রাসূলে করীম তাকে শয়তানী ঘোড়া বলেছেন। তার মূল্য গ্রহণ, তাকে ঘাস খাওয়ান এবং তার পীঠে সওয়ার হওয়াকে গুনাহ বলেছেন। (আহমদ)
তিনি বলেছেনঃ ঘোড়া তিন ধরনের হয়ে থাকে। আল্লাহর ঘোড়া, মানুষের ঘোড়া, শয়তানের ঘোড়া। যে ঘোড়া আল্লাহ্র পথে জিহাদের কাজে নিয়োজিত, তা আল্লাহ্র ঘোড়া। তাকে ঘাস খাওয়ান- তার পায়খানা পেশাব সবকিছুতেই কল্যাণ নিহিত। আর যে ঘোড়া জুয়া খেলায় বা বাজি ধরায় বা রেস খেলায় ব্যবহৃত, তা শয়তানের ঘোড়া! আর লোকেরা যে সব ঘোড়া বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে লালন-পালন করে, তা মানুষের ঘোড়া। তা দারিদ্র্য বিদূরণের কাজে লাগে।
শিকার করা
বড় উপকারী ও কল্যাণময় খেলা হচ্ছে শিকার করা। ইসলাম এ কাজকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে। বস্তুত এ কাজে যেমন সামগ্রী মেলে, উপার্জন হয়, তেমন তা ব্যায়াম চর্চাও বটে। তা কোন যন্ত্রের যেমন তীর বা বল্লমের সাহায্যে হোক কিংবা শিকারী কুকুর বা পাখি দ্বারা হোক, উভয় ধরনের শিকারই জায়েয। এ কাজের জরুরী শর্ত ও নিয়মাদি আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।
ইসলাম মাত্র দুটি সময়ে শিকার করতে নিষেধ করেছে। এ ছাড়া সব সময়ই তা করা যায়। সে দুটি সময় হচ্ছে, হজ্জ ও উমরার জন্যে বাঁধা ইহরাম অবস্থায়। কেননা এ হচ্ছে পরম শান্তি ও পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তার সময়। এ সময় হত্যাও করা যায় না, রক্তপাতও করা যায় না। যেমন আল্লাহ্ নিজেই বলেছেনঃ
হে ঈমানদার লোকেরা! ইহরাম বাঁধা থাকা অবস্থায় তোমরা শিকার হত্যা করো না। আর তোমরা যতক্ষণ ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ স্থলভাগের শিকারও হারাম করে দেয়া হয়েছে তোমাদের জন্যে।
আর দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে মক্কার হারাম শরীফের মধ্যে থাকাকালে। কেননা আল্লাহ্ তা’আলা হারাম শরীফকে সর্বদিক দিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার প্রাণকেন্দ্র বানিয়েছেন। এখানে প্রত্যেকের জন্যেই শান্তি ও নিরাপত্তা। এমনকি কোন জীবন্ত শিকার তথায় আশ্রয় নিলেও এবং তাকে কোন উড়ন্ত পাখি ধরতে পারলেও তা করা যাবে না। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ
সেখানকার শিকার শিকার করা যাবে না, সেখানকার গাছ কাটা যাবে না, তার কোন ঘাসও উপড়ান যাবে না।
পাশা খেলা
যে খেলায় জুয়া রয়েছে তা সবই এবং তার প্রতিটিই হারাম। আর যে খেলায় কোন আর্থিক লাভ বা লোকসান হয়ে থাকে, তাই জুয়া। কুরআন মাজীদে মদ্য, স্থানে বলিদান ও তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চাওয়া প্রভৃতি হারাম কাজের সঙ্গে মিলিয়ে এই জুয়ার উল্লেখ করেছে।
নবী করীম (সা) বলেছেন, কেউ যদি বলে যে, এস জুয়া খেলি, তবে তাতে যে গুনাহ্ হবে তার জন্যে তার সদকা করা উচিত। কেননা জুয়া খেলার আহবানটাও একটা পাপ এবং সে পাপের কাফফারা দেয়া বাঞ্ছনীয়।
পাশা খেলা এ পর্যায়েরই একটি খেলা। তার সাথে জুয়া শামিল হলে তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। আর কেউ কেউ বলেছেন, মাকরূহ- হারাম নয়। যাঁরা হারাম বলেন, তাঁরা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেছেন হযরত বুরায়াদ (রা) বর্ণিত হাদীস। রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক পাশা ছক্কা খেলা খেলেছে, সে নিজের হস্ত শূকরের রক্ত-মাংসে রঞ্জিত করেছে।
আবূ মূসা বর্ণিত হাদীস হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক পাশা ছক্কা খেলা খেলেছে, সে আল্লাহ্-রাসূলের নাফরমানী করেছে।
এ দুটি হাদীসে স্পষ্ট ভাষায়ই পাশা-ছক্কা খেলা হারাম বলা হয়েছে, তাতে জুয়া থাক, আরি না-ই থাক।
ইমাম শাওকানী লিখেছেনঃ ইবনে মুগফফল ও ইবনুল মুসাইয়্যেবের মতে জুয়া মিশ্রিত না হলে পাশা-ছক্কা খেলায় কোন দোষ নেই। তাঁরা দুজন উপরে উদ্ধৃত হাদীসসমূহকে জুয়া মিশ্রিত পাশা খেলা পর্যায়ের মনে করেছেন।
দাবা খেলা
খুব নামকরা খেলা হচ্ছে দাবা। আরবী ভাষায় বলা হয় শতরঞ্জ। ফিকাহবিদগণ এ খেলা সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। কেউ বলেছেন তা মুবাহ, কেউ বলেছেন মাকরূহ আর কারো মতে তা হারাম।
যাঁরা হারাম বলেছেন, তাঁদের দলিল নবী করীম (সা) থেকে বর্ণিত কতিপয় হাদীস। কিন্তু হাদীস-সনদের সমালোচক ও বিশেষজ্ঞগণ সেসব হাদিসের সত্যতা অস্বীকার করেছে, তাঁরা বলেছেন, এই দাবা খেলা সাহাবীদের জামানাতেই প্রচারিত ও প্রসারিত হয়। তার পূর্বে এই খেলার কোন অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই এপর্যায়ে কোন হাদীসের অস্তিত্ব স্বীকৃত নয়। সবই বাতিল। তাহলে এ ব্যাপারে সাহাবীদের কি মত ছিল? জানা যায়, তাঁদের মত এক রকম ছিল না। ইবনে উমর (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************) ‘দাবা খেলা পাশা-ছক্কা খেলার চাইতেও খারাপ’। হযরত আলী (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************) এই খেলাও এক প্রকার জুয়াই। কোন কোন সাহাবীর মতে তা মাকরূহ মাত্র।
আবার কোন কোন সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে তা মুবাহ, নির্দোষ খেলা। হযরত ইবনে আব্বাস, আবূ হুরায়রা, ইবনে সিরীন, হিশাম ইবনে ওরওয়া, যায়ীদ ইবনুল মুসাইয়্যেব ও যায়ীদ ইবনে জুরাইরা প্রমুখ এ মত প্রকাশ করেছেন।
এ গ্রন্থকারের মতে এ শেষোক্ত মহান বিশেষজ্ঞদের মতই সহীহ। কেননা সত্যি কথা এই যে, এ খেলা হারাম হওয়ার পক্ষে কোন অকাট্র দলিলই পেশ করা যায় নি। তা ছাড়া তাতে যথেষ্ট মানসিক চর্চা ও চিন্তার প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে। এ কারণে এ খেলাকে পাশা ছক্কা থেকে ভিন্নতর মনে করা আবশ্যক। এ করণে তাঁরা বলেছেন যে, পাশা-ছক্কা খেলায় শুধু আনন্দ স্ফূর্তি লাভ হয়। তা-ই তার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু শতরঞ্জ বা দাবা খেলার বিশেষত্ব হচ্ছে, তাতে মেধা ও চিন্তাশক্তির প্রাবল্য বিদ্যমান ও প্রয়োজন। কাজেই তাকে তীরন্দাজীর মত মনে করতে হবে।
এই খেলাকে যাঁরা জায়েয বলেছেন, তারা এ পর্যায়ে তিনটি শর্ত আরোপ করেছেনঃ (১) তার কারণে নামাযে যেন বিরম্ব না হয়। কেননা তাতে নামায সময়মত না পড়তে পারার একটা তীব্র আশংকা রয়েছে। (২) তাতে জুয়া থাকতে পারবে না এবং (৩) খেলোয়াড়রা খেলার সময় নিজেদের মুখকে গালাগাল, কুৎসিত-অশ্লীল কথাবার্তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র রাখবে। এ সব শর্ত লংঘিত হলে কিংবা তার অংশ বিশেষও ভঙ্গ করা হলে সে খেলাও হারাম হয়ে যাবে।
গান ও বাদ্যযন্ত্র
[এখানে সুযোগ্য গ্রন্থকার বাদ্যযন্ত্র সম্পর্কে সেই হাদীস উল্লেখ করে নি যাতে প্রিয় নবী (সা) ইরশাদ করেছেন, বাদ্যযন্ত্র মিটিয়ে ফেলার জন্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। বাদ্যযন্ত্র বলতে ঐ সব যন্ত্রকে বোঝায় যা দ্বারা মানুষের সুপ্ত যৌন আকাংখা জাগরিত হয়। -অনুবাদক]
যে কাজে সাধারণতঃ মানুষের মন আকৃষ্ট হয় ও অন্তর পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ করে এবং কর্ণ কুহরে মধু বর্ষিত হয়, তা হচ্ছে গান বা সঙ্গীত। ইসলামের দৃষ্টিকোণ হচ্ছে, নির্লজ্জতা, কুৎসিত-অশ্লীল ভষা কিংবা পাপ কাজে উৎসাহ উত্তেজনা দানের সংমিশ্রণ না হলে সেই সাথে বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারেও কোন দোষ নেই।
আনন্দ উৎসব ক্ষেত্রে খুশী ও সন্তোষ প্রকাশের জন্যে এ সব জিনিস শুধু জায়েযই নয়, পছন্দনীয়ও বটে। যেমন ঈদ, বিয়ে, হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়ের ফিরে আসা এবং ওয়ালীমা’র আকীকার অনুষ্ঠান ও সন্তান জন্ম হওয়াকালে এ সব ব্যবহার করা যেতে পারে দ্বিধাহীন চিত্তে।
হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, আনসার বংশের এক ব্যক্তির সাথে একটি মেয়ের বিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ হে আয়েশা! ওদের সঙ্গে আনন্দ-স্ফূর্তির ব্যবস্থা কিছু নেই? কেননা আনসাররা তো এগুলো বেশ পছন্দ করে। (বুখারী)
হযরত আয়েশা (রা) তাঁর এক নিকটাত্মীয় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন আনসার বংশের এক ছেলের সাথে। তখন নবী করীম (সা) এসে জিজ্ঞেস করলেন, দুলহিনকে কি পাঠিয়ে দিয়েছ? লোকেরা বলল, জ্বি হ্যাঁ। বললেনঃ তার সাথে একটি গায়িকা মেয়ে পাঠিয়েছ কি? লোকেরা বললঃ জ্বি না। তখন তিনি বললেনঃ
আনসার বংশের লোকেরা খুব গান পছন্দ করে। এ কারণে দুলহিনের সাথে তোমরা যদি এমন একটি মেয়ে পাঠাতে যে গাইতঃ আমরা তোমাদের কাছে এসেছি, আমরা তোমাদের বাড়ি এসেছি, আল্লাহ আমাদেরও বাঁচিয়ে রাখুন, তোমাদেরও, তাহলে খুবই ভাল হতো। (ইবনে মাজা)
হযরত আয়েশা (রা) বলেনঃ তাঁর কাছে উপস্থিত থেকে দুটি মেয়ে ঈদুল-আযাহা’র দিনে গান গাইতেছিল ও বাদ্য বাজাচ্ছিল। নবী করীম (সা) কাপড়মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। এ সময় হযরত আবূ বকর (রা) তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি এ দেখে মেয়ে দুটিকে ধমকালেন। নবী করীম (সা) তা শুনে মুখের কাপড় খুলে বললেনঃ হে আবূ বকর, ওদের করতে দাও। এখন তো ঈদের উৎসব সময়। (বুখারী, মুসলিম)
ইমাম গাজালী তাঁর ‘ইহয়া-উল-উলুম’ গ্রন্থে দুটি মেয়ের গান গাওয়া সংক্রান্ত বহু কয়টি হাদীসের উল্লেখ করেছেন। মসজিদে নববীতে হাবশীদের খেলার ও নবী করীম (সা) কর্তৃক তাদের উৎসাহ দানেরও উল্লেখ করেছেন। নবী করীম (সা) এ সময় হযরত আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলেনঃ তুমি কি এ খেলা দেখতে চাও? তার পরে তিনি তাঁর সঙ্গে লেগে থেকে তাকে দেখালেন এবং তাঁর এ সমস্ত হাদীসই বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, গান ও খেলা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম নয়। এ ব্যাপারে শরীয়তের যে রুখছত আছে, তারও প্রমাণ বিদ্যমান।
প্রথমত, খেলার ব্যাপারটি বিবেচ্য। হাবশীদের নৃত্য ও ক্রীড়ামোদিতা সর্বজনবিদিত। দ্বিতীয়ত, তা মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হওয়া এবং তৃতীয়ত, রাসূলে করীম (সা) কর্তৃক তাদের বাহবা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা দান প্রভৃতিই এসবের মুবাহ হওয়ার প্রমাণ। আর এ সব যখন রয়েছে, তখন তাকে কি করে হারাম বলা যেতে পারে?
চতুর্থ ব্যাপার হচ্ছে, হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর তাদের নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু নবী করীম (সা) উভয়কে বারণ করে তা চলতে দিলেন এবং কারণ দর্শালেন এই বলে যে, এটা ঈদ উৎসব। এইটা আনন্দস্ফূর্তি করার সময়। এ গুলোই হচ্ছে আনন্দ-স্ফূর্তি লাভের সামগ্রী।
পঞ্চম কথা, তা দেখার জন্যে নবী করীম (সা)-এর দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকা এবং হযরত আয়েশার সাথে আনুকূল্য করতে গিয়ে তাঁর নিজেরও শোনা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোক ও বাচ্চাদের খেলা দেখিয়ে তাদের আনন্দ দান করা উত্তম চরিত্রসম্পন্ন কাজ। কৃচ্ছ্রতা ও পরহেজগারীর শুস্কতা কঠোরতা গ্রহণ করে তা থেকে বিরত থাকা বা তা করতে না দেয়া- অন্যদের তা থেকে বিরত রাথার তুলনায় এ কাজ অনেক ভাল।
ষষ্ঠ হচ্ছে, তিনি শুরুতেই হযরত আয়েশাকে বললেনঃ
তুমি কি দেখতে চাও?
আর সপ্তম হচ্ছে, দুটো মেয়েকে গান গাইতে ও বাদ্য বাজাতে অনুমতি দান।
বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ীন গন শুনেছেন এবং তাতে কোন দোষ মনে করেন নি, একথা নির্ভরযোগ্য সূত্রে উদ্ধৃত হয়েছে। এ পর্যায়ে বর্ণিত নেষেধমূলক হাদীসগুলো সমালোচনার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। তার কোন একটিও এমন নয়, যার সম্পর্কে হাদীস বিজ্ঞানী ও ফিকাহবিদগণ আপত্তি তোলেন নি। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী বলেছেনঃ গান হারাম হওয়ার পর্যায়ে কোন একটি হাদীসও সহীহ্ নয়। ইবনে হাজম বলেছেনঃ এ পর্যায়ের সব বর্ণনাই বাতিল ও মনগড়া রচিত।
গান এ বাদ্যযন্ত্র সাধারণত উচ্চ পর্যায়ের বিলাস-ব্যসন ও শান-শওকতপূর্ণ অনুষ্ঠানাদিতে, মদ্যপানের আসরে ও রাত্রি জাগরণের মজলিসসমূহে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ করণে বহু আলিম তাকে হারাম বা মাকরূহ বলেছেন। আর অন্যান্য আলিমগণ মনে করেন, কুরআনের ভষায় এ গান-বাজনা সেই ‘লাহউল হাদীস’ যার কথা এ আয়াতে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
লোকদের মধ্যে এমনও আছে, যারা ‘লাহউল-হাদীস’ ক্রয় করে, যেন তারা লোকদের আল্লাহর পথ থেকে কোনরূপ ইলম ছাড়াই ভ্রষ্ট করে দিতে পারে। আর যেন তারা আল্লাহর পথকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে। এ লোকদের জন্যে খুবই অপমানকর আযাব রয়েছে।
ইবনে হাজম বলেছেন, যে ব্যক্তি ‘লাহউল-হাদীস’ গ্রহণ করে এ আয়াতটি তার পরিচিতিস্বরূপ বলেছে যে, সে ব্যক্তি নিঃসন্দেহে কাফির। কেননা সে আল্লাহর পথকে ঠাট্টাও বিদ্রুপ করে। সে যদি কোন বই ক্রয় করে লোকদের ভ্রষ্ট করে ও আল্লহর পথকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করে, তাহলে সে নিঃসন্দেহে কাফির। আল্লাহ্ তা’আলা উপরিউক্ত আয়াতে তার দোষের কথা বলেছেন। সে লোকের দোষ বলেন নি, নিন্দা করেন নি, যে লোক ‘লাহউল হাদীস’ কে লোকদের ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে নয়, কেবলমাএ খেলা তামাসা-স্ফূর্তি করার উদ্দেশ্যে খরিদ করে এবং তার দ্বারা স্বভাব মেজাজের সুষ্টতা ও সন্তুষ্টি বিধান করে।
যাঁরা বলেন যে, গান ঠিক নয়, তা অবশ্যই ভ্রষ্টতা, তাদের প্রতিবাদ করে ইবনে হাজম লিখেছেন, রাসূলে করীম (সা) বলেছেন, কার্যাবলীর ভাল-মন্দ নির্ভর করে নিয়তের ওপর। কাজেই যে লোক এ নিয়তে গান শুনল যে, তার দ্বারা গুনাহের কাজে উৎসাহ পাওয়া যাবে, তাহলে সে ফাসিক। পক্ষান্তরে যে লোক স্বভাব-মেজাজের সুষ্ঠতা লাভের উদ্দেশ্যে শুনল, আল্লাহনুগত্যমূলক কাজে শক্তি সাহস পাওয়ার এবং ভাল ও সৎকাজে আগ্রহ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে শুনল, তার এ কাজ নিশ্চয়ই অন্যায় বা বাতিল নয়। আর যে ব্যক্তি না আল্লাহনুগত্যের নিয়তে শুনল, না নাফরমানী নিয়তে, তার এ কাজ নিষ্ফল কাজের পর্যায়ে গণ্য। তা আল্লহ্ মাফ করে দেবেন। যেমন কারো বাগানে, খোলা মাঠে বা নদী-তীরে পায়চারী করার জন্যে বের হওয়া শুধু প্রাতঃ ভ্রমণ ও সন্ধ্যাকালীন বিহার করার উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ির দরজায় বসে থাকে আমোদ-প্রমোদ ও শিথিলতা সম্পাদনের জন্যে অথবা নিজের কাপড় হড়িৎ, সবুজ বা অন্য কোন বর্ণে রঞ্জিত করা ইত্যাদি।
তবে গানের ব্যাপারে কয়েকটি জিনিসের দিকে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবেঃ
১. গানের কথা বা বিষয় বস্তু ইসলামী শিক্ষা ও ভাবধারা পরিপন্থী হতে পারবে না। মদ্যের গুণ বর্ণনাকারী বা মদ্যপানে আমন্ত্রণকারী গান অবশ্যই হারাম। কেননা তা থেকে হারাম কাজ করার প্রেরণা পাওয়া যায়।
২. অনেক সময় দেখা যায়, গান হয়ত ইসলামী ভাবধারা পরিপন্থী নয়, কিন্তু গায়কের সঙ্গীত-ঝংকার ও পদ্ধতি হালালের সীমা ডিঙ্গিয়ে হারামের পর্যায়ে পৌঁছে দেয়। যেমন খুব হাস্য-লাস্যময়ী ও লজ্জাষ্কর অঙ্গভঙ্গি সহকারে, হেলে দুলে, নির্লজ্জতার ধরন অনুসরণ এবং হৃদয়াবেগে তুফানের উত্তেজনা ও আলোড়নের সৃষ্টি করে, লালসা উদ্দীপক ও দুর্ঘটনা সঙ্ঘটকরূপে তা উপস্থাপন করে।
৩. দ্বীন ইসলাম সর্বব্যাপারেই বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণের বিরোধী। ইবাদতের ব্যাপারেও এই কথা। লাহউন-এর ব্যাপারেও কোনরূপ সীমালঙ্ঘন বরদাশত যোগ্য নয়া। তাতে খুব বেশি সময় ব্যয় করা কখনই উচিত নয় অথচ সময়ই হচ্ছে জীবনের মূলধন।
সন্দেহ নেই, বৈধ কাজে সীমালংঘন ও বাড়াবাড়ি করা হলে প্রকৃত কর্তব্য সম্পাদনের ত্রুটি থাকা খুবই স্বাভাবিক। এ কারণে যথার্থই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
বাড়াবাড়িকে আমি এমন অবস্থায় দেখেছি যে, তার সম্মুখে প্রকৃত সত্য মার খেয়ে যাচ্ছে, বিনষ্ট হচ্ছে।
৪. কোন কোন গান শুনে ব্যক্তি নিজের কাছ থেকেই ফতোয়া পেয়ে যেতে পারে, সে গান শুনে হৃদয়াবেগ যদি উত্তেজিত হয়ে উঠে থাকে এবং তাতে বিপদ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে- আধ্যাত্মিকতার পরিবর্তে পাশবিকতার প্রাধান্য হতে দেখা যায়, তাহলে তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত এবং যে দুয়ার থেকে বিপদের হাওয়া আসে, তা বন্ধ করে দেয়া কাঞ্ছনীয়।
৫. এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, যে গানের সাথে মদ্যপান, ফষ্টিনষ্টি ও চরিত্রহীনতার মতো কোন হারাম জিনিসের সংমিশ্রণ হয়, সে গান হারাম। এ বিষয়ে নবী করীম (সা) কঠিন আযাবের দুঃসংবাদ শুনিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদ্যপান করবে এবং তার আসল নামের পরিবর্তে নতুন ও ভিন্নতর নাম রেখে দেবে। তাদের শীর্ষদেশে বাদ্য বাজানো হবে, গায়িকারা গান গাইবে। আল্লাহ্ জমিনে তাদের ধ্বসে দেবেন এবং ওদের কতিপয়কে বানর ও শূকর বানিয়ে দেবেন। (ইবনে মাজাহ)
এই কথানুযায়ী বিকৃতিটা আকার-আকৃতিতে আসা জরুরী নয়। এ বিকৃতি মন-মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েও হতে পারে অর্থাৎ মানব দেহের বানরের আত্মা ও মানসিকতা এবং শূকরের রূহ বিরাজ করবে। অন্য কথায় আকৃতিতে মানুষ কিন্তু প্রকৃতিতে বানর ও শূকর। [ মনে রাখতে হবে গ্রন্থকার এখানে গান মুবাহ হওয়ার পক্ষে যা লিখেছেন তার জন্যে এমন সব শর্তের উল্লেখ করেছেন, যা পালন করা খুবই দুষ্কর। অথচ আমাদের দেশে ও সমাজে সাধারণত যে সব গান শোনা বা শোনানো হয়, যে সব ফিল্মের গান প্রচার করা হয় তা উক্ত শর্তে উত্তীর্ণ হতে পারে না। কাজেই এগুলো জায়েয হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কেননা এগুলো হচ্ছে নির্লজ্জতা ও যৌনতা প্রচার-প্রসারের বড় মাধ্যম। নৈতিকতার জন্যে তা বড়ই মারাত্মক। গায়ক, গায়িকারা গান গেয়ে নারী-পুরুষদের মুগ্ধ বিমোহিত করে। অথচ ইসলাম নৈতিক পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতার ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। কোন নারীর পরপুরুষের সাথে অথবা পুরুষের পরনারীর মধুমিশ্রিত মোলায়েম কন্ঠে কথা বলাও জায়েয রাখা হয়নি। কুরআন মজীদে তা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে। ভিন পুরুষ মেয়েলোকের মধুর কন্ঠস্বর স্বাদ গ্রহণকে ইসলামে ব্যভিচার বলে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব এসব গান যে হারাম তাতে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না। তবে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা সৃষ্টিকারী ও জিহাদী তেজোবীর্য উদ্বোধক গানের মুবাহ হওয়াও সর্বজনস্বীকৃত।-অনুবাদক ]
জুয়া-সুরা-সঙ্গী
ইসলামে বহু কয় প্রকারের খেলা ও আনন্দ স্ফূর্তির অনুষ্ঠানকে জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে যে সব খেলার সাথে জুয়া মিশ্রিত, যে সব খেলায় আর্থিক লাভ-লোকসানের ব্যবস্থা অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে শামিল, তা সবই হারাম ঘোষিত হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূলে করীম (সা)-এর সেই কথাটি স্মরণীয়, যাতে তিনি বলেনঃ কেউ যদি বলে যে, আস, তোমার সাথে জুয়া খেলি, তাহলে তার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কাফফারা স্বরূপ সাদকা দেয়া কর্তব্য।
অতএব জুয়াকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসেবে যেমন গ্রহণ করা মুসলমানের জন্য জায়েয নয়, তেমনি তা খেলা, মনের সান্তনা-পরিতৃপ্তি ও অবসর বিনোদনের উপায়রূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে না।
জুয়া খেলার হারাম হওয়ার পেছনে অতীব অকাট্য যুক্তি ও উচ্চতর লক্ষ্য নিহিত।
১.মুসলমানের পক্ষে অর্থোপার্জনে আল্লাহর বেঁধে দেয়া নিয়ম ও পথ অনুসরণ করা একান্ত কর্তব্য। কার্যকারণের মাধ্যমে ফল লাভ করতে চাওয়া উচিত। ঘরে তার দরজা দিয়েই প্রবেশ করতে হবে, অবলম্বিত কারণ বা কাজের ফল চাইতে হবে – এটাই ইসলামের লক্ষ্য।
জুয়া-লটারীও মানুষের মধ্যে ভাগ্য ও ভিত্তিহীন আশা-আকাংখার ওপর নির্ভরতা গ্রহণের প্রবণতা জাগায়। আল্লাহ্ অর্থোপার্জনের জন্যে যেসব চেষ্টা-প্রচেষ্টা, শ্রম ও
কার্যকারণ অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ও আদেশ করেছেন, জুয়া তা গ্রহণের জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না।
২. ইসলাম মুসলমানের জন্যে অপর লোকের মাল হারাম করে দিয়েছে, অতএব তার কাছ থেকে তা নেয়া যেতে পারে কেবলমাত্র শরীয়ত-সম্মত বিনিময় মাধ্যমে অথবা সে নিজের খুশিতে যদি দান করে বা হেবা উপহার দেয় তবেই তা নেয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্য যে কোন উপায়ে তা নেয়া সম্পূর্ণ হারাম। এ দৃষ্টিতেই বলা যায়, জুয়া হচ্ছে পরের ধন অপহরণের বাতিল ও হারাম পদ্ধতি।
৩. জুয়া খেলা খোদ জুয়াড়ী ও খিলোয়াড়দের মধ্যে গভীর শত্রুতা ও হিংসা-প্রতিহিংসার সৃষ্টি করে দেয় অতি স্বাভাবিকভাবেই এবং এতে বিস্ময়ের কিছু নিই। মুখের কুথায় ও বাহ্যত মনে হবে তারা পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু আসলে তাদের মধ্যে জয়ী-বিজয়ীর দ্বন্দ্ব ও হিংসা-প্রতিহিংসার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে প্রতি মুহুর্তে। আর বিজিত চুপ হয়ে থাকলেও ক্রোধ, আক্রোশ ও ব্যর্থতার প্রতিহিংসায় সে জ্বলতেই থাকে। কেননা সে বিজিত এবং তার সব কিছুই সে খুইয়েছে। আর যদি সে ঝগড়া ও বাকবিতণ্ডা করতে শরু করে, তাহলে তার অন্তরে সেই চাপা ক্ষোভ তাকে প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে তোলে।
৪. খেলায় বাজি হেরে গেলে বিজিত ব্যক্তি আবার খেলতে শুরু করে। তখন সে আশা করতে থাকে যে, সে যা হারিয়েছে তা তো ফেরত পাবেই। সে সেই ধ্যানে মশগুল হয়। অপরদিকে বিজয়ী ব্যক্তির জিহ্বায় লোভ লেগে যায়, মুখে পানি টসটস করতে থাকে । সেজন্যে সে বারবার খেলতে বাধ্য হয়। আরও বেশি বেশি অর্থ লুণ্ঠনের লোভ তাকে অন্ধ ও অপরিণামদর্শী বানিয়ে দেয়।
খেলার ধারাবাহিকতা এ রূপেই অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। জয়ী বা বিজিত কেউ কাউকে ছাড়তে প্রস্তুত হয় না।
৫. এ কারণে জুয়া খেলার নেশা যেমন ব্যক্তির জন্যে বিপদ ডেকে আনে, তেমনি সমাজেও কঠিন বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে। এ নেশা মানুষের শুধু ধন-সম্পদই হরণ করে না, তার জীবনটাও বরবাদ করে দেয়।
এই খেলা খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ অকর্মন্য বানিয়ে দেয়। তারা জীবনে অনেক কিছুই গ্রহণ করে কিন্তু জীবনকে দেয় না কিছুই। তারা ভোগ করে উৎপাদন করে না। জুয়াড়ী জুয়া খেলায় এতই মত্ত হয়ে যায় যে, তার নিজস্ব দায়িত্ব কর্তব্যের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যায়। বান্দার প্রতি আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা নিজের পরিবার, সমাজ ও জনগণের কথা তার স্মরণ আসা অসম্ভব থেকে যায়। এ ধরনের লোক নিজের স্বার্থের বিনিময়ে তার নিজের দ্বীন ও ধর্ম, ইজ্জত-হুরমাত ও দেশকে বিক্রয় করে দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। কেননা জয়ার আকর্ষণ এতই তীব্র যে, তর সম্মুখে জুয়া খেলার প্রতি প্রেম ও আসক্তি এত অধিক ও তীব্র হয় যে, সে সব ব্যাপারে ও সব ক্ষেত্রে জুয়া খেলতে শুরু করে দেয়। এমনকি সে এক অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত উপার্জনের আশায় পড়ে তার নিজের ইজ্জত ও মর্যাদা এবং তর নিজের ও গোটা জাতির আকীদা-বিশ্বাসের সঙ্গেও সে জুয়া খেলতে শুরু করে দেবে, এটাই স্বভাবিক পরিণতি।
কুরআন মজীদ তার একটি আয়াত ও আদেশের মধ্যে মদ্য ও জুয়াকে একত্রিত করে ও একই ভাবে হারাম ঘোষণা করে কতো যে উচুমানের বাস্তবদর্শিতার প্রমাণ উপস্থাপিত করেছে, তা বিশ্লেষণ করার অপেক্ষা রাখে না। কেননা এ দুটির ক্ষতি ও মারাত্মক অপকারিতা সমানভাবে প্রবর্তিত হয় ব্যাক্তি, পরিবার, দেশ ও চরিত্র সবকিছুর ওপর। জুয়ার নেশা মনের নেশার মতোই সর্বাত্মক ও মারাত্মক। উপরন্তু এর একটি যেখানে তথায় অপরটির উপস্থিতি অবধারিত।
কুরআন বলেছে, এ দুটি শয়তানের কাজ এবং কুরআন এ দুটোকে ‘স্থান বলিদান’ ও ‘তীর দিয়ে ভাগ্য জানা’- এ দুটি কাজের সঙ্গে একত্রে উল্লেখ করে এ সবগুলো অত্যন্ত বড় বড় পাপ প্রতিষ্ঠান বলে পরিহার ও বর্জন করে চলার নের্দেশ দিয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআনের আয়াতটি হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! মদ্য, জুয়া, বলিদানের স্থান ও পাশা-ছক্কা- এসব অপবিত্র মলিনতা পংকিল শয়তানী কাজ। এগুলো পরিহার কর, যেন তোমরা কল্যাণ লাভ করতে পার। শয়তান তো শুধু এই চায় যে, মদ্য ও জুয়ায় তোমাদের মগ্ন ও নিমজ্জিত করে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি করে দেবে এবং তোমাদের আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। এমতাবস্থায় তোমরা এসব কাজ থেকে বিরত থাকবে কি?
লটারীও এক প্রকার জুয়া
লটারীও এক প্রকারের জুয়া! তাকে সাধারণ জিনিস মনে করা এবং জনকল্যানমূলক প্রতিষ্ঠান ও মানবীয় স্বার্থের নামে তাকে জায়েয মনে করা কোনক্রমেই সহীহ কাজ হতে পারে না। যাঁরা এ ধরনের কাজের জন্যে লটারীকে জায়েয মনে করেন, তাঁরা হারাম নৃত্য ও হারাম শিল্প ইত্যাদির দ্বারা এসব উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করতেও পিছপা হন না। কিন্তু তা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমরা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাইঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ তা’আলা পবিত্র পাক। তিনি পবিত্র জিনিসই কবুল করেন। (হাদীস)
এ লোকেরা মনে করে, জনগণের মধ্যে মানবীয় সহানুভূতি ও কল্যাণমূলক কাজের কোন ইচ্ছা বা প্রবণতা নেই। নেক কাজের কোন তাৎপর্যই তারা বুঝে না। কর্তব্য বোধ বলতেও তাদের কেছুই অবশিষ্ট নেই । আছে শুধু পাশবিক কামনা-বাসনা-লালসা। এ করণে জুয়া ও নিষিদ্ধ ধরনের খেলা ইত্যাদির তামাসাকে উপায় না বানিয়ে কোন কাজই করা যাবে না। কিন্তু ইসলাম মুসলমান সমাজ সম্পর্কে এই মনোভাব ও দৃষ্টিকোণ সমর্থন করে না এবং কোন নেক কাজের জন্য এ সব উপায় অবলম্বনের অনুমতি দেয় না। নেক ও পবিত্র উদ্দেশ্যের (Noble cause) জন্যে পবিত্র পন্থা ও উপায় অবলম্বনের জন্যে ইসলামের তাগিদ রয়েছে। আর সে উপায় হচ্ছে নেক কাজের আহ্বান, মানবীয় পবিত্র ভাবধারা জাগ্রত করা এবং আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানের ভিত্তিতে কল্যাণময় কাজের আমন্ত্রণ।
সিনেমা দেখা
এ কালের সিনেমা-থিয়েটার সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিকোণ কি, সিনেমা থিয়েটারে প্রবেশ করা ও দেখা মুসলমানদের জন্যে জায়েয কিনা, তা অনেকেই জানতে চান।
সিনেমা-থিয়েটার ও এ ধরনের অন্যান্য জিনিস যে চিও-বিনোদনের বড় মাধ্যম, তা অস্বীকার করা যায় না। সেই সাথে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে, এসব আধুনিক মাধ্যমকে ভাল ও মন্দ উভয় ধরনের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ইসলামের দৃষ্টিকোণে বলা যায়, সিনেমা বা ফিল্মে মূলত ও স্বতঃই কোন দোষ বা খারাপী নেই। তা কি কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা দিয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন করতে চাওয়া হচ্ছে, সেটাই আসল প্রশ্ন। এ কারণে এই গ্রন্থকারের মতে সিনেমা বা ফিল্ম ভাল ও উত্তম জিনিস। নিম্নোদ্ধৃত শর্তসমূহ সহকারে কাজে লাগালে তা খুবই কল্যাণকর হতে পারে।
প্রথমতঃ যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে তার দ্বারা প্রতিবিম্বিত ও প্রতিফলিত করা হয় তা যেন নির্লজ্জতা-নগ্নতা-অশ্লীলতা ও ফিসক-ফুজুরী থেকে সম্পর্ণ মুক্ত থাকে। সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও যেন ইসলামী আকীদা বিশ্বাস, শরীয়ত ও তার নিয়ম-কানুনের পরিপন্থী না হয়। উপস্থাপিত কাহিনী যদি দর্শকদের মধ্যে হীন যৌন আবেগ জাগরণকারী, গুনাহের কাজে প্রবণতা সৃষ্টিকারী, অপরাধমূলক কাজে উদ্বুদ্ধকারী কংবা ভুল চিন্তা-বিশ্বাস প্রচলনকারী হয়, তাহলে এ ধরনের ফিল্ম অবশ্যই হারাম। তা দেখা কোন মুসলমানের জন্যেই হালাল বা জায়েয নয় কিংবা তা দেখার উৎসাহও দেয়া যেতে পারে না।
[ আমাদের সব দেশে যে সিনেমা প্রদর্শিত হয় তাতে এসব ভুল ও মারাত্মক উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত কোন ফিল্ম হয় বলে মনে করা যায় না। সাধারণত যুবক-যুবতীদের পেম ও নারী নিয়ে দ্বন্দ্ব-এ সবই ফিল্মের আসল প্রতিপাদ্য। পুরুষ নারীদের রূপ ও যৌবন প্রদর্শনই এগুলোর প্রধান উপজীব্য, চাকচিক্য ও আকর্ষণ। সেই সাথে থাকে চিত্তহারী নৃত্য ও সঙ্গিত। সিনেমার প্রেমভরা লজ্জা-শরম বিধ্বংসী ও চরিত্র হানিকর কথোপকথন ও নৈতিক বিপর্যয়ের মূলে এ কালের এ ছবি-সিনেমার অবদান অনেক বেশি। কাজেই তা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। তবে কোন ফিল্ম যদি বাস্তবিকই এসব কদর্যতা মুক্ত ও কল্যাণময় ভাবধারা সম্পন্ন হয়, তবে তাতে কোন আপত্তি থাকর কথা নয়। -অনুবাদক ]
দ্বিতীয়তঃ কোনরূপ দীনী ও বৈষয়িক দায়িত্ব পালনের প্রতি যেন উপেক্ষা প্রদর্শিত না হয়। বিশেষ করে পাঁচ ওয়াক্ত নমায- যা মুসলিম মাত্রের ওপরই ফরয- আদায় করতে কোন বিঘ্ন দেখা না দেয়। ছবি দেখার কারণে নামায বিশেষ করে মাগরিবের নামায যেন বিনষ্ট না হয়। তাহলে তা দেখা কিছুতেই জায়েয হবে না। তাহলে তা কুরআনের এ আয়াতের মধ্যে পড়বেঃ ( আরবি*******************)
ধ্বংস সেসব নামাযীর জন্যে যারা নিজেদের নামাযের ব্যাপারে গাফিল বা উপেক্ষা প্রদর্শনকারী। (সূরা মাঊন)
এ আয়াতের ( আরবি*******************) শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, নামায সময়মত না পড়লেই তার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়। আর পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে মদ ও জুয়া হারাম হওয়ার অন্যতম কারণ স্বরূপ বলা পয়েছে যে, এ দুটো কাজ আল্লাহর যিকির ও নামায ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে, সে দিকে মনোযোগী হতে দেয় না।
তৃতীয়ত সিনেমা দর্শকদের কর্তব্য ভিন্ ও গায়র মুহাররম নারী-পুরুষদের সাথে সর্বপ্রকার সংমিশ্রণ বা ঢলাঢলি- ঢলাঢলি পরিহার করে চলা, এ ধরনের স্থান বা অবস্থা এড়িয়ে চলা। কেননা তাতে মানুষের নৈতিক বিপদ ঘটতে পারে, সেজন্যে লোকদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে বিশেষত এ কারণে যে, সিনেমা সাধারণত অন্ধকারেই দেখা হয়। পূর্বে এ হাদীসটি এক স্থানে উদ্ধৃত হয়ে থাকলেও এখানেও তা স্মরণীয়ঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কারো মস্তকে সুঁচ বিদ্ধ হওয়াও কোন অ-হালাল নারীর স্পর্শ হওয়ার তুলনায় অনেক উত্তম। (বায়হাকী, তিবরানী)
সামাজিক সম্পর্ক
ইসলাম সমাজের ব্যক্তিদের পারস্পরিক সম্পর্ককে দুটো ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে।
একটি হচ্ছে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। এ সম্পর্ক বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ ও অবিচ্ছিন্ন বন্ধনের কাজ করে। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অধিকার ও মান-মর্যাদা সংবরক্ষণ। প্রত্যেক ব্যক্তির রক্ত, মান-সম্মান ও ধন-মালের নিরাপত্তা ও সম্মানার্হতা। যেসব কথা ব্যবহার-আচরণ বা কাজ এই ভিত্তিদ্বয়কে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত করে, খারাপভাবে প্রভাবিত করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। এ ক্ষতি বৈষয়িক দৃষ্টিতে হোক বা সাংস্কৃতিক দৃষ্টিতে, তাতে কোন পার্থক্য হয় না। তা যে ধরনের যতটা মাত্রারই হোক-না-কেন, সেই দৃষ্টিতে ততটা মাত্রায়ই তা হারাম হবে। নিম্নোদ্বৃত আয়াতে সেসব হারাম জিনিসের উল্লেখ করা হয়েছে, যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও মানবীয় মান-মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকরঃ ( আরবি*******************)
মুমিন পরস্পরের ভাই। অতএব আপন ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা করিয়ে দাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, যেন তোমাদের প্রতি দয়া করা যায়। হে ঈমানদার লোকেরা! না কোন পুরুষ অপর পুরুষদের অপমান সুচক ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে,- কেননা, তারাও তো তার তুলনায় ভাল হতে পারে! তোমরা পরস্পরকে কষ্ট বা দুঃখ দেবে না, পরস্পর খারাপ উপাধিতে ডাকবে না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসিকী অত্যন্ত নিকৃষ্ট পর্যায়ের নাম। আর যারা তাওবা করে বিরত হবে না, তারাই জালিম।
হে ঈমানদার লোকেরা! অনেক ধরনের ভিত্তিহীন ধারণা থেকে দূরে থাক। কোন কোন ভিত্তিহীন ধারণা সুস্পষ্ট গুনাহ, আর তোমরা লোকদের দোষত্রুটি খোঁজ করে বেড়িও না, কেউ যেন কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ প্রচার না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইর গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? তোমরা তো তা ঘৃণাই কর। আর আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চিত জানিও আল্লাহ্ বড়ই তাওবা কবুলকারী দয়াশীল। (সূরা হুজরাতঃ ১০-১২)
প্রথম আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন, মুমিনরা পরস্পর ভাই। এতে মানবীয় ভ্রাতৃত্বের সাথে সাথে দ্বীনী ভ্রাতৃত্বও বর্তমান। দুটো একসাথে একত্রিত ও সমম্বিত। এ ভাতৃত্বের দাবি হচ্ছে, তারা পরস্পর নিঃসম্পর্ক বা অপরিচিত হয়ে থাকবে না। পরস্পরের মধ্যে গভীর একাত্মতা থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়, ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হয়ে থাকবে। পরস্পর কোন শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না, থাকবে অকৃত্রিম ভালবাসা, দয়া-সহানুভূতি। পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মতপার্থক্য থাকবে না, সম্পূর্ণ একমত হয়ে কাজ করবে। হাদীসে তাই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষে লিপ্ত হবে না, কেউ কারো পিছনে পড়ে যাবে না- কেউ কারো দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। পারস্পরিক ক্রোধ ও অসন্তোষের প্রশ্রয় দেবে না; বরং পারস্পরিক আল্লাহর বান্দা ও ভাই হয়ে থাকবে।
মুসলমান ভাইর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে না
এ কারণে কোন মুসলিম ভাইর প্রতি নির্মম ও পাষাণবৎ ব্যবহার করতে, বয়কট করতে ও তার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকতে নিষেধ ও হারাম করা হয়েছে। দুজন মুসলমানের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হলে ক্রোধ দমনের জন্যে মাত্র তিনটি দিনের সময় দেয়া হয়েছে। অতঃপর পারস্পরিক সন্ধি সমঝোতা ও মিলমিশ সৃষ্টি ও ক্রোধ হিংসা সৃষ্টির কারণসমূহ দূর করার জন্যে চেষ্টা করা কর্তব্য। কুরআন মাজীদে মুমিন মুসলমানের গুণ স্বরূপ বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
মুমিনদের জন্যে অত্যন্ত নম্র বিনয়ী সহানুভূতি সম্পন্ন। (সূরা মায়িদাঃ ৫৪)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইকে তিন দিনের অধিক সময়ের জন্যে সম্পর্কহীন করে রাখা হালাল বা জায়েয নয়। তিন দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তার সাথে তার সাক্ষাৎ করা ও তাকে সালাম দেয়া কর্তব্য। যদি সে সে সালামের জবাব দেয়, তাহলে দুজনই সাওয়াবে শরীক হলো। আর জবাব না দিলে সে-ই গুনাহগার হবে এবং সালামদাতা সম্পর্কচ্ছেদের গুনাহ হতে রক্ষা পেয়ে যাবে। (আবূ-দাউদ)
রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের সাথে আত্মীয়তা রক্ষা করাকে ইসলাম ওয়াজিব ঘোষণা করেছেল। এ সম্পর্ক যত গভীর সেই অনুপাতে তা রক্ষা করার তাগিদও ততই বেশি ও বলিষ্ঠ। এ সম্পর্ক ছিন্ন করা কঠিনভাবে হারাম। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************) এবং ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের কাছে নিজের হক বা অধিকারের দাবি কর। আর নিকটাত্মীয়তার সম্পর্ককেও ভয় কর-রক্ষা কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রত। (আন-নিসাঃ ১)
এই নিকটাত্মীয়তার গুরুত্ব এবং আল্লহর কাছে তার মূল্য ও মর্যাদা বোঝাবার জন্যে রূপকভাবে বলেছেলঃ ( আরবি*******************) রেহম- রক্ত সম্পর্কের নিকটাত্মীয়তা আরশের সাথে ঝুলে থেকে বলেঃ যে আমাকে রক্ষা করল, আল্লাহও তাকে রক্ষা করবেন। আর যে আমাক ছিন্ন করল, আল্লাহও তাকে ছিন্ন করবেন। (বুখারী, মুসলিম)
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
(রক্ত সম্পর্ক) ছিন্নকারী কখনই বেহেশতে যাবে না। (বুখারী, মসলিম)
এ হাদীসটির ব্যাখ্যায় আলিমগণ দুটো কথা বলেছেন। একটি হচ্ছে রক্ত সম্পর্ক ছিন্নকারী, আর অপরটি হচ্ছে ডাকাত, ছিনতাইকারী- পথে-ঘাটে হত্যাকারী অর্থাৎ এ দুটো লোক একই পর্যায়ের অপরাধী
রক্ত সম্পর্কের ব্যাপারটি এরূপ নয় যে, একজন নিকটাত্মীয় অপর নিকটাত্মীয়ের সাথে সমতা আচরণ করবে। সে রক্ষা করলে তবে এ-ও রক্ষা করবে, সে ভাল ব্যবহার করলে এ-ও ভাল ব্যবহার করবে, এরূপ জেদাজেদি অবাঞ্ছনীয়। এটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার। ওয়াজিব হচ্ছে, কেউ সম্পর্ক ছিন্ন করলেও সে তা রক্ষা করে চলবে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ (আরবি*******************) ছেলায়ে রেহমী রক্ষাকারী সে নয়, যে সমান সমান ব্যবহার করে। বরং ছেলায়ে রেহমী রক্ষাকারী হচ্ছে সে, যে তা ছিন্নকারীর সাথে তা রক্ষা করে। (বুখারী)
এ সম্পর্ক ছিন্নকরণ ও বয়কট যদি আল্লাহর জন্যে, আল্লাহর পথে এবং প্রকৃত সত্যের জন্যে না হয়, তাহলেই এ কথা। অন্যথায় ঈমানের দৃঢ়তা সাধনের বড় উপায় হচ্ছে, আল্লাহর জন্যে ভালবাসা, আল্লাহর কারণে হিংসা বিচ্ছেদ।
নবী করীম (সা) এবং তাঁর সাহাবিগণ তাবুক যুদ্ধে পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে পঞ্চাশ দিন সম্পর্কছিন্ন করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ শেষোক্ত লোকদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠল, প্রাণান্তকর অবস্থা দেখা দিল। কেউ তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করত না, কথা বলত না, সালামও দিত না। অতঃপর আল্লাহ্ তাদের তাওবা কবুল করার কথা বলে আয়াত নাযিল করেন।
নবী করীম (সা) তাঁর কোন কোন বেগমের সাথে চল্লিশ দিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা) তার পুত্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে মরেই গেল। তার কারণ ছিল এই যে, সে রাসূলে করীম (সা)-এর একটি হাদীসকে মোটেই আমল দেয়নি, যা তিনি রাসূল থেকে বর্ণনা করেছিলেন। সে হাদীসটিতে রাসূলে করীম (সা) মেয়েদেরা মসজিদে যাওয়া থেকে নিষেধ করেছিলেন। ( আরবি*******************)
কিন্তু এ পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও সম্পর্কচ্ছেদ যদি দুনিয়ার বৈষয়িক কোন কারণে হয়, নিতান্তই স্বার্থের দ্বন্দ্বের দরুন হয় তাহলে তা খুবই অকিঞ্চিৎকর জিনিস, একজন মুসলমান তার এক মুসলমান ভাইর সাথে কিভাবে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে, যখন তার ফলে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত থেকে বঞ্চিত থাকার আশংকা রয়েছে? সহীহ হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
জান্নাতের দ্বার সোমবার ও বৃহস্পতিবার খুলে দেয়া হয়। অতঃপর আল্লাহ্ মাফ করেন এমন প্রত্যেক বান্দাকে, যে আল্লাহর সাথে একবিন্দু শিরক করে না। তবে সে ব্যক্তিকে ক্ষমা করেন না, যার মধ্যে ও তার ভাইর মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ রয়েছে। তখন আল্লাহ্ বলেনঃ ওদের দুজনকে পরিহার কর, যতক্ষণ না তারা সংশোধিত হয়, ওদের দুজনকে পরিত্যাগ কর যতক্ষণ না তরা সন্ধি সমঝোতা করে নেয়, ওদের দুজনকে ছেড়ে দাও যতক্ষণ না তারা নিজেদের মধ্যে মিলমিশ করে নেয়। (মুসলিম)
আর যে লোকের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে তার ভাইর কাছে এসে মার্জনা চাইবে এবং তার কর্তব্য তাকে ক্ষমা করে দেয়া এবং ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত হওয়া। ক্ষমা চাইলে ও ওযর পেশ করলে তা প্রত্যাখ্যান করা হারাম। নবী করীম (সা) এরূপ ব্যক্তিকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিন সে লোক তার সন্নিধানে হাওযে কাওসারে উপস্থিত হতে পারবে না। ( আরবি*******************)
পারস্পরিক সন্ধি সমঝোতাকরণ
দুই বিবাদমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে, ভ্রাতৃসম্পর্কের দাবিতে তাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ দূর করা ও সন্ধি-সমঝোতা করে নেয়া। এ যেমন সত্য, তেমনি এ ব্যাপারে সমাজেরও দায়িত্ব রয়েছে। কেননা ইসলামী সমাজ বলতে বোঝায় মানুষের পারস্পরিক সাহায্যকারী পরিপূরক মানব সমষ্টি। অতএব সমাজেরই দুই ব্যক্তিকে পরস্পর দ্বন্দ্বমান ও মারা-মারিতে লিপ্ত দেখবে অথচ সমাজ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবে, নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবে, তা কল্পনাও করা যায় না। তা কোনক্রমেই জায়েয হতে পারে না। কেননা তাহলে তো তারা দুজন ঝগড়া-বিবাদের আগুনে দগ্ধ হতে থাকবে এবং সে আগুন ক্রমশ সম্প্রসারিত হয়ে সমগ্র সমাজটিকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেবে।
বরং সুস্থ অভিমতসম্পন্ন ও প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন লোকদের কর্তব্য হচ্ছে নিছক সত্য ও ইনসাফের খাতিরে সে বিবাদমান ব্যক্তিদ্বয়ের মধ্যে মীমাংসা করা ও মিলমিশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হস্তক্ষেপ করা, চেষ্টা প্রচেষ্টা চালানো এবং তাদের লালসার দাসত্ব করা থেকে দূরে সরে থাকা। আল্লাহ্ তা’আলা এই নির্দেশ দিয়েছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি-সমঝোতা করে দাও এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাহলে আশা করা যায় যে, তোমাদের প্রতি রহমত করা হবে। (সূরা হুজরাতঃ ১০)
এ সংশোধন ও মিলমিশ বিধানের উচ্চ মর্যাদা এবং পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের খারাপ পরিণতির কথা নবী করীম (সা) নিজেই বিশ্লেষণ করে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
নফল নমায, রোযা ও সাদকার তুলনায়ও অধিক উত্তম কাজের কথা কি আমি তোমাদের বলব? সাহাবিগণ বললেন, হ্যাঁ রাসূল, বলুল। বললেন, তা হচ্ছে পারস্পরিক সংশোধন ও মিলমিশ বিধান। কেননা পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ মুণ্ডনকারী জিনিস। আমি বলি না যে, তা চুল মুণ্ডন করে বরং বলি, তা দ্বীনকেই নির্মূল করবে।
অন্যদের বিদ্রুপ করা ঠিক নয়
পূর্বে উদ্ধৃত আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা এমন সব কাজকেই হারাম ঘোষণা করেছেন, যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ককে বিনষ্ট করে এবং যা মানুষের মর্যাদা হানিকর।
এ পর্যায়ের প্রথম জিনিস হচ্ছে লোকদের বিদ্রুপ অপমান করা, কাউকে হীন করতে চেষ্টা করা। অতএব আল্লাহকে চিনে-জানে এবং পরকালের মুক্তির লক্ষ্যে এমন কোন ঈমানদার ব্যক্তির পক্ষেই কোন একজন লোককেও ঠাট্টা-বিদ্রূপ অপমান লাঞ্ছিত করতে চাওয়া বা করা, কাউকে তিরষ্কার-মন্দ বলার লক্ষ্যে পরিণত করা এবং দিন-রাত তাকে জ্বালাতন করা কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। কেননা এ কাজ যে করে তার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন আত্মম্ভরিতা-অন্যদের তুলনায় নিজেকে বড় মনে করার হীন মানসিকতা রয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এ লোক আল্লাহর কাছে ভালত্বের মানদণ্ড কি তা আদৌ জানে না। এ জন্যেই আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
কোন লোক অপর কোন লোককে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করবে না। কেননা তারা তাদের চাইতে উত্তম হতে পারে। তেমনি কোন মেয়ে অপর মেয়েদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ অপমান করবে না, কেননা তারাও তাদের তুলনায় ভাল হতে পারে।
বস্তুত আল্লাহর কাছে ভালত্বের মানদণ্ড ঈমান, একনিষ্টতা ও আল্লাহর সাথে ভাল সম্পর্ক- এ নিয়ে গঠিত। আকার-আকৃতি, দেহ-আবয়ব, মান-সম্মান ও ধন-দৌলতের ওপর তা ভিত্তিশীল নয়। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
আল্লহ্ তোমাদের আকার-আকৃতি ও ধনমালের দিকে তাকান না, তার কোন গুরুত্ব দেন না। তিনি দেখেন তোমাদের হৃদয় ও আমলের দিকে- তার কাছে এরই গুরুত্ব রয়েছে।
এমতাবস্থায় কোন পুরুষ কি অপর পুরুষকে এবং কোন নারী কি অপর নারীকে দৈহিক গঠন, আঙ্গিক ত্রুটি-কমতি কিংবা দারিদ্র্য ও অসচ্ছলতার দরুন ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করতে পারে ? করা কি কোনক্রমে জায়েয হতে পারে ?
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)-এর নলার কাপড় খুলে গেলে দেখা গেল তা খুবই সরু পাতলা। উপস্থিত কেউ কেউ তা দেখে বিদ্রূপের হাসি হেসে উঠল। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা ওর হালকা-পাতলা-সরু পায়ের নলা দেখে হাসছ? যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর নামের শপথ, এ দুইখানি পা আল্লাহর দাড়ি-পাল্লায় ওহুদ পর্বতের চাইতেও অধিক ভারী।
অপরাধী মুশরিকরা মুমিন মুসলমানকে কি ভাবে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করত, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার বিলাল ও আম্মারের ন্যায় দুর্বল লোকদের, তার বিবরণ কুরআন মজীদে দেয়া হয়েছে। কিয়ামতের দিন পাল্লা কিভাবে উল্টে যাবে এবং আজকের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমানকারীরাই যে সেদিন ঠাট্টা-বিদ্রূপের পাত্র হবে, তাও বলে দিয়েছে। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যারা অপরাধী তারা ঈমানদার লোকদের দেখে ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাঁসি হাসত। তাদের কাছে গেলে তারা পরস্পরকে ইঙ্গিত-ইশারা করত। আর যখন নিজেদের ঘরের লোকদের কাছে ফিরে যেত, তখন খুব তৃপ্তি ও সার্থকতা প্রকাশ করত। তাদের দেখতে পেলে তারা বলত, এরা সব পথভ্রষ্ট লোক। অথচ তাদের ওপর এদেরকে রক্ষাকারী করে পাঠান হয়নি। তাই আজকের দিনে ঈমানদার লোকেরা কাফিরদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপের হাসি হাসবে।
এ আয়াতের প্রথমাংশের কথায়ই মেয়েদের পরস্পরে ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান করার নিষেধ শামিল রেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে স্পষ্ট ভাষায় বলার প্রয়োজন মনে করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, কোন মেয়েলোক যেন অপর মেয়েলোকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ-অপমান না করে। তার কারণ এই যে, মেয়েদের পরস্পরের এ কাজ খুবই জঘন্য ও বীভৎস চরিত্র ও মন-মানসিকতার পরিচায়ক এবং তাদের মধ্যেই এটা ব্যাপক ও প্রকট লক্ষ্য করা যায়।
দুর্নাম করা, দোষী করা
এ পর্যায়ের দ্বিতীয় নিষিদ্ধ কাজ হচ্ছে অন্য লোকদের দুর্নাম করা, দোষী করা। যে লোক অন্যদের দুর্নাম করে, দোষী করে, সে যেন তাদের তীর বা তরবারির আঘাতে আহত ও জখমি করে। কিন্তু মুখের কথায় আঘাত আরও মারাত্মক। আরবী কবিতায় বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
লেজা-বল্লমের ক্ষত তো শুকিয়ে ভাল হেয়ে যায়, কিন্তু মুখের কথার আঘাত কখনই সারে না।
আয়াতে যেভাবে শব্দটি বলা হয়েছে, তা আল্লাহর ওহীর বিশেষত্ব বৈ কি। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)-তোমরা নিজেদের আহত, ক্ষত করো না।
আর্থাৎ তোমরা পরস্পরকে আহত ক্ষত-বিক্ষত করো না। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, কুরআন মুসলিম সমাজকে ‘এক অখণ্ড ব্যক্তিত্ব’ মনে করে। কেননা তারা সকলেই পরস্পরের জন্যে দায়িত্বশীল, পরিপূরক। এক্ষণে একজন যদি তার ভাইকে আহত করে, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে তার নিজেকেই আহত ও ক্ষত-বিক্ষত করে।
খারাপ উপাধিতে ডাকা
অন্যকে ক্ষত-বিক্ষত করা হারাম হওয়ার সাথে সাথে পরস্পর খারাপ উপাধিতে ডাকাও হারাম। অন্যকে এমন শব্দে বা নামে ডাকা যা তার খুবরাপ লাগে, সে তা অপছন্দ করে। কেননা তাতে তাকে অপমান ও বিদ্রূপ করা হয় এবং ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। তার অন্তরে আঘাত দেয়া হয়। কিন্তু কোন মানুষেরই উচিত নয় তার কোন ভাইকে এভাবে কষ্ট দেয়া। এতে করে মানুষের মন-মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। ভ্রাতৃত্বের সীমা লংঘন করা হয়। সাধারণ সৌজন্য ও রুচির পরিপন্থী এ কাজ।
খারাপ ধারণা
ইসলাম চায় মুসলিম সমাজের ব্যক্তিগণ পরস্পরের প্রতি পরিচ্ছন্ন, নির্মল-নির্দোষ মন-মানসিকতা নিয়ে বসবাস করুক। পরস্পরের প্রতি পরম আস্থা ও নির্ভরতা স্থিতিশীল হোক। পরস্পরের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ অনাস্থা ও অবিশ্বাস পোষণ না করুক। কেউ কারো প্রতি যেন খারাপ ধারণা না রাখে, মিথ্যা দোষারোপ না করে। এ কারণ পূর্বোদ্ধৃত আয়াতে চতুর্থ নিষিদ্ধ-হারাম কাজ হিসেবে এই কথার উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা ইসলাম কোন অবস্থায়ই মানুষের মান-মর্যাদার ক্ষুণ্ণতা বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা, তোমরা লোকদের প্রতি বহু ধরনের ধারণা পোষণ এড়িয়ে চল। কেননা কোন কোন ধারণা গুনাহ হয়ে থাকে। (সূরা হুজরাতঃ ১২)
বলা বাহুল্য, ধারণা বলতে এখানে খারাপ ধারণা পোষণের কথাই বলা হয়েছে।
অতএব কোন মুসলমানেরই তার মুসলিম ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা উচিত নয়, যথক্ষণ না অকাট্য কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।
মানুষ সম্পর্কে মৌলিকভাবেই ধরে নিতে হবে যে, তারা নির্দোষ। খারাপ ধারণার ওয়াসওয়াসা নির্দোষ মানুষকে দোষী সাব্যস্ত করবে, তা কিছুতেই উচিত নয়। নবী করীম (সা) তাই বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
লোকদের সম্পর্কে কু-ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা কুধারণা অত্যন্ত মিথ্যা কথা।
একথা ঠিক যে, মানুষ মানবীয় দুর্বলতার কারণে কুধারণা ইত্যাদি থেকে অনেক সময় নিজেকে দূরে রাখতে সমর্থ হয় না। কোন কোন লোক সম্পর্কে তাদের মনে সন্দেহ জেগে উঠে। বিশেষ করে যাদের সাথে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছে তাদের বিষয়ে। কিন্তু মুসলমান মাত্রেরেই কর্তব্য সেই কু-ধারণার কাছে নতি স্বীকার না করা, মানে তাকে স্থান না দেয়া এবং তার পিছনে ছুটে না বেড়ান। এ পর্যায়েও হাদীস বর্ণিত হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমার মনে কু-ধারণার সৃষ্টি হলে তুমি তাকে সত্য মনে করে নিও না।
দোষ খুঁজে বেড়ান
অন্য লোকদের প্রতি অনাস্থা মানুষকে একটা গোপন মানসিক অবস্থার দিকে ঠেলে নেয়। আর তা হচ্ছে কু-ধারণা পোষণ। তখন সে একটা বাহ্যিক দৈহিক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সেটি হচ্ছে দোষ খুঁজে বেড়ান। অথচ ইসলাম মানব মসাজকে এক সাথে অন্তর-বাহির উভয় দিক দেয়ে পরিছন্ন ও নির্মল পরিবেশের মাধ্যে রাখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।
এ কারণে কু-ধারণা পোষণ করতে নিষেধ করার সাথে সাথে পরের দোষ খুঁজে বেড়ান থেকেও নিষেধ করেছেন। কেননা এ কু-ধারণাই দোষ খুঁজে বেড়ানর মূল কারণ হয়ে থাকে।
বস্তুত প্রতিটি মানুষের একটা সম্মান ও মর্যাদা রয়েছে। তার দোষ খুঁজে বেরিয়ে সম্মান মর্যাদার সে আচরণ ছিন্ন করা এবং তার লুকিয়ে থাকা বিষয়াদি জনসমাজে উন্মুক্ত ও উলঙ্গ করে দেয়া কিছুতেই জায়েয হতে পারে না। কেউ নিজস্বভাবে কোন দোষ বা পাপ কাজেই লিপ্ত থাক না কেন। তা যতক্ষণ গোপন থাকছে, ততক্ষণ কারো উদ্যোগী হয়ে তা প্রকাশ করে দেয়া সম্পূর্ণ অনুচিত ও অবাঞ্ছনীয় কাজ।
হযরত উকবা ইবনে আমের (রা)-এর দরবারী লেখক আবুল হায়সাম বলেন, আমি উকবা ইবনে আমেরকে বললামঃ আমার কিছু সংখ্যক প্রতিবেশী রয়েছে, তারা মদ্য পান করে, আমি পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দিতে চাই। তখন তিনি বললেনঃ না তা করো না। তাদের বুঝাও, উপদেশ দাও, নসীহত কর। বললঃ আমি তো ওদের অনেক নিষেধ করেছি কিন্তু ওরা শুনছে না। এমতাবস্থায় পুলিশ ডেকে ওদের ধরিয়ে দেয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে? তিনি বললেনঃ না, তোমার জন্যে আফসোস! তুমি তা করতে যেও না। আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বলতে শুনেছিঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কারো গোপন কথা গোপন রাখল- প্রকাশ করে দিল না, সে যেন কোন জীবন্ত প্রোথিতকে তার কবরে জীবিত করে দিল। (আবূ দাঊদ, নিসারী, ইবনে মাযাহ)
লোকদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ানকে নবী করীম (সা) মুনাফিকদের খাসলাতের মধ্যে গণ্য করেছে। আর মুনাফিক তারা, যারা মুখে বলে ঈমান এনেছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের অন্তর ঈমান আনেনি। নবী করীম (সা) লোকদের সামনেই এ লোকদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম (সা) মিম্বারের ওপর দাঁড়িয়ে উচ্চতর কণ্ঠে ডাক দিয়ে বললেনঃ ( আরবি*******************)
হে সেসব লোক- যারা মুখে ঈমান ও ইসলাম কবুল করেছে, কিন্তু তাদের অন্তর পর্যন্ত ঈমান পৌঁছাতে পারে নি। তোমরা মুসলমানদের কষ্ট দিও না। এবং তদের গোপন দোষ খুঁজে বেড়িও না। কেননা যে লোক তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ্ তার দোষ খুঁজে বেড়াবেন। আর আল্লাহ্ যার গোপন দোষ খুঁজবেন তাকে তিনি লজ্জিত অপমানিত করবেন যদিও সে তার ঘরের কোণে বসে থাকে। (তিরমিযী, ইবনে মাযাহ)
লোকদের মান-মর্যাদার পূর্ণ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা দানের উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) কারো ঘরের লোকদের অনুমতি ব্যতিরেকে প্রবেশ করাকে কঠোরভাবে হারাম করে দিয়েছেন। এ জন্যে ঘরের লোকদের তরফ থেকে যদি কোন প্রতিঘাত আসে, তাহলে কোন অপরাধ হবে না বলে জানিয়েছে। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক অপর কারো ঘরের ভিতরে উঁকি দিল তাদের অনুমতি ছাড়াই, ঘরের লোকদের জন্যে তার চক্ষু ফুটো করে দেয়া সম্পূর্ণ হালাল হয়ে গেছে।
ঘরের মধ্যে বসে লোকদের বলা কথাবার্তা তাদের অবহিত ও অনুমতি ছাড়া অপর লোকদের শোনা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক অন্য লোকদের কথাবার্তা চুরি করে শুনবে- সেই লোকেরা কিন্তু চায় না যে, তাদের কথা কেউ লকিয়ে থেকে শুনুক- কিয়ামতের দিন তার দুই কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (বুখারী)
কেউ যদি কারো সাথে সাক্ষাত করার উদ্দেশ্যে তার বাড়িতে গমন করে, তখন তার অনুমতি ছাড়া ও সালাম করা ছাড়াই ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া সম্পর্ণ হারাম। সে জন্যে তাকে প্রথমে সালাম করতে হবে ও প্রবেশের অনুমতি চাইতে হবে। এইটা ওয়াজিব। ইরশাদ হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা অন্যদের ঘরে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না অনুমতি চাইবে ও ঘরের লোকদের প্রতি সালাম করবে। তোমাদের জন্যে এটাই কল্যাণকর। সম্ভবত তোমরা মনে রাখবে। সে ঘরে যদি কাউকে না-ই পাও, তাহলে তাতে তোমরা প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না তোমাদের জন্যে পবিত্রতর কর্মনীতি। তোমরা যা কিছু কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ পুরাপুরি অবহিত। (সূরা নূর ২৭-২৮)
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোকই কোন গোপনীয় জিনিস উন্মুক্ত করবে এবং অনুমতি দেয়ার আগেই তার দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, তাহলে সে এমন সীমার মধ্যে প্রবেশ করল, যে সীমার মধ্যে প্রবেশ করা তার জন্যে হালাল নয়। (আহমদ, তিরমমিযী)
পরের দোষ খুঁজে বেড়ানো- লুকানো ত্রুটি আতিপাতি করে খুঁজে বের করা সাধারণভাবে সকলের জন্যেই হারাম। শসক-প্রশাসক এবং শাসিত জনগণ সকলের জন্যেই এই নিষেধ। কেউই এ থেকে মুক্ত নয়, কারো জন্যেই তার অনুমতি নেই। হযরত মুআবিয়া (রা) রাসূলে করীম (সা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তুমি যদি লোকদের গোপন দোষ তালাশ করে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের বিপর্যস্ত করবে কিংবা বিপর্যয়ের কাছে পৌঁছে দেবে। (আবূ দাউদ, ইবনে মাযাহ)
তিনি আরও বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
শসক বা প্রশাসক যখন লোকদের মধ্যে সন্দেহ সংশয়ের কথাবার্তা খুঁজে বেড়াতে শুরু করে, তখন সে তাদের বিপর্যস্ত করে দেয়। (আবূ দাউদ)
গীবত
উপরিউক্ত আয়াত ষষ্ঠ পর্যায়ে যে জিনিস হারাম করে দিয়েছে, তা হচ্ছে গীবত। আয়াতাংশ হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা যেন পরস্পরের গীবত করো না। (সূরা হুযরাতঃ ২১)
নবী করীম (সা) সওয়াল-জবাব পন্থায় তাঁর সাহাবীদের ‘গীবত’ শব্দের সংজ্ঞা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদের লক্ষ্য করে বললেনঃ ( আরবি*******************) – তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে?
সাহাবিগণ বললেনঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানে। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমার ভাইয়ের উল্লেখ এমনভাবে করা, যা সে নিজে পছন্দ করে না- তাই হচ্ছে গীবত। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূল, আমি যা বলি তা যদি আমার সেই ভাইয়ের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে থেকে থাকে, তাহলেও কি তা বলা গীবত হবে। বললেনঃ তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে থেকেই থাকে, তবেই তো গীবত হবে। আর যদি নাই থাকে, তাহলে তো বহতান- মিথ্যা দোষারোপ হবে। (মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী)
মানুষ পছন্দ করে না- এমন কথা তার জন্য তার অনুপস্থিতিতে বলা- এ পর্যায়ে তার দৈহিক গঠন আকার-আকৃতি, চরিত্র, কাজ-কর্ম, বংশ ও তার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিষয়ই এর অন্তর্ভুক্ত। হযরত আয়েশা (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমি রাসূলে করীম (সা)-কে বললামঃ আপনার বেগম সাফিয়ার খাঁটো হওয়াটাই যথেষ্ট। তখন নবী করীম (সা) বললেনঃ তুমি এমন একটা কথা বললে, যদি তা সমুদ্রের পানির সাথ মিলেয়ে দেয়া হয়, তাহলে সে পানির রং বদলে যাবে। (আবূ দাঊদ, তিরমিযী, বায়হাকী)
আসলে গীবত দ্বারা অন্যদের হীন পতিপন্ন করা কুপ্রবৃত্তিরই প্রকাশ ঘটে। তাদের অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের মান-সম্মান-মর্যাদাকে ক্ষণ্ণ করার প্রবল ইচ্ছাই কাজ করে। তা গীবতকারীর হীন মন-মানসিকতা, নীচতা ও কুপ্রবৃত্তির পরিচয় দিয়ে দেয়। কেননা তা পিছন থেকে আঘাত হানার শামিল। তা প্রমাণ করে যে, গীবতকারীর নিজের কোন কাজ নেই। সে-ই তো গীবত করার কাজে পটুতা দেখায়। গীবত প্রবণতা সমাজ বিধ্বংসী কার্যক্রম, কেননা যারা গীবত করতে অভ্যস্ত তাদের জিহবার তরবারির আঘাত থেকে খুব কম লোকই রক্ষা পেতে পারে।
এমতাবস্থায় কুরআন মজীদে যদি তার বীভৎস ও জঘন্য রূপ উদঘাটিত করে থাকে এবং এমনভাবে তার চিত্র উপস্থাপিত করে থাকে, যা মানুষের মনে তীব্র ঘৃণার উদ্রেক করে, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। সে চিত্রটি এইঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কেউ যেন অপর কারো গীবত না করে। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া?- তা তোমরা অপন্দ করই।
বস্তুত মানুষ মানুষের গোশত খাওয় আদৌ পছন্দ করতে পারে না। তাহলে নিজ ভাইয়ের গোশত খাওয়া- মৃত ভাইয়ের গোশাত খাওয়া কি করে তার পক্ষে সম্ভব হতে পারে?
নবী করীম (সা) যখনই সুযোগ, ক্ষেত্র ও পরিবেশ পেতেন, গীবতের এই চিত্র তখনই তিনি উদঘাটিত করতেন এবং লোকদের মনে এই বীভৎস ছবি সর্বদা জাগ্রত থাক, তাই তিনি চইতেন।
হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তখন মজলিসের বাইরে চলে গেল। তখন এক ব্যক্তি সে লোকটি সম্পর্কে অপমানকর কথা বলল। তখন নবী করীম (সা) এই ব্যক্তিকে বললেনঃ তুমি খেলাল কর। লোকটি বললঃ আমি কেন খেলাল করব, আমিতো কোন গোশত খাইনি? নবী করীম (সা) বললেনঃ তুমি এইমাত্র তোমান ভইয়ের গোশত খেয়েছ।
হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ( আরবি*******************)
আমরা নবী করীম (সা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন খুব দুর্গন্ধময় বাতাস প্রবাহিত হলো। নবী করীম (সা) বললেনঃ তোমরা জান, এইটা কিসের বাতাস?...এইটা হচ্ছে মুমিনদের যারা গীবত করে, তাদের বাতাস। (আহমদ)
গীবতের অনুমতি-সীমা
উপরে উদ্ধৃত সব কুরআনের আয়াত ও হাদীসে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ইসলামে ব্যক্তির মর্যাদা অত্যন্ত পবিত্র ও সুরক্ষিত।
কিন্তু ইসলামে বিশেষজ্ঞদের মতে গীবতের কয়েকটি দিক হারাম থেকে ব্যতিক্রম। প্রয়োজনের তাগিদে যেখানে গীবত না করে কোন উপায় থাকে না, তা হচ্ছে এই ব্যতিক্রমের দিক এবং এই ব্যতিক্রমের সুযোগ প্রয়োজনের দরুনই ব্যবহার করা যেতে পারে।
যে মজলুম জালিমের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ করে, সে জালিমের এমন সব কথা প্রকাশ করে যা তার খারাপ লাগলেও সে কথাগুলো সবই সত্য এবং তার সে অধিকারও আছে। এই জুলুমের ক্ষেত্রে ফরিয়াদ করার জন্যে কারো বিরুদ্ধে বলার প্রয়োজন দেখা দিলে তা অবশ্যই বলতে হবে। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ ত’আলা খারাপ ধরনের কথা প্রকাশ ও প্রচার করা আদৌ পছন্দ করেন না, তবে যার ওপর জুলুম হয়েছে, তার তা করা স্বতন্ত্র ব্যাপার। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত। (সূরা আন-নিসাঃ ১৪৮)
এক ব্যক্তি অপর এক নির্দিষ্ট ব্যক্তির সম্পর্কে জানতে চায় এই উদ্দেশ্যে যে, লোকটির ভাল চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারলে তার সাথে ব্যবসায়ে শরীক হবে অথবা কেউ তার কন্যা বিয়ে দেবে, প্রস্তাবক ছেলে সম্পর্কে সে জানতে চায়। এ সব ক্ষেত্রে একদিকে থাকে লোকদেরকে সঠিক কথা ও প্রকৃত অবস্থা জানানর দায়িত্ব আর অপরদিকে থাকে অনুপস্থিত ব্যক্তির ইজজত-আবরু রক্ষার কর্তব্য। এ দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে প্রবল বিরোধিতা ও সংঘর্ষ বিদ্যমান। কিন্তু প্রথম দায়িত্ব যেহেতু সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও পবিত্র, সেই কারণে সেটির অগ্রাধিকার অবশ্য স্বীকার করতে হবে। ফাতিমা বিনতে কাইস নবী করীম (সা)-কে তার বিয়ের জন্যে আসা দুটি প্রস্তাব সম্পর্কে অবহিত করে কোনটি গ্রহণ করবেন তার পরামর্শ চাইলেন। তখন তিনি তার একজন সম্পর্কে বললেনঃ এ লোকটি স্ত্রীকে খুব মারধোর করে। সে তার লাঠি কাঁধের ওপর থেকে কখনই নামায় না।
এ ব্যতিক্রমের মধ্যেই রয়েছে অন্যায় ও পাপকে বদলে দেয়ার উদ্দেশ্যে কথা বলা। হাদীস অনুযায়ীই এটা কর্তব্য।
কোন লোকের পরিচিতিই যদি হয় এমন নামে, যা সে নিজে পছন্দ করে না অথচ সেই নাম না বললে তাকে চেনাই যায় না- যেমন আরাজ- ‘ল্যংগরা’, আমাশ (দুর্বল দৃষ্টি শক্তিসম্পন্ন) বা অমুক মেয়ে লোকের পুত্র ইত্যাদি। তাই এ পরিচিতির উদ্দেশ্যেই তা বলতে হবে। সাক্ষী, হাদীস বর্ণনাকারী ও খবরদাতাদের জেরা করা- তাদের চারিত্রিক দোষ-গুণ আলোচনা করাও এ পর্যায়েরই কাজ।
এ পর্যায়ে ‘গীবত’ জায়েয হওয়ার দুটি ভিত্তি রয়েছেঃ
একটি, প্রয়োজন; দ্বিতীয়, নিয়ত- মনোভাব। অনুপস্থিত ব্যক্তি তার অসন্তুষ্টির বিষয়ে উল্লেখ করার প্রয়োজন তীব্র হয়ে দেখা না দেয়া পর্যন্ত এ নিষিদ্ধ ক্ষেত্রে কারোরই পদাচারণা করা উচিত নয়। যদি ইশারা-ইঙ্গিতে বললে প্রয়োজন মিটে যায়, তাহলে সুস্পষ্ট করে বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। অথবা নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা না বলে সাধারণ ভাবে কথাটি বলা যেতে পারে। যেমন জিজ্ঞেস করার একটা ধরনঃ এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি, যে এই এই কাজ করে? সেখানে ‘অমুকের পুত্র অমুকে’ বলা উচিত নয়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে আছে এমন বিষয়ে বলতে গেলে শর্ত প্রযোজ্য। কিন্তু তার মধ্যে নেই তা-ই যদি বলা হয়, তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ এবং তা সম্পূর্ণ হারাম।
নিয়ত, এটাই হচ্ছে এ পর্যায়ে সব ব্যাপারের চূড়ান্ত ফয়সালাকারী ব্যাপার। কি কারণে সে কথা বলছে, তা অন্যদের অপেক্ষা সে নিজেই ভাল জানেন। এ নিয়তের ভিত্তিতেই গীবত সমালোচনা, উপদেশ এবং দোষ প্রচার করা প্রভৃতির মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। আর এও সত্য যে, মুমিন তার নিজের মনোভাব সম্পর্কে নিজেই খুব কড়াভাবে হিসেব-নিকেশ করতে পারে এবং করেও থাকে।
ইসলামের দৃষ্টিতে এটাও নিশ্চিত কথা যে, গীবত যে শোনে সেও গীবত কার্যে শরীক মনে করতে হবে। আর প্রত্যেকেরই কর্তব্য তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার সাহায্য করা, তর পক্ষে কথা বলা। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত সংরক্ষণ করল তার দোষ স্খালন করল, তার হক হচ্ছে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাবেন। (আহমদ)
( আরবি*******************)
যে লোক তার ভাইয়ের ইজ্জত রক্ষা করল এ দুনিয়ায়, আল্লাহ্ তার থেকে কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে ফিরিয়ে নেবেন। (তিরমিযী)
যার এরূপ সাহসিকতা নেই, ভাইয়ের মর্যাদাহানির আঘাত থেকে যে তার ভাইকে রক্ষা করতে পারল না, তার অন্ততপক্ষে সে মজলিস ত্যাগ করে চলে যাওয়া এবং সেই লোকদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা কর্তব্য- যতক্ষণ না তারা অন্য কোন কথায় মনোনিবেশ করছে। তা-ও না করলে সে তো আল্লাহর এ বাক্যটির আওতার মধ্যে পড়ে যাবেঃ ( আরবি*******************) – তোমরাও এক্ষণে তাদের মতোই হয়ে গেলে। (সূরা নিসা ১৪০)
চোগলখোরী
গীবতের কথা যখনই বলা হয়, তখনই তার সাথে এমন আর একটি স্বভাবেরও উল্লেখ করা হয়, যা ইসলমের দৃষ্টিতে গীবতের মতোই কঠিনভাবে হারাম। আর তা হেচ্ছে চোগলখোরী। কারো মুখে একজনের বিরুদ্ধে কিছু শুনে তা সে ব্যক্তির কাছে এমনভাবে পৌঁছে দেয়া, যার ফলে দুজনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি অনুষ্টিত হয় এবং পারস্পরিক মনের পরিছন্নতা দূর হয়ে গিয়ে পংকিলতা ও ময়লার সৃষ্টি হয়। অথবা পূর্ব থেকে থাকা সেই পংকিলতা ও ময়লা আরও অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে যায়।
এ হীন ও মারাত্মক ধরনের খাছরতের প্রতিবাদ করে মক্কী সূরাসমূহেই আল্লাহর কথা নাযিল হয়। তাতে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
এমন ব্যক্তির কথা তোমরা মেনে নিও না, যে খুব বেশি কিরা-কসম খায় ও গুরুত্বহীন, যে লোকদের দুঃখ দেয়, অভিশাপ বর্ষণ করে বেড়ায় এবং চোগলখোরী করে ফিরে। (সূরা আল-কালামঃ ১০-১১)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
চোগলখোর জান্নাতে যাবে না। (বুখারী, মুসলিম)
এখানে ‘কাত্তাতুন’ শব্দটির অর্থ চোগলখোর। কেউ কেউ বলছেনঃ আসলে চোগলখোর সে, যে কথাবার্তায় মগ্ন একদল লোকের সঙ্গে শামিল থাকে, পরে তাদের বিরুদ্ধে গিয়ে চোগলখোরী করে। আর ‘কাত্তাতুন’ হচ্ছে সে, যে লোকদের অজ্ঞাহসারে তাদের কখাবার্তা শুনে তাদের বিরুদ্ধে বলতে শুরু করে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহর নিকৃষ্টতম বান্দা হচ্ছে তারা, যারা চোগলখোরী করে। বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ ও ফাটলের সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ লোকদের দোষ বের করার জন্যে চেষ্টা করতে থাকে। (আহমদ)
পারস্পরিক বিবাদ দূর করে মীমাংসা ও মিলমিশের জন্যে যারা চেষ্টা করে ইসলাম তাদের জন্যে এটা জায়েয বলেছে যে, একজনের সম্পর্কে খারাপতম কথা জানা সত্ত্বেও সে তা প্রকাশ করবে না। উপরন্তু নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু ভাল ভাল কথা বাড়িয়ে বলবে যদিও তা একজন সম্পর্কে অপরজনের কাছ থেকে শুনতে পায়নি।
যারা কোন খারাপ কথা কোথাও শুনতে পায়, আর অমনি তা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বা বিদ্বেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্যদের কাছে গিয়ে বলে দেয়, তাদের ওপর ইসলামের তীব্র ক্রোধ ও আক্রোশ। কেননা এরা সমাজে ধ্বংস ও বিপর্যয় সৃষ্টি করার কুমতলবেই তা করে থাকে।
এ ধরনের লোকেরা যতটুকু শুনে ততটুকু মূলধনের ওপরই নির্ভর করে না, সমাজ-বিধ্বংসী মনোবৃত্তি যা শুনেছে তার ওপর নিজেদের পক্ষ থেকে অনেক বাড়িয়ে দিতে এবং মনগড়াভাবে রচনা করে নিতেও কৃণ্ঠিত হয় না। আর তারা যদি ভাল কিছু শুনে তাহলে গোপন রাখে। আর খারাপ কিছু শুনলে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করে। আর না শুনলে মিথ্যা বলে।
এক ব্যক্তি হযরত উমর ইবনে আবদুল আজীজের কাছে অপর এক ব্যক্তির পক্ষ থেকে তাকে এমন কিছু শোনাল যা তিনি পছন্দ করেন নি। তখন খলীফা উমর (২য়) বললেনঃ তুমি চাইলে আমি তোমার ব্যাপারটা দেখব। আর তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তুমি কুরআনের এ আয়াতের পর্যায়ে পড়ে গেছঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কাছে কোন ফাসিক ব্যাক্ত এসে যদি কোন সংবাদ দেয়, তাহলে তোমরা তার সত্যতা- যথার্থতা অবশ্যই যাচাই করে দেখবে।
আর তুমে যদি সত্যবাদী হও, তাহলে তুমি এ আয়াতের আওতার মধ্যে গণ্যঃ ( আরবি*******************) আর তুমি যদি চাও, তাহলে তোমাকে আমরা মাফ করে দেব। লোকটি বললঃ ‘হে আমীরুল মুমিনিন, ক্ষমা করে দিন। আমি এ ধরনের কাজ আর করব না।’
মান-সম্মান সংরক্ষণ
ইসলাম তার উচ্চতর মানের শিক্ষার দ্বারা মানুষের মান-সম্মান ও মর্যাদা সংরক্ষণের ওপর কতখানি গুরুত্ব দিয়েুছে, তা আমরা দেখেছি। মানুষের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যাপারটি তার পবিত্রতা বিধানের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, তাও লক্ষণীয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) একদা কাবা ঘরের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেনঃ ( আরবি*******************)
হে কাবা! তোমার বিরাট মর্যাদা, তোমার মর্যাদার বিরাটত্ব বিষয়ে আর কি বলব। কিন্তু মুমিন লোকের মর্যাদা তোমার চাইতেও অনেক উচ্চ ও বড়। আর মুমিনের মর্যাদা প্রতিফলিত হয় তার ইজ্জতের, রক্তের ও ধন-মালের মধ্য দিয়ে।
বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (সা) বিরাট ইসলামী জনতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ ( আরবি*******************)
জেনে রাখো তোমাদের ধন-মাল, তোমাদের ইজ্জত-আবরু এবং তোমাদের রক্ত পরস্পরের ওপর হারাম-সম্মানার্হ, তোমাদের আজকের দিনের মর্যাদার মতো- তোমাদের এ মাসে তোমাদের এ নগরে।
ব্যক্তির ইজ্জত-আবরুও ইসলাম রক্ষা করেছে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা নিষেধ করে যা সত্য অথচ সে তা অপছন্দ করে। তাহলে যে-কথা মনগড়া ভিত্তিহীন, তা বলার সুযোগ কি করে থাকতে পারে? যদি তা বলা হয়, তাহলে তো অতি বড় পাকা অপরাধ ও গুনাহ হবে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কারো সম্পর্কে এমন কথা বলল- যা তার মধ্যে নেই- শুধু এ উদ্দেশ্যে যে, তাকে দোষী করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে বন্দী করে রাখবেন, যতক্ষণ না তার বলা কথার সত্যতা সে প্রমাণিত করে দেবে। (তাবারানী)
হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবিগণকে বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা কি জান, আল্লাহ্ কাছে সবচেয়ে বড় সুদ কি? সাহাবিগণ বললেনঃ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই জানেন। বললেনঃ সবচেয়ে বড় সুদ আল্লাহর কাছে মুসলমানদের ইজ্জত নষ্ট করতে চাওয়। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াত পাঠ করলেন, যার আর্থঃ যারা মুমিন পুরুষ ও মেয়েলোকদের তাদের নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট ও পীড়ন দেয়, তারা মিথ্যা দোষারোপ ও সুস্পষ্ট গুনাহের অভিশপ নিজেদের মাথায় তুলে নেয়। (সূরা আহযাবঃ ৫৮)
এ পর্যায়ে সবচাইতে বড় গুনাহ হচ্ছে মনুষের ইজ্জত আবরুর ওপর আক্রমণ চালানো। যেমন পবিত্র চরিত্রা ঈমানদার মুমিন মহিলদের ওপর চরিত্রহীন কাজের দোষারোপ করা। কেননা এতে তাদের সুনাম সুখ্যাতি, তাদের বংশ ও পরিবারের মান-মর্যাদার যেমন ক্ষতি হওয়ার আশংকা, তেমনি তাদের ভবিষ্যতের জন্যেও বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। উপরন্তু এরূপ করে মুমিনদের সমাজে নির্লজ্জতা ও চরিত্রহীনতার ব্যাপক প্রচার সাধনের প্রবণতাও দেখতে পাওয়া যায়।
এ কারণে নবী করীম (সা) এ কাজটিকে সাতটি ধ্বংসাত্মক কবীরা গুনাহের মধ্যে গণ্য করেছেন এবং কুরআন মজীদ এ কাজের দরুন কঠোর ভাষায় নির্মম পরিণতির ওয়াদা করেছে। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যেসব লোক মুমিন অসতর্ক পবিত্র চরিত্র সম্পন্না মহিলাদের ওপর চারিত্রিক দোষারোপ করে, দুনিয়া ও পরকালে তাদের ওপর অভিসম্পাত এবং তাদের জন্যে বড় আযাব রয়েছে। সেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের মুখ, হাত ও পা, তারা যা যা করেছে সে সম্পর্কে। এ দিন আল্লাহ্ তাদের সত্য প্রতিফলটা পূর্ণ করে দেবেন এবং তারা জানতে পারবে যে, আল্লাহই হচ্ছেন মহাসত্য।
আরও বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যেসব লোক মুমিনদের সমাজে নির্লজ্জতা ও পাপ কাজের ব্যাপক প্রচলন প্রসারতা ঘটাতে ভালবাসে, তাদের জন্যে আযাব দুনিয়ায় ও আখিরাতে- সর্বত্র। আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। (সূরা আন-নূরঃ ১৯)
রক্তের মর্যাদা
ইসলাম মানব জীবনকে সর্বাধিক সম্মানার্হ ও মর্যাদাবান বানিয়েছে। মানবাত্মার পবিত্রতার কথা ঘোষণা করেছে। আর তার ওপর হস্তক্ষেপকে আল্লাহর কাছে কুফরের পর সবচেয়ে বড় গুনাহ রূপে চিণ্হিত করেছে। কুরআন মজীদে ঘোষণা করেছেঃ ( আরবি*******************)
কোনরূপ হত্যার বা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়াই যে লোক একজন মানুষকে হত্যা করে, সে যেন সমস্ত মনুষকে হত্যা হরার অপরাধ করল। তা এ জন্যে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানুষ একই পরিবারভুক্ত। এমতাবস্থায় তাদের একজনকে হত্যা করা হলে- সীমালংঘন করা হলে সমস্ত মানব-প্রজাতির ওপরই তার আঘাত পড়ে। তার কুফল সকলেই ওপর প্রবর্তিত হয়।
কিন্তু নিহত ব্যক্তি যদি মুমিন হয় তাহলে হারাম হওয়ার ব্যাপারটি অধিকতর কঠিন ও তীব্র হয়ে দাঁড়ায়। কুরআন মজীদে এজন্যে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক ইচ্ছা করে কোন মুমিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তার প্রতিফল হচ্ছে জাহান্নাম। তাতে সে চিরদিন থাকবে। আল্লাহ্ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করবেন এবং তার জন্যে বড় আযাব প্রস্তুত করে রাখবেন।
রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লহর কাছে একজন মুসলমানের নিহত হওয়ার তুলনায় সারা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়াও অনেক হালকা ব্যাপার। (মুসলিম, নিসায়ী, তিরমিযী)
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
মুমিন দ্বীনের দিক দিয়ে প্রশস্ততার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ না হারাম নর হত্যার অপরাধ করে।
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ তা’আলা সম্ভবত সমস্ত গুনহই মাফ করে দেবেন। তবে যে লোক মুশরিক অবস্থায় মরেছে অথবা কোন মুমিন ব্যক্তিকে ইচ্ছা করে হত্যা করেছে তাকে নয়।
এ সব আয়াত ও হাদীসের ভিত্তিতে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) মনে করেছেন যে, হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে না। অন্য কথায় তিনি মনে করেছেন, তওবা কবুলের জন্যে শর্ত হচ্ছে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হক ফিরিয়ে দেয়া কিংবা তাকে সন্তুষ্ট কারা। কিন্তু ব্যক্তির হক কি করে ফিরিয়ে দেয়া যেতে পারে কিংবা তাকে সন্তুষ্টই বা করা যেতে পারে কিভাবে ?
অন্যরা বলেছেন, খালেস তওবা অবশ্যই কবুল হবে। এ ধরনের তওবা শিরকের গুনাহ পর্যন্ত মাফ করিয়ে দেয়। তাহলে তার চাইতে কম মাত্রার গুনাহ কেন তওবায় মাফ হবে না ?
আল্লাহ্ তা’আলা তো বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যেসব লোক আল্লাহর সঙ্গে দ্বিতীয় ইলাহ্ ডাকে না, কোন মানুষকে বিনা কারণে হত্যা করে না এবং জ্বেনা করে না- যে লোক এই এই কাজ করে সে তার গুনাহের বদলা পাবে। কিয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তার মধ্যে অপমানিত অবস্থায় চির দিন থাকবে। তবে যে লোক তাওবা করবে, ঈমান আনবে এবং নেক আমল করবে, আল্লাহ্ তাদের খারাপ কাজগুলোকে ভাল ও নেক কাজে পরিবর্তিত করে দেবেন। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়াবান। (সূরা আল-ফুরক্বানঃ ৬৮-৭০)
হন্তা ও নিহত উভয়েই জাহান্নামী
নবী করীম (সা) মুসলিমদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়াকে কুফরির একটা দুয়ার বলে ঘোষণা করেছেন। এটা জাহিলিয়াত যুগের কাজ বলে অভিহিত করেছেন। কেননা তখনকার লোকেরা যুদ্ধে সব সময় লিপ্ত থাকত এবং একটি উষ্ট্রী বা ঘোড়ার কারণে তারা রক্তের বন্যা প্রবাহিত করতেও দ্বিধা করত না। নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
মুসলমানকে গাল দেয়া ফাসিকী কাজ এবং তার সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া সুস্পষ্ট কুফরি। (বুখারী, মুসলিম)
নবী করীম (সা)-এর আর একটি কথাঃ ( আরবি*******************)
আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা পশ্চাদপসরণ করে কাফির হয়ে যেও না ও পরস্পরের কল্লা কাটতে শুরু করে দিও না। (বুখারী, মুসলিম)
অপর এক হাদীসে বলা হয়েছেঃ দুজন মুসলমানের একজন যখন তার ভাইর ওপর অস্ত্র ধারণ করে, তখন তারা দুজনই জাহান্নামের কিনারে উপস্থিত হয়। অতঃপর একজন যখন অপরজনকে হত্যা করে, তখন দুজনই জাহান্নামে যায়। প্রশ্ন করা হলো হে রাসূল, হত্যাকারীর জাহান্নামে যাওয়া তো বোধগম্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন জাহান্নামে যাবে? বললেনঃ ( আরবি*******************)
সেও তো তার সঙ্গীকে হত্যা করতে চেয়েছিল। (বুখারী, মুসলিম)
এ কারণে নবী করীম (সা) এমন সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করেছেন, যার পরিণতি হত্যা বা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। অস্ত্রের দ্বারা ইঙ্গিত করাও এ পর্যায়ে পড়ে। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কেউ যেন তার ভাইর প্রতি অস্ত্রের দ্বারা ইশারা না করে, কেননা শয়তান কখন তার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবে ও সে জাহান্নামের গর্তে পড়ে যাবে, তা সে হয়ত টেরও পাবে না। (বুখারী, মুসলিম)
বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যেলোক তার ভাইয়ের প্রতি কোন অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে তখন ফেরেশতা তার ওপর অভিশাপ করে, যতক্ষণ না সে তা থেকে বিরত হয়, যদিও তার আপন ভাই-ই হোক না কেন। (মুসলিম)
তিনি আরও বলেছেঃ ( আরবি*******************)
কোন মুসলমানের জন্যে জায়েয নয় আর একজন মুসলমানকে ভয় দেখান।
গুনাহ কেবলমাত্র হত্যাকারী পর্যন্তই সীমিত হয়ে থাকে না। বরং তাতে যে লোক কোনরূপ কথা বা কাজ দ্বারা শরীক হয়, সেও এ হত্যা পাপের অংশীদার হয়। তার এই অংশ গ্রহণের মাত্রা অনুযায়ীই আল্লাহর ক্রোধ রোষ ও অসন্তোষ তার ওপর পড়ে। এমন কি হত্যাকাণ্ডের অকুস্থলে যে লোক উপস্থিত থেকেও নিষ্ক্রিয় থাকবে, সেও এই পাপে শরীক হবে। হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যেখানে কোন লোককে বিনা কারণে জুলুম হিসেবে হত্যা করা হয়, তথায় যেন কেউ না দাঁড়ায়। কেননা এ হত্যাকাণ্ডে যে লোক উপস্থিত থাকবে ও তাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে না, তার ওপরও অভিশাপ অবতীর্ণ হবে।
চুক্তি সম্পন্ন ও যিম্মী ব্যক্তির রক্ত মর্যাদা
এসব আয়াত ও হাদীসে মুসলমানকে হত্যা ও মুসলমানের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া থেকে সাবধান করা হয়েছে। এটা শরীয়তেরই বিধান মুসলিম সমাজে বসবাসকারী মুসলমানদের জন্যে এ পথ-নির্দেশ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অমুসলিমের রক্ত বুঝি হালাল! আসলে মানুষ মাত্রেরই রক্ত অবশ্য রক্ষণীয়। মানুষ হিসেবেই তাকে বাঁচাতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অমুসলিম মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হবে, তাকে হত্যা করা যাবে না। হ্যাঁ যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অমুসলিম যুদ্ধ ঘোষণা করে, তাহলে তখন তার রক্তপাত করা যেতে পারে। আর সেই অমুসলিম যদি মুসলিম রাষ্ট্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় কিংবা হয় যিম্মী, তাহলে রক্তের নিরাপত্তা অবশ্যম্ভাবী। মুসলিমানের পক্ষে সীমালংঘন করা কিছুতেই হালাল হবে না। এ সম্পর্কে নবী করীম (সা)-এর কথা হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুঘ্রাণ তো চল্লিশ চছর পথের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যায়।
অপর বর্ণনায় বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন যিম্মীকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাবে না।
রক্তের মর্যাদা কখন থাকে না
আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা মানুষকে হত্যা করবে না, যাকে আল্লাহ্ হারাম করেছেন। তবে সত্যতা সহকারে হত্যা করার কথা স্বতন্ত্র। (সূরা আন-আমঃ১৫১)
এখানে যে সত্যতার কথা বলা হয়েছে। যার কারণে নর হত্যা করা যায়, তা হচ্ছে কোন অপরাধের দণ্ডস্বরূপ হত্যা করা। আর সেই অপরাধ তিনটিঃ
১. জুলুম করে হত্যা করা। যে লোকের হত্যাকাণ্ডের অপরাধ প্রমাণিত হবে, তার কিসাস করা ওয়াজিব এবং সেই কিসাস হচ্ছে, হত্যার দণ্ড স্বরূপ হত্যাকারীকে হত্যা করা। অর্থাৎ জানের বদলে জান। কুরআনে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হত্যার দণ্ডস্বরূপ হত্যা করাই তোমাদের জন্যে জীবন নিহিত।
২. প্রকাশ্যভাবে জ্বেনা করা এমনভাবে যে, চারজন ভাললোক তা নিজেদের চোখে প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে সাক্ষ্যও দেবে। তবে শর্ত এই যে, এ লোকটি হালাল পদ্ধতির বিয়ে সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকতে হবে। আর সাক্ষী না পাওয়া যাওয়া সত্ত্বেও অপরাধী নিজেই যদি বিচারকের সম্মুখে নিজের অপরাধের অন্তত বারবার স্বীকারোক্তি করে তাতেও অপরাধ প্রমাণিত হবে ও সে অনুযায়ী দন্ড দেয়া হবে।
৩. ইসলাম কবুল করার পর দ্বীন-ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেও শাস্তিস্বরূপ তাকে হত্যা করা যাবে। মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে তার এ বিদ্রোহ যখন একটা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে, তখনই এ অবস্থা দেখা দেবে। ইসলাম তো কাউকেই জবরদস্তি বধ্য করে না ইসলাম কবুল করার জন্যে। কিন্তু দ্বীন-ইসলাম নিয়ে কেউ খেলা করেবে- তা কবুল করবে, আবার তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে, ইসলাম তা বরদাস্ত করতে পারে না। ইয়াহূদীরা এরূপ শরু করেছিল। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, তারা তাদের লোকদের বলতঃ ( আরবি*******************)
সকাল বেলা তোমরা ঈমান গ্রহণ কর সেই দ্বীনের প্রতি যা মুসলমানদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং দীনের শেষে তার প্রতি কুফরি কর। সম্ভবতঃ তা দেখে এ লোকেরা সে দ্বীন থেকে ফিরে যাবে। (সূরা আলে-ইমরানঃ ৭২)
কারো রক্তপাত হালাল ও মুবাহ হওয়ার জন্যে নবী করীম (সা) এ তিনটি ভিত্তিকেই সীমিত করে দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেনঃ ( আরবি*******************)
মুসলমানের রক্তপাত করা হালাল নয় এ তিনটি কারণ ছাড়া (১) জানের বদলে জান লওয়া (২) বিবাহিত ব্যক্তি জ্বিনাকার হলে এবং (৩) যে লোক দ্বীন-ইসলাম ত্যাগ করে মুসলিম জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে যায়।
কিন্তু এ তিনটি অপরাধের দণ্ড হিসেবে মুসলমানের রক্তপাত করা কেবল শসনকর্তা বা প্রশাসকের পক্ষেই জায়েয ও মুবাহ। ব্যক্তিদের পক্ষে নিজস্বভাবে এ দণ্ড দানের কাজ করা আদৌ জায়েয নয়। কেননা তা হলে শাসন-শৃঙ্খলা বলতে কিছুই থাকবে না। চরম অরাজগতা দেখা দেবে। সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তখন নিজস্বভাবে বিচারক ও দণ্ডমুণ্ডের মালিক হয়ে বসবে। ইচ্ছাপূর্বক নরহত্যার ক্ষেত্রে কিসাস করা ওয়াজিব। তবে ইসলাম নিহতের উত্তরাধিকারীদের এ অধিকার দিয়েছে যে, প্রশাসক কর্তৃপক্ষ উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের হাতে কিসাস গ্রহণ করতে পারে। তাতে তাদের মনের দুঃখ ক্ষোভ ও আক্রোশ মিটবে, প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা চারিতার্থ এবং আল্লাহর এ কথারও বাস্তবায়ন হবেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক অন্যায়ভাবে অকারণ নিহত হবে, তার উত্তরাধিকারীদের জন্যে আমরা (কিসাসুল ওয়ার) এ কর্তৃত্ব দিয়েছি, কিন্তু সে হত্যার কাজে সীমালংঘন করা যাবে না। সে অবশ্যই সাহায্য প্রাপ্ত হবে।
আত্মহত্যা
হত্যা অপরাধ পর্যায়ে যে বিধান এসেছে ব্যক্তির আত্মহত্যার ক্ষেত্রে তা পুরোপুরি প্রযোজ্য, যেমন অন্যকে হত্যা করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । কাজেই যে লোক আত্মহত্যা করবে তা যার সাহায্যেই করুক না কেন, সে এমন একটা নরহত্যা ঘটালো যা আল্লহ্ তা’আলা বিনা কারণে অন্যায়ভাবে হত্যা করাকে হারাম করে দিয়েছেন।
বস্তুত কোন মানুষের জীবনই তার নিজের মালিকানাভুক্ত নয়। কেননা সে নিজেকে সৃষ্টি করেনি। তার দেহের একটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা একটা জীব-কোষ পর্যন্তও সে নিজে বানায়নি। তার জীবন ও প্রাণ তার কাছে একটা আমানত, আল্লাহই তার কাছে এ আমানত অর্পণ করেছেন। অতএব তার ওপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই তার থাকতে পারে না। তাহলে সে তা হত্যা করতে পারে কিভাবে? এ জীবন থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে কোন নিজস্ব উদ্যোগ নিশ্চয়ই অপরাধ হবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করো না। কেননা আল্লাহ্ তো তোমাদের প্রতি অতীব দয়াবান। (সূরা আন-নিসাঃ ২৯)
ইসলাম চায়, মুসলমানরা জীবনের কঠোর কঠিন বাস্তবতার মুকাবিলা করায় অত্যন্ত সাহসী, দুর্বিনীতি ও অনমনীয় হবে। জীবন থেকে পলায়ন করার কোন কেন অধিকার কোন অবস্থায়ই কাউকে দেয়া হয়নি। বিপদ দেখলেই বা কোন সংকট ও সমস্যা দেখা দিলেই জীবনের এ পরিচ্ছেদটি খুলে ফেলে পালাতে চেষ্টা করবে, কোন আশায় ব্যর্থ মনোরথ হয়ে জীবনকেই অস্বীকার করবে, এ অধিকার কারো থাকতে পারে না। মুমিনকে তো জিহাদ-প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা করার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, অকর্মন্য হয়ে বসে থাকার জন্যে নয়। সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়াই তার কর্তব্য, পলায়ন বা পশ্চাদপসরণ তার জন্যে অশোভন। তার ঈমান ও চরিত্রই তাকে জীবনের ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যেতে ও নিজেকে সরিয়ে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তার কাছে এমন হাতিয়ার রয়েছে যা কখনও পুরাতন হয় না, সম্পদের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার রয়েছে যা কখনই নিঃশেষ হবে না। আর তা হচ্ছে ঈমানের হাতিয়ার, যা খুবই দৃঢ় ও মযবুত এবং সে ভাণ্ডার হচ্ছে অনমনীয় নৈতিকতার ভাণ্ডার।
যে লোক আত্মহত্যার এ জঘন্য অপরাধ করতে অগ্রসর হবে, সে আল্লাহ্ তা’আলার রহমত থেকে বঞ্চিত হবে ও জাহান্নামে পড়ে আল্লাহর তীব্র রোষ ও অসন্তোষের শিকার হবে বলে নবী করীম (সা) আগে থেকেই হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের পূর্বে চলে যাওয়া লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, সে আহত হয়ে গেল আর সেজন্যে সে ছটফট্ করতে শুরু করে দিল। এ অবস্থায় সে ছুরি হাতে নিয়ে নিজেই নিজের হাত কেটে ফেলল। তাতে এত বেশি রক্ত ঝরল যে, তাতে তার মৃত্যু সঙ্ঘটিত হল। আল্লাহ্ তা’আলা এ ব্যক্তি সম্পর্কে বলেছেনঃ আমার এ বান্দা নিজের ব্যাপারে খুব তাড়াহুড়া করে ফেলেছে। এ কারণে আমি তার প্রতি জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। (বুখারী, মুসলিম)
জখমের কষ্ট সয্য করতে না পেরে নিজের হত্যাকাণ্ড নিজেই ঘটিয়েছে বেলে তার ওপর জান্নাত হারাম হয়ে গেল। এ যখন অবস্থা, তখন যারা নিজেদের ব্যবসায় সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি, চাকুরীতে উন্নতি না হওয়া বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পারা, অথবা আশায় ভঙ্গ হওয়ার দরুন আত্মহত্যা করে তাদের ব্যাপার কত কঠিন এবং আল্লাহর কাছে কতটা অমার্জনীয় হবে, তা সহজেই বোধগম্য হতে পারে। দুর্বল মনোভাবের লোকদের এ হুঁশিয়ারী শুনে নেয়া কর্তব্য, যা নবী করীম (সা)-এর হাদীসে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক নিজেকে পর্বতের ওপর থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে চির দিনই পড়ে থাকবে- কখনই তা থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। যে লোক বিষ পান করে আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামের আগুনে চিরকালই নিজ হাতে বিষ পান করতে থাকবে। আর যে লোক কোন লৌহাস্ত্র দ্বারা আত্মহত্যা করল, সে জাহান্নামে চিরদিন চিরকাল ধরে লৌহের সেই জিনিসটি দ্বারা নিজেকে আঘাত দিতে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)
ধন-মালের মর্যাদা
মুসলমানের পক্ষে হালাল পথে ও পন্থায় ধন-মাল উপার্জন করা ও সঞ্চয় করা এবং শরীয়তসম্মত উপায়ে তার পরিমাণ বৃদ্ধি করা কোন দুষণীয় কাজ নয়। অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে যেখানে বলা হয়েছেঃ ধনী লোক আসমানী-সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না উষ্ট্র সুঁচের ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করবে, সেখানে ইসলাম ঘোঘণা করেছেঃ ( আরবি*******************)
ইসলাম হালাল ধন-মালের ওপর ব্যক্তির ব্যক্তিগত মালিকানা জায়েয বলে ঘোষণা করেছে। তাই শরীয়তী আইনের সমর্থনে ও নৈতিক পথ নির্ধারণের সাহায্যে তার ওপর সীমালংঘনকারীদের হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করেছে এবং অপহরণ, চুরি বা ডাকাতি করাকে হারাম করে দিয়েছে।
ধন-মালের এই মর্যাদা, রক্তের মর্যাদা ও মান সম্মানের মর্যাদার কথা নবী করীম (সা) এক সাথে উল্লেখ করেছেন এবং চৌর্যবৃত্তিকে ঈমানের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
চোর যখন চুরি করে তখন সে ঈমানদরি থাকে না।
আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
পুরুষ চোর ও মেয়েলোক চোরের হাত কেটে দাও তাদের কাজের প্রতিফলস্বরূপ এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রবর্তিত শাস্তিস্বরূপ। আর আল্লাহ্ দুর্জয়-শক্তিমান মহাবিজ্ঞানী। (সূরা মায়িদাঃ ৩৮)
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
কারো সন্তুষ্টি ভিত্তিক অনুমতি ছাড়া তার লাঠিখানি নেয়াও মুসলমানের জায়েয নয়।
মুসলমানের ধন-মাল মুসলমানের কাছে অত্যন্ত সম্মানার্হ এবং তা অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম, এ তীব্রতা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই নবী করীম (সা) এরূপ কথা বলেছেন। আল্লাহ্ তা’আলা আরও বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদারা, তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-মাল ভক্ষণ করো না। তবে তোমাদের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ের মুনাফা হলে তাতে কোন দোষ নেই। (সূরা আন-নিসাঃ ২৯)
ঘুষ হারাম
বাতিল উপায়ে ও অন্যায়ভাবে লোকদের ধনমাল ভক্ষণ করার একটি পস্থা হচ্ছে ‘ঘুষ’। কেননা প্রভাব ও কর্তত্বসম্পন্ন বা সাধারণ দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্যে ধনমাল দেয়া যে, সে তার পক্ষে রায় দেবে, তার প্রতিপক্ষের ওপর তাকে জিতিয়ে দেবে কিংবা তাকে কোন কাজ দেবে বা তার শত্রুর কাজকে বিলম্বিত করে দেবে প্রভৃতি উদ্দেশ্যে, তা-ই ঘুষ।
শাসক-প্রশাসক বা তার সহকারীদের জন্যে ঘুষের পথ অবলম্বন করাকে ইসলাম চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। তাদের জন্যে তা দেয়া হলে তা কবুল করা বা দাতা-গ্রহীতার মধ্যে মাধ্যম হওয়া- এ সবই হারাম। আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেলঃ ( আরবি*******************)
তোমরা তোমাদের ধনমাল পরস্পরে বাতিল পন্থায় ভক্ষণ করো না, না প্রশাসকদের সামনে তা এ উদ্দেশ্যে পেশ কর যে, লোকদের ধন-মালের একাংশ তোমরা নিজেরা ভক্ষণ করবে পরের হক নষ্ট করে এবং জেনে-শুনে।
নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
সরকারী ও রাষ্টীয় ব্যপারাদিতে যে ঘুষ দেয় এবং যে ঘুষ খায়- এ উভয় ব্যক্তির ওপরই আল্লাহর অভিশাপ। (আহমদ)
হযরত সওবান (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
ঘুষদাতা, ঘুষ গ্রহীতা এবং উভয়ের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনকারী- এ সকলেরই ওপর রাসূলে করীম (সা) অভিশাপ বর্ষণ করেছেন। (আহমদ, হাকেম)
ঘুষ গ্রহণকারী যদি কারো ওপর জুলুম করার উদ্দেশ্যে ঘুষ নেয়, তাহলে তার অপরাধের মাত্রা আরও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে যায়। আর যদি সুবিচার করার মানসে এ ঘুষ গ্রহণ করে, তাহলে সুবিচার করা তো তার দায়িত্ব, সেজন্যে কোনরূপ ধনমাল গ্রহণের কোন অধিকার থাকতে পারে না।
রাসূলে করীম (সা) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা)-কে ইয়াহূদীদের কাছে প্রেরণ করেন এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তাদের খেজুর ফসলের খারাজ কত টাকা হয় তার পরিমাণ তিনি নির্ধারণ করবেন। তখন তারা তাঁর সামনে ঘুষ স্বরূপ কিছু ধনমাল পেশ করে। হযরত ইবনে রাওয়াহা তা দেখে তাদের বললেন, তোমরা যে ঘুষ পেশ করেছ, তা তো হারাম। আমরা তা কিছুতেই খাব না। (ইমাম মালিক)
ইসলাম ঘুষ-রিশওয়াত হারাম করেছেন, এটা কোন আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। এতে যে যে লোক শরীক হয়, তাদের ব্যাপারেও কঠোরতা অবলম্বন করেছে, তাও বিচিত্র নয়। কেননা যে সমাজে এর ব্যাপকতা হয়, সে সমাজ জুলুমে জর্জরিত হতে বাধ্য এবং তার ধ্বংস অনিবার্য। যে লোক অন্যায়ভাবে প্রশাসন চালানো বা বিচারের রায় দিল কিংবা সত্য ও ন্যয়ভিত্তিক বিচার করতে প্রশাসন অস্বীকার করল। যে পিছনে তাকে অগ্রে এনে দিল এবং যে অগ্রবর্তী তাকে পশ্চাদবর্তী করে দিল, সে সমাজে কর্তব্যপরায়ণতার ভাবধারার পরিবর্তে স্বার্থপরতার ভাবধারা প্রবল হয়ে দেখা দেয়।
শাসক – প্রশাসকদের জন্যে উপটৌকন
ঘুষ- তা যে কোন রূপ যে কোন নামেই হোক, ইসলাম তা হারাম ঘোষণা করেছে। তাকে যদি হাদিয়া-তোহফা বা উপহার-উপটৌকন বলা হয় তবু তা হারামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে হালালের আওতার মধ্যে পড়বে না।
হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, রাসূলে করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোককে আমরা কোন কাজে নিযুক্ত করেছি ও তার বেতন নির্দিষ্ট করে ধার্য করে দিয়েছি, সে যদি তার পরও কিছু গ্রহন করে, তবে তা হবে খিয়ানত। (আবূ দাঊদ)
খলীফা উমর ইবনে আবদুল আজীজের সম্মুখে কিছু হাদিয়া পেশ করা হয়। তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন তাঁকে বলা হয়ঃ স্বয়ং রাসূলে করীম (সা) হাদিয়া-তোহফা গ্রহণ করতেন আর আপনি করছেন না? জবাবে তিনি বললেনঃ হ্যাঁ, তা তো তাঁর জন্যে ‘হাদিয়াই ছিল কিন্তু তা আমাদের জন্যে ঘুষ ছাড়া আর কিছু নয়।
রাসূলে করীম (সা) সাদকা যাকাত সংগ্রহের দায়িত্ব দিয়ে আজদ গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। সে যখন তাঁর কাছে ফিরে এল তখন কিছু ধনমাল নিজের হাতে রেখে দিয়ে বললঃ এ মাল আপনার আর এসব আমাকে উপটৌকন হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে নবী করীম (সা) খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমার এ কথাই যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি তোমার মা-বাবার ঘরে বসে থাকতে, তখন দেখা যেত, কে তোমাকে হাদিয়া দিচ্ছে ? পরে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
ব্যাপর কি, আমি তোমাদের মধ্য থেকে একজনকে সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করি। পরে সে বলেঃ প্রাপ্ত ধনমালের এ অংশ আপনার আর এ অংশ আমার জন্যে হাদিয়া বাবদ দেয়া? সে কেন তার মায়ের ঘরে বসে থাকেনি, তারপর যদি হাদিয়া দেয়া হতো তাহলে না হয় তার এ কথার যথার্থতা বোঝা যেত। যাঁর হাতে আমার জীবন তার শপথ, তোমাদের কেউ যদি নাহকভাবে কোন ধনমাল গ্রহণ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে তা আল্লাহর কাছে বহন করে নিয়ে উপস্থিত হতে হবে। তাই তোমরা কিয়ামতের দিন যেন নিজেদের কাঁধে করে উষ্ট্র, গরু-গাভী বা ছাগল নিয়ে আসতে বাধ্য না হও- এরূপ অবস্থায় যে, সে জন্তুটি চিৎকার করছে। পরে তিনি তাঁর দুই হস্ত ঊর্ধ্বে উত্তোলিত করলেন এতটা যে, তার দুহাতের বগলের সাদা অংশ দৃশ্যমান হয়ে উঠল। অতঃপর বললেনঃ হে আল্লাহ্! আমি কি কথা পৌঁছে দিয়েছি?
ইমাম গাযযালী বলেছেনঃ ঘুষের ব্যাপারে এসব কঠোরতা ও তীব্রতা প্রচণ্ডতা দেখে বলতে হয় যে, বিচারক প্রশাসক কিংবা তাদের মতো দায়ীত্বশীল ব্যক্তিদের উচিত তাদের মা-বাবার ঘরে বসে থাকা। তাদের পদচ্যুত করে দেয়ার পর তাদের মায়ের ঘরে থাকা অবস্থায় তাদের যদি ‘হাদিয়া-তোহফ’ দেয়া হয়, তাহলে তা গ্রহণ করা তাদের জন্যে জায়েয হতে পারে, পদে অভিষিক্ত থাকা অবস্থায়ও। আর যে সম্পর্কে জানতে পারবে যে, তা তার পদে অভিষিক্ত থাকার কারণেই দেয়া হয়েছে, তা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ হারাম। আর বন্ধু-বান্ধবদের দেয়া হাদিয়া-তোহফা যদি পদচুত হওয়ার পরও দিত বলে জানা না যায়, তাহলে তাতে সন্দেহ রয়েছে। কাজেই তা পরিহার করা কর্তব্য। ( আরবি*******************)
জুলুম বন্ধের জন্যে ঘুষ দেয়া
অবস্থা যদি এমন হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজের ন্যায্য হকও ঘুষ না দিলে পাওয়ার কোন উপায় নেই কিংবা এমন জুলুমের মধ্যে পড়ে গেছে যে, ঘুষ না দিলে তা থেকে নিষ্কৃতি কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়, তাহলে তার ধৈর্য ধারণ ও সবর ইখতিয়ার করা উচিত, যতক্ষণ না আল্লাহই তার জন্যে হক পাওয়া ও জুলুম মুক্তির কোন উত্তম পথ ও পন্থা করে দেন।
এ কারণে ঘুষের পথে অগ্রসর হলে ঘুষ গ্রহণকারীই গুনাগার হবে। এরূপ অবস্থায় ঘুষদাতা গুনাহগার হবে না, যদি অন্যান্য হালাল সব পথই যাচাই করে দেখে ফল না পেয়ে শেষ উপায় হিসেবে তা অবলম্বন করে ও সেই সাথে সে যদি শুধু নিজের ওপর থেকে জুলুম বিদুরণ ও ন্যায্য হক পাওয়া এবং অন্যান্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে থাকতে পারে।
কোন কোন আলিম এই মতের সমর্থন দলিল স্বরূপ উল্লেখ করেছেন সেসব হাদীস, যাতে উল্লেখিত হয়েছে যে, একদল লোক রাসূলে করীম (সা)-কে জড়িয়ে ধরত সাদকা পাওয়ার জন্যে। তখন ওরা কিছু পাওয়ার ন্যায় অধিকারী না হওয়া সত্ত্বেও তিনি এদের কিছু দিয়ে দিতেন। হযরত উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম (সা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তোমাদের কেউ কেউ আমার কাছ থেকে সাদকার মাল নিয়ে বগলে চেপে বের হয়ে যায় অথচ তা তার জন্যে আগুন। হযরত উমর (রা) বললেনঃ আপনি নিজেই যখন জানেন যে, তা তার জন্যে আগুন, তখন আপনি তাকে দেন কেন?
জবাবে বললেনঃ আমি কি করব? ওরা এমনভাবে চাইতে থাকে ও ধরে বসে যে, ওদের ছাড়ানই যায় না। আর আল্লাহ্ মহান মহিম চান না যে, আমি কার্পণ্য করি।
বারবার ও চেপে ধরে চাওয়ার দরুন রাসূলে করীম (সা) যখন প্রার্থীকে কিছু না কিছু ধন-মাল দিতেন, একথা জেনেও দিতেন যে, তা তার জন্যে আগুন, তাহলে জুলুম বন্ধ করা ও নিজের ন্যায্য হক ও পাওনা আদায়ের প্রয়োজনে ঘুষ দেয়া জায়েয হবে না কেন?
নিজেদের ধন-মাল অপব্যয় করা
প্রত্যেকের পক্ষে অন্য লোকের ধন-মালের যেমন একটা মর্যাদা আছে, তাতে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে কোনরূপ সীমালংঘনমূলক হস্তক্ষেপ যেমন হারাম, অনুরূপভাবে প্রত্যেকের কাছে তার নিজের ধন-মালেরও একটা মর্যাদা রয়েছে। সেজন্যে সে ধন-মাল অপচয় অপব্যয় করা, নষ্ট করা, ধ্বংস করা, কিংবা ডান হাতে বাম হাতে ছিটানও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
তা এজন্যে যে, ব্যক্তিগণের ধন-মালে জাতি ও সমাজ-সমষ্টির হক রয়েছে। সব মালিকের উর্ধ্বে তার মালিকানা অধিকার অবশ্যিই স্বীকৃতব্য। এ করণেই যে নির্বোধ ধন-মালিক স্বীয় ধন-মাল বিনষ্ট করে, সমাজের অধিকার ও কর্তৃত্ব রয়েছে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার। কেননা সে ধন-মালে সমাজ সমষ্টিরও অংশ কয়েছে। এ পর্যায়ে কুরআন মজীদ বলেছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা নির্বোধ লোকদেরকে দিও না তোমাদের ধন-মাল, যাকে আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের জন্যে উপজীব্য বা প্রতিষ্ঠার বাহন বানিয়েছেন, আর তাদের রিযক দাও তা থেকে এবং তাদের জন্যে ভাল ও উত্তম প্রচলিত কথা বল।
এ আয়াতে আল্লাহ্ তা’আলা মূলত সম্বোধন করেছেন সমাজ-সমষ্টিকেঃ তোমরা দিও না তোমাদের ধন-মাল বলে। যদিও বাহ্যত এ ধন-মাল ব্যক্তিদের নিজ মালিকানার। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির ধন-মাল আসলে গোটা সমাজ সমষ্টিরই জাতীয় সম্পদ।
বস্তুত ইসলাম সুবিচার, ইনসাফ ও ভারসাম্যতার দ্বীন। আর মুসলিম উম্মত হচ্ছে মধ্যম অর্থাৎ মধ্যম নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত উম্মত। মুসলমানের আদর্শ হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে সুবিচার ও ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠা। এ কারণেই আল্লাহ্ তা’আলা মুমিনদের স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছেন ধন-মালের অপব্যয় ও অপচয় করতে যেমন নিষেধ করেছেন কার্পণ্য ও বখিলি করতে। বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেকবার মসজিদে উপস্থিতিকালে তোমাদের সৌন্দর্য-অলংকার গ্রহণ কর। আর তোমরা খাও, পান কর, কিন্তু অপব্যয়-অপচয় করবে না। কেননা আল্লাহ্ অপব্যয় অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না।
আল্লাহর হারাম করে দেয়া কাজে ধন-সম্পদ ব্যয় করা হলেও অপচয় অপব্যয়ই হবে, যেমন মদ্যপান, বিবেক-বুদ্ধি আচ্ছন্নকারী দ্রব্যাদি, স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রাদি ক্রয় ইত্যাদি এ ক্ষেত্রে ব্যয় করা ধন-মালের পরিমান কম হোক, বেশি হোক, সবই নিষিদ্ধ।
ধন-মাল নিজের জন্যে বা অন্য লোকদের জন্যে অপব্যয় কারারও কোন অনুমতি নেই ইসলামে। নবী করীম (সা) ধন-মাল বিনষ্ট করতে স্পষ্ট ভাষয় নিষেধ করেছেন। (বুখারী)
অপ্রয়োজনীয় কাজে খুব বেশি অর্থব্যয় ও অপচয় অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ অপব্যয়-অপচয় মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দেয়। শেষ পর্যন্ত নিজের কাছে এমন পরিমাণ সম্পদও থাকে না, যদ্বারা নিজের মৌলিক প্রয়োজনটুকুও পূরণ করা যেতে পারে।
কুরআন মজীদের আয়াতঃ ( আরবি*******************)
লোকেরা তেমার কাছে- হে নবী- জিজ্ঞেস করে, তারা কি ব্যয় করবে? বল- আল-আফওয়া। (সূরা বাকারাঃ ২১৯)
এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী লিখেছেনঃ
আল্লাহ্ তা’আলা লোকদের অর্থ সম্পদ ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। উক্ত আয়াতে নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলেছেনঃ আত্মীয়দের তাদের হক দাও, মিসকীন ও মুসাফিরকেও এবং বেহুদা অর্থ ব্যয় করবে না। বেহুদা ব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই পর্যায়ে গণ্য। (আল-ইমরান-২৬) এবং বলেছেনঃ তুমি তোমরা হস্ত নিজের গলার সঙ্গে বেঁধে রেখো না, আর তাকে একেবারে খুলেও দিওনা। (আল-ইমরান-২৯) বলেছেনঃ যারা ব্যয় করে, কিন্তু না অপব্যয় করে, না সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয় (আল-ফুরকান-৬৭) আর নবী করীম (সা) বলেছেনঃ তোমাদের কারো কাছে ধন-মাল থাকলে তার ব্যয় শুরু করবে নিজের থেকে। পরে যারা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্বাধীন লোক তাদের জন্যে আর তাদের পরে অন্যান্যদের জন্যে ব্যয় করবে। (মুসলিম) বলেছেনঃ সর্বোত্তম সাদকা হচ্ছে তা যা করা হলে ব্যক্তিকে সচ্ছল থাকতে দেয়। (তাবারানী) হযরত জাবীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেনঃ আমরা রাসূলে করীম (সা)-এর দরবরে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি ডিমের সমান পরিমাণ স্বর্ণ নিয়ে তাথায় উপস্থিত হলো এবং বললঃ এটা দান হিসেবে কবুল করুন। আল্লাহর শপথ। আমার কাছে এ ছাড়া আর কিছু নেই। নবী করীম (সা) তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। কিন্তু সে ব্যক্তি আবার সম্মুখে উপস্থিত হলো। তখন তিনি বললেনঃ দাও। খুব অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ সহকারে তা গ্রহণ করে সেটি তার দিকে এমনভাবে নিক্ষেপ করলেন যে, কারো দেহে লেগে গেলে সে আঘাত পেত। পরে বললেনঃ তোমাদের এক-একজন তার সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে আসে, পরে সে লোকদের সামনে হস্ত প্রসারিত করে ভিক্ষার জন্যে বসে। দান সাদকা তো তা-ই যা সচ্ছল অবস্থার ব্যক্তির সচ্ছলতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে করা হবে। এটা নিয়ে নাও, আমার কোন প্রয়োজন নেই তাতে। (আবূ দাঊদ, হাকেম) নবী করীম (সা) তাঁর ঘরের লোকদের জন্যে এক বছরের খাবার জমা করে রাখতেন। (বুখারী)। বুদ্ধিমানরা বলেন, বেশি বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজনের চাইতেও কম- এ দুই প্রান্তিকের মধ্যবর্তী নীতিই উত্তম। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করা বেহুদা খরচ। আর কম ব্যয় করা কার্পণ্য, বখিলি। ভারসাম্যপূর্ণ নীতিই সর্বোত্তম আর ‘বল আল-আফওয়া’ বলে তা-ই বলেছেন আল্লাহ্ তা’আলা। এ সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় তত্ত্ব অনুধাবন ও সংরক্ষণের ওপরই মুহাম্মাদী শরীয়ত নির্ভরশীল। কেননা ইয়াহূদী শরীয়ত কৃচ্ছতা কঠোরতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর খ্রিস্টানদের ধর্ম-বিধান পরম ঔদার্য ও ঢিলা নীতির অনুসারী। এ সব ব্যাপারে মুহাম্মাদী শরীয়তই মধ্যম নীতির ধারক ও প্রবর্তক। এ কারণে তা অপর শরীয়তগুলোর তুলনায় অতীব পূর্ণাঙ্গ ও পূর্ণ পরিণত বিধান (তাফসীর, ফখরুদ্দীন রাযী, ৬ষ্ঠ খণ্ড)
অমুসলিমের সাথে সম্পর্ক
দ্বীন-ইমলামের বিরুদ্ধবাদীদের সাথে আচার-আচরণ অবলম্বনের ব্যাপারে ইসলামের নীতি ও আদর্শকে সংক্ষেপে বলতে হলে কুরআন মজীদের দুটি আয়াতের উল্লেখই যথেষ্ট। এ আয়াত দুটি এ পর্যাযে ব্যাপক সংবিধান হওয়ার উপযুক্ত। তা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহ্ তা’আলা তোমাদের সেই লোকদের সাথে ভাল ও সুবিচারমূলক আচরণ গ্রহণ করতে নিষেধ করছেন না, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেনি। আল্লাহ্ তো সুবিচারকারীদের পছন্দ করেন। তিনি তোমাদের বিরত রাখছেন শুধু এ থেকে যে, তোমরা বন্ধুতা করবে না তাদের সাথে, যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে ও তোমাদের ঘর থেকে তোমাদের বহিষ্কৃত করেছে এবং তোমাদের বহিষ্কৃতকরণে পরস্পরের সাথে সহযোগিতা করেছে। এ লোকদের সাথে যারা বন্ধুতা করবে, তারাই জালিম।
যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ বা কোনরূপ শত্রুতা নেই, যারা দ্বীনের ব্যাপার নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি ও তাদের ঘর থেকে বহিষ্কৃতও করেনি, প্রথমোক্ত আয়াতে তাদের প্রতি শুধু সুবিচার ও ন্যায়পরতা গ্রহণের উৎসাহ দেয়া হয়নি; বরং তাদের প্রতি ভাল ও শুভ আচরণ করণ ও তাদের কল্যাণ সাধনের জন্যে উৎসাহিত করা হয়েছে। আয়াতে ব্যবহৃত ( আরবি*******************) শব্দটি কল্যাণ ও মঙ্গলের ব্যাপক অর্থবোধক, সুবিচার ও ন্যায়পরতারও ঊর্ধ্বে তা, মানবীয় অধিকারের সর্বোচ্চ মান বুজে থাকেন মুমলমানরা এই শব্দ থেকে। যেমন ( আরবি*******************) বলতে পিতামাতার অধিকার আদায়ে পূর্ণ মাত্রায় কল্যাণ সাধন বুঝে থাকে। এই পর্যায়ে কুরআনের কথা হলোঃ ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সুবিচার ও ন্যায়পরতাকারীদের ভালবাসেল।’ আর ঈমানদার লোক মাত্রই সব সময় সে কাজ করতেই অধিক ভালবাসে, তৎপর হয়, যা আল্লাহ্ পছন্দ করেন- ভালবাসেন। এতো সর্বজনবিদিত।
‘আল্লাহ্ তোমাদের নিষেধ করছেন না’ কথায় ভাল আচরণ গ্রহণ ইপ্সিত হওয়াটার বিপরীত কিছু বোঝায় না। কথা বলার এই ধরনটি গ্রহণ করা হয়েছে এজন্যে যে, মুসলমানরা হয়ত মনে করতে পারেন যে, দ্বীনের বিরুদ্ধপন্থীরা বুঝি ভাল আচরন ও ন্যায়পরতা পাওয়ার অধিকারী নয়। এই ভুল ধারনা দূর করার উদ্দেশ্রে স্পষ্ট করে বলা হলো যে, আল্লাহ্ বিরোধীদের সাধে ভাল আচরণ গ্রহণ, বন্ধুতা ও সুবিচার করা থেকে বিরত রাখেন না- তা করতে নিষেধ করছেন না। তিনি শুধু সেসব লোকদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করেন যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন গ্রহণ করছে।
এখানকার এ কথার ধরন ঠিক অপর একটি আয়াতের মতোই। আয়াতটি হচ্ছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক হজ্জ্ব করল কিংবা উমরা করল, তাদের ওপর কোন দোষ নেই যদি তারা সাফা-মারওয়ার তওয়াফ করে।
কথা বলার এ ভঙ্গির কারণ হচ্ছে কতিপয় লোক জাহিলিয়াত আমলের নিদর্শনাবলীর কারণে ইসলামের আমলেও পর্বতদ্বয়ের তওয়াফ করতে দ্বিধাবোধ করেছিলেন, সেই দ্বিধা-সংকোচ দূর করাই প্রথম লক্ষ্য। ‘দোষ নেই’ বলা হলো দ্বিধা দূর করার উদ্দেশ্যে, যদিও এ দুটো পর্বতের তাওয়াফ করা ওয়াজিব এবং হজ্জের জরুরী অনুষ্ঠানের মধ্যে গণ্য।
আহলি কিতাবের প্রতি বিশেষ সুবিধা দান
ইসলাম যখন দ্বীন-ইসলামের বিরোধীদের সাথেই সর্বোচ্চ মানের ভাল ব্যবহার ও ন্যায়পরতা গ্রহণ থেকে নিষেধ করে না, মূর্তি পূজারী মুশরিক হলেও নয়- যেমন প্রথমে উদ্ধৃত আয়াতদ্বয়ে বলা হয়েছে, যা আরবের মুশরিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছিল। তখন আহলি কিতাব- ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি যে ইসলাম বিশেষ সুবিধাদি দান করবে- তারা ইসলামী দেশের অধিবাসী হোক কি তার বাইরে- তা তো অতি স্বাভাবিক।
কুরআন মজীদে এই ইয়াহূদী খ্রিস্টানদের সম্বোধন করা হয়েছে আহলি ‘কিতাব’- সেই লোক যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে- বলে। এ থেকে বোঝাতে চেয়েছে যে, আসলে এরা আল্লাহর নাযিল করা দ্বীনের ধারক লোক। অতএব মুসলমান ও তাদের মাঝে নিকটাত্মীয়তা সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা’আলা তাঁর নবী-রাসূলগণকে যে মৌল দ্বীন ও বিধান সহ পাঠিয়েছেন, আসলে তা এক ও অভিন্ন। একটি আয়াত উল্লেখ্যঃ ( আরবি*******************)
তিনি তোমাদের জন্যে সেই দ্বীনই সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার নির্দেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন, আর যা আমরা তোমার প্রতি ওহী করে পাঠিয়েছি, আর তার পথ-নির্দেশ করেছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসকে এই বলে যে, তোমরা সকলে এই দ্বীনকে কায়েম কর এবং এ ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না। (সূরা শূরাঃ ১৩)
মুসলমানদের তো নির্দেশ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নাযিল করা সমস্ত কিতাবের প্রতি ঈমান গ্রহণের জন্যে। তাই সব নবী-রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ মুসলমানের কর্তব্য। এছাড়া তাদের ঈমান সত্য ও যথার্থই হতে পারে না। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা বলঃ আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি ও যা নাযিল হয়েছে আমাদের প্রতি, আর যা নাযিল হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও বংশধরদের প্রতি, আর যা দেয়া হয়েছে মূসা, ঈসা ও আল্লাহর প্রেরিত নবীগণের প্রতি- আমরা তাদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করি না, আমরা তো সেই এক আল্লাহরই অনুগত। (সূরা বাকারাঃ ১৩৬)
আহলি কিতাবের লোকেরা যখন কুরআন পাঠ করে তখন তারা দেখতে পায়, কুরআনে তাদের ধর্ম গ্রন্থের ও নবী-রাসূলগণের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে। অতএব মুসলমানরা যখন আহলি কিতাবের লোকদের সাথে তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হবে, তখন অবশ্যই এমন সব কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকবে যা পারস্পরিক ঘৃণা ও বিদ্বেষ বৃদ্ধি করে। বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
আহলি কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না- তবে উত্তম পন্থায়, তাদের ছাড়া, যারা ওদের মধ্যে জালিম। আর বল, আমরা ঈমান এনেছি সেই জিনেসের প্রতি, যা আমাদের প্রতি নাযিল করা হয়েছে, সে জিনিসেরও যা তোমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে। আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ এক ও অভিন্ন। আর আমরা তাঁরই অনুগত- আত্মসমর্পিত। (সূরা আনকাবুতঃ ৪৬)
আহলি কিতাবের সাথে পানাহার করা ও তাদের যবেহ করা জন্তু খাওয়া এবং তাদের মেয়ে বিয়ে করা- যদিও বিয়েটা পরম প্রীতি ও ভালবাসার লীলাকেন্দ্র- জায়েয করে দিয়ে ইসলাম যে উদার নীতি অবলম্বন করেছে তার বিস্তারিত আলোচনা আমরা করেছি। এ পর্যায়ে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ্যঃ ( আরবি*******************)
আহলি কিতাবের খাবার তোমাদের জন্যে হালাল, তোমাদের খাবারও হালাল তাদের জন্যে। আর সুরক্ষিতা পবিত্রা নারী মুসলমানদের ও তোমাদের পূর্বে কিতাব পাওয়া লোকদের- তাও হালাল। (সূরা মায়িদাঃ ৫)
আহলি কিতাবের ব্যাপারে এ হচ্ছে ইসলামের সাধারণ নীতি। তবে খ্রিস্টানদের প্রতি একটা বিশেষ ধরনের নীতি অবলম্বিত হয়েছে। কুরআন তো তাদের সম্পর্কে বলেছে, তারা মুসলমানদের হৃদয়ের নিবিড় নৈকট্যে অবস্থিত। বলেছেঃ ( আরবি*******************)
তোমরা ঈমানদার লোকদের বন্ধুত্বে নিকটবর্তী পাবে সেই লোকদের, যারা বলেছেঃ আমরা নাসারা-খ্রিস্টান। তা এজন্যে যে, তাদের মধ্যে বহু পণ্ডিত বিদ্বান রয়েছে, আর তারা অহংকার করে না। (সূরা মায়িদাঃ ৮২)
যিম্মি
উপরে যেসব উপদেশ উদ্ধৃত হয়েছে, তা সকল আহলি কিতাবকেই শামিল করে নেয়। তারা যেখানেই বসবাস করুক, কারো ব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নেই। তবে ইসলামী রাষ্ট্রের ছায়াতলে যে সব অমুসলিম বাস করে, তাদের জন্যে ইসলাম বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মুসলিম পরিভাষায় তাদের বলা হয় ‘যিম্মী’। ‘যিম্মী’ শব্দের অর্থ ‘চুক্তি’- ওয়াদা। এ শব্দটি জানিয়ে দেয় যে, এদের জন্যে আল্লাহর এবং তার রাসূলের একটা ওয়াদা বয়েছে। মুসলিম জামায়াত সে ওয়াদা পালনে বাধ্য। আর তা হচ্ছে এই যে, তারা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত- জীবন যাপন করতে পারবে।
আধুনিক ব্যাখ্যায় এরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী- নাগরিক। প্রথম দিন থেকেই মুসলিম সমাজ এ সময় পর্যন্ত এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের জন্যে যে অধিকার, অমুসলিমদের জন্যেও সেই অধিকার। তাদের যা দেয়-দায়িত্ব, এদেরও দায়-দায়িত্ব তা-ই। তবে শুধু আকিদা, বিশ্বাস ও দ্বীন-সংক্রান্ত ব্যাপারাদিতে তাদের সাথে কোন মিল বা সামঞ্জস্য নেই। কেননা ইসলাম তাদেরকে তাদের দ্বীন ধর্মের ওপর বহাল থাকার পূর্ণ আযাদী দিয়েছেন।
যিম্মীদের সম্পর্কে নবী করীম (সা) খুব কড়া ভাষায় মুসলমানদের নসীহত করেছেন এবং সেই নসীহতের বিরোধিতা বা লংঘন হলে আল্লাহর অসন্তোষ অবধারিত বলে জানিয়েছেন। হাদীসে নবী করীমের কথা উদ্ধৃত হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট বা জ্বালা-যন্ত্রণা দিল, সে যেন আমাকে কষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণা দিল। আর যে লোক আমাকে জ্বালা-যন্ত্রণা ও কষ্ট দিল, সে মহান আল্লাহকে কষ্ট দিল। (তাবারানী ফিল আওসত)
( আরবি*******************) যে লোক কোন যিম্মীকে কষ্ট দিল, আমি তার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী। আর আমি যার বিরুদ্ধে মামলা দায়েরকারী, তার বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি মামলা লড়ব। (আল-খাতিব)
( আরবি*******************) যে লোক কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির ওপর জুলুম করবে কিংবা তার হক নষ্ট করবে অথবা শক্তি-সামর্থ্যের অধিক বোঝা তার ওপর চাপাবে কিংবা তার ইচ্ছা ও অনুমতি ছাড়া তার কোন জিনিস নিয়ে নেবে, কিয়ামতের দিন আমি তার বিরুদ্ধে মামলা লড়ব। (আবূ-দাঊদ)
রাসূলে করীম (সা)-এর খলীফাগণ এসব অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার আদায় ও মর্যাদা রক্ষায় সব সময় সচেতন-সতর্ক থাকতেন। ইসলামের ফিকাহবিদগণ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও এ সব অধিকার ও মর্যাদার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।
মালিকী মাযহাবের ফিকাহবিদ শিহাবুদ্দীন আল-কিরাফী বলেছেনঃ
যিম্মীদের সাথে কৃত চুক্তি আমাদের উপর তাদের কতিপয় আধিকার ওয়াজিব করে দিয়েছে। কেননা তারা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে আমাদের সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার অধীন এসে গেছে। আল্লাহ্, রাসূল ও দ্বীন-ইসলাম তাদের নিরাপত্তা দিয়েছে। কাজেই যে লোক তাদের ওপর কোন রকমের বাড়াবাড়ি করবে সামান্য মাত্রায় হলেও তা আল্লাহ্ তাঁর রাসূল এবং দ্বীন-ইসলামের দেয়া নিরাপত্তা বিনষ্ট করার অপরাধে অপরাধী হবে। তাদের খারাপ কথা বলা, তাদের মধ্যে থেকে কারো গীবত করা বা তাদের কোনরূপ কষ্ট জ্বালা দেয়া অথবা এ ধরনের কাজে সহযোগিতা করা ইত্যাদি সবই এ নিরাপত্তা বিনষ্টের দিক।
যাহেরী মাযহাবের ফিকাহবিদ ইবনে হাজম বলেছেনঃ
যেসব লোক যিম্মী, তাদের ওপর যদি কেউ আক্রমণ করতে আসে, তাহলে তাদের পক্ষ হয়ে সশস্ত্র যুদ্ধ করার জন্যে অগ্রসর হওয়া ও তাদের জন্যে মৃত্যুবরণ করা আমাদের কর্তব্য। তাহলেই আমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের নিরাপত্তা দেয়া লোকদের সংরক্ষণ করতে পারব। কেননা এ রূপ অবস্থায় তাদের অসহায় ও সহজ শিকার হতে দেয়া নিরাপত্তা দেয়ার দায়িত্ব পালনের পক্ষে বড্ড ক্ষতিকারক হবে।
অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের রূপ
প্রশ্ন উঠতে পারে, অমুসলিমদের সাথে ভাল ব্যবহার ও সুসম্পর্ক স্থাপন কি করে সম্ভব, যখন কুরআন নিজেই কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করতে ও তাদের নিজেদের মিত্র ও বন্ধু বানাতে নিষেধ করছে?
যেমন কুরআনে বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করো না। ওরাই পরস্পরের বন্ধু! অতএব তোমাদের যে লোকই ওদের বন্ধু-পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করবে, সে তাদের মধ্যে গণ্য হবে। নিশ্চেয়ই আল্লাহ্ জালিমদের হেদায়েত করেন না। তুমি লক্ষ্য করছ, যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তারা তাদেরা মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে।
এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, এসব আয়াত সাধারণভাবে প্রযোজ্য নয়। আর সব ইয়াহূদী-খ্রিস্টান-কাফির একই রকমের নয়। যদি তা-ই মনে করা হয়, তাহলে এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াত ও দলিল- যাতে যে কোন ধর্মাবলম্বী লোকদের সাথে কল্যাণকামী ও সদাচারী লোকদের সাথে ভাল আচরণ ও সুসম্পর্ক রক্ষার বৈধতা ঘোষিত হয়েছে- এর সাথে বৈপরীত্য ঘটবে। আহলি কিতাবের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের মেয়ে বিয়ে কারার অনুমতিও তো রয়েছে। অথচ বিয়ে সম্পর্কে আল্লাহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
তিনি তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা ও দয়া সহানুভূতি সম্পন্ন সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন।
আর খ্রিস্টানদের সম্পর্কে বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যারা বলেছেঃ আমরা নাসারা-খ্রিস্টান- ঈমানদার লোকদের সাথে বন্ধুতার ব্যাপারে তাদেরকে তুমি নিকটবর্তী পাবে।
বস্তুত যেসব আহলি কিতাবের সাথে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন নিষেধ রয়েছে তা প্রযোজ্য হচ্ছে দ্বীন-ইসলামে দুশমন ও মুসলমানের সাথে যুদ্ধ্যমান লোকদের ব্যাপারে। এ লোকদের সাহায্য করা, পৃষ্ঠপোষকতা করা- তাদের গোপন তথ্য জানান ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে তাদের মিত্র বানিয়ে তাদের অতি কাছে নিয়ে আসা কোন মুসলমানের পক্ষেই আদৌ জায়েয নয়। অন্যান্য আয়াতে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। একটি আয়াত উল্লেখ করা যায়ঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা তোমাদের ছাড়া অন্যদের অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে না। তারা তোমাদের ক্ষতি সাধন করতে কোন ত্রুটিই রাখবে না। যা তোমাদের জন্যে কষ্টদায়ক, ক্ষতিকর, বিপদজনক তা-ই তাদের মনপুতঃ তাদের শত্রুতা হিংসা-ক্রোধ তাদের মুক থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। আর যা কিছু তারা নিজেদের মনে লুকিয়ে রেখেছে, তা তো তার চেয়েও অনেক বড়, ভীষণ। আমরা তোমাদের জন্যে আইন বিধান স্পষ্ট করে বলেছিলাম। এখন তোমরা যদি বুঝে শুনে কাজ কর। তোমরা সতর্ক থাকবে, তোমরা ওদের খুব ভালবাস; কিন্তু ওরা তোমাদের আদৌ পছন্দ করে না।
যাদের সাথে বন্ধুতার সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ, উপরিউক্ত আয়াতে তাদের পরিচয় স্পষ্ট ভাষায় দিয়ে দেয়া হয়েছে। আসলে ওরা মুসলমানদের প্রতি চরম বক্রতা পোষণ করে অন্তরে লুকিয়ে রাখে। তা সত্ত্বেও তাদের মুখ থেকে তার নিদর্শনাদি প্রকাশ হয়ে পড়ে।
আল্লহ্ তা’আলা বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যারা আল্লাহ্ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার, তাদের তুমি কখনও এমন লোকদের প্রতি বন্ধুতা পোষণ করতে দেখবে না, যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষাণ করে। এরা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্তাতি বা বংশের লোক হলেও। (সূরা মুজাদিলাঃ ২২)
বস্তুত আল্লাহ্ ও তার রাসূলের সাথে শত্রুতা পোষণ নিছক কুফরি নয়। তা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে আগ্রাসন।
আল্লাহ্ বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু- পৃষ্ঠপোষকরূপে গ্রহণ করো না- বানিও না। তোমরা তো ওদের প্রতি পরম বন্ধুতা-প্রীতি দেখাও। কিন্তু তোমাদের কাছে যে মহাসত্য এসেছে, ওরা তার প্রতি কুফরি করেছে। ওরা রাসূলকে এবং তোমাদের বহিষ্কৃত করে শুধু এই অপরাধে যে, তোমরা ঈমানদার তোমাদের রব্ব আল্লাহর প্রতি।
মক্কার যেসব মুশরিক আল্লাহ্ ও রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল এবং মুসলমানদেরকে তারা তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত করেছিল। শুধু মাত্র একটুকু অপরাধে যে, তাঁরা বলেছিলেন, আমাদের রব্ব হচ্ছেন আল্লাহ্। উপরিউক্ত আয়াত তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সাথে বন্ধুতা-ভালবাসা স্থাপন করা মুসলমানদের জন্যে কখনোই জায়েয নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও ওদের অন্তরের পরিষ্কার পরিছন্ন হওয়ার ব্যাপারে কুরআন চূড়ান্তভাবে নৈরাশ্যের কথা বলেনি। বরং ওদের এ মন-মানসিকতারও যে পরিবর্তন পতে পারে এবং এখনকার মতো শত্রুতার মনোভাব একদির না-ও থাকতে পারে, এ আশাবাদই প্রকাশ করা হয়েছে। উপরোদ্ধৃত আয়াতের পরই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
এটা খুব একটা অসম্ভব বা বিস্ময়কর নয় যে, আল্লাহ্ তোমাদের ও যাদের প্রতি তোমরা শত্রুতা পোষণ কর- যাদের শত্রুতার তোমরা আশংকা কর, তাদের মধ্যে বন্ধুতা-প্রীতির সৃষ্টি করে দেবেন। আল্লহ্ তো মহাশক্তিমান। আর আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (সূরা মুমতাহিনাঃ ৭)
এটা কুরআনের সতর্ক বাণী। এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শত্রুতা পোষণ ও ঝগড়া-বিবাদের একটা সীমা নির্ধারণ একান্তই প্রয়োজনীয়। এর আলোকে বিচার করলে শত্রুতার মাত্রা তো অনেক হ্রাস পেয়ে যায়। হাদীসেও তাই বলা হয়েছেঃ ( আরবি*******************)
তোমার শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ ভাবাটা খানিকটা কম করে রাখবে। কেননা সে তো একদিন তোমার একজন বন্ধুও হয়ে যেতে পারে।
শত্রু পক্ষ যখন খুব শক্তিশালী হয় যে, লোকেরা তাদের প্রতি আশাও পোষণ করে, তাদের ভয়ও করে, তাহলে এরূপ অবস্থায় তাদের সাথে বন্ধুতা-প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন অধিকতর বেশি ও তীব্রভাবে হারাম হয়ে যায়। কেননা এরূপ অবস্থায় মুনাফিক ও অন্তরের রোগীরাই তাদের সাথে বন্ধুতা করার ব্যাপারে খুব অগ্রসর থাকবে। তাদের সাথে একটা গোপন সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, যেন কাল তা তাদের ফায়াদা দিতে পারে। যেমন আল্লাহ্ বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
যাদের অন্তরে রোগ, ওদের দেখবে তারা সব সময় সেই লোকদের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করে- তৎপরতা দেখায়। বলে- আমরা ভয় পাই। আমরা বিপদের আবর্তে পরে না যাই। কিন্তু খুব সম্ভব আল্লাহ্ তোমাদের জয়দান করবেন কিংবা নিজের কাছ থেকে অন্য কিছু প্রকাশ করে দেবেন, তখন এরা নিজেদের অন্তরে যা কিছু লুকিয়ে রেখেছে তাতে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। (সূরা মায়িদাঃ ৫২) ( আরবি*******************)
মুনাফিকদের সুসংবাদ দও যে, তাদের জন্যে পীড়াদায়ক আযাব নির্দিষ্ট রয়েছে। ওরা তারাই, যারা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের সাথে বন্ধুতা করে- তাদের পৃষ্ঠপোষক বানায়। ওরা কি তাদের কাছে ইজ্জত বা শক্তি-ক্ষমতা পেতে চায়? আসলে সমস্ত ইজ্জত-শক্তি ক্ষমতা-আধিপত্য সবই আল্লাহর। (সূরা আন-নিসাঃ ১৩৮-১৩৯)
অমুসলমানের কাছে সাহায্য চাওয়া
মুসলিম অমুসলিমের কাছে দ্বীনী ব্যাপারাদি ছাড়া চিকিৎসা, শিল্প, কৃষি প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিতে সাহায্য চাইতে পারে, তাতে কোন দোষ নেই। শাসন কর্তৃপক্ষ এবং সাধারণ মানুষ সকলের জন্যেই এ অনুমতি রয়েছে। তবে একথা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ যে, এ সব ক্ষেত্রেই মুসলমানদের স্বনির্ভরতা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা অর্জন করা একান্তই কর্তব্য।
নবী করীম (সা) নিজে অমুসলিমের কাছ থেকে বিভিন্ন কাজে ও ক্ষেত্রে মজুরীর বিনিময়ে সাহায্য নিয়েছেন, কাজ করিয়েছেন। হিজরত করার সময় পথ দেখানর উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার মুশরিক আবদুল্লাহ ইবনে আরীকতের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। আলিমগণ বলেনঃ কেউ কাফির হলে যে-কোন বিষয়েই তাকে বিশ্বাস করা যাবে না, এমন কথা জরুরী নয়। মদীনার পথে মক্কা ত্যাগ করার মতো কাজে পথ দেখিয়ে সাহায্য করার জন্যে একজন মুমরিকের সাহায্য গ্রহণ করায় এ পর্যায়ের সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সহজেই দূর হয়ে যায়।
সবচেয়ে বড় কথা, মুসলমানের নেতার পক্ষে অমুসলিমের কাছে সাহায্য চাওয়া বিশেষ করে আহলিকিতাবের লোকদের কাছে- সম্পূর্ণ জায়েয বলে বিশষজ্ঞ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যুদ্ধে এদের শরীক করা ও বিজয় লাভ হলে মুসলমানদের ন্যায় তাদেরও গনিমতের মাল দিয়েছেন। হুনাইন যুদ্ধে ছওয়ান ইবনে উমাইয়া মুশরিক পওয়া সত্ত্বেও রাসূলে করীম (সা)-এর সঙ্গী হয়ে যুদ্ধ করেছেন।
তবে শর্ত এই যে, যে-অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণ করা হবে, মুসলমানদের ব্যাপারে তার ভাল মত ও দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে। যদি তাদের বিশ্বাস করা না যায়, তাহলে অবশ্য সাহায্য গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা বিশ্বাস-অযোগ্য মুসলমানের সাহায্য গ্রহণই যখন নিষিদ্ধ, তখন বিশ্বাস-অযোগ্য কাফিরের সাহায্য গ্রহণের তো কোন প্রশ্নই উঠে না।
মুসলিম অমুসলিমকে হাদিয়া তোহফা দিতে পারে, তার দেয়া হাদিয়া তোহফা গ্রহণও করতে পারে। নবী করীম (সা) অমুসলিম রাজা-বাদশাদের দেয়া হাদিয়া-তোহফা কবুল করেছেন। এ পর্যায়ে বহু সংখ্যাক হাদীস বর্ণিত ও উদ্ধৃত হয়েছে। নবী-বেগম হযরত উম্মে সালমা (রা)-কে নবী করীম (সা) বলেছিলেনঃ ( আরবি*******************)
আমি নাজ্জাশী বাদশাকে রেশমী চাদর ইত্যাদি তোহফা পাঠিয়েছিলাম।
বস্তুত ইসলাম মানুষকে মানুষ হিসেবেই মর্যাদা দেয়, সম্মান করে। তাহেলে আহলি কিতাব, যিম্মী ও চুক্তিবদ্ধ কোন মানুষের সাথে অনুরূপ মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণ অবলম্বিত হবে না কেন?
নবী করীম (সা)-এর কাছ দিয়ে একটি জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তা দিখে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তখন তাঁকে বলা হল- ইয়া রাসূলুল্লাহ্, এ তো এক ইয়াহূদীর লাশ! তিনি বললেনঃ কেন, ইয়াহূদী কি মানুষ নয়? ইসলামে তো মানুষ মাত্রেরই একটা মান ও মর্যাদা আছে।
ইসলাম একটা সাধারণ রহমত
ইসলাম তো প্রত্যেক প্রাণীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন কি বাকশক্তিহীন জন্তু-জানোয়ারের প্রতিও কোনরূপ নির্মমতা দেখাতে নিষেধ করেছে। তাহলে কোন অমুসলিম মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার কেমন করে জায়েয হতে পারে মুসলমানদের পক্ষে?
তেরো’শ বছর পূর্ব থেকেই ইসলাম জীব-জন্তুর প্রতি দয়া প্রদর্শন করার নির্দেশ দিয়েছে। তাদের প্রতি দয়া দেখানকে ঈমানের অঙ্গ বলেছে। আর ওদের কোনরূপ কষ্টদানকে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ বলে ঘোষণা করেছেন।
নবী করীম (সা) তাঁর সাহাবীদের কাছে বর্ণনা করেছেন, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে হাঁপাচ্ছিল। তা দেখে এক ব্যক্তি কুপে অবতরণ করে পায়ের ‘মোজা’ খুলে তাতে পানি তুলে কুকুরকে পানি পান করিয়ে তৃপ্ত করে দিয়েছিল। রাসূল করীম (সা) বলেন- আল্লাহ্ তা’আলা তার এ কাজকে পছন্দ করেছেন এবং তার গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। সাহাবিগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ( আরবি*******************)
হে রাসূল! জন্তু-জানোয়ারের প্রতি ভাল কাজ করা হলেও কি আমরা সওয়াব পাব? বলেছেনঃ যে কোন জীবন্ত সত্তার প্রতি ভাল ব্যবহার করা হলে অবশ্যই শুভ কর্মফল পাওয়া যাবে। (বুখারী)
আল্লাহর ক্ষমা পাওয়া অনিবার্য করে তোলার এ উজ্জ্বল চিত্রের পাশাপাশি নবী করীম (সা) আর একটি চিত্র অংকিত করেছেন। তা হচ্ছে, আল্লাহর আযাব ও গযব অনিবার্য করে তোলার ছবি। তিনি বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
একটি মেয়েলোক জাহান্নামে প্রবেশ করল একটি বিড়ালের সাথে নির্মম আচরণ গ্রহণের দরুন। সে সেটিকে বন্দী করে রেখেছিল- সেটিকে না খাবার দিত, না ছেড়ে মুক্ত করে দিত। ফলে বিড়ালটি পোকা-মাকড় খেয়েও যে বাঁচবে, তাও সম্ভব হয়নি। (বুখারী)
জন্তু-জানোয়ারের ব্যাপারে চূড়ান্ত মাত্রায় গুরুত্বারোপ দেখতে পাই নবী করীমের আচরণে। তিনি একটি গাধাকে দেখলেন, সেটির মুখাবয়বের উপর দাগ দেয়া হয়েছে। তিনি এর প্রতিবাদ করলেন এবং বললেনঃ ( আরবি*******************)
আল্লাহর কসম, এরূপ দাগ দেয়া ঠিক না। আমি তো মুখাবয়ব বাদ দিয়ে অনেক দূরে দাগ দিয়ে থাকি। (মুসলিম)
অপর একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে, একটি গাধা তাঁর কাছ দিয়ে চলে গেল। তিনি দেখলেন, গাধাটির মুখের ওপর দাগানো হয়েছে। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি*******************)
তোমরা কি জানো না যে, আমি অভিশাপ দিয়েছি সেই ব্যক্তিকে, যে জন্তুর মুখের ওপর দাগায় কিংবা মুখের ওপর মারে? (আবূ দাঊদ)
পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হযরত ইবনে উমর (রা) কতিপয় লোককে দেখলেন তারা একটি মুরগীকে লক্ষ্য করে তার ওপর তীর নিক্ষেপণ ও লক্ষ্য ভেদের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। তখন তিনি বললেনঃ ( আরবি*******************)
যে লোক কোন জীবন্ত জিনিস লক্ষ্যরূপে গ্রহণ করে নিক্ষেপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে, নবী করীম (সা) তার ওপর অভিশাপ করেছেন।
হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেনঃ ( আরবি*******************)
নবী করীম (সা) জন্তুগুলোকে পারস্পরিক লড়াইয়ে নিযুক্ত করতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)
তিনি আরও বর্ণনা করেছেনঃ ( আরবি*******************)
নবী করীম (সা) জন্তুকে খাসি করতে তীব্র ভাষায় নিষেধ করেছেন। (বাজ্জার)
জাহিলিয়াতের যুগে লোকেরা জন্তু-জানোয়ারের কান কেটে চিরে দিত। কুরআন এ বীভৎস কাজের প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং এটা যে নিতান্ত শয়তানী কর্ম- শয়তানের প্ররোচনাই তা করা হয়, তাও স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে।
যবেহ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে, যবেহর জন্তুটিকেও শান্তি ও সহজতা দানের ওপর ইসলাম যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। ছুরি খুব তীক্ষ্ণ শাণিত করতে ও যবেহর পূর্বে সেটি জন্তুর নজরের আড়ালে রাখতে বলেছে।
একটি জন্তুকে দেখিয়ে আর একটিকে যবেহ করতেও নিষেধ করা হয়েছে। জন্তু- জানোয়ারের প্রতি শান্তি দানের এতটা গুরুত্ব দুনিয়ায় কোন ধর্মে বা মতাদর্শে দেয়া হয়েছে কি?
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি