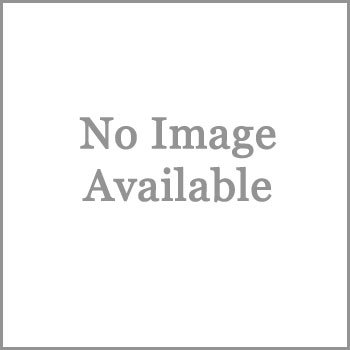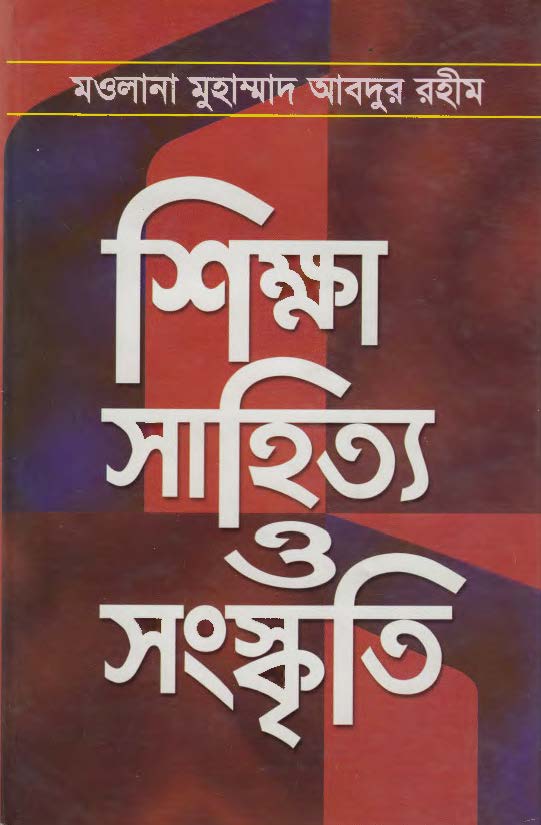সংস্কৃতি
সংস্কৃতির গোড়ার কথা
জীবনের কুল-কিনারাহীন মহাসমুদ্রে মানুষের অস্তিত্ব এক ক্ষুদ্র তৃণখণ্ড সদৃশ মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈচিত্র্য ও সামাজিক উত্তরাধিকারের পার্থক্যের দৃষ্টিতে বহুতর মহাসমুদ্রের ব্যাপকতা ও বিশালতা রয়েছে মানুষের সত্তায়। মানুষ শুধু নিজের আকার-আকৃতি ও সামাজিক উত্তরাধিকার বৈচিত্র্যেরই প্রতীক নয়, বরং ভাষা-সাহিত্য, বিশ্বাস-প্রত্যয়, চিন্তা-পদ্ধতি ও জ্ঞান-বুদ্ধির রকমারি শাখা-প্রশাখারও প্রতিচ্ছবি এই মানুষ। স্পষ্টত মনে হয়, এ বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতাই মাটি-পানির এই জগতের সৌন্দর্য-শোভা। জীবনের স্থিতি ও দৃঢ়তা এ বৈচিত্র্যেরই ফসল।
মানুষের সমাজ-জীবনের ইতিহাস-পূর্বকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যেসব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতি যে বিকাশমান পর্যায়সমূহকে অতিক্রম করে এসেছে, তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের নিকটই ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আজও তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠেনি মানুষের সামনে; বরং অস্পষ্টতার এক ছায়াঘন আবরণ তাকে আচ্ছন্ন ও প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা যা কিছু জানতে পেরেছি, তা শুধু আন্দাজ-অনুমান বই আর কিছু নয়।
মানুষ এক বিশেষ ধরণের পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে। সে পরিবেশ বিশেষ ধরণের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। জন্ম মুহূর্ত থেকেই নানারূপ জ্ঞানগর্ভ কথাবার্তা ও মিষ্টি-মধুর ভাষা তার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়; তার চোখ দেখতে পায় বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদি এবং অসংখ্য সক্রিয় প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা। সে প্রতি মুহূর্তেই পরিবেশ থেকে প্রেরণা লাভ করছে, প্রভাব মেনে নিচ্ছে, প্রভাবান্বিত হচ্ছে এবং অবচেতনভাবে তার ব্যক্তিসত্তা, ব্যক্তিত্ব ও মন-মানস এক বিশেষ ধরণের ছাঁচে ঢেলে গঠিত হচ্ছে। পরিবেশ থেকে গৃহীত এসব প্রভাব তার ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং উত্তরাধিকারলব্ধ প্রকৃতির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে তাকে এক বিশেষ ধরণের ব্যক্তিসত্তায় পরিবর্তিত ও পরিণত করে দেয়। পরিভাষায় একেই বলা হয় সংস্কৃতিবান তথা সভ্য মানুষ (Cultured man)।
মানবতার বিরাট মর্যাদাপূর্ণ প্রাসাদ অবশ্য পাশবিকতার ভিত্তির ওপরই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ মানুষ নিশ্নশ্রেণীর পাশবিক গুণ-বৈশিষ্ঠ্যে উৎকর্ষ ও উন্নতি লাভ করে উচ্চতর মানবীয় মূল্যমানে ভূষিত হয়। কেননা বিশ্বস্রষ্টা তাকে বিবেক-বুদ্ধি এবং মন-মানস দিয়ে ধন্য করেছেন। যদিও মানুষের বুদ্ধি-বিবেক (Reason) ও মননশক্তি (mind) খোদার বিশেষ দান, না মানুষ নিজেরই চেষ্টা-শ্রম ও সাধনার ফলে তা অর্জন করে নিয়েছে, এ বিষয়ে একটা বিতর্ক রয়েছে; কিন্তু সে বিতর্ক বাদ দিলেও আমাদের একথা অনস্বীকার্য সত্য।
মানুষ সম্পর্কে দুনিয়ার নানা চিন্তাবিদ নানা মত প্রকাশ করেছেন। ডারউইন (Darwin) তার ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে, জীবতাত্ত্বিক দিক দিয়ে মানুষ সাধারণ পর্যায়েরই একটি জীব বিশেষ। তার শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা, হজম-রীতি এবং রক্তের প্রবাহও জীব-জন্তুর এসব দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এমন কি জন্ম-মুহূর্তে মানুষ জীব-জন্তুর মতোই বাক্শক্তিহীন হয়ে থাকে। উত্তরকালে দীর্ঘ সময়-কাল অতিক্রম করার পর তার পরিবেশ থেকে সে বাকশক্তি অর্জন করে। ডারউইন তার বক্তব্য বলিষ্ঠ করার উদ্দেশ্যে একটি আরণ্যক মেয়ের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। মেয়েটিকে ১৭৩১ সনে ফ্রান্সের ক্যালন (CHALON) নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছিল। সে কথা বলার পরিবর্তে শুধু চিৎকার করতো। ১৯৫৬ সনে মধ্য-ভারতেও অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটে। রামু নামে নেকড়ের একটি বাচ্চা (Ramu the Wolf boy) জঙ্গলে পাওয়া যায়। সেটি ঘাস খেতো এবং জন্তুর মতোই খুব জোরে চিৎকার করতো। বাচ্চাটিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেখে তার পশুসুলভ আদত-অভ্যাসের গভীর ও সূক্ষ্ণ পযর্বেক্ষণ করে তার মধ্যে মানবীয় আদত-অভ্যাস সৃষ্টির চেষ্টা করা হল। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হলনা। বস্তুত সব জীব-জন্তুই আঙ্গিকের দিক দিয়ে পরস্পর সদৃশ্য। অতএব বুদ্ধি-বিবেক, মন-মানস, চিন্তাশক্তি সবই ক্রমবিকাশের ফসল আর তা নিছক শ্রমলব্ধ ও অজির্ত গুণ-বিশেষ।
কিন্তু ডিকার্টে (Descartes) এ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি বলেন, মানুষের মন ও মনন আল্লাহর এক বিশেষ অবদান। এ শক্তি আল্লাহ তা’আলা কেবল মানুষকেই দিয়েছেন; সৃষ্টির মাঝে এ গুণ তিনি আর কাউকেই দেননি। তবে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সাহায্যে তাকে অধিক তীক্ষ্ণ ও শাণিত করে তোলা যেতে পারে; তাকে উত্তম পন্থায় প্রয়োগ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। মানুষের মন সম্পর্কে চিন্তাবিদ মিল (Mill)-এর অভিমত হল এই যে, তার চিন্তা, গবেষণা ও অনুভূতি অত্যন্ত জটিল এবং ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মোটকথা, এদের মতে যতই বিভিন্নতা থাকুক না কেন, মানুষের-সে পুরুষই হোক কি নারী- বুদ্ধি-বিবেক ও মন-মানসই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশিষ্টতার বিশেষ সম্পদ। এর বদৌলতে মানুষ যেমন দুনিয়ার অন্যান্য সৃষ্টি থেকে পৃথক, তেমনি সে বিশিষ্ট ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। অবশ্য ডারউইন এ বিষয়েও আপত্তি জানিয়েছেন। তিনি মনে করেন, সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)-র বিশেষত্বই হল এই যে, তা জ্ঞান-বুদ্ধির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকেই কাজ করে। জীব-জন্তুর মধ্যে চেতনা তেমন উন্নত ও উৎকর্ষলব্ধ নয়, অথচ মানুষের চেতনা দীঘর্কাল যাবতই উন্নতমানের রয়েছে। মানুষের মগজ (Cerebral cortex) নিত্য-নব অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে বহুকাল থেকেই; যদিও তার স্নায়ুবিক পদ্ধতি (Nervous system) শুরুতেই নিভুর্লভাবে পৃথককরণ এবং স্মরণ রাখার ব্যাপারে এতো তীক্ষ্ণ শক্তির অধিকারী ছিল না। এ থেকে ডারউইনের ক্রমবিকাশ তত্ত্ব দেহ-কেন্দ্রিক হওয়ার বদলে মন-কেন্দ্রিক হওয়ার দিকে ঘুরছে বলে মনে হয়। যান্ত্রিক অস্ত্রশস্ত্র, বই-পুস্তক, সাহিত্য, চিত্রকলা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, সুন্দর-সুরম্য প্রাসাদ, সুনীতি ও সুষ্ঠুতা, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক জ্ঞান, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিধি-বিধান, এই পর্যায়ের সব প্রতিষ্ঠানাদি এবং আধুনিক ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থা সবকিছুই মানব মনের চিন্তা-ভাবনা ও বুদ্ধি-প্রতিভারই বিস্ময়কর ফসল। এগুলো মানুষ নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-গবেষণা ও অভ্যাস-অনুশীলনের সাহায্যে বতর্মান পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে। মানুষের নতুন বংশধরেরা এ উত্তরাধিকারকে, যার নাম সংস্কৃতি, হারাতেও পারে, এর সমৃদ্ধি সাধনও করতে পারে-পারে ভালোভাবে এর সংরক্ষণ করতে।
একেবারে প্রাথমিক কালের অবস্থা লক্ষ্য করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সেদিন নিজের পরিবেশে যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত করে পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূল বানিয়ে নিয়েছিল-পরিবেশের সাথে স্থাপন করে নিয়েছিল পূর্ণ সামঞ্জস্য। চক্মকির ব্যবহার, গুহা-প্রাচীরের গায়ে (স্পেন ও ফ্রান্সে) চিত্র অঙ্কন ও পাথরের অস্ত্র মানব সমাজে শত-সহস্র বছর পূর্বে প্রচলিত ছিল। পরবতর্তীকালে পশু শিকার-নির্ভর এ আরণ্যক জীবন পরিহার করে মানুষ স্থিতিশীল সামাজিক জীবন যাপন শুরু করে।
মানুষের বুদ্ধি-জ্ঞান, চিন্তা-ভাবনা ও মননশীলতায় যতোই উৎকর্ষ দেখা দিল, মানুষ ততোই আদিম ও আরণ্যক জীবন থেকে দূরে সরে গেল। কিন্তু এসব হল কিভাবে? এ পর্যায়ে কেবল ধারণা –অনুমানই করা চলে, কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি-প্রমাণ-নির্ভর জ্ঞান লাভ করা যায়না।
অবশ্য ক্ষেতে ফসল বোনা, ফসল আহরণ, সূতা কাটা, কাপড় বোনা এবং তামা ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যকে ব্যবহারাধীন করে নেয়ার খবর পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে লেখার পদ্ধতি চালু হয়। এর ফলে মানব জীবনে এক মহাবিপ্লব সূচিত হয়। এসব আবিষ্কার-উদ্ভাবনী মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ক্রমবিকাশমান সংস্কৃতি এরই মাধ্যমে সভ্যতায় পরিণত হয়। আরো পরে ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামরিক কার্যক্রমের সাহায্যে তাকে ব্যাপকতর সম্প্রসারিত করা সম্ভব হয়।
আবিষ্কার-উদ্ভাবনীকে এক আকস্মিক ব্যাপারই বলা যায় আর তা হচ্ছে ত্যাগ-তিতিক্ষা, অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার ফসল। তা যখন লোকদের নিকট সমাদৃত হয়, তখন তা-ই সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে; সমাজ-মানুষের চিন্তায়-মননে এবং আদত-অভ্যাসে তার গভীর প্রতিফলন ঘটে। চিন্তা করা যেতে পারে, মানুষ আজ যদি আগুনের ব্যবহার না জানত, কথা বলতে না পারত, খাদ্য ও পোশাকের কোন ব্যবস্থা না হতো, তাহলে মানুষের জীবন কি গভীর শূণ্যতায় ভরে যেত না? এ দুনিয়ায় যত ব্যক্তিসত্তাই জন্ম নেয়, তারা প্রত্যেকেই নিজকে এক বিশেষ প্রাকৃতিক ছাঁচে ঢেলে তৈরী করে নেয় আর এ ছাঁচের গড়নেও দীর্ঘকালের সাধনার প্রয়োজন। তার অভ্যাস, প্রবণতা, মনোভাব, বিশ্বাস, প্রচলন প্রভৃতি সবকিছুই হয় আবিষ্কার-উদ্ভাবনীর মাধ্যম। এটা না হলে ব্যক্তিদের অসভ্য মনে করা যেত। এজন্যে তারা বাধ্য হয়েই উত্তরাধিকার সূত্রে লব্ধ মতাদর্শ ও চিন্তা-বিশ্বাসকে মন-প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করে; বরং বলা যায়, তার নিজের বাছাই করে কোন একটাকে গ্রহণ করার পূর্বেই এগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়।
বস্তুত সংস্কৃতির বিকাশ ও ফলন দৈহিক বর্ধনশীলতা ও বিরাট আকৃতির সাথে অনেকটা জড়িত। পরিবেশ ও পরিবেষ্টনীর প্রভাব, ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ এবং নৈতিক মূল্যমানের আনুকূল্য, দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতা ও প্রস্তুতির ওপর নির্ভরশীল। দৈহিক আকৃতির তৎপরতা ও সুক্রিয়াশীলতার সাথে কথা বলার গুরুত্বও অপরিসীম। তার জন্যে চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধান, সমীক্ষণ এবং সচেতন পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এসব চিন্তা-ভাবনা ও তত্ত্ব-তথ্যের মাঝে একটা নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তা কখনো ছিন্নভিন্ন হতে পারেনা। কর্মের ওপর শব্দ তার প্রাসাদ নির্মাণ করে এবং প্রাচীনকালে ভাষার উৎপত্তি হয়েছিল হু, হ্যাঁ ইত্যাদি ধ্বনি থেকেই। আর লেখার উৎপত্তি হতে এসব ঘটনা ও ক্রিয়াকাণ্ডের চিত্র অঙ্কন করতে বহু কষ্ট স্বীকারের প্রয়োজন হয়েছিল অবশ্যই। মিশরীয় শিলালিপি, চিত্রলেখা এবং তার পরিবর্তনগুলোকে ধ্বনি-কেন্দ্রিক নিদর্শনই প্রকাশ করে থাকে। এ থেকেই বর্ণের উৎপত্তি আর এ পর্যায় অতিক্রান্ত হয়েছিল আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে। এ থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, শব্দ মূলতই কাজ ও কর্ম মাত্র আর তার শক্তি সর্বজনবিদিত।
সংস্কৃতির আবেগ ও উচ্ছ্বাসমূলক দিকটি শব্দের সাথে সম্পর্কিত আর বুদ্ধি ও মন হচ্ছে কর্ম, শুধু মাধ্যমেই নয়। কেননা সক্রিয় ও প্রভাবশালী চিন্তা-ভাবনার দ্বারা সংস্কৃতি দানা বেঁধে ওঠে আর চিন্তা, মনোভাব, গবেষণা ও মননশীলতার সাথে শব্দের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এজন্যে নাম ও শব্দের পরস্পর সম্পর্কিত হওয়া আবশ্যক। ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথে অনুভূত হয়, যেন কোন একটা জিনিস উপস্থিত করে দেয়া হয়েছে। এভাবে তা বস্তুনিচয়ের সাথে একাত্মতার সৃষ্টি করে। এভাবে এই চেতনা পর্যায়ক্রমিক বিকাশধারায় নিজের জন্যে উপযুক্ত শব্দ ও ভাষার উপাদান সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে অস্তিত্ব লাভ করে এক সম্পদশালী ভাষা।
মানব সমাজে ভাষার বিভিন্নতা ও পার্থক্য কেন? তার কারণ এই যে, স্নায়ুবিক প্রক্রিয়া ও জ্ঞানগত ধারণা বিভিন্ন অবস্থা ও ধ্বনির সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি ও বিশেষ শব্দের পশ্চাদপটের অবস্থা ও পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যে যে হাতিয়ার ব্যবহার করা যেতে পারে, তা দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলে যায়। সাধারণ উন্নতি ও ভাষাতাত্ত্বিক জ্ঞান, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারসমূহের সাথে সাথে আত্মপ্রকাশ করে। এ কারণে ভাষা যে সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অস্পষ্ট ও চুপচাপ কথাবার্তা চিন্তার মতোই নিঃশব্দ। যদি শব্দই না থাকে, তাহলে চিন্তা, গবেষণা ও সমীক্ষণও থাকেনা। মানুষ কেবল সজাগ থেকেই চিন্তা করে না, ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায়ও তার চিন্তাকর্ম অব্যাহত থাকে। প্রাচীনকালে মানুষের জন্যে এ দৃষ্টিভ্রম বা অস্পষ্টতা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাতিসমূহের আকীদা বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ ও নীতি-পদ্ধতির সাথে তাদের স্বপ্নের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ জিনিস এমন কারণসমূহের অন্যতম, যার দরুণ সভ্যতার প্রাসাদ উন্নতশির হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত সামগ্রিক, ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক শক্তিসমূহের শুভ সংমিশ্রনেরই অপর নাম হচ্ছে ‘সংস্কৃতি’।
সংস্কৃতির মৌল উপাদান
মানুষের প্রয়োজন-তা আত্মিক হোক কি দৈহিক, রাজনৈতিক হোক কি নৈতিক, ব্যক্তিগত হোক কি সমষ্টিগত, তা সমাজবদ্ধতা ও সংস্থা-সংগঠনের মাধ্যমেই পূর্ণ হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক মানুষের (Man of Nature) কোন অস্তিত্ব নেই, থাকতে পারেনা। তার প্রতিরক্ষা, খাদ্য, গ্রহণ, স্থানান্তর ও গতিবিধি সবই সামগ্রিক সহযোগিতামূলক কাজের ওপর নির্ভরশীল। এ সামাজিক দলবদ্ধতা এমন লোকদের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে, যারা স্থানীয়, দেশীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত। তা ছাড়া অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্ম-তৎপরতার দিক দিয়েও তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়েই থাকে। এসব সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের সকলেরই মনজিল এক এবং অভিন্ন। চলার পথও সমান। এ জীবনপথে চলার ব্যাপারে তাদের আচরণও বিশেষ রীতিনীতি ও আইন-বিধানানুগ আর সেগুলোর মৌল উৎস হচ্ছে ধর্মীয় নৈতিক বিধান।
মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণাবলীর মধ্যে নীতিবাদিতা, মানসিক আবেগ এবং আল্লাহর ভয় এমন কার্যকারণ, যা বিশেষ অবস্থায় বিশেষ ধরণের আচরণ সৃষ্টির নিমিত্ত হয়ে থাকে। সর্বসমর্থিত মূল্যমান মানুষের আচরণকে প্রভাবান্বিত করে আর তার নির্ভুল ও পূর্ণ বিন্যাস হতে পারে এক বিশেষ ধরণের সংস্কৃতিতে। মনের ইচ্ছা-বাসনা ও আবেগ-উচ্ছ্বাসের পারস্পরিক সংযোজন হতে পারে এসব ব্যবস্থাপনার অধীন। জাতি, সরকার, জাতীয় পতাকা ইত্যাদির পশ্চাতেও অন্তর্নিহিত থাকে জীবন্ত সংস্কৃতির মহাসত্য আর নতুন বংশধরদের মাঝে তার মোটামুটি মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব জৈবজীবনের বিভিন্ন অভিব্যক্তিতে রূপ পরিগ্রহ করে।
ক্রমবিকাশমূলক চিন্তায় বিশ্বাসী লোকদের মতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবৃদ্ধি স্বতঃস্ফূর্ত (Spontaneous) পরিবর্তন ধারার পরিণতি। তা সুসংবদ্ধ মৌল নীতিসমূহের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হয়। তাকে একটির পর একটি পর্যায় ও স্তর অতিক্রম করে অগ্রসর হতে হয়। অগ্নির অস্তিত্ব লাভ, তৈজসপত্র নির্মাণ, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার এবং তার বিভিন্ন ‘ডিজাইন’, ‘প্যাটার্ন’ ও অর্থনৈতিক উন্নতি একথার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।
এসব পর্যায় ও স্তরের পরিব্যপ্তি ও সম্প্রসারণশীলতার (Diffusion) সূচনা কি করে হল, কি করে ও কিভাবে তা ক্রমোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে অগ্রসর হল এবং তার কোথায় কোথায় ও কতখানি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার সন্ধানের ওপর ঐতিহাসিক চিন্তাবাদের ভিত্তি সংস্থাপিত। সংস্কৃতিকে এভাবেই বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়। এজন্যে গোত্র-ভিত্তিক জীবন-ধারা, ধর্মীয় সংঘবদ্ধতা, বস্তুগত ও বৈষয়িক উন্নতি, সামাজিক মূল্যমান ও সামষ্টিক প্রতিষ্ঠানাদি ইত্যাকার বিশেষত্বকে সামনে রেখেই সংস্কৃতিকে বিবেচনা করা হয়। এ সবের বিস্তার যে একই নিয়মে সংঘটিত হতে পারেনি, তা সুস্পষ্ট। বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরণের বিশেষত্ব পাওয়া যেতে পারে বটে; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাইরের তথা বৈদেশিক সভ্যতা-সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রভাবও তার ওপর প্রতিফলিত হতে পারে। মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনাবলী পরিপূরণে আদত-অভ্যাসের বৈচিত্র্যও বিশেষ ধরণের পটভূমির অধিকারী। ছড়ি বা লাঠি অন্ধকার যুগে মাটি খোদাইর কাজে ব্যবহৃত হতো। কালের অতিক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তার দ্বারা চালনা-দণ্ডের কাজও করা হয়েছে। উত্তরকালে তা আবার ভ্রমণ-ছড়ি রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে এই ছড়িই উচ্চতর মান-মর্যাদার নিদর্শন। আবার শিক্ষাঙ্গনে তা দৈহিক পীড়নের উপকরণ। এককথায় ছড়ির সঙ্গে যেসব ধারণা ও চিন্তা-বিশ্বাস জড়িত, তা সমাজে প্রচলিত মূল্যমান দ্বারা প্রভাবিত। সোরাহীকে এক কালে পানির সঞ্চয় রক্ষা ও তা শীতল করার কাজে ব্যবহার করা হতো। পরিবর্তিত চিন্তা-বিশ্বাস ও ধারণা-মতবাদ তার ব্যবহারের ওপর সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বর্তমানে সেই সোরাহীই শিল্পীর উচ্চমানের শিল্পকর্মের নিদর্শন হয়ে ড্রয়িং রুমের শো-কেসে স্থান লাভ করেছে এবং লোকদের সৌন্দর্য-পিপাসু মন-মানসের স্পৃহা চরিতার্থ করছে। নৌকার গঠন-প্রকৃতি, তার সংগঠন পরিপক্কতা এবং তাকে কর্মোপযোগী বানানোর কাজে যুগ যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হাজার রকমের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। নৌকা বা জাহাজ নির্মাণ কৌশলে দক্ষতা নৌ-পরিচালনা বিদ্যা ও পদ্ধতি সব কিছুই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশেষে বর্তমান যুগে এসে তা একা সর্বাত্মক সৌন্দর্য ও ব্যবহারিক যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।
জমির ওপর লাঙ্গল চালানো, বীজ বপন করা ও ফসল তোলা- এই সব কিছুই একটা নিয়ম ও শৃংখলার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এসব তৎপরতা বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশ-পরিবেশে বিভিন্ন ধরণের পন্থা-পদ্ধতি ও হাতিয়ার অবলম্বন করেছে। এভাবে মানবীয় প্রয়োজন যথার্থভাবে ও পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করার একটা বিশেষ ভঙ্গি অস্তিত্ব লাভ করেছে। এগুলোর পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও সংযোজন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের (Traits) পরিণতি নয়; বরং তা সে সব সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের (Institutions) অবদান যেসব সংস্থা নিজেদের সুসংবদ্ধ ও সুসংহত চেষ্টা-প্রচেষ্টার দরুন এ পর্যায়গুলো অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অতিক্রম করেছে। একটি জিনিসের ব্যবহারের সাংস্কৃতিক পটভূমি (Cultural Context), চিন্তা-ভাবনা, প্রচলন এবং আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা (Attachment) অনিবার্য- তা কোন ব্যক্তির দ্বারাই ব্যবহৃত হোক, কি কোন সমাজ সমষ্টি কর্তৃক। ছড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, তার ওপর নানা রূপ নকশা অংকন ও চাকচিক্য বৃদ্ধিতে একটি সাংস্কৃতিক, আনুষ্ঠানিক, ঐতিহ্যিক ও ধর্মীয় সম্পৃক্ততা বলিষ্ঠভাবে বর্তমান আর তা-ই তার মৌলিক ব্যবহারের ওপর পরিব্যাপ্ত।
সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজেদের তৎপরতাকে বিভিন্ন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের কাজে ব্যবহার করে থাকে আর এই উদ্দেশ্য লাভের জন্যেই সে সব সংগঠন গড়ে তোলা হয়। তাতে জীবন-জীবিকা, বংশানুক্রম, প্রতিরক্ষা ও সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকার গুরুত্ব সর্বাগ্রগণ্য। অর্থনৈতিক উন্নতির জন্যে ধনসম্পদ বিনিয়োগ, উপায়-উপকরণের ব্যবহার, হাট-বাজার, যোগাযোগ ও নিয়ম-নীতি-পদ্ধতি গড়ে ওঠে আর নিত্যকার ব্যস্ততার মধ্যে মাছ-ধরা, বাগান রচনা, পশু পালন, বন্য পশু শিকার ও চাষাবাদ এর মধ্যে শামিল। এসবের সাহায্যেই আর্থিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়ে থাকে।
পরিবার সংস্থা
বংশের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যে একটি পারিবারিক বা ঘরোয়া পরিবেষ্টনীর একান্ত প্রয়োজন। পরিবার পরিবেষ্টনী একটি সংক্ষিপ্ত একক (Unit)। আইনগত ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও বংশানুক্রমিক মূল্যমানের (values) ওপর এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ভিত্তি সংস্থাপিত। পরিবার পরিবেষ্টনী একটি ক্ষুদ্রায়তন সংস্থা। প্রচার ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা এই পরিবার পরিবেষ্টনীর ওপরই নির্ভরশীল।
বিভিন্ন ভঙ্গি, প্রয়োগ পদ্ধতি, ধরন-ধারণ, দ্বীনী চিন্তা-চেতনা, নৈতিক মূল্যমান, দাম্পত্য জীবন, সামাজিক দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ উত্তরাধিকার নিয়মে এক বংশ থেকে আর এক বংশে উত্তরিত হয়। এর সংরক্ষণের জন্যে নিম্নোদ্ধৃত পদক্ষেপসমূহ জরুরীঃ
১. ব্যভিচার বা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধকরণ।
২. পারিবারিক দায়িত্বসমূহের মান-সম্ভ্রম রক্ষা ও সামাজিক কর্তব্য পালন।
৩. পারিবারিক আইন-বিধান ও নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ মাত্রায় প্রতিফলন।
ব্যভিচার তথা অবৈধ যৌন সম্পর্কের ফলে একদিকে বংশগত পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, অপরদিকে গোটা সমাজ-পরিবেশে নোংরামী, পংকিলতা, নগ্নতা, নির্লজ্জতা, অশ্লীলতা ও পারস্পরিক হিংসা-দ্বেষ, শত্রুতা, নরহত্যা ও রক্তপাত ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। পারিবারিক ও বংশীয় একত্ব ও ঐতিহ্য চূর্ণ হয়ে বংশের ধারা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। আত্মীয়তা এবং তার মান-সম্ভ্রম ক্ষুণ্ন ও বিলীন হয়। যে সমাজে ব্যভিচার সমর্থন পায়, তা অনিবার্যভাবে উন্নত মানবীয় ও সাংস্কৃতিক মূল্যমান থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়। সেখানে ব্যক্তিদের মধ্যে স্বার্থপরতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মকেন্দ্রিকতার পরিবেশ জেগে ওঠে; ফলে সামাজিক উন্নতি ও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়।
পাশ্চাত্য দেশসমূহে প্রেমাভিসার বা কোর্টশিপ (Court Ship) প্রচলনের মূল উদ্দেশ্য যা-ই থাকনা কেন, বর্তমান যুগে ও পরিস্থিতিতে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেছে এবং এখন তা নিতান্তই কাম-লিপ্সা ও যৌন-স্পৃহা চরিতার্থ করার একটা প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ফলে পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনের পবিত্রতা ও সম্ভ্রম এবং মানসিক স্থৈর্য ও শান্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে। ব্যভিচারের এই ব্যাপকতা দৈহিক রোগ-ব্যাধির মারাত্মক প্রকোপ সৃষ্টি করেছে [পাশ্চাত্যের তথাকথিত উদার ও যৌন-শিথিল সমাজে ব্যভিচারের প্রাবল্য একদিকে পরিবার-ব্যবেস্থাকে প্রায় অকার্যকর করে দিয়েছে অপরদিকে এইডস (AIDS) এর ন্যায় ভয়াবহ যৌন-ব্যাধি মানব জাতির অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে। এ কারণে সেখানকার চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এখন এইডস-এর প্রতিরোধের জন্যে পরিবার ব্যবস্থার সুরক্ষা ও যৌন পবিত্রতা সংরক্ষণের উপর সবচেয়ে গুরুত্ব আরোপ করছেন।- সম্পাদক] এবং আত্মিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিচারে চরম অধঃপতন ঘটিয়েছে।
পারিবারিক পরিবেষ্টনীকে পবিত্র, সুশৃংখল ও নির্ঝঞ্ঝাট রাখার জন্যে স্বামী-স্ত্রীকে নিজেদের কর্তব্য পালনে পূর্ণমাত্রায় আন্তরিক ও সদাতৎপর হতে হবে। নরনারীর দায়িত্বহীন সম্পর্ক সমাজে নানারূপ জটিল নৈতিক মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে দায়িত্বানুভূতি তিক্ত ও বিষাক্ত মুহূর্তগুলিতে উৎকট মানসিক অবস্থা বিদূরণে সফল সঞ্জীবনীর কাজ করে। এর অনুপস্থিতি জীবনকে একটা স্থায়ী অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে দেয়।
স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মতানৈক্য বা ভুল বোঝাবুঝি অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ, মনোমালিন্য ও ঝগড়া-ঝাটি নিতান্তই অবাঞ্ছনীয়। এরূপ অবস্থা দেখা দিয়ে তার প্রতিরোধ ও প্রতিবিধানমূলক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের উপস্থিতি অপরিহার্য। তার সুষ্ঠু প্রয়োগে স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ কার্যকরভাবে রোধ করা এবং পরিবারের লোকদের মধ্যে পূর্ণ মিলমিশ ও মতৈক্য অক্ষুণ্ন রাখা ও কোনরূপ বিভেদ সৃষ্টি হতে না দেয়া সম্ভবপর। লোকদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও চেষ্টা-প্রচেষ্টামূলক ভাবধারা জাগিয়ে রাখা একান্তই জরুরী আর তা সম্ভবপর কেবল তখন, যখন ব্যক্তিগত সামষ্টিক স্বার্থের তাগিদে ব্যক্তিগত স্বার্থ কুরবানী দিতে প্রস্তুত হবে-যখন সামাজিক নিয়মবিধির প্রতি সদাজাগ্রত থাকবে অবিচল সম্ভ্রমবোধ। মূল্যমানের (Values) যথার্থ প্রয়োগ একটি প্রাত্যহিক প্রয়োজন আর সম্মিলিত সামাজিক ব্যতিব্যস্ততা ও আমোদ-প্রমোদমূলক অনুষ্ঠানাদিতে নিয়ম-শৃংখলা রক্ষা করা অত্যাবশ্যক। শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সাহায্যে লোকদের মধ্যে সভ্যতা-ভব্যতা, শালীনতা, সুষ্ঠুতা ও আদব-কায়দা সংরক্ষণ-প্রবণতার সৃষ্টি করতে হবে। এমনিভাবেই ঐতিহ্যের সাহায্যে সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতে পারে আর এজন্যে অক্ষর বা বর্ণমালাই প্রথম অবলম্বন।
ভাষা-ধ্বনি ও ভঙ্গির ধারক। সাংস্কৃতির অভিজ্ঞতা সেখানে সুপ্রকট। প্রাচীন মানুষের মধ্যে মৌখিক বর্ণনা-ধারার সাধারণ প্রচলন ছিল। কিন্তু উন্নত সংস্কৃতিতে লেখন শিল্পকেও শামিল করা হয়েছে। এক কথায়, সংস্কৃতির উজ্জীবনে অর্থনৈতিক সংগঠন সংস্থা, আইন-বিধান ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ বরাবরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।
ধর্ম-বিশ্বাস
জীবনকে সহজ ও সুন্দর করার জন্যে মানুষের মন-মানস তথা বুদ্ধি-বিবেক, চিন্তা-বিবেচনা ও গবেষণা-শক্তি বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে-লাভ করেছে সুদীর্ঘ ও সুব্যাপক অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্মুখবর্তী অবস্থা, পরিস্থিতি ও নিত্য-সংঘটিত ঘটনাবলী মানুষকে বিব্রত, দিশেহারা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ় করে দেয়। তখন সে হয়ে যায় অসহায় –নিরূপায়। তার অনেক বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তা-শক্তি ও অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও সে দিশা করতে পারে না, এখন তার কি করা উচিত!
মানুষ মহাসমুদ্রে চলাচল করার উদ্দেশ্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করেছে। এই জাহাজ চালানো জন্যে সে বাতাসের গতির ওপর নির্ভরশীল থাকেনি। সে আপন শক্তি বলেই সমুদ্রের বুকে যে দিকে ইচ্ছা জাহাজ চালিয়ে দিতে সক্ষম। জাহাজের গতি ও স্থিতি পূর্ণমাত্রায় তার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু হঠাৎ উত্থিত প্রচণ্ড ঝড় ও উত্যুঙ্গ তরঙ্গমালার সম্মুখে সে নিতান্তই অসহায় হয়ে পড়ে। সে সময় তার সব শক্তিমত্তা ও জ্ঞান-বুদ্ধির অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতাকে সে মর্মে মর্মে অনুভব করে- স্বীকার করে। যুদ্ধের ময়দানে সেনাপতি অত্যাধুনিক ও শত্রু হননকারী দূরপাল্লার শক্তিশালী অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে উপস্থিত হয়। তার নিজের বীরত্ব, সাহসিকতা ও যুদ্ধ-কৌশলের ওপর সে পুরোপুরি আস্থাবান। তার সৈন্যসংখ্যা শত্রুপক্ষের অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তাকেই হতে হয় পরাজিত। কিন্তু এটা কেন? এর নির্ভুল জবাব সে সন্ধান করেও জানতে পারে না। তার বিবেক-বুদ্ধি তাকে এ ব্যাপারে কোনই সান্ত্বনা দিতে সক্ষম নয়। কৃষক ক্ষেত্রে-খামারে সোনালী ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে প্রাণ-পণ চেষ্টা করে, নিঃশেষে শ্রম প্রয়োগ করে। হাল হালিয়ে, কোদাল মেরে মাটির বক্ষ সে বিদীর্ণ ও ওলট-পালট করে দেয়। এজন্যে নিজের দেহের রক্ত পানি করে দিতে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও এতটুকু কুণ্ঠিত হয়না। চেষ্টা ও শ্রমেও সে একবিন্দু ত্রুটি থাকতে দেয়না। ফলে সুন্দর শ্যামল ও সতেজ অংকুর ফুটে বের হয়, গাঢ় সবুজে মাঠ একদিক থেকে অন্যদিকে ভরে যায়। সে মনোরম দৃশ্য দেখে কৃষকের চোখ জুড়িয়ে যায়, কলিজা শীতল হয়। কিন্তু সহসাই ঝাঁকে ঝাঁকে পোকা এসে মাথা তুলে উঁচু হয়ে ওঠা ফসলের চারাগুলো জাপটে ধরে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সবগুলো খেয়ে ফেলে। মাঠের সবুজ-শ্যামল শোভা অন্তর্হিত হয়ে পান্ডুবর্ণ ধারণ করে, গাছগুলো নিঃশেষে মরে পঁচে যায়।
অনুরূপভাবে সহসা উদ্বেলিত হয়ে আসা বন্যা-প্লাবনের স্রোতে ক্ষেতের ফসল ভেসে যায়। বৃষ্টি কম বা বেশী হলেও এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ করে দেয়। এটা দেখে কৃষক নৈরাশ্য ও হতাশায় ভেঙে পড়ে। এ সময় তার মনে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার মেঘপুঞ্জ জমে ওঠে। তা দূর করার কি উপায় থাকতে পারে? এ এমন দুঃখ যা মানব জীবনের তিক্ত বাস্তব ও তার আশাব্যঞ্জক প্ল্যান-প্রোগ্রামের মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের ফলে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। মৃত্যুর অবিচল মহাসত্য মানুষের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন, শক্তি ও পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেয়। ঘটনাবলীর মৌল উপাদানসমূহের এই বিশ্লিষ্টতা এবং মৃত্যুর এই অমোঘ আক্রমণ দেখে সে বিদ্রোহ করতে উদ্ধত হয়; এমনকি কখনো-সখনো হতাশায় তার আত্মহত্যা করার ইচ্ছা জাগে। এই সময় একটি বিশ্বাসই তাকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেয়। তা হচ্ছে মহান স্রষ্টা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস। এই বিশ্বাসই তার সম্মুখে জমাটবাঁধা পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মাঝে উজ্জ্বল আলোক-বর্তিকা হয়ে পথ দেখায়-আশার প্রতীক হয়ে তাকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত এই বিশ্বাসই মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল অবস্থায় সব রকমের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম। তাই মানুষের জীবন ধারাকে নৈতিক ও ধর্মীয় বিধি-বন্ধনের ছাঁচে ঢেলে তৈরী করা অপরিহার্য। খোদার প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্য করে চলার মানসিক প্রস্তুতিই তার এই প্রয়োজন পূরণ করে-জীবনকে সুন্দর, সুসংবদ্ধ ও সুশংখল করে তোলে। এই বিশ্বাসই তার জীবনে এনে দেয় কাংক্ষিত গতিময়তা, অপরিসীম শক্তি-সাহস। এভাবেই সংস্কৃতিতে খোদা-বিশ্বাস, অন্যকথায় ধর্মবোধ একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে বসেছে। কেননা যে জ্ঞান-বিদ্যা মানুষকে দূরদর্শীতা ও আলো দান করে, নিয়তির উপরিউক্ত জটিল আবর্তে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। তখন এই বোধ ও বিশ্বাসই হয় তার একমাত্র অবলম্বন। তার কারণ হল, যে সব পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক-সম্বন্ধ সারা জীবন ধরে সুদৃঢ় হয়ে রয়েছে তা মানব মনে একটা আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করে আর এই আবেগ-উচ্ছ্বাসই তাকে এসব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। মানুষের এসব প্রয়োজনের দরুণই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের একটা উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব স্বীকৃত। ধর্মের ভিত্তিতে সংস্কৃতি যেমন পায় দৃঢ়তা ও পরিপক্কতা, তেমনি লাভ করে নতুন জীবন-প্রেরণা ও শক্তিমত্তা।
খেলা-ধূলা ও আনন্দোৎসব
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি ভালোবাসা বংশীয় আনুগত্যের প্রাণ-কেন্দ্র। স্থাপিত সহানুভূতি ও কল্যাণ-কামনামূলক আবেগ-উচ্ছ্বাস, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বংশীয় সম্পর্ক-সম্বন্ধের ওপর সংস্কৃতি-প্রাসাদের ভিত্তি স্থাপিত। এ সবের সমন্বয়ে সৃষ্ট রকমারি ব্যস্ততা ও উৎসব-অনুষ্ঠান চিত্তবিনোদনের উৎস। লোকদের স্নায়ুবিক শ্রান্তি বিদূরণের সুসংগঠিত পন্থা হচ্ছে প্রতিদিনকার খেলা-ধূলা ও শিল্প-কলা সংক্রান্ত নৈপুণ্য ও দক্ষতা। এগুলো প্রাত্যহিক চিন্তা-ভাবনা ও ব্যতিব্যস্ততার ঝঞ্ঝাট থেকে মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের মনে এনে দেয় গভীর প্রশান্তি, স্থিতি ও চিরসতেজতা। শিশু তার কণ্ঠে ধ্বনি তুলে আপন পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও বংশ-পরিবারের অন্যান্য লোকদের সাথে নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। তার জীবনের বিভিন্ন স্তরে তার খেলা-ধূলাও হয়ে যায় বিভিন্ন ধরণের। অন্য কথায়, তার খেলা-ধূলায় নিত্য পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। এই সময়-কালেই শিশুর মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়, ধীরে ধীরে চরিত্রের সুস্পষ্ট বিশেষত্ব ও গুণাবলীও প্রকাশ পেতে থাকে। অন্যদিকে পারস্পরিক বন্ধুতা ও ভালবাসার সম্পর্কও গড়ে উঠতে শুরু করে অনেকের সাথে। নিজেদের মধ্যে গোপন বন্ধুতা এবং বয়স্ক সহচরদের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা বিশালতা লাভ করে। শিশুরা যখন যৌবনে পদার্পণ করে, তখন তাদের মেজাজ-প্রকৃতি অনেকখানি বদলে যায়। তখন সামান্য বিষয়াদি নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেয়া হয়। অভিনয় ও নৃত্যের অনুশীলন কিংবা কোন শৈল্পিক দক্ষতাজনিত ব্যস্ততা, তা সাজসজ্জামূলক অলংকরণ হোক কি চাক্চিক্যপূর্ণ ছবিই হোক-তাতে একটা সৃজনশীল ও চিত্তবিনোদনমূলক ভাবধারা নিহিত থাকে। এ ভাবধারা স্বভাবতঃই পূর্ণতা ও ক্রমন্নোয়নের দাবি রাখে আর এ সবের মাধ্যমে সামাজিক ঘনিষ্ঠতা পরিপক্কতা ও জাতীয় চরিত্র রূপ পরিগ্রহ করে।
শিল্প সাধনা
সমগ্র সাংস্কৃতিক তৎপরতায় শিল্পসাধনা আন্তর্জাতিক ও আন্ত-বংশীয় মূল্যায়নের সর্বাগ্রগণ্য। গান-বাজনা এ সমস্ত শিল্প সাধনায় একটা বিমূর্ত ও পরিচ্ছন্ন শিল্প রূপে গণ্য। তাতে প্রযুক্তিবিদ্যা ও কলা-কৌশলগত ব্যাপারের বিশেষ কোন সংমিশ্রণ নেই। তাতে সুর ও তাল বা ধ্বনির উত্থান-পতনের দিকেই লক্ষ্য আরোপ করা হয়। নৃত্যে এই ভাবধারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গতিময়তা ও হাত-পা সঞ্চালনের দ্বারাই প্রকাশ পায়।
অবয়ব ও মুখাকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও সুসজ্জায়নে বিভিন্ন রং-এর প্রয়োগ ও নানা রকমের নিপুণ অংকন, পোশাক-পরিচ্ছদের নানা স্টাইল, দ্রব্যাদির নানা রং ও বর্ণময় ছবি, মিনা রচনা ও কারুকার্যখচিত আলপনা ইত্যাদির সমন্বয় ঘটে। ভাস্কর্য, কাঠের ওপর কারুকার্য সংক্রান্ত সমস্ত কাজে সৌন্দর্য ও রুচিশীলতাই প্রকট। কবিতা রচনা, কবিতা আবৃত্তি, ভাষার সচলতা ও নাটকীয় শৈল্পিক অভিব্যক্তি উন্নতমানে সম্ভবত সমান ব্যাপকতা লাভ করেনি; কিন্তু তা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে বিলীনও হয়ে যায়নি। এসব শিল্প-কুশলতার বহিঃপ্রকাশ ইন্দ্রিয়নিচয়কে প্রভাবিত করে। সৌন্দর্য বিষয়ক রুচিশীলতা এখান থেকেই পায় প্রাণ-স্পর্শ। নানা ধরণের সুগন্ধিময় ও সুস্বাদু উপাদেয় খাদ্য-পানীয়ও এ পর্যায়ে গণ্য।
একজন দক্ষ শিল্পী ও কারিগর যেসব জিনিস তৈরী করে, তাতে সমাজের লোকদের বিশেষ আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। একারণেই শিল্পীদের উচ্চ মান-মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। শিল্পীর নৈপুণ্যের দরুণ এসব দ্রব্যের অর্থনৈতিক মূলমানও বৃদ্ধি পায়। সৌন্দর্য-স্পৃহা ও রুচিশীলতার চরিতার্থতা বিধানের দরুন সামাজিক সন্তোষ ও পৃষ্ঠপোষকতা অর্জিত হয় এবং ক্রমশ এসব দ্রব্য জনগণের সৌন্দর্যবোধ এবং অথনৈতিক ও প্রকৌশলী মানদণ্ড প্রকাশের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়। দুর্লভ কারুকার্যখচিত শাল, কার্পেট, কম্বল, চাটাই ও পিতল নির্মিত তৈজসপত্র ও মিনা-করা থালা-বাসনও এর মধ্যে শামিল।
ধর্ম-বোধ ও শিল্প-কলা
অতি-প্রাকৃতিক (Super natural) সত্তায় মানুষের রয়েছে দৃঢ় প্রত্যয়। এ প্রত্যয় অতি সুপ্রাচীন। মূর্তি, ছবি, প্রতিমূর্তি (Statue), কারুকার্য, নকশা, সাধারণ অনুষ্ঠানাদি, মৃত্যু সম্পর্কিত কার্যাদি, কুরবানী বা বলিদান ইত্যাকার কাজগুলো তাকে এসব অতি-প্রাকৃতিক সত্তাসমূহের নৈকট্য লাভে সাহায্য করে; তার হৃয়াবেগকে উদ্বেলিত করে। মৃতের জন্য বিলাপ করা, গীত গাওয়া ও শোক-গাথা গাওয়ার ফলে লাশটি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে পরজগতে স্থানান্তরিত হয় বলে মনে করা হয়। প্রাচীন মিশরে মমির চতুঃপাশে নানা রূপ আলপনা ও মাঙ্গল্য চিত্র অংকন করা হতো। আর এভাবেই এক জগত থেকে অপর জগত পর্যন্তকার পথ অতিক্রম করা হতো। অন্যদিকে বড় বড় জন-সম্মেলনে নৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের কাজ সম্পন্ন করানো হতো। এখনো খৃষ্টানদের গীর্জায় গীত গাওয়া হয়, হিন্দুদের পূজা-মন্দিরে দেবমূতির্র সম্মুখে আরতি করা হয়। শিখ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও অনুরূপ কাজই করা হয়। গান-বাজনা তাদের ধর্মানুষ্ঠান ও পূজা-পার্বন অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অংশরূপে গণ্য। আর এসব শৈল্পিক দক্ষতাপূর্ণ অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সমবেত হয়ে সমস্ত কাজ-কর্ম একত্রে সম্পন্ন করে।
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-কলা
জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে সাহিত্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পযর্বেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষাও অপরিহার্য। শিল্প-কলা পরিবেশ পযর্বেক্ষণ ও অধ্যয়নের আগ্রহ ও উৎসুক্যের সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে শিল্প-কলারই সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। ফলে বৈজ্ঞানিক উপায় ও পদ্ধতির উৎকর্ষ লাভে পরোক্ষভাবে শিল্প-কলারও উৎকষের্র একটা পথ তৈরী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে উপকথা ও গল্প-উপাখ্যান, শিল্প ও বিজ্ঞানের সংমিশ্রণ আর এই সব সাংস্কৃতিক সুসংবদ্ধতা কোন বিশেষ জিনিস সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে বতর্মান থাকা জরুরী।
এক কথায় সংস্কৃতি একটি অত্যন্ত কল্যাণময় সত্য ও বাস্তবতা। মানুষের প্রয়োজন পরিপূরণে তার প্রয়োগ অত্যন্ত ফলপ্রসূ। সংস্কৃতি মানুষকে একটি আপেক্ষিক ও দৈহিক বিস্তৃতি ও বিশালতা দান করে। তার ফলে ব্যক্তিসত্তা লাভ করে সংরক্ষণ ও প্রতিরক্ষার অনুভূতি। পরন্তু ব্যক্তিত্বের সে বিস্তৃতিতে রয়েছে গতিময়তা। তা মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে যখন তার অন্তঃসারশূণ্য ও রিক্ত দেহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।
সংস্কৃতি মানুষের সামষ্টিক সৃষ্টি। তা ব্যক্তি মানুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মশক্তি ব্যাপকতর করে দেয়; চিন্তাশক্তিকে দেয় গাম্ভীর্য ও গভীরতা, দৃষ্টিকে করে সম্প্রসারিত। দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে তার উপস্থিতি কল্পনাতীত। কেননা এই সব কিছুর উৎস হচ্ছে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তা ও কর্মশক্তির সমন্বয়।
এ কারণে সংস্কৃতি ব্যক্তি সত্তাকে সুসংগঠিত রূপে ঢেলে গঠন করে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে এক অন্তহীন ধারাবাহিক জীবন দান করে। মানুষের কার্যাবলীর পারস্পরিক সামঞ্জস্য তার দৈহিক ও স্বভাবগত চরিত্রের কারণে ঘটে, মানুষ এ অর্থে কোন সামষ্টিক সত্তা নয়।
সংগঠন ও সামষ্টিক কর্মপদ্ধতি ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্নতা ও অক্ষুন্নতার ফসল। তা বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাবগত চরিত্রে বহুবিধ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। আর তা এভাবে মানুষের ওপর কেবল অনুগ্রহই বর্ষণ করে না, তার ওপর নানাবিধ দায়িত্বও আরোপ করে এবং তাকে বহু প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা পরিহার করতে উদ্বুদ্ধ করে। এর অনিবার্য পরিণতি সামষ্টিক কল্যাণ।
নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা এবং আইন ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা মানুষের কর্তব্য। কর্তব্য পালন ও বলন-কথনকে একটা বিশেষ ছাচে ঢেলে গড়ে নিতে হয় তাকে। তাকে এমন সব কাজ নিষ্পন্ন করতে হয়, যার কল্যাণ লাভ করে অন্যান্য বহু লোক। পক্ষান্তরে তার নিজের জরুরী কার্যাবলী সুসম্পন্ন করার ব্যাপারে তাকে অনুগৃহীত হতে হয় অন্য লোকদের।
সংক্ষেপে বলা যায়, মানুষের পর্যবেক্ষণ শক্তি ও দূরদর্শিতা এমন সব কামনা-বাসনার সৃষ্টি করে, যে সবের চরিতার্থতা ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-চর্চা পদ্ধতি এবং সাহিত্য ও শিল্পের উৎকর্ষ সাধন করে।
সংস্কৃতি মানব প্রকৃতির অন্তর্গত চাহিদার পরিতৃপ্তি ও চরিতার্থতারই ফসল। তা মানুষকে নিছক পশুর স্তর থেকে উন্নীত করে ভিন্নতর এক সত্তা দান করে। ফলে মানুষের নিতান্ত জৈবিক কামনা-বাসনা ও তার পরিতৃপ্তির ক্ষেত্র ও পরিধি সীমাবদ্ধ হয়ে যায়।
যন্ত্র নির্মাণকারী ও কর্মীসত্তা হিসেবে মানুষের প্রয়োজন বিপুল ও ব্যাপক। তার ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক সুস্পষ্টঃ
একজন ব্যক্তি (Individual) হিসেবে সে এমন একটি সমাজের সদস্য, যার লোকেরা পরস্পর মিল-মিশ ও কথা-বার্তার সূত্রে পরস্পর সংযুক্ত-সম্পর্কশীল। এহেন এক সহযোগিতা-ভিত্তিক শ্রমজীবি এককের (Unit)সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যিক ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের যিম্মাদার। অতীতের স্মৃতি তার মানসপটে চির-জাগ্রত। এ স্মৃতির সাথে রয়েছে তার মায়ার সম্পর্ক। কিন্তু তার সামনে অনাগত ভবিষ্যত। তারই ওপর নিবদ্ধ তার সমস্ত সত্তার লক্ষ্য-দৃষ্টি। এই ভবিষ্যতই তার হৃদয়-মনে আশা-আকাংক্ষার নির্মল আলো বিকীরণ করে।
শ্রমবণ্টন ও ভবিতব্যের সীমাহীন সম্ভাবনা এমন সব সুযোগ মানুষের সম্মুখে নিয়ে আসে, যার রূপ-সৌন্দর্য, চাক্চিক্য ও সুর-ঝংকারে তার হৃদয়-মন পরম উল্লাসে হয় চিরনৃত্যশীল।
সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য
ব্যক্তির সার্বিক সুস্থতা ও ক্রমপ্রবৃদ্ধির জন্যে তার দেহ ও প্রাণ বা আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ উৎকর্ষ একান্তই জরুরী। এ যেমন সত্য, তেমনি একটি জাতির উন্নতি তখনি সম্ভব, যখন তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা পুরোপুরি সংরক্ষিত হবে। কেননা সংস্কৃতি হচ্ছে প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে দেহ।
অর্থাৎ মানব জীবন দুটি দিক সমন্বিতঃ একটি বস্তুনির্ভর, অপরটি আত্মিক বা আধ্যাত্মিক। এ দুটিরই রয়েছে বিশেষ বিশেষ চাহিদা ও দাবি-দাওয়। সে চাহিদা পরিপূরণে মানুষ প্রতিমুহূর্ত থাকে গভীরভাবে মগ্ন ও ব্যতিব্যস্ত। একদিকে যদি দৈহিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজন তাকে টানে এবং জীবিকার সন্ধানে সে হয় নির্লিপ্ত, তাহলে তার আত্মার দাবি পরিপূরণ ও চরিতার্থতার জন্যে তার মন ও মগজ হয় গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।
তাই মানুষের বস্তুনিষ্ঠ বৈষয়িক প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান তার সহায়তা করে। আর ধর্ম-বিশ্বাস, শিল্প-কলা, সৌন্দর্যবোধ ও দর্শন নিবৃত্ত করে তার আত্মার পিপাসা। অন্যকথায়, ব্যক্তিদের সূক্ষ্ণ ও সুকোমল আবেগ-অনুভূতি এবং হৃদয় আত্মার দাবি ও প্রবণতা পূর্ণ করে যেসব উপায়-উপকরণ, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। সঙ্গীত, কবিতা, ছবি অংকন, ভাস্কর্য, সাহিত্য, ধর্মবিশ্বাস, দার্শনিক চিন্তা প্রভৃতি এক-একটা জাতির সংস্কৃতির প্রকাশ-মাধ্যম এবং দর্পণ। কোন বাহ্যিক ও বৈষয়িক উদ্দেশ্য লাভের জন্যে এসব তৎপরতা সংঘটিত হয় না। আত্মিক চাহিদা পূরণই এগুলোর আসল লক্ষ্য। এসব সৃজনধর্মী কাজেই অর্জিত হয় মন ও হৃদয়ের সুখানুভূতি-আনন্দ ও উৎফুল্লতা। একজন দার্শনিকের চিন্তা ও মতাদর্শ, কবির কাব্য ও কবিতা, সুরকার ও বাদ্যকারের সুর-ঝংকার-এসবই ব্যক্তির হৃদয়-বৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। এসবের মাধ্যমেই তার মন ও আত্মা সুখ-আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে। এসব মূল্যমান, মূল্যবোধ, হৃদয়ানুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাস থেকেই হয় সংস্কৃতির রূপায়ন। কিন্তু সভ্যতার রূপ এ থেকে ভিন্নতর। এখানে সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা তুলনামূলক পরিচয় দেয়া যাচ্ছেঃ
১. বস্তুনিষ্ঠ জীবনের প্রয়োজন পূরণ ও সাবলীলতা বিধানে যা কিছু সাহায্যকারী তা সভ্যতা নামে অভিহিত।
কিন্তু মন-মানস ও আত্মার কামনা-বাসনা ও সূক্ষ্ণ আবেগ-অনুভূতির চরিতাথর্তার উপায়-উপকরণকেই বলা হয় সংস্কৃতি।
২. বস্তুনিষ্ঠ জীবনের রূঢ় বাস্তব ও প্রকৃত উন্নতির স্তর ও পর্যায়সমষ্টি হচ্ছে সভ্যতা। বিশেষ-নির্বিশেষ সকলের পক্ষেই তার মূল্য ও মান হৃদয়ঙ্গম করা সহজ ও সম্ভব।
কিন্তু সংস্কৃতি অদৃশ্য ধারণা ও মূল্যমান সমষ্টি; তার মূল্যায়ন অতীব দুরূহ কাজ।
৩. সভ্যতা ক্রম-বিকাশমান, প্রতি মুহূর্ত উন্নতিশীল। প্রাচীন মতাদর্শের সাথে তার দূরত্ব ক্রম-বর্ধমান। তা নিত্য-নতুন দিগন্তের সন্ধানী।
কিন্তু সংস্কৃতি প্রাচীনপন্থী। প্রাচীনতম দৃষ্টিকোণ ও মতাদর্শ থেকে নিঃসম্পর্ক হওয়া তার পক্ষে কঠিন।
৪. সভ্যতা দেশের সীমা-বন্ধনমুক্ত- বিশ্বজনীন ভাবধারাসম্পন্ন। প্রায় সব চিন্তা-বিশ্বাসের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য।
কিন্তু সংস্কৃতির ওপর পরিবেশ ও ভৌগোলিক বিশেষত্বের ব্যাপক প্রভাব প্রবর্তিত হয়। অর্থাৎ সংস্কৃতি আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুলাংশে বন্দী; কেবলমাত্র সমমতের লোকদের পক্ষেই তা গ্রহণযোগ্য হয়। যেমন মুসলমান, হিন্দু, খৃস্টান ও বৌদ্ধদের সাংস্কৃতিক মেজাজ-প্রকৃতির ওপর তাদের বিশেষ ধমের্র সর্বাত্মক প্রভাব বিরাজিত। সেই সঙ্গে উপমহাদেশের একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও সংস্কৃতির দিক দিয়ে দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মুসলমানদের থেকে বহুলাংশে ভিন্নতর।
৫. সভ্যতা স্থিতিশীল ও দৃঢ়তাপ্রবণ। তার প্রভাব সহজে নিশ্চিহ্ন হবার নয়।
কিন্তু সংস্কৃতি প্রতিক্ষণ, প্রতিমুহূর্তই অস্থায়িত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরতার ঝুঁকির সম্মুখীন।
৬. সভ্যতা মানুষের বাহ্যিক জীবন নিয়ে আলোচনা করে। বস্তুগত প্রয়োজনাবলীই তার লীলাক্ষেত্র। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও বিভিন্ন শৈল্পিক দুর্লভ উপকরণ ও প্রতিষ্ঠানাদি (সভ্যতার মহাকীর্তি) এক দেশ ও জাতি থেকে ভিন্নদেশ ও জাতির মধ্যে চলে যেতে পারে। অনুন্নত জাতিগুলোও তা থেকে উপকৃত হতে পারে। স্বভাব-প্রকৃতিগত পার্থক্য তার পথে বাধা হতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তিই তা ব্যবহার করে কল্যাণ লাভ করতে পারে। তার কল্যাণ লাভে কোন প্রতিবন্ধকতাই নেই। বাছাই-প্রক্রিয়াও এখানে অচল।
কিন্তু সংস্কৃতি সাধারণত এক বংশ থেকে তারই অধঃস্তন বংশে উত্তরিত হয়। তা সম্যকভাবে অর্জিত হয় না। বাছাই-প্রক্রিয়া এখানে পুরোপুরি কার্যকর। কেবলমাত্র বিশেষ পরিমণ্ডলের লোকদের পক্ষেই তার কল্যাণ লাভ করা সম্ভব। দার্শনিকসুলভ চিন্তা-গবেষণা ও কবিসুলভ উচ্চমার্গতার অনুভূতি যার-তার পক্ষে আয়ত্তযোগ্য নয়।
৭. সভ্যতা অর্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজ কাজ। সেখানে তেমন কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়না। জাপান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতাকে আপন করে নিয়েছে; কিন্তু এ কার্যক্রমের ফলে তার সাংস্কৃতিক কাঠামো খুব শীগ্গীর প্রভাবিত হতে পারেনি। উপমহাদেশের জনগণের ওপর ইংরেজের শাসনকার্যের ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবে এখানকার সভ্যতা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানকার সংস্কৃতি তার আসল চরিত্র বা রূপরেখা হারায়নি।
কেননা সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ জীবন-কেন্দ্রিক। অন্তর্নিহিত জীবনই সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র। এই জীবনের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের মাধ্যম হচ্ছে সংস্কৃতি। অর্থাৎ সংস্কৃতি হচ্ছে মন ও মগজ-কেন্দ্রিক- আবর্তন-বিবর্তনের স্বতঃস্ফূর্ত ও উন্মুক্ত বহিঃপ্রকাশ। এই কারণে সংস্কৃতি স্বাধীন-মুক্ত সমাজ-পরিবেশেই যথার্থ উৎকর্ষ লাভ করতে পারে।
মোটকথা, আমরা যা ভাবি, চিন্তা করি, বিশ্বাস করি, তা-ই সংস্কৃতি। হৃদয়ানুভূতি, চিত্তবৃত্তি, আবেগ-উচ্ছ্বাস ও মানসিক ঝোঁক-প্রবণতার সাথে তার নিবিঢ় সম্পর্ক। কেননা এগুলো মানুষের মধ্যে স্বভাবগত ও প্রকৃতিকগতভাবেই বতর্মান। মানব-প্রকৃতি তার সাথে নিঃসম্পর্ক হতে পারে না কখনই। সভ্যতায় রয়েছে মানুষের সামাজিক ও অনৈতিক প্রয়োজনাবলীর প্রশ্ন। মানব জীবন যদি শিল্প-কারখানা ছাড়াই অবাধে চলতে পারে, এবং তার যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা হতে থাকে, তাহলে তার জন্যে সামান্যতম কাতর হওয়ারও কোন প্রয়োজন বোধ হবে না কারোর।
সভ্যতা ও সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু ঢালাওভাবে এটা ঠিক নয়। তবে এ দুটির মাঝে মূল্যমানের সাদৃশ্য অনস্বীকার্য। মোটরগাড়ি সভ্যতার উৎপাদন। সংস্কৃতি তাতে সৌন্দর্য, শোভনতা ও চিত্ত-বিনোদনমলূলক কারুকাজ ও সূক্ষ্ণ উপকরণাদি বৃ্দ্ধি করেছে। সভ্যতা আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মাণ করেছে; সংস্কৃতি সে প্রাসাদকে সুদৃশ্য, মহিমামণ্ডিত এবং বিস্ময়কর প্যাটার্নে সুশোভিত করে দিয়েছে। বস্তুত সভ্যতা ও সংষ্কৃতি দুটিই মানব জীবনের মৌল প্রয়োজন। যে জাতির জীবনে একসঙ্গে এ দুটিরই সমন্বয় ঘটেনি, তার উন্নতি অসম্ভব। সভ্যতা একটা জাতিকে বস্তুনিষ্ঠ শক্তিতে মহিমাময় করে আর সংস্কৃতি তাকে গতিবান করে নিভুর্ল পথে। মানব সভ্যতার আধুনিক পর্যায়ে এ দুটির মাঝে গভীর একাত্মতা প্রকট। তাই সভ্যতার অর্থে সংস্কৃতি বা সংস্কৃতি অর্থে সভ্যতাকে গ্রহণ করা কিছুমাত্র অশোভন নয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ এভাবেই পূর্ণ পরিণতি পযর্ন্ত পৌঁছে গেছে বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হবে না।
সংস্কৃতির সূচনা ও নানা দৃষ্টিকোণ
সমাজবিজ্ঞানী ও ঐতিহাসিকগণ সংস্কৃতির সূচনা ও ক্রমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ পেশ করে তার বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
কারোর দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেসব অঞ্চলে জৈবিক ও অর্থনৈতিক উপকরণের অনটন প্রকট, সেখানে প্রয়োজনের প্রবল তাগিদে মানুষ পরিশ্রম ও চেষ্টা-সাধনায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়। দুনিয়ার দিকে দিকে ও দেশে দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ে। ফলে নিত্য-নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংঘটিত হয়। এর ফলে নানা সংস্কৃতির পারস্পরিক মিশ্রণ ঘটে আর তার ফলে একটি নবতর সংমিশ্রিত রূপের উদ্ভব হয়।
অনুরূপভাবে যেসব দেশের আবহাওয়ায় আর্দ্রতার অংশ শতকরা ৭৫ ভাগ বা ততোধিক সেখানে ঝড়-ঝাপটা ও ঝঞ্ঝা-তুফান নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এর দরুণ সেখানকার জনজীবন কঠিনভাবে বিধ্বস্ত হয়। তাদের মন-মানসিকতার ওপর এর তীব্র প্রভাব প্রতিফলিত হওয়া অবধারিত। এই পরিমণ্ডলের লোকেরা বাধ্য হয়ে স্থানান্তরে গমন করে ও ভিন্নতর অনুকূল পরিবেশের সন্ধানে ছুটে যায় এবং নিজেদের চেষ্টায় এমন সব স্থানে গিয়ে বসবাস শুরু করে, যেখানে তাদের মনের আশা-আকাংক্ষা উজ্জীবিত হয়, চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি ও বোধশক্তি পায় তীব্রতা-তীক্ষ্ণতা। প্রাচীনতম কালে পৃথিবীর বিশেষ কয়েকটি অঞ্চল সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাকেন্দ্র ছিল। এশিয়ায় দজলা ও ফোরাত নদীর উপকূল, গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর বেলাভূমি, আফ্রিকার নীল উপত্যকা, ইউরোপে টায়র উপত্যকা-যার উপকূলে রোম শহর অবস্থিত ইত্যাদি এ পর্যায়ে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। অনুরূপভাবে আজ থেকে প্রায় পনেরো শো বছর পূর্বে মেক্সিকো (Mexico), হন্ডুরাস (Honduras) ও গুয়েতেমালায় (Guatemala) মায়েন (Mayan) সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল।
অতীতের মূল্যবান জাতীয় সম্পদের অবলুপ্তি, দাসপ্রথার ব্যাপক প্রসার এবং অবসাদ-অবজ্ঞায় অভ্যস্ত হওয়ার ফলেও জাতিসমূহের রীতি-নীতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। গ্রীক ও ভারতীয় সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল তাদের দেশসমূহের ভৌগোলিক ধরণ-ধারণের কারণে। এসব দেশের নদ-নদীর বেলাভূমি এবং উপত্যকাসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। মরুচারী জীবন পদ্ধতিতে দুগ্ঘ ও গোশত প্রচুর পরিমাণে সহজলভ্য হওয়ার দরুণ সেখানকার অধিবাসীরা শক্তি ও বীরত্ব-গুণে ধন্য হয়ে থাকে আর তার ফলেই তাদের মধ্যে কঠোরতা নির্মমতা ও স্বৈরাচারমূলক ভাবধারা তীব্রতর রূপে দেখা দেয়। এ শ্রেণীর লোকেরা দুনিয়ার দিকে দিকে বিজয়ী ও শাসক হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। বেবিলনীয়, আসিরীয়, কালদানীয় এবং দজলা ও ফোরাত অঞ্চলের সংস্কৃতিসমূহের উৎকর্ষ ও প্রসার লাভের পিছনে এই কারণই নিহিত রয়েছে। তারা মধ্য এশিয়া থেকে উত্থিত হয়ে পারস্য ও ভারতীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে আধুনিক ইউরোপের গুরুর মর্যাদা লাভ করে। এই মরুচারী লোকেরাই কাব্য-সাহিত্য ও নানা ধর্মমতের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠাতা হয়ে দাঁড়ায়।
ইতিহাসবিদ-দার্শনিক ইবনে খালদুন এবং আধুনিক কালের বিশ্ব-বিশ্রুত ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবি (Arnold Toyenbee) এ সম্পর্কে যে দৃষ্টিকোণ পেশ করেছে তা এখানে উল্লেখযোগ্য। তা হলঃ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে মানুষ নিজেদের প্রাচীন জীবনধারা পরিত্যাগ করে এবং নবতর দিগন্তের সন্ধানে দিশেহারা হয়ে নানা দেশে ও নানা অঞ্চলে ঘুরে বেড়ায় আর এভাবেই সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপিত হয়।
এভাবে জনতার স্থানান্তর, মরু পরিক্রমা, যাযাবর জীবন-ধারা, চিন্তা-বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধের ধরণ প্রভৃতি সংস্কৃতির ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ইতিহাস-পূর্ব কালের ব্যবসায়িক সড়ক, রোম্যান গীর্জা এবং বিভিন্ন ধরণের রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতি একালের সংস্কৃতির ওপর খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে। কাল-পরিক্রমায় দক্ষিণ আমেরিকা, মধ্য আফ্রিকা, দূরপ্রাচ্য ও ভূমধ্যসাগরিয় এলাকার প্রাচীনতম সংস্কৃতিসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তার কারণ এই যে, স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ডের অধিবাসীরা নিজেদের শিক্ষাগত, রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক তৎপরতার সাহায্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে ঐসব অঞ্চলের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম-চিহ্ন ও প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত ও নিঃশেষ করে দিয়েছে। অন্যদিকে নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সংস্কৃতিসমূহ পশ্চাদপদ রয়ে গেছে ।কেননা উন্নতিশীল রাষ্ট্রগুলো থেকে এ অঞ্চলগুলো বহুদূরে অবস্থিত ছিল এবং উন্নতি ও বিকাশ লাভের কোন কারণ বা উদ্যোগই সেখানে ছিলনা। বৈদেশিক আক্রমণ থেকেও এদেশগুলো মুক্ত রয়েছে এবং দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা-সংস্কৃতিরও কোন ছায়াপাত ঘটেনি এসব দেশের ওপর। নৈসর্গিক উপায়-উপকরণ দুনিয়ার সব দেশের মানুষের জন্যেই সমান। কিন্তু বংশীয় পার্থক্য-বৈষম্য, দৈহিক-মনস্তাত্বিক বিশেষত্ব, লিঙ্গগত প্রভেদ, সমাজের বিশেষ গঠন-প্রণালী ও নিয়মতন্ত্র একটি বিশেষ ধরণের অবয়ব গড়ে তোলে এবং এগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্বও একটি নবতর বিজয়ী সংস্কৃতির অস্তিত্ব ও উৎকর্ষ দান করে। সংস্কৃতির উৎকর্ষে এমন একটা পর্যায়ও আসে, যখন অধিকতর উৎকর্ষ লাভ ও তার সম্ভবনা ম্লান হয়ে আসে। তবে বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণ, অর্থনৈতিক তৎপরতা ও গণতান্ত্রিক শাসন-পদ্ধতি সংস্কৃতির উৎকর্ষে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে।
বিশ্বজনীন সংস্কৃতি
আধুনিক সভ্যতা এক বিশ্বজনীন সংস্কৃতিরই বিকশিত রূপ। তাতে বিভিন্ন সংস্কৃতির নির্যাস ও বাছাই-করা উপাদান নিঃশেষে লীন হয়ে রয়েছে। গ্রীক, রোমান, তুরান প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য সুসভ্য ও সংস্কৃতিবান জাতির উত্তরাধিকার এতেই একীভূত। তার কারণসমূহ এইঃ
১. দূরত্বের ব্যবধান নিঃশেষ হওয়া
২. নিকটতার সম্পর্ক-সম্বন্ধ
৩. অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা
৪. রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিন্ন ধারণা
৫. অভিন্ন ও সদৃশ ভাষা ব্যবহার
যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত পরিবর্তনশীলতা দেশে ও জাতিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। পূর্বের যে দূরত্ব লোকদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল, এক্ষণে তা সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারা পরস্পরের ঘনিষ্ট ও নিবিড়তম সান্নিধ্যে আসতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও যোগাযোগ যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতাও বৃ্দ্ধি পেয়েছে বহুলাংশে। তার ফলে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন জাতি পারস্পরিক দেখাদেখি ও রাজনৈতিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছে খুবই স্বাভাবিকভবে। সংসদীয় গণতন্ত্র ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা এবং প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতির মধ্যে একারণেই টাগ-অব-ওয়ার চলছে। সম্পর্ক-সম্বন্ধ স্থাপনে ভাষার অভিন্নতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এক্ষেত্রে ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কেননা দুনিয়ার অধিকাংশ দেশে তুলনামূলকভাবে খুব বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে এ দুটি ভাষা। ফলে জাতি ও মিল্লাতসমূহ নিজেদের একক ও সামষ্টি বিরোধ-বিসম্বাদ সত্ত্বেও একটি বিরাট পরিবারের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এক্ষেত্রে স্বার্থের অভিন্নতা এবং আবেগ অনুভূতিতে একই ভাবধারার প্রবাহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।
ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনা
ইসলামী সংস্কৃতিঃ ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। একজন্যই তা এক আপোষহীন ‘দ্বীন’ নামে অভিহিত। তার নির্দিষ্ট সীমা বা পরিমণ্ডলের ভেতর মানুষ নিজ ইচ্ছা প্রয়োগ করতে পারে। ইসলামের নির্ধারিত এ সীমা অপরিববর্তনীয়, চিরন্তন ও শাশ্বত সত্যের ধারক। বিশ্বলোকের চিরন্তন মূল্যমানের উৎস যে খোদায়ী গুণাবলী তা ইসলামের সীমার মধ্যে নিজের আয়ত্তাধীন করে নিতে প্রত্যেক ব্যক্তিই সক্ষম হতে পারে।
ইসলামী বিধানের অধীনের ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন শৃংখলা (Discipline) ও নিয়মানুবর্তিতার সৃষ্টি হয়, যার দরুন খোদায়ী গুণাবলীর আনুপাতিক প্রতিফলন হওয়া সম্ভবপর। ইসলামের পরিভাষায় একেই বলা হয় ই’তিদাল-ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা।
সেখানে ব্যক্তিগণের মধ্যে এমন যোগ্যতার উদ্ভব হয়, যার ফলে প্রকৃত বিজয়ের সুফলকে বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়।
ইসলামের উপস্থাপিত বিশ্বভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার এককত্ব ও অনন্যতা এবং জাতীয় সংহতি ও অখণ্ডতার সুদৃঢ় ধারণা এমন এক একাত্মতা ও অভিন্নতার সৃষ্টি করে যার দরুন মানব সমাজের বাধ্যবাধকতা নিঃশেষে দূরীভূত হয়ে যায়।
এই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি অপরের জন্যে জীবিত থাকে বিধায় সমস্ত ব্যক্তির জীবন-প্রয়োজন স্বতঃই পূর্ণ হতে থাকে।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতিঃ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দার্শনিক ভিত্তি হচ্ছে-এই জীবনটা কতকগুলো মৌলিক উপাদানের আপতিক বা দুর্ঘটনামূলক সংমিশ্রণে অস্তিত্ব লাভ করেছে। তার মূলে কোন উদ্দেশ্য নেই; তার লক্ষ্য ও পরিণতি বলতেও কিছু নেই। এসব উপাদানের বিশ্লিষ্ট ও বিক্ষিপ্ত হওয়ারই নাম মৃত্যু। এই মৃত্যুর পর আর কোন জীবন অকল্পনীয়। জীবন একটা দুর্ঘটনা মাত্র। তাই দুনিয়ায় নেই কোন শাশ্বত মূল্যমান-নেই কোন দায়-দায়িত্ব, কোন প্রতিশোধ বিধান।
এই চিন্তা দর্শনে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা কল্যাণকর, তা-ই ভালো। অন্য ব্যক্তি বা জাতির জীবন-শিরা যদি তাতে ছিন্ন-ভিন্নও হয়ে যায়, তবু তা ভালোই। পক্ষান্তরে ব্যক্তি ও জাতির পক্ষে যা-ই ক্ষতিকর,তা-ই মন্দ –তাতে অন্যান্য মানুষের বা জাতিসমূহের যতই কল্যাণ নিহিত থাক না কেন।
এক কথায় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি সম্পূর্ণত স্বার্থবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল। একারণে দুনিয়ার বিভিন্ন ব্যক্তি ও জাতির মধ্যে কঠিন দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ-বিগ্রহই তার অনিবার্য পরিণতি। পাশ্চাত্য সমাজে ভাঙন ও বিপর্যয়ই সাধারণ দৃশ্য। সেখানে শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিত, মালিক ও শ্রমিক এবং শোষক ও শোষিত শ্রেণীগুলোর মধ্যে সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।
বিজিত ও পদানত জাতিসমূহের সেখানে প্রকৃতি বিজয়ের মূল তত্ত্ব বা রহস্য উন্মোচনে শরীক করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিরোধী জনমনে দৃঢ়মূল করে দেয়াই তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
মানব জীবনে সংস্কৃতির ভূমিকা
ভাষা-বিশেষজ্ঞরা ‘সংস্কৃতি’ শব্দটিকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। ভূমি চায় বা জমি কর্ষণ, শিক্ষা-দীক্ষার সাহায্যে মন-মানসের পরিচ্ছন্নতা ও উৎকর্ষ বিধান, নৈতিক-চরিত্র ও মানসিক যোগ্যতার পরিবর্ধন, স্বভাব-মেজাজ, আলাপ-ব্যবহার ও রুচিশীলতার পরিমার্জন এবং এসব উপায়ে কোন জন-সমাজ বা জাতির অর্জিত গুণ-বৈশিষ্ট্য –এসবই ‘সংস্কৃতি’ শব্দে নিহিত ভাবধারা। এ থেকেই সংস্কৃতির অর্থ করা হয় ‘অর্জিত কর্মপদ্ধতি’। এ অর্জিত কর্মপদ্ধতিতে রয়েছে আমাদের অভ্যাস, ধরণ-ধারণ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মূল্যমান, যা এক সুসংবদ্ধ সমাজ বা মানবগোষ্ঠী কিংবা একটা সঠিক পরিবার-সংস্থার সদস্য হওয়ার কারণে আমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে। আমরা নিজেরা তা রক্ষা করে চলি এবং মনে মনে কামনা পোষণ করি তার উৎকর্ষ ও বিকাশ লাভের।
সংস্কৃতির এ তাৎপর্য অনেক ব্যাপক-ভিত্তিক। এর মধ্যে শামিল রয়েছে এমন সব জিনিসও, যাকে সাধারণত এর অন্তর্ভুক্ত মনে করা হয় না। ব্যাপক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে বোঝা যাবে, প্রতিটি কর্মপদ্ধতির মূলে রয়েছে কতকগুলো বিশেষ কার্যকারণ; সেগুলো কি সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়? আমাদের মধ্যে ক্ষুধার উন্মেষ হয়, আমরা তা দূর করার চেষ্টায় লিপ্ত হই; সেজন্যে কিছু-না-কিছু কাজ আমরা করে থাকি। ক্ষুধা নিবারণ-শুধু ক্ষুধা নিবারণ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত নয়; কিন্তু যে নিয়মে আমরা ক্ষুধা নিবৃত্ত করি, সেজন্যে যে ধরণের খাদ্য আমরা গ্রহণ করি এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহে আমরা যে নিয়ম ও পন্থা অনুসরণ করি, তা সবই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। আমাদের যৌন-প্রকৃতি কিংবা বলা যায় যৌন কার্যকারণ- মূলত একটি দৈহিক প্রবণতা; তার সাথে সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটে এমন বিশেষ পন্থা ও পদ্ধতিতে, যা মানস সমাজের বিশেষ অভ্যাস ও রসম-রেওয়াজের অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। এই দিক দিয়ে এই বিশেষ ধরণ ও পদ্ধতি অবশ্যই সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত।
সংস্কৃতিক পরিবেশ
মানবতা-বিশেষজ্ঞরা সংস্কৃতির সাধারণ মূলনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। যে কর্মপদ্ধতি সব সংস্কৃতিতেই সমানভাবে বিরাজমান এবং সব সংস্কৃতির জন্যেই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হচ্ছে ভাষা; এটি স্বতঃই সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ আর দ্বিতীয় হচ্ছে পারিবারিক সংগঠনের কোন না কোন রূপ। বস্তুত কোন সংস্কৃতিই তাকে জানবার ও তার আত্মপ্রকাশের উপায় ও মাধ্যম ছাড়া বাঁচতে পারে না। অনুরূপভাবে বংশ সংরক্ষণের কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ব্যতিরেকে সংস্কৃতিই স্বীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখতে পারেনা। এর চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ সত্য এই যে, সংস্কৃতি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সাধারণ মূলনীতির মর্যাদার অধিকারী হয়ে থকে। মানুষ কোথাও একত্রে বসবাস করবে অথচ তার কোন সংস্কৃতিই থাকবেনা, এটা অসম্ভব; অন্তত এরূপ এক মানব-সমষ্টির অস্তিত্ব ধারণাই করা যায় না। এমন কি দুনিয়ার ও লোক-সমাজের সাথে সর্বপ্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে যে ব্যক্তি নিবিড় অরণ্যের এক নিভৃত কোণে বসে আছে, যে মনে করে নিয়েছে যে, সে দুনিয়ার সব নিয়ম-নীতিকেই পরিহার করে চলেছে, মূলত সে-ও অবচেতনভাবে অন্য লোকদের কাছ থেকে নেয়া কিছু-না-কিছু নিয়ম-নীতি অবশ্যই পালন করে চলছে-সে তা স্বীকার করুক আর না-ই করুক। তার চিন্তা-বিশ্বাস, তার কাজ-কর্ম সারা জীবন ধরে তার সঙ্গে লেগেই থাকে; কিন্তু তা কোথায় যে রয়েছে এবং কবে থেকে, তা সে বুঝতে এবং জানতেই পারে না।
সংস্কৃতির এ সার্বিক বৈশিষ্ট্যকে মানবীয় বিকাশের ফসল বলা যেতে পারে অনায়াসেই। মানুষ সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারছে শুধু এজন্যে যে, সে নিজের মধ্যে এমন কিছু যোগ্যতা ও প্রতিভার লালন ও বিকাশ সাধনের সাফল্য অর্জন করেছে, যার ফলে সংস্কৃতির সৃষ্টি তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সংস্কৃতির উদ্ভাবন করে মানুষ যেন নিজেরই পরিবেষ্টনীর এক নব-দিগন্তের সৃষ্টি করে নিয়েছে। এর ফলে পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া খুবই সহজ হয়েছে তার পক্ষে। আর এ সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে সেদিন থেকেই, যেদিন এ দুনিয়ার বুকে মানব জীবনের প্রথম সূর্যোদয় ঘটেছিল সেই দূর অতীতকালে।
এ জমিনের বুকে সেই প্রথম যেদিন মানুষের আবির্ভাব হয়েছিলো, সেদিন থেকে মানুষের জ্ঞান ও বুদ্ধির যথেষ্ট বিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের এ সংস্কৃতির বাহ্য রূপও বিবর্তিত হয়েছে অনেক। মানব জীবনের সেই প্রথম পর্যায়টি ছিল সর্বতোভাবে স্বভাব-ভিত্তিক – স্বভাব-নিয়মে চলত সে জীবনের দিনগুলো। খাদ্য গ্রহণ এবং বসবাস করার ধরণ-ধারণ ও নিয়ম-পদ্ধতি ছিল অতীব স্বাভাবিক ও স্বভাব-নিয়মসম্মত। কোন কৃত্রিমতার অবকাশ ছিলনা সে জীবনে। সেকালে খাদ্য আহরণের ক্ষেত্র ছিল এই বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতি, জীবনযাত্রা ছিল প্রকৃতি-কেন্দ্রিক, সহজ ও স্বচ্ছন্দ। মানুষ ক্রমশ এখানে তার অন্তর্নিহিত কর্মক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রকৃতিকে নিজের জীবন-যাত্রার অনুকূল করে তুলতে শুরু করে। প্রকৃতির বুকে মানুষের শক্তি-প্রয়োগের যে অভিযান সেদিন শুরু হয়েছিল, ক্রমবিকাশের নানা স্তর অতিক্রম করে, তা আজো সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে সব বাধা ও প্রতিবন্ধকতাকে চূর্ণ করে, দুমড়ে দিয়ে। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজের ব্যবহারে লাগাবার জন্যে মানুষ তৈরী করে নিয়েছিল নানা হাতিয়ার। দিন যতোই অগ্রসর হয়েছে মানুষ এ প্রকৃতির বুকে পেয়েছে নানা অপূর্ব সম্পদ ও মহামূল্য দ্রব্য-সম্ভারের সন্ধান এবং তাকে ব্যবহার করার জন্যে মানুষ তৈরী করেছে তার উপযোগী হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি। এতে করে মানুষের চিন্তা-শক্তি একদিকে যেমন বিকশিত হয়েছে, তেমনি হয়েছে তাতে সূক্ষ্ণতা, গভীরতা ও বিশালতার উদ্ভব। তাই আজ একদিকে মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভার অপূর্ব বিকাশ সাধিত হয়েছে, অপরদিকে মানুষ তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে বহু বিচিত্র ধরণের জটিল ও জটিলতর যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার। আজ মানুষ সক্ষম হয়েছে জটিলতার ও সূক্ষ্ণতর কর্ম সম্পাদনে। মানবীয় সংস্কৃতির বর্তমান বিকশিত রূপ মানুষের বুদ্ধি এবং কর্মদক্ষতা উভয়েরই পরিণতি। কিন্তু এ বিকশিত রূপ যতোই বিভিন্ন ও বিচিত্র হোক না কেন, মানব প্রকৃতির আসল রূপ আজো ঠিক তা-ই রয়ে গেছে, যা ছিল তার বৈষয়িক জীবনের প্রথম সূচনাকালে। পরিবর্তন ও বিবর্তন হয়েছে অনেক; কিন্তু তা সবই বাহ্যিক-পোশাকী পর্যায়ের। বিবর্তন ও পরিবর্তনের এ আঘাত মানব-প্রকৃতির মূল ভাবধারায় পারেনি কোন পরিবর্তন সূচিত করতে। এ এমনই এক সত্য, যা মানব-প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারেনা।
মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক কি? মানুষ কি প্রকৃতির দাস, না মানুষের অধীন এই প্রকৃতি? প্রকৃতি কি মানুষকে নিজের মতো গড়ে তোলে, না মানুষ নিজের মতো গড়ে নেয় প্রকৃতিকে? এ এক জটিল এবং অত্যন্ত মৌলিক প্রশ্ন। প্রকৃতি ও মানুষ সম্পর্কে যত গভীর ও সূক্ষ্ণ চিন্তাই করা যাবে, ততোই এ সত্য প্রতিভাত হয়ে উঠবে যে, কথাটি কোন দিক দিয়েই পুরোমাত্রায় সত্য নয়; বরং সর্বদিক দিয়েই তা আধা-সত্য। মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, একথা ঠিক; কিন্তু প্রকৃতি ছাড়া মানুষের জীবন ধারণাতীত। প্রকৃতি মানুষকে নিজের মত গড়ে; কিন্তু সে গড়ন বাহ্যিক-দৈহিক মাত্র। মানসিকতার কোন নব রূপায়ন বা তাকে নতুনভাবে ঢেলে তৈরী করা প্রকৃতির সাধ্যের বাইরে; বরং দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতির ওপর নিজের সূক্ষ্ণ বুদ্ধিবৃত্তি, প্রতিভা ও অপ্রতিহত কর্মক্ষমতার সুস্পষ্ট ছাপ আঁকতে পারে। মানুষ প্রকৃতির ওপর নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করতেই সতত সচেষ্ট। সে নিজের ইচ্ছা মতো তার পরিবেশকে গড়ে তুলতে চায়। সেজন্যে সে নিজের অভিপ্রায় অনুসারে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করে, প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে এবং প্রকৃতির কাঁচা মালকে নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রয়োগ করে সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস তৈরী করে নেয়; কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা যায়, মানুষ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে কোনরূপ পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম হয়নি; বরং মানুষের বুদ্ধি-প্রতিভা, চিন্তা-গবেষণা ও কর্মশক্তির যা কিছু প্রয়োগ, তা এই প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই কার্যকর হয়ে থাকে, তার বিপরীত কিছু করা সম্ভব হয়না মানুষের পক্ষে।
মানুষের সাংস্কৃতিক ভাবধারায় এরই সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। মানুষ এখানে এক নির্জীব পদার্থের মত পড়ে থাকতে প্রস্তুত নয়। সে চায় নিজের ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে যেতে স্বীয় পরিবেশ ও প্রকৃতির বুকে। এজন্যে সে গভীর চিন্তা-ভাবনা, গবেষণা ও পরিকল্পনা শক্তি এবং কর্মের ক্ষমতা ও সামর্থ্য এ দুটিকেই পুরোমাত্রায় প্রয়োগ করে। আর মনের সুষমা মিশিয়ে সে এখানে যা কিছু করে, যা কিছু বলে, যেভাবে জীবন যাপন করে, যেভাবে লোকজনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, যেভাবে পরিবার, সমাজ, অর্থ-সংস্থা ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলে, তার সব কিছুতেই তার নিজস্ব চিন্তা-বিশ্বাস, ধারণা-অনুমান ও কর্মক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এভাবে মনের ও মানসিকতার যে প্রতিফলন ঘটে সমগ্র পরিবেশের ওপর আমাদের ভাষায় তাকেই আমরা বলি সংস্কৃতি। এ হচ্ছে মানসিক ভাবধারা ও মানসিকতারই বাহ্য প্রকাশ। তাই যা ব্যক্তির মানসিকতা, যা তার মানসিক ভাবধারা, তা-ই সংস্কৃতির মূল উৎস এবং একই মানসিকতাসম্পন্ন বহু মানুষের বাস্তব জীবনের এ মৌল উৎসের যে প্রতিফলন ঘটে, তা-ই সে সমাজের সংস্কৃতি।
ব্যক্তি জীবন সমাজ-নিরপেক্ষ নয়, হতে পারেনা। ব্যক্তি-মানসিকতা সংস্কৃতির যে মৌল উৎস, তারও সামাজিক ও সামষ্টিক প্রতিফল এবং প্রতিষ্ঠা একান্তই স্বাভাবিক। এর ব্যত্যয় হতে পারেনা কখনো। তাই ব্যক্তি-সংস্কৃতি শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে ব্যক্তির সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে পারেনা। তার বিকাশ, প্রকাশ, সম্প্রসারণ ও পরিব্যপ্তি অবশ্যম্ভাবী। এটাই হচ্ছে সংস্কৃতির পরিবেশ।
সংস্কৃতির নিজস্ব ভাষা প্রয়োজন। এমন কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায়না, যার নিজস্ব কোন ভাষা নেই-নেই নিজস্ব কোন পরিভাষা। সংস্কৃতি যতই জটিল সূক্ষ্ণ হোক এবং তার প্রকাশ যতই কঠিন হোক না কেন, মানসিক ভাবধারা প্রকাশের প্রয়োজনীয়তাও হয় ততই তীব্র। মানব মনের চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা স্বতঃই প্রকাশের মুখাপেক্ষী-প্রকাশপ্রবণ। এর প্রাব্যল্য যত তীব্র হবে, মানুষের মগজও হবে তত বেশী কর্মক্ষম ও সৃজনশীল। মন ও মগজের এ বিকাশশীলতার চাপে মানুষের সংস্কৃতিও হয়ে ওঠে ততই বিকাশমান ও গঠনোন্মুখ। এভাবে সংস্কৃতির যতই অগ্রগতি ঘটে, জন-মানস এবং মানসিকতাও ততই উৎকর্ষ লাভ করে আর মানুষও তার সাথে সামঞ্জস্য স্থাপনে ততই সক্ষম হয়ে ওঠে। এর ফলে মানব-বংশের ক্রমবিকাশের সাথে সাথে মানব-সংস্কৃতিরও প্রকাশ ঘটে নানাভাবে, নানা রূপে এবং নানা উপায়ে। এজন্যে বলতে হবে, মানুষ ও সংস্কৃতি পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত-অবিচ্ছিন্ন।
বিকাশমান দুনিয়ার সংস্কৃতি
এতক্ষণ যা কিছু বলা হল, তা দ্বারা সংস্কৃতি সম্পর্কিত ধারণাকে স্পষ্টতর করে তুলতেই চেষ্টা করা হয়েছে। সংস্কৃতি যে আমাদের জীবনের জন্যে অপরিহার্য, আমাদের জীবন গঠনে তার ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং গভীরভাবে প্রভাবশালী এবং কাযর্কর তা এ আলোচনা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে, আশা করি। বস্তুত সংস্কৃতি মৌল ভাবধারার দিক দিয়ে একটি প্রবহমান নদী। এ নদী যেখান থেকেই প্রবাহিত হয়, জীবনের অস্তিত্ব, অবয়ব ও চৈতন্যের ওপর তার গভীর স্বাক্ষর রেখে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ সংস্কৃতি-নদীর প্রবাহ সাধারণ মানুষের দৃষ্টির আড়ালেই থেকে যায়। তারা হয় তা দেখেতেই পায় না কিংবা দেখেও ঠিক অনুভব করতে সক্ষম হয় না। তাকে দেখবার ও অনুভব করার জন্য চাই অনুভূতিশীল মন এবং সূক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন চোখ। কথাটি এভাবেও বলা যায় এবং তা বলা যুক্তিযুক্তই হবে যে, অনুভূতিশীল মন এবং দৃষ্টিসম্পন্ন চোখই সংস্কৃতির প্রয়োজন অনুভব করতে পারে- স্পষ্টত অবলোকন করতে পারে তার ভালো ও মন্দ রূপ। আর নদীর ঘোলা-পানির পরিবর্তে পরিচ্ছন্ন ও স্বচ্ছ পানি গ্রহণের ন্যায় পংকিল সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে পবিত্র ও নির্মল ভাবসম্পন্ন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারে কেবলমাত্র সচেতন লোকেরাই। যাদের মন চেতনাহীন, মগজ বুদ্ধিহীন ও চোখ আলোশূণ্য, সংস্কৃতির প্রবহমান দরিয়া থেকে তারাও আকণ্ঠ পানি পান করে বটে; কিন্তু সে পানি হয় ঘোলাটে ময়লাযুক্ত, পুঁতিগন্ধময় ও অপরিচ্ছন্ন। এজন্য সংস্কৃতির শালীন, পরিচ্ছন্ন ও পরিত্র এবং অশালীন ও অপরিচ্ছন্ন তথা পংকিল ও কদর্য-এ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়া একান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার-ঠিক যেমন প্রবহমান নদী-নালায় এ দু ধরণেরই পানিস্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হতে থাকে চিরন্তনভাবে। যেসব লোক অন্ধ ও অচেতনভাবে স্বীয় সংস্কৃতির চতুঃসীমার মধ্যে থাকে অথচ তার প্রয়োজন ও দাবি-দাওয়ার সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করেনা, সেজন্যে তারা কোন সচেতন ও সজাগ চেষ্টায় নিয়োজিত হয়না-সেজন্যে তাদের ভেতর জেগে ওঠেনা কোন আত্মানুভূতি, তারা এই শেষোক্ত পর্যায়ের সংস্কৃতিরই ধারক হয়ে থাকে। কেননা তাদের মতে সংস্কৃতি কখনো ভাল বা মন্দ কিংবা স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে না- হতে পারেনা তা পবিত্র ও শালীনতাপূর্ণ।
আমাদের কর্মনীতি, কার্যপদ্ধতি ও মূল্যমান বরং আমাদের চিন্তা-ভাবনা সবকিছুই আমাদের সংস্কৃতির ফসল। সংস্কৃতিই এসব গড়ে তোলে পরিচ্ছন্ন ও শালীনতাপূর্ণ করে। মানবীয় চেতনায় ও বোধিতে যা কিছু বিশ্লিষ্টতা থাকে স্বাভাবিকভাবে, সাংস্কৃতিক অনুভূতি ও নিজস্ব মূল্যবোধই তাকে উৎকর্ষ দান করে, সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রূপে গড়ে তোলে। এটাই মানুষকে অবচেতনার অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে চেতনার আলোকোজ্জ্বল পরিবেশ তথা বাইরের দুনিয়ায় নিয়ে আসে এবং তাকে প্রস্ফুটিত করে তোলে। কিন্তু তাই বলে তার মৌল সাংস্কৃতিক চেতনায় কোন ব্যতিক্রম ঘটেনা-ঘটেনা কোনরূপ পরিবর্তন। অবশ্য একথা ঠিক যে, সংস্কৃতি মানুষের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ মাধ্যম। অন্য কথায়, কোন জাতির সংস্কৃতি সে জাতির তাবৎ লোকদের মানসিক যোগ্যতা-প্রতিভারই প্রতিবিম্ব। এজন্যে একদিকে যেমন বলা যায় যে, অসভ্য জাতিগুলোর সংস্কৃতিবোধ ও সাংস্কৃতিক প্রকাশ নিম্নমানের হয় এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারও বিকাশ ঘটে, তেমনি অপরদিকেও বলা যায় এক-এক ধরণের আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ হয় এক এক ধরণের। অর্থাৎ বিভিন্ন রূপ আকীদা-বিশ্বাস ও জীবন-দর্শন বিশিষ্ট জাতির সংস্কৃতি ও তার প্রকাশ বিভিন্ন রূপ হতে বাধ্য। কেননা সংস্কৃতির মৌল উৎস জীবনবোধ, চিন্তা-বিশ্বাস ও মানসিকতা। অতএব জীবন-দর্শনের পার্থক্যের কারণে সাংস্কৃতিক বোধ ও প্রকাশেও অনুরূপ পার্থক্য হওয়াই অনিবার্য ব্যাপার। সংস্কৃতির এ পার্থক্যের প্রতিফলন ঘটে লোকদের মননে ও জীবনে এবং মৌল অনুভূতিতে যেমন, তার প্রকাশ মাধ্যমেও তেমন। তাই ইতিহাসে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, এক ব্যক্তির এক প্রকারের জীবন-দর্শন থাকাকালে তার মানসিক অবস্থা ও জীবন-চরিত্র ছিল এক ধরণের; কিন্তু পরবর্তীকালে তার সে জীবন-দর্শনে যখন মৌলিক পরিবর্তন সূচিত হল, তখন তার মানসিকতা, জীবনবোধ ও চরিত্রেও আমূল পরিবর্তন সুস্পষ্ট হয়ে উঠল-তার সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রকাশ-মাধ্যমও গেল সমূলে বদলে। এ পরিবর্তনের মূলে জীবন-দর্শনের পরিবর্তন ছাড়া আর কোন কারণই পরিদৃষ্ট হয়না। আরব জাতির ইতিহাসই এ পর্যায়ের দৃষ্টান্ত। যে আরব জনগণ ছিল সভ্যতা-ভব্যতা ও শালীনতা-শিষ্টাচার বিমুখ, অনুন্নত সামাজিক সংস্থা ও ব্যবস্থাসম্পন্ন, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রতীক, লুঠতরাজ ও মারামারি-কাটাকাটিতে অভ্যস্ত-যাদের নিকট মানুষের জীবনের মূল্য ছিল অতি তুচ্ছ, মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তারা এক নবতর জীবন-দর্শনের ধারক লোক-সমষ্টি হিসেবে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠল এবং আঠারো বছরের মধ্যেই সেই আরব জাতির মন-মানস, জীবন-চরিত্র, মূল্যমান ও জীবনবোধ আমূল পাল্টে গেল এবং সম্পূর্ণ নতুন রূপ পরিগ্রহ করল। পূর্বের অন্ধকার জীবন নবীন আলোকচ্ছটায় ঝলমল করে উঠল, মনের সংকীর্ণতা ও নীচতা-হীনতা ঘুচে গিয়ে পারস্পরিক ঔদার্য, প্রেম-প্রীতি, সহনশীলতা ও মার্জিত রুচিশীলতার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটল মনন ও জীবনের সর্বত্র। পূর্বে যা ছিল অন্যায়, এক্ষণে তা-ই অপরিহার্য কর্তব্য বিবেচিত হতে লাগল। মানুষের মূল্য ও মর্যাদা হল প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজনস্বীকৃত। অশালীনতা ও অশ্লীলতা দূর হয়ে সেখানে স্থান নিল লজ্জাশীলতা ও সুরুচিশীলতা। যে সমাজে মানুষের মর্যাদা ছিল কুকুর-বিড়ালের চাইতেও নিকৃষ্ট, সেখানে তা এমন অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করল যে, একমাত্র সৃষ্টিকর্তার পর আসমান ও জমিনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে নির্ধারিত হল তার স্থান। উদ্দেশ্যহীন ও লক্ষ্যহারা মানুষের সামনে এক মহত্তম জীবন-লক্ষ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। অন্ধকার যবনিকার অবসানে ঘটল নতুন এক আলোকজ্জ্বল দিবসের সূর্যোদয়। একই ব্যক্তি ও একই জাতির জীবনে রাত্রির অবসানে দিনের সূর্যোদয়ের এ ঘটনা সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে আমাদের সামনে। জীবন-দর্শনের পরিবর্তনে সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশের পরিবর্তন হওয়ার এ ঘটনা এক শাশ্বত ও চিরন্তন ব্যাপার এবং একে অস্বীকার করার উপায় নেই।
পূর্বেই বলেছি,মানব সমাজে পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। লক্ষ লক্ষ বছরের দীর্ঘ এক প্রস্তরযুগ অতীত হয়ে গেছে মানব সমাজের ওপর দিয়ে। তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখার সময়-কালও আমাদের সমগ্র ঐতিহাসিক যুগের তুলনায় অনেক দীর্ঘ। তা সত্ত্বেও লক্ষ লক্ষ বছরে বিস্তীর্ণ এ দীর্ঘ যুগে মানুষ পাথরের অসমান ও অমসৃণ হাতিয়ার ব্যবহার করেছে। প্রস্তর যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কৃষিকাজ ও পশু পালনের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এতে করে মানুষের খাদ্য সংগ্রহের পন্থা ও অর্থনৈতিক মান বদলে যায়। অতঃপর তাম্র ও লৌহ যুগে এ পরিবর্তনের গতি অধিকতর তীব্র হয়ে ওঠে। আর বর্তমানের এ পারমাণবিক যুগে মানুষের সমাজ-জীবনে পরিবর্তনের ধারা আরো তীব্রতর হয়ে উঠেছে। এ পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষও বদলে গেছে অনেক। কিন্তু মনুষ্যত্ব ও মানবিকতার মৌল চেতনায় যেমন কোন পরিবর্তন আসেনি- কোন পরিবর্তনই সূচিত হয়নি মানুষের মানসিকতায়, মূল্যমানে, চরিত্র-নীতিতে, তেমনি পরিবর্তন সূচিত হয়নি সংস্কৃতিতে, সাংস্কৃতিক ধারণায় ও জীবনবোধে। যদি বলা হয় যে, সমাজ বিবর্তনের এ অমোঘ ধারায় মানুষের সংস্কৃতিও বদলে গেছে, তাহলে বলতে হবে, সংস্কৃতি যতটা বদলেছে ততটাই তা রয়ে গেছে অপরিবর্তিত-যেমনটি ছিল মানবতার প্রথম সূচনাকালে। বস্তুত সমাজ-বিবর্তন এবং মানুষের বাহ্যিক পরিবর্তনে মৌল মানব-প্রকৃতি আদৌ বদলে যায়নি। স্বভাব-প্রকৃতির দিক দিয়ে মানুষ আজো তেমনি মানুষই রয়ে গেছে, যেমন ছিল সে পার্থিব জীবনের প্রথম সূচনায়।
সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন
কোন মুমূর্ষূ বা মৃত সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন কি সম্ভবপর? এ একটা গুরুত্বপূর্ণ জিজ্ঞাসা এবং সুধী সমাজে এ জিজ্ঞাসা নিয়ে বিভিন্ন সময় প্রচণ্ড আলোচনার ঝড় তোলা হয়। দুনিয়ায় এমন অনেক লোক আছেন যারা মনে করেন যে, একট সংস্কৃতিকেও একজন ব্যক্তি-মানুষের জীবনের ন্যায় বিভিন্ন স্তর পার হয়ে অগ্রসর হতে হয়। প্রথমে তা থাকে শৈশাবস্থায়, তারপর যৌবনে পদার্পণ করে-এবং সব শেষে তা বলবান ও সতেজ হয়ে পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট সময়-কালের মধ্যে সংস্কৃতি ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে এবং পরিপক্কতার পর্যায় অবধি পৌঁছে। তখন সম্মুখে আসে শিল্প ও অংকনের স্বর্ণযুগ। তারপর অতীন্দ্রিয় পদ্ধতিতে একটা পতনের যুগ সূচিত হয়ে যায়। শিল্পে অংকনে ও লেখনে প্রেরণার প্রবহমান স্রোতধারা খুব দুর্বল ও ক্ষীণ হয়ে সাম্প্রতিক শুষ্কতার রূপ ধারণ করে। প্রতিটি জীবন্ত সংস্কৃতিই এর অপেক্ষা করে-এটাই হচ্ছে সমস্ত ঐতিহাসিক পতনের মর্মকথা ও মৌলতত্ত্ব। গুরুত্বহীন পরিবর্তন সহ ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, মিশরীয়, গ্রীক এবং আরবদের জীবন-ইতিহাস এমনিভাবে গড়ে উঠেছে। ইতিহাসের পূর্ণতার মধ্যে এই দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায় যে, বিপুল সময়ের বিস্মৃতির মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে সীমাহীন অভিন্ন মানবীয় সংস্কৃতির স্রোত-তরঙ্গ। সেই সবগুলোই নাটকীয়ভাবে স্ফীত হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল দীপ্তিমান পথে, বিস্তৃত ও সম্প্রসারিত হয়েছে, পুনরায় ধ্বংস হয়েছে এবং সময়ের উপরিতলে আর একবার একটা ঘুমন্ত ধ্বংস আত্মপ্রকাশ করেছে।
এই তত্ত্বটির একটি যুক্তিসঙ্গত বিশ্লেষণ হিসেবে বলা যায়, সমস্ত মানবীয় সংস্কৃতির একটা সূচনা ছিল। তা পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার পর সেগুলো একটা অন্তহীন রাত্রির মৃত্যুগর্ভে বিলীন ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এক্ষণে সেগুলোর পুনরুজ্জীবনের কথাবার্তা একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তির বাল্যকাল পুনরুজ্জীবনের মতই হাস্যকর ব্যাপার মনে হয়, যা কেবলমাত্র ধারণা বা কল্পনার জগতেই সম্ভব-কঠিন বাস্তবতায় তা কিছুতেই সম্ভব নয়।
কিন্তু এই তত্ত্বটির গভীর ও সূক্ষ্ণ বিচার-বিশ্লেষণ একজন সাধারণ মানুষের নিকটও প্রকাশ করে দেবে যে, এসব তত্ত্বের প্রস্তাবকরা সংস্কৃতি বলতে মনে করেন শুধু ভালোর মানের বাহ্যিক প্রকাশ, যা একটি জনগোষ্ঠী বা একটা জাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা তাদের লক্ষ্য আরোপ করেন শুধু বাহ্যিক প্রকাশের ওপর। তারা একথা কখনই অনুধাবন করেন না যে, সংস্কৃতি মূলত একটা আভ্যন্তরীণ তাগিদের বাহ্য প্রকাশ মাত্র, যা মানবীয় হৃৎপিণ্ডে ধুক্ ধুক্ করতে থাকে অনির্বাণ দীপ-শিখার মত। রেডিও, টেলিভিশন ও উড়োজাহাজ প্রভৃতি বস্তু নিজস্বভাবে কোন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারেনা। এগুলো হচ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের অগ্রগতির লক্ষণ মাত্র। এগুলো শুধু একথাই প্রমাণ করে যে, মানুষ তার পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের চেষ্টা করছে। প্রকৃতপক্ষে বৈষয়িক জীবন সংস্কৃতি প্রকাশের সত্যিকার মাধ্যম নয়। মানুষের মনই হচ্ছে সমস্ত মানবীয় কর্মতৎপরতার আসল উৎসস্থল। সংস্কৃতিরও উৎস ও লালন-ভূমি হচ্ছে মন। কাজেই সংস্কৃতি বলতে মানুষের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন ধরণ বুঝায় না। আসলে তা হচ্ছে মনের একটা বিশেষ ধরণের আচরণভঙ্গি, চিন্তার একটা বিশেষ প্রক্রিয়া, যা মানবীয় চরিত্রের একটা বিশেষ ধরণ গড়ে তোলার জন্য চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অন্যকথায, সংস্কৃতি হচ্ছে একটা জাতির বিশেষ ধরণের মানসিক গঠন-প্রকৃতি। আমাদের বর্তমান নৃ-বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক স্থলভাগীয় চিত্রের একটা জরিপ প্রমাণ করে যে, আধুনিক ইতিহাস প্রজাতিসমূহের মানবীয় সমাজ উৎপাদন করতে গিয়ে নিজেকে প্রায় বিশবার পুনরাবৃত্তি করেছে। বর্তমান পাশ্চাত্য সমাজ তা থেকেই ইৎসারিত। প্রাচীন রোমান, গ্রীক এবং আজকের পাশ্চাত্য জাতিসমূহ সেই ঐতিহাসিক পটভুমিই বহন করে চলেছে। সময় ও স্থানের বিরাট আবর্তন সত্ত্বেও তারা সংস্কৃতির সেই একই পরিমণ্ডলে অবস্থান করছে। এমন কি বর্তমান সময়েও বিশ্বের বহু সংখ্যক জাতি- যদিও তারা জাতিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জর্জরিত-মানবজীবনের মৌলিক সমস্যাবলীর ব্যাপারে পরস্পর একমত হবে। ইংল্যান্ড, আমেরিকা, জাপান বা জার্মানী সবাই ব্যক্তি মূলধন ও শ্রম, শিল্পপতি ও শ্রমিক, ব্যক্তি ও সমাজ প্রভৃতি সামষ্টিক মৌল সমস্যাবলীর সমাধান করতে চেষ্টা করছে এক বাস্তব ও অভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানে তাদের পরস্পরের মধ্যে এই বিস্ময়-উদ্দীপক সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় কেন? এর প্রকৃত কারণটা খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। সেটা এই যে, বস্তুবাদের একই প্রাণ-শক্তি কাজ করছে তাদের বিচিত্র ধরণের জীবনের বহু দিকের বুনট ও গড়নে। জীবনের হট্টগোল ও দৌড়ঝাঁপে যেভাবেই হোক তারা বিস্তীর্ণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু হৃদয়াবেগ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব, তাৎক্ষণিক চাহিদার চাপ ও বলপ্রয়োগে স্বার্থ লাভের গোলমালে তারা তাদের আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই হারিয়ে ফেলেনি। আর সেটা হচ্ছে বস্তুগত সুবিধা অর্জন। তারা নিজেদের জন্যে এমন একটা আদর্শ লাভ করার ইচ্ছা রাখে যা অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কাঠামোর সর্বপ্রধান বিভাগগুলোতে-তাদের শিল্পে ও বিজ্ঞানে, দর্শনে ও ধর্মে, আইনে ও নৈতিকতায়, স্বভাবে ও আচরণে, পরিবার ও বিবাহে খাপ খাইয়ে চলবে। সংক্ষেপে এ এমন একটা লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যা পাশ্চাত্য সমাজের জীবন পদ্ধতিতে, চিন্তা ও চরিত্রে ধুক্ ধুক্ করে চলতে থাকবে।
একটা মহান সংস্কৃতি কোন অবসাদগ্রস্ত স্থানে নয়, বরং অসম সাংস্কৃতিক বাহ্য প্রকাশের জনারণ্যে ও পাশাপাশি এবং একটির সঙ্গে অন্যটি সম্পর্কহীনভাবে অবস্থান করতে পারে। তা একটা ঐক্য কিংবা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য উপস্থাপন করে যার বিভিন্ন অংশ সমর্থিত হয়েছে সেই একই ভিত্তিগত মৌলনীতি থেকে এবং সেই একই মৌলিক মূল্যমান গ্রন্থিবদ্ধ করেছে। এই মূল্যমান এর প্রধান মুখবন্ধ ও মানসিকতার কাজ করে। আমরা যদি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার উপরি-কাঠামোটি ঘনিষ্ঠভাবে অধ্যয়ন করি, তাহলে দেখতে পারব, তা এমন একটা ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছে যা পূর্ণমাত্রায় ও খাঁটিভাবে সংবেদজ অভিজ্ঞতালব্ধ বৈষয়িক ও এই পৃথিবীকেন্দ্রিক। তা এই নতুন মৌল মূল্যমানকে কেন্দ্র করে ঐক্যবদ্ধ এবং তার ভিত্তিতেই তা গড়ে উঠছে। সন্দেহ নেই, যুগে যুগে নতুন নতুন সভ্যতা এসেছে এবং বিস্মৃতির অতল-গহ্বরে তা বিলীন হয়ে গেছে; কিন্তু সংস্কৃতি সব সময়ই রক্ষা পেয়েছে ও ক্রমশ সাফল্য লাভ করেছে বিভিন্ন জাতির মধ্যে নিজেকে বারবার পুনরুজ্জীবিত করে। চীনের প্রাচীন সভ্যতা খৃস্টপূর্ব সপ্ত শতকে যখন ভেঙে পড়ল তখন তা প্রাচীন পৃথিবীর অন্য সীমান্তে অবস্থিত গ্রীক সভ্যতাকে তার উচ্চতর লক্ষ্যপানে ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারল না। অনরূপভাবে যখন গ্রাকো-রোমান সভ্যতা শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে গেল খৃস্ট যুগের পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর দীর্ঘকালীন যুদ্ধ ও শ্রেণী বিদ্রোহের রোগে, তাও এই প্রায় তিনশ বছর সময়ের মধ্যে দূরপ্রাচ্যে এক নতুন সভ্যতার জন্মলাভকে ঠেকাতে পারল না। [A Toyenbee: Civilisation on Trial]. বস্তুত এভাবেই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে। কেননা কোন জনসমষ্টি কিংবা জাতি যখনই জীবনের কোন দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমাণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে, তখন তার বাস্তবায়ন তার পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব থাকে না; বরং তখন এই দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমান তার সমস্ত কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত ও নতুন রঙে রঙীন করে তুলতে সক্ষম হয়ে ওঠে।
কোন জনসমষ্টিই যদি একটা বিশেষ ধরণে ও পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তবে তা-ই তাদের সংস্কৃতিতে রূপায়িত করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রভাবশালী দৃষ্টিকোণ বা মূল্যমানের প্রতিষ্ঠা। তা-ই একটা বিশেষ ধরণের আকার-প্রকারে অভ্যস্ত কার্যকলাপের সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতার পটভূমি আর সভ্যতা বলতে সাধারণত ‘পরিস্থিতির সীমাবদ্ধতার মধ্যে সংস্কৃতির অভিব্যক্তি’ বুঝায়। তাই সভ্যতায় সামান্য ব্যতিক্রম ঘটতে পারে সময়ের ও স্থানের পার্থক্যের কারণে; কিন্তু জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিকোণ যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হতে বাধ্য। সময়ের ভাগ্য পরিবর্তনের দরুন মানব-প্রকৃতি কখনই বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়নি। ইতিহাস তার অকাট্য সাক্ষ্য উপস্থাপন করেছে। ক্ষমতা-লিপ্সা, জ্ঞান-অন্বেষা, নির্মাণ-প্রীতি, সঙ্গী-সাথীদের জন্য ত্যাগ স্বীকার-এই সবই প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় তৎপরতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আজকের দিনেও এই কথার সত্যতায় কোনই সন্দেহ জাগেনি। এতো সেই প্রাচীনতম অতীতের কথা, যা আমাদের সম্মুখে এসেছে ভবিষ্যতের পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে। আমরা ভাবি, হয়ত নতুন কিছু জেগে উঠেছে মানুষের করোটিতে, প্রাচীনের অস্তিত্বে এবং এই পুরাতন ও নতুনের পরস্পরের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই; কিন্ত এটা প্রকৃত সত্যের অপলাপ মাত্র। যুদ্ধ এবং শ্রেণী-বিভেদ আমাদের চিরসঙ্গী-আদিকালের মানুষের জীবনে প্রথম যে সভ্যতা জেগে উঠেছিল সেই সময় থেকেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন কালে গৃহযুদ্ধ ছিল একটা তুলনাহীন ঘটনা। আমরা দেখি অন্যান্য এমন সব ঐতিহাসিক ঘটনা, যা আমাদের সম্মুখে যথেষ্ট সাদৃশ্য তুলে ধরে। ঘটনাবলীল অসংখ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে এতে ইতিহাস নিজেকে বারবার পুনরাবৃত্তি করেছে। মার্কিন ইতিহাসে গৃহযুদ্ধ যে সংকট সৃষ্টি করে তা নিশ্চয়ই তাৎপর্যপূর্ণভাবে পুনরাবৃত্তি ঘটায় জার্মান ইতিহাসের সমসাময়িক সংকট রূপে, যা উপস্থাপিত হয়েছে ১৮৬৪-৭১ সনের বিসমার্কের যুদ্ধরূপে। উভয় ঘটনায়ই একটা অপরিপক্ক রাজনৈতিক সংস্থা সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দেয়ার ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উভয় ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক সংস্থা ভেঙে দেয়ার ও তার কার্যকর প্রতিষ্ঠা লাভের মধ্যে মূল সমস্যার সমাধানকারী ছিল এই যুদ্ধ। উভয় ঘটনায়ই কার্যকর সংস্থার পক্ষমূহ নিজেরাই এবং দুটিতেই তাদের ইতিহাসের কোন একটি কারণে ছিল বিরুদ্ধ পক্ষের ওপর তাদের প্রকৌশলী ও শৈল্পিক ক্ষমতার প্রাধান্য। শেষ পর্যন্ত উভয় ক্ষেত্রেই স্ব স্ব সংস্থার বিজয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একটা বিরাট শৈল্পিক সম্প্রসারণ দ্বারা যা দুটিকেই -যুক্তরাষ্ট্র এবং জার্মানীকে- গ্রেটবৃটেনের একটা ভয়াবহ শৈল্পিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা ইতিহাসের আর একটি পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি ১৮৭০ সন নাগাদ শেষ হওয়া সময় কালের মধ্যে। গ্রেটবৃটেনের শিল্প বিপ্লব সম্ভবত একটা বিরল ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, যাতে ১৮৭০ পর্যন্ত তার প্রকৃত ও খুব দ্রুত সঙ্ঘটিত অর্থনৈতিক রূপান্তর ঘটেছিল। ঘটনাবশত তা আরো বহু সংখ্যক ইউরোপীয় তথা পাশ্চাত্য দেশেও সঙ্ঘটিত হয়েছিল। উপরন্তু, শিল্পায়নের সাধারণ অর্থনৈতিক অবয়ব থেকে আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি ফেডারেল ইউনিয়ন ধরণের রাজনৈতিক অবয়বের দিকে ফিরাই, তাহলে আমরা দেখব, যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানির ইতিহাস এই ক্ষেত্রে নিজেদের আর একবার পুনরাবৃত্তি করে তৃতীয় শতকের ইতিহাসে। এক্ষেত্রে গ্রেটবৃটেন নয়, কানাডা তার সংযোগকারী প্রদেশগুলিসহ তাদের বর্তমান ফেডারেশনে প্রবেশ করেছে ১৮৫৭ সনে- ১৮৬৫ সনে যুক্তরাষ্ট্রের ঐক্যের বাস্তব (De-facto) পুনঃপ্রতিষ্ঠার দুই বছর পর এবং ১৮৭১ সনে দ্বিতীয় জার্মান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওযার চার বছর পূর্বে।
বর্তমান পাশ্চাত্য জগতে বহু সংখ্যক যুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। এগুলোর অন্যান্য দেশসমূহের শিল্পায়নে আমরা দেখতে পাই, ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে একই মানবীয় সাফল্যের বহুসংখ্যক সমসাময়িক দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে। বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সমসাময়িকতা অনুমানাতীত নয়। গ্রেট বৃটেনে শিল্প বাহ্যত একটা একক ঘটনা হিসেবেই সংঘটিত হয়েছে, আমেরিকা ও জার্মানীতে তা সংঘটিত হওয়ার অন্তত দুই যুগ পূর্বে। এ ঘটনা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, এটা মূলত একটা পুনরাবৃত্তিকারী বাহ্য প্রকাশ।
অ-নিরাপদভাবে যুক্ত গৃহযুদ্ধ-পূর্ব যুক্তরাষ্ট্র চার সাফল্যাংক ও সাত বছর এবং জরাজীর্ণ নেপোলিয়ন –উত্তর জার্মান কনফেডারেশন অর্ধ শতাব্দীর জন্যে ১৮৬০-এর মারাত্মক ঘটনার পূর্বে প্রমাণ করে যে, ফেডারেল ইউনিয়নটা মূলতই একটা পুনরাবৃত্তিকারী ধরণ ছিল, যা পুনরায় ঘটল কেবল কানাডায়ই নয়, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলেও। [Arnold Toyenbee: Civilisation on Trial]
উচ্চস্তরের পরিবর্তন তার অভ্যন্তরভাগেও পরিবর্তন সাধনের তাৎপর্য বহন করবে, তা জরুরী নয়। সভ্যতার যে করাভাঁ অন্ধকারাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে অগ্রসর হয়েছিল প্রাসাদোপম ঘরবাড়ি, গাধার পৃষ্ঠে আরোহন থেকে উড়োজাহাজে আরোহণ পর্যন্ত, প্রায় ন্যাংটা অবস্থা থেকে উন্নতমানের সুন্দরতম কাট-ছাঁটের জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান পর্যন্ত, তা একটি মাত্র সত্যই প্রমাণ করে। আর সে সত্যটি হচ্ছে, তা অগ্রযাত্রার মাধ্যমে শক্তি অনুসন্ধান ও পুনর্গঠনের প্রবল ইচ্ছা দ্বারা চালিত হয়েছে এবং তা মানুষের সেই প্রবল বাসনা ও সুদৃঢ় সংকল্প, যা মানবতাকে পরিচালিত করেছে এই সমগ্র যুগে-প্রস্তর যুগ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদী উৎপাদনের বৈদ্যুতিক চাক্চিক্যময় যুগ পর্যন্ত। এই দীর্ঘ সময়ে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সব কিছুর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়া সত্ত্বেও মানুষের প্রকৃতিতে এক বিন্দু পরিবর্তন আসেনি। যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবধারা প্রাগৈতিহাসিক গোত্রসমূহকে অন্তর্গোত্রীয় সংঘর্ষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে, তা এখন বর্তমান কালের মানুষের মনে সূক্ষ্ণ ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করেছে এবং সে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রাদি আবিষ্কারে ও নির্মাণে দিনরাত ব্যতিব্যস্ত হয়ে আছে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে বিশ্ব-মানবতাকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে। সীজার যদিও নিহত হয়েছে অনেকদিন আগে; কিন্তু সীজারবাদ এখনো মানুষ শিকার করছে। ইতিহাসে আধুনিক প্রবণতাকে স্থূল দৃষ্টিতে যারাই লক্ষ্য করেছে তারাই স্বীকার করবে যে, আজকেও নিষ্পেষণ পদ্ধতি, বিদ্রোহ এবং ক্রমশ বিপুল সংখ্যক লোক দ্বারা সমাজের ভিতরে ও বাইরে বেশী বেশী রাজনৈতিক অধিকার লাভ করা মানুষের ইতিহাসে চলমান ঘটনা বিশেষ। এটাই সেই অভিন্ন মানসিকতা যা আধুনিক মানুষের মধ্যে কাজ করছে। এখানে যদি কোন পার্থক্য থেকে থাকে, তবে তা শুধু গতিবেগ ও কাঠামোগত মাত্র; অন্য কোন দিক দিয়েই একবিন্দু পার্থক্যও লক্ষ্যভূত নয়।
প্রত্যেকটি সংস্কৃতির একটা নিজস্ব ভাবধারা রয়েছে যা স্বতঃই প্রকাশিত হয় সভ্যতার বিভিন্ন দিক ও শাখা-প্রশাখায়। এই ভাবধারা দুর্বল হতে পারে; কিন্তু কখনই মরে যেতে পারে না। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আত্মার মৃত্যুর পর অন্য দেহে তার চলে যাওয়া ও স্থান করে নেয়ার নিয়ম নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলছে। ফলকথা, সভ্যতা জন্ম নেয় এবং কিছু দিন পর বিলুপ্ত হয়ে যায়; কিন্তু সংস্কৃতির আত্মা অন্য কোন সভ্যতার দেহে স্থান গ্রহণ করে এবং অতঃপর বিশ্বের ওপর কর্তৃত্ব চালাতে থাকে; তবু মরে যায় না কিংবা সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয় না।
আমরা সংস্কৃতির এই আবর্তনমূলক গতিশীলতার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শুরু করব শিল্পকলা, নীতিদর্শন এবং আইন ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে। শিল্পকলা সমাজের খুব বেশী সংবেদনশীল দর্পন; সংস্কৃতি তার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সমাজ ও সংস্কৃতি যা, তার শিল্পকলাও তা-ই হবে। এখানে আমরা শিল্পের একটা ধর্মীয় ও সংবেদনশীল ধরনের সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক প্রতিকৃতি তুলে ধরছি।
‘আর্ট’কে দুভাবে ভাগ করা চলে। একটি হচ্ছে উত্তেজক আর্ট (Sensate Art) আর অপরটি স্বর্গীয় আর্ট (Divine Art)। এই পরিসরে ও এই নমুনার মধ্যে ‘ডিভাইন আর্ট’ স্বগীয় সংস্কৃতির এক বিরাট মুখবন্ধ গড়ে তোলে এবং উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করে যে, প্রকৃত ও বাস্তব মূল্যমান হচ্ছেন একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা ও নিয়ন্তা আল্লাহ তা’আলা। এই মূল্যমান মানুষকে পৃথিবীর বুকে আল্লাহর খলীফা রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। কাজেই তা স্বভাবতই মানুষের ভাল দিকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। তা এমন একটা আর্ট যা ইচ্ছা করেই সব অশ্লীল, কুৎসিৎ ও নেতিবাচক জিনিস থেকেই চোখ বন্ধ করে রাখে ও সেসবকে উপেক্ষা করে চলে। কেননা উত্তেজক আর্ট শুধুমাত্র স্থূল চিন্তা-ভাবনার জন্যে দাঁড়ায়। তা মানুষের মধ্যে নীচ উপকরণ নিয়ে আলোচনা করে; সব নীচতাকে প্রকট করে তোলে। তার হিরো সাধারণত দেহপশারিণী, দুস্কৃতিকারী, ভণ্ড এবং দুরাত্মা লোকেরা। ইন্দ্রিয় ভোগ-সম্ভোগের চেষ্টা করা, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত রাখা, শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলিকে উত্তেজিত করা, স্থূল আনন্দ-স্ফূর্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিবেশন এবং ইন্দ্রিয়জ আপ্যায়নই তার একমাত্র লক্ষ্য।
এই প্রেক্ষিতে বলা যায়, Sensate Art বা উত্তেজক সংস্কৃতি যেখানে গেছে, সৈসূর্য শিল্প তাকে অনুসরণ করেছে এবং যেসব জাতি জীবনের একটা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ গড়ে তুলেছে, তাদের আর্টও সেই একই পথে অগ্রসর হয়েছে-উৎকর্ষ লাভ করেছে। কাজেই এই আর্ট সেই আগের কালের ‘প্যানিওলিথিক’ মানুষের শিল্পের চলমান রূপ বলা চলে। এরা বহু প্রাচীন গোত্রের মানুষ, ঠিক যেমন আফ্রিকার বুশম্যান। অনেক ভারতীয় ও সিথিয়ান গোত্রও তাদের মতই লোক। তারা আসিরীয় সৌন্দর্য শিল্পকে পরিব্যাপ্ত করেছে- অন্ততত ইতিহাসের কোন এক অধ্যায়ে এবং প্রাচীনযুগের শেষ দিকের অতি পুরানো মিশরীয়দের থেকে অনেক বেশী। মাঝামাঝি ধরণের রাজত্ব ও নতুন সাম্রাজ্য-বিশেষ করে এদের শেষের দিকের Saite, Polemic ও রোমান যুগ যা Cheto Mycenacen-এর শেষ জানা যুগ এবং Gracco Roman Culture-এর যুগকে নিশ্চিত রূপে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত তা পাশ্চাত্য সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশীল হয়ে রয়েছে বিগত পাঁচ শতাব্দীকাল ধরে। ডিভাইন আর্টকে Ideational Art বলা যায়, যা একটা বিশেষ কালে প্রভুত্ব করেছে Tacisi China Art-এর ওপর, তিব্বতের বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং অতি পুরাতন মিশরীয় ও গ্রীকি শিল্পের ওপর, খৃস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। তা ছিল প্রাচীন মধ্যযুগীয় খৃস্টান-পশ্চিম সংস্কৃতি এবং তা-ই অব্যাহত থাকে বহুদিন পর্যন্ত।
সে যা হোক, ললিতকলা বহু দিক দিয়েই বিভিন্ন, যেমন প্রাচীন ও সভ্য যুগের মানুষ। কিন্তু সে সবের আভ্রন্তরীণ বা বাহ্যিক চারিত্রিকে ঠিক একই রকমের দেখায় যখন তারা অভিন্ন ধরণের অবস্থান করে। এটা এই সত্যকে প্রমাণ করে যে, ললিতকলার ক্ষেত্রে এই আকৃতির বা ঐ আকৃতির প্রাধান্য শৈল্পিক যোগ্যতার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ব্যাপার নয়; বরং তা হচ্ছে বিশেষ ধরণের দৃষ্টিকোণের ফল, যা পর্যায়ক্রমে লোকেরা বিভিন্ন সময়ে ধারণ করেছে। [P.A. Sorokin: The Crisis of Our Age]
সত্য ও জ্ঞানের পদ্ধতিতেও ঠিক এই ব্যাপারই রয়েছে। Senate Truth এবং বাস্তবতার যে কোন পদ্ধতি বলতে বুঝায় সম্পূর্ণ বেপরোয়া আচরণ- যে কোন Super-Sensory Reality বা value-এর অস্বীকৃতি। তাতে বোধশক্তি সম্বন্ধীয় সংস্কৃতি, আল্লাহর প্রকৃতি ও Super-Sensory Phenomena কুসংস্কার অথবা নিকৃষ্ট ধারণা অনুমান ও ধর্ম হিসেবে গণ্য। তা যদি শেষ পর্যন্ত অনুসৃত হয়, তাহলে তা হবে নিছক বৈষয়িক উদ্দেশ্যে এবং তা যদি সহ্য করা হয়, তবে তা হবে ঠিক যেমন অনেক সখ বরদাশ্ত করা হয় ঠিক তেমনি। সত্যের এই ব্যবস্থা Sensory world অধ্যয়নের খুব জোরালোভাবে আনুকূল্য করে তার দৈহিক, রাসায়নিক ও জীব-বিজ্ঞানী সম্পদ ও সম্পর্কসহ। সমস্ত জ্ঞানগত উচ্চাভিলাষ কেন্দ্রীভূত হয় এই সব Sensory Phenomena-তে, তাদের বস্তুগত ও দৃশ্যমান সম্পর্কতায় এবং প্রকৌশলী আবিষ্কার সেই লক্ষ্য আমাদের অনুভূতি সম্বন্ধীয় প্রয়োজন পূরণ করে। মূলত এর সবটাই বস্তুতান্ত্রিক এবং প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে তা দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে তার বস্তুগত দিকটির ওপর। শুদ্ধ কিংবা ভুল, ভাল কিংবা মন্দ নির্ধারণের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় Sensory utility অথবা Sensory Pleasure.
সত্যের খোদায়ী ব্যবস্থা, অন্য কথায়, বিশ্বাস বা প্রত্যয় ইতিবাচক নৈতিক মূল্যমানসম্পন্ন। তা অহীর মাধ্যমে পাওয়া ও খোদায়ী প্রেরণার ওপর ভিত্তিশীল। তা যে নির্ভরযোগ্য ও নিরংকুশ হবে, তাতে সন্দেহ নেই। নৈতিকতা বা বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন যুক্তিযুক্ততা নয়, তার একটা বিশেষ অর্থ আছে- আছে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। তা সময় ও অবস্থার শর্তাধীন নয়, বরং তা চিরন্তন অপরিবর্তনীয় এবং শাশ্বত।
ইতিহাসের Objective অধ্যয়ন প্রকাশ করে দেবে সত্যের এ ব্যবস্থাসমূহের প্রতিটি বারংবার প্রচলিত ও পুনঃপ্রচলিত হয়েছে। The Sensate truth of Creto Mycenacean সংস্কৃতি খৃস্টপূর্ব অষ্ট থেকে ষষ্ঠ শতকের গ্রীস Ideational truth-কে পথ করে দিয়েছিল; পরে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে খৃস্টীয় চতুর্থ শতক পর্যন্তকার সময়ে তা Sensate truth দ্বারা উৎখাত হয়ে যায়। তারপর খৃষ্টীয় Ideational truth বা Formation of ideas অনুসৃত হয়েছিল ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যকার সময়কালে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে Ideational truth-আর একবার প্রধান হয়ে ওঠে, যার স্থলাভিষিক্ত হয় তৃতীয় একটা ব্যবস্থা যা ষোল শতক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। অনুরূপভাবে Sensate truth-এর কথিত প্রগতিশীল সরল প্রবণতা ইতিহাসের গোটা অধ্যায় আঁকড়ে থাকা সত্ত্বেও একটা প্রভাবশালী ব্যবস্থা থেকে অপর ব্যবস্থা পর্যন্ত অব্যাহত দোলা দিতে দেখতে পাচ্ছি। [P.A. Sorokin: The crisis of our age]
শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই ঘূর্ণায়মান আন্দোলনসমূহ বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে প্রমাণ উপস্থাপন করেছে এই সত্যের পক্ষে যে, পৃথিবীর সভ্যতায় বহুসংখ্যক পরিবর্তন সাধিত হওয়া এবং সভ্যতার উত্থান-পতন হওয়া সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত সভ্যতার আত্মা যে সংস্কৃতি, তা নিজেকে ইতিহাসে বহুবার পুনরাবৃত্ত করেছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতি সেই একই ধরণের শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি করেছে-সেই একই ধরণের সত্য ও একই ধরণের দর্শন ও ধর্ম সৃষ্টি করেছে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে ও পর্যায়ে। প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের যে স্থানে সেই সভ্যতা জন্ম নিয়েছে সেখানে পরিবর্তনের কারণে হয়ত তাতে সামান্য পার্থক্য বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়েছে; কিন্তু সভ্যতার অন্তঃসলিলা স্রোতধারা এক ও অভিন্নই রয়ে গেছে। Sensory Civilisation-এর আকৃতিতে Sensate Culture আত্মপ্রকাশ করেছে, তা পঞ্চম শতক হোক, বিংশ শতাব্দী হোক অথবা আরব কিংবা ইংল্যান্ড অথবা আমেরিকান শতাব্দী হোক। বর্তমান সভ্যতার জাঁকালো অট্টালিকা দেখে কিছু লোক এ সিদ্ধান্ত নিয়ে অবাক হয়ে থাকে যে, মানবতা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিদ্যার ক্ষেত্রে অতীতে কখনোই এ ধরণের লক্ষ্যযোগ্য অগ্রগতি লাভ করতে পারেনি। কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলো এই সরল দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, ভূপৃষ্ঠে বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার বাহ্যিক উজ্জ্বলের চাইতেও অধিক উজ্জ্বল বহু সংখ্যক সভ্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেগুলো বস্তুগত অগ্রগতি ও অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যের সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল বলে স্পষ্ট মনে হয়। সেগুলো তাদের পিতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেছে তাদের হাস্য-মুখর প্রাচুর্যের পরিমণ্ডলে। এ সভ্যতা পূর্ণমাত্রার বস্তুবাদী ভিত্তির ওপর অবস্থিত এবং তার বাইরে থেকে প্রবিষ্ট হয়ে Sensual Pleasure-এর ভাবধারা দ্বারা একাধিকবার দুনিয়ার ওপর কর্তৃত্ব করেছে। তার প্রধানতম নীতি সব সময়ই ছিল এই পৃথিবীকেন্দ্রিকতা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সুবিধাবাদ। এই ধরণের একটি Sensory সংস্কৃতির বুনানির মধ্যে মানব জীবন বহু সময়ই তার জীবন-নাট্যের নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। ইতিহাসজ্ঞান যদ্দূর যায়, আমরা জানতে পারি যে, প্রথমে যে জাতি এই সংস্কৃতির জন্য দাঁড়িয়েছিল তারা ছিল আরবের আদ জাতি। এই জাতির জীবন পদ্ধতি দেখলে স্পষ্টত মনে হয়, এ জাতি শুধুমাত্র বৈষয়িক ও বস্তুতান্ত্রিক স্বার্থের দ্বারা চালিত হতো। তাদের প্রায় সমস্ত পুত্র কন্যার অন্তর স্বার্থ-প্রণোদিত হওয়ার দরুন স্বার্থের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জর্জরিত হয়েছিল। ধন-সম্পদ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উত্তাপ ও উচ্ছাস তাদেরকে মৃগীরোগে আক্রান্ত করে দিয়েছিল। তারপর এই জাতির পতন ঘটে। তখন সামুদ নামের অপর এক জাতি নতুন তেজবীর্য ও উদ্দীপনাসহ ভূ-পৃষ্ঠে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মানসিকতার অবস্থা ছিল এই যে, তা কলংকিত করেছিল বস্তুবাদের কালো বর্ণকেও। ‘‘No Stretch of imagination, could her members ever think there is a life beyond this life.’’ ফলে এ জাতিরও কর্মতৎপরতা প্রাথমিক ও মূলগতভাবে বৈষয়িক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনের দিকেই নিয়োজিত হয়েছিল।
এ ক্ষেত্রে রোমানরা অবশ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করেছিল। জীবনের সংবেদন দর্শন, সংবেদজ নৈতিকতা, সংবেদজ রীতিনীতি তাদের জীবনে পুরোমাত্রায় চালু হয়েছিল। সে যুগের মোটামুটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল বিলাসিতামূলক। তখন বিপুল জাতীয় সম্পদ অল্প সংখ্যক লোকের করায়ত্ত হয়ে বিপুল সংখ্যক লোকের দারিদ্র্যের ওপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছিল। সে পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন এবং অসাম্যকে লঘু করার যে কোন চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে অমানুষিক নির্যাতন দ্বারা দমন করা হয়েছিল। সেখানে ধর্মীয় ও নৈতিক বিধানের প্রতিটি ধারাকে লংঘন করা হয়েছিল। যেখানেই মানুষ সততা, দয়ার্দ্রতা, বদান্যতা ও সহানুভূতির পথ অনুসরণের চেষ্টা করেছে, সেখানেই তারা ভোগ করেছে সীমাহীন নির্মমতা। নির্যাতকরা নিজেদেরকে গৌরবান্বিত বোধ করেছে, অহংকারের অট্টহাস্যে ফেটে পড়েছে এবং তাদের নির্মমতার একটা অন্তহীন মিছিল চালিয়েছে। এভাবে কিছুকাল অতিবাহনের পর এই রকমের জাঁকালো অট্টালিকা তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে। অতঃপর সেই একই ধ্বংসস্তুপের ওপর বর্তমান সভ্যতার কঠামোটি গড়ে উঠেছে। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা লক্ষ্য করছি ক্ষমতার দাপট ও ধন-দৌলতের লোভ অভিন্নতাকে তাণ্ডব নৃত্যে মেতে উঠেছে।
‘The average Europen-he may be a demcrat or a fascist, a capitalist or a bolshavik, a manual worker or an intellectual-knows only one positive religion, and that is the worship of material progress.’
‘‘সাধারণ ইয়োরোপবাসী হোক সে গণতন্ত্রবাদী অথবা উগ্রজাতীয়তাবাদী পূঁজিবাদী অথবা একজন বলশেভিক, একজন সাধারণ শ্রমিক অথবা একজন বুদ্ধিজীবি নির্দিষ্টরূপে একটি মাত্র ধর্মকেই তারা জানে তাহল বস্তুবাদী উন্নয়নের একাগ্র বন্দনা।’’
বর্তমান সভ্যতার ভিত্তি হল এই বিশ্বাস যে, এই জীবনকে নিরবচ্ছিন্নভাবে চালিয়ে যাওয়া এবং আকণ্ঠ ভোগ করা ভিন্ন জীবনের আর কোন লক্ষ্য নেই। এই জীবনকে যতদূর সম্ভব সহজতর করা কিংবা আধুনিক ভাবধারায় প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে অনসুরণ করাই একমাত্র লক্ষ্য। এই ধর্মের মন্দির হচ্ছে বিরাট বিরাট ফ্যাক্টরী, সিনেমা, থিয়েটার হল, রাসায়নিক পরীক্ষাগার, নৃত্যু-গীত, পানি-বিদ্যুৎ প্রকল্প (hydro-electric works) আর তার ধর্মযাজক হচ্ছে ব্যাংক পরিচালক, প্রকৌশলী, ফিল্মস্টার, শিল্পপতি ও বণিক সম্প্রদায় ক্ষমতা ও সুখের সন্ধানে এই মহাযাত্রার অনিবার্য ফল হচ্ছে বিরুদ্ধবাদী জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করা এবং স্বার্থের সংঘর্ষের স্থানে পরস্পর দ্বারা পরস্পরকে ধ্বংস করা আর সংস্কৃতির ক্ষেতে এমন ধরনের মানুষ সৃষ্টি করা যাদের নৈতিকতা কেবলমাত্র বৈষয়িক সুবিধা অর্জনের চেষ্টার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ভাল ও মন্দের বস্তুগত সাফল্য যাদে সুউচ্চ মানদণ্ড। [Islam at the cross roads: Mohammad Asad]
এর ফল দাঁড়িয়েছে, দুঃখী মানুষকে মান-সম্মান ও অধিকার নিয়ে বাঁচার সুযোগ দানের পরিবর্তে তার দুঃখজনক অবস্থাকে আরো স্থায়িত্ব দান করেছে। মানবীয় জ্ঞানের প্রবৃদ্ধিলব্ধ বিজ্ঞান আধুনিক মানুষকে যে শক্তির যোগান দিয়েছে এবং তার বাড়াবাড়িকে নিরবচ্ছিন্ন প্রশ্রয়দান করেছে, তা গোটা সভ্যতার শিল্প-নৈপুণ্যকে বিপন্ন করে তুলেছে। জাতীয়তার ভাবধারা ব্যক্তিগণের ও জাতিসমূহের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও সহযোগিতাবোধ জাগ্রত করছে না, বরং তা জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকার সৃষ্টি করে, জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির চেতনা সৃষ্টি করছে এবং প্রতিটি জাতিকে অপর জাতির বিরুদ্ধতায় প্রবলভাবে প্রলুব্ধ করছে। দুর্ভাগ্যবশত জাতীয়তাকে একটা অলংঘনীয় খোদায়ী বিধান হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই নীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছুকেই বরদাশত করা হচ্ছে না। এই লোকদের নিকট তাদের অধিকার ও মর্যাদার অনুকূল যা, তা-ই সত্য এবং তার জন্য যা করা উচিত তা করাই তাদের নৈতিকতা বলে প্রতীত হয়েছে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সহজ উক্তি হচ্ছেঃ
‘Innocent people and nations are being cruelly sacrificed to the greed for power and supremacy which is devoid of all sense of justice and human consideration.’
‘‘ক্ষমতা ও প্রভূত্বের লালসার কাছে নিরপরাধ জনগোষ্ঠী ও জাতিসমূহকে নিষ্ঠুরভাবে বলি দেয়া হচ্ছে, যে ক্ষমতা ও প্রভূত্ব সব রকমের ন্যায়বিচার ও মানবীয় বিবেচনা বোধ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।’’
ইন্দ্রিয়-সুখ ও বৈষয়িক সুবিধা একাকিই আধুনিক মানুষের মনের ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করেছে আর তা লাভ করার জন্য সে কোন আইনের ধার ধারার প্রয়োজন মনে করে না। সত্যিকার অর্থে তার কোন বিচার নেই- নেই কোন নৈতিকতা।
সংস্কৃতির এই ভাবধারাই বহুসংখ্যক সভ্যতায় অনুপ্রবেশ করেছে এবং তাদের মধ্যে একটা কাঠামোগত সাদৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। আদ, সামুদ, রোমান, গ্রীক এবং আজকের ইউরোপীয় ও আমেরিকান জাতিসমূহ সেই একই সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী। বিস্তারিত ও খুঁটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও তাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করা যায় না। এরা সকলে জীবনকে একই দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখে আর তা হচ্ছে বস্তুগত স্বার্থ ও সুবিধা।
এরপর আমরা মানবজীবনের কতিপয় মৌলিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবো এবং নিজেদের মতো দেখবো, এগুলো বার বার সম্মুখে কি করে উপস্থিত হল? আর কি করে সেই ভাবধারা রীতিনীতি পরিগৃহীত হল বিভিন্ন ব্যক্তির দ্বারা, যারা সবাই একই সংস্কৃতি উপস্থাপন করছিল? দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যষ্টি ও সমষ্টির পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারটিই ধরা যাক এবং তার বৃত্তাকারে আবর্তনশীল গতিশীলতা লক্ষ্য করা যাক।
এটা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, প্রাচীন সমাজ-স্তরে কোন সুসংগঠিত রাজনৈতিক সংস্থার অস্তিত্ব ছিল না। কিন্তু তা একথা বুঝায় না যে, সেখানে আদপেই কোন কাঠামো ছিল না; সমাজে তখন শুধু গণ্ডগোল উচ্ছৃংখলতাই বহাল ছিল। তখনকার সময়ে যে সমাজ ব্যবস্থা চলমান ছিল তা হয়তো খুব অপরিচ্ছন্ন ও অ-সংস্কৃত ছিল। কিন্তু একটা কিছু যে ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। ব্যক্তিরা তখন নিশ্চয়ই কোন সুনির্দিষ্ট নীতিতে নিজেদের জীবন পরিচালনা করতো, যা তখন চালু ছিল। এই ব্যবস্থাপনায় এক এক ব্যক্তি বাধাবিমুক্ত স্বাধীনতা ভোগ করেছে এবং সমাজের বুনট এতটা দুর্বল ছিল যে, এক ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির দুর্বার হয়ে দাঁড়াবার পথে কোন প্রতিকূলতা ছিল না। সমাজের ওপর এই এক ব্যক্তির প্রাধান্য বিস্তারের স্তর পরবর্তীকালে সামন্তবাদ ও রাজতন্ত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। যেখানে এক একটি লোক হীন-তোষামুদে দাস হয়ে পড়েছে এক একজন স্বেচ্ছাচারী শাসনকর্তার, সেখানে সে একাই গোটা রাষ্ট্রের ওপর নিরংকুশভাবে কর্তৃত্ব করেছে। ফলে প্রজাসাধারণের জীবন ও সম্পত্তি রাষ্ট্রের ইচ্ছা পূরণের অগ্নিকুণ্ডে উৎসগীকৃত হতে লাগল। দিনগুলো এমনিভাবেই চলে যাচ্ছিল এবং অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিল যে, এই ধরণের সমস্যা অতীতে বোধ হয় আর কোন দিনই উদ্ভূত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে না।
কিন্তু ইতিহাসের পরবর্তী ঘটনাবলী সর্বাত্মকভাবে প্রমাণ করল ব্যাপারটি অন্যভাবে। এমনকি বর্তমান শতকেও আমরা ব্যক্তি-স্বার্থকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের দেয়াল ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দোদুল্যমান হতে দেখলাম। আধুনিক গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি হচ্ছে ব্যক্তি-স্বার্থের ওপর স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করা। জন স্টুয়ার্ট মিল স্বাধীনতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মন্তব্য করেছেনঃ
‘In the conduct of human beings towards one another, it is necessary that general rules should for the most part be observed in order that people may know what they have to expect, but in each person’s won concern his individual spontaneity is entitled to free exercise, consideration to aid his judgement, exhortation to strengthen his will, may be offered to him, even abdruded on him by others, but he himself is the final judge, all errors which he is likely to commit against advice and warning are far outweighed by the evil of allowing others to constrain him to what they deem his good.’
‘‘একে অপরের প্রতি মানুষের আচরণে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাধারণ নিয়ম-বিধি মেনে চলা প্রয়োজন, যাতে তারা জানতে পারে যে, তাদের কি প্রত্যাশা করতে হবে। কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থে তার ব্যক্তিগত প্রবণতাকেই অবাধ চর্চার জন্যে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে সহায়তা, তার ইচ্ছাকে সমর্থন করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও উৎসাহ প্রদান করা যেতে পারে। এমনকি অন্যের দ্বারাও এগুলো তার ওপর চাপিয়ে দেয়া যায়। কিন্তু সে নিজেই তার ব্যাপারে চূড়ান্ত বিচারক। অন্যের উপদেশ এবং সতর্কীকরণ সত্ত্বেও তার দ্বারা যেসকল ত্রুটি হতে পারে তার চেয়েও অনেক বড় অপরাধ হবে যদি সে মঙ্গল বা কল্যাণে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে অন্যের মতামতকে প্রশয় দেয়।’’
একটা গণতান্ত্র্রিক ব্যবস্থায় এই সীমাহীন স্বাধীনতা ব্যক্তি কর্তৃক ভোগ করা অত্যন্ত শোচনীয় পরিণতি নিয়ে এলো। সে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ব্যক্তির স্বাধীনতা পদদলিত করার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করল। নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা বিধানের জন্যে গোটা দেশের উপায়-উপকরণ শোষণ করার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা পেল। এ অবস্থায় রাষ্ট্র কার্যত ব্যক্তিগণের শৃংখল ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পর তার একটা বড় প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। খুব শীগগিররই এটা অুভব করা গেল যে, Every man for himself and the devil take the hindmost.
এহেন সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি একটি পরিতৃপ্ত সমাজের জন্যে যথেষ্ট ভিত্তি জোগাড় করে দিতে পারে না; বরং তার বাস্তব প্রয়োগে সংঘটিত দারিদ্র্য রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নীতি পর্যন্ত পরিচালিত করলো। শুধু শিল্প প্রতিষ্ঠান ও অর্থনৈতিক কার্য পদ্ধতিতেই নয়, মানব জীবনের সকল বিভাগেই তা সংঘটিত হল। ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজম গোটা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত ও শাসন করেছে। এই দুটি ব্যবস্থার অধীন সরকারের হাতে সীমাহীন ক্ষমতা এসে গেল, যা মাত্র এক ব্যক্তির দ্বারা চালিত হয়েছে অথবা খুবই মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তি দ্বারা। সাধারণ মানুষকে বুঝানো হলঃ জাতীয় রাষ্ট্রকে শক্তিশালী সরকার গঠনে অক্লান্তভাবে অবশ্যই কাজ করতে হবে। বিশেষ করে, সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্ব সংখ্যাগুরুর চাপ বা নিয়ন্ত্রণ নীতির বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত থাকবে। সেখানে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে না; কিন্তু দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত নিছক একটা সংস্থা- যা প্রাচীন অর্থে Council নামে অভিহিত-তার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেয়া হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিরই কাউন্সিলার হবার অধিকার স্বীকৃত বটে; কিন্তু সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এক ব্যক্তির দ্বারা। হিটলার যা-ই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার কাউন্সিল তাকে ঠিক মনে করে নিয়েছে-তাদের নিকট তা-ই চিরকাল ‘সত্য’ হয়ে থাকবে। তৎকালীন জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী Herr Frick একদা ঘোষণা করলেনঃ
‘To serve Hitler is to serve Germany, to serve Germany is to serve Gog.’
‘হিটলারের সেবা করা মানে জার্মানীর সেবা করা, জার্মানীর সেবা করা মানে ঈশ্বরের সেবা করা।’
কমিউনিস্ট সমাজ জনগণের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে আরও এক কদম অগ্রসর হয়ে গেল এবং তার সবটাই টোটালিটারীয়ান বা সর্বগ্রাসী। এখানে ব্যক্তিরা প্রধানত রাষ্ট্রের জন্য বাঁচে। তার প্রধানকে যে নামেই ডাকা হোক, তার ক্ষমতা কোন ডিক্টেটরের চাইতে একবিন্দু কম নয়। তার কল্পনা-শক্তি যদ্দূর যায়, তদ্দূরই সে একটা নিয়ন্ত্রণ চাপানো দাবি করে এবং সেই কল্পনা-শক্তি দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলে।
নারী-পুরুষের পারস্পরিক যৌন সম্পর্কের একটা দৃষ্টান্ত আমার বক্তব্যের অনেকখানি ব্যাখ্যা করতে সহায়ক হবে। মানব ইতিহাসের সেই আদিম স্তরে এই সম্পর্ক মোটামুটি পশুদের মতোই অনিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তি তার যৌন কামনা চরিতার্থকরণে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতো বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির কাছ থেকে। সময়ের অগ্রগতিতে এক সময় পরিবার-প্রথা স্থাপিত হয়। সেই সাথে বিবাহ প্রথাটাও উন্নতি লাভ করতে থাকে। এটা চলমান স্বাধীনতার ওপর সংযম ও নিয়ন্ত্রণ আরোপে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। পরিবার ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে; কিন্তু উত্তরকালে তা একটা গুরতর বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তা প্লেটোর ন্যায় একজন উচ্চমানের দার্শনিকের হাতে। তিনি প্রস্তাব করলেনঃ
‘All healthy men and women should at one time be brought together at a certain place and be allowed to indulge in sexual intercourse.’
‘সকল স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং নারীকে এক সময়ে একত্রে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আনা হোক এবং ব্যবস্থা করা হোক যৌন সঙ্গমে তাদের স্বাধীন ইচ্ছা চরিতার্থ করার।’
তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এভাবেই বাচ্চারা নির্দিষ্টভাবে একজন পুরুষ ও একজন নারীর স্নেহ-বাৎসল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং গোটা সমাজ ও রাষ্ট্রের সাথে তাদের নির্বিশেষ ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। খুব বেশী দিন যেতে না যেতেই এই Absurdity-র আত্মহত্যামূলক পরিণতি জনগণের নিকট প্রতিভাত হয়ে ওঠে। তখন তারা বিবাহ ও পরিবার প্রতিষ্ঠানটিকে সুদৃঢ় করার জন্য চেষ্টা শুরু করে দেয়।
এই দিক দিয়ে বিগত তিনটি শতাব্দীকাল অত্যন্ত ঘটনাবহুল। বলা হয়েছেঃ
‘In the first decade of Bolshevist administration there was a understanding that sexual intercourse was a personal matter, taking place by mutual consent between men and women of the same of different races, colour or religion, for which no religion of other ceremony was required whilst even official registration of the Union was entirely optional.’ (Where Sprenglarism Fails)
‘বলশেভিক শাসনের প্রথম দশকে এইমর্মে একটা ধারণা চিল যে যৌন সঙ্গম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। যা একই অথবা বিভিন্ন গোত্রের, ধর্ম ও বর্ণে নারী এবং পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে ঘটে থাকে, যার জন্য কোন ধর্মীয় অথবা সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই, যখন এমন কি রাষ্ট্রীয়ভাবে নিবন্ধন করাটাও নিতান্ত ঐচ্ছিক।’
দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে আমরা একটা ক্রমিক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। কামুকদের প্রতি লেনিনের কোন সহানুভূতি ছিল না। রুশ বিপ্লবের পর প্রাথমিক দিনগুলোতে তিনি এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, যৌন মিলন একটা প্রাকৃতিক ব্যাপার, যেমন প্রাকৃতিক ব্যাপার ক্ষুধার পর খাদ্য গ্রহণ। তা পিপাসার দরুণ একগ্লাস পানি পান করার কাজটির অধিক কিছু নয়। সামাজিক দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে তাঁর অভিমত যৌন সংক্রান্ত ব্যাপারে অন্তত কমিউনিস্ট পার্টির জন্যে প্রামাণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি বলেছিলেনঃ
‘Is marriage a private relation between rwo legged animals that interest only themselves, and in which society has no right to meddle.’
‘বিবাহ একটি নিজস্ব সম্পর্ক, দুটি দু’পেয়ে জন্তুর মধ্যে, যা শুধুমাত্র তাদেরই স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, এর মধ্যে সমাজের কোন অধিকার নেই হস্তক্ষেপ করার।’
Ryazonov লিখেছেনঃ ‘We should teach young communists that marriage is not personal act, but act of deep social significance. Marriage has two sides, the intimate side and social.’
‘তরুণ কমিউনিস্টদেরকে আমাদের এই শিক্ষা দেয়া উচিত যে, বিবাহ নিতান্তই কোন ব্যক্তিগতকর্ম নয় বরং কাজটি গভীরভাবে সামাজিক গুরুত্ব বহনকালী। বিবাহের দু’টি দিক রয়েছে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক।
আর Soltz বলেছেনঃ and we must never forget the social side. We are against a profligate of disorderly life. Because it affects the children.’
‘এবং অবশ্যই আমরা কখনো সামাজিক দিকটা ভুলে যাবনা। আমরা অগোছালো জীবনো বিরোধী; কেননা তা শিশুদের ক্ষতি করে।
[Sidney and Biatrice Webbes: Soviet Communism, A New Civilization]
এরপর পরিবার ও বিবাহ ব্যবস্থা আবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।
ইতিহাস আমাদের বলছেঃ ‘এমনকি যে গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টারী সিস্টেমের গভর্ণমেন্ট এ যুগের অবদান হিসেবে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে, তা-ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের ডিমের গভীরতম পর্যায়ে প্রচ্ছন্ন নিউক্লিয়াস হিসেবে বিদ্যমান।
অনুরূপভাবে, একটি সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি এবং তার সমগোত্রীয় সমস্যাবলী সিদ্ধান্তমূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, সভ্যতা যদিও জন্মে ও মরে যায়, কিন্তু সংস্কৃতিতে মৌলিকভাবে কোন পরিবর্তন ঘটে না। তার আন্দোলিত হওয়ার ক্ষেত্র বদলে যেতে পারে বটে; কিন্তু তার মৌল ভাবধারা সর্বত্র নিজেকে প্রকাশ করে। এখানে আত্মার স্থানান্তর আছে, যা সংস্কৃতির বাপারে কাজ করে। মানবীয় যে কোন গোষ্ঠীবদ্ধতায়-যে কোন স্তরে-মনের কোণে একটা নির্দিষ্ট আচরণ অবলম্বিত হতে পারে- তা সুবিধাবাদী হোক কিংবা অন্য কিছু। তদনুযায়ী সে তার জীবনকে পুনর্গঠিতও করতে পারে-যেমন মানব প্রকৃতি এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত হয়ে গেছে সময়ের, অবস্থার ও ভাগ্যের শত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও। তাই তার সমস্যাবলীও ঠিক সেই পুরাতনই রয়ে গেছে। পরিবর্তন যা কিছু হয়েছে তা শুধু বস্তুজগতে। দিনে পর রাত্রির অভিন্ন বাহ্য প্রকাশ এবং রাত্রির পর দিনের পুনরাগমণ শুধু ঘটছেই না, সেই অপরিবর্তিত বাহ্য প্রকাশ মানবীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও সেই অভিন্ন অবস্থা বিরাজিত রেখেছে। যেমন পৃথিবীর কতক অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে রাত্রিকালে, অনুরূপভাবে কতগুলো দেশ ও জাতি Sensate culture-এর ভৌতিক ডানার নীচে চাপা পড়ে থাকে। রাত্রির অবসানে যেমন দিনের আলোর স্পর্শ ঘটে, Ideational সংস্কৃতির নব প্রভাতও অনুরূপ রীতিতে উদিত হতে থাকে। তবে এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে, যা উপেক্ষা করা উচিত নয়। প্রাকৃতিক ও বস্তুজগতে যা কিছুই ঘটুক, তা প্রকৃতির অনমনীয় বিধান মেনে চলে- যা উপেক্ষা বা লংঘন করার কোন সুযোগই নেই। প্রকৃতি তার দায়িত্ব পালন করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে; কিন্তু মানবীয় তৎপরতার অবস্থা সেরূপ নয়। তাকে দেয়া হয়েছে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি এবং তা প্রয়োগের স্বাধীনতা। সে পসন্দ করতে পারে, বাছাই করতে পারে গ্রহণ বা বর্জন তথা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতে পারে তার নিজের ইচ্ছানুযায়ী। কাজেই কোন সংস্কৃতির যদি উত্থান হয় কিংবা পতন ঘটে, তবে তা সবই তার অনুসারীদের গ্রহণ বা বর্জনের কারণে। তাদের উত্থান ও অগ্রগতির বা পতনের কোন নির্দিষ্ট সময় আগে থেকে চিহ্নিত করা যেতে পারেনা। মানব-সত্তার নৈতিক চেষ্টা-প্রচেষ্টা তার অগ্রগতিকে নিশ্চিত করে। সাফল্য আসে শুধু সেই সমাজ ব্যবস্থার জন্যে যা পবিত্রতা ও ন্যায়পরতার বৃহত্তর ব্যবস্থা উপস্থাপন ও পরিগ্রহণ করে। কিন্তু এই পবিত্রতা ও ন্যায়পরতা পাওয়া যেতে পারে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিগণের সচেতন ও ইচ্ছামূলক চেষ্টা-প্রচেষ্টার ফলে, যারা একত্রিত হয়ে একটা সমাজ-সংস্থা গড়ে তুলেছে। কাজেই সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন যে সম্ভব, তা এক অনস্বীকার্য সত্য। এই সত্য যারা অস্বীকার করতে চায়, তারা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার মতেই গোঁড়ামি দেখানোর চেষ্টা করে মাত্র।
বস্তুত, এটা বিশ্বমানবতার জন্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, Sensate বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞায় মানুষকে ‘merely a complex of electrone and protons, an animal organism, a reflex mechanism, a variety of stimulus response relationship or a psyco-analytical bag filled with psycho-logical libido.’ (ইলেকট্রন ও প্রোটনের একটি যৌগিক ছাড়া আর কিছই নয়। একটি পাশবিক দেহ সংগঠন আর একটি জীবন যন্ত্রের প্রতিবিম্ব। ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সম্পর্কের একটি বিচিত্র প্রকাশ অথবা একটি মনঃসমিক্ষণ গত ব্যাগ যেটি নানা বিদ্যাগত কর্মপ্রেরণা বা কর্মশক্তিকে ভরা।) বলে আখ্যায়িত করেছে।
এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মানুষ একটা নিছক biological organism-এ পরিণত হয়ে গেছে। তাই তো সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মানবীয় জীবনও জন্ম-মৃত্যুর সেই একই আইন মেনে চলছে, যা পশু জীবনের ওপরও সমানভাবে কর্তৃত্ব করছে। এটা অনস্বীকার্য যে, যা পতনের দিকে চলে ও শেষ হতে থাকে তা অবশ্যই শক্তিহীন হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত তা মরবেই। প্রধানত জীববিদ্যা সংক্রান্ত সাদৃশ্য (Analogy) ভিত্তিক এসব তত্ত্ব ভিত্তিহীন। কেননা মানুষ কোনক্রমেই ‘পশু’ নয়, পশুর ঊর্ধ্বে তার স্থান। তার ভিতরে রয়েছে কাজের তাগিদ, রয়েছে নিজেকে চালিত করার চেতনা। এখানে এমন কোন অভিন্ন আইন নেই যে, সংস্কৃতি ও সমাজকে বাল্যকাল, পরিপক্কতা, বার্ধক্য ও মৃত্যু এই স্তরগুলো পার হতেই হবে। উপরন্তু এই বহু পুরাতন তত্ত্বেও কোন প্রবক্তা এমন কিছু দেখান নি, যদ্দারা সমাজের এই বাল্যকাল কিংবা সংস্কৃতির বাধ্যক্য অর্থাৎ প্রতিটি যুগ বা স্তরের বিশেষ চারিত্র বুঝা যেতে পারে। একটা যুগ কখন শেষ হবে ও পরবর্তীটা কখন শুরু হবে, একটা সমাজ কি ভাবে মরে এবং সমাজ ও সংস্কৃতির মৃত্যু বলতে কি বুঝায়? এগুলো নিছক অবান্তর ও অবাস্তব দাবি মাত্র। ঠিক যেমন এক ধরণের জীবন যাত্রার অন্যটির স্থলাভিষিক্ত হওয়া থেকে কখনো তার মৃত্যু বুঝায় না। বস্তুত কোন সংস্কৃতির মৌল আকার-আকৃতি ও ধরণের অপরটির স্থলাভিষিক্ত হওয়া সেই সমাজ ও সংস্কৃতির মৃত্যুর সমার্থক নয়, বরং তা এই রূপান্তরের মধ্যদিয়ে এগিয়ে চলে। আসলে যে ভুল ধারণার দরুন দুনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত মনীষীরা ভ্রমের মধ্যে পড়েছেন-তা হচ্ছে সংস্কৃতিকে একটি সুনির্দিষ্ট organism রূপে দেখা-তাদের কাছে সংস্কৃতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগের কোন সূত্র না থাকা। মূলত সংস্কৃতি একটা organism নয়, তা একটা আন্দোলন তথা চিরন্তন গতিশীলতা। ঐতিহাসিক তথ্য এই সত্য স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, একটি সংস্কৃতির সুস্পষ্ট আলোকধারা যখন গাঢ়ভাবে প্রবাহিত হয়, তখন তা কদাচিৎ শুকিয়ে যায়। তা জনগণের চিন্তা ও জীবনধারার ওপর নিজের প্রভাব অব্যাহতভাবে চালিয়ে যায় এবং একটি নতুন সংস্কৃতি উপস্থাপন করে। উপসংহারে Briffault লিখিত Making of Humanity গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়ঃ
‘Science is the most momentous contribution of Arab civilization to the modern world; but its fruits were slow in repening-not until long after Moorish culture had sunk back into darkness did the giant which it had given birth rise in his might, other and manifold influences from the civilisation of Islam communicated its first glow to European life.’
‘For although there is not a single aspect of European growth in which the decisive influence of Islamic culture is not traceable nowhere is it so clear and momentous as in the genesis of that power which constitutes the permanent distinctive force of the modern world, and the supreme source of its victory, natural science arose in Europe as a result of a new spirit of enquiry of new methods of investigation of the method of experiment, observation measurement, of the development of mathematics in form unknown to Greeks. That spirit and methods were introduced indo European world by the Arabs.’
‘আধুনিক বিশ্বে আরব সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে বিজ্ঞান; কিন্তু এর সুফল পরিণতি বিলম্বে হয়েছিল। তবে বেশিদিন পরে নয়, যখন স্পেন-বিজয়ী আরবদের সংস্কৃতি পুনরায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছিল, তখন এই বিজ্ঞান প্রভূত শক্তি নিয়ে এক বিশাল সফলতা দেখিয়েছিল, ইসলামী সভ্যতার বহুবিধ প্রভাব এই বিজ্ঞানের প্রথামিক আলো ইউরোপীয়দের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিল।’
‘যদিও ইউরোপীয় উন্নয়নের এমন কোন দিক নেই যেখানে ইসলামী সংস্কৃতির চরম প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না, আধুনিক বিশ্বের মধ্যে স্থায়ী এবং বৈশিষ্ট্যমূলক শক্তি হিসেবে খ্যাত ঐ বৃহৎ শক্তি যে অংশটির মধ্যে এর প্রভাব এত বেশী স্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ যা অন্য কোথাও তেমনটা মনে হয় না এবং এর বিজয়ের প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান যার উদ্ভব ঘটেছে ইউরোপে। পরীক্ষা, নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ এবং গ্রীকদের নিকট অপরিচিত ফর্মে গণিতের যে উৎকর্ষ সাধন ইত্যাদির পদ্ধতিতে অভিনব অনুসন্ধান প্রক্রিয়া সম্বন্ধে তদন্ত চালানোর নব্য চেতনার ফলে এই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উদ্ভব ঘটেছে। ইউরোপীয় বিশ্বে আরবরাই সেই চেতনা এবং পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল।’
ইসলামী সংস্কৃতির মৌল দৃষ্টিভঙ্গি
প্রতিটি জাতীয় সংস্কৃতি তার নিজস্ব পরিবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। একটা বিশেষ দেশের সীমারেখার মধ্যে জীবন যাপনকালী লোকদের উত্তরাধিকারই হয় সেই দেশের সংস্কৃতি। কিন্তু ইসলাম বিশ্বজনীন জীবনাদর্শ। সমগ্র মানব বংশের প্রতিই তার সমান আহ্বান। কোন বিশেষ জাতি, বংশ, গোত্র, সম্প্রদায় বা ব্যক্তির প্রতি তার কোন পক্ষপাত নেই; তার দৃষ্টিকোণ বিশাল, বিস্তীর্ণ, ব্যাপক ও সার্বিক। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের ওপরই তার লক্ষ্য নিবদ্ধ। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা ব্যক্তিগত ও বংশীয় বিশেষত্বের উৎকর্ষ বিধানের জন্যে চেষ্টা-সাধনা চালাতে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করে। আর তার ফলে যে সাংস্কৃতিক ফসল পাওয়া যায়, তার প্রতি তার নেই কোন অনীহা।
একালে শিল্পকলা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ওপর সীমাহীন গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এগুলোর ওপর পূজা-উপাসনার মতোই সংবেদনশীলতার এক মোহময় আবরণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এ ধরণের বাড়াবাড়ি দেখে যে কোন ঈমানদার ব্যক্তি বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেনা। পাশ্চাত্য দেশসমূহে এ বিষয়গুলো সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটা হঠাৎ ঘটে-যাওয়া বিপ্লব রূপে গণ্য হতে পারে কিংবা তাদের জন্যে তা জীবনের একটা লক্ষ্য হতে পারে হয়তবা। কিন্তু মুসলমানরা একে জীবন লক্ষ্য রূপে গণ্য করতে পারে না। তবে এসব সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্প পর্যায়ের কীর্তিসমূহের প্রতি মুসলমানদের মনে কিছুমাত্র অনীহা অথবা ঘৃণা রয়েছে তাও মনে করার কোন কারণ নেই। [অবশ্য ইসলামের তওহীদী চেতনা ও নৈতিকতার দৃষ্টিতে কোন সাহিত্য ও শিল্পকলা আপত্তিকর বিবেচিত হলে সেটা ভিন্ন কথা।- সম্পাদক]। মুসলমানরা এগুলোকে খোদার অনুদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করে এবং নিছক একটা সহায়ক ও বিনোদনমূলক উপাদানই মনে করে। অথচ এগুলো হচ্ছে পথিকের চলার পথের সহজাত আয়েশ ও বিশ্রাম লাভের উপকরণ মাত্র, নিজেই কোন লক্ষ্য বা মনজিল নয়। বড়জোর এগুলো উদ্দেশ্য লাভে ও লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পথে সাহায্যকারী মাত্র। মুসলমানরা এই সাহায্য ও আরাম-আয়েশের পূজারী আদৌ নয়। এ ধরণের কাব্য-সাহিত্য এবং বৈজ্ঞানিক ও শিল্পকলামূলক দুর্লভ সম্পদকে দুটি দিক দিয়ে সাহায্যকারী ও বিনোদনমূলক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। বিশেষত কাব্য-সাহিত্য ও স্থাপত্যশিল্প উভয় দিকেই গণ্য হতে পারে; অর্থাৎ তা যেমন সাহায্যকারী, তেমনি বিনোদনমূলকও।
সমাজবদ্ধ মানব-সমষ্টির মধ্যে মুসলিম জাতির লক্ষ্য, পথ-প্রদর্শক ও আলোক-বর্তিকা এক ও অভিন্ন। আল্লাহর সন্তোষ লাভ তাদের চূড়ান্ত জীবন লক্ষ্য। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সা. তাদের পথ-প্রদর্শক। তাদের অগ্রগতি সাধিত হয় আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদের নিষ্কলংক আলোকের দিগন্তপ্লাবী উজ্জ্বলতায়। ফলে তার (কুরআনের) উপস্থাপিত জীবন ব্যবস্থার প্রতিফলনে যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির উন্মেষ ঘটে কেবলমাত্র তা-ই হতে পারে ইসলামী সংস্কৃতি। মুসলমান নামধারী লোকেরা অতীতে কোন এক সময় যে সংস্কৃতিকে আপন করে নিয়েছিল অথবা ভিন্নতর আদর্শানুসারী জীবন যাত্রার ফলে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, ইসলামী সংস্কৃতি বলতে তা বুঝায়না কখনো। ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্ব-মানবতার সার্বিক ও সামষ্টিক কল্যাণ।
মানবতার কল্যাণ ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের ঐকান্তিক চেষ্টা। ইসলাম মানুষের মন-মগজ ও যোগ্যতা-প্রতিভাকে এরই সাহায্যে পরিচ্ছন্ন ও পরিপুষ্ট করে তুলতে সচেষ্ট। এই বিকাশমান ধারাবাহিকতায় এমন কোন পরিবর্তন বা পর্যায় যদি এসে পড়ে, যা কুরআন মজীদ বা রাসূলের সুন্নাহ অনুমোদিত নয়, তাহলে বুঝতে হবে, সে পরিবর্তন বা পর্যায় ইসলামের মধ্য থেকে সূচিত হয়নি, তার উৎস রয়েছে বাইরে। তাই তা ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন-ধারার পরিণতি বা প্রতিফলন নয় এবং সে কারণে ইসলামী আদর্শ বিশ্বাসী লোকেরা তা গ্রহণও করতে পারে না-তা বরদাশত করে নেয়াও তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। কেননা তার পরিণতিতে মুসলিম জনতা সার্বিকভাবে ধ্বংস, বিপর্যয় ও সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারে না।
শিল্পকলা নামে পরিচিত একালের মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণসহ কয়েক ধরণের সৃষ্টিকর্ম ইসলামে সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ। কেননা মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবে যে প্রতিমা-পূজা ও মুশরিকী ভাবধারা নিহিত মূর্তি বা ভাস্কর্য নির্মাণ তারই চরিতার্থতা ও বহিঃপ্রকাশ মাত্র। প্রথমটির সঙ্গে রয়েছে দ্বিতীয়টির পূর্ণ সাদৃশ্য। এ কারণে শিল্পকলার আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানাদিকে নির্মল করে তোলা মানব জাতির উৎকর্ষ ও কল্যাণ সাধনের জন্যে অপরিহার্য। এই দুনিয়ার জীবনকে কেবলমাত্র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, রূপ-শোভামণ্ডিত ও চোখ-ঝলসানো চাক্চিক্যে সমুজ্জ্বল করে তোলাই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হতে পারে না। মানব জীবনকে ধন্য ও সুসমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বিত পথ ও পন্থা সম্পূর্ণ স্ততন্ত্র ও ভিন্নতর।
সংস্কৃতির কোন কোন উচ্চতর নিদর্শন ও প্রতীক, তা যতই উন্নত মানসম্পন্ন হোক, পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল সংস্কৃতির দর্পন হতে পারে না। কতিপয় ব্যক্তির এইরূপ সৃষ্টিকর্ম অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তিরূপে গৃহীত হওয়া স্বাভাবিক নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। কেননা তাদের প্রধান অংশই পশ্চাদপদ, দীন-হীন ও নিম্নমানের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত। অতএব কথিত শিল্পকর্মকে অধিকাংশ লোকের মহৎ কীর্তি নয়; বরং হীন মন-মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ রূপে গণ্য করতে হবে।
পাশ্চাত্যের পত্র-পত্রিকায় একটা প্রশ্ন নিয়ে যথেষ্ট বাগ-বিতণ্ডা চলেছিল। প্রশ্ন ছিল এই, একটি কক্ষে যদি একটি নিষ্পাপ শিশু থাকে আর সেখানেই এক মূল্যবান, দুর্লভ ও অনন্য গ্রীক ভাষ্কর্য প্রতিমা থাকে আর হঠাৎ কক্ষটিতে আগুন ধরে যায় এবং সে আগুন গোটা কক্ষটিকে গ্রাস করে ফেলে আর সময়ও এতটা সমান্য থাকে যে, তখন হয় শিশুটিকে রক্ষা করা যেতে পারে, নাহয় ভাস্কর্যের নিদর্শনটি, তখন এ দুটির মধ্যে কোন্টিকে বাঁচানোর চেষ্টা করা বাঞ্ছনীয়-মানব শিশুটিকে কিংবা ভাস্কর্য শিল্পটিকে? এই প্রশ্নটি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর জনগণ যে জবাব দিয়েছিল তা ছিল মানব শিশুটির পরিবর্তে ভাস্কর্যটিকে রক্ষা করার পক্ষে। এটা ছিল মানব শিশুটির প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন এবং শিল্পকলার প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের সিদ্ধান্ত। কিন্তু এই জনমতকে কি কোনক্রমে বিবেকসম্পন্ন ও যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায়? তা যায়না। কারণঃ
১. যে শিশুটিকে একটা নিষ্প্রাণ-নির্জীব প্রস্তর মূর্তিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে জ্বলে-পুড়ে মরার জন্যে ছেড়ে দেয়া হল সে একদিন সমাজের এক বিরাট কল্যাণ সাধন করতে পারতো হয়তোবা। আর সে জীবনে বেঁচে থেকে প্রস্তর মূর্তির চাইতেও অনেক অনেক বেশী মূল্যবান ও দুর্লভ জিনিস সৃষ্টির কারণ হতে পারত।
২. সে প্রস্তর মূর্তিটি একটা বিরাট ও উত্যুঙ্গ সভ্যতার খুবই ক্ষুদ্র ও নগণ্য অংশ মাত্র। সেটি জ্বলে-পুড়ে ভস্ম হয়ে গেলে মানবতার এমন কি ক্ষতি সাধতি হতো? কিছুই না।
৩. নৈতিক মূল্যমানের দৃষ্টিতে এ প্রস্তর মূর্তিটি নিতান্তই গুরুত্বহীন একটি বস্তু, অথচ সংস্কৃতিতে নৈতিক মূল্যমানের ভূমিকা অত্যন্ত প্রকট ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।
আলোচ্য ঘটনায় দেখা গেল, মানুষের তুলনায় প্রস্তর মূর্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর প্রস্তর মূর্তির তুলনায় মানুষ অতীব তুচ্ছ-মূল্যহীন! পাশ্চাত্য সুধীদের এই মনোভাবের ফলে মূর্তি পূজার একটা নবতর সংস্করণ প্রসার ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এ অবস্থা অস্বাভাবিক ও অকল্পনীয়। ইসলাম মানবতার এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে কাজ করে। মানুষের কোন মূল্যবান শিল্পকর্মের জন্যে একটা মহামূল্য মানব সন্তানের জীবন উৎসর্গ করা ইসলামের ধারণাতীত। মানুষের দুর্লভ কীর্তির প্রতি এই আসক্তি ও ভক্তি কার্যত আল্লাহর প্রতি ঈমানের অস্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ যখন নিজের চিন্তা-বিশ্বাসকে খোদায়ী বিধান হতে স্বতন্ত্র ও নিঃসম্পর্ক করে নেয়, তখন তার ভ্রষ্টতা ও বিভ্রান্তি সীমাহীন হয়ে যায়। তখন চূড়ান্ত ধ্বংসই হয় তার অনিবার্য পরিণতি। এই দৃষ্টিকোণের ধারকরা বলেন, শিল্প-সৌন্দর্য ক্রমশ হ্রাসপ্রাপ্ত হচ্ছে। প্রাচীন মানব সভ্যতা পতনোন্মুখ। একারণেই ভাষ্কর্যের নিদর্শনটিকে রক্ষা করা অপরিহার্য। কেননা অতীতের দুর্লভ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি কিছুতেই উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু এইটুকু যুক্তিকে মানুষের সৃষ্টির তুলনায় আল্লাহর সৃষ্টিকে মূল্যহীন ভাবাকে কোন মানুষই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারে না।
ইসলামের কল্যাণমূলক দৃষ্টিকোণ ব্যক্তির অন্তরে একদিকে শুভেচ্ছা ও শুভাকাঙ্ক্ষা এবং অন্যদিকে অনুতাপ ও তিরস্কারের ভাব জাগ্রত করে আর এটাই হচ্ছে সাফল্য ও সার্থকতা লাভের প্রধান উপায়। যাকাতের মাধ্যমে এই চেতনা কার্যকর হয় মূলধনের হ্রাস-প্রাপ্তির ফলে আর তার ফলেই মূলধন পবিত্র ও ক্রমবৃদ্ধি লাভ করে। ইসলাম জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সমানভাবে পরিব্যপ্ত। তাতে ধর্মচর্চা ও ধর্মনিরপেক্ষতার পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ ও প্রগতিই ইসলামের কাম্য। এখনে শুধু ভালো ও মন্দ তথা কল্যাণ ও অকল্যাণের পার্থক্যই স্বীকৃত। বৈরাগ্যবাদ বা দুনিয়াত্যাগের কোন অনুমতি বা অবকাশ ইসলামে নেই। প্রতিটি ব্যক্তির রয়েছে বহুমুখী কর্তব্য ও দায়িত্ব। সফল ও সার্থক কার্যাবলী সংঘটিত হয়ে সে সব সমর্পিত কর্মক্ষমতার দরুন, যা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহ তা’আলা নিজের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি দ্বীনের সর্বাত্মক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তা বাস্তব, অবিমিশ্র ও সারবত্তাপূর্ণ পূর্ণাঙ্গ দ্বীনী ব্যবস্থা; জীবনের প্রতিটি মূহুর্তেই তা অবশ্য অনুসরণীয়। কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক ইবাদতসমূহের নির্দিষ্ট সময়টুকুতে তার অনুসরণ নিতান্তই অর্থহীন।
ফরাসী ও রুশ বিপ্লবে আল্লাহর কোন স্থান স্বীকৃত নয়। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ হল বৈষয়িক জীবন ও রাজনীতিতে আল্লাহর কোন অংশ নেই। কিন্তু এ বিশ্বলোকে এবং মানব সমাজে প্রতি মুহূর্তে ও প্রতি নিমিষে এমন অসংখ্য ঘটনাবলী সংঘটিত হচ্ছে, যে বিষয়ে কোন ভবিষ্যৎবাণী কোন মানুষ করতে সক্ষম নয়- তা কাঙ্ক্ষিত বা প্রার্থিতও নয়। এ ধরনের ঘটনাবলীর আকস্মিক আত্মপ্রকাশ মানুষের সব পরিকল্পনা ও প্রস্তাবনাকে চুরমার করে দেয়- ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয় তার সব স্বপ্ন-সাধ। কিন্তু আল্লাহকে বা আল্লাহর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে অস্বীকার করে সে সবের কি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে?
মধ্যযুগীয় ধর্মচর্চা হচ্ছে বিস্ময়কর ঘটনাবলীর গল্প-কাহিনী, রসম-রেওয়াজ, উপাসনা-আরাধনা ও উপাসনালয়-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠানাদি সমন্বিত। জগতের রূঢ় বাস্তবতা, বৈষয়িক তৎপরতা ও ব্যতিব্যস্ততা থেকে পলায়নের পথ হিসেবেই তা অবলম্বিত হতো। সেকালের লোকদের অভিমত ছিল, বাস্তব জীবনকে অবশ্যই ধর্মহীন বা ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত হতে হবে। আর কৃচ্ছসাধক ও একনিষ্ঠ পূজারীদের তা-ই হচ্ছে রক্তিম স্বপনের পরকাষ্ঠা। এ দৃষ্টিকোণের মারাত্মক প্রভাব আজ দুনিয়ার সর্বত্র ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত। হীন স্বার্থের কুটিল চক্রান্তে লিপ্ত হয়ে মানুষ আজ সমাজের সাধারণ শান্তি ও শৃঙ্খলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। ক্ষমতাবানরা মানুষের মৌলিক ও বৈধ অধিকার হরণ করেছে নিষ্ঠুরভাবে। জনগণের রক্ত পানি করে উপার্জন করা বিত্ত-বৈভবের ওপর চলেছে নির্মম লূটপাটের পৈশাচিকতা। সব দুষ্কর্মের পশ্চাতে ব্যক্তি-স্বার্থই ছিল প্রধান নিয়ামক। কিন্তু যারা ভালোমানুষ, সত্যই তারা ব্যক্তি-স্বার্থকে সামষ্টিক স্বার্থের জন্যে উৎসর্গ করে। কেননা তাতেই নিহিত রয়েছে মানবতার বৃহত্তর কল্যাণ ও সাফল্য। ব্যক্তিবাদের ওপর সমষ্টিবাদের প্রাধান্য এভাবেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ হচ্ছে চরম লক্ষ্যের নিকটবর্তী পর্যায়। নৈতিক ভিত্তিসমূহ তখন হয় পাকা-পোক্ত, অবিচল ও অনড়। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী ও নিত্য-নব উদ্ঘাটন তার ভিত্তিমূলের ওপর কোন প্রতিকূল প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না।
মোটকথা, ইসলামী সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে দ্বীন-ভিত্তিক। এই দ্বীনি ভাবধারাই তার প্রাণ-শক্তি ও আসল নিয়ামক। দ্বীনী ভাবধারাশূণ্য সংস্কৃতি কখনও ইসলামী পদবাচ্য হতে পারে না-হতে পারে অন্য কিছু। এখানে প্রতিটি কাজ, পদক্ষেপ বা অনুষ্ঠানের বৈধতা দ্বীন-ইসলাম থেকে গ্রহণীয়। কেননা তা আল্লাহর দেয়া বিধি-বিধান ও নির্দেশনার সমষ্টি। জীবনের প্রতিটি বাঁকে, প্রতিটি স্তরে ও প্রতিটি চড়াই-উৎরাইয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনাকে পথিকের যাত্রা সুগম করে ও তাকে অগ্রগমনের প্রেরণা দেয়। বিশ্বনবীর বাস্তব জীবনে ও কর্ম-ধারায় তা পূর্ণমাত্রায় প্রতিফলিত। তাতে স্পষ্টত প্রত্যক্ষ করা যায় যে, ইসলামী সংস্কৃতি নিছক কতকগুলো আকীদা-বিশ্বাসেরই সমষ্টি নয়। বাস্তব কর্ম সম্পাদনই তার আসল কথা আর জাতীয় সাফল্য ও সার্থকতা লাভ কেবলমাত্র এভাবেই সম্ভবপর।
ইসলামী সংস্কৃতি ও মানব জীবনে তার কার্যকারিতা উপলব্ধি করার জন্যে আরও একটা দিক দিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। কুরআন মজীদে ‘তাযকিয়া’ শব্দটি বহুল-ব্যবহৃত। ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ভাষায় এ শব্দটির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আমাদেরকে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কিত প্রকৃত ধারণা (conception) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তিনি বলেছেনঃ
‘‘তায্কিয়া’ অর্থ পবিত্র হওয়া, পবৃদ্ধি লাভ করা-অন্যায় ও কদর্যতা পরিহার করে চলা, যার ফলে আত্মার শ্রীবৃ্দ্ধি, আধিক্য ও প্রাচুর্য সাধিত হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেনঃ সফলতা পেল সে, যে আত্মাকে পরিচ্ছন্ন করল। একারণে যাকাত শব্দের অর্থ কখনও বলা হয় প্রবৃদ্ধি, আধিক্য বা পাচুর্য আর কখনও করা হয় পবিত্রতা, পচ্ছিন্নতা ও ময়লা-আবর্জনা দূর করা। কিন্তু সত্য কথা হল যাকাত শব্দে এ দুটি অর্থেরই সমন্বয় ঘটেছে। অন্যায় ও ময়লা দূর করা যেমন এর অর্থ তেমনি কল্যাণ ও মঙ্গল বৃদ্ধি করাও এর মধ্যে শামিল।’
এ ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়ঃ কুরআনে যে ‘তাযকিয়ায়ে নফস’ (আত্মশুদ্ধি)-এর কথা বলা হয়েছে, তাতে এক সঙ্গে কয়েকটি কথা নিহিত রয়েছেঃ
১. তাযকিয়ার আসল অর্থ মানবাত্মার উৎকর্ষ সাধন ও উন্নতি বিধান করা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-যোগ্যতা ও কর্ম-ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ-উচ্চকিত করা, সতেজ বা ঝালাই করা, ময়লা-আবর্জনা-দুর্বলতা ও পংকিলতামুক্ত করা এবং তাকে পূর্ণ পরিণত করে তোলা। দেহ ও আত্মা, মন ও মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচার-আচরণের যে সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের দরুন জীবন পূর্ণত্ব লাভ করতে পারে-পারে সফল ও সার্থক হতে, তা অর্জনের সঠিক চেষ্টা-সাধনাই আত্মার তাযকিয়া। আর ইসলামী সংস্কৃতির মূল লক্ষ্যও তা-ই।
২. জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তোলার মানে সর্বপ্রকারের অন্যায়, অশ্লীলতা ও পংকিলতা থেকে তাকে মুক্ত ও পবিত্রকরণ (Purification)। কেননা এছাড়া জীবনের সংস্কার ও উন্নয়ন সাধন অসম্ভব। বাস্তবতার দৃষ্টিতেও এ জিনিসটি জীবনে শোভা-সৌন্দর্য, বৈশিষ্ট্য-বিশেষত্ব ও মহিমা-মাহাত্ম্য অর্জনের আগেই অর্জি হওয়া উচিত। পবিত্রকরণ ও সংস্কার সাধন জীবনের ‘তাযকিয়া’ ও পূর্ণত্ব বিধানের প্রাথমিক কাজ। এইসব কারণে অনেক সময় পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ এবং সংস্কার সাধনের অর্থেও ব্যবহৃত হয় এই তাযকিয়া শব্দ।
এখানে নফসের বা আত্মার তাযকিয়া বলে যা কিছু বোঝাতে চাওয়া হয়েছে তাতে কেবল মানব জীবনের খারাপ দিকের তাযকিয়া বা পবিত্র-পরিচ্ছন্নকরণই লক্ষ্য নয়-বরং সমগ্র মানব সত্তাই এর ক্ষেত্র। কুরআনে বলা হয়েছেঃ
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا – فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا – قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا – وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
‘‘মানব প্রকৃতি এবং সেই সত্তার শপথ, যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন; অতঃপর তার পাপাচার ও তার সতর্কতা (তাকওয়া) তার প্রতি ইলহাম করেছেন। নিঃসন্দেহে কল্যাণ পেল সে, যে নিজের নফসের পবিত্রতা বিধান করল আর ব্যর্থ হল সে, যে তাকে খর্ব ও গুপ্ত কর।’’ (সূরা আশ্-শামসঃ ৭-১০)
এ আয়াতে মানুষেরর গোটা সত্তাকেই সামনে রাখা হয়েছে। এ পর্যায়ের অন্যান্য আয়াতেও মানুষের সমগ্র সত্তার পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও সংস্কার সাধন এবং উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠা বিধান অর্থেই এ শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে।
৩. আত্মার তাযকিয়া সম্পর্কে কুরআন যে ধারণা পেশ করেছে, তা হল Self-perfection-এর ধারণা। এর ভিত্তি দুটি জিনিসের ওপর সংস্থাপিত। একটি হচ্ছে মানুষের রূহ বা আত্মা-তথা মন ও মগজের সমস্ত শক্তির একটা সমন্বিত ও সুসংহত রূপ। আল্লাহ তা’আলা মানুষকে তাঁর সৃষ্ট-ক্ষমতার সর্বোত্তম ও সর্বাঙ্গীন সুন্দর নিদর্শনরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই সৃষ্টিকর্মে মানুষের নানাবিধ যোগ্যতা ও প্রবণতায় এক উচ্চ মানের ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে। এ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সত্তার আত্মা ও বস্তু, জ্ঞান ও বিবেক, বাহির ও ভিতরের মাঝে আল্লাহ কোন বিরোধ বা বৈষম্যকে স্বীকার করেন না। এসবের মাঝে গুরুত্বের দিক দিয়ে শ্রেণী-পার্থক্য রয়েছে বটে; কিন্তু সে শ্রেণীগুলোর মধ্যে কোন দ্ব্ন্দ বা বিরোধ স্বীকৃত নয়। একটির উৎকর্ষের জন্যে অপরটিকে অবলুপ্ত করা বা অবদমন (Suppression) করা জরুরী নয়; বরং একটির পূর্ণত্ব অপরটির উন্নয়নের জন্যে পরিপূরক।
এ জন্যেই কুরআনের শিক্ষা হল এই কামনা করাঃ
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
‘‘হে আমাদের প্রতিপালক। আমাদেরকে কল্যাণ ও মঙ্গল দাও এই দুনিয়ায় এবং পরকালেও আর জাহান্নামের আযাব থেকে আমাদেরকে বাঁচাও।’’ (সূরা বাকারাঃ ২০১)
দ্বিতীয় বিষয় হল, মানুষের সমগ্র সত্তার যুগপৎ উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য এবং কাম্য। এ সত্তার পতিটি অংশই মহামূল্য এবং তার সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধকরণ, পুনর্গঠন ও উন্নয়নই বাঞ্ছনীয়। দৈহিক উন্নতি এবং নৈতিক ও আত্মিক পূর্ণত্ব-এর প্রতিটিই নিজ নিজ সীমার মাঝে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও চিন্তা, মন ও মগজ, চরিত্র ও স্বভাব, সৌন্দর্যপ্রীতি ও সুরুচি-প্রবণতা এবং দেহ ও মনের সব দাবির ভারসাম্যপূর্ণ পূরণ এবং সুসামঞ্জস্য সংস্কার সাধন ও পূর্ণত্ব বিধানকেই বলা হয় ‘তায্কিয়া’ এবং তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। মনের ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে দৈহিক সীমা লংঘন কিংবা দৈহিক চাহিদা পূরণে মনের তাগিদ উপেক্ষা করা ইসলামের সংস্কৃতি চেতনার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কিন্তু কোন বিশেষ মুতূর্তে এ দুটির মাঝে তারতম্য করা যদি অপরিহার্যই হয়ে পড়ে তাহলে দেহের পরিবর্তে মনের গুরুত্ব-বস্তুর তুলনায় আত্মার এবং প্রস্তর বা ভাস্কর্য অপেক্ষা মানুষের গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। [সংস্কৃতি সংক্রান্ত আলোচনায় ইদানীং ‘অপসংস্কৃতি’ বলে একটি শব্দের ব্যবহার প্রায় লক্ষ্য করা যায়। এর সর্বসম্মত কোন সংজ্ঞা নির্ণয় করা খুবই মুশকিল। তবে সংস্কৃতির নামে যাকিছু মানুষের সুস্থ চিন্তা-ভাবনা নৈতিকতা রুচিবোধ, শালীনতা ইত্যাদিকে কলূষিত করে তাকেই আমরা অপসংস্কৃতি বলতে পারি।- সম্পাদক]
মোটকথা, কুরআনের যেসব স্থানে ‘তাযকিয়া’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, সেসব স্থানে সংস্কৃতি শব্দ বসিয়ে দিলে যেরূপ দাঁড়ায় ইসলামী সংস্কৃতির তাৎপর্য বিশ্লেষণে তা-ই বক্তব্য। অন্য কথায়, কুরআনে ‘তাযকিয়া’ শব্দের যে ব্যাখ্যা এখানে দেয়া হল তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি-ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা।
ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারা
ইসলামী সংস্কৃতি বলতে বুঝায় উন্নততর মতাদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান (Values)। আর এর মৌল ভাবধারা হচ্ছে সে সব মূলনীতি, যার ওপর আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর দৃঢ়তা ও স্থিতি নির্ভরশীল। সে মূলনীতিগুলোকে ব্যাপকভাবে গণনা করলে তার সংখ্যা অনেক হবে; তবে পরে আমরা সংক্ষেপে বিশিষ্ট মূলনীতিসমূহের উল্লেখ করব।
ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা হল একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ তা’আলা গোটা বিশ্বলোকের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভূ। হযরত মুহাম্মদ সা. দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি এবং কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম-হেদায়েতের সর্বশেষ বিধান।
ইসলামী মতাদর্শে তওহীদ বিশ্বাস হল সর্বপ্রথম এবং সর্বাধিক মৌলিক বিষয়। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ মা’বুদ নেই (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ)- এই ঘোষণাটি হচ্ছে তওহীদের সার নির্যাস, অন্য কথায় আল্লহকে প্রকৃত মা’বুদ রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁরই নিরংকুশ প্রভূত্ব ও কর্তৃত্ব (সার্বভৌমত্ব) স্বীকার করার পর মানুষ দুনিয়ায় খোদায়ীর দাবিদার অন্যান্য দেব-দেবী, অবতার, রাজা-বাদশাহ এবং সম্পদ-দেবতার দাসত্বের অভিশাপ থেকে চিরকালের তরে মুক্তি লাভ করতে পরে। তওহীদের এ আকীদার দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতি বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য-বিরোধ, আর্থিক অবস্থাভিত্তিক শ্রেণী-পার্থক্য, ভৌগোলিক সীমাভিত্তিক শত্রুতা প্রভৃতিকে আদৌ বরদাশত করতে পারেনা; অথচ এসবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা। মানুষে মানুষে যৌক্তিক ও সঠিক সাম্যই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামী সংস্কৃতির একমাত্র দৃষ্টি। আল্লাহকে এক ও লা-শরীক সর্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকারসম্পন্ন মেনে নেয়া-শুধু মৌখিকভাবে মেনে নেয়াই নয় বাস্তবক্ষেত্রেও সেই অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালিত করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মমাণী। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে একজন শ্রমজীবীও তেমনি সম্মানার্হ যেমন সম্মানীয় কোন কারখানার মালিক। নিগ্রো মুষ্ঠিযোদ্ধা মুহাম্মাদ আলী ক্লে ও শ্বেতাঙ্গ চিন্তাবিদ মুহাম্মাদ মার্মাডিউক পিক্থল অভিন্ন শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলামী সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই তার খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন অবাধে পূরণের অধিকারী। এ অধিকার সত্যিকারভাবে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করাই ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।
ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ভারসাম্যপূর্ণ আচরণ রীতি এবং সংযত, নিয়ন্ত্রিত ও সক্রিয় জীবনের গুরুত্ব সর্বাধিক। মানুষের জীবন অবিভাজ্য; বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী অংশ বা বিভাগে তাকে ভাগ করা যায় না। মানুষের সত্যিকার উন্নতি নির্ভর করে দেহ ও আত্মা তথা বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক জীবনের ঐকিক কল্যাণের উপর। দেহ ও আত্মার বিরোধ মিটিয়ে একাকার করে দেয়াই ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য, যদিও দুনিয়ার অনেক সংস্কৃতিরই লক্ষ্য এ দুয়ের মাঝে বিরোধ ও দ্বৈততাকে বজায় রাখা এবং একটি নস্যাৎ করে অপরটির পরিতৃপ্তি সাধন।
Hedonism বা ভোগবাদী ও আনন্দবাদী চিন্তা-দর্শনে বিশ্বাসীরা আজো আত্মার দাবিকে অস্বীকার করে এবং আত্মার মর্যাদা ও প্রবণতাকে অমর্যাদা করে কেবল দৈহিক সুখ ভোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করছে। তাদের মূল মন্ত্র হলঃ Pleasure is the highest good- ‘সুখ ভোগ বা আনন্দ লাভই শ্রেষ্ঠতর কল্যাণ।’
কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি দেহ ও আত্মার মাঝে পরিপূর্ণভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্প। এর কোনটিকে অস্বীকার করা কিংবা একটি দিকের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা এবং সেদিকেই গোটা জীবনকে পরিচালিত করা ইসলামের সাংস্কৃতিক আদর্শের পরিপন্থী। এ ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতিবাদীদের লক্ষ্য করেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ
وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا
‘‘এমনিভাবেই তোমাদেরকে আমরা মধ্যম নীতির অনুসারী করে বানিয়েছি, যেন তোমরা সমগ্র মানুষের পথ-প্রদর্শক হতে পার এবং রাসূল হতে পারে তোমাদের পথ-প্রদর্শক।’’ (সূরা বাকারাঃ ১৪৩)
অন্যকথায় রাসূলের আদর্শ অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ। এ ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ অনুসারীরাই বিশ্বমানবের নেতৃত্বের অধিকারী হতে পারে সংস্কৃতি ও সভ্যতা উভয় দিক দিয়েই। আর একটি ভারসাম্যপূর্ণ জাতিই পারে এক ভারসাম্যপূর্ণ সংস্কৃতির জন্ম দিতে। সে কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি না একথা বলেছে যে, মানুষ বৈরাগ্যবাদ গ্রহণ করবে এবং দুনিয়ার কাজকর্ম ও দায়-দায়িত্ব ছেড়ে দূরে নিবিড় জঙ্গলে কিংবা খানকার নির্জন পরিবেশে আশ্রয় নেবে আর না এ শিক্ষা দিয়েছে যে, সে কেবল দুনিয়ার কাজকর্মকেই জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে গ্রহণ করবে-তাতেই মশগুল হয়ে থাকবে একান্তভাবে; বরং তার শিক্ষা হল, মানুষ দুনিয়ার জীবনেক সঠিক পন্থায় এবং পুরোমাত্রায় যাপন করে আল্লাহর সন্তোষ লাভে জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করবে; এটাই হল আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের একমাত্র কাজ। ইসলামী সংস্কৃতি এ উভয় দিকে নিহিত অযৌক্তিক প্রবণতা ও অবৈজ্ঞানিক ভাবধারাকে পরিহার করে এবং এ দুয়ের মাঝে সমন্বয় সৃষ্টি করে এক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ-পরিবেশ গড়ে তুলতে চায়। অর্থাৎ দুনিয়ায় থেকেও দুনিয়াবিমুখ হওয়া এবং দুনিয়াবিমুখ হলেও দুনিয়া ভোগ করা-এই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মবাণী। রসূলে করীম সা. একথাই বুঝিয়েছে তাঁর এ উক্তি দিয়েঃ
‘‘দুনিয়ায় বসবাস করবে যেন তুমি পথ অতিক্রমকারী এক মুসাফির।’’
ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য হল ব্যক্তিসত্তা ও সমাজ-সংস্থার পূর্ণত্ব বিধান। প্রধানত দুটি দিক দিয়েই ইসলামী সংস্কৃতির ধারণা (Conception) অন্যান্যদের ধারণা থেকে ভিন্ন ও বিশিষ্ট। একটি এই যে, ইসলামের উপরিউক্ত লক্ষ্য ইসলামী শরী’আতের সীমার মাঝে এবং কুরআন ও সুন্নাহর পরিচালনাধীনে অর্জিত হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়টি হল, এ পর্যায়ে যা কিছু চেষ্টা-সাধনা, আয়োজন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, সব হতে হবে আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা সহকারেই আল্লাহর সন্তোষ লাভের এ চেষ্টা চলতে হবে।
কুরআন ও সুন্নাহর দৃষ্টিতে ব্যক্তির সংশোধন, পুনর্গঠন ও পূর্ণতা বিধানের জন্যে সমাজ ও সমষ্টির সংশোধন ও পুনর্গঠন একান্তই জরুরী। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি প্রায় অসম্ভব। অধিকাংশ ব্যক্তি-সত্তার সংস্কার সংশোধন ও পূর্ণত্ব বিধান গোটা সমাজের সংশোধন ও সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল। শেষের কাজটি না হলে প্রথমটি আদৌ সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে সমাজ সংশোধন ও সংস্কার প্রচেষ্টাই ব্যক্তি জীবনে এনে দেয় সংশোধন ও সংস্কারের বন্যা-প্রবাহ। তাই এ প্রচেষ্টা হতে হবে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক যেমন, সমাজ-কেন্দ্রিকও তেমনি।
এই প্রসঙ্গে একটি ভুল ধারণার অপনোদন করা প্রয়োজন। কিছু লোক মনে করে যে, মুসলমান নামধারী ব্যক্তি বা সমাজ যেসব অনুষ্ঠান ও ভাবধারাকে সংস্কৃতি রূপে গ্রহণ করেছে, তারই নাম ইসলামী সংস্কৃতি; কিন্তু এ ধারণা মোটেই সঠিক নয়। ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিই মুসলিম সংস্কৃতি নামে অভিহিত হতে পারে, যার সন্ধান পাওযা যায় কুরআন ও সুন্নাতে কিংবা যার সমর্থন মেলে আল্লাহ ও রাসূলের কাছ থেকে এবং যার লক্ষ্য মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন। মুসলিম সমাজে এমন কোন ভাবধারা বা সংস্কৃতি যদি দেখা যায়, কুরআন ও সুন্নাহ যার অনুমতি দেয় না, তাহলে বুঝতে হবে, তা ইসলামী সংস্কৃতি নয়, তা মুসলমানদের নিজস্ব জিনিসও নয়; বরং তা মুসলিম সমাজের বাইরে থেকে আমদানী করা জিনিস। তা গ্রহণ করে মুসলমানরা নিজেদের ধ্বংসেরই ব্যবস্থা করতে পারে। এছাড়া কোন কল্যাণই তাতে নেই-থাকতে পারে না।
Fine Arts বা ললিতকলার যেসব ধরণ-বা উপকরণ ইসলামে নিষিদ্ধ, তা নিষিদ্ধ এই কল্যাণদৃষ্টির কারণেই। ইসলামী সংস্কৃতি মানুষের জীবনকে চায় সুন্দর সুষমামণ্ডিত, সবুজ-সতেজ, আনন্দমুখর ও উৎফুল্ল করে গড়ে তুলতে; কিন্তু তা সবই করতে চায় কুরআন ও সুন্নাতের আলোকে, মানুষের সঠিক কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে।
সংস্কৃতির পাশ্চাত্য মূল্যয়ন
সংস্কৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দর্শন মানবতাবাদী নয়-নয় তা মানষের জন্যে কল্যাণকর। এ দর্শনে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানব সন্তানের চেয়ে নিষ্প্রাণ প্রস্তর মূর্তির মূল্য অনেক বেশি। এ ব্যাপারে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করাই যথেষ্ট। একবার পশ্চিমা পত্র-পত্রিকায় নিশ্চিত ধ্বংসের কবল থেকে একটি নিষ্পাপ শিশু অথবা গ্রীক ভাস্কর্যের একটি দুর্লভ, অদ্বিতীয়, উন্নত মানের নিদর্শনের কোন্টিকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করা উচিত এই মর্মে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। পাঠক সাধারণের তরফ থেকে এ প্রশ্নের জবাবে একবাক্যে মানব শিশুর পরিবর্তে ভাস্কর্যশিল্পের অতুলনীয় নিদর্শনটিকে বাঁচাবার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। তার মানে এই দাঁড়ায় যে, পাশ্চাত্য সমাজের দৃষ্টিতে মানুষের চাইতেও অধিক প্রিয়, অধিক মূল্যবান এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাস্কর্য শিল্প-প্রস্তরনির্মিত একটি নিষ্প্রাণ প্রতিমা। এমনিভাবে নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয়ের যত অনুষ্ঠানই আজ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামে মানবসমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার সবক’টিতেই যে মনুষ্যত্বের অপমান-মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু ঘটে,তাতে কোন সন্দেহ আছে কি? বস্তুত মানবতার ধ্বংসই এসবের একমাত্র পরিণতি। আর ইসলামের দৃষ্টিতে যা কিছু মানবতাবিধ্বংসী তথা মানব চরিত্র বিকৃতকারী, তা মানুষের পাশববৃত্তির চরিতার্থতা, চিত্তবিনোদন ও আনন্দ বিধানের যত বড় আয়োজনই হোকনা কেন, তা সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ারই যোগ্য নয়। এই ধরণের আচার-অনুষ্ঠানকে ইসলামী সংস্কৃতি নামে অভিহিত করার মতো ধৃষ্টতাও আর কিছু হতে পারে না।
ইসলামী সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনাঃ
এই পর্যায়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ইসলামী সংস্কৃতির মৌল ভাবধারাকে পাশাপাশি রেখে তুলনা করলে কথাটি আরো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।
ইসলামী সংস্কৃতি ও পশ্চিমা সংস্কৃতি
১. ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। তার নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থেকে মানুষ নিজ ইচ্ছা ও ক্ষমতার প্রয়োগ করতে পারে। এ সীমা ও জীবন-লক্ষ্য শাশ্বত, অপরিবর্তনীয়, চিরন্তন সত্যের ধারক ও বাহক। অতএব এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই আ্ল্লাহর গুণাবলীকে-যা বিশ্বলোকে স্থায়ী মূল্যমানের উৎস-নিজের মাঝে প্রতিফলিত করে নিতে পারে।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মূল দর্শন হল, এ জীবন কয়েকটি মৌল উপাদানের উদ্দেশ্যহীন সংমিশ্রণের ফলে অস্তিত্ব লাভ করেছে। এর কোন লক্ষ্য নেই-নেই কোন পরিণতি। এসব মৌল উপাদানের পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ারই নাম মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কিছুই নেই-আছে শুধু অন্তহীন শূণ্যতা।
ইসলামী সংস্কৃতি সমাজে ব্যক্তিদের মাঝে এমন শৃংখলা গড়ে তোলে, যাতে করে ব্যক্তি-চরিত্র ও সমাজ-সংস্থায় আল্লাহর ভারসাম্যপূর্ণ গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটতে পারে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে জীবন যেহেতু একটা আকস্মিক ঘটনা-একটা accident মাত্র, এজন্যে দুনিয়ায় কোন স্থায়ী মূল্যমান (Permanent Values) নেই- নেই প্রতিফল দানের বা প্রতিফল পাওয়ার কোন সুব্যবস্থা।
ইসলামী সংস্কৃতি ব্যক্তিদের মাঝে এমন যোগ্যতা ও প্রতিভা জাগিয়ে দেয়, যার কারণে প্রকৃতি জয়ের ফলাফল সাধারণভাবে সমগ্র মানব জাতির কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে।
পশ্চিমা সংস্কৃতি-দর্শনে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির সুবিধা হয-তা অপর ব্যক্তি বা জাতির জীবন ধ্বংস করেই হোক না কেন- তা-ই ন্যায়, সত্য, ভালো ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে যে কথা ও কাজে ব্যক্তি বা জাতির অসুবিধা বা স্বার্থহানি হয়, তা-ই অন্যায়, তা-ই পাপ।
ইসলামী সংস্কৃতিতে বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব, স্রষ্টার একত্ব ও মিল্লাতের অভিন্নতার ভিত্তিতে এক ব্যাপকতর ঐক্য ও সম্মিলিত ভাবধারা গড়ে ওঠে। এ ফলে মানব সমাজ থেকে সবরকমের জোর-জবরদস্তি, স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, জুলুম-শোষণ ও হিংসা-দ্বেষ দূরীভূত হয়ে যায় এবং পরস্পরের আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।
পশ্চিমা সংস্কৃতি যেহেতু ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুখবাদী দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে, সেজন্যে এরই ফলে বিশ্বের ব্যক্তি ও জাতিগুলোর মাঝে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম, হিংসাদ্বেষ, রক্তারক্তি ও কোন্দল-কোলাহয অনিবার্য হয়ে ওঠে। এরই কারণে চারদিকে চরম বিপর্যয় ও অশান্তি বিরাজমান থাকে-শাসক ও শাসিত, বিজয়ী ও বিজিতের বিভিন্ন শ্রেণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।
ইসলামী সংস্কৃতিবান প্রতিটি ব্যক্তি অন্য মানুষের জন্যে বেঁচে থাকে। এ কারণে শ্রেণী-ভেদ নির্বিশেষ সমাজের প্রতিটি মানুষের জীবন-জীবিকা ও যাবতীয় প্রয়োজন আপনা থেকেই পূরণ হতে থাকে।
পশ্চিমা সংস্কৃতি বিজিত জাতিগুলোকে প্রকৃতি-জয়ের সব তত্ত্ব, তথ্য ও গোপন রহস্য থেকে সম্পূর্ণ গাফিল বানিয়ে রাখে- বঞ্চিত রাখে সব প্রাকৃতিক কল্যাণ, সম্পদ ও সম্পত্তি থেকে। এ সংস্কৃতি সব কিছুকে নিজেদের একচেটিয়া ভোগ-দখলে রেখে দেয় এবং বিজয়ী জাতির প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের মন-মগজেহ বদ্ধমূল করে দিতেই সচেষ্টা হয়।
ইসলামী সংস্কৃতির মৌল বৈশিষ্ট্য
উপসংহারে ইসলামী সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাচ্ছেঃ
১. তওহীদ, ২. মানবতার সম্মান, ৩. বিশ্ব-ব্যাপকতা, সর্বজনীনতা (universality), ভৌগোলিক অভিন্নতা, ৪. মানবীয় ভ্রাতৃত্ব ৫. বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, ৬. বিশ্ব-মানবের ঐক্য, ৭.. কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ, ৮. পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা এবং পংকিলতা থেকে মুক্তি, ৯. ব্যক্তি-স্বতন্ত্র্যের মর্যাদা, ১০. ভারসাম্য, সুষমতা ও সামঞ্জস্য।
এসব মৌল উপাদান ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, তা-ই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি। যে সংস্কৃতিতে এর কোন একটি উপাদান ও ভাবধারার অভাব থাকবে, তা আর যাই হোক ইসলামী সংস্কৃতি হবে না এবং তা হতে পারেনা ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসীদের গ্রহণযোগ্য সংস্কৃতি।
বর্তমান মুসলিম সমাজে এর বিপরীত আদর্শের উপাদান ও ভাবধারায় গড়া সংস্কৃতি বিরাজমান। বিদেশী বিজাতীয় ভাবধারার প্রভাবে মুসলিম সংস্কৃতি আজ পংকিলতাময়। আজ আমাদের সংস্কৃতিকে বিদেশী ও বিজাতীয় উপাদান ও ভাবধারা থেকে মুক্ত করে ইসলামী আদর্শের মানে উত্তীর্ণ এক নতুন সংস্কৃতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ইসলামী আদর্শবাদীদের সংগ্রাম চালাতে হবে। এ সংগ্রাম কঠিন, ক্লান্তিকর ও দুঃসাধ্য। এ পথে পদে পদে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কিন্তু পরিপূর্ণ নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সাথে এ সংগ্রাম চালাতে পারলে এর জয় সুনিশ্চিত। বর্তমান বিশ্ব এমনি ভারসাম্যপূর্ণ, মানবতাবাদী ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর এক সংস্কৃতির প্রতীক্ষায় উদগ্রীব।
ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তওহীদ। তওহীদ বা একত্ববাদ বলতে বুঝায় আল্লাহ তা’আলার নিরঙ্কুশ এককত্বের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন। তওহীদ ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিক সম্পর্কে ধারণা উপস্থাপন করে। ইতিবাচক ধারণা এই যে, বিশ্বলোকে সৃষ্টিকর্তা আছেন এবং তিনি এক ও একক। আর নেতিবাচক ধারণা এই যে, তাঁর মতো কেউ নেই-কিছু নেই; কেউ হতে পারেনা তাঁর সমতুল্য। গোটা বিশ্বলোকে তিনি একক এখতিয়ারসম্পন্ন ও নিরংকুশ ক্ষমতার অধিকারী সত্তা। তিনি যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারেন; যা ইচ্ছা তারই ফয়সালা করেন-আদেশ ও নির্দেশ দেন। ইসলামের দৃষ্টিতে তওহীদের ধারণা পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ। ‘ইলাহ’ হিসেবেও তিনি এক ও একক। তিনি ছাড়া আর কেউ ‘ইলাহ’ নয় এবং ‘ইলাহ’ হওয়ার যাবতীয় বৈশিষ্ট্য কেবল এককভাবে তাঁরই জন্যে শোভনীয়-তার সত্তায়ই নিহিত।
স্রষ্টা বা খোদাকে ‘এক’ বলে জানার ও মানার কথা অন্যান্য ধর্মে ও সংস্কৃতিতে স্বীকৃত হলেও তাতে রয়েছে অসংখ্য ভূল-ভ্রান্তি। কেউ তাকে এক শক্তিমাত্র মনে করেছে কেউ মনে করেছে প্রথম কার্যকারণ (First cause of causes)। কেউ তাঁর সাথে বংশধারাকে সংযোজিত করেছে কেউ কেউ আবার তাঁকে আকার-আকৃতি বিশিষ্ট মনে করেছে। কিন্তু ইসলামের তওহীদী ধারণা এ সব কলুষতা থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। ইসলামের খোদা পবিত্র ও মহান সত্তার অধিকারী। তাঁর সত্তা যাবতীয় মহৎ গুণে বিভূষিত। তিনি কারোর মুখাপেক্ষী নন, সবকিছু বরং তাঁরই মুখাপেক্ষী। তিনি সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী। তাঁর রহমত সর্বব্যাপক। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সর্বজয়ী। তাঁর হিকমত ও সুবিচার নীতিতে কোন ত্রুটি বা বিচ্যুতি নেই। তিনিই জীবনদাতা ও জীবন সামগ্রীর একমাত্র পরিবেশক। ক্ষতি ও কল্যাণের যাবতীয় শক্তি তাঁরই হাতে নিবদ্ধ। হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও পুরস্কার তাঁরই ইখতিয়ারভুক্ত। তিনিই চিরন্তন মা’বুদ, অবিনশ্বর ইলাহ। পূর্ণত্বের সব গুণ তারই সত্তায় নিহিত। তাঁর কোন গুণ-বৈশিষ্ট্যে নেই একবিন্দ দোষ-ত্রুটি। বস্তুত খোদা সম্পর্কে এ ধারণা অত্যন্ত ইতিবাচক। এরই পাশাপাশি রয়েছে নেতিবাচক ধারণাও। অর্থাৎ খোদার এ মহৎ গুণাবলী খোদা ছাড়া আর কারোর মধ্যে নেই। খোদা সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়, তা আর কারোর সম্পর্কেই বলা যেতে পারে না। বিশ্বলোকের অন্য কোন শক্তি বা সত্তা এই গুণাবলীর অধিকারী নয়। এ কারণে অপর কেউই, কোন কিছুই ‘ইলাহ’ হতে পারে না।
ইসলামের তওহীদী ধারণার পূর্ণতার একটি অপরিহার্য দিক হল নবুওয়্যাত বা রিসালাত বিশ্বাস। তওহীদী ধারণায় আল্লাহ-ই যেহেতু সর্বক্ষেত্রে চূড়ান্ত ফায়সালা গ্রহণকারী-একমাত্র বিধানদাতা, তাই মানুষের নিকট তাঁর বিধান পৌঁছানোর মাধ্যম হল এই রিসালাত বা নবুওয়াত। এ জন্যে মানব সমাজের মধ্য হতেই এক এক ব্যক্তিকে তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী বাছাই করে নেন এবং এ কাজ সম্পাদনের জন্যে মনোনীত করেন। মানুষের ইতিহাসে এ ধরণের বহু মনোনীত পুরুষের আবির্ভার ঘটেছে এ দুনিয়ায়। এদের মধ্যে সর্বশেষ ও পূর্ণ-পরিণত ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ সা.। তিনি কিয়ামত অবধি সমস্ত মানুষের জন্যে রাসূল।
বস্তুত নবুওয়াত ও রিসালাত মানুষের বিবেক, বুদ্ধি, চিন্তা ও কর্মের দিক দিয়ে একটি অপরিহার্য প্রয়োজন। মানুষের জীবনে যতটা প্রয়োজন খাদ্য ও পোশাকের, তার চাইতেও অধিক প্রয়োজন এই রিসালাতের। মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে যে আইন বিধানের প্রয়োজন, তা সবই এই রিসালাতের মাধ্যমে পূরণ হয়েছে। আর এসব আইন বিধানের ভিত্তিতে মানুষের জীবন যতটা উন্নত মানে চলতে পারে, ততটা উন্নত মান অপর কোন বিধানের সাহায্যেই অর্জিত হতে পারে না। এখন মানুষ যদি নবুওয়াত বা রিসালাতকে গ্রহণ না করে তাহলে নিজের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান হয় সে নিজেই রচনা করবে, নচেত অপর কোন মানুষকে তা রচনার অধিকার দিতে হবে কিংবা বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে বিভিন্ন পর্যায়ের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান রচনার দায়িত্ব অর্পন করতে হবে অথবা প্রতিটি জন-সমাজ নতুন করে আইন-বিধান রচনার পরিবর্তে প্রচলিত রসম-রেওয়াজের আশ্রয়ে জীবন পরিচালিত করবে। এছাড়া মানুষের সামনে অন্য কোন উপায় আছে কি?… কিন্তু বর্ণিত উপায়সমূহ গভীরভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টত দেখা যাবে, এর কোন একটি উপায়ও মানুষকে নিশ্চিত ও সন্দেহাতীত জ্ঞানের সন্ধান দিতে সমর্থ নয়। এ কারণে মানুষ তার সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞানবুদ্ধির সাহায্যে কোন সর্বজনীন, সর্বকালীন ও সর্ব মানুষের জন্যে কল্যাণকর বিধান রচনা করতে পারে না; বরং তার (মানুষের) মানসিক যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের পার্থক্যের কারণে মানব-সমাজের বিভিন্ন অংশ চরম দুর্গতি ভোগ করে আসছে যুগ যুগ ধরে। দুনিয়ার সাংস্কৃতিক বিপর্যয়ের মূলে প্রধানত এ কারণটিই নিহিত।
এদিক থেকে বিবেচনা করলে মানুষকে শেষ পর্যন্ত মহান সৃষ্টিকর্তার দেয়া বিধানের নিকটই আত্মসমর্পণ করতে হয়-এছাড়া তার আর কোনই উপায় নেই। ইসলামের দাবি হল, মানুষের মর্যাদা রক্ষা তথা সুষ্ঠু ও সুন্দর জীবন যাপনের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-বিধান দানের অধিকার কেবল আল্লাহরই রয়েছে। রিসালাত হচ্ছে এ বিধান দানের একমাত্র মাধ্যম। রাসূল তার বিশেষ ধরণের যেগ্যতা-প্রতিভা ও খোদায়ী নিয়ন্ত্রণ লাভের কারণে সাধারণ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি আল্লাহর বিধানকে যথাযথভাবে পৌঁছানো ও তার বাস্তবায়নে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করেন। তাই আল্লাহর বিধান সঠিকভাবে লাভ করতে মানুষের কোন অসুবিধে হয়নি। বস্তুত রাসূলের উপস্থাপিত বিধানে সর্বশ্রেণী মানুষের এবং জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় আইন-কানুন বর্তমান। মানব-জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগে সামঞ্জস্য রক্ষা করা কেবলমাত্র এই রাসূল-বিশ্বাসের সাহায্যেই সম্ভবপর।
রিসালাত বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তওহীদী আকীদার আর একটি অপরিহার্য দিক হল পরকাল বিশ্বাস। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির আধ্যাত্মিক কাঠামোর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল আল্লাহর নিকট জবাবদিহীর সন্দেহাতীত বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই মানুষের চিন্তা ও কর্মকে পবিত্র ও নির্দোষ করে তোলে। মানুষ এর তাগিদেই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্-ভীতি ও তাক্ওয়ার নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়। এক পরিপূর্ণ চিন্তা-ব্যবস্থা ও যুক্তিধারার ওপর ভিত্তিশীল হচ্ছে এই আকীদাটি। মানুষের নৈতিক সুস্থতার জন্যে এর মত প্রভাবশীল দৃঢ় ভিত্তি আর কিছুই হতে পারে না। এ আকীদার মূল কথা হল, মানুষ প্রতিটি বিষয়ের জন্যে নিজেকে দায়িত্বশীল মনে করবে। কোনরূপ বাহ্যিক চাপ, প্রলোভন ও লালসা ছাড়াই মনের ঐকান্তিক তাগিদে সে আল্লাহর বিধান পালন করে চলবে। এই হল পরকালে বিশ্বাসের লক্ষ্য।
মানবতার সম্মান
ইসলামী সংস্কৃতির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল মানবতার সম্মান। মানুষ মানুষ হিসেবেই সম্মানার্হ। মানবতার এই সম্মান নির্বিশেষ-পার্থক্যহীন। মানুষে মানুষে নেই কোনরূপ তারতম্য। উচ্চ-নীচ ও আশরাফ-আতরাফের বিভেদ মানবতার পক্ষে চরম অপমান স্বরূপ। সমাজের সব মানুষই সমান মর্যাদা ও অধিকার পাওয়ার যোগ্য। সুতরাং আইনের দৃষ্টিতেও কোনরূপ পার্থক্য ও বৈষম্য করা চলতে পারেনা। ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, উচ্চ পদাধিকারী ও নিম্নপদস্থ কর্মচারী, গ্রামবাসী ও শহরবাসী, নারী আর পুরুষ-ইত্যাদির মধ্যে কোনই পার্থক্য বা বৈষম্য স্বীকৃতব্য নয়। ইসলামী সংস্কৃতি এধরণের কৃত্রিম ভেদ-বৈষম্যকে নিঃশেষ ও নির্মূল করে দিয়ে সব মানুষকে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে। বংশ, বর্ণ, ভাষা, স্বদেশিকতা, আঞ্চলিকতা, শাসন-সংস্থা প্রভৃতি দিক দিয়ে মানুষের মাঝে কোনরূপ পার্থক্য সৃষ্টি করা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। ইসলামী সংস্কৃতিতে সব মানুষের সম্মান, মর্যাদা, অধিকার, ক্ষমতা সর্বতোভাবে সমান। এখানে পার্থক্য কেবলমাত্র একটি দিক দিয়েই করা হয়। তাহল মানুষের চিন্তা-বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনধারা। অন্য কথায়, কুফর ও ইসলাম এবং ইসলামী সমাজের তাক্ওয়ার বিভিন্ন মানগত অবস্থা হচ্ছে পার্থক্যের মাপকাঠি।
ইসলামী সংস্কৃতি উচ্চ-নীচের অন্য সব ব্যবধান নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মানবতার ইতিহাসে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত এ সাম্যের কোনই তুলনা নেই। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের এ সাম্য দুনিয়ার অপর কোন সংস্কৃতিই কায়েম করতে পারেনি।
বিশ্ব-ব্যাপকতা ও সর্বজনীনতা
ইসলামী সংস্কৃতি এক সর্বজনীন সংস্কৃতি। তা বিশেষ কোন গোত্র, বর্ণ, শ্রেণী, বংশ, কাল বা অঞ্চলের উত্তরাধিকার নয়। তার সীমা-পরিধি সমগ্র বিশ্বলোক এবং গোটা মানবংশে পরিব্যাপ্ত ও বিস্তীর্ণ। তাতে বিশেষ ভাষা বা বংশের দৃষ্টিতে কোন সংকীর্ণতার অবকাশ নেই। ইসলামী সংস্কৃতির এ হল তৃতীয় বৈশিষ্ট্য। আল্লাহর একত্ব ও হযরত মুহাম্মাদ সা. এর রিসালাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক ব্যক্তিই এ সংস্কৃতির অধিকারী-সে যে ভাষায়ই কথা বলুক, তার গায়ের বর্ণ যা-ই হোক, সে প্রাচ্য দেশীয় হোক, কি পাশ্চাত্য দেশীয়। তার আচার-আচরণ ও জীবনযাত্রা ইসলামী ভাবধারায় পরিপুষ্ট, ইসলামী রঙে রঙীন-এটুকুই যথেষ্ট। এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতি ব্যাপক ও সর্বাত্মক ভূমিকার অধিকারী।
বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব
ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি হল ‘দ্বীন’। রক্ত সম্পর্ক এর তুলনায় একেবারেই গৌণ। তাই এ দুটির কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রশ্ন উঠলে দ্বীনী সম্পর্কের দিকটিই প্রাধান্য পাওয়ার অধিকারী হবে। ইতিহাসে এ সংস্কৃতির প্রথ প্রকাশ ঘটেছে হিজরতের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে। এ ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠেছিল রক্ত-সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়-ভাষার, বর্ণের বা স্বাদেশিকতার ভিত্তিতেও নয়; বরং তা গঠিত হয়েছিল একমাত্র দ্বীনের ভিত্তিতে। এরা সবাই ছিলেন একই দ্বীনে বিশ্বাসী, একই জীবনাদর্শের অনুসারী, একই ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ ও একই লক্ষ্য-পথের যাত্রী। হাবশার (আবিসিনিয়া) বেলাল, রোমের সুহাইব, পারস্যের সালমান, মক্কার আবুবকর, উমর রা. ও মদীনার আনসারগণ এ আদর্শ-ভিত্তিক ও সংস্কৃতিবান সমাজে নিঃশেষে একাকার হয়ে গিয়েছিলেন। এভঅবে একটি মানস সমাজ তার সাংগঠনিক পর্যায়ে একই সংস্কৃতির অনুসারী একটি মহান মিল্লাতে পরিণত হয়েছিল। এ মিল্লাতটি ছিল যেন একটি পূর্ণাঙ্গ মানব-দেহ। এর যেকোন অঙ্গে ব্যথা অনুভূত হলে পূর্ণ দেহটিই সে ব্যথায় জর্জরিত হয়ে উঠত। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতির এটাই হয়ে থাকে পরিণতি।
বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ
ইসলামী সংস্কৃতির পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বশান্তির প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। সমাজে অকারণ রক্তপাত কিংবা বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া এবং প্রতিবেশী জাতি বা রাজ্যের সাথে নিত্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী। যা কিছু ভালো-কল্যাণময়, তার সম্প্রসারণ এবং যা কিছু মন্দ ও ক্ষতিকর, তার প্রতিরোধই হল এ সংস্কৃতির ধর্ম। অন্যায়কে প্রতিরোধ করার জন্যে শক্তি প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে উঠলে তাকে এড়িয়ে না যাওয়াও এর বৈশিষ্ট্য। বিশ্বশান্তি স্থাপনে ইসলামী সংস্কৃতির ভূমিকা চিরকালই সুস্পষ্ট ও বিজয়দৃপ্ত। বিশ্ব-সমাজকে যুদ্ধের দাবানল থেকে মুক্ত রাখতে হলে ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারাই হল একমাত্র উপায়।
বিশ্ব-মানবের ঐক্য
মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে হলে মানুষের পারস্পরিক ঐক্য অপরিহার্য। ঐক্য ছাড়া যেমন মানবতার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার ধারণা করা যায়না, তেমনি বিশ্বশান্তিরও বিঘ্নিত ও বিনষ্ট হওয়া অবধারিত। বিশ্ব-মানবের পরস্পরে পরিপূর্ণ ঐক্য সৃষ্টি করতে হলে চিন্তার ঐক্য বিধান সর্বপ্রথম কর্তব্য; তারপরই হল কর্মের ঐক্য ও সামঞ্জস্য। অন্যকথায়, মানব সমাজের সার্বিক ঐক্য তাদের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের উপর নির্ভরশীল। বস্তুত মানুষের মনন-চিন্তা ও মানসিকতার ঐক্য ও সামঞ্জস্যই হচ্ছে বিশ্ব-মানবের কাংক্ষিত ঐক্যের একমাত্র উপায়।
ইসলাম যে ‘কালেমায়ে শাহাদাত’ মানব-সাধারণের নিকট উপস্থাপন করেছে এবং তার যে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ পেশ করেছে, চিন্তার ভারসাম্য রক্ষার জন্যে তা-ই হল প্রধান হাতিয়ার। এর সাহায্যে চিন্তা-বিশ্বাস ও মননশীলতায় যে ঐক্য দানা বেঁধে ওঠে, তা-ই বাস্তব কর্মে নিয়ে আসে ঐক্যের ধারাবাহিকতা। বিরোধ ও বিভেদের সমস্ত প্রাচীর এর বন্যা-প্রবাহে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে বাধ্য। মানুষ এরই ভিত্তিতে সমান মর্যাদার অধিকারী হয়ে এক আল্লাহর বান্দাহ হয়ে উঠতে পারে এবং মানব-সমাজের ওপর থেকে এক আল্লাহ ছাড়া অপর শক্তিগুলোর প্রভাব-প্রতিপত্তি, কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বকে উৎখাত করে মানুষ সর্বপ্রকার লাঞ্ছনা ও অবমাননা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে। তাই তওহীদ হচ্ছে মানবতার মুক্তি সনদ। শিরক্ হচ্ছে এর বিপরীত অশান্তি ও বিপর্যয়ের সর্বনাশা বীজ; তা মানুষকে নানাভাবে বিভক্ত করে। এসব থেকে মানুষ যখন মানসিক দিক দিয়ে পবিত্রতা লাভ করে, তখনই আসে মন ও মননশীলতার ঐক্য এবং তখন বাহ্যিক ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে আন্তরিক ঐক্যের সৃষ্টি করা আর কঠিন হয়ে দাঁড়ায় না। তাই এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যে ইসলামের বিশেষ কর্মনীতি ও সুফলদায়ক কর্মপন্থা গৃহীত হয়েছে। বাহ্যিক ঐক্য স্থাপনের জন্যে যেখানে নামায ও হজ্জের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আন্তরিক ঐক্য বিধানের জন্যে সেখানে গৃহীত হয়েছে রোযা ও যাকাতের ব্যবস্থা। পাঁচ ওয়াক্ত নামায হোক কিংবা জুম’আ ও দুই ঈদের নামায, উভয় ক্ষেত্রেই সীমিত ধার্মিকতা ও জাতীয়তার ঊর্ধ্বে উঠে মানুষ আন্তর্জাতিকতোর উদার পরিবেশে স্থান গ্রহণ করে। আর বায়তুল্লাহ্র হজ্জ্ব বিশ্ব-মানবের এক পোশাকে, এক আল্লাহর দরবারে, একই ভাষায়, একই দিকে মুখ করে একই প্রকারের আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে, পারস্পরিক সহানুভূতির সাথে, একত্র সমাবেশের এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা করে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে জোয়ার-ভাঁটা তথা উপার্জনে কম-বেশী হওয়া এক স্বাভাবিক অবস্থারই লক্ষণ। অন্যথায় বৈচিত্র্যহীনতা ও একঘেয়েমীতে মানব সমাজে এক চরম অচলাবস্থা সৃষ্টির পূর্ণ আশংকা দেখা দিত। এমনকি, এর ফলে আবর্তন স্তিমিত হয়ে যেত। এ কারণে মানব জাতির বেঁচে থাকার জন্যে ব্যক্তির অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের অবাধ সুযোগ-সুবিধে থাকা একান্তই বাঞ্ছনীয়। একদিকে প্রয়োজন, অপর দিকে উপার্জন। এ দুয়ের পারস্পরিক সহযোগিতা এবং পরস্পরের পরিপূরক হওয়া অপরিহার্য। এ কারণেই ইসলামে যাকাত ও সাদকার সুষ্ঠু মানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজের প্রতিটি মানুষই এ কারণে পরস্পরের সাথে সম্পর্ক রেখে চলতে বাধ্য হয়। এর দরুন ব্যষ্টি ও সমষ্টির সংযোজনে এক বৃহত্তর সমাজ গড়ে উঠতে পারে। বস্তুত উম্মতে মুসলিমা এমনিভাবেই স্বীয় উন্নত মানের সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিশ্বজনীন ঐক্যের পতাকা ঊর্ধ্বে উড্ডীন করতে পারে।
কর্তব্য ও দায়িত্বানুভূতি
ইসলামী মিল্লাতের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন অবহিত হতে হয় নিজের দায়িত্ব ও কতর্ব্য সম্পর্কে, তেমনি সমষ্টির প্রতি স্বীয় দায়িত্ব ও কতর্ব্য সম্পকেও তাকে বিস্তারিতভাবে জানতে হবে। একজন অনুগত সন্তান, স্নেহময় পিতা, সহৃদয় ভাই-বোন এবং বিশ্বাসী স্বামী ও স্ত্রীরূপে প্রত্যেকেরই অধিকার এখানে সুনির্ধারিত। কর্তব্যের অনুভুতি তাকে সমগ্র জীবনভর সক্রিয় করে রাখে। অধিকার হরণ বা লঙ্ঘন তার কাছে চিরন্তন আযাবের কারণ রূপে বিবেচিত। এ জন্যে রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থায় পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে সে বদ্ধপরিকর। এতে করে অর্থনৈতিক শোষণ ও লুণ্ঠন আপনা-আপনি নিঃশেষ হয়ে যেতে বাধ্য। তার ফলে এ সমাজে অথর্নেতিক অসাম্যের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না-পারে না নৈতিক চরিত্র-বিধ্বংসী প্রবণতা জেগে উঠতে।
পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা
পরিবত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে চলাও ইসলামী সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ পবিত্রতা যেমন বাহ্যিক, তেমনি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক। এ জন্যে ইসলাম যেমন শিরক্কে সম্পূর্ণ বজর্ন করে চলার আদেশ কেরেছে, তেমনি হারাম ও অনৈতিক কর্ম-কাণ্ডকে সম্পূর্ণ বজর্ন করে চলার নিদের্শ দিয়েছে। ‘তাক্ওয়া’ বা আল্লাহভীতি আধ্যাত্মিক পরিচ্ছন্নতার জন্যে অতিশয় কার্যকরি হাতিয়ার। এর অনুশীলনের ফলে সমগ্র সমাজ-পরিবেশ এক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র ভাবধারায় মূর্ত হয়ে উঠে। এ জন্যে ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ও চরিত্র নিমর্ল ও পবিত্র হয়ে ওঠে।
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা
ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে সমাজের মূল ভিত্তি প্রস্তর। এছাড়া ব্যক্তির সুষ্ঠু উন্নয়ন ও বিকাশ কখনো সম্ভবপর নয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে যে জীবন-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে সামষ্টিক স্বাথের্র বেদীমূলে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানে ‘কমিউন’ প্রথা চালু করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও পারিবারিক জীবনের মর্যাদাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া হয়েছে। সে সমাজের জনগণের প্রেম-ভালোবাসা, মানসিক, শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষনের উপায় এবং জীবন-জীবিকার উৎস হচ্ছে সরকার বা রাষ্ট্র। নারী-পুরুষ, বালক-শিশু, যুবক-বৃদ্ধ নির্বিশেষ সকল মানুষই সরকারের মালিকানা। কাজেই সরকারী নির্দেশ মেনে চলায় কোনরূপ দ্বিধা-কুণ্ঠা প্রকাশ করার একবিন্দু অবকাশ নেই সে সমাজে। জমি-জায়গা, অর্থ-সম্পদ, বিত্ত-সম্পত্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই কোন ব্যক্তির মালিকানা থেকে কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় সোপর্দ করা হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য হয়েছে সরকারী অর্থ শোষণের এক প্রবল হাতিয়ার। নানা বাধা-প্রতিবন্ধকতার আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী হয়ে সেখানকার জনগণ যেন জেলখানার কয়েদি। ব্যক্তি-স্বাধীনতার কোন নামগন্ধ নেই সেখানে। তার জন্যে কোন সামান্য চেষ্টা করা হলেও তা হয় বিদ্রোহের নামান্তর। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে হাঙ্গেরী ও চেকোশ্লাভাকিয়ায় সোভিয়েত আক্রমণের দৃষ্টান্ত বিশ্ববাসীর চোখ খুলে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাকামী সোভিয়েত ট্যংক বহরের প্রতিরোধে এসে প্রাণ দিয়েছে। নব্য উপনিবেশবাদী সমাজতন্ত্রের সর্বগ্রাসী অভিযান তাদের স্বাধীনতা লাভের অধিকারকে নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে।
পাশ্চাত্যের তথাকথিত সভ্যতা-সংস্কৃতিও জনগণকে সত্যিকার কোন স্বাধীনতা দিতে সক্ষম হয়নি। তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলোর শাসনতন্ত্রে একথা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকে যে, সরকার যে কোন সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণা কিংবা নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জাতীয় আইনের সাহায্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা হরণ করতে পরে। নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্টকালের জন্যে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখার অধিকারও এ সরকারের জন্যে সুরক্ষিত। বিশেষত জরুরী অবস্থায় সমস্ত জনগণ সরকারেরই নিরংকুশ কর্তৃত্বাধীনে চলে যেতে বাধ্য হয়; তাতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। অন্যদিকে নারী-পুরুষের সমতার নামে নারীর মর্যাদা সেখানে চরমভাবে ভূ-লুণ্ঠিত। আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার নামান্তর বই কিছুই নয়। সেখানে কেউ কারোর জন্যে এক বিন্দু সহানুভুতি বোধ করেনা। পারস্পরিক প্রেম-ভালোবাসা ও সহানুভুতি কর্পূরের মতো উবে গেছে সে সমাজ থেকে। আত্মহত্যার ঘটনা সেখানে এক নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।
কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতি এ অমানবিক বন্যতার প্রশ্রয় দেয়নি। ব্যক্তি স্বতন্ত্র্য ও সমাজ-স্বার্থের মাঝে এখানে ভারসাম্যপূর্ণ এক সীমারেখা অংকিত। যার ফলে এ দুটি দিকই পরস্পরের জন্যে রহমত হয়ে ওঠে। মানুষের মৌল অধিকারে কোন বৈষম্য বা তারতম্য এখানে স্বীকৃত নয়। প্রত্যেকেরই স্থান ও মর্যাদা সুনির্দিষ্ট এখানে। এতে কম-বেশি করার এতটুকু অবকাশ নেই। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য হরণ করার অধিকার এখানে কাউকেই দেয়া হয়নি। ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপরও অকারণ সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপের অধিকার কারো নেই। প্রত্যেকের জন্যেই যথোচিত কাজের ও স্বীয় প্রতিভার বিকাশ সাধনের অবাধ সুযোগ এখানে স্পষ্টভাবে স্বীকৃত। জনগণের সম্পদ পরিমাণে কম-বেশি হতে পারে; কিন্তু তাদের মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন অপূর্ণ থাকার কোন কারণ ঘটতে পারে না এ সমাজে।
এ পর্যায়ের সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য হল সর্বক্ষেত্রে ও সর্বদিকে পরম ভারসাম্য রক্ষা। বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন, উচ্ছৃঙ্খলতা- এক কথায় সর্বপ্রকার জুলুম, অত্যাচার ও কদাচার ইসলামী সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সততা, ন্যায়পরায়নতা ও ইনসাফ এ সংস্কৃতির উজ্জ্বল দ্বীপশিখা।
ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা
বর্তমান কালে সংস্কৃতির কথা বললেই সাধারণভাবে প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, অংকন বা চিত্রশিল্প, কাব্য ও সাহিত্য চর্চা বা নৃত্যকলা, সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং অন্যান্য ললিতকলার কথা আপনা থেকেই মনের পটে ভেসে ওঠে। ‘সংস্কৃতির’ কথা বললে লোকেরা এসবই মনে করে বসে। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে সত্যই কি বুঝায় কিংবা অধুনা যেসব জিনিসকে সংস্কৃতি বলে মনে করা হচ্ছে, সেগুলো সত্যই সংস্কৃতি নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য কিনা এবং এগুলে ছাড়া সংস্কৃতির আর কোন অর্থ আছে কি না, তা সাধারণত কারোর মনেই জাগেনা। এর ফলে আমরা দেখতে পাই, এগুলোকেই সাংস্কৃতিক কাজ বলে ধরে নেয়া হচ্ছে এবং এ পর্যায়ের এক-একটা কাজকে ‘সাংস্কৃতিক’ অনুষ্ঠান বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে; বরং বর্তমানে তো কেবলমাত্র নৃত্য-সঙ্গীত ও নাট্যাভিনয়ই সংস্কৃতি চর্চা বা সাংস্কৃতিকি অনুষ্ঠান বলে পরিচিতি লাভ করছে। এসবের জন্যে এ শব্দটির ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কিনা, তা এ কালের লোকেরা একবার ভেবে দেখবারও অবকাশ পাচ্ছেনা। শুধু তা-ই নয়, সংস্কৃতির নামে প্রচলিত এসব জিনিসকে আবার ইসলামী বলে চালিয়ে দিতেও অনেকে দ্বিধাবোধ করছে না।
কিন্তু আমার মনে হয, সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন রয়েছে। সংস্কৃতির নামে সমাজে যা কিছু চলছে, অবলীলাক্রমে তাকেই সংস্কৃতি বা Culture [কথাটিকে উর্দূতে ‘তাহযীব’ এবং আরবীতে ‘সাক্বাফাত’ বলা হয়। আমাদের এতদাঞ্চলে ‘তামাদ্দুন’ শব্দটিকেও সংস্কৃতির সমার্থক মনে করা হয়। কিন্তু শব্দটির প্রকৃত অর্থ হচ্ছে সভ্যতা-সংস্কৃতি নয়।- সম্পাদক] বলে মেনে নেয়া অন্তত চিন্তাশীল ও বিদগ্ধজনের পক্ষে কিছুতেই শোভন হতে পারে না। তাই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আবশ্যক।
সংস্কৃতিঃ তাৎপর্য ও সংজ্ঞা
‘সংস্কৃতি’ বাংলা শব্দ। নতুন বাংলা অভিধানে-এর অর্থ লেখা হয়েছেঃ
‘সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ, কৃষ্টি, Culture’। অপর এক গ্রন্থকারের ভাষায় বলা যায়ঃ ‘সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি মার্জিত রুচি বা অভ্যাসজাত উৎকর্ষ।’ সংস্কৃতিকে ইংরেজীতে বলা হয় Culture। এ শব্দটি ল্যাটিন শব্দ CALTURE থেকে গৃহীত। এর অর্থ হল কৃষিকার্য বা চাষাবাদ। তার মানে-জমিতে উপযুক্তভাবে বীজ বপন ও পানি সিঞ্চন করা; বীজের রক্ষণাবেক্ষণ, লালন-পালন ও বিকাশ-বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা। বিশেষজ্ঞরা Culture শব্দের অনেকগুলো অর্থ উল্লেখ করেছেন বটে; কিন্তু এ শব্দকে সাধারণত উত্তম স্বভাব-চরিত্র এবং ভদ্রজনোচিত আচার-ব্যবহার ও আচরণ অর্থেও ব্যবহার করা হয়। ললিত-কলাকেও Culture বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। অশিক্ষিত ও অমার্জিত স্বভাবের লোকদেরকে Uncultured এবং সুশিক্ষাপ্রাপ্ত সুরুচি-সম্পন্ন ও ভদ্র আচরণবিশিষ্ট মানুষকে Cultured man বলা হয়। আবার কেউ কেউ মনে করেন, Culture বা সংস্কৃতি বলতে একদিকে মানুষের জাগতিক, বৈষয়িক ও তামাদ্দুনিক উন্নতি বুঝায় আর অপরদিকে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা যায়।
এ দেশের চিন্তাবিদ কলম-নবিশের মতেঃ সংস্কৃতি শব্দটি ‘সংস্কার’ থেকে গঠিত। অভিধানে তার অর্থঃ কোন জিনিসের দোষ-ত্রুটি বা ময়লা-আবর্জনা দূর করে তাকে ঠিক-ঠাক করে দেয়। অর্থাৎ সংশোধন ও পরিশুদ্ধিকরণ তথা মন-মগজ, ঝোঁক-প্রবণতা এবং চরিত্র ও কার্যকলাপকে উচ্চতর মানে উন্নীতকরণের কাজকে ‘সংস্কৃতি’ বলা হয়। খনি থেকে উত্তোলিত কাঁচা স্বর্ণকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নকরণ এবং পরে তা দিয়ে অলংকারাদি বানানোও সংস্কৃতির মূল কাজ। ইংরেজী শব্দ Culture-এর বাংলা অর্থ করা হয় সংষ্কৃতি। মূলত সংস্কৃতি সংস্কৃত ভাষার শব্দ। তার সাধারণ বোধগম্য অর্থ হল, উত্তম বা উন্নত মানের চরিত্র।
অধ্যাপক MURRY তার লিখিত ইংরেজী ডিক্শনারীতে বলেছেনঃ Civilization বা সভ্যতা বলতে একটি জাতির উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বুঝায়, যাতে রাষ্ট্র-সরকার, নাগরিক অধিকার, ধর্মমত, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা, আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক আইন বিধান এবং সুসংগঠিত শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমান রয়েছে। আর Culture বা সংস্কৃতি হচ্ছে সভ্যতা বা Civilization-এরই মানসিক ও রুচিগত ব্যাপার। তাতে থাকা-খাওয়ার নিয়ম-নীতি, সামাজিক-সামষ্টিক আচার-অনুষ্ঠান, স্বভাব-চরিত্র এবং আনন্দ স্ফূর্তি লাভের উপকরণ, আনন্দ-উৎসব, ললিতকলা, শিল্পচর্চা, সামষ্টিক আদত-অভ্যাস, পারস্পরিক আলাপ-ব্যবহার ও আচরণ বিধি শামিল রয়েছে। এসবের মাধ্যমে এক একটা জাতি অপরাপর জাতি থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট রূপে পরিচিতি লাভ করে থাকে।
প্রখ্যাত মার্কিন ঐতিহাসিক Will Duran এক নিবন্ধে Culture বা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবেঃ ‘সংস্কৃতি সভ্যতার অভ্যন্তর ও অন্তঃস্থল থেকে আপনা থেকেই উপচে ওঠে, যেমন ফুলবনে ফুল আপনা থেকেই ফুটে বের হয়ে আসে।’ তাঁর মতে সংস্কৃতিতে Regimentation বা কঠোর বিধিবদ্ধতা চলেনা। জাতীয় সভ্যতার প্রভাবে যেসব আদত- অভ্যাস ও স্বভাব-চরিত্র আপনা থেকে গোটা জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থাকে, তা-ই সংস্কৃতি। জাতীয় সংষ্কৃতি বলে কোন জিনিসকে জোর করে চালু করা যায় না। তা পয়দা করা হয় না, বরং আপনা থেকেই পয়দা হয়ে ওঠে। অবশ্য বিশেষ বিশেষ চিন্তা-বিশ্বাসের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন আসা সম্ভব। প্রখ্যাত দার্শনিক কবি T.S. Eliot Culture বা সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেনঃ ‘সংস্কৃতির দুটি বড় চিহ্ন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ- একটি ভাবগত ঐক্য আর দ্বিতীয়টি তার প্রকাশক্ষেত্রে সৌন্দর্যের কোন রূপ বা দিক’। তাঁর মতে সংস্কৃতি ও ধর্ম সমার্থবোধক না হলেও ধর্ম সংষ্কৃতিরই উৎস। সংস্কৃতি রাষ্ট্র-শাসন পদ্ধতি, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা এবং দর্শনমূলক আন্দোলন-অভিযানেও প্রভাবিত হতে পারে। Oswald Spengler –এর মতে, একটি সমাজের সংস্কৃতি প্রথমে উৎকর্ষ লাভ করে। তারই ব্যাপকতা ও উৎকর্ষের ফলে গড়ে ওঠে সভ্যতা, যা তার প্রাথমিক ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনা, তা ছড়িয়ে পড়ে ও সম্প্রসারিত হয়ে অপরাপর দেশগুলোর ওপরও প্রভাব বিস্তার করে বসে। কিন্তু ডুরান্টের মতে, প্রথমে রাজ্য ও রাষ্ট্র এবং পরে সভ্যতা গড়ে ওঠে আর এরই দৃঢ় ব্যবস্থাধীনে সংস্কৃতি আপনা থেকে ফুটে ওঠে। আর রুচিগত, মানসিক ও সৃজনশীল প্রকাশনার অবাধ বিকাশের মাধ্যমে সৌন্দর্যের একটা রূপ গড়ে ওঠে। তাতে গোটা জাতির ওপর প্রভাবশালী ধারণা-বিশ্বাস ও মূল্যমানের একটা প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্বিত হয়। এ পর্যায়ে আরবী শব্দ সাক্বাফাতের ব্যাখ্যাও আমাদের সামনে রাখতে হবে। তাতে সংস্কৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।
বাংলা ভাষায় সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, ইংরেজীতে তা-ই কালচার এবং আরবীতে তাই হল সাক্বাফাত। আরবী ‘তাহযীব’ শব্দটিও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়। ‘সাক্বাফাত’ এর শাব্দিক বা আভিধানিক অর্থ হলঃ চতুর, তীব্র, সচেতন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ও সতেজ-সক্রিয় মেধাশীল হওয়া। আরবী ‘সাক্বাফ’ অর্থ সোজা করা, সুসভ্য করা ও শিক্ষা দেয়। আর আস-সাক্বাফ বলতে বুঝায় তাকে যে বল্লম সোজাভাবে ধারণ করে। আরবী ‘হায্যাবা’ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ‘গাছের শাখা-প্রশাখা কেটে ঠিকঠাক করা, পবিত্রপরিচ্ছন্ন করে তোলা, পরিশুদ্ধ ও সংশোধন করা। আর ইংরেজী Culture মানে কৃষিকাজ করা, ভূমি কর্ষণ করা ও লালন-পালন করা (Oxford Dictionary)। এর আর একটি অর্থ লেখা হয়েছঃ Intellectual Development, Improvement by (mental of physical) Training: অর্থাৎ (মানসিক বা দৈহিক) ট্রেনিং-এর সাহায্যে মানসিক উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধন।
এ তিনটি শব্দেই ঠিকঠাক করা ও সংশোধন করার অর্থ নিহিত রয়েছে। এর পারিভাষিক সংজ্ঞাতেই এই অর্থটি পুরোপুরি রক্ষিত।
রাগেব আল বৈরুতী তাঁর ‘আস-সাক্বাফাহ্’ নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ
‘‘সাক্বাফাহ্’ মানে মানসিকতার সঠিক ও পূর্ণ সংশোধন এমনভাবে যে, সংস্কৃতিবান ব্যক্তির সত্তা পরিপূর্ণতা ও অধিক গুণ-বৈশিষ্ট্যের দর্পণ হবে। …..খারাবীর সংশোধন এবং বক্রতাকে সোজা করাই হল ‘সাক্বাফাত’ বা সংষ্কৃতি।’
ইংরেজী ‘কালচার শব্দের অর্থ ও তাৎপর্য পুরোপুরি সুনির্ধারিত হতে পারে নি। বিশেষজ্ঞরা নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। সে সংজ্ঞাগুলো পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল যেমন, তেমনি পরস্পর-বিরোধীও।
Philip Baghy তাঁর Culture and History নামক গ্রন্থ Concept of culture শীর্ষক এক নিবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি বলেনঃ সর্বপ্রথম ফরাসী লেখক ভল্টেয়ার ও ভ্যানভেনার্গাস (Voltair and Venvenargues) এ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। এদের মতে, মানসিক লালন ও পরিশুদ্ধকরণেরই নাম হচ্ছে কালচার। অনতিবিলম্বে উন্নত সমাজের চাল-চলন, রীতি-নীতি, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান শিক্ষা ইত্যাদিও এ শব্দের আওতায় গণ্য হতে লাগল। অক্সফোর্ড ডিক্শনারীর সংজ্ঞা মতে বলা যায়, ১৮০৫ সন পর্যন্ত ইংরেজী ভাষায় এ শব্দটির কোন ব্যবহার দেখা যায় না। সম্ভবত ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থ ‘কালচার’ পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছেন। …..সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত এ শব্দটি অস্পষ্টই রয়ে গেছে। এর অনেকগুলো সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। আলোচ্য গ্রন্থকার A.L Krochs and Kluck Halm-এর সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, এর একশত একষট্টিটি সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। [Culture, Critical Review of concept and defination]
এই গ্রন্থকারের মতে এ শব্দটির এমন সংজ্ঞা হওয়া উচিত, যা মানব জীবনের সর্বদিকে পরিব্যাপ্ত হবে। ধর্ম, রাজনীতি, রাষ্ট্রক্ষমতা, শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রকৌশলবিদ্যা, ভাষা, প্রথা-প্রচলন ইত্যাদিকে এর মধ্যে শামিল মনে করতে হবে; বরং মানবীয় বিষয়ের বিশেষজ্ঞরা তো মতাদর্শ, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, ক্ষমতা এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিসকেও এর মধ্যে শামিল মনে করেছেন। টি. এস. ইলিয়ট কালচার শব্দটির তাৎপর্য এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ
‘চালচলন ও আদব-কায়দার পরিশুদ্ধতাকেই ‘কালচার’ বা ‘সংস্কৃতি’ বলে।’
একটু পরে তিনি বিষয়টির আরো বিশ্লেষণ করেছেন এ ভাষায়ঃ
‘কালচার (সংস্কৃতি) বলতে আমি সর্বপ্রথম তা-ই বুঝি যা ভাষা-বিশেষজ্ঞরা বর্ণ করেন; অর্থাৎ এক বিশেষ স্থানে বসবাসকারী বিশেষ লোকদের জীবনধারা ও পদ্ধতি’। [T.S. Eliot, Notes Towards the Defination of Culture. P-13]
ম্যাথু আর্ণল্ড তাঁর Culture and Anarchy গ্রন্থে শব্দটির অর্থ লিখেছেন এভাবেঃ
‘কালচার হল মানুষকে পূর্ণ বানাবার নির্মল প্রচেষ্টা। অন্যকথায় কালচার হল পূর্ণত্ব অর্জন।’
কালচার শব্দের বিভিন্ন সংজ্ঞার সমালোচনা করে তিনি বলেন যে, এগুলোকে ভালো ভালো ও চমৎকার শব্দ তো বলা যায়; কিন্তু এগুলো কালচার বা সংস্কৃতির ব্যাপক অর্থ ও তাৎপর্যকে যথার্থভাবে ব্যক্ত করতে পারে না। তবে তিনি Montesqueu এবং B. Wilson-এর দেয়া সংজ্ঞাকে অতীব উত্তম বলে মনে করেন আর তা হলঃ এক বুদ্ধিমান ও সচেতন মানুষকে অধিকতর বুদ্ধিমান ও সচেতন বানানো এবং সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির উৎকর্ষ ও আল্লাহর সন্তোষ লাভে জন্যে অব্যাহত চেষ্টা করা। কিন্তু তার মতে কালচারের এ সংজ্ঞা সঠিক নয়। তিনি মনে করেন, কালচার ধর্ম হতেও ব্যাপক অর্থবোধক। তাঁর গ্রন্থের বিশেষ ভূমিকা লেখক মুহসিন মেহদী ‘কালচার’ শব্দের উল্লেখ করেছেন এভাবেঃ
‘এ কালচার মানুষের সাধারণ জীবনধারা থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কালচারের অর্থ হল মানবীয় আত্মার সাধারণ জমিনকে পরিচ্ছন্ন করা, তাকে কর্ষণের যোগ্য করে তোলা।’ [Mohsin Mehdi: Ibne Khaldun’s Philosophy of History. P-181]
মুহসিন মেহদী কালচার শব্দ সম্পর্কে এমনিতর আরো বলেছেনঃ
‘সংস্কৃতি না যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতাকে বলা যায, না মানুষের সত্তার অন্তর্নিহিত কামনা-বাসনাকে; বরং সত্যি কথা এই যে, তাহল সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও বৈষয়িক সৃজনশীলতার অভ্যস্ত ও প্রচলিত রূপ।’ [Mohsin Mehdi: Ibne Khaldun’s Philosophy of History. P-181]
চিন্তাবিদ ফায়জী কালচার শব্দের দুটো সংজ্ঞা দিয়েছেনঃ একটি সমাজকেন্দ্রিক, অপরটি মানবিক। একটি সংজ্ঞার দৃষ্টিতে কালচার ‘তামাদ্দুন’ শব্দ থেকেও ব্যাপকতর আর অপরটির দৃষ্টিতে কালচার হচ্ছে মানবীয় আত্মার পূর্ণতা বিধান।
তিনি লিখেছেনঃ
‘কালচার-এর দুটি অর্থঃ সমাজতাত্ত্বিক ও মানবিক।
১. কালচার হচ্ছে এমন একটা পূর্ণরূপ-যাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, নৈতিক আইন-বিধান, রসম-রেওযাজ এবং আরো অনেক যোগ্যতা ও অভ্যাস-যা মানুষ সমাজের একজন হিসেবে অর্জন করেছে-শামিল রয়েছে।
২. ‘মানবীয় কালচার’ হচ্ছে মানবাত্মার পরিপূর্ণ মুক্তির দিকে ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলন।’’
কালচার শব্দের এ নানা সংজ্ঞাকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি, ফিলিপ বেগবী (Philip Bagby) প্রদত্ত সংজ্ঞা অপেক্ষাকৃত উত্তম। তিনি ‘কালচার’- এর সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ
‘‘আসুন আমরা এ বিষয়ে একমত হই যে, ‘কালচার’ বলতে যেমন চিন্তা ও অনভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কর্মনীতি-পদ্ধতি ও চরিত্রের সবগুলো দিককেও পরিব্যাপ্ত করে।’’ [Philip Bagby: Culture and History, P-80]
গ্রন্থকার সমাজ জীবন, মনস্বত্ত্ব ও তামাদ্দুনকে সামনে রেখে ‘কালচার’ শব্দের খুবই ব্যাপক সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেছেনঃ
‘‘সমাজ সদস্যদের আভ্যন্তরীণ ও স্থায়ী কর্মনীতি ও কর্মপদ্ধতির নিয়মানুবর্তিতা ও নিরবচ্ছিন্নতাকে বলা হয় সংস্কৃতি। সুস্পষ্ট বংশানুক্রমের ভিত্তিতে যে ধারাবাহিকতা, তা-ও এর মধ্যে শামিল।’’ [Philip Bagby: Culture and History, P-80]
তিনি আরো বলেছেনঃ
‘‘কোন বিশেষ কাল বা দেশের সাধারণ জ্ঞান-উপযোগী মানকেই বলা হয় কালচার বা সংস্কৃতি।’’
কালচার শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করায় সবচাইতে বেশী অসুবিধে দেখা দেয় এই যে, তার পূর্ণ চিত্রটা উদ্ঘাটিত কার জন্যে মন ঐকান্তিক বাসনা বোধ করে বটে। কিন্তু তার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণের জন্যে বিশেষজ্ঞরা খুব বেশী ডিগবাজি খেয়েছেন। এ কারণে অনেক স্থানেই সংস্কৃতির বাহ্যিক আনুষ্ঠানিকতাকে নাম দেয়া হয়েছে ‘কালচার’ বা সংস্কৃতি। টি. এস. এলিয়ট যথার্থ বলেছেনঃ
‘‘লোকেরা শিল্পকলা, সামাজিক ব্যবস্থা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিকে কালচার মনে করে, অথচ এ জিনিসগুলো কালচার নয়; বরং তা এমন জিনিস যা থেকে কালচার সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায় মাত্র। [T.S. Eliot, Notes Towards the definition of culture, P-120]
সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন
সংস্কৃতির অর্থ ও তাৎপর্যে কিছু অস্পষ্টতা রয়ে গেছে এজন্যে যে, তাকে অপর কয়েকটি শব্দের সাথে মিলিয়ে একাকার করে দেয়া হয়েছে। যেমন তামাদ্দুন, Civilization বা সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা সংস্থা (Social Structure) ও ধর্মমত (Religion)। এ তিনটির প্রতিটিই যেহেতু মানুষের জীবন ও সত্তার সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত, এ জন্যে অনেক সময় সংস্কৃতির স্বরূপ নির্ধারণে সভ্যতা, সমাজ সংগঠন বা ধর্মের প্রভাব, ফলাফল ও কর্মনীতির প্রভাব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সবচাইতে বেশী গোলক-ধাঁধার সৃষ্টি করেছে ‘তামাদ্দুন’ শব্দ। কেননা সাধারণ তামাদ্দুন ও সংস্কৃতি- এ দুটি শব্দকে একই অর্থবোধক মনে করা হয়। আর একটি বলে অপরটিকে মনে করে নেয়া হয়- একটির প্রভাবকে অপরটির ফলাফল গণ্য করা হয়। এ জন্যে সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পৃথক করে প্রতিটির স্বতন্ত্র ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দান করার জন্যে প্রতিটির সীমা নির্ধারণ করা লোকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। টি. এস. এলিয়ট এ দুঃখই প্রকাশ করেছেন। তিনি তার গ্রন্থের সুচনায় স্বীয় অক্ষমতার কথা সুস্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন।
চিন্তাবিদ ফায়জী তামাদ্দুন-এর যে-সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতেও সংস্কৃতি বা কালচার- এর সংজ্ঞা স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেনঃ
‘‘তামাদ্দুন বলতে দুটির একটি বুঝাবেঃ একটি হল সুসভ্য হওয়ার পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি মানব সমাজের পূর্ণাঙ্গ ও উৎকর্ষপ্রাপ্ত রূপ।’’
আন্তর্জাতিক ইসলামিক কলোকিয়ম-এর নিবন্ধকারদের মধ্যে কেবলমাত্র এ. জেড. সিদ্দিকী কালচার-এর সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে সঠিক কথা বলেছেন। তিনি কালচার-এর কেবল সংজ্ঞাই দেন নি, সেই সঙ্গে তামাদ্দুন-এর সাথে তার তুলনাও করেছেন। এ তুলনা নির্ভুল এবং এতে করে উভয়েরই সত্যিকার রূপ নির্ধারিত হতে পারে। তিনি বলেছেনঃ
‘‘সাক্বাফাত’ বা সংস্কৃতি পরিভাষাটি দ্বারা চিন্তার বিকাশ ও উন্নয়ন বুঝায় আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা সামাজিক উন্নতির উচ্চতম পর্যায়কে প্রকাশ করে। কাজেই বলা যায়, সংস্কৃতি মানসিক অবস্থাকে প্রকাশ করে আর সভ্যতা বা তামাদ্দুন তারই সমান প্রকাশ ক্ষেত্রকে তুলে ধরে। প্রথমটির সম্পর্ক চিন্তাগত কর্মের সাথে আর দ্বিতীয়টির সম্পর্ক বৈষয়িক ও বস্তুকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে। প্রথমটি একটি আভ্যন্তরীণ ভাবধারাগত অবস্থা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাহ্যিক জগতে তার কার্যকারিতার নাম। [M.Z. Siddiqui, International Colloquium, P-26]
ফায়জী সংস্কৃতির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা সংক্ষিপ্ত হলেও নির্ভুল। তিনি বলেছেনঃ
‘‘সংস্কৃতি আভ্যন্তরীণ ভাবধারার নাম আর তামাদ্দুন বা সভ্যতা হল বাহ্য প্রকাশ’। [Faizee, Islamic Culture]
এ পর্যায়ে মাওলানা মওদূদী যা কিছু লিখেছেন তা সারকথা হলঃ
‘‘সংস্কৃতি কাকে বলে তা-ই সর্বপ্রথম বিচার্য। লোকেরা মনে করে, জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, নিয়ম-নীতি, শিল্প-কলা, ভাষ্কার্য ও আবিস্কার-উদ্ভাবনী, সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতার ধরণ-বৈশিষ্ট্য ও রাষ্ট্র-নীতিই হল সংস্কৃতি। কিন্তু আসলে এসব সংস্কৃতি নয়, এসব হচ্ছে সংস্কৃতির ফল ও প্রকাশ। এসব সংস্কৃতির মূল নয়, সংস্কৃতি-বৃক্ষের পত্র-পল্লব মাত্র। এ সব বাহ্যিক রূপ ও প্রদর্শনীমূলক পোশাক দেখে কোন সংস্কৃতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে বটে; কিন্তু আসল জিনিস হল এ সবের অন্তর্নিহিত মৌল ভাবধারা। তার ভিত্তি ও মৌলনীতির সন্ধান করাই আমাদের কর্তব্য। [ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা]
টি. এস. ইলিয়ট, এম. জেড. সিদ্দিকী এবং মাওলানা মওদূদী পূর্বোদ্ধৃত ব্যাখ্যা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে চিন্তা ও মতাদর্শের পরিশুদ্ধি, পরিপক্কতা ও পারস্পরিক সংযোজন, যার কারণে মানুষের বাস্তব জীবন সর্বোত্তম ভিত্তিতে গড়ে উঠতে এবং পরিচালিত হতে পারে।
সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য
সভ্যতা ও সংস্কৃতির মাঝে যে পার্থক্য, তা-ও এখানে সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়া দরকার।
গিস্বার্ট (Gisbert) সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে নিম্নলিখিত প্রভেদ নিরূপণ করেছেন, যথাঃ
ক. দক্ষতার ভিত্তিতে সভ্যতার পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে; কিন্তু সংস্কৃতির বিচার হয় মানুষের বৃদ্ধিবৃত্তিক ও মানসিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে। সভ্যতার পরিমাপ করতে গিয়ে আমরা বাইরের উন্নতি লক্ষ্য করি, যেমন-হাতেবোনা তাঁতের তুলনায় যান্ত্রিক তাঁতের ক্ষমতা অনেক বেশী। আর শিল্পকলার ক্ষেত্রে মতভেদের কারণে কোন ভাল চিত্র কারোর দৃষ্টিতে সুন্দর, কারোর চোখে তা অসুন্দর-নিন্দনীয়।
খ. সভ্যতার অবদানগুলোকে সহজেই বোঝা যায়- উপলব্ধি করা যায়। সংস্কৃতির অবদান সাধারণ মানুষ অতো সহজে উপলব্ধি করতে পারেনা। সাধারণ লোক সামান্য শিক্ষা পেলেই আধুনিক যন্ত্রপাতির কলাকৌশল ও ব্যবহার-পদ্ধতি বুঝে নিতে পারে; কিন্তু কোন লোককে কবিতা বা ছবি আঁকা ভালোভাবে শেখালেই যে ঐ বিষয়ে সে দক্ষতা লাভ করবে, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।
গ. সভ্যতার গতি যেমন দ্রুত, সংস্কৃতির গতি তেমন দ্রুত নয়। সংস্কৃতির গতি অনেক বাধাপ্রাপ্ত হয়; ফলে একটা থমথমে নিশ্চল ভাব দেখা যায়। কখনো-বা সংস্কৃতি হয় পশ্চাদগামী।
ঘ. সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণতি বা ফলাফল হল বড় কথা। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিণতির বদলে কাজটা হল বড়- সেটাই হল লক্ষ্য। তাছাড়া সভ্যতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা যত তীব্র, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা তত তীব্র নয়। মানুষ সৌন্দর্যকে নানাভাবে উপভোগ করতে করতে পারে- বুদ্ধির সাধনায় নানাভাবে আত্মনিমগ্ন হতে পারে; কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে দেখি, আধুনিকতা সভ্যতার অবদান প্রাচীন আবিষ্কারকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে।
বস্তুত ব্যক্তির সুস্থতা, সঠিক লালন ও বর্ধন লাভের জন্যে যেমন দেহ ও প্রাণের পারস্পরিক উন্নতিশীল হওয়া আবশ্যক, ঠিক তেমনি একটি জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার পুরোপুরি সংরক্ষণ একান্তই জরুরী সে জাতির সঠিক উন্নতির জন্যে। বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে জীবন বা প্রাণ আর সভ্যতা হচ্ছে তার জন্যে দেহতুল্য।
মানব জীবনের দুটি দিক। একটি বস্তুগত আর দ্বিতীয়টি আত্মিক বা প্রাণগত। এ দুটি দিকেরই নিজস্ব কিছু দাবি-দাওয়া রয়েছে-দেহেরও দাবি আছে, মনেরও দাবি আছে। মানুষ এ উভয় ধরণের দাবি-দাওয়া পূরনের কাজে সব সময়ই মশগুল হয়ে থাকে। কোথাও আর্থিক ও দৈহিক প্রয়োজন তাকে নিরন্তর টানছে; জীবিকার সন্ধানে তাকে নিরুদ্ধেশ ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। কোথাও রয়েছে আত্মার দাবি-আধ্যাত্মিকতার আকুল আবেদন। সে দাবির পরিতৃপ্তির জন্যে তার মন ও মগজকে সব সময় চিন্তা-ভারাক্রান্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। মানুষের বস্তুগত ও জৈবিক প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থাপনার কাজ করে আর ধর্ম, শিল্প, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন তার মনের ক্ষুধা মিটায়। বস্তুত যেসব উপায়-উপকরণ একটি জাতির ব্যক্তিদের সূক্ষ্ণ অনুভূতি ও আবেগময় ভাবধারা এবং মন ও আত্মার দাবি পূরণ করে, তা-ই হচ্ছে সংস্কৃতি। নৃত্য ও সঙ্গীত, কাব্য ও কবিতা, ছবি আঁকা, প্রতিকৃতি নির্মাণ, সাহিত্য চর্চা, ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস এবং দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা একটি জাতির সংস্কৃতির বাহ্যিক প্রকাশ-মাধ্যম। মানুষ তার অন্তরের ডাকে সাড়া দিতে গিয়েই এসব কাজ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এগুলো থেকে তৃপ্তি-আনন্দ-স্ফূর্তি ও প্রফুল্লতা লাভ করে। দার্শনিকের চিন্তা-গবেষণা, কবির রচিত কাব্য ও গান, সুরকারের সঙ্গীত- এসবই মানুষের অন্তর্নিহিত ভাবধারাই প্রকাশ করে। এসব থেকে মানুষের মন তৃপ্তি পায়, আত্মার সন্তোষ ঘটে আর এই মূল্যমান, অনুভূতি ও আবেগ-উচ্ছ্বাসই জাতীয় সংস্কৃতির রূপায়ণ করে।
এখানেই শেষ নয়। এই মূল্যমান, অনুভূতি ও হৃদয়াবেগ এমন, যা এক-একটি জাতিকে সাংস্কৃতিক প্রকাশ-মাধ্যম গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ছাঁটাই-বাছাই চালানের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। যা মূল্যমান ও মানদণ্ডের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়, তা-ই সে গ্রহণ করে আর যা তাতে উত্তীর্ণ হতে পারে না তা সর্বশক্তি দিয়ে প্রত্যাখ্যান করে-এড়িয়ে চলে। এ কারণেই দেখতে পাই, পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদী ও বুর্জোয় সংষ্কৃতির প্রতি ঘৃণা পোষণ করে- তাকে নির্মূল করতে চায়। ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকট এ কারণেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রশ্ন অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দেয়।
সংস্কৃতি ও ধর্ম
একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যাবে যে, ধর্মকে যতই অস্বীকার করা হোকনা কেন, ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারা মানুষের রক্ত-মাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে-গভীরভাবে মিলে-মিশে একাকার হয়ে আছে, থাকবেও চিরকাল। এ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, জ্ঞান-গবেষণা এবং চিন্তা ও কল্পনার চরমোৎকর্ষ সত্ত্বেও তাকে এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়, যখন ধর্মের প্রভাব অকপটে স্বীকার না করে কোনই উপায় থাকে না। এমনকি, কট্টর নাস্তিকও এমন সব অবস্থায় ধর্ম ও ধর্মীয় ভাবধারাকেই একমাত্র আশ্রয় রূপে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, যা কয়েক বছর পূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। খবরটি ছিল এইরূপঃ একটি রুশ সামুদ্রিক জাহাজ আমেরিকার দূর-প্রাচ্যের সমুদ্র-বক্ষে ঝড়ের দাপটে টালমাটাল। এক্ষুণি বুঝি সব শেষ হয়ে যাবে। কোথাও আশার আলো চোখে পড়ছেনা। এই দূরপ্রাচ্যের সমুদ্র উপকূলের কোথাও যে কোন উপসাগরের অস্তিত্ব আছে, তারও কোন প্রমাণ ছিলনা। সহসা মাতাল ঝড়ে নাস্তানাবুদ জাহাজখানি বাত্যাতাড়িত হয়ে এক শান্ত পোতাশ্রয়ে ঢুকে পড়ল। সমুদ্র-বক্ষের দূরন্ত বাতার ও উন্মত্ত গর্জন যেন কোন জাদুমন্ত্রবলে এখানে শান্ত হয়ে পড়ে আছে। ধড়ে ফিরে-পাওয়া-প্রাণ নাবিকরা সোল্লাসে চীৎকার করে উঠলঃ ‘না-খোদা’ (রুম ভাষায় এ শব্দটির মানে দাঁড়ায় খোদা-প্রেরিত)।
এ ঘটনাটি যেন কুরআনেরই প্রতিধ্বনি-
وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ
‘‘উত্তাল তরঙ্গমালা যখন চারদিক থেকে তাদের পরিবেষ্টিত করে ফেলে সমাচ্ছন্ন মেঘের মত তখন তারা অতীব আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্কে ডাকে, তাঁরেই জন্যে আনুগত্য একান্ত করে দেয়। তার পরে যখন তারা মুক্তি পেয়ে সমুদ্র কিনারে পৌঁছায়, তখন তারা ভিন্ন পথে চলতে শুরু করে।’’ (সূরা লুকমানঃ ৩২)
মানুষ সমুদ্র সফরের জন্যে বড় বড় জাহাজ নির্মাণ করে মহাসাগরে অথৈ পানিতে ভাসিয়ে দেয়। তাকে চালাবার ও থামিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ শক্তিমান। কিন্তু প্রচণ্ড ঝড়-তুফানের মুখে মানুষ একেবারে অক্ষম ও অসহায়। তাকে সকল শক্তি-ক্ষমতার অপারগতা ও সীমাবদ্ধতা অনিবার্যভাবে স্বীকার করে নিতে হয়। যুদ্ধ-সংগ্রামে মানুষ পূর্ণ সজ্জিত ও সশস্ত্র হয়ে ময়দানে উপস্থিত হয়। সেখানে সে তার অতুলনীয় সাহস ও বিক্রমের ওপর নির্ভর করে শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার সঙ্গী-সাথী সৈনিকদের সংখ্যাও প্রতিপক্ষের তুলনায় হয় অনেক বেশী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে হয়। …. কিন্তু কেন? এর জবাব তালাশ করেও সে ব্যর্থ হয়। কোন সত্যিকার জবাবই সে খুঁজে পায়না। মানুষ ক্ষেতে-খামারে ও ফলের বাগানে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে রক্তকে পানি করে দেয়। সমস্ত ক্ষেত-খামার ও বাগ-বাগিচা সবুজ-শ্যামলে ও রস-টলমেল ফলের গুচ্ছে একাকার হয়ে যায়। তা দেখে তার চোখ জুড়ায়, ধড়ে পানি আসে, সোনালী ভবিষ্যতের উজ্জ্বল আশায় বুক ভরে উঠে। কিন্তু হঠাৎ এমন ঘটনা ঘটে যায়, যার ফলে সমস্ত ক্ষেত-খামার আর বাগ-বাগিচা হয় জ্বলে-পুড়ে শূণ্য মাঠে পরিণত হয় কিংবা বন্যার পানিতে সব ডুবে পচে নষ্ট হয়ে যায়; ফলে তার সব আশা মাটি হয়ে যায়। কিন্ত কেন ঘটল এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনা, এমন অভাবিতপূর্ণ দূরবস্থা? মানুষ নিজ থেকে এর কোন জবাবই পেতে পারেনা। বাহ্যিক কার্যকারণ যা-ই থাকনা কেন এ দূরবস্থার মূলে, অন্তর্নিহিত আসল কারণ-মনের সেই আসল প্রশ্নের জবাব-মানুষ ধর্মের কাছ থেকেই জানতে পারে। তাই ধর্ম মানুষের প্রকৃত আশ্রয়; জীবনের তিক্ত বাস্তবতা এবং তার রঙীন স্বপ্নে মাঝে সৃষ্ট দ্বন্দ্বের কারণে মানুষ যখন দিশেহারা হয়ে পড়ে; তখন ধর্ম এসে তাকে দেয় সান্ত্বনা, অসহায়ের সহায় হয়ে দাঁড়ায় এই ধর্মবিশ্বাস। বস্তুত জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের সব আবেগ-অনুভূতি, ব্যাথা-বেদনা ও দাবি-দাওয়ার সত্যিকার জবাব হচ্ছে এই ধর্ম। জীবনের গতিধারাকে ধর্ম ও নৈতিকতার নিয়ম-বিধি অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে মানুষ বাধ্য হয়। মানুষের সমস্ত চাল-চলনকে নিয়ন্ত্রিত ও সুষ্ঠু পথে পরিচালিত করার ব্যাপারে ধর্ম একটি সক্রিয় উদ্বোধক শক্তি হিসেবে কাজ করে। এ উদ্বোধক শক্তিই মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত করে তোলে আর এভাবেই সংস্কৃতির প্রশ্নে ধর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য হয়ে উঠে। সমাজবদ্ধ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক জীবনকে সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও সুনিব্যস্ত করে, তার মধ্যে জাগিয়ে দেয় এক গভীর ও সূক্ষ্ণ আবেগ। এ হৃদয়াবেগই হল সংস্কৃতির উৎসমূল আর এ কারণেই মানব জীবনে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মের আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে; বরং ধর্মের প্রেরণায় যে সংস্কৃতি পরিপুষ্ঠ, তা যেমন হয় সুদৃঢ়ভিত্তিক, তেমনি হয় স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন ও মলিনতাহীন-জঘন্যতা, অশ্লীলতা ও বীভৎসতামুক্ত। তার শিকড় হয় মানুষের মন-মগজ, স্বভাব-চরিত্র ও আচরণের গভীরে বিস্তুত ও প্রসারিত।
ম্যাথু আর্ণল্ডের মতে, সংস্কৃতি ধর্ম হতেও ব্যাপকতর অর্থবোধক; বরং তাঁর মতে, ধর্ম সংস্কৃতিরও একটা অংশ। অধিকাংশ মনীষীর মতে, সংস্কৃতি ও ধর্ম পর্যায়ে এ-ই হল একমাত্র কথা। ফায়জী ‘ইসলামিক কালচার’ গ্রন্থে এ মতটি প্রকাশ করেছেন এ ভাষায়ঃ
‘ধর্ম, ভাষা, বংশ দেশ এসবের ভিত্তিতে সংস্কৃতির রকমারি আঙ্গিকতা গড়ে ওঠে।’
আর এ কথাটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে, যদি সংস্কৃতির সংজ্ঞার সাথে সাথে ধর্মের সংজ্হাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে এবং এ দুয়ের প্রভাব-সীমা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু তবু সংস্কৃতি ও ধর্মের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটা অসুবিধে থেকে যাবে। কেননা সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেয়া একটা কঠিন ও জটিল ব্যাপার, এ থেকে মুক্তি পাওয়া খুব সহজসাধ্য নয়। ইন্সাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ান এ্যান্ড এথিক্স’- এর এক প্রবন্ধকার ধর্মের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের বিবিধ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন। এখানে আমরা কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করবো। কিন্তু তার পূর্বে উক্ত প্রবন্ধকারের একটা কথা পেশ করা আবশ্যক। সি. সি. জে. ওয়েব (C.C.J. Webb) ধর্মের সংজ্ঞাদান প্রসঙ্গে বলেছেনঃ
‘‘ধর্মের কোন সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে, ব্যক্তিগতভাবে আমি তা মনে করিনে। তা সত্ত্বেও ধর্মের অনেক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে।
১. Religion is a belief in super-natural being (E.B.Tylor)
‘ধর্ম হল অতি-প্রাকৃতিক সত্তাকে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করা’ (ই.বি. টেলর)
২. A Religion is unified system of belief and practices relatives to sacred things that is to say, things set apart, and forbidden-believes and practices while unite into one single moral community called a church. (Durkhem)
‘ধর্ম আকীদা ও আমলের এমন এক সমন্বিত ব্যবস্থা, যার সম্পর্ক হচ্ছে পবিত্র জিনিসগুলোর সঙ্গে-সেসব জিনিস, যেসবকে বিশিষ্ট গণ্য করা হয়েছে আর যা নিষিদ্ধ। আকীদা ও আমল, যা নৈতিক দিক দিয়ে একটি সুসংগঠিত কেন্দ্রিকতার সৃষ্টি করতে পারে-যাকে ‘উপাসনালয়’ বলা হয়।’ (ডুরখেম)
৩. Religion is man’s faith in power beyond himself whereby he seeks to satisfy his emotional needs and gains stability of life and which he expresses in acts of worship and service. [Encyclopedia of Religion and Ethics VXP 622, Article-Religion]
‘ধর্ম অর্থ ব্যক্তির অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, এমন শক্তি যার কাছ থেকে সে তার আবেগ-কেন্দ্রিক মুখাপেক্ষিতা ও ফায়দা লাভের প্রয়োজন পূরণ করতে চায় আর জীবনের স্থায়িত্ব, যাকে সে পূজা-উপাসনা ও সেবামূলক কাজ রূপে প্রকাশ করে।’
W.D. Gundry তার Religion নামক গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ধর্মকে সুনির্দিষ্ট করতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেনঃ
‘ধর্ম যেহেতু মানবজীবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে, এ কারনে প্রতিটি মানুষ স্বীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ধর্মের সংজ্ঞা দিয়েছে। যেমনঃ ধর্ম হল আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস, ভালোভাবে জীবন যাপন করাই ধর্ম, আভ্যন্তরীণ গভীর অভিজ্ঞতারই একটা বিভাগ হল ধর্ম ইত্যাদি।’
এ অধ্যায়ে ধর্ম সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ
‘নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হবে, ধর্ম হচ্ছেঃ
১. বিশ্বলোক সম্পর্কে একটা চিন্তা-পদ্ধতি, মানুষও তার মধ্যে গণ্য
২. ধর্ম হচ্ছে একটা কর্ম-পদ্ধতি
৩. ধর্ম হচ্ছে অনুভূতির একটা পন্থা
‘আমরা বলতে পারি, ধর্মে একটা চিন্তা, নৈতিকতা ও অভিজ্ঞতার দিক রয়েছে; বরং বিষয়গতভাবে বলতে গেলে প্রতিটি ধর্মেরই একটা আকীদা, একটা নেতিক বিধান ও একটা নিয়ম-শৃংখলা রয়েছে।’ (উক্ত বইয়ের ৬ পৃ)
ধর্মীয় ভাবধারার বিশ্লেষণ করে এ গ্রন্থকার লিখেছেনঃ
‘ধর্মে সাধারণত এ তিনটি বিষয় আলোচিত হয়ঃ
১. দুনিয়ার অস্তিত্ব কেমন করে হল, কোথায় এর পরিণতি? এ দুনিয়ায় মানুসের স্থান কোথায়, তার মর্যাদা কি? এবং মৃত্যুর পর কি হবে?
২. কথাবার্তা ও কর্মনীতি সম্পর্কে সেসব জরুরী আইন-বিধান, যা না হলে কোন সমাজই মজবুত ও সুদৃঢ় হতে পারে না।
৩. আরাধনা-উপাসনা, যা ছাড়া আল্লাহ ও বান্দাহ্র মাঝে কোন সম্পর্ক স্থাপিত হতে ও রক্ষা পেতে পারেনা।’
গ্রন্থকারের মতে, অনেক সময় এ তিনটির সমন্বিত নামই ধর্ম আাবার অনেক সময় এর একটিমাত্র দিককেই ধর্ম বলা যায়। এতে একথা সুস্পষ্ট যে, গ্রন্থকারের মতে ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক বিষয়, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে এটা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেনঃ
‘ধর্ম মানব জীবনের একটা বিভাগমাত্র নয়; বরং তা সমগ্র জীবনকে পরিব্যাপ্ত করে।’ [W.D. Gundry- Religion, P-7]
ধর্মের এ বিভিন্ন সংজ্ঞার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এর সংজ্ঞাদান পর্যায়ে কোন স্থায়ী ও চূড়ান্ত কথা বলা যেতে পারেনা। কেউ কেউ একে জীবনের সমগ্র দিকব্যাপী বিস্তৃত মনে করে, আবার কেউ মনে করে জীবনের একটা দিক মাত্র।
ক. ধর্ম জীবনের একটা দিকমাত্র হলে তা সংস্কৃতির সমার্থবোধক হয়ে যায় আর তার একটা অংশও।
খ. ধর্ম যদি মানুষের সমগ্র জীবনকে শামিল করে, তাহলে সংষ্কৃতি ধর্মের একটা অংশ হবে। কেননা ধর্ম মানুষের চিন্তা ও কর্ম উভয় দিকব্যাপী বিস্তৃত হয়ে থাকে আর সংস্কৃতির আওতা হচ্ছে শুধু চিন্তাগত বিকাশ ও উৎকর্ষ। ধর্মের এ ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা অপর কোন ধর্ম সম্পর্কে সত্য হোক আর না-ই হোক, ইসলাম সম্পর্কে তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এজন্যে কুরআন মজীদে ইসলামকে ‘দ্বীন’ বলা হয়েছে আর ‘দ্বীন’ হচ্ছে সমগ্র জীবনের জন্যে পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ বিধান। মানব জীবনের সবকিছুই তার মধ্যে শামিল রয়েছে; জীবনের কোন একটি দিকও- কোন একটি ব্যাপারও-তার বাইরে নয়। আল্লাহ্ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ
‘আল্লাহর নিকট সত্য ও গ্রহণযোগ্য জীবন ব্যবস্থা হচ্ছে একমাত্র ইসলাম।’
دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
‘‘তা এক মজবুত ও সুদৃঢ় জীবন ব্যবস্থা-ইব্রাহীমের অনুসৃত জীবন আদর্শ। তাতে একবিন্দু বক্রতা নেই আর ইব্রাহীম মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।’’ (সূরা আন’আমঃ ১৬১)
বস্তুত ইসলাম এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানব জীবনের এ বিশাল ও বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে পথ-প্রদর্শনের জন্যে চিন্তার দিক হল সংস্কৃতি। ইসলাম সভ্যতা ও সংস্কৃতি-তাহযীব ও তামাদ্দুন-উভয় দিকেরই সমন্বয়। এ কারণেই ইসলামের মনীষীগণ ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী সভ্যতা- এ দুটি পরিভাষাই ব্যবহার করেছেন; কেননা এ দুটি দিকই ইসলামের অন্তর্ভুক্ত।
ধর্ম ও শিল্পকলা
সংস্কৃতি পর্যায়ের আলোচনায় শিল্পকলার প্রশ্নটিও সামনে ভেসে ওঠে। মানুষ দুনিয়ার জীবনে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য হয়। প্রতিমা, প্রতিকৃতি, কারুকার্যখচিত চিত্রকলা, আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠানাদি, জন্ম-মৃত্যু, কুরবানী ইত্যাদি সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি মানুষকে অতি-প্রাকৃতিক শক্তির অতি নিকটে পৌঁছে দেয়; তার হৃদয়াবেগকে সঞ্জীবিত ও প্রাণচঞ্চল করে তোলে। মৃত্যুর শেষ ক্রিয়াদিতে মাতম করা, গীত গাওয়া, মর্সীয়া, কবিতা ও শোক-গাঁথা পাঠ করা প্রভৃতির মাধ্যমে মৃতকে পরকাল যাত্রায় প্রস্তুত করে দেয়া হয়। প্রাচীন মিশরে লাশগুলোকে মমি বানিয়ে রাখা এবং লাশের চারপাশে নানা চিত্র অংকন করা হতো আর এভাবে সম্পন্ন করা হতো এক জগত থেকে অন্য জগতের মহাযাত্রা। অনুরূপভাবে বড় বড় সমাবেশে নৃত্য ও সঙ্গীতের সাহায্যে ধর্ম প্রচার করা হতো। বর্তমানে খৃস্টান গীর্জায় সঙ্গীত গেয়ে এবং হিন্দু ও শিখ ধর্মে বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে পূজা অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। এভাবে নানারূপ শৈল্পিক প্রকাশনার মাধ্যমে বহু মানুষের সাথে যোগাযোগ গড়ে তোলা; মানুষ একাত্ম হয়ে ওঠে এসবের প্রভাবে। কাজেই সংস্কৃতির সাথে শিল্পের যে নিবিড় সংযোগ রয়েছে, তা মানতেই হবে। তবু তাতেও ধর্মের দৃষ্টিতে গ্রহণীয় ও বর্জনীয়ের ছাঁটাই-বাছাই চলা একান্তই বাঞ্ছনীয়।
জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলা
জ্ঞান ও বিজ্ঞান চর্চায় সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শনের গুরুত্বও অনস্বীকার্য। শিল্পদৃষ্টি মানুষের মাঝে পরিবেশ পর্যবেক্ষণ এবং পরিবেশ অধ্যয়নের উদ্বোধন জাগায়। বৈজ্ঞানিক চেতনার রূপায়নে শিল্পের সাহায্য প্রত্যক্ষ। এমনিভাবে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ পরোক্ষভাবে শিল্পের উন্নতির পথও সুগম হয়। যে কোন জিনিস সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে সাংস্কৃতিক বন্ধনের কথা অবশ্যই সামনে রাখতে হবে।
সংস্কৃতির মূল্যায়ন
মানুষের পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত আছে মানব জীবনের পরম কল্যাণ। মানুষ তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে যখন কামনা-বাসনা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ইত্যাদি নিম্নতর বৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রিত করে, তখনই তার আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি মানব জীবনের পরম কল্যাণ লাভের পক্ষে সহায়ক। যে ব্যক্তি সংস্কৃতিবান সে তার প্রকৃতি বা স্বভাবকে সম্পূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্যে যত্নবান হয়। জ্ঞানের অধিকারী হওয়া বা সুন্দর গুণের অধিকারী হওয়াই সংস্কৃতি নয়; সত্য, মহান ও সুন্দরের প্রতি যে ব্যক্তি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ অর্জন করেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিবান ব্যক্তি। প্রকৃতি ও মানুষের জীবনে যা কিছু সুন্দর, তার প্রকৃত তাৎপর্য বা মূল্য উপলব্ধি করতে তিনিই সক্ষম। কাজেই পার্থিব জগতের মাপকাঠিতে তিনি যদি দীন ও নিঃস্বও হন, তবু প্রকৃতপক্ষে তিনি এক মহান সম্পদের, এক অতুল বৈভবের অধিকারী।
বস্তুত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবশ্য পালনীয় মূল্যবোধের সৃষ্টি ও মূল্যবোধ ধারণের প্রচেষ্টা থেকেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলোর উৎপত্তি উৎপত্তি ঘটে থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি, নৈতিকতা ও সৌন্দর্য সম্পকীয় মূল্যগুলোর সমন্বয় থেকেই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলোর উদ্ভব হয়। অবশ্য সমাজ-সমাজ-আদর্শ ভেদে এই মূল্যেরও যে পার্থক্য ঘটে, সংস্কৃতির মূল্যায়নে একথা স্পষ্টভাবেই মনে রাখতে হবে।
সংস্কৃতির সামজিক মূল্যায়নে মানুষ ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্ক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেকে মানুষের তুলনায় সমাজকেই বড় করে দেখেন। কিন্তু এ সত্য কোনক্রমেই ভুলে যাওয়া চলেনা যে, মানুষ নিয়েই সমাজ, মানুষকে বাদ দিয়ে সমাজের কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। মানুষের প্রকৃতিকে উন্নত করাই সমাজের লক্ষ্য। ম্যাকেঞ্জী (Mackenzie) Culture বলতে এই ব্যষ্টিগত ব্যক্তিত্বে (Individual Personality) অনুশীলনকেই বুঝেছেন। শিক্ষার ব্যাপকতর এবং সংকীর্ণতর দু’ধরণের তাৎপর্য আছে। ব্যাপকতর অর্থে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা-ই হল সংস্কৃতি। ম্যাকেঞ্জী বলেনঃ সংকীর্ণ অর্থে এ হল জন-সমাজের জীবনে দীক্ষা লাভ করা আর ব্যাপকতর অর্থে এ হল মানুষের আধ্যাত্মিক প্রকৃতিকে উন্নত করা, যার জন্য সমাজ জীবন হল একটি উপায় মাত্র। [Outlines of Social Philosophy: P-228]
বস্তুত সংস্কৃতি এমন একটা কর্মোপযোগী সত্য যা মানুষের প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট সাহায্য করে। সংষ্কৃতি মানুষকে এক আপেক্ষিক দৈহিক প্রশস্ততা দান করে। তার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অনুভূতি জাগে। ব্যক্তিত্বে একটা সাম্প্রসারণতা-যাতে রয়েছে চাঞ্চল্য ও গতিশীলতা-মানুষকে এমন অবস্থায় সাহায্য করে, যখন নিছক একটা রক্ত-মাংসের দেহ কোন কাজেই আসেনা।
সংস্কৃতি সমাজবদ্ধ মানুষের ফসল। মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা ও কর্মশক্তিকে তা ব্যাপক, গভীর ও প্রশস্ত করে দেয়। তা চিন্তার ক্ষেত্রে এনে দেয় গাম্ভীর্য, শালীনতা ও সুসংবদ্ধতা; দৃষ্টিকে বানিয়ে দেয় উদার, বিশাল ও সুদূরপ্রসারী। অন্যান্য জীবজন্তু এ গুণ-বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত। মানুষের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-ক্ষমতা-প্রতিভার সামাজিক সামষ্টিক রূপ এবং পারস্পরিক চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তিই হয় এসব অবস্থার উৎসমূল।
সংস্কৃতি ব্যক্তিদের সমন্বয়ে সুসংগঠিত সমাজ গড়ে তোলে আর সে সমাজগুলোকে এক অন্তহীন জীবন-ধারাবাহিকতা প্রদান করে। সংগঠন ও সুসংবদ্ধ সমাজ-কর্ম হচ্ছে ক্রমিক ও ধারাবাহিক ঐতিহ্যের ফসল আর তা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পরিবেশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে। সংস্কৃতি মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতেও বহু তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত করে। তা মানুষের প্রতি কেবল দয়াই করেনা, সেই সঙ্গে তার ওপর অনেক বড় বড় দায়িত্বও চাপিয়ে দেয়। এসব দায়িত্ব পালনের জন্যে ব্যক্তিকে তার নিজের অনেক স্বাধীনতাও কুরবানী দিতে হয়; সে আত্মস্বার্থ বিসর্জন দেয় নিজের ভিতর থেকে পাওয়া প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আর তারই ফলে সম্পাদিত হতে পারে সামগ্রিক কল্যাণ।
মানুষকে নিয়ম-শৃংখলা, আইন-কানুন ও ঐতিহ্যের প্রতি অবশ্যই সম্মান দেখাতে হয়; নিজের স্বভাব-চরিত্র ও কাথাবার্তার ধরণ-ধারণ এক বিশেষ ছাঁচে ঢেলে গড়ে নিতে হয়। তাকে এমন অনেক কাজই আঞ্জাম দিতে হয় যা থেকে সে নিজে নয়- পুরোপুরি অন্যরাই ফায়দা লাভ করে আর তাকে তার নিজের প্রয়োজনের জন্যে হতে হয় অন্যের দ্বারস্থ।
মানুষের দূরদৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ শক্তি তার মনের মাঝে অনেক প্রকার কামনা-বাসনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়। ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা এবং সাহিত্য ও শিল্পকলা তাকে করে প্রশমিত- পরিতৃপ্ত।
সংস্কৃতি প্রকৃতপক্ষে মানব আত্মারই পরিতৃপ্তির উপকরণ আর তারই দরুন মানুষ পশুর স্তর থেকে অনেক ঊর্ধে ওঠে এক উন্নত মানের বিশিষ্ট সৃষ্টির মর্যাদা লাভ করে।
মানবীয় ব্যক্তিত্বের অনেকগুলো দিক। একদিকে সে এক ব্যক্তি, একটা সমাজের অঙ্গ বা অংশ আর সমাজ গড়ে ওঠে মানুষের পারস্পরিক মেলা-মেশা, আদান-প্রদান ও সম্পর্ক-সম্বন্ধের বন্ধনের ফলে। এরূপ একটি পারস্পরিক সহযোগিতা-ভিত্তিক সমাজের সদস্য হিসেবে মানুষ ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে দায়ী হয়, অতীতের স্মৃতি তার মনে-মগজে ও হাড়ে-মজ্জায় মিশে একাকার হয়ে থাকে। সে স্মৃতি প্রতি তার হৃদয়ে থাকে অটুট মমতা। কিন্তু সেই সঙ্গে সে ভবিষ্যতকে ভুলে যেতে পারেনা। ভবিষ্যতের অপরিসীম সম্ভাবনা তার সামনে এমন সব সুযোগ এনে দেয়, যার দরুণ সে বিশ্বপ্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, সুর ও ধ্বনি থেকে আনন্দ লাভ করতে ও পরিতৃপ্ত হতে পারে।
মোটকথা, মানুষের জীবনকে বাদ দিয়ে কোন সংস্কৃতির ধারণা করা যায়না আর ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটিই জীবন-কেন্দ্রিক। জীবন-নিরপেক্ষ সংস্কৃতি অচিন্ত্যনীয়। অন্যদিকে সমাজ-জীবনকে জড়িয়ে নিয়েই ঘটে সংস্কৃতির বিকাশ ও রূপান্তর। তাই সামাজিক আদর্শ ভিন্ন হলে সমাজ-সংস্কৃতিও ভিন্ন হতে বাধ্য।
সংস্কৃতির মৌল উপাদান
সংস্কৃতির সংজ্ঞাদান যেমন কঠিন, তেমনি কঠিন তার মৌল উপাদান নির্ধারণ। কেননা কোন জিনিসের মৌল উপাদান নির্ধারণ তার মৌলিক ধারণা ও তাৎপর্যের ওপর নির্ভরশীল। সংস্কৃতি বলতে যদি মানব জীবনের যাবতীয় কাজ বুঝায়, তা হলে শিল্প-কলা, সমাজ-সংস্থা, আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ এবং ধর্মচর্চা প্রভৃতি সবই তার মৌল উপাদানের মধ্যে শামিল মনে করতে হবে। আর তার অর্থ যদি হয় বিবেক-বুদ্ধি ও মানসিকতার পরিচ্ছন্নতা বিধান এবং তার লালন ও বিকাশদান, তাহলে তা মৌল উপাদান হবে মতাদর্শিক ও চিন্তামূলক। ওপরে সংস্কৃতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমরা এই শেষোক্ত দৃষ্টিকোণকে গুরুত্ব দিয়েছি। একারণে আমাদের মতে সংস্কৃতি মৌল উপাদান হবে মানসিক ও বিবেক-বুদ্ধি সংক্রান্ত। এক কথায় বলা যায়, নিম্নলিখিত বিষয়গুলোই সংস্কৃতির মৌল উপাদান হতে পারেঃ
১. মানুষের জীবন ও জগত সম্পর্কিত ধারণা-দুনিয়া কি, মানুষ কি এবং এ দুয়ের মাঝে সম্পর্ক কি? দুনিয়ার জীবন কিভাবে যাপন করতে হবে?
২. মানব জীবনের লক্ষ্য কি, কোন্ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানুষ চেষ্টা-সাধনা করবে, কি তার কর্তব্য?
৩. মানুষের জীবন ও চরিত্র কোন্ সব বিশ্বাস ও চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠবে? মানুষের মানসিকতাকে কোন্ ছাচে ঢেলে গড়তে হবে? উদ্দেশ্য লাভের জন্যে মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা ও সাধনা করবে কোন্ কারণে, কে তাকে উদ্বুদ্ধ করবে এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে?
৪. মানুষকে কোন্ সব গুণ-বৈশিষ্ট্যের ধারক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে? মানুষের আভ্যন্তরীণ গুণ-গরিমা কিরূপ হওয়া উচিত?
৫. মানুষের পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক কিরূপ হবে? পারস্পরিক এ সম্পর্ককে বিভিন্ন দিক দিয়ে কিভাবে রক্ষা করতে হবে?
এ কটি মৌল উপাদানের দৃষ্টিতে আমরা এক-একটি সংস্কৃতির ভাল-মন্দ বিচার করতে পারি-বুঝতে পারি তা সুসংবদ্ধ, না অবক্ষয়মান।
আর এ ক’টি মৌল উপাদানই হচ্ছে সংস্কৃতির চিন্তাগত ভিত্তি, মৌল নীতি-ভঙ্গি এবং চিন্তার উপকরণ। এ ক’টির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণেই সংস্কৃতির কাঠামো গড়ে ওঠে এবং এ ক’টির ভিত্তিতে যে বাস্তব রূপ গড়ে ওঠে, তা-ই হল সভ্যতা বা তামাদ্দুন (Civilization)। মানুষের জীবনের দুটি দিক প্রধান। একটি চিন্তা, অপরটি বাস্তব কাজ। চিন্তা হল তার সংস্কৃতি আর তার বাস্তব প্রকাশ হল তার তামাদ্দুন। পরন্তু চিন্তা যেমন ভালোও হতে পারে, মন্দও হতে পারে, তেমনি সংস্কৃতিও হতে পারে ভালো এবং মন্দ; বরং আরেকটু স্পষ্টভাবে বলতে পারি, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতি যেমন স্থূল হতে পারে, তেমনি হতে পারে গভীরতাপূর্ণ। অনুরূপভাবে সংস্কৃতিও হতে পারে স্থূল ও গভীরতাপূর্ণ। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের ভাষায় বলা যায়, মানুষের প্রকৃতির সাথে মানবীয় সংস্কৃতির সেই সম্পর্ক, যা মানুষের আদত-অভ্যাস, রসম-রেওয়াজ ও সৃজনশীল গুণপনার রয়েছে মানুষের প্রকৃতির সাথে। এ কারণে সংস্কৃতি যেমন স্বভাবসিদ্ধ হতে পারে, তেমনি হতে পারে কৃত্রিম। [Mohsin Mehdi, Ibn-Khaldun’s Philosophy, P-181]
ইসলামী সংস্কৃতি কি?
সংস্কৃতি সম্পর্কে এ তত্ত্বমূলক আলোচনার পর আমার বক্তব্য হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামেরও কি কোন সংস্কৃতি আছে? থাকলে কি তার দৃষ্টিকোণ? কি তার রূপরেখা?
ইসলামের সংস্কৃতি আছে কিনা কিংবা সংস্কৃতি সম্পর্কে ইসলাম কোন সুস্পষ্ট ধারণা দেয় কি-না, সে আলোচনা পরে করা হচ্ছে। তার আগে বলে রাখা দরকার যে, দুনিয়ার প্রখ্যাত কয়েকজন মনীষী ‘ইসলামী সংস্কৃতি’ বলতে কোন জিনিসকে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি আবার কি? কেউ কেউ বলেন, ইসলামের কোন সংস্কৃতি আছে না-কি? থাকলেও গ্রীক, রোমান, প্রাচীন মিশরীয়, পারসিক বা ভারতীয় সংস্কৃতিকেই ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত নেহেরূ তাঁর আত্মচরিত্রে ‘ইসলামী সংস্কৃতি’ কথাটির ওপর বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তিনি এ পর্যায়ের আলোচনায় উপমহাদেশীল মুসলিম সমাজের কতিপয় বেশিষ্ট্য সম্পর্কে বিদ্রুপ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ ‘মুসলিম সংস্কৃতি’ কে বুঝতে আমি যথেষ্ট চেষ্টা করেছি। শেষ পর্যন্ত আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, উত্তর ভারতের মধ্যম শ্রেণীর মুসলমান ও হিন্দু ফারসী ভাষা ও কিংবদন্তীতে খুবই প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে জানতে পারা যায় যে, এক বিশেষ ধরনের পাজামা-না লম্বা না খাটো-বিশেষ ধরণে গোঁফ মুণ্ড করা, দাড়ি রাখা এবং এক বিশেষ ধরণের লোটা-যার বিশেষ ধরণের থুথনি হবে, এগুলোই হচ্ছে মুসলিম সংস্কৃতি’। মুসলিম সংস্কৃতি তথা ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে মিঃ নেহেরুর এ উক্তি শুনে হাসবো কি কাঁদবো, ঠিক করা যাচ্ছেনা।
ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরাও (Orientalists) মিঃ নেহেরুর চাইতে কোন অংশে কম যান না। জার্মান পণ্ডিত ভন ক্রেমার ও লেবাননী পণ্ডিত ফিলিপ হিট্টিও ইসলামী সংস্কৃতির অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। তাদের মতে মুসলমানরা যখন পারস্য ও মিশর জয় করে, তখন তারা প্রাচীন সভ্যতার ধারক লোকদের সম্মুখীন হয় এবং তারা সবকিছু এদের কাছ থেকে শিখে নেয়। আরো বলা হয়, আরব মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে কিছুই ছিলনা। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, স্থাপত্যবিদ্যা, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও রাজ্য-শাসন এ সবের কিছুই জানতনা মুসলমানরা। তবে এসব কিছু জানবার ও শেখবার বড় অসাধারণ যোগ্যতা ও প্রতিভা মুসলমানদের মাঝে ছিল। এ পর্যায়ে প্রাচ্যবিদরা বলেনঃ গ্রীক, পারসিক ও আর্মেনিয়ান শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে পুনর্জীবন দান করেন প্রথমে আরব মুসলমানরা এবং পরে দুনিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় মুসলমানরা।
পণ্ডিত নেহেরুই হোন আর প্রাচ্যবিদ এসব বড় বড় পণ্ডিতরা, এরা কেউ-ই যে ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে পারেননি, তা বলাই বাহুল্য। আর ইসলামী সংস্কৃতিকে বুঝতে না পারার মূল কারণ যে ইসলামের প্রকৃত ভাবধারাকে বুঝতে না পারা, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। অথবা বলা যায়, তারা জেনে-শুনেই ইসলামী সংস্কৃতিকে বিদ্রুপ করেছেন, তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন কিংবা এ-ও হতে পারে যে, তারা একটি ছিদ্র দিয়ে ইসলামকে দেখার চেষ্টা করেছেন বলেই তাদের ধারণা এতদূর বাঁকা ও অর্থহীন হয়ে গেছে যে, তাঁরা তা টেরেই পাননি।
কেবল প্রাচ্যবিদরাই নন-নয় কেবল প্রাচীন পণ্ডিতদের কথা, ইসলামী সংস্কৃতিকে অস্বীকৃতি জানাতে কসুর করেননি এ যুগের এবং এ দেশের প্রতিবেশী অমুসলিম জাতিও। শুধু তা-ই নয়, তাদের ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত ও ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানে পারদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তিরা এবং তথাকথিত মুসলিম নামধারী লেখকরাও ইসলাম সংস্কৃতিকে-সংস্কৃতির ইসলামী ধ্যান-ধারণাকে তথা ইসলামী রূপরেখাকে বুঝতে পারেন নি; হয়ত-বা বুঝতে চেষ্টাই করেননি অথবা বুঝতে চাননি কিংবা বলা যায় বুঝতে পেরেও তাকে অস্বীকারই করতে চেয়েছেন। কেননা অস্বীকার না করলে কিংবা তাকে সংস্কৃতি বলে স্বীকৃতি দিয়ে সংস্কৃতির নামে চলমান বর্তমানের আবর্জনা, অশ্লীলতা ও জঘন্যতাকে পরিহার করতে হয় আর তাকে পরিহার করলে জীবনের আনন্দ-স্ফূর্তির উৎসই যে বন্ধ হয়ে যাবে-মৌচাক যাবে শুকিয়ে। তখন জীবন যে যাবে মরু আরবের মত ঊষর-ধূসর-রূক্ষ্ণ-নিরস হয়ে। তখন বেঁচে থাকার স্বাদটুকুও যে নিঃশেষ হয়ে যাবে; ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের জীবন-স্রোতে ভাবতে হবে, জীবনের গতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে, বইতে হবে ভিন্ন স্রোত-বেগে আর তা তাদের পক্ষে সহ্য করা কিছুতেই সম্ভব হবেনা। অতএব তাদের বলতে হয়েছেঃ
‘‘স্থূলভাবে যারা ধর্মাচরণ এবং ধর্মভিত্তিক ধ্যান-ধারণার সমষ্টিকে সংস্কৃতি বা তামাদ্দুন মনে করেন অথবা আরব-পারস্যের জ্ঞান-চর্চা ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকেই সারা মুসলিম জাহানের সংস্কৃতি বলতে চান, তাদের সঙ্গে তর্ক দুঃসাধ্য।’’ (দৈনিক সংবাদ)
হ্যাঁ, দুঃসাধ্যই বটে! দুনিয়ার মনীষীদের মত অনুযায়ী ‘ধর্মকে সংস্কৃতির উৎস’ রূপে স্বীকার করে নিলে যে ধর্মকে মানতে হয়, মেনে নিতে হয় ধর্মীয় অনুশাসনে, সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতে হয় বর্তমানে সংস্কৃতির নামে চলমান অনেক অশ্লীলতা, জঘন্যতা ও বীভৎসতার আবর্জনাকে। আর এক শ্রেণীর পোকা যে ময়লার স্তুপ ত্যাগ করলে মরে যায়, তাতো সকলেরই জানা কথা।
সংস্কৃতি ও ইসলাম
ইসলাম দুনিয়ার সকল জনগোষ্ঠীর সকল মৌল সত্যের সমষ্টি। তার সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক মর্যাদাসম্পন্ন, সর্বজনীন ও সুদূরপ্রসারী। দুনিয়ার অন্য যেসব সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক উপাদান তার মৌল ভাবধারার অনুকূল, তা সবই সে গ্রহণ করে নেয়। বস্তুত যে সংস্কৃতিতে ইসলাম-বিরোধী উপাদান ও উপকরণ রয়েছে, তা-ই সুস্পষ্টভাবে মানবতা বিরোধী; তার সাথে ইসলামের রয়েছে চিরন্তন সংঘর্ষ। ইসলামী সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উৎকর্ষ দান কোন সাম্প্রদায়িক সংষ্কৃতির উত্তরাধিকারের সংরক্ষণ নয়। তাতে বরং সমগ্র মানব কল্যাণকর সংস্কৃতিই সংরক্ষিত হয় এবং তাতে করেই সমস্ত তামাদ্দুনিক সৌন্দর্যের উৎকর্ষ সম্ভব হতে পারে।
ইসলামী সংস্কৃতি গ্রীক সংস্কৃতি নয়-নয় তা পারসিক সংস্কৃতি। কাজেই গ্রীক বা পারসিক সংস্কৃতিকে ইসলামী সংস্কৃতি বলে চালিয়ে দেয়া যেতে পারে না। ইসলামী সংস্কৃতি ইসলামী মতাদর্শের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। আল্লাহর কালাম কুরআন মজীদেই এ মতাদর্শের বিস্তারিত রূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এবং নবী করীম সা.-এর মহান জীবন ও শিক্ষায় তা পুরোপুরি প্রতিফলিত হয়েছে।
ইসলামী সংস্কৃতির গোড়ার কথা
ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা আর এ জীবন ব্যবস্থার চিন্তামূলক দিকই হল ইসলামী সংস্কৃতি। তাই ইসলামী সংস্কৃতি বলতে নিম্নোক্ত তিনটি জিনিস বুঝায়ঃ
১. উন্নততর চিন্তার মান, যা ইসলামী রাষ্ট্রের কোন এক যুগে বাস্তবায়িত হয়েছিল।
২. ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এবং শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অর্জিত সাফল্য।
৩. মুসলমানদের জীবনধারা, ধর্মীয় কাজকর্ম, ভাষার ব্যবহার ও সামাজিক নিয়ম-প্রথার বিশেষ সংযোজন। [Islamic Culture, P-6]
অপর এক চিন্তাবিদদের দৃষ্টিতে ইসলামী সংস্কৃতির দুটি অর্থঃ একটি তার চিন্তার দিক আর অপরটি হল সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজ-সংস্থা। কিন্তু আমরা প্রথমটিকেই সংস্কৃতি মনে করি বলে বলা যায়, সংস্কৃতি হচ্ছে এক বিশেষ ধরণের মানসিক অবস্থা, যা ইসলামের মৌল শিক্ষার প্রভাবে গড়ে ওঠে; যেমন আল্লাহর একত্ব, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও মানব বংশের ঐক্য ও সাম্য সংক্রান্ত বিশ্বাস। [International colloqium, P-26]
মানুষের চিন্তাগত জীবন এ দৃষ্টিভঙ্গিতেই আলোক-উদ্ভাসিত হয় এবং গোটা মানববংশ প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে এ আলোকচ্ছটায়। আসলে ইসলামী সংস্কৃতি আলোর এক সু্উচ্চ মিনার; এ থেকেই ইসলামী সভ্যতা রূপায়িত হয়। এ মিনারই সমগ্র জগতের সংস্কৃতিসমূহকে প্রভাবান্বিত করেছে, আপনও বানিয়ে নিয়েছে।
ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য
দুনিয়ার সব জিনিসের মতো সংস্কৃতিরও একটা লক্ষ্য রয়েছে। লক্ষ্যহীন সংস্কৃতি আদতেই সংস্কৃতি নামের যোগ্য নয়; তা নিতান্ত তামাসা মাত্র-তা ছেলেখেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। যদিও উদ্দেশ্যহীনতাই বর্তমান সভ্যতার মৌল ভাবধারা; সর্ব-প্রযত্নে উদ্দেশ্যবাদকে (Objectivity) পরিহার করে চলাই এখনকার সমাজের একটা ফ্যাশান। কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা বলবার মতো সময় এখন উপস্থিত যে, উদ্দেশ্যহীনতা নেহাত পশুকুলের বিশেষত্ব; পক্ষান্তরে মানুষের বৈশিষ্ট্যই হল তার উদ্দেশ্যবাদিতা। তাই উদ্দেশ্যবাদকে হারালে মানুষে আর পশুতে কোন পার্থক্য থাকেনা। উদ্দেশ্যবাদ তথা উদ্দেশ্যের বিচারে ভুল-নির্ভুল নির্ধারণ এবং ভুল-কে বাদ দিয়ে নির্ভুল-কে গ্রহণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।
তাহলে মানবীয় সংস্কৃতির উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কি? সংস্কৃতি শব্দটিই উদ্দেশ্যের প্রবণতা ব্যক্ত করে। বাংলা সংষ্কৃতি, ইংরেজী কালচার (Culture) এবং উর্দু-আরবী তাহযীব কিংবা সাক্বাফাত-এ শব্দ তিনটির যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সংস্কৃতির একটা না একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকতেই হবে। অন্যথায় তার কোন অর্থ হয় না-হতে পারে না তার কোন বাস্তব রূপ এবং মানব জীবনেও তার কোন সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যাবে না।
সংস্কৃতি বলতে বুঝায় সংস্কার, সংশোধন, পরিশুদ্ধিকরণ ও পরিচ্ছন্নতা বিধান। আর কালচার বলতে বুঝায় কৃষিকাজ। তাহযীবও পরিচ্ছন্নকরণ ও উন্নয়নকে বুঝায় আর সাক্বাফাতের অর্থ হল তীক্ষ্ণ, শানিত ও তেজস্বী করে তোলা। এর প্রতিটি অর্থেই উদ্দেশ্যের ব্যঞ্জনা বিধৃত। ‘সংশোধন’ শব্দ শোনামাত্রই চোখের সামনে ভেসে ওঠে ভুলগুলোকে বাদ-সাদ দিয়ে তদস্থলে সঠিক ও নির্ভুল জিনিস সংস্থাপন। পরিশুদ্ধিকরণ তখনি বলা চলে, যখন অপবিত্র ও অশুদ্ধ জিনিস দূর করে দেয়া হবে। আর কৃষিকাজ হল জমির আগাছা-পরগাছা ও ঝাড়-জঙ্গল কেটে ফেলে, অবাঞ্ছিত তৃণ-লতা উপড়ে ফেলে লাঙ্গল দিয়ে হাল চালিয়ে জমিকে নরম-মসৃণ করে সেখানে বীজ বপন করা। এসব ক্ষেত্রেই ভাঙা-গড়ার ন্যায় নেতিবাচক কাজের পর ইতিবাচক কাজের অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট। একদিকে ছাঁটাই-বাছাই ও বর্জন এবং অপরদিকে মনন, আহরণ ও গ্রহণ। বস্তুত এসব কাজের নির্ভুল, যৌক্তিক ও বিচক্ষণ সম্পাদনেই গড়ে ওঠে সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতি অবশ্যই উদ্দেশ্যমূলক।
সংস্কৃতির উদ্দেশ্যমুখীনতা অনুধাবনের জন্যে কৃষিকাজের কথাটা অধিকতর সুস্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। জমিতে যেসব আবর্জনা, ঝাড়-জঙ্গল, ঘাসের শিকড় ইত্যাদি ছড়িয়ে থাকে, চাষী সেগুলোকে লাঙ্গলের ফলার সাহায্যে উপড়ে ফেলে মাটির সাথে গুড়িয়ে মিশিয়ে দেয়। আর যেগুলো মাটির সাথে মিশে একাকার হয়ে যেতে রাজী নয়, সেগুলোকে সে নিড়িয়ে আলাদা করে রাখে, যেন তা ফসলের চারা গজাতে ও তাতে ফসল ফলতে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করতে না পারে।
এরপর শুরু হয় তার দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। এ পর্যায়ে মাটিকে অত্যন্ত নরম তুলতুলে করে তুলে তার উপর বীজ বপন করা হয়, যেন মাটি সহজেই বীজকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করতে পারে এবং তার শিকড় গজাতে ও অংকুর বের হতে কোন প্রকার অসুবিধা দেখা না দেয়; বরং একাজে মাটি পুরোমাত্রায় অনুকূল ও সহায়ক হয়।
এখানেই চাষীর কাজ শেষ হয়ে যায়না। জমিতে বপন করা বীজ যাতে করে পচে যেতে না পারে, উড়ো পাখী বা পোকা-মাকড় তা খেয়ে না ফেলে এবং লোনা পানি বা কচুরীপানা এসে গোটা ক্ষেতকে ধ্বংস করে না দেয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও তার জন্যে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করাও তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। চাষীর এ গোটা কর্মধারারই অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। সংস্কৃতির ব্যাপারটিও অনেকটা তাই।
সংস্কৃতির ক্ষেত হল মানুষের মন-মগজ, রুচিবোধ, আচার-অনুষ্ঠান এবং জীবন ও চরিত্র। এ সমগ্র ক্ষেত্রব্যাপী মানুষের একক ও সামষ্টিক প্রচেষ্টাই সংস্কৃতির সাধনা। চাষীর শ্রম-মেহনত, চেষ্টা-সাধনা ও সতর্কতা যেমন উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না, তেমনি সংস্কৃতির সাধনাও কোন পর্যায়েই উদ্দেশ্যবিহীন হওয়া কাম্য নয়।
চাষীর লক্ষ্য যেমন ক্ষেত-ভরা সোনার ফসল ফলানো, তেমনি সংস্কৃতি-সাধনারও লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন, সুস্থ, মার্জিত, ভদ্র এবং আদর্শবান, রুচিশীল ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলা।
জমিতে কিছু একটা ফলাতে হলে চাষ করা অপরিহার্য। অবশ্য ফসলের তারতম্যের কারণে চাষের ধরণ ও মাত্রায় পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে যে-ধরণের মানুষ সৃষ্টি লক্ষ্য হবে, সেই ধরণের সংস্কৃতি-চর্চা করা ছাড়া উপায় নেই। আর মানুষ সম্পর্কিত ধারণা বিভিন্ন হওয়ার কারণে সংস্কৃতির ধারণা, তার অনুশীলন ও অন্তর্নিহিত ভাবধারায়ও আকাশ-পাতালের পার্থক্য হওয়া অবধারিত। চাষী যে ফসল ফলাতে ইচ্ছুক তাকেও তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই জমিতে অনুরূপ চাষই দিতে হবে, তারই বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে এবং তার পক্ষে যা যা ক্ষতিকর তার প্রতিরোধও করতে হবে। অন্যথায় তার সব শ্রম-মেহনত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সংস্কৃতি মানুষ গড়ার প্রধান হাতিয়ার। তাই যে ধরণের মানুষ সৃষ্টি লক্ষ্য হবে, তারই অনুরূপ ধারণা-বিশ্বাস, মূল্যমান, রুচিবোধ ও ভাবধারার বীজ মানুষের হৃদয়ে বপন করতে হবে; তার লালন, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। আর তার পক্ষে ক্ষতিকর যেসব মূল্যবোধ ও আকীদা-বিশ্বাস, তাকে রোধ করার ও তার হামলা থেকে জন-সমাজকে রক্ষা করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে চিন্তা-বিশ্বাস, শিক্ষা প্রচার এবং শাসন ও জন-জীবন গঠনের ক্ষেত্রে। এরূপ করা সম্ভব হলেই আশা করা যেতে পারে যে, বাঞ্ছিত মানুষ গড়ে উঠবে।
এভাবে যেসব মানুষ গড়ে উঠে কিংবা বলা যায়, যাদের জীবনে ও চরিত্রে এভাবে সংস্কৃতির রূপায়ন ঘটে-প্রতিফলিত হয় সংস্কৃতির স্বচ্ছ ও পূর্ণ-পরিণত ভাবধারা, তারাই হল সংস্কৃতিবান মানুষ (Cultured man)।
বস্তুত সংস্কৃতির লক্ষ্য যেমন মানুষের অভ্যন্তরে বিশেষ গুণাবলী সৃষ্টি করা, তেমনি মানুষের বাহ্যিক জীবনকে-তার আচার-আচরণকে একটি বিশেষ আদর্শে রূপায়িত করে তোলাও তার লক্ষ্যের মধ্যে শামিল। যেসব জ্ঞান,চিন্তা, বিশ্বাস, রুচি ও ভাবধারা মানুষের মনোলোককে বিশেষ সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণে আলোকোদ্ভাসিতক করে তোলে এবং যেসব বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান মানুষের অন্তরে সাংস্কৃতিক চেতনা জাগ্রত করে, যেসব কমর্কাণ্ড দ্বারা মানুষের বাহ্যিক জীবনকে-ব্যক্তি জীবন ও সামষ্টিক জীবনকে- বিশেষ আদশের্র ভিত্তিতে প্রোজ্জ্বল করা সম্ভব, তা-ই হল সংস্কৃতির বাহন।
প্রচলিত ধরণের শিক্ষা, জ্ঞানানুসন্ধান, শিক্ষণীয় বিষয়াদির অনুশীলন এবং বিশেষভাবে প্রত্নতত্ত্ব, স্থাপত্য, ভাস্কর্য নির্মাণ, চিত্র-শিল্প, কাব্য-সাহিত্য চর্চা, নৃত্য-সঙ্গীত, নাট্যাভিনয় এবং এ পর্যায়ের অন্যান্য ললিতকলা হচ্ছে সংস্কৃতির বিশেষ উপাদান ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান। একটা নাচ-গানের অনুষ্ঠানকে যেমন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলা হয়, তেমনি ডিবেট, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ফ্যাশান শো, সৌন্দর্য প্রতিযোগিতা, মীনা বাজার ইত্যাদি অনুষ্ঠানকেও সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়। এসব বাহ্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে চিত্ত-বিনোদন, মনের তৃপ্তি-স্বস্তি এবং সুখ ও আনন্দ লাভই হচ্ছে এর মূলে নিহিত আসল লক্ষ্য। তাই বলা যায়, আধুনিক ধারণামতে সংস্কৃতির এই হল লক্ষ্য এবং কম-বেশি এ ক’টি জিনিসকেই সংস্কৃতির মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে।
কিন্তু আসল ব্যাপার হল, সংস্কৃতি কেবলমাত্র এ ক’টি অনুষ্ঠানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়-নয় কেবলমাত্র এ’কটিই তার নির্দিষ্ট মাধ্যম। বস্তুত সংস্কৃতির পরিধি অতীব ব্যাপক। তার মাধ্যম হল মানুষের সমগ্র জীবন, জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগ-সমস্ত কাজ, ব্যস্ততা ও তৎপরতা। শুধুমাত্র চিত্তবিনোদন ও আনন্দ-সুখ লাভ করাকেই সংস্কৃতির লক্ষ্য মনে করা এবং কেবলমাত্র উপরোক্ত অনুষ্ঠান ক’টিকেই সংস্কৃতির মাধ্যম বলে ধরে নেয়া সংস্কৃতিরই অপমান।
ফিলিপ বাগবীর কথায় এরই পূর্ণ সমথর্ন পাওয়া যাচ্ছে। তিনি বলেছেনঃ
‘‘কালচার বলতে যেমন চিন্তা ও অনুভূতির সবগুলো দিক বুঝায়, তেমনি তা কমর্নীতি, কাযর্পদ্ধতি এবং চরিত্রের সবগুলো দিককে পরিব্যাপ্ত করে।’’
বাগবীর এ উদ্ধৃতিতে সংস্কৃতির একটা ব্যাপক ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। আসলে সংষ্কৃতির এ ব্যাপক সংজ্ঞাতেই তার তাৎপর্য নিভুর্লভাবে বিধৃত। ইসলামের সংস্কৃতি চেতনা এমনি ব্যাপক ও সর্বাত্মক। তা বিশেষ কয়েকটি কিংবা নিদির্ষ্ট কতকগুলো উপাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কয়েকটি বাহ্যিক অনুষ্ঠানই নয় তার একমাত্র অভিব্যক্তি।
কিন্তু সংস্কৃতির মৌল উদ্দেশ্য কি? সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে যে মানুষ গড়তে হবে, সে মানুষ কেমন হবে-কি হবে তার নৈতিক মূল্যমান? তার ভালো কি মন্দ কি, কি গ্রহণীয় এবং কি বজর্নীয়? তার উচিত বা অনুচিত বোধের ভিত্তি কি হবে? কোন্ জিনিসে তার মনে আনন্দের সঞ্চার হওয়া উচিত এবং কোন্টায় দুঃখ ও ব্যাথা?….. এ সবের জবাব এক-একটা আদশের্র দিক দিয়ে এক এক রকম। এ বিষয়ে ইসলামী ধারণা ও আধুনিক চিন্তাধারায় মৌলিক পাথর্ক্য বিদ্যমান।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা রাজপথ। যে কোন দিকে যেতে হলে এ পথ দিয়েই যেতে হবে সবাইকে। কিন্তু প্রশ্ন হল, যাওয়া হবে কোন্ দিকে, কিভাবে এবং কেন? এই কোন্ দিকে, কিভাবে এবং কেন’র পশ্ন নিয়েই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে আধুনিক চিন্তাধারার যত বিরোধ ও সংঘাত। এ কথাটি খুবই বিস্তারিতভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে।
সংস্কৃতিকে মনে করা যেতে পারে একটা প্রবহমান নদী। নদীতে যেমন স্বচ্ছ পানি প্রবাহিত হয়, তেমনি প্রবাহিত হয় কাদা পানি- ময়লা ও আবজর্নাযুক্ত পানি।
যে লোক এ নদী থেকে স্বচ্ছ পানি গ্রহণ করতে চায়, তাকে অন্ধের মত নদীর যে কোন স্থান থেকে পানি তুলে নিলে চলবে না। তাকে অবশ্যই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে হবে, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন পানি কোনখানে প্রবাহিত হচ্ছে। মাঝ নদী কিংবা গভীর তলদেশ-যেখানেই তা পাওয়া যাবে, সেখান থেকেই তাকে পানি তুলে নিতে হবে। এ স্বচ্ছ পানি তুলে নেয়ার সময়ও লক্ষ্য রাখতে হবে, তার সাথে যেন কোন ময়লা, আবজর্না কিংবা সাপ-বিচ্ছু চলে না আসে। তা না হলে শুধু কাদা পানি কিংবা ময়লা-আবজর্না যুক্ত পানিই তাকে পান করতে হবে অথবা স্বচ্ছ পানি পান করার সঙ্গে সঙ্গে সাপ-বিচ্ছুর দংশনেও জজর্রিত হতে হবে।
এ থেকে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সংস্কৃতির ব্যাপারে মূল লক্ষ্য ও দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব সব চাইতে বেশী। আসলে এটাই হল খাঁটি স্বর্ণ ও কৃত্রিম স্বর্ণ যাচাইয়ের কষ্টিপাথর।
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ ছাঁটাই-বাছাই এর গুরুত্ব কোনক্রমেই অস্বীকার করা যেতে পারে না। কেননা সংস্কৃতি-অনুরাগী মানুষ সংস্কৃতি নামে প্রচলিত আবর্জনাকে গ্রহণ করতে কখনো রাজী হতে পারে না। সে তো যাচাই-বাছাই করে এক ধরণের সংস্কৃতিকে বর্জন করবে আর অপর এক ধরনের সংস্কৃতিকে মন-প্রাণ-হৃদয় ও জীবন দিয়ে গ্রহণ করবে। সত্যিকার সংস্কৃতিবান মানুষের এইতো পরিচয়। সংষ্কৃতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বর্জন-গ্রহণের এ মানদণ্ড হচ্ছে প্রত্যেকের জীবন দশর্ন। যার জীবন দর্শনের উৎস থেকেই সংস্কৃতি তারই অনুরূপ-তার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল কেননা জীবন-দশর্নের উৎস থেকেই সংস্কৃতি উৎসারিত।
দুনিয়ার প্রায় সব মানুষেরই একটা জীবন দশর্ন রয়েছে। আর জীবন-দশর্নে যেহেতু পাথর্ক্য রয়েছে সেই কারণে সংস্কৃতি-বিষয়ক ধারণা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতেও মৌলিক পাথর্ক্য হওয়া অবধারিত। এখানে স্বর্তব্য যে, জীবন-দর্শন উদ্ভূত হয় জীবনাদর্শ থেকে। জীবনাদর্শ যা, জীবন-দর্শনও তাই। আর দুনিয়ার মানুষের জীবনাদর্শ যেহেতু বিভিন্ন, তাই জীবন-দর্শনেও বিভিন্নতা স্বাভাবিক। জীবন-দর্শনের এই বিভিন্নতার কারণে সংস্কৃতিরও বিভিন্ন রূপ ও পরস্পর বৈসাদৃশ্য একান্তই অনিবার্য।
তাই তো দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদ যাদের জীবনাদর্শ, তাদের সংস্কৃতি জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত; আন্তর্জাতিকতা সেখানে সযত্নে পরিত্যক্ত। আবার জাতীয়তাবাদের ভিত্তিও বিভিন্ন রূপ। ভাষা-ভিত্তিক জাতীয়তার সংস্কৃতিতে অন্য ভাষার প্রতি বিদ্বেষ বর্তমান; আঞ্চলিক জাতীয়তায় অপর অঞ্চলের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা এক স্বাভাবিক ব্যাপার। বর্ণভিত্তিক জাতীয়তার অবস্থাও অনুরূপ। সর্বোপরি জাতীয়তাবাদ একটা বস্তু-নির্ভর ব্যাপার বলে সেখানে বস্তুর প্রাধান্য সর্বত্র। নির্বস্তুক (Abstract) আদর্শমূলক সংস্কৃতির সেখানে কোন স্থান নেই।
কেবল জাতীয়তাবাদেই নয়, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রেও অনুরূপ অবস্থাই পরিদৃষ্ট হচ্ছে। পুঁজিবাদী সমাজ সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ পুঁজিবাদী সংষ্কৃতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় না; বরং তাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ বর্তমান। একটি অপরটির মূলোচ্ছেদে পূর্ণ শক্তি নিয়োজিত করতেও দ্বিধাবোধ করে না।
ইসলামী আদর্শবাদীদের নিকটও তাই সংস্কৃতির একটা ইসলামী ধারণা নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে ছাঁটাই-বাছাই তথা বর্জন ও গ্রহণের নীতি অবলম্বন অতীব স্বাভাবিক। সংস্কৃতি নামে চলমান যে কোন জিনিসকেই ইসলামী জনতা সংস্কৃতি বলে মেনে নিতে প্রস্তুত হতে পারে না।
বস্তুত প্রতিটি জীবন-ব্যবস্থাই তার নিজস্ব মানে ব্যক্তি ও সমাজ গঠন করে। তাই যে ধরণের মানুষ ও সমাজ গঠন তার লক্ষ্য সেরূপ মানুষ ও সমাজ গড়ে উঠতে পারে যে সংস্কৃতির সাহায্যে, তা-ই সে কার্যকর ও বাস্তবায়িত করে তোলে পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগ করে এবং তার বিপরীত সংস্কৃতিকে প্রতিহত করে কার্যকর ব্যবস্থাপনার সাহায্যে। ইসলামও একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ-একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা। তাই তার ব্যক্তি ও সমাজ গঠনের মান (Standard) সম্পূর্ণ ভিন্ন হবে এবং তার পরিকল্পিত মানুষ ও সমাজ গঠনের উপযোগী সংস্কৃতি তাকে অবশ্যই গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে হবে।
পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শন মানুষকে পশুর উত্তরাধিকারী এক বিশেষ জীবমাত্র মনে করে; তা বিশ্বলোককে মনে করে খোদাহীন, স্বয়ম্ভু। তাই এই দর্শনের দৃষ্টিতে আল্লাহকে মেনে চলার এবং আল্লাহর দেয়া কোন বিধান তথা ধর্মমত মেনে নেয়ার কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের নেই। আর মানুষ নিতান্ত পশু বলে তার কোন মূল্যবোধ (Sense of Value) ও মূল্যমান থাকারও প্রয়োজন নেই।
এই মৌলিক কারণেই সংস্কৃতি নিছক চিত্ত-বিনোদনের উপায় ও মাধ্যম বলে পাশ্চাত্য সমাজে বিবেচিত এবং যে সব অনুষ্ঠানে এই চিত্ত-বিনোদন পূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হতে পারে তা অবশ্য গ্রহণীয়। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে চিত্তের দাবির কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সেখানে তো প্রতি মুহূর্ত ‘আরো চাই, আরো দাও’-এর দাবিই উচ্চারিত হতে থাকে। তাই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে সেখানে নিত্র-নতুন ধরণে ও অভিনব ভঙ্গিতে চমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে জনগণের সাংস্কৃতিক ক্ষুধু নিবৃত্ত করার চেষ্টা করা হয় অবিশ্রান্তভাবে।
পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাথমিক উপকরণ হল গান-বাজনা ও নৃত্য। আসলে এগুলো প্রাচীন গ্রীক, রোমান ও হিন্দু সমাজের ধর্মীয় পূজা-অচৃনার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বহুকাল থেকে চলে এসেছে। দেবতার সামনে সুন্দরী যুবতী রমনীর আরতি দান দেব-পূজারই এক বিশেষ অনুষ্ঠান। হাতে পূজার অর্ঘ্য নিয়ে নৃত্যের তালে তালে মিষ্টি মধুর কণ্ঠে গান গেয়ে গেয়ে দেবতার পদতলে অর্ঘে্যর ডালি সঁপে দেয়া হিন্দু সমাজের এক বিশেষ ধরণের পূজা অনুষ্ঠান। উত্তরকালে সংস্কৃতি-পূজারীরা এ পূজা অনুষ্ঠানকেই মন্দিরের সংকীর্ণ পরিবেশ থেকে বের করে এনে একে বিশাল হলে ঘরের সুসজ্জিত ও সুউচ্চ মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। যা ছিল দেবতার সম্মুখে নিজকে পূর্ণমাত্রায় নিবেদিত করার একটা বিশেষ ধরণের অনুষ্ঠান, উন্মুক্ত মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করে তাকেই বানানো হলো চিত্তবিনোদন তথা রস-পিপাসু মানুষের সম্মুখে উপভোগ্য রূপে নিজেকে নিবেদন করার প্রধান মাধ্যম। অতঃপর নাচ-গান ও বাজনার এ অনুষ্ঠান মঞ্চের ওপর এসে ক্রমশ বিকাশ ও উৎকর্ষ লাভ করতে করতে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছে। একক নৃত্য, যুগলনৃত্য, বল নাচ, ফ্লোর-নাচ ইত্যাদি নানা বৈচিত্র্যময় নাচ-গানের সঙ্গে এসে মিশেছে অভিনয় এবং তা অবশ্যই প্রেমাভিনয়। এ সব দ্বারা চিত্তবিনোদন হয় বলে এখন এটা পাশ্চাত্য ও বস্তুবাদী জীবন-দর্শনপ্রসূত সংস্কৃতির অপরিহার্য় অঙ্গে পরিণত। প্রথম দিকে ছিল একক গান, এখন তা যুগ্ম ও সমবেত। এর সাথে শুরু হল নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর সহ-অভিনয়- প্রেমাভিনয়; কিন্তু তাতেও চিত্তবিনোদনের কাজ সম্পূর্ণতা পেল না। ফলে শুরু হল অর্ধ নগ্ন ও প্রায় উলঙ্গ নৃত্য-সমৃদ্ধ অনুষ্ঠান। নারী-পুরুষের প্রকাশ্য চুম্বন, আলিঙ্গন ও যৌন মিলনের অুনষ্ঠানও মঞ্চের ওপরই দেখানো শুরু হল শত-সহস্র নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর বিস্ফোরিত ও বিস্মিত চোখের সামনে। কেননা এটা না দেখানো পর্যন্ত চিত্তবিনোদনের অন্তত ক্ষুধা নিবৃত্ত হতে পারেনা-চরিতার্থ হতে পারেনা মনের অসীম-উদগ্র কামনা।
পূর্বেই বলেছি, আলোচ্য সংস্কৃতি দর্শনে মানুষ পশু শ্রেণীরই একটি জীবমাত্র এবং সে কারণেই তাদের নৈতিকতা ও চরিত্রের কোন প্রশ্ন ওঠতে পারেনা বলে মানুষের লজ্জা ও শরমেরও কোন বালাই থাকার কথা নয়। তাই সংস্কৃতি-মঞ্চে বেশী বেশী নির্লজ্জতা ও নগ্নতা প্রদর্শন শিল্প-সৌকর্যেরই পরাকাষ্ঠা হয়ে দাঁড়াল। আর যে তা যত বেশী দেখাতে পারবে, সে সকলের নিকট বরিত হবে তত বেশী সার্থক শিল্পী রূপে। সংস্কৃতি জগতের সে হবে একজন বিরাট ‘হীরো’।
পশ্চিমা সমাজে যে যুবক-যুবতীরা যুগ্ম ও সমবেতভাবে প্রায়-নগ্ন কিংবা সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে রৌদ্রকোজ্জ্বল উন্মুক্ত প্রান্তরে রৌদ্রস্নান এবং সমুদ্র-সৈকতে সমুদ্র-স্নানের উৎসব পালন করছে, তারা তো চিত্তবিনোদনেরই নানা অনুষ্ঠান উপভোগ করছে। এত কোন লজ্জা নেই-নেই কারোর একবিন্দু আপত্তি; বরং সমগ্র শিক্ষা ও পরিবেশ থেকেই তা নিত্য বাহ্বা পাচ্ছে। কেননা এসব নিতান্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বই তো কিছু নয়!
এভাবে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী দর্শন-যার একটি শাখায় রয়েছে পুঁজিবাদ এবং অপর দিকে রয়েছে সমাজতন্ত্র-আর সেই সঙ্গে স্থানীয়ভাবে পাওয়া গেছে হাজার বছরের পৌত্তলিক সংষ্কৃতি; এই সব মিলে আজকের মানুষকে ঠিক পশুর পর্যায়ে নামিয়ে দিয়েছে। কেননা এ দর্শন মানুষকে নিতান্ত পশু বা পশুর বংশধর ছাড়া কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত সৃষ্টি মনে করে না। আর পশুকে অধিক পাশবিকতা শিক্ষা না দিলে তাকে যেমন সত্যিকার পশু বানানো যায় না, তেমনি পাশবিকতার কাজে অগ্রগতি ও উৎকর্ষ লাভও সম্ভবপর হয়না। তাই বর্তমান কালের সংস্কৃতিতে এ পর্যন্ত যতটা উৎকর্ষ লাভ করে গিয়েছে, তা সবই পাশবিকতারই উন্নতি সাধন করেছে। এ ‘পশু’কে মনুষত্বে রূপান্তরিত করার কোন চিন্তাই এখানে করা হয়নি-মনুষ্যত্বের দিকে প্রত্যাবর্তনের কোন খেয়ালই জাগেনি এই ‘পশুত্ববাদী’দের সংস্কৃতি চর্চায়।
কিন্তু ইসলামী জীবন-ব্যবস্থা আগাগোড়াই তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও আলাদা পথে অগ্রসরমান এক আদর্শ। ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ শুধু একটি সৃষ্টিমাত্র নয়-যেমন অন্যান্য হাজারো সৃষ্টি; বরং মানুষ হল আল্লাহর এক বিশেষ সৃষ্টি-বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক ও দায়িত্বশীল সৃষ্টি। মানুষ আল্লাহর সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বোন্নত প্রজাতি-আশরাফুল মাখলুকাত। অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র এক বিশেষ দায়িত্ব পালন করা মানুষের এ জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। সে লক্ষ্য এ দুনিয়ায়ই অর্জিত হতে হবে- সে দায়িত্ব পালন করতে হবে এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার মধ্যেই। কিন্তু তার সবটাই এখানে শেষ হবে না, তার পূর্ণ পরিণতি ও প্রতিফলন ঘটবে এই জীবনের অবসান ঘটার পর অপর এক জগতে। সেজন্যে এই জগতের জীবনকে মানুষ পরকালীন জীবনের আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে একান্তভাবে উৎসর্গ করে দেবে পরিপূর্ণ ইসলামী জীবন যাপনের মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা’আলা দুনিয়ায় মানুষের বসতি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের রচিত জীবন বিধান (ইসলাম) নাযিল করেছেন তাঁরই মনোনীত ব্যক্তিদের মারফতে।
ইসলামের লক্ষ্য হল মানুষকে আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দাহ রূপে গড়ে তোলা। আর আল্লাহর মনোপুত কাজের মাধ্যমে তাঁর সন্তোষ লাভের অধিকারী হওয়াই হল ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। তাই নিজেকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর উপযুক্ত বান্দাহ রূপে গড়ে তোলাই হল ইসলামের দৃষ্টিতে সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা, সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কুরআন মজীদের এ কথাই বলা হয়েছে নিম্নোদ্ধৃত ভাষায়ঃ
‘‘যে ‘তাযকিয়া’ লাভ করল এবং তার আল্লাহর নাম স্মরণ করল সেই সঙ্গে নামাযও পড়ল, সে-ই সত্যিকার কল্যাণ ও সাফল্য লাভ করল। কিন্তু তোমরা তো দুনিয়ার জীবনকেই অধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিচ্ছ, যদিও পরকালই হচ্ছে অধিক উত্তম চিরস্থীয়।
এ আয়াতে যে ‘তাযকিয়া’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে হলো পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধি লাভ-চিন্তা ও বিশ্বাসের পরিচ্ছন্নতা, মন-মানস, আকীদা-বিশ্বাস দৃষ্টিকোণ ও মূল্যমান তথা মন ও দেহের পরিশুদ্ধতা আর ইসলামী সংস্কৃতিও এটাই।
অতএব যে সব কাজে সে পরিশুদ্ধতা ও পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়, তা-ই ইসলামী সংস্কৃতি। যাতে তা বলা হয় বরং যাতে যাতে মন-মানস তথা জীবন ও চরিত্র হয় কলুষিত তা ইসলামী সংষ্কৃতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
এ আয়াতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তা’আলাকে স্মরণ করা, তাঁকে কখনো কোন অবস্থায়ই ভুলে না যাওয়া, তাঁর বন্দেগীর প্রবল তাগিদে রীতিমত নামায পড়া-এগুলোই হল ইসলামী সংস্কৃতির বাছাই করা অনুষ্ঠান। এ সবের মাধ্যমে নরনারীর আস্থা মন-মানস ও জীবনের যে পরিশুদ্ধ ও পরিচ্ছন্নতা বিধান হয়, তা-ই হল ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য।
অতএব এ বৈষয়িক জীবনকে অত্যাদিক গরুত্ব দেয়া, বস্তুসর্বস্ব আয়েশ-আরাম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ সম্ভোগে লিপ্ত হওয়া এবং পরকালীন জীবনের অনিবার্য সত্যকে বেমালুন ভুলে যাওয়া কিংবা তা উপেক্ষা করে চলা ইসলামী সংস্কৃতির পরিপন্থী ভাবধারা। পক্ষান্তরে পরকালকে সম্মুখে রেখে-পরকালের কল্যাণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখে আদর্শবাদী জীবন যাপন করা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনের যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদনই হল ইসলামী সংস্কৃতির অনুকূল জীবনাচরণ।
অন্যকথায, আত্মার প্রকৃত কল্যাণ ও তৃপ্তি পরিবর্তে দেহের ক্ষণস্থায়ী আরাম ও তৃপ্তি লাভ ইসলামী সংস্কৃতির লক্ষ্য নয়। তা হল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য। একে কে কথায় বলা যায় ভোগবাদী সংস্কৃতির লক্ষ্য।
তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতিতে বৈষয়িক ও দৈহিক পরিতৃপ্তি কোন স্থান নেই, এটা মনে করাও ভুল। কেননা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দুনিয়ার সর্বপ্রকারের করণীয় কাজ সুসম্পন্ন করা, আল্লাহর দেয়া যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রী ভোগ-ব্যবহার করা এবং তার শোকর আদায় করা ইসলামী সংস্কৃতিরই ঐকান্তিক দাবি। কিন্তু যে ধরণের দৈহিক ও বস্তুগত ভোগ-বিলাস ও আচার-আচরণে আল্লাহর বিধান লংঘিত হয়-আল্লাহর অসন্তোষ উৎক্ষিপ্ত হয়, তা অবশ্যই পরিহার করতে হবে। অন্যথায় বৈষয়িকতা-রূপ দানবের পদতলে দলিত-মথিত ও চূর্ণ-বিচূর্থ হয়ে যাবে ইসলামী সংস্কৃতির সব সুকোমল কুসুম-কলি।
বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতি কোন সংকীর্ণ জিনিস নয়-নয় কোন নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। মানুষের জীবন যত ব্যাপক, ইসলামী সংস্কৃতির ক্ষেত্রও ততই বিস্তীর্ণ। জীবনের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়েই প্রতি মুহূর্ত ইসলামী সংস্কৃতির ভাবধারা সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে, মূর্ত হয়ে ওঠে প্রতিটি কথার মধ্য দিয়ে, ধ্বনি-মর্মরিত হয়ে ওঠে প্রতিটি পদক্ষেপে। বালবের (Bulb) স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎছটা যেমন করে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে ও আলোকোদ্ভাসিত করে তোলে সব কিছু, ইসলামী সংস্কৃতির তেমনি প্রতিফলন ঘটে সমগ্র জীবনে। অনুরূপভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিও সে জীবন-দর্শনের অনুসারী লোকদের প্রতিটি কাজের ভিতর দিয়েই পরিস্ফুট হয়ে থাকে। ফলে প্রতিটি মানুষের কথাবার্তা, কাজকর্ম, চলাফিরা, ওঠা-বসা এবং এই সবের ধরণ, পদ্ধতি ও কর্মকৌশলের মাধ্যমেই জানতে পারা যায় সে কোন্ সংস্কৃতির ধারক।
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, খাবার খাওয়া। খায় সবাই-মানুষ মাত্রই খাদ্য গ্রহণে বাধ্য। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক ‘বিসমিল্লাহ’ বলে খাওয়া শুরু করবে, ডান হাত দিয়ে খাবে, খাওয়ার সময় সে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করবে ও তাঁর শোকরের ভাবধারায় তার অন্তর ভরপুর হয়ে থাকেবে। বাহ্যত সে হাতে ও মুখে খাবে; কিন্তু তার মন তাকে বলতে থাকবে, এ খাবার একান্তভাবে আল্লাহর অনুগ্রহেই পাওয়া গেছে। তিনি না দিয়ে খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা তার পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তাই সে খাবারের প্রতি কোন অবহেলা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করবেনা, অহঙ্কারীর মত বসে খাবেনা এবং খেয়ে মনে কোন অহঙ্কার বা দাম্ভিকতা জাগতে দেবেনা; বরং খাওয়া শেষ করে সে আন্তরিকভাবে বলবেঃ
‘‘সমস্ত শোকর ও তারীফ-প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি আমাদের খাইয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন।’’
খাওয়া মানুষের জীবন ধারণের েক অপরিহার্য কাজ। না খেয়ে কেউ বাঁচতে পারেনা। মানুষকেও খেতে হয়-খেতে হয় জন্তু-জানোয়ারকেও। কিন্তু মানুষের খাওয়া ও গরুর খাওয়া কি একই ধরণের, একই ভাবধারার ও অভিন্ন পরিণতির হবে? তাহলে মানুষ ও পশুতে পার্থক্য থাকল কোথায়? তাই মানুষের মতো খাওয়া এবং খেয়ে মানবোচিত পরিণতি লাভই হল খাওয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতি। পক্ষান্তরে গরুর মতো জাবর কাটা এবং কোনরূপ আত্মিক সম্পর্কহীনভাবে খাদ্য গ্রহণ হল পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিশেষত্ব।
ইসলামী সংস্কৃতিবান ব্যক্তিও পথ চলে, যেমন চলে দুনিয়ার হাজারো মানুষ। কিন্তু তার পথ চলা নিরুদ্ধেশ, দিশেহারা ও লক্ষ্যহীন নয়; পথ চলার সময় তার মনে জাগেনা অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার অস্বাভাবিক ভাবধারা। পথ চলতে গিয়ে আল্লাহর নির্ধারিত সীমাকে সে কখনো লংঘন করেনা। প্রতিটি পদক্ষেপে পথি-পার্শ্বের দৃশ্য অবলোকনে, লক্ষ্য নির্ধারণে এবং সহযাত্রীদের সাথে আচার-আচরণে কোথাও সে মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে হারায় না। হারাম পথে তার পা বাড়ায় না, অন্যায় কাজে সে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ হয় না। পথ চলাকালে সে কোন মুহূর্তে ভুলে যায় না আল্লাহর এ নির্দেশঃ
وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا
‘‘দুনিয়ায় অহংকারী হয়ে পথ চলোনা। কেননা যত অহঙ্কারই তুমি করো না কেন, না তুমি ভূপৃষ্ঠকে দীর্ণ ও চূর্ণ করতে পারবে, না পারবে পর্বতের ন্যায় উচ্চতায় পৌঁছতে।’’ (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ৩৭)
এ কারণে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক যখন পথে বের হয়, তখন তার দ্বারা কারোর কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। সে নিজেকে হাজার মানুষের সমান কাতারে একাকার করে দেয়, নিজের বড়ত্ব দেখাবার মতো কোন কথাও বলেনা-কোন কাজও করে না; তেমন কোন আচার-অনুষ্ঠানকেও সে হাসি মুখে বরণ করে নিতে পারেনা। কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি-বিশ্বাসী লোকের আচার-আচরণ, কথা-কাজ, ভাবধারা ও অনুষ্ঠানাদি হয় এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তার চলার ভঙ্গি দেখে সাধারণ মানুষের মনে ধারণা জাগে, কোন দৈত্য-দানব যেন ছুটেছে সব কিছু দলিত-মথিত করে-সকলের জীবনে অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে। তার এ পথচলায় সাধারণ মানুষের মনে জাগে ভীতি ও আতঙ্ক। আনুষ্ঠানিক সম্বর্ধনা ও ব্যক্তিগত বড়াইসূচক জয়ধ্বনি সে পায় প্রচুর; কিন্তু তাতে আন্তরিকতার খুশবু থাকে না একবিন্দুও।
ইসলামী সংস্কৃতির ধারকও জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যয়ন করবে-শিখবে ও চর্চা করবে। কিন্তু গর্দভের বোঝা বহনের মতো হবেনা তা। তার মাধ্যমে বস্তুর পুতুলনাচে মুগ্ধ হয়ে পুতুল-পূজায় মেতে উঠবেনা সে। বস্তুর বিশ্লেষনে ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদির সন্ধান পেয়ে সে বিস্মিত হবে এবং আল্লাহর অসীম কুদরাতের সামনের নিজেকে করে দেবে বিনয়াবনত। তার কণ্ঠে স্বতঃই উচ্চারিত হবে আল্লাহর প্রশংসাঃ
‘‘কত পবিত্র মহান তুমি হে খোদা কত সুন্দর উত্তম সৃষ্টিকর্তা তুমি! হে খোদা! তুমি কোন একটি বস্তুও অর্থহীন, তাৎপর্যহীন ও উদ্দেশ্যহীন করে সৃষ্টি করো নি!’’
কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতিতে এর বিপরীত ভাবধারার সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। একটা গরুর চোখের পাতায়ও প্রতিফলিত হয় এ পৃথিবীর মনোরম দৃশ্যাবলী, একজন মানুষের চোখেও তাই। কিন্তু মানুষের চোখের প্রতিফলন ও গরুর চোখের প্রতিফলন কি কোন দিক দিয়েই এক হতে পারে? এখানে যে পার্থক্য ধরা পড়ে বস্তু-বিজ্ঞান বিশ্লেষণে, ঠিক সেই পার্থক্যই হচ্ছে ইসলামী সংষ্কৃতি ও পাশ্চাত্য তথা পৌত্তলিক সংস্কৃতির মাঝে।
জীবিকা নির্বাহের জন্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও শ্রম-মেহনত সবাইকে করতে হয়। কিন্তু ইসলামী সংস্কৃতির ধারক এ সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন-কানুন, বিধি-নিষেধ ও বাধ্যবাধকতা মেনে চলে নিজের মনের ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে-ঈমানের তাগিদে। এ সবের মাধ্যমে সে যা কিছু অর্জন করে, তাকে আল্লাহর দান মনের করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার হৃদয়-মন কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তা দিয়ে সে একদিকে যেমন নিজের ও পরিবারবর্গের প্রয়োজন পূরণ করে, সেই সঙ্গে তাতে সমাজের অন্যান্য অভাবগ্রস্থ মানুষেরও প্রাপ্য রয়েছে বলে সে মনে করে। ফলে তার অর্থব্যয়ে এক অনুপম ভারসাম্য স্থাপিত হয়। সে না নিজেকে বঞ্চিত রাখে, না অন্যকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে; বরং সে নিজ থেকেই পৌঁছে দেয় যার হক্ তার কাছে।
সেজন্যে সে কারোর উপর না স্বীয় অনুগ্রহ ও দয়া-দাক্ষিণ্যের বাহাদুরী দেখায়, না তার বিনিময়ে কাউকে নিজের গোলাম বানাতে চেষ্টা করে। তার মনোভাব হয় এই যে, তার একার শ্রম-শক্তিই তা অর্জন করেনি; বরং তাতে আল্লাহর অনুগ্রহও শামিল রয়েছে। (এ শ্রম-শক্তির তো তার নিজস্ব কিছু নয়, তাও তো আল্লাহরই প্রদত্ত) তাহলে তার মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ তার একার ভোগাধিকারের বস্তু হবে কেন? তাতে কেন স্বীকৃত হবেনা আল্লাহর এমন সব বান্দাহদের অধিকার, যারা তার সমান কিংবা প্রয়োজন অনুরূপ উপার্জন করতে পারেনি? …..তাই সে নিজের একারই ভোগ-বিলাস, আয়েশ-আরাম ও সুখ-সজ্জায় তার যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করে নিঃশেষ করে দিতে পারে না; বরং নিজের মধ্যম মানের প্রয়োজন পূরণে ব্যয় করার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে, তা সে তুলে দেবে তারই মত সমাজের হাজারো বঞ্চিত মানুষের হাতে তাদের ন্যায্য অধিকার হিসেবে।
কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের মাঝে সৃষ্টি হয় এর সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারা ও অবস্থা। সেখানে মানুষ অর্থোপার্জনেও ন্যায়-অন্যায় ও হক-না হকের তারতম্য করে না, বাছ-বিচার করেনা ব্যয় করার বেলায়ও। অর্জিত সম্পদ-পরিমাণ তার যা-ই হোকনা কেন-একান্তভাবে মালিকেরই ভোগ্য; তাতে স্বীকৃত হয়না অন্য কারোর একবিন্দু অধিকার। শোষণ, বঞ্চনা ও ব্যায়-বাহুল্যই সে সংস্কৃতির অনিবার্য প্রতিফল। এর প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় সমাজের সর্বদিকে। হিংসা ও বিদ্বেষের প্রচণ্ড আগুন জ্বলে ওঠে বঞ্চিত লোকদের মন-মগজে। তখন তাদের বিরুদ্ধে ধূর্ত শোষকরা আর একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ‘সর্বহারাদের রাজত্বের’ দোহাই দিয়ে এমন এক সমাজ-ব্যবস্থা কায়েম করা হয়, যেখানে এ বঞ্চিত ও সর্বহারাদের চিরদিনের জন্যে বঞ্চিত, নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে থাকতে বাধ্য করা হয়। তখন তারা না পারে তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে, না পারে বিদ্রোহ করে সে সমাজব্যবস্থাকে খতম করতে। ফলে শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতনের অবসান ঘটেনা তার রূপটা বদলে যায় মাত্র। পরিবর্তিত অবস্থায় তার তীব্রতা হয় আরো নির্মম, আরো মারাত্মক এবং মনুষ্যত্বের পক্ষে চরম অবমাননাকর।
যৌন প্রবৃত্তির চরিতার্থতার জন্যে ইসলামী সংস্কৃতির ধারক বিবাহ-সম্পর্ককে একমাত্র মাধ্যম বা উপায়রূপে গ্রহণ করে এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ড এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। এর বাইরে কোথাও বিচরণকে সে সম্পূর্ণ হারাম ও পরিত্যাজ্য মনে করে। তাই হাজারো সম্মুখবর্তী সুযোগ পেয়েও সে নিজেকে দূরে সারিয়ে রাখে-পবিত্র রাখে। কোনক্রমেই সে এ হারাম কাজে নিজেকে কলঙ্কিত ও পথভ্রষ্ট হতে দেয়না। তার মন তার বিবাহিতা স্ত্রী কিংবা স্বামীতেই পরিতৃপ্ত। ভিন্ন মেয়ে বা পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকানোকেও সে ঘৃণা করে। সব মেয়ের ইজ্জত-আব্রুই তার নিকট সম্মানার্হ ও সংরক্ষিতব্য। স্বামী ছাড়া সব পুরুষই তার নিকট হারাম ও পরিত্যজ্য।
কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ধারকদের নিকট বিবাহের বিশেষ কোন দাম, গুরুত্ব বা মর্যাদা নেই। যৌন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্যে নিজের স্ত্রী বা স্বামী কিংবা বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হওয়ার কোন শর্ত নেই। পরস্ত্রী, পরপুরুষ, রক্ষিতা, বন্ধুর স্ত্রী, স্বামীর বন্ধু অথবা স্ত্রীর বান্ধবী ও পুরুষ বন্ধু এসবকে নিজ স্ত্রী বা স্বামীর মত বিবেচনা করতে কোন দ্বিধা বা লজ্জা-শরমের অবকাশ নেই।
এজন্যেই পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে অবিবাহিত যুবকদের মেয়ে-বন্ধু ও অবিবাহিতা মেয়েদের পুরুষ-বন্ধু একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। এর ফলে অবৈধ সন্তানের সংখ্যা যেন ক্রমশ অংকের হিসাবকেও হার মানতে বাধ্য করেছে। [পাশ্চাত্যের কোন কোন ‘উন্নত’ ও ‘সুসভ্য’ দেশে প্রতি পাঁচটি শিশুর মধ্যে তিনটিই অবৈধভাবে জন্মলাভ করছে। আর এটাও ঘটছে জন্মনিরোধের জন্যে সর্বপ্রকার নিরাপদ (?) ব্যবস্থা গ্রহণের পর।- সম্পাদক]। এ সংস্কৃতিতে নারী-পুরুষের যৌন ক্ষুধা উন্মত্ততার সৃষ্টি করে এবং তা যেকোন স্থানে গিয়ে আঘাত হানার অধিকার রাখে; উভয়পক্ষের রাজী হওয়াটাই কেবল সেখানে একমাত্র শর্ত। এ ক্ষুধা এতো ব্যাপক ও প্রবল যে, সমগ্র সমাজ-ব্যভস্থাই যেন তার নির্বাধ পরিতৃপ্তি লাভের আয়োজনে নিয়োজিত। তাই যুবক-যুবতী বা নারী-পুরুষের একক ও যুগল সঙ্গতি-নৃত্য সে সংস্কৃতির এক অপরিহার্য অঙ্গ।
ইসলামী সংস্কৃতি সার্বিকভাবে এক পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ভাবধারার উদ্বোধক। কেননা পরিচ্ছন্ন ও চরিত্রবান মানুষ গড়ে তোলাই তার লক্ষ্য। তাই যেসব কাজ, অনুষ্ঠান ও ভাবধারা এরূপ মানুষ পড়ার পথে বাধার সৃষ্টি করে তা ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। ইসলামের মানুষকে সংস্কৃতির প্রবহমান নদী থেকে স্বচ্ছ পানি সন্ধান করে তুলে নিতে বলছে, অন্ধের ন্যায় ময়লা, আবর্জনা ও কাদাযুক্ত বা বিষাক্ত পানি খেতে বলেনি।
পূর্বেই বলেছি, সর্বদা আল্লাহর স্মরণ এবং সেজন্যে রীতিমত নামায পড়া, কেবল পরকালের কল্যাণ লাভের উদ্দেশ্যে সব কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং নিছক বৈষয়িক আনন্দ বা তৃপ্তি-সুখ লাভের জন্যে কোন কাজ না করাই হল ইসলামী সংস্কৃতির মূল কথা। একারণে ইসলামী সমাজে মসজিদ হল প্রধান সংস্কৃতি-কেন্দ্র- রঙ্গালয় বা নৈশ ক্লাব নয়। ইসলামী সংস্কৃতির ধারকরা দিন-রাত পাঁচবার এখানে একত্রিত হয়ে আল্লাহর স্মরণে দাঁড়ায়, কুরআন পাঠ করে এবং রুকু ও সিজদায় সম্পূর্ণ রূপে অবনমিত হয়ে ইসলামী সংস্কৃতিরই এক বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। বছরের এক মাসকাল রোযা পালন ও দুটি ঈদের নামায ও উৎসব পালন মুসলিম সমাজের সর্বজনীন সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান। বস্তুত আল্লাহর সামনে সমষ্টিগতভাবে অবনমিত হওয়াই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির সামাজিক রূপ।
বিয়ে-শাদীর উৎসব, সন্তানের নামকরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ নির্বাচন, খাদ্য-পানীয় বাছাই, পরীক্ষিত বন্ধু ও আত্মীয় গ্রহণ, রুজি-রোজগারের জন্যে পেশা গ্রহণ, দিন-রাত্রির জীবন অতিবাহন-এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটা আবশ্যক; কেননা তার ব্যাপক প্রভাব থেকে এর একটিও মুক্ত থাকতে পারে না। এ সব ক্ষেত্রেই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব ভাস্বর হয়ে ওঠে। আর এ সব কিছুর মধ্য দিয়েই এ বিশাল মানব-সমুদ্রের মাঝে এক বিশিষ্ট মানব সমাজ গড়ে ওঠে। তাই ইসলামী সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য সূর্যের মতই দেদীপ্যমান এবং তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।
তবে কি ইসলামী সংস্কৃতি কেবল নিরস ও শুষ্ক উপকরণ দিয়ে গড়া? অথচ সংস্কৃতিতে রসের সমাবেশ হওয়া আবশ্যক। রসই যদি না থাকল তা হলে আর সংস্কৃতি কি? সংস্কৃতি হলেও তা দিয়ে আমাদের কি লাভ?
সংষ্কৃতি ‘রস-ঘন’ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, এ কথা ঠিক। কিন্তু রসের তো বিশেষ কোন রূপ নেই। রস আপেক্ষিক। এক ব্যক্তি যেখানে রসের সন্ধান পাবে, অন্যের কাছেও তা-ই যে রসের আকর হবে, এমন কথা জোর করে বলা যায় কি? এক জনের কাছে যা রস, অন্যের নিকট তা বিরসও তো হতে পারে। আসল জিনিস হল মনের তৃপ্তি। যেখানে যার তৃপ্তি, তা-ই তাকে অফুরন্ত রসের যোগান দেয়। এক ব্যক্তি যে সংস্কৃতি গ্রহণ করে, তাতেই সে তৃপ্তি পায়, স্বাদ পায়-পায় আনন্দ ও অমৃত-রসের সন্ধান। ইসলামী সংস্কৃতিতে এ তৃপ্তি, এ স্বাদ, আনন্দ ও রস সৃষ্টি করে আল্লাহর যিকর। তাই কুরআন মজীদ বলেছেঃ
أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
‘‘জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণই মানুষের মনকে পরিতৃপ্ত ও প্রশান্তিময় করে তোলে।’’ (সূরা রা’দঃ ২৮)
মনের তৃপ্তিই যদি কাম্য হয়, লক্ষ্য হয় যদি চিত্তবিনোদন, তা হলে ইসলামী সংস্কৃতিতে রয়েছে তার অপূর্ব সমাবেশ। তবে পার্থক্য হল এই যে, কেউ কাঁচা গোশত খেতে পসন্দ করে, কেউ ভালবাসে প্রচুর মসলা সহযোগে পরিপাটী রূপে রান্না করা গোশত খেতে। আবার এমন খাদকেরও অভাব নেই এ দুনিয়ায়, যারা পচা-গলা ও পুঁতিগন্ধময় গোশতকেও পরম তৃপ্তিদায়ক ও রুচিকর খাদ্য বলে মনে করে এবং তা খাওয়ার সময় স্ফূর্তির ফোয়ারা ছোটাতেও লজ্জাবোধ করে না।
চিত্তবিনোদন ও ইসলামী সংস্কৃতি
ইসলামী আদর্শানুসারী জীবন একটি বিশেষ পদ্ধতিতে চালিত হয়। তাতে যেমন বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনের অবকাশ নেই, তেমনি নেই সংকোচন ও মাত্রা হ্রাসকরণের সুযোগ। শরী’আতের দৃষ্টিতে যা বৈধ, তাকে অবৈধ কিংবা কোন অবৈধকে বৈধ করার ক্ষমতা বা অধিকার কাউকেই দেয়া হয়নি। ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন ভারসাম্যপূর্ণ। কোন দিকের বাড়াবাড়ি বা সীমালংঘন দ্বারা সে ভারসাম্য বিনষ্ট করা সম্ভব নয়।
ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে উদ্দেশ্যহীন জীবন মানুষের গ্রহণযোগ্য নয়। বরং সুনির্দিষ্ট আইন-বিধি ও ব্যবস্থাধীন লক্ষ্যানুগ জীবনই ইসলামের কাম্য। যে জীবনের লক্ষ্য বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তোষ লাভ, ইসলামের দৃষ্টিতে তা-ই সফল জীবন। সে জীবনে খোদার নাফরমানী বা সীমালংঘনের একবিন্দু স্থান নেই। বস্তুত ইসলামী সংস্কৃতিময় জীবন স্থবির, নিষ্ক্রিয় বা অথর্ব নয়। প্রকৃতপক্ষে এই জীবনই সক্রিয়, গতিশীল ও কর্ম-কোলাহলে মুখরিত। এ জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই ইবাদত-বন্দেগীতে অতিবাহিত হয়। এরূপ জীবন যাপন যে বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ জীবন বৈরাগ্যবাদী নয়; কেননা দুনিয়াত্যাগী জীবন কোন মাপকাঠিতেই মানবীয় নয়; দুনিয়ার দ্রব্য-সামগ্রী ও উপাদান-উপকরণ যথাযথভাবে ভোগ-ব্যবহার এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে সব কিছু কুরবানী করাই ইসলামের লক্ষ্য। সাংস্কৃতিক জীবনের স্বল্প ও সীমিত মুহূর্তগুলোকে অর্থহীন আরাম-আয়েস বা প্রবৃত্তির দাসত্বে অতিবাহিত করা জীবনের চরম অবমাননা এবং এটাই হচ্ছে জীবনের চরম ব্যর্থতার নামান্তর মাত্র। ইসলামে হালাল খাদ্য গ্রহণে, হালাল পানীয় পান করায় এবং হালাল পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহারে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়নি। এখানে নিষিদ্ধ হল মাত্রাতিরিক্ততা, অপব্যয়-অপচয়, অপব্যবহার ও অপপ্রয়োগ। কেননা এর ফলে মানব মনে অসুস্থ ভাবধারা ছাড়াও পরিবার ও সমাজ বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়া অবধারিত। এক কথায়, ইসলাম মানুষের বৈষয়িক জীবনে নানাবিধ প্রয়োজন উত্তম পন্থায় ও যথার্থ ভারসাম্য সহকারে পরিপূরণে ইচ্ছুক। কিন্তু জীবনে একবিন্দু বিপর্যয় সূচিত হোক তা বরদাশত করতে ইসলাম প্রস্তুত নয়।
মানুষ ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিটি মুহূর্ত উজ্জীবিত থাকুক, ইসলাম এটাই দেখতে চায়। তার জীবনের একটা মুহূর্তও উদ্দেশ্যহীন কাজে অপচয় হোক, তা ইসলামের কাম্য নয় আদৌ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও সত্য যে, নিরবচ্ছিন্ন কর্মব্যস্ততা মানুষের জীবনের সব রস নিঃশেষে শুষে নিয়ে সেখানে সৃষ্টি করে রুঢ়তা ও রুক্ষতা। তাই চিত্তবিনোদন প্রতিটি মানুষের জীবনে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো অপরিহার্য। কাজের মাঝে চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধা না থাকলে জীবনটাই একটা দুর্বহ বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে অতি স্বাভাবিকভাবেই। তখন জীবনের সব মাধুর্য, হাস্য-রস, আনন্দ-স্ফূর্তি তেলহীন প্রদীপের মতই নিঃশেষ হয়ে যায় অনিবার্য পরিণতিতে। তাছাড়া কর্মের গভীর চিন্তায় নিরন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে থাকলে কর্মশক্তির অবক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। তাই বাস্তব জীবনের দুর্বহ বোঝা সঠিকভাবে বহন করে চলার জন্যে মনকে সব সময় সতেজ, সক্রিয় ও উদ্যমশীল রাখা আবশ্যক। আর তার জন্যে আনন্দ স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদনের নানা উপায় ও মাধ্যম অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত। আনন্দ-স্ফূর্তি ও চিত্তবিনোদন ব্যবস্থার দরুন মানব মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর। এর ফলে জীবনের প্রতি জাগে অপরিসীম কৌতুহল, মমত্ববোধ এবং তদ্দরুন মানুষ স্বীয় দায়িত্ব পালনে বিশেষ উদ্যমশীল হয়ে উঠতে পারে কিংবা অন্তত অল্প সময়ের জন্যে হলেও জীবনের নানাবিধ দুঃখ চিন্তা ও মর্মবেদনা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে পারে, মনের দুঃসহ বেদনা অনেকখানি হালকা করতেও সক্ষম হয়। এতে সন্দেহ নেই যে, মানব জীবন নানা দুঃখ-বেদনা ও আনন্দের সমষ্টি মাত্র। ঘটনা-পরম্পরার ঘাত-প্রতিঘাত মানুষকে কখনো দেয় দুঃখ আর কখনো দেয় আনন্দ। এই হচ্ছে জীবনের বাস্তবতা। একারণে দুঃখ ও দুশ্চিন্তার দুর্বহ ভারটা যদি মানুষের মনের ওপর বেশিক্ষণ চেপে বসে থাকে, তাহলে তা মনস্বত্ত্ব নৈতিকতা ও স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে তার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হতে পারে। পক্ষান্তরে আনন্দের এক পশলা হালকা বারিপাত লোকদের মানস-প্রান্তরে রচনা করতে পারে ফুল ও ফল-ভরা গুল-বাগিচা। বস্তুত হাস্যোৎফুল্ল মনের পক্ষে অধিক কর্মক্ষম হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। আর তারই জন্যে মানুষের জীবনে চিত্তবিনোদনের সামগ্রী যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। অতএব চিত্তবিনোদনও সংস্কৃতিরই এক অপরিহার্য দিক।
ইসলাম মূলগতভাবে চিত্তবিনোদনের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে নি; বরং নির্দোষ হাস্যরস, আনন্দ-স্ফূর্তি ও কৌতুককে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে; কিন্তু এক্ষেত্রেও ভারসাম্যকে উপেক্ষা করতে ইসলাম রাজী হয়নি। মানুষ কেবল আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুল হয়ে থাকবে এবং ভাল-মন্দ নির্বিশেষ সর্ব প্রকারের চিত্তবিনোদনে জীবনে মহামূল্য সময় অতিবাহিত করবে, ইসলাম তা মোটেই পসন্দ করেনি। কেননা তার ফলে মানুষ আল্লাহর যিক্র থেকে গাফিল হয়ে যেতে পারে। আর আল্লাহর যিক্র থেকে গাফিল হয়ে যাওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে নৈতিক ও মানবিক উভয় দিকের চরম বিপর্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যাবে, চিত্তবিনোদনের ব্যাপারটা বহুলাংশেই আপেক্ষিক। কার চিত্ত কিসে বিনোদন করবে আর কিসে হবে দুঃখ-ভারাক্রান্ত সে ব্যঅপারে কোন স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আসল লক্ষ্য হল চিত্তের বিনোদন। এখানে আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব আছে; কিন্তু তা মুখ্য নয়, গৌণ। চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু তার জন্যে ইদানিং যে সব অনুষ্ঠানের আশ্রয় গ্রহণ করা হচ্ছে সাধারণভাবে তা নিশ্চয়ই অপরিহার্য নয়। কেননা চিত্তের বিনোদনের জন্যে তা-ই নয় একমাত্র উপায়। এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও চিত্তের বিনোদন সম্ভব। ইসলাম এ দৃষ্টিতেই চিত্তবিনোদনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে অনুষ্ঠান হিসেবে কেবল তা-ই সমর্থন করেছে যা নির্দোষ-যার পরিণাম ভাল ছাড়া মন্দ নয়, যাতে করে মানুষের নৈতিকতার পতন ঘটার পরিবর্তে উন্নতি সাধিত হয়, যার দ্বারা মনুষ্যত্বের সুমহান মর্যাদা রক্ষা পায়, যার ফলে মানুষ তার উন্নত মর্যাদা থেকে পশুর স্তরে নেমে যায় না। এ ধরণের যা কিছু অনুষ্ঠান ও উপকরণ হতে পারে, তা-ই ইসলামে সমর্থিত এবং মানুষের পক্ষেও তা বর্জন করা কর্তব্য। এই দৃষ্টিতে বর্তমানে চিত্তবিনোদন সামগ্রী বা মাধ্যম হিসেবে গৃহীত কতিপয় অনুষ্ঠান সম্পর্কে খানিকটা বিস্তারিত আলোচনা করা যাচ্ছে।
সিনেমা, টেলিভিশন ও নাট্যাভিনয়
বর্তমান কালে সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে এক সস্তা চিত্তবিনোদন মাধ্যম রূপে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। সিনেমার মূল উপকরণ হল ফিল্ম। ফিল্ম বিদ্যুতের ন্যায়ই এক প্রাকৃতির ও নৈসর্গিক শক্তি। কিন্তু এ নৈসর্গিক শক্তিকে বর্তমানে যে অন্যায় ও অশোভন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হচ্ছে, তা কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। একটা শক্তিশালী প্রচার-মাধ্যম হিসেবে সিনেমা সম্পর্কে কিছু না বললেও ইদানিং সিনেমায় যা কিছু দেখানো হয় সে সম্পর্কে একথা পুরোপুরি প্রযোজ্য। ফিল্মকে বর্তমানে অশ্লীল, নির্লজ্জ ও নৈতিকতা-বিবর্জিত দৃশ্যাবলীর প্রদর্শনীর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাতে যে কাহিনী বা গল্প চিত্রায়িত হয়, তা অবৈধ ভালবাসা ও প্রণয়াসক্তির বিচিত্র গতি-প্রকৃতি ও রোমান্টিক ঘটনা-পরম্পরার আবর্তনে উদ্বেলিত। তা দর্শকদের, বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মন-মগজ ও চরিত্রের ওপর অত্যন্ত খারাপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রূপালী পর্দায় আলো-ছায়ার বিচিত্র ও রহস্যময় খেলায় যা কিছু দেখানো হয়, হুবহু তারই প্রতিফলন ঘটে দর্শকদের চরিত্রে। যা থাকে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, তাকেই ধরতে ছুঁতে ও কল্পনাকে বাস্তবে রূপদান করার জন্যে পাগল-পারা হয়ে ওঠে দর্শকবৃন্দ। এটা যে একান্তই স্বাভাবিক তাতে কারোর এতটুকু সন্দেহ থাকতে পারেনা এবং কেউ এর বিপরীত মতও প্রকাশ করতে পারে বলে ধারণা করা যায় না। [আধুনিক টিভি নাটক, টেলিফিল্ম ও ভিডিও ক্যাসেট সম্পর্কেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার এসব অনুষ্ঠান বহুতর ক্ষেত্রে সিনেমার চেয়েও মারাত্মকভাবে দর্শক চিত্তের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করছে। বিশেষত স্যাটেলাইট চ্যানেলের বদৌলতে আকাশ-সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তৃতি এবং ইন্টারনেট প্রোগ্রামের দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এখন মানবীয় চরিত্র ও নৈতিকতার পক্ষে এক ভয়ংকর ঘাতকে পরিণত হয়েছে। -সম্পাদক]। এ ধরণের দৃশ্যাবলী প্রত্যক্ষ করায় দর্শকদের মধ্যে তাৎক্ষণিক যৌন উন্মাদনা ও দুর্দমনীয় আবেগ-উচ্ছ্বাস সৃষ্টি হওয়াও কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। এ ধরণের কাহিনীকে চিত্রায়িত করার জন্যে প্রথমেই নারী-পুরুষ তথা উদ্ভিন্ন-যৌবন যুবক-যুবতীদের অবাধ মেলামেশা, নগ্নতা-উচ্ছৃংখলতা, অমুহাররম নারী-পুরুষের মধ্যে অন্যায় ও অসত্য সম্পর্ক স্থাপন, নির্লজ্জ অঙ্গভঙ্গি এবং তার পরিণামে পাশবিক আচার-আচরণে অভ্যস্ত হওয়া অবধারিত। কেননা এসব উপাদান ছাড়া কোন ‘রোমান্টিক’ কাহিনীই চিত্রায়িত হতে পারেনা। শুধু তা-ই নয় এক্ষেত্রে নির্লজ্জতা ও পাশবিকতার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি করার দাবি তীব্র হতেও তীব্রতর হয়ে ওঠে। আর দাবি এ দাবি পূরণ নাহলে সিনেমার দর্শকদের সংখ্যাও কমে যায়। যে সিনেমায় এ দাবি পূরণ করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তাকে যে কোন অজুহাতে উপেক্ষা করা হয়। তাছাড়া দর্শকদের যৌন পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সিনেমায় নায়ক-নায়িকার আবেগ উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গন ও চুম্বন-এমনকি (বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে) যৌন মিলনের বাস্তব দৃশ্যের অবতারণা করাও আবশ্যক হয়ে দেখা দেয়। কিন্তু এসব অশ্লীল, গর্হিত ক্রিয়া কর্ম ইসলাম আদৌ সমর্থন করেনা; শুধু তা-ই নয়, কোন সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও রুচিশীল মানুষই তা বরদাশত করতে পারেনা। এগুলো যে মনুষ্যত্বের চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননা, তা কি বলবার অপেক্ষা রাখে?
সিনেমা ও নাট্যাভিনয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে বারে বারে ও ঘনঘন নিজেদের ভূমিকা বদলাতে হয়। বহু রূপে রূপান্তরিত করতে হয় নিজ নিজ ব্যক্তিত্বকে- ব্যক্তি-চরিত্রকে আর তার ফলে তাদের চরিত্র নিজস্ব স্বকীয়তা ও বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে। অতঃপর কেউ আর নিজস্ব কোন চারিত্রিক রূপ আছে বলে দাবি করতে পারেনা। এর ফলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের চরিত্র পুরোপুরি বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যখন প্রতিটি মানুষকে তার আয়ুষ্কালের প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে দায়ী করেছেন এবং কোন মানুষকে তার ব্যক্তি-সত্তার স্বাতন্ত্র্যকে কুরবান করার নির্দেশ দেননি, তখন এ ধরণের কোন কাজ যে তাঁর নিকট পসন্দনীয় হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। অনেক ক্ষেত্রে সৎ লোককে অসৎ লোকের ভূমিকায় ও অসৎ লোককে সৎ লোকের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয় এবং নিজেকে অনুরূপ সাজসজ্জায় ভূষিত করে দর্শকদের সামনে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। এর ফলে তাদের চরিত্রে এক ধরণের কৃত্রিম গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটে অনিবার্যভাবে। এটা মানবতার পক্ষে খুবই মারাত্মক। কেননা এতে মহান স্রষ্টার স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি চরম অবজ্ঞা ও উপহাস করা হয়। একারণে ফিল্মের বর্তমান অন্যায় ব্যবহার বন্ধ করা ছাড়া মানবতার মর্যাদা রক্ষার আর কোন উপায় নেই।
মূলত সিনেমা ও ফটোগ্রাফী গৃহীত হয় নিষ্প্রাণ প্লাষ্টিক ফিতার (Negative Film) ওপর। একে যদি ইতিবাচক শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় তাহলে মানব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হতে পারে। সেটা করা হলে চলচ্চিত্র এমন একটা শক্তি হয়ে উঠতে পারে, যার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষকে শুধু অক্ষর জ্ঞানসম্পন্নই নয়, অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিতদেরকেও উচ্চতর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুসমৃদ্ধ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়। বহু মানুষকে দুনিয়ার সাধারণ জ্ঞান (General Khowledge) এবং নিত্য-নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার-উদ্ভাবনী সম্পর্কে পূর্ণ অবহিতি দিয়ে ধন্য করা যেতে পারে। [সিনেমা বা চলচ্চিত্রকে যে কত চমৎকারভাবে সৃজনশীল ও গঠনমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়, ইসলামী বিপ্লবোত্তর ইরানী চলচ্চিত্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আল্লাহর দেয়া স্বভাব-নিয়মকে কিছুমাত্র বিকৃত না করে এবং ইসলামী শরী’আতের চৌহদ্দীর মধ্যে থেকেই ইসলামী ইরান তার চলচ্চিত্র শিল্পেও এক ইতিবাচক বিপ্লব ঘটিয়েছে, যা মানবতার কল্যাণে অসামান্য অবদান রাখছে।- সম্পাদক]। ইসলামী শরী’আতের দৃষ্টিতে এতে অন্যায় কিছু থাকেনা। এতেও হয়ত প্রাণীর ছবি পর্দায় ভেসে উঠবে; কিন্তু তা দর্পনে প্রতিফলিত প্রতিবিম্বের মতই ক্ষণস্থায়ী। আর দর্পনে প্রতিফলিত ছবি যে নিষিদ্ধ নয় তা সকলেরই জানা কথা। তা সেই ছবি নয়, যা শরী’আতে নিষিদ্ধ।
ছবি অঙ্কন ও প্রতিকৃতি নির্মাণ
প্রাণীর ছবি অঙ্কন বা প্রতিকৃতি (Salute) নির্মাণ ইসলামে নিষিদ্ধ। রাসূলের হাদীসে এ সম্পর্কে কঠিন নিষেধবাণী উচ্চারিত হয়েছে। নিছক চিত্তবিনোদনের খাতিরে এ ধরণের কাজ করা কিছুতেই উচিত হতে পারে না। অবশ্য নিষ্প্রাণ জিনিসের ছবি তোলা বা তার প্রতিমূর্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ নয়। [অবশ্য আধুনিক কালের আলোক চিত্র ও ছবি অঙ্কনের মধ্যে একটা মৌল পার্থক্য বিদ্যমান। ছবি অঙ্কনটা কৃত্রিম ও কাল্পনিক; কিন্তু আলোকচিত্র হচ্ছে একটি বস্তুর হুবহু স্থিরচিত্র। একালের পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াও বহুতরো নিরাপত্তামূলক কাজে আলোকচিত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।- সম্পাদক]। তাতে দোষেরও কিছু নেই। এরূপ কাজে বরং ড্রয়িং ও প্রকৌশল বিদ্যার যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে। ইসলামে প্রতিমূর্তি নির্মাণ- বর্তমানে যাকে বলা হয় ভাস্কর্য- শুরু থেকেই নিষিদ্ধ এবং অন্যায় বলে চিহ্নিত। নবী ও রাসূলগণ এরূপ কাজের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন। মুসলিম জাতি প্রথম দিন থেকেই মূর্তিভাঙা জাতি নামে পরিচিত। কাজেই প্রতিমূর্তি নির্মাণ কোন মুসলমানের কাজ হতে পারেনা, আধুনিক শিল্পকলার দৃষ্টিতে তার যত বেশী মর্যাদাই স্বীকার করা হোক-না কেন। একটি মূর্তি-পূজক জাতির পক্ষেই এটা শোভা পায়। ইসলামে মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ এজন্যে যে, এটা শিরকের উৎস আর শিরক ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শ। যে সমাজে শিরক অনুষ্ঠিত হয়, সে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে সংক্রামক ব্যধির মতোই এই রোগ সংক্রমিত হয় এবং সকলকে মুশরিক বানিয়ে ছাড়ে। এই কারণ অল্প সময়ের তরে বা শিল্প-কলার খাতিরেও এই কাজকে বরদাশত করা যেতে পারে না। ইসলামী সমাজের আদর্শ পুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর জাতির মূর্তি খামারের সব ক’টি মূর্তিই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন। আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কা বিজয়ের পর কা’বা ঘরে অবস্থিত তিনশ’ ষাটটি মূর্তিকে বাইরে নিক্ষেপ করে ঘোষণা করেছিলেন- ‘‘সত্য এসেছে, মিথ্যা ও অসত্য নির্মূল ও বিলীন হয়ে গেছে।’’
তাই মূর্তি নির্মাণের কাজ তওহীদ বিশ্বাসীদের পক্ষে কোনরূপ গৌরবজনক হতে পারে না, কাল বিবর্তনে তার নাম যাই হোক-না কেন। প্রকৃতপক্ষে একাজ মানবতার ললাটে কলঙ্ক টিকামাত্র। আধুনিক Finearts (ললিতকলা) ও Sclupture (ভাস্কর্যবিদ্যা)- এ এইসব পঙ্কিল ভাবধারা পুরোমাত্রায় স্থান পেয়েছে। আসলে মূর্তি-পূজার প্রাচীনতম ভাবধারা আধুনিক যুগে ভাস্কর্য শিল্পের ছদ্মাবরণে শিরককেই সংস্থাপিত করতে চাচ্ছে। শিল্পকে এই শিরকী ভাবধারা থেকে মুক্ত ও পবিত্র করা ইসলামী সংস্কৃতিবানদের কর্তব্য।
তাস, দাবাখেলা ও জুয়া
বর্তমানকালে তাস, দাবা খেলা ও জুয়ায় মত্ত হয়েও বহু মানুষ অবসর বিনোদন করে এবং এসব খেলার মাধ্যমে আনন্দ লাভ করে। অনেকে এসব খেলায় মেতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ, পরকালের চেতনা ও শরী’আতের অনুসরণ, ঘর-সংসার ও যাবতীয় দায়-দায়িত্বের কথা বেমালুন ভুলে থাকতে চাইছে। তাদের সামনে জীবনের কোন বৃহত্তর বা মহত্তর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে পারেনা। কোন প্রকার আনন্দ-স্ফূর্তিতে মশগুলে হয়ে জীবনের মহামূল্য মুহূর্তগুলো কাটিয়ে দেয়ার এই প্রয়াস মানব সমাজের জন্যে অত্যন্ত মারাত্মক। তাস ও দাবা খেলায় চিন্তাশক্তি সূক্ষ্ণতা লাভ করে বলে দাবি করা হয়; কিন্তু একথা কোন নির্বোধ ব্যক্তির পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব। এতে বরং জীবনের মহামূল্য সময়ের অকারণ অপচয় ঘটে। যে জাতির বেশীরভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত সে জাতি ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ও সমস্যা-সংকুল এই জগতে কখনও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। প্রতিযোগিতায় পরাজিত হওয়া ও শেষ পর্যন্ত বিশ্ব পটভূমি থেকে চিরবিদায় গ্রহণই হয় সে জাতির ললাট-লিখন। ইদানীং লটারীসহ নানা ধরণের জুয়াকে এদেশে সরকারীভাবেই উৎসাহিত করা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জুয়া খেলা হচ্ছে অন্যায়ভাবে অর্থলুণ্ঠন কিংবা অসতকর্তার মধ্যে নিজের সর্বস্ব খুইয়ে সবর্হারা হওয়ার একটা কাযর্কর মাধ্যম। ইসলামে এ কারণেই সবর্প্রকার জুয়া নিষিদ্ধ। বিশাল মোগল সম্রাজ্য ও অযোধ্যার মুসলিম রাজত্বের নিমর্ম পতন ঘটার মূলে এই জুয়া খেলা যে প্রধান কারণ তা ঐতিহাসিকভাবেই সত্য।
নাচ-গান ও বাদ্য-যন্ত্র
নৃত্য-সঙ্গীত ও বাদ্য-যন্ত্রের সূর মুর্ছনা বর্তমান সমাজে চিত্তবিনোদনের আকর্ষণীয় উপকরণরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত। বিশেষভাবে শিক্ষা-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী যুবতীরাই সাধারণত নাচ-গানের আসরে নামে। নৃত্যহীন সঙ্গীত অথবা নিঃশব্দ নৃত্য দুটিই বর্তমান কালের সংস্কৃতিচর্চার বিশেষ মাধ্যম। নৃত্যসঙ্গীত মূলত ত্রয়ার্থবোধক। তাতে রয়েছে গীত, বাদ্য ও নৃত্য। এ তিনটির সমন্বয়েই নৃত্য-সঙ্গীত। স্বতন্ত্রভাবে নাচ ও গানের বিশ্লেষণ করা হলে এর আসল রূপটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।
গান মিষ্টি কণ্ঠের সুমর্জিত সুর-ঝঙ্কার। তার স্বাভাবিক আকর্ষণ তার সুরের ও তালের মধ্যে নিহিত। বিশেষ মানে ও ভঙ্গিতে কণ্ঠধ্বনির উত্থান-পতন লয় তথা ছন্দই হচ্ছে গান। শ্রোতৃবৃন্দ এ সুর-মূর্ছনায় মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে যায়। তাদের কর্ণকূহরে যেন মধুবর্ষণ হয়। গানের এ সুর-তরঙ্গে থাকে এক প্রকারের মাদকতা। শ্রোতাকে তা মাতাল করে দেয়। অনেকে আবার গানের সুরেই সন্তুষ্ট বা তৃপ্ত নয়। গান যার কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে-গলে গলে নিঃসৃত হচ্ছে যার কণ্ঠনালী দিয়ে এ মধুর সুর-ঝংকার তার প্রতি-তার অবয়বের প্রতিই শ্রোতাদের আকর্ষণ সর্বাধিক [সঙ্গীত শিল্পীর কণ্ঠের ন্যায় তার রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি শ্রোতাদের এই আকর্ষণ সম্পর্কে খোদ শিল্পীও থাকে সচেতন। তাই সঙ্গীত পরিবেশনের সাথে সাথে নিজের দেহ প্রদর্শনের ব্যাপারেও শিল্পীকে অত্যন্ত সচেষ্ট দেখা যায়। -সম্পাদক]। কণ্ঠস্বর ও অবয়ব উভয়ই যদি মনোমুগ্ঘকর ও চিত্তাকর্ষক হয়, তাহলেই সোনায় সোহাগা। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতে এই দুটিই মানুষ ও মনুষ্যত্বের জন্যে বিষের মতো সংহারক। বিষ দেহকে হত্যা করে, জীবনের অবসান ঘটায় আর নাচ মন্যুত্বকে করে পর্যুদস্ত। কেননা শুধু হাত-পা নাড়ানোই নৃত্য নয়। নাচের মুদ্রা প্রয়োগের সাথে সাথে দেহ যখন কথা কয়, তখনই নাচ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আর নৃত্যের তালে তালে দেহ কথা বলে ওঠে তখন যখন অঙ্গ-ভঙ্গি দেখে ক্ষুধাতুর দর্শকবৃন্দ তা ধরবার ও মন্থন করবার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে আর এই অবস্থাটাই ইসলামের দৃষ্টিতে বর্জনীয়। কেননা এর পরবর্তী পর্যায়ই হচ্ছে যৌন মিলনের পিয়াসার আস্বাদন। এতে যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা নিঃসন্দেহ; কিন্তু সে সংস্কৃতি পশুপালের, মানুষকুলের নয়। যুবক-যুবতীর যুগল বা দলবদ্ধ নৃত্য যৌন-কাতর চিত্তেরই বিনোদন করে। যে চিত্তে খোদার যিক্র নিহিত, তার কাছে এ বিনোদন শুধু বিরক্তিরই নয়, অসহ্যও।
নৃত্য ও সঙ্গীতের এ অনুষ্ঠানের উৎপত্তি পৌত্তলিকদের দেব-মন্দিরে পূজার আরতি দানের আত্মনিবেদেনে। তা যখন সাংস্কৃতির অনুষ্ঠান রূপে মঞ্চে উপস্থাপিত, তখন শ্রোতৃবৃন্দই হয় তার দেবতা এবং গান ও নৃত্যের মাধ্যমে যুবতী নারী শিল্প তাদের নিকট করে আত্মনিবেদন। বিদেশী ও বিধর্মীদের প্রায় দু’শ বছরের গোলামীর যুগে এসব জিনিস মুসলিম সমাজে-বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেননা সেকালের শিক্ষা, সমাজ ও পরিবেশ থেকেই এর সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। ফলে মুসলিম সমাজে এমন সব লোক জন্মেছে যারা মনে করে সঙ্গীত, যুগল নৃত্য ও সহ-অভিনয়ে কোন দোষ নেই। ব্যক্তি চরিত্র ও আদর্শবাদের চরম বিপর্যয়ই যে এর একমাত্র কারণ, তাতে সন্দেহ নেই।
নারী কণ্ঠের সুরেলা ঝংকার ভিন পুরুষের মাঝে যৌন স্পৃহার উদ্বেলিত তরঙ্গ মালার সৃষ্টি করে, সে কথা সবাই জানে-সবাই বুঝে। এ জন্য নবী করীম সা. সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ
‘‘সঙ্গীত ব্যভিচারের তুলনায় অধিক মারাত্মক।’’
কেননা গান-বাদ্য-নৃত্যের মাদকতা মানুষের মন-মগজকে সহজেই বিভ্রান্ত করে। তাতে জাগিয়ে দেয় এক ধরণের আবেশ-আসক্তি। যার অনিবার্য পরিণতি হল নৈতিক বন্ধনের শিথিলতা আর তারই পরবর্তী পর্যায় হচ্ছে নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি। [অনেক ক্ষেত্রেই এ ‘পরিতৃপ্তি’ সহজে অর্জিত হয় না বলে তা লোকদেরকে নারী ধর্ষণসহ নানা গুরুতর অপরাধের জন্যে প্ররোচিত করে। এমনকি, অনেক হত্যাকাণ্ডের পিছনে কাজ করে এই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা। -সম্পাদক]।
কুরআন মজীদে সঙ্গীত-গান-বাজনা-নৃত্যকে ‘লাহওয়াল হাদীছ’ বলা হয়েছে। এর শাব্দিক অর্থ হল এমন কথা, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, দায়িত্ব ও কর্তব্যে তাকে গাফিল ও অসতর্ক বানিয়ে দেয়। নিরপেক্ষ ও অনাসক্ত মন-মানসিকতা নিয়ে যারা এ জিনিসের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবেন তারাই কুরআনের এ ঘোষণার যথার্থতা ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে সক্ষম হবেন। সুসজ্জিত ও মনোরম দৃশ্য সমন্বিত রঙ্গমঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় ডুবে রঙ-বেরঙের তরঙ্গের তালে তালে সুন্দরী যুবতী তথা উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারী পুরুষ যখন কণ্ঠে কণ্ঠ ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ও হাতে হাত ধরে এবং প্রয়োজনে বুকে বুক মিলিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্যের মূর্ছনার সৃষ্টি করে, তখন দর্শককূল যে সম্পূর্ণরূপে বিভোর, আত্মহারা ও দ্বিগিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে যায়, তাদের ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলোপ ঘটে, সুস্থ অনুভূতিসম্পন্ন কোন মানুষই তা অস্বীকার করতে পারেনা। তাই এসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে কুরআন-হাদীসের ঘোষণাবলীর সত্যতার ও যৌক্তিকতা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আসলে এগুলো হচ্ছে মানুষের মনুষ্যত্ব, রুচিবোধ ও নৈতিকতা ধ্বংস করার এক সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। সত্যিকার ঈমান ও বলিষ্ঠ ইসলামী চরিত্র দিয়েই এ ষড়যন্ত্রজাল ছিন্ন-ভিন্ন করা যেতে পারে, অন্য কিছু দিয়ে নয়।
মনে রাখা আবশ্যক, এখানে যা কিছু বলা হল, তা আনুষ্ঠানিক ও প্রকাশ্য উন্মুক্ত মঞ্চস্থ নৃত্য ও সঙ্গীত সম্পর্কে প্রযোজ্য। কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পর্যায়ে, …..একান্তভাবে মেয়েদের পরিবেশে কেবল মেয়েরাই এবং পুরুষদের মজলিসে কেবল পুরুষরাই কোনরূপ আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই যদি ভাল অর্থপূর্ণ গান গায় এবং তাতে নিষিদ্ধ বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তাতে উপরোক্ত দোষত্রুটি থাকেনা বলেই তা নিষিদ্ধ নয়-দোষনীয় নয় যদি ছোট ছোট মেয়েরা শৈশবকালীন খেলা-তামাশায় মেতে গিয়ে নিজস্বভাবে তেমন কিছু করে। নবী করীম সা. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ে এ ধরণের জাঁক-জমকহীন অনুষ্ঠানকে নিষেধ করেন নি –নিষেধ করেননি উষ্ট্র চালকের একক মরু সঙ্গীতকে। তাই নিষিদ্ধ নয় মাঝির নিরহঙ্কার ও বাদ্যযন্ত্রহীন ভাটিয়ালী সুরের গান, চাষীর আবেগ-বিধুর কণ্ঠের চৈতালী সুর।
পূর্বেই বলেছি, ইতিহাসের পৃষ্ঠার খোঁজ করলে জানতে পারা যাবে যে, নৃত্য-সঙ্গীত তথা গান ও নাচ সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক রূপ পেয়েছে আদিম কালের দেব-দেবীর পূজা-উপাসনায় ও তাদের উদ্দেশ্যে আত্মনিবেদনের অনুষ্ঠানে। ভজন নৃত্যের তালে তালে দেবতার সামনে আত্মসমর্পণ হিন্দেুদের পূজা-অর্চনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। খৃস্টানদের অর্কেস্ট্রা (Orvhestra) তাদের শির্ক-পঙ্কিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামান্তর। ইসলামে তা অনিবার্য কারণেই নিষিদ্ধ। যদিও মিষ্ট কণ্ঠধ্বনিতে কুরআন মজীদ পাঠ শুধু জায়েজই নয়, প্রশংসনীয়ও; কিন্তু তার সাথে সঙ্গীতের তাল-লয় ও সমবেত সুরের সংমিশ্রণ সম্পূর্ণ হারাম।
সুরাপান
সুরাপান কুরআনের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট হারাম এবং তা মারাত্মক অপরাধ-কবীরা গুনাহ। কিন্তু চরিত্রহীন লোকেরা নিছক চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে সুরা পান করে থাকে। এ প্রতিক্রিয়ায় তাদের মন-মগজে গুনাহর অনুভূতিটুকু জাগেনা। বস্তুত সুরা হল সব রকমের অশ্লীলতা, চরিত্রহীনতা ও অপরাধপ্রবণতার মৌল উৎস। শরী’আতের দৃষ্টিতে তা পান করা, পান করানো, তৈরী করা এবং বিক্রয় ও পরিবেশ করা অকাট্যভাবে হারাম। কেননা সূরা পানের ফলে পানকারীর জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-শক্তি সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে যায়। তার কাছে মা-বোন, ঔরসজাত কন্যা ও স্ত্রীর মধ্যে কোন পার্থক্যবোধ অবশিষ্ট থাকেনা। স্নায়ুবিক দিক দিয়ে উচ্ছ্বাস-বিজিত হয়ে যায়। ফলে জাতির চরিত্র, মূল্যবোধ ও অর্থনীতির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয় [সুরা বা মদ হচ্ছে মাদক জাতীয় দ্রব্যের একটি প্রকরণ মাত্র। একালে বিভিন্ন নামে এর আরো অনেক প্রকরণ চালু হয়েছে, তার মধ্যে গাঁজা, চরস, হিরোইন, ফেনসিডিল ইত্যাদি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মানব জীবনের এগুলোর প্রতিক্রিয়া খুবই ভয়াবহ। পবিত্র কুরআন ‘খাম্র’ শব্দ দ্বারা এর সবগুলো প্রকরণকে একত্রে ‘শয়তানের কাজ’ আখ্যায়িত করে চিরতরে হারাম করে দিয়েছে। -সম্পাদক] । অনেকে সুরাকে একটা সাধারণ পানীয়ই মনে করে। এজন্যে এ ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ। এ মারাত্মক পরিণতির কথা তারা চিন্তা ও বিবেচনা করতেই প্রস্তুত নয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সুরা একটা পানীয় বা নিছক চিত্তবিনোদন উপকরণ মাত্রই নয়। আসলে সুরা একটা সংস্কৃতি, একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতার ভিত্তি। এমন কি, তা একটা জীবন পদ্ধতিও এবং তা কোনক্রমেই ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামী সভ্যতা ও ইসলামী জীবন পদ্ধতির মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে না। সুরা পানের অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে ন্যায়-অন্যায় বোধের বিলুপ্তি, নারী-পুরুষের অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং সঙ্গে জড়িত থাকবে অপরাধপ্রবণতা, বিশেষত নরহত্যা বা রক্তপাত। তার ফলে গোটা সমাজ ও জাতিই চরম ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়াতে বাধ্য।
বস্তুত মনের স্বস্তি-প্রশান্তি-স্থিতি ও পবিত্রতা-পরিচ্ছন্নতাই হচ্ছে ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা। আল্লাহ, রাসূল ও পরকালের প্রতি অকৃত্রিম ও ঐকান্তিক বিশ্বাস এবং তদভিত্তিক ও তদনুকূল অনুষ্ঠানাদিই তার চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যম। ইসলামী অনুষ্ঠানাদি মানুষকে মূর্খতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি দেয়। তাদের অন্তরে জাগিয়ে তোলে খোদাভীতি, পরকালের জবাবদিহি এবং জীবনের প্রতিপদে, প্রতি ক্ষেত্রে রাসূলে অনুসরণের সুদৃঢ় ভাবধারা।
সংস্কৃতি ও নৈতিকতা
ইসলামী সংস্কৃতির দৃষ্টিতে নৈতিকতা গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবেও নৈতিকতার এ গুরুত্ব সর্বকালে ও সর্ব সমাজে স্বীকৃত। সুদূর অতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সকল চিন্তাবিদ ও দার্শনিকই নৈতিকতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর দুনিয়ার তাবৎ ধর্মসমূহের ভিত্তিই রচিত হয়েছে এই নৈতিকতার ওপর এবং সে কারণে প্রত্যেক ধর্মই তার অনুসারীদের জন্যে অলংঘনীয় নৈতিক নিয়ম-বিধান পেশ করেছে। কেননা ধর্মের দৃষ্টিতে মানবজীবনের সাফল্য এই নৈতিকতার ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। উপরন্তু দুনিয়ার শান্তি, স্বস্তি, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, প্রগতি ইত্যাদি নির্বিঘ্নতা, নিরাপত্তা ও নৈতিকতা ছাড়া আদৌ সম্ভবপর নয়। এটা অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। যে ব্যক্তি বা জাতি উত্তম ও নির্মল চরিত্রগুণে গুণান্বিত সে-ই সর্বপ্রকার কল্যাণ ও খোদায়ী রহমত ও বরকত লাভের অধিকারী। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বা জাতি তা থেকে বঞ্চিত তার পক্ষে কল্যাণ লাভ তো দূরের কথা, কালের ঘাত-প্রতিঘাতে টিকে থাকাই অসম্ভব; কেননা সামাজিক ও তামাদ্দুনিক শঙখলা কেবলমাত্র উত্তম নৈতিকতার দরুণই সংরক্ষিত হতে পারে আর তা না থাকলে সে শৃঙ্খলা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়ে গোটা সমাজের উচ্ছৃংখলতা ও অরাজকতার অতল গহ্বরে নিপতিত হওয়া একান্তই স্বাভাবিক। সমাজতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস-দার্শনিক আল্লামা ইবনে খালদুনের দৃষ্টিতে জাতিসমূহের উত্থান ও পতনের মূলে নিহিত আসল নিয়ামক হচ্ছে এই নৈতিকতা। তিনি লিখেছেনঃ
‘‘আল্লাহ তা’আলা যখন কোন জাতি, বংশ-গোষ্ঠী বা দলকে দেশ-নেতৃত্ব ও রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব দিয়ে মহিমান্বিত করতে চান, তখন সর্বপ্রথম তার নৈতিক অবস্থার সংশোধন করে নেন আর তারপরই এই মর্যাদা তাকে দান করেন। অনুরূপভাবে কোন জাতি, গোষ্ঠী বা দলের হাত থেকে এই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব যদি কেড়ে নেবার সিদ্ধান্ত করেন, তাহলে পূর্বেই তাকে চরিত্রহীনতা ও দুরাচারে উদ্বুদ্ধ করে দেন। তার মধ্যে এনে দেন সব রকমের দুষ্কৃতি, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলতা আর অন্যায় ও খারাপের পথে তাকে বানিয়ে দেন দ্রুত অগ্রসরমান। এরই ফলে সে নেতৃত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রশাসনিক যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তার শাসন-দণ্ড শক্তিহীন হয়ে ক্রমশ তার হস্তচ্যুত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আসল শাসন ক্ষমতাই তার হাতে থেকে চলে যায় আর তার স্থানে অন্যরা ক্ষমতাসীন হয়ে বসে (মুকাদ্দমা)।’’
দুনিয়ার প্রতিটি ব্যক্তিই তার জীবনে সাফল্য লাভের অভিলাষী। এই অভিলাষ কেবল মাত্র দুটি জিনিসের সাহায্যেই সাফল্যমণ্ডিত হতে পার। একটি হল আল্লাহর প্রতি দুঢ় ঈমান আর দ্বিতীয়টি হল সদাচার ও শুভ কর্ম। অন্যকথায়, জীবন ও জগত সংক্রান্ত মৌলনীতি ও বিশ্বাসসমূহের প্রতি অবিচল প্রত্যয়েরই অপর নাম ঈমান আর তদনুযায়ী বাস্তব কাজই হল শুভ কর্ম, সদাচার বা নেক আমল। জীবনের সাফল্যের জন্যে এ দুটির সমন্বয় অপরিহার্য। ইসলাম মানুষের মুক্তি এ দুটি জিনিসের ওপর ভিত্তিশীল করে দিয়ে এ তত্ত্বেরই বাস্তবায়ন চেয়েছে। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি অবিচ্ছেদ্য-ওতপ্রোত জড়িত। তবে ঈমান হল ভিত্তি আর নেক আমল হল তার ওপর গড়ে ওঠা প্রাসাদ। ঈমান হল বীজ আর নেক আমল হল সেই বীজ থেকে অঙ্কুরিত বিরাট মহীরুহ। ‘নেক আমল’ এক বিরাট ও বিশাল তাৎপর্যমণ্ডিত বিশেষ পরিভাষা। মানব জীবনের সব রকমের কাজই এর অন্তর্ভুক্ত। তা সত্ত্বেও একে দুটি ভাগে বিভক্ত করা চলে। একটি ভাগের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সঙ্গে আর অপর ভাগটির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হচ্ছে মানুষ তথা সৃষ্টিকুলের সঙ্গে। প্রথমটির প্রচলিত নাম ‘ইবাদত’ আর দ্বিতীয়টিকে বলা যায় ‘মুআমিলাত’। দ্বিতীয়টিকেও দু’ভাবে ভাগ করা যেতে পারে। তার কতকগুলো হচ্ছে মানবীয় কর্তব্য বিশেষ, যাকে বলা হয় আখলাক বা নৈতিকতা আর অন্যগুলো আইনগত দায়িত্ব পর্যায়ের। সাধারণত একেই বলা হয় মু’আমিলাত।
এই ইবাদাত ও নৈতিকতার সমন্বয়েই ইসলামী জীবন বিধান গঠিত। এ দুটি বিষয় ইসলামী জীবন বিধানের দুটি বাহু বিশেষ। তাই এর কোনটিরই গুরুত্বকে কিছুমাত্র হালকা করে দেখা যেতে পারে না। নিছক ইবাদত মানুষকে পূর্ণ মুসলমান বানাতে পারে না যেমন, তেমনি এককভবে শুধু নৈতিকতাও তা সম্পাদন করতে অক্ষম। কুরআন মজীদ এ সত্যকে যথার্থ মর্যাদা দিয়েছে। তাতে যেখানেই ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই বলা হয়েছে শুভ কর্ম ও সদাচার তথা নৈতিকতা অবলম্বনের কথা-বলা হয়েছে সমান গুরুত্ব সহকারে। নিম্নোদ্ধৃত আয়াতটি লক্ষ্যনীয়ঃ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
‘‘হে ঈমানদার লোকেরা! ঈমান আন, রুকূ দাও, সিজদা করো এবং তোমাদের রব্ব-এর দাসত্ব ও বন্দেগী করো আর যাবতীয় ভালো ভালো কাজ সুসম্পন্ন কর; তা হলেই তোমাদের কল্যাণ লাভ সম্ভব।’’ (সূরা হজ্বঃ ৭৭)
বিশ্বনবীর এ দুনিয়ায় আগমণের উদ্দেশ্য ছিল মানব জাতিকে নৈতিক বিধান, কর্মনীতি ও আদর্শবাদিতা শিক্ষা দেয়া এবং এই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আদর্শ মানুষ তৈরী করা, চরিত্রবান মানুষকে খোদানুগত-খোদার বন্ধু বানিয়ে দেয়। নবী করীম সা.-এর আগমণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেছেনঃ
هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
‘‘সেই মহান আল্লাহ্ই নিরক্ষর লোকদের ভেতর তাদের মধ্য থেকেই একজনকে রাসূল রূপে পাঠিয়েছেন। সে রাসূল তাদের সামনে আল্লাহর নিদর্শন ও বাণীসমূহ তুলে ধরবে, তাদেরকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন করবে এবং তাদেরকে কিতাব ও সুষ্ঠু জ্ঞান-বু্দ্ধি শিক্ষা দিবে।’’ (সূরা জুম’আঃ ২)
কোন কোন বিশেষজ্ঞের মতে এখানে ‘হিকমত’ শব্দের অর্থ হচ্ছে চরিত্র বা নৈতিকতা। ইসলাম চরিত্রের গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা নিম্নোদ্দৃত আয়াত থেকে আরও সুস্ষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।
সূরা আহযাবে বলা হয়েছেঃ
لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
‘‘আল্লাহর রাসূলে মধ্যে তোমাদের জন্যে অতীব উত্তম আদর্শ রয়েছে, এতে কোনই সন্দেহ নেই।’’ (আয়াত ২১)
সূরা ক্বালামে বলা হয়েছেঃ
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ
‘‘নিশ্চয়ই তুমি চরিত্রের অতীব উচ্চ মানে অভিষিক্ত।’’ (আয়াত ৪)
স্বয়ং রাসূলে করীম সা. ও ইরশাদ করেছেনঃ
‘‘অতীব সুন্দর ও নির্মল চরিত্রকে পূর্ণ পরিণত করার উদ্দেশ্যেই আমি প্রেরিত হয়েছি।’’
তিনি আরো বলেনঃ
‘‘উত্তম গুণাবলীকে পূর্ণত্ব দানের উদ্দেশ্যেই আমাকে পাঠানো হয়েছে।’’
রাসূলে করীম সা.-এর এই সব উক্তি থেকে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হয় যে, চরিত্রেরই অপর নাম হচ্ছে ইসলাম আর দ্বীন-ইসলামের সমগ্র বিষয়ই হচ্ছে উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর উৎস।
এ পর্যায়ে রাসূলে করীম সা.-এর আরও কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ
১. তোমাদের মাঝে ঈমানের বিচারে পূর্ণ মুমিন সে, চরিত্রের বিচারে তোমাদের মাঝে যে উত্তম ব্যক্তি।
২. তোমাদের মাঝে সৎ সেই ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে তোমাদের সকলের তুলনায় ভাল।
৩. কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাহর পাল্লায় উত্তম ও ভাল চরিত্র অপেক্ষা অধিক ভারী জিনিস আর কিছু হবে না।
৪. জান্নাতের উচ্চ পর্যায়ে একখানি ঘর তাকে দেয়ার দায়িত্ব আমি গ্রহণ করেছি, যে নিজের চরিত্রকে উত্তম ও নিষ্কলুষ বানাবে।
৫. কিয়ামতের দিন তোমাদের মাঝে আমার প্রিয়তর ও নিকটতর হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে। আর আমার অপসন্দনীয় ও কিয়ামতের দিন আমার থেকে দূরবতীয় হবে সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মাঝে খারাপ চরিত্রের অধিকারী।
৬. একবার নবী করীম সা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলঃ জান্নাতে কোন্ জিনিসটি সবচেয়ে বেশী প্রবেশ করবে? জবাবে নবী করীম সা. বললেনঃ তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র।
৭. আমানত রক্ষাকারী ও সত্যনিষ্ঠ মুসলমান কিয়ামতের দিন শহীদদের সঙ্গী হবে।
৮. মানুষ উত্তম চরিত্রগুণে এমন মর্যাদা লাভ করতে পারে যা সারাদিন রোযা রেখে ও সারা রাত ইবাদত করেই লাভ করতে পারে।
৯. উত্তম চরিত্রেরই অপর নাম হচ্ছে দ্বীন।
১০. শুভ চরিত্র ইবাদতের অপূর্ণতা ও অপর্যাপ্ততার ক্ষতিপূরণ করে। কিন্তু চারিত্রিক দুর্বলতার ক্ষতি ইবাদত দ্বারা পূরণ হয় না। মানুষ তার শুভ চরিত্রের বলে জান্নাতের উচ্চতর ও উন্নততম মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে যদিও সে একজন ‘আবেদ’ নামে পরিচিত হয় না। আর নিজের চরিত্রহীনতার কারণে দোজখের সর্বনিম্ন অংশে পৌঁছে যায়, যদিও সে একজন ইবাদতকারী ব্যক্তি রূপে পরিচিত।
১১. প্রতিটি জিনিসেরই একটা ভিত্তি থাকে আর ইসলামের ভিত্তি হচ্ছে শুভ চরিত্র। [ইবনে আব্বাস রা.]
১২. লোকদের সাথে ভাল চরিত্র নিয়ে মেলামেশা কর এবং (খারাপ) কাজের দরুনই তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হও। [হযরত উমার রা.]
১৩. চরিত্রের বিশালতা ও উদারতায়ই নিহিত রয়েছে জীবিকার সম্ভার।
১৪. চারটি জিনিস মানুষকে উচ্চতর মর্যাদায় পৌঁছে দেয়-যদিও তার আমল ও জ্ঞান-বিদ্যা কম আর তা হলঃ ধৈর্য-সহিষ্ণুতা, বিনয়, দানশীলতা ও শুভ চরিত্র। (হযরত জুনাইদ বাগদাদী)
১৫. চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ও সৌন্দর্য মানুষের স্বভাবগত গুণাবলীকে পূর্ণমাত্রায় উৎকর্ষ দান করে, লোকদের অন্তরে মমতা ও ভালবাসার বীজ বপন করে এবং আল্লাহ তা’আলার নিকটতর করে দেয়। (ইমাম গাজ্জালী)
চরিত্র ও ঈমান
মুসলমান হওয়ার প্রথম ও মৌল শর্ত হল ঈমান। কিন্তু ঈমান মন-মানস ও হৃদয়-মনের একটা বিশেষ অবস্থা ও ভাবধারা এবং প্রচ্ছন্ন অন্তর্নিহিত ব্যাপার। আল্লাহ্ ছাড়া তার অস্তিত্ব ও অবস্থা সম্পর্কে কেউই অবহিত হতে পারেনা। এই কারণে আল্লাহ তা’আলা সৎ ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রকে মুমিনের ঈমানের মানদণ্ড রূপে নির্ধারিত করেছেন। ইমাম গাজ্জালীর মতে ইসলামের ঈমানের সাথে চরিত্রের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ও নিবিড়। মানব-মনে হীন, নীচ ও অসৎ ভাবধারা লালিত-পালিত হয় বিধায় তার ক্ষতি ও অনিষ্ঠকারিতা প্রবৃদ্ধি লাভ করে। ফলে এমন একটা অবস্থা দেখা দেয়, যখন মানুষ দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে বসে। তখন সে কার্যত নিজেকে লোকদের মানসে উলঙ্গ করে দেয়। এরূপ অবস্থায় তার ঈমানের দাবি মিথ্যা প্রমাণিত হয়। সূরা ‘আল-মুমিনূন’-এ ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রকে ঈমানদার লোকদের জরুরী গুণপনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ দুটির ওপরই মানুষষের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল।
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ – الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ – إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ – فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ – وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ -
‘‘এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, সেসব মুমিনরাই প্রকৃত সাফল্য লাভ করেছে যারা নিজেদের নামাযে ভীত-সন্ত্রস্ত অন্তরে দণ্ডায়মান হয়, যারা অর্থহীন ও উদ্দেশ্যহীন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যারা নিরন্তর নিজেদের পবিত্র ও পরিচ্ছন্নকরণ প্রচেষ্টায় নিরত থাকে, যারা নিজেদের লজ্জাস্থানসমূহকে (হারাম ব্যবহার থেকে) রক্ষা করে, যারা আমানতসমূহ ও ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি সংরক্ষণ করে আর যারা নিজেদের নামাযসমূহকে সংরক্ষণ করতে থাকে…..।’’ (সূরা মুমিনূনঃ ১-৯)
স্বয়ং নবী করীম সা. বহু সংখ্যক হাদীসে বহু সংখ্যক গুণ-বৈশিষ্ট্যকে ঈমানদার লোকদের অপরিহার্য বিশেষত্ব রূপে গণ্য করেছেন। সেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে যতটা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে, ঈমানের অবস্থায়ই সেই অনুপাতে তারতম্য ঘটবে। তার অর্থ এই যে, আমাদের বাহ্যিক চরিত্র ও আচার-আচরণ আমাদের অন্তর্নিহিত ঈমানী অবস্থার মাপকাঠি বা পরিমাপ যন্ত্র। কোন লোকের ঈমানী অবস্থা বাস্তবিকপক্ষে কি তা এর দ্বারাই প্রমাণিত হয়। নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেনঃ
১. ঈমানের সত্তরটির অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার একটি হচ্ছে লজ্জা।
২. ঈমানের বহু শাখা-প্রশাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তওহীদের ঘোষণা আর সবচাইতে কম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লোক চলাচলের পথ থেকে পীড়াদায়ক জিনিসের অপসারণ।
৩. তিনটি কথা ঈমানের অংশ। দরিদ্রাবস্থায়ও আল্লাহর পথে ব্যয় করা, দুনিয়ায় শান্তি ও নিরাপত্তার প্রসারতা বিধান এবং স্বয়ং নিজের বিরুদ্ধেও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
৪. মুসলমান সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে আর মুমিন সে যার ওপর এতটা বিশ্বাস ও আস্থা হবে যে তার নিকট নিজের জান ও মালও আমানতরূপে অক্ষুণ্ন থাকবে।
৫. মুমিন সে, যে অন্যকে ভালবাসে। যে লোক অন্যকে ভালবাসেনা এবং তাকেও কেউ ভালবাসে না তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই।
৬. মুমিন কারোর ওপর অভিসম্পাত করেনা, কাউকে বদদো’আ দেয় না, কাউকে গালাগাল করেনা এবং কারোর সাথে মুখ খারাপও করেনা।
৭. মুমিন সে, যাকে লোকেরা বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসভাজন মনে করবে। মুসলিম সে যার মুখ ও হাত থেকে লোকেরা নিরাপদ থাকবে।
৮. তিনটি জিনিস দ্বারাই বেঈমান ও মুনাফিকের পরিচিতি পাওয়া যা। তাহল, যখন কথা বলবে মিথ্যা বলবে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করবে এবং তার কাছে আমানত রাখা হলে সে তা বিনষ্ট করবে।
৯. নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যাকে লোকেরা তার খারাপ মুখের দরুণ পরিত্যাগ করেছে।
১০. মানুষকে যা কিছুই দেয়া হয়েছে, তাতে উত্তম জিনিস হয় সৎ বা শুভ চরিত্র।
১১. ইসলামে অশ্লীল কথাবার্তা বলার কোন স্থান নেই। উত্তম মুসলমান সে, যে চরত্রের দিক দিয়ে অতীব উচ্চ মর্যাদাবান।
চরিত্র ও আল্লাহ প্রেম
ভালবাসা মানুষের প্রতি আল্লাহ তা’আলার একটি মূল্যবান অবদান। বিশেষ করে আল্লাহর ভালবাসা একটি অতিবড় সম্পদ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মহামূল্য সম্পদ অর্জনের উপায় কি?
যে সব উপায়ে এই মহামূল্য সম্পদ লাভ করা যেতে পারে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হল শুভ চরিত্র। আর যেসব কারণে এই মহামূল্য সম্পদ অপহৃত হয় তন্মধ্যে চরিত্রহীনতা ও অসদাচরণ অন্যতম।
কুরআনের দৃষ্টিতে নিম্নোদ্দৃত নৈতিক গুণাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম ও ভালবাসা অর্জিত হতে পারেঃ
১. দয়া ও অনুগ্রহ। বলা হয়েছেঃ
‘‘দয়া-অনুগ্রহকারীদেরকে আল্লাহ তা’আলা ভালবাসেন।’’
২. সুবিচার ও ন্যায়পরতাঃ
‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচার ও ইনসাফকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।’’
৩. নৈতিক ও দৈহিক পবিত্রতা বা নিষ্কলুষতাঃ
‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্রতা রক্ষাকারী ও পরিচ্ছন্নতা অবলম্বনকারী লোকদেরকে ভালবাসেন।’’
নিম্নোদ্ধৃত বিষয়গুলো আল্লাহর ভালবাসা থেকে মানুষকে বঞ্চিত করেঃ
১. আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘনঃ
‘‘আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।’’
২. বিশ্বাসঘাতকতা ও আমানতে খিয়ানত করাঃ
‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ খিয়ানতকারীদেরকে ভালবাসেন না।’’
‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা’আলা এমন ব্যক্তিকে পসন্দ করেন না, যে বেশী খিয়ানতকারী ও পাপিষ্ঠ।
৩. বিপর্যয় ও অশান্তি সৃষ্টি করাঃ
‘‘অশান্তি ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন না।’’
৪. উচ্ছৃংখলতা, অপব্যয় ও বাড়াবাড়ি করাঃ
‘‘আল্লাহ বাড়াবাড়ি, উচ্ছৃংখলতা ও অপব্যয়কারীদেরকে পসন্দ করেন না।’’
৫. অহংকার ও আত্মম্ভরিতাঃ
‘‘কোন অহংকারী ও দাম্ভিক লোককে আল্লাহ ভালবাসেন না।
আল্লাহর গুণাবলী ও চরিত্র
বস্তুত ইসলাম উত্তম ও শুভ চরিত্রের একটি অতীব উন্নত মান ও চিন্তা-চেতনা উপস্থাপন করেছে আর তাহল উত্তম শুভ চরিত্র। এটি মূলত খোদায়ী গুণাবলীর ছায়া এবং তারই সামান্য প্রতিফলন মাত্র। রাসূলে করীম সা. বলেছেনঃ
‘‘শুভ চরিত্র আসলে আল্লাহ তা’আলার মহান ও সুউচ্চ চরিত্রেরই প্রতিফলন মাত্র।’’
আমাদের দৃষ্টিতে উত্তম চরিত্র তা-ই যা আল্লাহর মহান গুণাবলীর প্রতিবিম্ব আর খারাপ চরিত্র বলতে আমরা বুঝি সেই সবকে, যা আল্লাহর গুণাবলীর পরিপন্থী। ইসলাম মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের উপায় রূপে নির্দিষ্ট করেছে চরিত্রকে। তার কারণ হল, চরিত্র খোদায়ী গুণাবলীর জ্যোতিমালা থেকে গৃহীত ও নিঃসৃত। এই গ্রহণ ও অর্জনে আমরা যতটা অগ্রগতি লাভ করব, আমাদের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ততই বেশী নিশ্চিত হবে এবং তার ধারাবাহিকতা থাকবে অব্যাহত।
চরিত্র ও ইবাদত
ইসলামী আদর্শে গুরুত্বের দিক দিয়ে চরিত্রের স্থান যদিও তৃতীয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইবাদতের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিবেচনা করলে জানতে পারা যাবে যে, ইবাদতসমূহ মূলত মানুষকে আদর্শ চরিত্রবান বানাবারই উপায় মাত্র। মানুষ সত্যনিষ্ঠ, সততাবাদী ও নিষ্কলুষ চরিত্রগুণের অধিকারী হয়ে গড়ে উঠুক, এক মহান নৈতিক গুণাবলী আয়ত্ত ও আত্মস্থ করে মনুষ্যত্বের চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের যোগ্যতা অর্জন করুক, সেই সঙ্গে নিজের অধিকার ও কর্তব্য যথাযথভাবে আঞ্জাম দিক-ইবাদতসমূহের এই তো পরম ও চরম উদ্দেশ্য আর এরই অপর নাম হল চরিত্র।
বস্তুত মানব-মনের নৈতিক প্রশিক্ষণের একটা কার্যকর মাধ্যম রূপেই ইবাদতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এরই সহায়তায় মানুষ নিজের হৃদয়াবেগ ও কামনা-বাসনা সংযত করতে সক্ষম হতে পারে। আল্লাহকে স্মরণ করা ও তাঁর সামনে মস্তক অবনত করার অর্থ হচ্ছে, আমরা একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে মন-মানস ও কামনা-বাসনার স্বাধীনতাকে ত্যাগ করেছি। ইবাদতের সময় এই অনুভূতি না জাগলে এবং নিজেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন, বিমুক্ত ও স্বেচ্ছাচারী মনে করলে ইবাদতের কোন শুভফল অর্জিত হতে পারে না। কেননা ইবাদতের মর্মই হল, মহান আল্লাহই আমাদের একমাত্র মা’বুদ এবং আমরা একান্তভাবে তাঁরই দাসানুদাস। তাই তাঁর মুকাবিলায় আমাদের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই-কিছু থাকতে পারে না। আমাদের কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনাবলী আমাদের ধর্মীয় ও নৈতিক লক্ষ্যানুগ ও তারই অধীন। কুরআনের একটি আয়াতে নামায তরক করা ও লালসা-বাসনার অনুসরণ করার কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করে একথা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, কামনা-বাসনা-লালসার আনুগত্য ও অনুসরণ সম্ভব ও সহজ হয়ে ওঠে ইবাদত ত্যাগ করলে। ইবাদত যথাযথ পালন করা হলে তা হতে পারে না।
সাধারণত লোকদের ধারণা হল, ঈমানের পরই নামায, রোযা, যাকাত ও হজ্জ এই চারটি স্তম্ভের ওপরই ইসলামের সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মিত। নৈতিক চরিত্রের কোন গুরুত্ব এতে আছে বলে মনে করা হয় না। অথচ আল্লাহ তা’আলা স্বয়ং নৈতিক চরিত্রের গুরুত্বকে কিছুমাত্র উপেক্ষা করেন নি। তাই যেখানেই কোন ইবাদত ফরয হওয়ার কথা বলা হয়েছে, সেখানেই স্বষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মানুষের উত্তম ও উন্নত চরিত্র গড়ে তোলা ও তার পূর্ণত্ব বিধানই মানুষের চরমতম লক্ষ্য। নামায ফরয হওয়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তা মানুষকে সর্বপ্রকার অন্যায়, পাপাচার ও নির্লজ্জতা থেকে বিরত রাখে। রোযা ফরয করেই বলে দেয়া হয়েছে, তা মানুষের মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতির সৃষ্টি করে। যাকাত বিত্তবানদেরকে মহানুভবতা ও সহৃদয়তার শিক্ষা দেয় এবং হজ্জও বিভিন্নভাবে মানুষের নৈতিক সংশোধন ও উৎকর্ষ বিধানের কাজ করে বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে।
নামায সম্পর্কে রাসূলে করীম সা. ইরশাদ করেছেনঃ যার নামায তাকে অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার নামায তাকে আল্লাহর নিকট থেকে আরও দূরে নিয়ে যায়।
রোযা সম্পর্কে একটি হাদীসে বলা হয়েছেঃ রোযা রেখেও যে লোক মিথ্যা ও প্রতারণা পরিহার করেনি, নিজের পানাহার সে বন্ধ রাখুক- তাতে খোদার কোন প্রয়োজনই নেই।
একটি হাদীসের কথা হল, মুমিন তার উত্তম ও শুভ চরিত্রের বলে (নফল) রোযাদার ও (নফল) নামাযীর মর্যাদা লাভ করতে পারে।
যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়ার বিষয় বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, নিজের বংশ ও পরিবার-পরিজনের মৌল অধিকার যথাযথ আদায় না হওয়া পর্যন্ত কারোর ওপর তা ফরযই হয় না। অন্য কথায়, আল্লাহ্ তা’আলা বান্দাহ্র ওপর নিজের অধিকার ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিব করেন না, যতক্ষণ সে বান্দাহ্দের অধিকারসমূহ আদায় না করছে।
আল্লাহর হক্ব ও বান্দাহর হক্ব
ইবাদত ও চরিত্রকে যথাক্রমে আল্লাহর হক্ব ও বান্দাহর হক্ব বলে চিহ্নিত করা যায়। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ, লেনদেন ও আদান-প্রদানেরই অপর নাম চরিত্র। আর ইবাদত হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ফরয রূপে ধার্য কর্তব্য। একটু গভীর ও সূক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে বুঝতে পারা যাবে যে, চরিত্রের গুরুত্ব ইবাদতের তুলনায়ও অনেক বেশী। শিরক ও কুফর একান্তভাবে আল্লাহর অধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপার। এ ছাড়া আল্লাহর অধিকারের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য গুনাহ ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু মানুষের অধিকার অনাদায় থাকলে তা ক্ষমার অযোগ্য। আল্লাহ নিজে তা ক্ষমা করে দেবেন না; তা ক্ষমা করার অধিকার ঠিক সেই মানুষের হাতেই রাখা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর নিকট থেকে যে দয়া-অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করা যায়, তাতো আর মানুষের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করা যায় না। তাই নবী করীম স. ইরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির ওপর (যে তার ভাই) জুলুম করেছে সেই জালিম (ভাই)-র কর্তব্য হল, এই দুনিয়ায়ই সেই মজলুম ভাইর নিকট থেকে জুলুমের ক্ষমা চেয়ে নেয়া। অন্যথায় কিয়ামতে তার ক্ষতিপূরণ করার জন্যে কারোর নিকট কোন টাকা-পয়সা (দিরহাম ও দীনার) থাকবে না- থাকবে শুধু আমল। জালিমের নেক আমলসমূহ মজলুম পেয়ে যাবে। নেক আমল না থাকলে মজলুমের পাপসমূহ জালিমের আমল-নামায় লিখে দেয়া হবে।
নৈতিক চরিত্র ও আইন
মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের মধ্যেই তাকে বাস করতে হয়। সমাজ ছাড়া মানুষের জীবন অচল। বহু সংখ্যক মানুষ যখন একত্রে জীবন যাপন করে তখন তাদের মধ্যে কোন-না-কোন বিষয়ে মত-বৈষম্য, দ্বন্দ্ব-কলহ ও বিবাদ-বিসম্বাদের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব কিছু নয়-নয় কিছুমাত্র অস্বাভাবিক। এই সমাজে একজনের অধিকার অপরজন কর্তৃক অপহৃত হওয়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। শক্তিশালী এখানে দুর্বলের ওপর অন্যায় ও বাড়াবাড়ি করতে পারে- পারে তাকে পর্যুদস্ত করবার চেষ্টা করতে। ধনী নির্ধনের ওপর অন্যায় আচরণ ও শোষণ চালাতে পারে। এই সব কিছুর মুকাবিলা করে প্রতিটি ব্যক্তির জীবন, ধন-সম্পদ ও মান-সম্মানের নিরাপত্তা দিয়ে শান্তি ও শৃংখলাপূর্ণ সমাজ গঠন করা মানুষের সুখী জীবনের জন্য অপরিহার্য। এ জন্যে যে আইন ও বিধান রচিত হয়েছে, তার একটা অংশ নৈতিক এবং তা অনুসরণ করা বা না-করা ব্যক্তির ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল; সেজন্য কাউকে জোরপূর্বক বাধ্য করা যেতে পারে না। অবশ্য এমন কিছু নিয়ম-বিধি রচিত হয়েছে, যা পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্তব্য। এই নিয়ম-বিধিকেই পরিভাষায় বলা হয় আইন। এই আইন ও নৈতিকতার মূল লক্ষ্য যদিও এক ও অভিন্ন; কিন্তু তা লাভ করার পথ ভিন্ন ভিন্ন। এককভাবে এর কোনটিই প্রয়োজন পূরণে সক্ষম নয়- সব ক’টি দিককে পরিব্যাপ্ত করতে পারে না। তাই এর একটির অসম্পূর্ণতা অন্যটির দ্বারা পূর্ণত্ব লাভ করে। আইন অন্যায় ও পাপ কাজকে বন্ধ করতে পারে বটে; কিন্তু মানব মনে তার প্রতি ঘৃণা জাগাতে পারে না। ফলে আইনের বাঁধন যখনই শিথিল হবে বা আইন রক্ষাকারীরা চোখের আড়াল হবে, তখনই পাপ ও অন্যায় সংঘটিত হবে; তখন তা ঠেকিয়ে রাখা আর সম্ভব হবে না। কিন্তু নৈতিক চরিত্রের সাহায্যে যে পাপ ও অন্যায় দূর হয়, তা স্থায়িত্ব লাভ করে। তার পুনরাবৃত্তি হয় না বললেই চলে। কেননা চরিত্র ও নৈতিকতা মানবমনে অন্যায় ও পাপের প্রতি একটা তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রথমটির পাহারাদারী কখনো সার্বক্ষণিক হতে পারে না। সার্বক্ষণিক পাহারাদারী হতে পারে দ্বিতীয়টির; কেননা তা মানুষের অভ্যন্তরে অবস্থিত। সুতরাং তা-ই হতে পারে মানুষের দ্বীন ও ঈমানের অতন্দ্র প্রহরী, প্রতিরোধকারী। উপরন্তু আইন শুধু মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ ও জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে। মানুষের মন-মানস ও চিন্তা-বিশ্বাসের মর্মমূলে তার কোন ছায়াপাত ঘটেনা। কিন্তু চারিত্রিক প্রতিরোধের অবস্থান মানুষের অন্তরে। মানুষের মন-মানস ও হৃদয়-বৃত্তির সাথে তার গভীর ও ঘনিষ্ট সম্পর্ক; বরং তার উৎসই হচ্ছে এই মন-মানস ও হৃদয়-বৃত্তি। তাই মানুষের হৃদয়-মন যতক্ষণ জাগ্রত ও সচেতন থাকে ততক্ষণ তার দ্বারা পাপ ও অন্যায় কাজ সম্ভব হতে পারে না।
একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারা যায়, আইনের তুলনায় নৈতিকতাই অধিক গুরুত্বের অধিকারী। চরিত্র আসলে আইনেরই সংরক্ষক; বরং একথা বললেও অত্যুক্তি হবে না যে, আইনের ভিত্তিই হচ্ছে চরিত্র। একটি জাতির ও একটি সমাজের নৈতিক অবস্থারই দর্পন হচ্ছে আইন। যে জাতির চরিত্র উত্তম, তার আইন-কানুনও নমনীয়। আর জাতীয় চরিত্র যদি হয় খারাপ, তাহলে তার জন্যে কঠোর আইন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। জনগণ যতি স্বতঃই নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তৎপর হয়, তাহলে রাষ্ট্র-সরকারকে কঠোর উৎপীড়কের আইন রচনা করতে কখনো বাধ্য হতে হবে না।
ইসলাম মানব প্রকৃতি ও মানবীয় মনস্তত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে চরিত্র ও আইন উভয়কেই প্রয়োগ করেছে। যে সব অন্যায় ও পাপের প্রতিক্রিয়া অন্যদের প্রভাবিত করে কিংবা বলা যায়, যে সব অন্যায় ও পাপ সমগ্র সমাজ ও জাতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাকে আইনের অধীন নিয়ে নেয়া হয়েছে। হত্যা, চুরি, ডাকাতি ও অন্যায় কাজের দোষারোপ প্রভৃতি এই পর্যায়ে গণ্য। আর যে সব বিষয় ও ব্যাপারে ব্যক্তির আত্মার সাথে সম্পর্কিত- যেমন মিথ্যা না বলা, দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন, গরীবদের সাহায্য প্রভৃতি- এগুলোকে নৈতিক চরিত্রের ব্যাপার বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই প্রেক্ষিতে আমরা অতি সহজেই বলতে পারি যে, দ্বীন-ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মাদ সা. প্রবর্তিত শরী’আত হচ্ছে আইন ও নৈতিক চরিত্রের সমন্বয়।
ইসলাম নৈতিকতাকে প্রতিটি ব্যক্তির হাতে তুলে দিয়েছে- যদিও তার একটা সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বও রয়েছে-আর আইনকে অর্পন করেছে সমাজ ও রাষ্ট্রের হাতে। আইনের ভিত্তির ওপর সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। তাকে সরিয়ে দিলে রাষ্ট্র-সংস্থা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়তে বাধ্য। তখন কারও জান-মাল ও ইজ্জত-আবরু সংরক্ষিত থাকবেনা বরং থাকার সম্ভবনাই শেষ হয়ে যাবে। তাই সংস্কৃতির দোহাই পেড়ে বা সংস্কৃতির নামে চরিত্র বিনষ্টকারী কোন অনুষ্ঠানকেই বরদাশত করা যেতে পারেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে সংস্কৃতি মানব চরিত্রকে উন্নত ও নির্মল করবে। পক্ষান্তরে যে সংস্কৃতিই মানব চরিত্রকে বরবাদ করে তা-সংস্কৃতি নয়- দুষ্কৃতি মাত্র।
বিমূর্ত শিল্প ও জাতীয় চরিত্র
বর্তমান দুনিয়ায় এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট (Abstract art) বা বিমূর্ত শিল্পের ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও প্রচলন লক্ষণীয়। বিশ্বের পত্র-পত্রিকা ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া এই শিল্পের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের দিক থেকে এ ব্যাপারে একটি প্রশ্ন প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। তা হচ্ছে, এই এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট কি বাস্তবিকই আমাদের জনগণের রুচিসম্মত, আমাদের দ্বীনী আকিদা-বিশ্বাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ? তা কি বাস্তবিকই এখানকার জনগণের শিল্প? অথবা তা মূলত বাইরের জিনিস, আমাদের জনগণের ওপর তা বিশেষ উদ্দেশ্যে ও পরিকল্পিতভাবে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং একটি মারাত্মক ধরণের ষড়যন্ত্র হিসেবেই এটিকে আমাদের সমাজে প্রচলিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে?
পরন্তু, তা যদি বিদেশ ও ভিন্নতর সমাজ থেকে নিয়ে এসে আমাদের সমাজে চালু করার একটা অপচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে কারা- কোন্ শ্রেণীর ও কোন্ মতাদর্শের লোকেরা তা করছে? এই বিষয়গুলো একটু খতিয়ে দেখা দরকার।
এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট অনুধাবনের জন্যে অবশ্য ওয়াসিলি কাণ্ডিনিস্কির সময়ে অধ্যয়ন আবশ্যক। কেননা এই কাণ্ডিনিস্কিই আমেরিকায় আর্টের এই নবতর আন্দোলনকে সুপরিচিতি ও সুসংগঠিত করেছেন। নিউিইয়র্কে তিনিই একটি আর্ট মিউজিয়াম স্থাপন করেছেন, যার নাম হচ্ছে ‘দি মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্ট’। যারা মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতি (Psycho-politics)-এর ইতিহাসে অভিজ্ঞ, তারা ভালো করেই জানেন যে, এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর এই আন্দোলন সর্বপ্রথম রাশিয়ায় ‘অক্টোবর বিপ্লবের’ পর শুরু হয়েছিল। যান্ত্রিক মানুষের স্রষ্টা এ, কে, গুস্তাফ এবং তার অনুসারীরা এক ধরণের এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট উদ্ভাবন করেছিলেন, যাকে বলা হয় ‘কন্স্ট্রাকটিভ সিমবলিক রিপ্রেজেন্টেশনাল আর্ট’ বা গঠনমূলক প্রতীকধর্মী প্রতিনিধিত্বশীল শিল্প। এ শিল্পকলা সম্পর্কে যাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে, তিনি সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, আজকের এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট মূলত রাশিয়ার প্রাথমিক বিপ্লবকালীন সময়ের আর্টের ফসল হিসেবেই অস্তিত্বলাভ করেছে। এ আর্টের মূলে যে তত্ত্ব নিহিত তা হচ্ছে সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক সিস্টেমের অভিন্নতা ও সংহতি চূর্ণবিচূর্ণ করার জন্যে তাতে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সংহতি বিরোধী ভাবধারা ও উপকরণাদি প্রবিষ্ট করিয়ে দিতে হবে। এই তথাকথিত গঠনমূলক নীতির অনুসারী আর্টের লক্ষ্যই হচ্ছে প্রাচীন ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত মূল্যমান ও সাংস্কৃতিক জীবনে চরম বিপর্যয় সৃষ্টি করা।
রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক কালে বলশেভিকবাদের দর্শন কয়েকটি দিক দিয়ে ব্যাপক হয়ে উঠেছিল- যেমন মেকানিক, কাব্য ও সঙ্গীত, যান্ত্রিক থিয়েটার, যান্ত্রিক প্রতিমূর্তি নির্মাণ এবং সবশেষে যান্ত্রিক মানুষ। আর্টের এই বিভিন্ন মাধ্যমের (Media) লক্ষ্য ছিল প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাসমূহে বিপর্যয় সৃষ্টি করা। কান্ডিনিস্কী ‘আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংস্থা’র সদস্য ছিলেন। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টকে জনপ্রিয় করে তোলার দায়িত্ব দিয়ে তাকে আমেরিকায় পাঠানো হয়েছিল। কান্ডিনিস্কী নিউইয়র্ক শহরে আধুনিক শিল্পের যাদুঘর ‘মিউজিয়াম অফ মডার্ণ আর্ট’ স্থাপন করতে সাফল্য অর্জন করেন। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর সৌভাগ্যই বলতে হবে, হিটলার এই শিল্পের শিল্পীদেরকে এই সময় জার্মানী থেকে বহিষ্কৃত করেছিলেন। এ বহিষ্কৃত শিল্পীরাই আমেরিকায় গিয়ে বসবাস গ্রহণ করলেন। ফলে আমেরিকা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর লীলাভূমিতে পরিণত হয়ে গেল। এভাবে এ আর্টের সাহায্যে আমেরিকান জনগণের মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিপর্যয় (Personality Fragmentation) সৃষ্টির বীজ বপনে সাফল্য লাভ করার পর স্বয়ং রাশিয়া এক্ষণে বাস্তববাদী শিল্পে (Realistic art) প্রত্যাবর্তন করেছে।
পূর্বেই বলেছি, এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের ভাঙন ও বিপর্যস্তকরণ। যে সব উপায়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট গড়ে ওঠে, তা হচ্ছে বিশ্লিষ্টতা ও আকৃতিসমূহের বিকৃতি (Distortion), চিন্তার বিশৃঙ্খলা, নির্বীর্যতা। আর মূলত পরাজিত আত্মা ও ব্যর্থকাম মন-মানসিকতার অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে এই চৈন্তিক অরাজকতা। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর পক্ষে যেসব সাহিত্যিক লেখনী চালনা করেছেন, তারাও এই চৈন্তিক উচ্ছৃঙ্খলতা ও মানসিক ভারসাম্যহীনতায় চরমভাবে আক্রান্ত। তাঁরা তাদের রচনাবলীতে এই বিপর্যয় ও বিশ্লিষ্টতাময় শব্দাবলী বাছাই (Fragmental Fregiology) ও ব্যবহার করে পাঠকদের মনে-মগজেও অনুরূপ বিপর্যয় বিশ্লিষ্টতা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন।
এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর একজন পূজারী জনৈক এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্ট সম্পর্কে লিখেছেনঃ যে জিনিসটির ঝুলন্ত বা সাঁতার কাটা অবস্থায় থাকা আবশ্যক, তাকে কাঁচা হাতে ও কঠোরতার সাথে অবিকল রূপ দান করা এই এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্ট রীতিমত ঘৃণা করে। জিনিসগুলিকে তার আসল স্বাভাবিক রূপে উপস্থাপনকে সে অর্থহীনভাবে প্রত্যাখান করেছে। এই সত্য অনুধাবনে অক্ষম হওয়ার কারণে বেশ কিছু লোক পলায়নী আচরণ অবলম্বন করেছে। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর তত্ত্ব সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তির প্রথম প্রতিক্রিয়া হয় ঘৃণার। সে বড়জোর এই প্রতিক্রিয়াকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে; কিন্তু রুচিহীনতা যা বিকৃতরুচি লুকোতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হয়। নগরস্থ প্রখ্যাত ড্রয়িং-রুমসমূহের সাজ-সজ্জা-সামগ্রী পর্যায়ে এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর উল্লেখ হলেই কোন কোন লোক ঘৃণায় নাক সিঁটকাতে শুরু করে এবং তাদের বিশ্বাসঘাতক ওষ্ঠে একটি কৃত্রিম বক্র হাসি খেলে যায়। কেউ কেউ আবার প্রথম শ্রেণীর নির্বোধ লোকদের ন্যায় পূর্ণমাত্রার আস্থা সহকারে কথা বলে।
এটা এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট ভক্তদের চিন্তার বৈসাদৃশ্য ও বিশ্লিষ্টতার একটা ক্ষুদ্র নিদর্শন মাত্র।
একটা বিপর্যস্ত ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন সব জনসংস্থা গড়ে তোলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক-অনেক সময় তা অপ্রাসঙ্গিকও হয়ে থাকে। কিছু লোক মানসিক পূর্ণতা ও সামাজিক পরিপক্কতা লাভ করতে পারে না, এমনটা হয়ে থাকে। তার প্রমাণ হচ্ছে, যেসব লোকের কারণে তারা ক্ষুদ্রত্বের অনুভূতি বা হীনমন্যতা রোগে (Inferiority Complex) ভোগে তাদের প্রতি বিদ্রুপবান নিক্ষেপ করার একটা প্রবণতা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। লোকদের যখন দেখা যায়, বাইরের লোকদের সাফল্যের প্রশংসা করছে, কিন্তু নিজেদের সমাজের লোকদের স্মরণযোগ্য অবদানের মূল্যও স্বীকার করতে দ্বিধান্বিত হচ্ছে, তখন মনে দুঃখানুভূতি জেগে ওঠে স্বাভাবিকভাবেই।
একটি জাতি বা জনসমষ্টিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করার অনেকগুলো পন্থা থাকতে পারে। অনুরূপভাবে মানবীয় মান ও মগজকে দাসত্বের নিগঢ়ে বন্দী করার পন্থাও হতে পারে বহুবিধ। তবে মানব-মনকে পরাভূত করার আধুনিকতম পন্থা হচ্ছে, তাদের সম্মুখে এমন সব নিদর্শন পেশ করতে এবং তাদের চতুঃষ্পার্শ্বে এমন পরিবেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে, যার ফলে তারা বন্দী থেকেই নিয়ম-শৃঙ্খলা পালনের গৌরব বোধ করতে পারে। বিগত শতাব্দীতে দেশবিজয়ী জাতিগুলো তাদের বিজিত জনগোষ্ঠীর ওপর যে নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা ও পাশবিকতা চালিয়েছে এ পন্থায় অবশ্য সে সবের আশ্রয় নেয়ার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না; বরং বর্তমান কালের বিজয়ীরা বিজিতদের সম্মুখে অর্থহীন, উদ্দেশ্যহীন ও দুর্বোধ্য সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডের নিদর্শন পেশ করা ও তাতে তাদের মুগ্ধবিমোহিত করে তুলতে পারাকেই যথেষ্ট মনে করে। বস্তুত কোন একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে নৈরাশ্য ও হতাশাগ্রস্থ করে দেয়ার জন্যে অর্থহীন ও লক্ষ্যহীন ক্রিয়াকাণ্ডে মশগুল করে দেয়া একটা অত্যন্ত শানিত ও কার্যকর হাতিয়ার। অস্পষ্টতা ও লক্ষ্যহীনতাই এই কাজকে সার্থক ও সচল করে দিতে পারে। একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীকে মানসিক অধঃপতনের নিম্নতম স্তরে পৌঁছে দেয়ার জন্যে রাজনৈতিক মনস্তত্ব বিশারদরা যে ক’টি সাংস্কৃতিক উপায়-উপাদান প্রয়োগ করে থাকে ‘এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট’ তন্মধ্যে অন্যতম।
বঞ্চনার অনুভূতির তীব্রতা অনেক সময় ব্যক্তিত্বের বিশ্লিষ্টতায় প্রকট হয়ে ওঠে। অনুভূতির এ তীব্রতা অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা ও উদ্দেশ্যহীনতাকে খুঁজে নেয় আর এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর ভক্তদের সুস্পষ্ট বিশেষত্ব এটাই। এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট মানবীয় আচরণের এমন পন্থা ও বঞ্চনানুভূতি ও বিশ্লিষ্টতার এমন সব নিদর্শন উপস্থাপন করে, যার পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত হৃদয়াবেগ ও উচ্ছ্বাস সব সুস্থতা ও ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে।
এ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট-এর লক্ষ্য কি? শিল্পী তার মাধ্যমে কি পয়গাম তুলে ধরে দর্শকদের নিকট? প্রভাব বিস্তারকারী শিল্পী (Impressionist) নানা রঙের ওপর আলোর বিচ্ছুরণ দেখায়। প্রকাশপন্থী (Expressionist) চেষ্টা চালায় বস্তু নিচয়ে অন্তর্নিহিত সত্যকে যতটা সম্ভব ব্যক্ত করে দিতে। আর ইঙ্গিতধর্মী চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির অনুসারী (কিউবিস্ট) বস্তুসমূহে জ্যামিতিক মৌল রূপরেখার সন্ধান করে-মহাজাগতিক (সিওরিলিস্ট) অবচেতনকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয়। একজন সমালোচক তে বলেই ফেলেছেন যে, এ্যাবস্ট্রাক্ট রেখাসমূহ আসলে অত্যন্ত পবিত্র এবং খোদায়ী গুণাবলীকে অধিকতর পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রকাশ করে। কেননা তা বস্তুগত খোলস, দেহের ভার ও মুখাবয়বের স্পষ্টতা ছাড়াই অস্তিত্ববান হয়েছে। আর বস্তুগুলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে অভিব্যক্তি না করেই সে সবের অন্তর্নিহিত ও অর্ধোস্ফূট কলিসমূহের দ্বারা বিশ্বপ্রাণ পর্যন্ত পৌঁছাবার চেষ্টায় পরিণতি হচ্ছে সেই আর্ট, যাকে আমরা অদ্বৈতবাদী দৃষ্টিকোণে ধর্মীয় বলতে পারে।
ইসলামী দৃষ্টিকোণে আর্ট
ইসলামের দৃষ্টিতে আর্টের লক্ষ্য বুঝবার জন্যে দেখতে হবে তার নিকট জীবনের লক্ষ্য কি? কুরআনের দৃষ্টিতে মানবজীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা বিধান, যা সৃষ্টিধর্মী পথে মানবতার জন্যে কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে অর্জিত হয়। ব্যক্তিত্বের পূর্ণত্ব বিধানের একটি দিক হচ্ছে, সে লক্ষ্যে মানবীয় আবেগ-উচ্ছ্বাসকে সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলীতে নিয়োগ করা।
বস্তুত সৃষ্টিধর্মী ও সৃজনশীল গুণাবলী বা যোগ্যতাসমূহ মানুষের জন্যে মহান আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত। আসলে তা মানুষের ক্ষেত্রে আল্লাহর ছায়া বিশেষ। সৃষ্টিধর্মী কার্যাবলী চিরস্থায়িত্বের ধারক। আর প্রতিটি সৃষ্টিধর্মী কাজ মানবীয় ব্যক্তিত্ব নির্মাণ ও পুনর্গঠনের মৌল উপকরণ বিশেষ।
মানুষের স্বভাবগত সৃজনশীলতার গুণ স্বতঃই প্রমাণ করে যে, মানুষ অন্যান্য মানুষের জন্যে সহমর্মিতার প্রবল ভাবধারার অধিকারী-একটা সুস্পষ্ট ধারণা ও কল্পনার মালিক। বিপন্ন মানবতাকে উদ্ধার করা ও তার শান্তি ও স্থিতির ব্যবস্থা করা এবং অন্যান্য মানুষকে কল্যাণময় জ্ঞানের আলো দ্বারা সমুদ্ভাসিত করাই তার নিরন্তর চেষ্টা ও সাধনা। এখানে ‘কল্যাণময় জ্ঞান’ এর কথাটি সচেতনভাবেই বলা হয়েছে; কেননা নবী করীম সা. দো’আ করতেনঃ হে আল্লাহ! আমাকে ‘অকল্যাণকর জ্ঞান’ থেকে রক্ষা করো। আর ‘অকল্যাণকর জ্ঞান’ হচ্ছে তা-ই যা মানুষের কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ বা ক্ষতি সাধন করে।
মানব প্রকৃতিতে নিহিত সৃষ্টিধর্মী গুণাবলী হারিয়ে ফেললে তার অর্থ এই দাঁড়াবে যে, মানুষ স্বার্থপরতা ও প্রতিহিংসার ধারক হয়ে বসেছে; ফলে কোন মানুষই অপর মানুষের একবিন্দু কল্যাণ সাধনেও কিছুমাত্র সক্ষম হবে না। অথচ মানবতার কল্যাণ সাধনই হচ্ছে এমন একটা লক্ষ্য যা মানব মনে সুখানুভূতি লাভের বিশেষ সহায়ক। তাছাড়া অন্যান্য লক্ষ্যসমূহ মানুষকে ব্যর্থতা ও বঞ্চনার দিকে পরিচালিত করে।
জীবন-লক্ষ্য সম্পর্কিত এই বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় অগ্রগতি ও উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা দানকেই শিল্পের লক্ষ্য রূপে নির্ধারিত করেছে ইসলাম। অতীব উত্তম মানের রূপরেখা তৈরী করে কলাশিল্প শিল্পব্যবসায়ের অনেক উৎকর্ষ সাধন করেতে পারে এবং দেশের জনকল্যাণমূলক শিল্পায়নে বিরাট অবদান রাখতেও সক্ষম। নির্মাণশিল্প, বস্তশিল্প, মৎস্যশিল্প, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র শৈল্পিক উপকরণ, শিল্পসম্মত উপায়ে কাঁচা মাল থেকে নানা দ্রব্য উৎপাদন, কাপড়ের চিত্তাকর্ষক, উন্নত ও সূক্ষ্ণ শিল্প-নৈপুণ্য বিশিষ্ট রূপরেখা তৈরী করা- এই সব কাজ ভাষা বা শব্দের পরিবর্তে রেখাঙ্কনের সাহায্যে অতি চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা যায়। [এ পর্যায়ে চারুকলার প্রসঙ্গটি উল্লেখ করা যেতে পারে। অধুনা আমাদের দেশে এই শিল্প-মাধ্যমটির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এক দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিয়োজিত না করে ব্যবহার করা হচ্ছে পৌত্তলিক সংস্কৃতির চর্চা ও অনুশীলনে। ফলে এর পিছনে জাতীয় মেধা ও অর্থের ব্যবহার একটি বিরাট অপচয় রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। -সম্পাদক]
বস্তুত শিল্পের লক্ষ্য হচ্ছে বাহ্যিক ও বাস্তব শিক্ষাদান। রৈখিক অভিব্যক্তির যতগুলো উপায় রয়েছে, তা সবই অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনা ও অনুভূতিরই প্রকাশ মাধ্যম। আর এ সবই শিল্পের আওতামুক্ত। তা চেতনা, মেধা-প্রতিভা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ শক্তির কার্যকরতার ওপর নির্ভরশীল। এ শিক্ষাকে বাদ দিলে মনস্তাত্ত্বিকভাবে ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার আশংকা প্রবল। সৌভাগ্যবশত এই মর্মান্তিক পরিণতি থেকে বেঁচে গেলেও চিন্তা ও কর্মের বিচারে অপরিপক্ক ও অপরিণত থেকে যাওয়া অবধারিত। ফলে একটা যান্ত্রিক জীবন প্রণালীর নির্বিকার অধীনতা ও দাসত্ব করে যাওয়া তার সারা জীবনের ভাগ্যলিপি হয়ে পড়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।
শিল্প একটা আত্মিক সত্য; আত্মার সাথে তার সম্পর্ক নিবিড়, গভীর। তা ধর্মবিশ্বাসের রক্তে সিক্ত মানবতাকে সেই সব যান্ত্রিক বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে, যা আমাদের বর্তমান জীবনকে দুঃখজনকভাবে বেঁধে রেখেছে। শিল্প মানবাত্মার মুক্তির নিয়ামত হতে পারে যদি তাকে ইসলাম নির্ধারিত জীবন-লক্ষ্যের অনুকূলে প্রয়োগ করা হয়। আর তাহলেই এ শিল্প একটি কল্যাণকর মাধ্যম হতে পারে- পরিগণিত হতে পারে জনগণের শিল্পে। অন্যথায় তা-ই আবার মানব আত্মাকে নতুন করে দাসত্বের নিগড়ে বাঁধতে পারে, যা থেকে মুক্তি লাভ চিরকালই অসম্ভব থেকে যাবে।
যাকিছু বাইরের তা-ই পরিত্যাজ্য বা অগ্রহণযোগ্য, এই মনোভাব ছাড়াও একটি বিশেষ সংস্কৃতিতে বিশ্বাসী ব্যক্তির মনের প্রশ্ন হচ্ছে, বাইরে থেকে যা আমদানী করা হচ্ছে, সামগ্রিকভাবে তা আমাদের সমাজ-মানসের অনুকূল বা কল্যাণকর কিনা? বস্তুত শিল্প বাইরে থেকে আমদানী করা হোক কিংবা ঘরেই নির্মিত হোক, তা যদি আমাদের সুস্থ মানসিকতায় বিকৃতির বাহন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অত্যাধুনিকতার দোহাই পেড়ে তার প্রচলন করার অধিকার কারোরই থাকতে পারেনা। উদারতার নামে উদরে নিশ্চয়ই পচা আবর্জনা ভর্তি করা কোন বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবেনা।
— সমাপ্ত —
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি