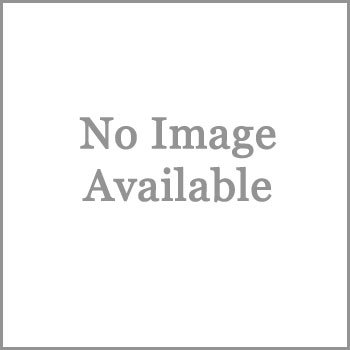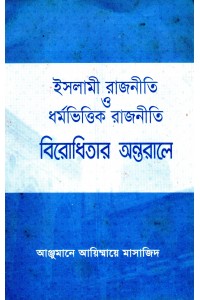তৃতীয় খন্ড
ইসলামী শাসনের মূলনীতি
• মৌলিক মানবাধিকার
• অমুসলিমদের অধিকার
• ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার
• ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার পথনির্দেশক মূলনীতি
দ্বাদশ অধ্যায়
• মৌলিক মানবাধিকার
দীর্ঘদিন থেকে কিছু লোকের মনমগযে একটি প্রশ্ন ঘুরপাক থাচ্ছে যে, ইসলাম মৌলিক মানবাধিকারের আদৌ কোনো গ্যারান্টি দিয়েছে কি? যারা কেবল পাশ্চাত্যের ইতিহাস এব্ং রাজনৈতিক উন্নতির ব্যাপারেই ওয়াকিফহাল, অজ্ঞতাবশত এসব লোকের ধারণা হলো, মানবাধিকার সংরক্ষেণের বিষয়টি কেবল পাশ্চাত্য দেশগুলোতেই উন্নতি সাধিত হয়েছে। অথচ এ ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত। ইসলামতো ঐ সময়ই মৌলিক মানবাধিকার সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিয়েছে এবং বাস্তবেও মানবতা তা সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভোগ করেছে, যখন অন্যদের মধ্যে মানবাধিকারের ধরণাই জন্মায়নি। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদুদী লাহোর রোটারী ক্লাবের আহ্বানে মৌলিক মানবাধিকারে ওপর বক্তব্য পেশ করেন এবং প্রসংগক্রমে সে ভাষাটি উল্লেখ করে দেয়া হলো।
মানবাধিকার একদিকে ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের অবিচ্ছেদ্য অংশ, অপরদিকে ইসলামে যারতীয় নীতিমালার জন্যে অগ্রগন্য মূলনীতির মর্যাদা সম্পন্ন। গ্রন্থের তৃতীয় খন্ড এসব অধিকারের বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করা হলো।– সংকলক
মৌলিক মানবাধিকার
[এটা মূলত একটা বক্তৃতা। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী (রহঃ) লাহোরের রোটারী ক্লবে এই বক্তৃতা দেন। মাওলানা খলীল আহ্মদ হামেদী তা লিপিবদ্ধ করেন।]
মৌলিক অধিকার কোনো নতুন ধারণা নয়
আমাদের মুসলমানদরে সম্পর্কে বলা যায়, ‘মৌলিক মানবাধিকার’ মতবাদ আমাদের জন্য কোনো নতুন জিনিস নয়। হতে পারে অন্যদের দৃষ্টিতে এই অধিকারের ইতিহাস সম্মিলিত জতিসংঘের মহাসনদ থেকে অথবা ইংল্যান্ডের ম্যাগনা কারটা [Magna Carta] থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতে এই মতবাদের সূচনা অনেক পূর্বে হয়েছে। এখানে আমি মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর আমাদের মতে এই মতবাদের সূচনা অনেক পূর্বে হয়েছে। এখনে আমি মানুষের মৌলিক অধিকারের ওপর আলোকপাত করার পূর্বে “মানবীয় অধিকার” মতবাদের সূচনা কি করে হলো তা সংক্ষেপে বলে দেয়া জরুরী মনে করি।
মৌলিক অধিকারের প্রশ্ন উঠেছে কেন?
দুনিয়াতে মানুষই এমন এক জীব যার সম্পর্কে স্বয়ং মানুষের মধ্যেই বারবার প্রশ্ন উঠছে যে, তার মৌলিক অধিকার কি? বাস্তবিবপক্ষে এ এক আশ্চর্য ধরনের কথা। মানবজাতি ছাড়া দুনিয়ায় বসবাসরত অন্যান্য মাখলুকাতের অধিকার স্বয়ং প্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং তারা তা ভোগ করে যাচ্ছে। এজন্য তাদের কোনোরূপ চিন্তা ভাবনা করতে হয়না। কিন্তু মানুষই এমন মাখলূক যার সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে যে, তার অধিকারসমূহ কি? এবং তাদের এ অধিকার নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।
অনুরূপভাবে এটাও আশ্চর্যর ব্যাপার যে, বিশ্বে এমন কোনো প্রকার সৃষ্টি নেই যে তার নিজস্ব শ্রেণভুক্ত অপর সদস্যের সাথে সেই ব্যবহার করছে যা মানুষ তার সমগোত্রের সাথে করছে। বরং আমরা তো দেখছি প্রাণীদের কোনো শ্রেণী এমন নেই যা অপর শ্রেণীর ওপর নিছক আনন্দ উপভোগ অথবা প্রভুত্ব করার জন্য আক্রমণ করছে।
প্রাকৃতিক বিধান যদিও এক ধরনের জীবকে অপর ধরনের জীবের খাদ্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে, কিন্তু তা কেবল খাদ্যের সীমা পর্যন্ত। এমন কোনো হিংস্র জন্তু নেই যে খাদ্যের প্রয়োজন ছাড়া অথবা এই প্রয়োজন পূরণ হয়ে যাওয়ার পর বিনা কারণে অন্যান্য প্রাণী হত্যা যাচ্ছে। মানুষ তার সমগোত্রীয়েদের সাথে যে আচরণ করছে জীব জন্তুর মধ্যে কোনো প্রাণিই তার সমগোত্রীয়দের সাথে তদ্রূপ আচরণ করেনা। আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন এটা খুব সম্ভব তারই ফল। মানুষ দুনিয়াতে যে অসাধারণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হচ্ছে তা আল্লাহ্ তায়ালা কর্তৃক তাদেরকে প্রদত্ব জ্ঞান ও আবিষ্কার শক্তিরই চমৎকারিত্ব।
বাঘেরা আজ পর্যন্ত কোনো সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেনি। কোনো কুকুর আজ পর্যন্ত অন্যান্য কুকুরগুলোকে গোলামে পরিণত করেনি। কোনো ব্যাঙ আজ পর্যন্ত অন্য ব্যাঙদের বাকশক্তি হরণ করেনি। কেবল মানুষই যখন আল্লাহ্ তায়ালার নির্দেশ উপেক্ষা করে তাঁর দেয়া শক্তিকে কাজে লাগাতে শুরু করে, তখন নিজের সগোত্রীয়দের ওপরই যুলুম শুরু করে দেয়। দুনিয়াতে মানব জাতির গোড়াপত্তন হওয়া থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত পশুরা এতো মানুষ হত্যা করেনি যতোগুলো মানুষের জীবন কেবল দ্বিতীয় মাহযুদ্ধে মানুষে ছিনিয়ে নিয়েছে। এতে প্রমাণ হয় যে, বাস্তবিকপক্ষে মানুষ অন্য মানুষের অধিকারের কোনো তোয়াক্কা করেনা। এ ক্ষেত্রে কেবল আল্লাহ্ তায়ালাই মানব জাতিকে পথ প্রদর্শন করেছেন এবং তাঁর নবী রসূলদের মাধ্যমে মানবীয় অধিকার সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করেছেন। মানবজাতির অধিকার নির্ধারণকারী মূলত মানুষের স্রষ্টাই হতে পারেন। সুতরাং মহান স্রষ্টাই মানুষের অধিকারসমূহ বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছেন।
আধুনিক যুগে মানবাধিকার চেতনার ক্রমবিকশ
মানাধিকারের ইসলামী মেনিফেষ্টোর দফাগুলো সম্পর্কে আলোচনা করার পূরেব বর্তমান যুগে মানবাধিকার চেতনার ক্রমবিকাশ ইতিহাসের ওপর সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যুক্তিসঙ্গত হবে।
১.ইংল্যান্ডের রাজা জন ১২১৫ খৃষ্টাব্দে যে ম্যাগনা কারটা জারি করেন তা মূলত ছিলো তার পারিষদবর্গের নির্যাতনের ফল। রাজা এবং পারিষদবর্গের মধ্যে এর মর্যাদা ছিলো একটি চাক্তিপত্রের সমতুল্য। অধিকান্তু তা পারিষদবর্গের স্বার্থ রক্ষার জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের অধিকারের কোনো প্রশ্ন এখানে ছিলোনা। পরবর্তীকালে লোকেরা এর মধ্যে আবিষ্কার করে যে, তা এই সনদ প্র্রণয়নকারীদের সামনে পাঠ করা হলে তারা হয়রান হয়ে যেতো। সপ্তদশ শতকের পেশাদার আইনবিদরা তার মধ্যে আবিষ্কর করলো , বিচার বিভাগের অযথা কয়েদ করার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা এবং কর আরোপ করার ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার অধিকার ইংল্যান্ডের অধিবাসীদের এই সনদের মধ্যে দেয়া হয়েছে।
২.টম পেনের [Paine Thomas-1737-1809] মানবাধিকার [Right of man] নামক পুস্তিকা পাশ্চাত্যবাসীদের চিন্তাধারায় ব্যাপক বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করে। তার এই পুস্তিকা [১৭১৯] পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মানবাধিকারের ধারণাকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়। এই ব্যক্তি আসমানী কোনো ধর্মের সমর্থন ছিলেননা। আর তার যুগটাও ছিলো আসমানী ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যুগ। এজন্য পাশ্চাত্যের জনগণ মনে করে বসলো আসমানী ধর্মগুলোতে মানবাধিকার সম্পর্কে কোনো বক্তব্য নেই।
৩. ফরাসী বিপ্লবের ঘটনাবলীর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে “মানবাধিকার ঘোষণা” [Declaration of the Rights of man] যা ১৭৮৯ সালে প্রকাশ পায়। এটা অষ্টাদশ শতকের সমাজদর্শন এবং বিশেষ করে রুশোর “সামাজিক আচরণ তত্ত্বের” [Social contact theory] ফল। এতে জাতীয় সরকার, স্বাধীনতা, সাম্য এবং মালিকানার স্বাভাবিক অধিকার সমর্থন করা হয়েছে। এতে ভোট দানের অধিকার, আইন প্রণয়ন এবং কর আরোপ করার এখতিয়ারের ওপর জনমতের নিয়ন্ত্রণ, বিচার বিভাগ কর্তৃক অপরাধের কারণ অনুসন্ধান [Trail by jury] ও পর্যালোচনা ইত্যাদির সমর্থন করা হয়েছে।
ফান্সের আইন পরিষদ বিপ্লব যুগে মানবাধিকারের উক্ত ঘোষণাগত্র এই উদ্দেশ্যে প্রণয়ন করেছিল যে, যখন সংবিধান প্রণয়ন করা হবে তখন এটা তার ভূমিকায় সংযোজন করা হবে এবং গোটা সংবিধানে এর ভাবধারা ও প্রাণসত্তাকে উজ্জীবিত রাখা হবে।
৪. মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের [USA] সংবিধানের দশটি সংশোধনীতে বৃটিশ গণতান্ত্রিক দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল মানবাধিকারের প্রায় সবগুলো ধারাই গ্রহণ করা হয়েছে।
৫. যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলো ১৯৪৮ সালে বেগোটা সম্মেলনে ‘মানুষের অধিকারও কর্তব্য’ সম্পর্কিত যে ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে তাও যথেষ্ট গুরুত্বের অধিকারী।
৬. জাতিসংঘ [UNO] গণতান্ত্রিক দর্শনের অধীনে অর্যায়ক্রমে অনেকগুলো ইতিবাচক ও সংরক্ষণমূলক অধিকার সম্পর্কে প্রস্তাব পাশ করে। পরিশেষে তা “মানবাধিকারের ঘোষণাপত্র” নামে সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়।
১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ একটি প্রস্তাব পাশ করে। এতে গণহত্যা বা অন্য যে কোনো উপায়ে জাতি বা সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধনের [Genocide] চেষ্টাকে আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে চরম অপরাধ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।
পুনরায় ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে গণহত্যার প্রতিরোধ এবং শাস্তি প্রদানের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করা হয় এবং ১৯৫১ সালের ১২ জানয়ারী তা কর্যকর হয়। তাতে গণহত্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছেঃ কোনো জাতি, সম্প্রদায়, ধর্মীয় সম্প্রদয় অথবা এর কোনো একটি অংশকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য নিন্মে উল্লেখিত যে কোনো পন্থা অবলম্বন করাঃ
ক. এই ধরনের কোনো সম্প্রদায়ের লোকদের হত্যা করা।
খ. তাদেরকে কঠোর দৈহিক অথবা মানসিক শাস্তি দেয়া।
গ. উদ্দেশ্যমূরকভাবে এ ধরনের কোনো সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রায় এমন পরিস্থিতি চাপিয়ে দেয়া যা তাদের দৈহিক অস্তিত্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অথবা আংশিকভাবে ধ্বংসকর হবে।
ঘ. এই সম্প্রদায়ের সংশধারা রোধ করার জন্য স্বৈরাচারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
ঙ. জবরদস্তীমূলকভাবে এই সম্প্রদায়ের সন্তানদের অন্য কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থানান্তর করা।
১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর যে “মানবাধিকারের মহাসনদ” পাশ করা হয় তার ভূমিকায় অন্যান্য সংকল্পের সাথে মোটামুভাবে এও প্রকাশ করা হয় যে, “মৌলিক মানবধিকারের ক্ষেত্রে মানবজাতির মান সম্মান ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে পুরুষ এবং নারীদের সমঅধিকারের ধর্মীয় বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার জন্য।”
অনন্তর উক্ত ভূমিকায় জাতিসংঘের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, “মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রতিষ্ঠার জন্য এবং জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতিকে মৌলিক স্বাধিকার প্রদানের কাজে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা লাভ।”
অনুরূপভাবে উক্ত সনদের ৫৫ ধারায় জাতিসংঘের এই ঘোষণাপত্র বলছেঃ “জাতিসংঘ পরিষদ মানবধিকার এবং সবার জন্য মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বব্যাপী সম্মান এবং সংরক্ষণে ব্যাপকতা আনয়ন করে।”
এই ঘোষণাপত্রের কোনো একটি অংশ নিয়েও কোনো দেশের প্রতিনিধিই দ্বিমত পোষণ করেননি। দ্বিমত পোষণ না করার কারণ ছিলো এই যে, এটা ছিলো সাধারণ মূলনীতিসমূহের ঘোষণা এবং প্রকাশ মাত্র। কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা কারো ওপর আরোপ করা হয়নি। এটা এমন কোনো চুক্তি নয় যার ভিত্তিতে স্বাক্ষর দানকারী রাষ্ট্রগুলো এর আনুগত্য করতে বাধ্য হয় এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী তাদের ওপর আইনগত বাধ্যবাধকাত আরোপ হতে পারে। তাতে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, এটা একটা মানদন্ড যে পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা করা উচিত। তাতে উপরন্তু কোনো কোনো দেশ এর সপক্ষে অথবা বিপক্ষে ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকে।
এখন দেখুন এই ঘোষণাপত্রের ছত্রছায়ায় সারা দুনিয়াব্যাপী মানবতার একেবারে প্রাথমিক অধিকারসমূহের নির্বেচার হত্যা চলছে। স্বয়ং সভ্যতার চরম শিখরে উন্নিত হওয়ার দাবীদার এবং দুনিয়ার নেতৃত্বদানকারী দেশগুলোর অভ্যন্তরে মানবাধিকারের নির্বিচার গণহত্যা চলছে।
অথচ তারাই এ সনদ পাশ করিয়েছিলেন।
এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, [এক] পশ্চিমা জগতের কাছে মানবাধিকার ধারণা সংক্রান্ত দুই তিন শতাদ্বী পূর্বের কোনো ইতিহাস নেই। [দুই] আজ যদিও এসব অধিাকরের উল্লেখ করা হচ্ছে, কিন্তু তার পিছনে কোনো সনদ [Sanction] এবং কোনো কার্যকরকারী শক্তি [Authority] নেই। বরং এটা শুধু চিত্তাকর্ষক অভিলাষ মাত্র। এর বিপরীতে ইসলাম কুরআন মজীদে মানবাধিকারের যে ঘোষণাপত্র দিয়েছে এবং যার সংক্ষিপ্তসার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জ্বের মাহাসম্মেলনে ঘোষণা করেছেন তা উল্লেখিত সনদগুলোর তুলনায় অধিক প্রাচিন একান্তই বাধ্য। তাছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বাস্তবে তা কার্যকর করে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ইসলাম মানুষকে যেসব অধিকার দান করেছে এখন আমি তা সংক্ষেপে আলোচনা করবো।
১. জীবনের মর্যাদা এবং বাঁচার অধিকার
কুরআন মজীদে দুনিয়ার সর্বপ্রথম হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ছিলো মানবজাতির ইতিহাসের সর্বপ্রথম দুর্ঘটনা এতে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির জীবন সংহার করেছে। এ সময় প্রথম বারের মতো মানুষকে তাদের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধের শিক্ষা দেয়ার এবং প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তোলার প্রয়োজন দেখা দিলো। কুরআন এই ঘটনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছেঃ
“যে ব্যক্তি হত্যার অপরাধ কিংবা বিশ্বে বিপর্যয় সৃষ্টির অপরাধ ছাড়া অপর ব্যক্তিকে হত্যা করলো, সে যেনো গোটা মানব জাতিকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি তাকে বাঁচিয়ে রাখালো সে যোনো গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখলো।” [সূরা ময়েদাঃ ৩২]
কুরআন মজীদ উল্লেখিত আয়াতে একটি মাত্র মানুষেকে হত্যা করার অপরাধকে গোটা মানব জগতকে হত্যা করার সমতুল্য অপরাধ গণ্য করেছে এবং এর বিপরীতে একজন মানুষকে বাঁচিয়ে রাখাকে গোটা মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমান গণ্য করেছে। ‘আহ্ইয়া’ শব্দের অর্থ হচ্ছে জীবিত করা। অন্য কথায় বলা যায় যে, ব্যক্তি মানুষের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলো সে তাকে জীবন্ত করার কাজ করলো। এই প্রচেষ্টাকে সমগ্র মানব জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার সমতুল্য সৎকাজ কলে গণ্য করা হয়েছে। এই মূলনীতি থেকে দু’টি বিষয়কে ব্যতিক্রম করা হয়েছেঃ
এক. যদি কোনো ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে তাহলে তাকে কিসাসের আওতায় মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে।
দুই. কোনো ব্যাক্তি পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করলে তকেও মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। এসব অবস্থা ছাড়া মানুষের জীবনকে ধ্বংস করা যেতে পারেনা।
মানুষের জীবনের নিরাপত্তার এই নীতিমালা মানবেতিহাসের সূচনা লগ্নেই আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন। মানব জতি সম্পর্কে এ ধারণা করা সম্পূর্ণ ভুল যে অন্ধকারের মধ্যেই তার যাত্রা শুরু হয়েছে এবং নিজের সমজাতীয় প্রাণীদের হত্যা করতে করতে কোনো এক পর্যায়ে সে চিন্তা করলো মানুষ খুন উচিত নয়। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং আল্লাহ্ তায়ালা সম্পর্কে সংশয়ের ওপর ভিত্তিশীল। কুরআন আমাদের বলছে, আল্লাহ্ তায়ালা মানব জাতির গোড়াপত্তন থেকেই তাদের পথপ্রদর্শন করে আসছেন। তিনি মানুষকে মানুষের অধিকারের সাথেও যে পরিচয় করিয়েছেন, তাও এই পথপ্রদর্শনের মধ্যে শামিল রয়েছে।
২. অক্ষম ও দুর্বলদের নিরাপত্তা
দ্বিতীয় যে কথা কুরআন থেকে জানা যায় এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে তা হচ্ছে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং রুগ্নদের ওপর কোনো অবস্থাতেই হাত উঠানো বৈধ নয়। চাই সে নিজের জাতির হোক অথবা শত্রু পক্ষের। তবে এদের মধ্যে যারা সরাসরি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তাদের কথা স্বতন্ত্র। অন্যথায় তাদের ওপর অন্য কোনো অবস্থায় হাত তোলা নিষেধ। এই মূলনীতি কেবল নিজের জাতির জন্যই নিদিষ্ট নয়, বরং সমগ্র মানব জতির সাথেই এই নীতি অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে ব্যাপক পথনির্দেশ দান করেছেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের অবস্থা ছিলো এই যে, তাঁরা যখন শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান সেনাবাহিনী পাঠাতেন তখন তাঁরা গোটা বাহিনীকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতেনঃ শত্রুদের ওপর আক্রমণকালীন অবস্থায় কোনো নারী, শিশু, বৃদ্ধ, আহত এবং অসুস্থ ব্যক্তিদের ওপর হাত তোলা যাবেনা।
৩. মাহিলাদের মান সম্ভ্রমের হিফাযত
কুরআন থেকে আমরা আরো একটি মূলনীতি জানতে পারি এবং হাদীসেও তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ রয়েছে। তা হচ্ছঃ যে কোনো অবস্থায় নারীদের সতীত্ব, পরিত্রতা ও মান সম্ভ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যাবশ্যক। অর্থাৎ যুদ্ধের মাঠে যদি শত্রু পক্ষের কোনো নারী সামনে এসে যায় তাহলে কোনো মুসলিম সৈনিকের জন্য তাকে স্পর্শ জায়েয নয়। কুরআনের দৃষ্টিতে যেনা ব্যভিচার সাধারণত হারাম তা যে কোনো মাহিলার সাথেই করা হোক, চাই সে নারী মুসলমান হোক অথবা অমুসলিম, নিজ সম্প্রদায়ের হোক
অথবা ভিন্ন সম্প্রদায়ের, মিত্র রাষ্ট্রের হোক অথবা শত্রু রাষ্ট্রের।
৪.অর্থনৈতিক নিরাপত্ত
একটি মৌলনীতে হচ্ছে এই যে, ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে যে কোনো অবস্থায় খাদ্য দান করতে হবে। উলংগ ব্যক্তিকে যে কোনো অবস্থায় বস্ত্র দিতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির জন্য যে কোনো অবস্থায় চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে হবে, চাই তারা শত্রু হোক অথবা বন্ধু। এটা চিরন্তন [Universall] অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। দুশমনদের সাথেও আমরা এই ব্যবহার করবো। শত্রু পক্ষের কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের কাছে চলে আসে, তাহলে তাকে ক্ষুধার্ত, উলংগ না রাখা আমাদের জন্য ফরয। যদি সে আহত অথবা রুগ্ন হয় তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।
৫. সুবিচার
কুরআন করীমের স্থায়ী নীতি হলো, মানুষের সাথে আদল ও সুবিচার করতে হবে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
“কোনো বিশেষ দলের শত্রুতা তোমাদের যেনো এতোটা উত্তেজিত না করে [যার ফলে] তোমরা সুবিচার ত্যাগ করে ফেলবে। ন্যায়বিচার করো। বস্তুত খোদাভীতির সাথে এর গভীর নৈকট্য ও সামঞ্জস্য রয়েছে।” [সূরা মায়েদাঃ ৮]
এ আয়াতে ইসলাম এই নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, মানুষকে ব্যক্তি, সমাজ, জাতি নির্বিশেষে সবার সাথে যে কোনো অবস্থায় সুবিচার করতে হবে। আমরা বন্ধুদের সাথে সুবিচার করাবো আর শত্রুদের ক্ষেত্রে এই নীতি বিসর্জন দেবো ইসলামে তা চূড়ান্তভাবেই নিষিদ্ধ।
৬. সৎ কজে সহযোগিতা অসৎ কাজে অসহযোগিতা
কুরআন মজীদের নির্ধারিত আরেকটি মূলনীতি হচ্চেঃ সৎ কাজে এবং অধিকার পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে প্রত্যেকের সাথে সহযোগিতা করতে হবে আর খারাপ কাজ ও যুলুমের ক্ষেত্রে কারোরই সহযোগিতা করা যাবেনা। নিজের ভাইও যদি খারাপ কাজ করে তবে আমরা তার সহযোগিতা করবোনা। আর ভালো কাজ যদি দুশমনরাও করে তাহলে তাদের প্রতি সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দেবো। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
“ন্যায় ও খোদাভীতিমূলক কাজে সবাইর সহযোগিতা করো এবং যা সীসালংঘনমূলক ও গুনাহের কাজ তাতে করো সহযোগিতা করোনা।” [সূরা মায়েদাঃ২]
এ আয়াতে সৎ, ন্যায় ও ভালো কাজ বুঝাবার জন্যে ‘বির’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।
এ ‘বির’ শব্দের অর্থ কেবল সৎকাজই নয় বরং আরবী ভাষার এ শব্দ ‘অধিকার পৌঁছে দেয়ার’ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ অন্যের প্রাপ্য অধিকার প্রদান, তাকওয়া ও খোদাভীতির কাজে আমরা প্রত্যেকেরই সহযোগিতা করবো। এটা কুরআনের স্থায়ী মূলনীতি।
৭. সমতার অধিকার
আরো একটি মূলনীতি যা কুরআন মজীদ জোরেসোরে বর্ণনা করেছে। তা হচ্ছে সব মানুষ সমান। যদি কারো প্রধান্য থেকে তাহলে এটা নির্ধারিত হবে চরিত্র ও নৈতিকতার মাপকাঠিতে। এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছেঃ
“হে মানুষ! আমরা তোমাদের একজন পুরুষ এবং একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও গোত্রে এজন্য বিভক্ত করেছি যেনো তোমরা পরস্পরকে কাছে সর্বাধিক সম্মনিত।”[সূরা হুজরতঃ ১৩]
এ আয়াতে প্রথম কথা বলা হয়েছে, গোটা মানব জাতি একই মূল থেকে উৎসারিত। বংশ, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদির পার্থক্য মানব জাতিকে বিভক্ত করার জন্য মূলত কোনো যুক্তিযুক্ত কারণই নয়।
দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে, আমরা এই জাতিগত বন্টন পরিচয় লাভের জন্য করেছি। অন্য কথায় এক গোষ্ঠী, এক গোত্রের এবং এক জাতির লোকদের অন্যদের ওপর এমন কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই যে তারা নিজেদের অধিাকারের তালিকা দীর্ঘায়িত করবে এবং অন্যদের তালিকা সংকুচিত করবে। আল্লাহ্ তায়ালা এই যে পার্থক্য করেছেন, পরস্পরের দৈহিক কাঠামো ভিন্ন ভিন্ন বানিয়েছেন, ভাষায় প্রার্থক্য রেখেছেন, এসব কিছু গৌরব ও অহংকারের জন্য নয় বরং পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টি করার জন্যই তা করেছেন। যদি সমস্ত মানুষ একই রকম হতো তাহলে পার্থাক্য করা যেতো না। এদিক থেকে এই বিভক্তি প্রকৃতিগত, কিন্তু অন্যদের অধিকার আত্মসাত করা এবং অনর্থক স্বাতন্ত্র্যবোধ প্রতিষ্ঠার জন্য নয়। সম্মান ও গৌরবের ভিত্তি নৈতিক অবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ভিন্ন পন্থায় বর্ণনা করেছেন।
“কোনো অনারবের ওপর কোনো আরবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই এবং কোনো আরবের ওপরও কোনো অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই। কিন্তু তাকওয়ার ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব হতে পারে। বংশের ভিত্তিতেও কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই।
অর্থাৎ দীনদারী, সততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতেই শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণিত হয়। এমন তো নয় যে, কোনো ব্যক্তিকে রূপা দিয়ে, কোনো ব্যক্তিকে পাথর দিয়ে আর কোনো ব্যক্তিকে মাটি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে, বরং সমস্ত মানুষ এক।১.[১ ফেরউনী ব্যাবস্থাকে কুরআন মজীদ যেসব কারণে বাতিল সাব্যস্ত করেছে তার একটি এই যেঃ “নিশ্চয়ই ফেরাউন যমীনের বুকে দুর্বিনীত হয়ে পড়েছিলো এবং দেশের জনগণকে দলে উপদেলে বিভক্ত করে দিয়েছিল। তাদের একদলকে (বনী ইসলাঈল) সে এতাটা দুর্বল করে দিয়েছিল যে ….।” (সূরা কাসাসঃ ৪)
অর্থাৎ ইসলাম এই নীতির পোষাকতা করেনা যে, কোন সামাজে মানুষকে উচ্চ শ্রেণী এবং নিন্ম শ্রেণী অথবা শাসক ও শাসিত শ্রেণীতে বিভক্ত করে রাখা হবে।]
৮. পাপাচার থেকে বাঁচার অধিকার
আরেকটি মূলনীতে হচ্ছে, কোনো ব্যাক্তিকে পাপের কাজ করার নির্দেশ দেয়া যাবেনা এবং কোনো ব্যক্তিকে যদি খারাপ কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয় তাহলে এই নির্দেশ পালন করা তার জন্য বাধ্যতামূলকও নয় এবং বৈধও নয়। যদি কোনো অফিসার তার অধীনস্থ কর্মচারীকে নাজায়েয কাজ করার নির্দেশ দেয়, অথবা কারো ওপর হাত তোলার নির্দেশ দেয়, তাহলে এ ক্ষেত্রে কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী অধীনস্থ কর্মচারীর জন্য তার ঊর্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ পালন করা বা তার আনুগত্য করা মোটেই জায়েয নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, স্রষ্টা যেসব জিনিসকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন এবং অপরাধ বলে সাব্যস্ত করেছেন সুগুলো করার জন্য কেউ কাউকে নির্দেশ দেয়ার অধিকার রাখেনা। কোনো নির্দেশদাতার জন্যও এরূপ কাজের নির্দেশ দেয়া বৈধ নয় এবং এ ধরনের নির্দেশ পালন করাও কারো পক্ষে বৈধ নয়।
৯.যালিমের অনুগত্য করতে অস্বীকার করার অধিকার
ইসলামের একটি মহান নীতি হলো, কোনো যালিমের আনুগত্য দাবী করার অধিকার নেই। কুরআনে করীমে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তায়ালা ইবরাহীম আলাইহিস্ সালামকে নেতৃত্বেরপদে নিয়োগ করে বললেনঃ “ আমি তোমাকে মানুষের নেতা নিযুক্ত করেছি।” তখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্ সালাম আল্লাহ্র কাছে আরয করলেন, “আমার বংশধরদের জন্যও কি এই ওয়াদা?” আল্লাহ্ তায়ালা জবাবে বললেনঃ “যালিমদের ক্ষেত্রে আমার এ ধরনের ওয়াদা নেই।”২. [২ সূরা বাকারাঃ ১১৪] ইংরেজী ভাষায় Letter of Appointment- এর যে অর্থ এখানে ‘আহদুন’ শব্দটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাংলায় এর অর্থ নিয়োগপত্র। এ আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন, ‘যালিমদের এরূপ কোনো নিয়োগপত্র দেয়া হয়নি যার ভিত্তিতে সে অন্যদের আনুগত্য দাবী করতে পারে। ৩. [৩ আরো ব্যাখ্যার জন্য এই আয়াতগুলো সামনে রাখুন। অর্থাৎ
ক. “যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি করে সেই লাগামহীন লোকদের আনুগত্য করোনা।” (সূরা শুয়ারাঃ ১৫১) খ. “যে ব্যক্তির দিলকে আমার স্মরণশূন্য করে দিয়েছি তার আনুগত্য করোনা।” (সূরা কাহ্ফঃ ২৮) গ. তাগুতের বন্দেগী থেকে দূরে থাক।” (সূরা নাহলঃ ৩৬) ঘ. “এবং সেই আদ জাতি যারা তাদের প্রতিপালকের নির্দেশ প্রত্যাখান করেছিল, তাঁর রসূলদের আগ্রহ্য করেছিল এবং তারা প্রত্যেকে অবাধ্য স্বৈরাচারীর নির্দেশের অনুসরণ করেছিল।” (সূরা হূদঃ ৫৯)
ইমাম আবু হানীফা (রাঃ) বলেন, কোনো যলিম ব্যক্তির মুসলমানদের নেতা হওয়ার অধিকার নেই। যদি এরূপ ব্যক্তি নেতা হয়ে যায় তাহলে তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। তাকে শুধু সহ্য করা যেতে পারে মাত্র।৪.[৪ এ পর্যায়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্যে গ্রন্থকারের খিলাফত ও রাজতন্ত্র গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।
১০. রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের অধিকার
মানুষের মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে একটি বড় অধিাকর ইসলাম এই নির্দিষ্ট করেছে যে, সমাজের প্রতিটি ব্যক্তি জাতীয় সরকারের অংশীদার। সবার পরামর্শক্রমে সরকার গঠন হতে হবে। কুরআনে বলা হয়েছেঃ
“আল্লাহ্ তায়ালা তাদের (অর্থাৎ ঈমানদারদের) পৃথিবীল বুকে রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করবেন।” [সূরা নূরঃ ৫৫]
এখানে বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, আমরা কতিপয় লোককে নয় বরং গোটা জাতিকে খিলাফত দান করবো। রাষ্ট্র কোনো এক ব্যক্তির বা এক বংশের বা এক শ্রেণীর নয়, বরং গোটা জাতির এবং সমগ্র জনগণের পরামর্শ অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে।
কুরআনে বলা হয়েছেঃ
“এই রাষ্ট্র পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলবে।” [সূরা শূ’রাঃ ৩৮]
এ ব্যাপারে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর পরিষ্কার বক্তব্য মওজূদ রয়েছেঃ “মুসলমানদের সাথে পরামর্শকরা ব্যতিবেকে তাদের শাসন করার অধিকার কারো নেই। তারা যদি সম্মত হয় তাহলে তাদের ওপর শাসন পরিচালনা করা যাবে। আর যদি রাযী না হয় তাহলে তা করা যাবেনা। এই নির্দেশের আলোকে ইসলাম একটি ‘গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকারী ব্যবস্থার নীতি’ নির্ধারণ করে। এটা ভিন্ন ব্যাপার যে, আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী আমাদের ওপর রাজতন্ত্র চেপে রয়েছিল। ইসলাম আমাদের এ ধরনের রাজতন্ত্রের অনুমতি দেয়নি। বরং এটা ছিলো আমাদের আহাম্মকির ফল।
১১. ব্যক্তি স্বাধীনতার সংরক্ষণ
ইসলামের একটি মূলনীতি এই যে, সুবিচার ব্যতিরেকে কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা যাবেনা। হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন “ইসলামের নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া গ্রেফতার করা যাবেনা।” এর পরিপ্রেক্ষিরত আদ্ল ও ইনসাফের সেই দর্শনই কায়েম হয়, যাকে আধুনিক পরিভাষায় Judicial process of law [বিচার বিভাগীয় কার্যপ্রণালী] বলা হয়। অর্থাৎ কারো ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করতে হলে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন, প্রকাশ্য আদালতের তার বিচরকার্য পরিচালনা এবং তাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। এছাড়া কোনো কার্যক্রমের ওপর সুবিচারের বৈশিষ্ট্য আরোপ করা যায়না। এতো সাধারণ জ্ঞানের ব্যাপার যে, অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার সুযোগ না দিয়ে বন্দী করে রাখা ইসলাম অনুমোদন করেনি। ইসলামী রাষ্ট্র, সরকার এবং বিচার বিবাগের জন্য ইনসাফের দাবী পূর্ণ করা কুরআন অত্যাবশ্যকীয় করে দিয়েছে।
১২. ব্যক্তি মালিকানা সংরক্ষণ
ইসলাম ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দেয়। কুরআন আমাদের সামনে ব্যক্তি মালিকানার চিত্র তুলে ধরেছে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
“তোমরা বাতিল পন্থায় একে অপরের সম্পদ আত্মসাৎ করোনা।” [সূরা বাকারাঃ ১৮৮]
কুরআন, হাদীস এবং ফিক্হ অধ্যয়নে জানা যায়, অপরের সম্পদ ভোগ করার কোন্ কোন্ পন্থা ভ্রান্ত। ইসলাম এসব পন্থা অম্পষ্ট রাখেনি। এই মূলনীতির আলোকে কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে অবৈধ পন্থায় মাল হস্তগত করা যাবেনা। কোনো ব্যক্তি বা সরকারের এ অধিকার নেই যে, সে আইন ভঙ্গ করে এবং ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত পন্থাসমূহ ব্যতিরেকে কারো মালিকানার ওপর হস্তক্ষেপ করবে।
১৩. মানসম্ভ্রমের হিফাযত
মান সম্মান ও ইজ্জত আব্রুর হিফাযাত করার মৌলিক অধিকার প্রতিটি মানুসের রয়েছে। সূরা হুজুরাতে এই অধিকারের বিস্তারিত বর্ণনা মওজূদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছেঃ
“তোমাদের কেউ অপরকে ঠাট্রা বিদ্রূপ করবেনা।”
“তোমরা একে অপরকে নিকৃষ্ট উপাধিতে ডিকোনা।”
“একে অপরের দোষ চর্চ করোনা।” [আয়াতঃ ১১,১২]
অর্থাৎ মানুষের মান সম্মানের প্রতি আঘাত করার যতোগুলো পন্থা রয়েছে তা সবই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। পরিষ্কর বলে দেয়া হয়েছে কোনো ব্যক্তি চাই উপস্থিত থাক বা না থাক, তাকে ঠাট্রা বিদ্রূপ করা যাবেনা, তাকে নিকৃষ্ট উপাধি দেয়া যাবেনা। তার ক্ষতি করা যাবেনা এবং তার দোষ চর্চ {গীবত} করা যাবেনা। প্রত্যক ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, কেউ তার ইজ্জতের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। এবং হাতের দ্বারা অথবা যবানের দ্বারা তার ওপর কোনোরূপ বাড়াবাড়ি করতে পারবেনা।
১৪. গোপনীয়তা রক্ষা করার অধিকার
ইসলামের মৌলিক অধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিটি লোক ব্যক্তিগত জীবনের গোপণীয়তা রক্ষা করার অধিকার রাখে। এ ব্যাপারে সূরা নূরে পরিষ্কার বলে দেয়া হয়েছেঃ
“নিজের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করোনা।” (আয়াতঃ ২৭)
সূরা হুজুরাতে বলা হয়েছেঃ
“গোয়েন্দাগিরি করোনা” [আয়াতঃ ২৭]
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীঃ ‘অন্যের ঘরে উকি মারার অধিকার কোনো ব্যক্তির নেই।’ যে কোনো ব্যক্তির আইনগত অধিকার রয়েছে যে, সে তার নিজের ঘরে অপরের শোরগোল, উকিঝুকি এবং অনুপ্রবেশ থেকে নিরাপদ থাকবে। তার সংসারের শান্তি শৃংখলা ও পর্দাপুশিদা রক্ষা করার অধিকার তার রয়েছে। এমনকি কোনো ব্যক্তির চিঠিপত্রের ওপরও
অন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টি নিক্ষেপ করার অধিকার নেই, পড়া তো দূরের কথা। ইসলাম মনুষের ব্যক্তিগত গোপণীয়াতার পূর্ণ হিফাযত করে এবং পরিষ্কারভাবে নিষেধ করে দেয় যে, অন্যের ঘরের মধ্যে উকিঝুকিমারা যাবেনা। কারো ডাক বা চিঠিপত্র দেখা যাবেনা। কিন্তু কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে যদি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানা যায় যে, সে ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত আছে তাহলে স্বতন্ত্র কথা। অন্যথায় কারো পিছনে অযথা গিায়েন্দাগিরে করা ইসলামী জায়েয নেই।
১৫. যুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অধিকার
ইসলাম প্রদত্ত মৌলিক অধিকারের মধ্যে একটি হলো, যে কোনো ব্যক্তি যুলুমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার অধিকার রাখে। মহান আল্লাহ্ বলেনঃ
“মানুষ খারাপ কথা বলুক তা আল্লাহ পছন্দ করেননা। তবে কারো প্রতি যুলুম করা হয়ে থাকলে ভিন্ন কথা।” [সূরা নিসাঃ ১৪৮]
অর্থাৎ যালিমের বিরুদ্ধে মযলুমের সোচ্চার হওয়ার অধিকার রয়েছে।
১৬. মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা
আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাকে বর্তমান যুগে মত প্রকোশের স্বাধীনতা
[Freedom of Expression] বলা হয়, কুরআন তা অন্য পরিভাষায় বর্ণনা করে। কিন্তু দেখুন, তুলনামূলকভাবে কুরআনের দর্শন কতো উন্নত। কুরআনের বাণী হচ্ছে “সত্য ও ন্যায়ের প্রতষ্ঠা” এবং “অন্যায় ও অসত্যের প্রতরোধ” করা কেবল মানুষের অধিকারই নয় বরং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।
“তোমরাই হচ্ছো সর্বোত্তম উম্মহ্ যাদেরকে মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্য কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা ন্যায় কাজের নির্দেশ দাও, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে লোকদের বিরত রাখো।” [সূরা আলে ইমরানঃ১১০]
কুরআনের দৃষ্টিকোণ থেকেও এবং হদীসের বলবে এবং মুতাবিকও মানুষের কর্তব্য হচ্ছে সে লোকদের ভালো কাজ করার কথা বলেবে এবং খারাপ কাজ থেকে তাদের প্রতিরোদ করবে। যদি কোনো খারাপ কাজ সংঘটিত হয় তাহলে এর বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলেই দায়িত্ব শেষ হয়না। বরং এর সূলোৎপাটনের চিন্তা ভাবনা না করা হয় তাহলে উল্ট গুনাহ হবে। ইসলামী সমাজকে পাক পরিত্র রাখা মুসলমানদের উপর ফরয। এ ক্ষেত্রে যদি মুসলমানদের কন্ঠরোধ করা হয়, তাহলে এর চেয়ে বড় আর যুলুম হতে পারেনা। যদি কেউ ভালো কাজের প্রতিরোধ করে তাহলে সে কেবল একটি মৌলিক অধিকারই হরণ করেনি বরং একটি ফরয আদায় করতে বাধা দিচ্ছে। সমাজের স্বাস্থ্য অটুট রাখতে হলে মানুষের সব সময় এ অধিকার থাকতে হবে। কুরআন মজীদ বনী ইসলাঈল জাতির অধপতনের কারণসমূহ বর্ণনা করেছে। তার মধ্যে একটি কারণ এই বর্ণনা করা হয়েছেঃ
“তারা একে অপরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতোনা।” [সূরা মায়েদাঃ৭৯]
অর্থাৎ যদি কোনো জাতির মধ্যে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়ে যায় যে, তাদের মধ্যে দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আওয়ায তোলার মতো কোনো লোক নেই তাহলে শেষ পর্যন্ত গোটা জাতির মধ্যে ক্রমান্বয়ে দুষ্কৃতি ছড়িয়ে পড়ে। পরিশেষে তা একটি শূন্য ঝুড়ির মতো হয়ে যায় যা তুলে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করা হয়। এই রকম জাতি আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হওয়ার আর কোনো ঘাটতিই অবশিষ্ট থাকেনা।
১৭. বিবেক ও আকীদা বিশ্বাসের স্বাধীনতা
ইসলাম মানব জাতিকে “দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই” [সূরা বাকারাঃ ২৫৬] এই সূলনীতি দান করেছে। এর অধীনে সে প্রতিটি মানুষকে কুফর অথবা ঈমান, এর যে কোনো একটি পথ অবলম্বন করার ইখতিয়ার দিয়েছে। ইসলাম যদি শক্তির প্রয়োগ থেকে থাকে তাহলে দু‘টি প্রয়োজনে। এক. ইসলামী ব্যবস্থা, সামাজিক শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং দুষ্কৃতি ও বিচ্ছিন্নতার মূলোৎপাটনের জন্য বিচার বিভাগীয় এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ।
লক্ষ্য ও আকীদা বিশ্বাসের স্বাধীনতাই ছিলো মূল্যবান অধিকার যা অর্জন করার জন্য মক্কার তের বছরের বিপদ সংকূল যুগে মুসলামানরা মার খেয়ে খেয়ে সত্যের কালেমা সমুন্নত করেছে। অবশেষে যেভাবে অর্জন করেছে, অনুরূপভাবে অন্যদের জন্যও এর পূর্ণ স্বীকৃতি দান করেছে। মুসলমানরা নিজেদের অমুসলিম প্রজাদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করছে, অথবা কোনো জাতিকে নির্যাতন করে কালেমা পড়তে বাধ্য করেছে ইসলামের ইতিহাসে এমন কোনো দৃষ্টান্ত নেই।
১৮. ধর্মীয় মানসিক নির্যাতন থেকে সংরক্ষণ
ইসলাম এটা কখনো সমর্থন করেনা যে, বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় একে অপরের বিরুদ্ধে কটুবাক্য ব্যবাহার করেবে, একে অপরের ধর্মীয় নেতাদের বিরুদ্ধে কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ি করবে। কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছেঃ
“এসব লোক আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদের মা’বূদ বানিয়ে ডাকে তোমরা তাদের গালাগালি করোনা।” [সূরা আনয়ামঃ১০৮]
অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্ম ও আকীদা বিশ্বাসের ওপর যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা, যুক্তিরপন্থায় সমালোচনা করা অথবা মতভেদ ব্যক্ত করা তো বাক স্বাধীনতার অন্তুর্ভুক্ত। কিন্তু মনে কষ্ট দেয়ার জন্য অভদ্র ভাষায় কথা বলা মোটেও সমীচীন নয়।
১৯. সভা সংগঠন করার অধিকার
বাক স্বাধীনাতার দার্শনিক ফলশ্রুতিই সভা সমিতি করার অধিকারের সূত্রপাত হয়। মতবৈষম্যকে মানব জীবনের একটি বাস্তব সত্য হিসেবে কুরআন বারবার ঘোষণা করেছে। তাহলে মতভেদ সৃষ্টি হওয়াকে কিভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব? সব লোক একই মত পোষণ করে কিভাবে একত্রিত হতে পারে? একই মূলনীতি এবং দৃষ্টিভংগির অধিকারী একটি জাতির মধ্যেও বিভিন্ন মাযহাব [School of thoughts] হতে পারে। এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অবশ্য পরস্পরের কাছাকাছিই থাকবে। কুরআনের বাণীঃ
“তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে।” [সূরা আলে ইমরানঃ ১০৪]
কর্মসয় জীবনে যখন ‘কল্যাণ’ ‘অন্যায়’ এর ব্যাপক ধারণার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয় তখন জাতির মৌলিক অখন্ডতা অটুট রেখেও তার মধ্যে বিভিন্ন চৈন্তিক গোষ্ঠীর উদ্ভাব হয়ে থাকে। একথা কাংখিত মানের যতো নিচেই হোক দল উপদলের আত্মপ্রকাশ ঘটছেই। সুতরাং আমাদের এখানে কথাবার্তায়, ফিকহ্ ও আইন কানুন এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগির ক্ষেত্রেও মতবিরোধ হয়েছে এবং সাথে সাথে বিভিন্ন দল উপদল অস্তিত্ব লাভ করেছে।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী সংবিধান এবঙ মানবাধিকারের ঘোষণাপত্রের দৃষ্টিতে বিভিন্ন দল উপদলগুলোর সভা সমিতি করার অধিকার আছে কি? এই প্রশ্ন সর্বপ্রথম হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সামনে খারিজী সম্প্রদায়ের আত্মপ্রকাশের পর উঠেছিল। তিনি তাদের সংগঠন ও সভা সমিতি করার অধিকার স্বীকার করে নেন। তিনি খারিজীদের বলেন, “তোমরা যতক্ষণ তরবারির সাহায্য নিজেদের মতবাদ অন্যের ওপর চাপাতে চেষ্টা না করবে তোমরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে।”
২০. একের অপরাধের জন্য অন্যকে দায়ী করা যাবেনা।
ইসলামে যে কোনো ব্যক্তিকে কেবল নিজের কার্যকলাপ এবং নিজের অপরাধের জন্যই জবাবদিহি করতে হয়। অপরের কার্যকলাপ ও অপরাধের জন্য তাকে গ্রেফতার করা যায়না। কুরআন এই নীতি নির্ধারণ করেছে যেঃ
“কোনো ভার বহনকারীই অপর কারো ভার বহন করতে বাধ্য নয়।” [সূরা আনয়ামঃ১৬৪]
অপরাধ করবে দাড়িওয়ালা আর আত্মরক্ষার এ অধিকার রয়েছে যে, তদন্ত ও অনুসন্ধান ছাড়া তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া যাবেনা। এ ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, কারো বিরুদ্ধে কিছু অবগত হলে তদন্ত করে নাও। এরূপ যেনো না হতে পারে যে, কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অজ্ঞাতসারে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে বসো। কুরআনে বলা হয়েছেঃ
“ হে ঈমানদারগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি তোমরাদের কাছে কোনো খবর নিয়ে এলে তার সত্যতা যাচাই করে নিও। এমন যেনো না হয় যে, তোমরা অজ্ঞাতসারে কোনো মানব গোষ্ঠীর ক্ষতি সাধন করে বসবে, আর নিজেদের কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হবে।” [সূরা হুজুরাতঃ ৬]
উপরন্তু কুরআন এ হিদায়াতও দান করা হয়েছেঃ
“খুব বেশী খারাপ ধারণা পোষণ থেকে বিরত থাকো।” [সূরা হুজুরাতঃ ১২]
সংক্ষেপে এই হচ্ছে সেই সব মৌলিক অধিকার ইসলাম যা মানব জাতিকে দান করেছে। এর দর্শন সম্পুর্ণ পরিষ্কার এবং পরিপূর্ণ যা মানুষকে তার জীবনের সূচনাতেই বলে দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বর্তমান সময়েও দুনিয়াতে মানবাধিকারের যে ঘোষণা [Declaration of Human Rights] প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তার না আছে কোনো প্রকারের স্বীকৃতি আর না আছে কার্যকর হওয়ার শক্তি। ব্যস একটি উন্নত মানদন্ড পেশ করা হয়েছে, কিন্তু এই মানদন্ড অনুযায়ী কাজ করতে কোনো জাতিই বাধ্য নয়। এটা এমন কোনো সর্বজন গ্রাহ্য চুক্তিপত্রও নয় যা সকল জাতির কাছ থেকে এসব অধিকার আদায় করে দিতে পারে। কিন্তু মুসলমানদের ব্যাপার সম্পূর্ণ ভিন্ন, তারা আল্লাহ্র কিতাব এবং তাঁর রসূলের হিদায়াতের আনুগত্যকারী আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল মৌলিক অধিকারসমূহের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যে রাস্ট্রই ইসলামী রাষ্ট্র হতে চায় তাকে এ অধিকারগুলো অবশ্যই লোকদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মুসলমানদের ও এ অধিকার দিতে হবে এবং অমুসলমানদেরও। এ ক্ষেত্রে এমন কোনো চুক্তিপত্রের প্রয়োজন নেই যে, অমুক জাতি আমাদের যদি এই অধিকার দেয়, তাহলে আমরাও তাদের দেব। বরং মুসলমানরা এ অধিকার দিতে বাধ্য শত্রুকেও মিত্রকেও।
ত্রয়োদশ অধ্যায়
অমুসলিমদের অধিকার
শাসনতান্ত্রিক সমস্যাগুলোর মধ্যে সংখ্যালঘু সংক্রান্ত সমস্যা সবচেয়ে জটিল। এ ব্যাপারে অনেক ভুল বুঝাবুঝি পরিক্ষিত হয় এবং সেজন্য মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যাপক আকার ধারণ করছে। মাওলানা আবুল আ’লা মওদূদী এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন এবং এর সকল দিক বিশ্লেষণ করে বলেন, মাওলানা সাহেবের সে নিবন্ধটাই দিনি স্বয়ং সম্পাদনা করে দেয়ার পর প্রকাশ করা হচ্ছে। এটি ১৯৪৮ সালের আগষ্ট মাসের তরজমানুল কুরআন থেকে নেয়া হয়েছে। এতে একদিকে অমুসলিমদের সাংবিদানিক অবস্থান মুসলিম সমাজের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলিই হচ্ছে অমুসলিমদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণের নির্দেশক মূলনীতি। সংকলক।
অমুসলিমদের অধিকার
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এ কথা বুঝে নেয়া দরকার যে, ইসলামী রাষ্ট্র আসলে একটা আর্দমবাদী [Ideologica] রাষ্ট্র এবং তার ধারণ ও প্রকৃতি একটা জাতীয় গণতান্ত্রিক[National Denocratic] রাষ্ট্র থেকে একেবারেই ভিন্ন। এই উভয় ধরনের রাষ্ট্রের উক্ত প্রকৃতিগত পার্থক্যের দরুন আলোচ্য বিষয়ের ওপর কিরূপ পড়ে, সেটা নিন্মোক্ত বক্তব্যসমূহ দ্বারা ভালোভাবে বুঝা যাবে।
১. যে আর্দশ ও সূলনীতির ওপর ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, তাকে কে মানে আর কে মানেনা, সে হিসেবেই ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় নাগরিকদের বিভক্ত করে থাক। ইসলামী পরিভাষার উক্ত দুই ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে মুসলিম ও অমুসলিম বলা হয়ে থাকে।
১. যে জাতি মূলত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক, কারা সেই জাতির বংমোদ্ভুত আর কারা তা নয়, তার ভিত্তিতেই একটা জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় নাগরিকদেরকে বিভক্ত করে ফেলে। আধুনিক পরিভাষায় উক্ত দু’ধরনের জনগোষ্ঠীকে যথাক্রমে সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু বালা হয়ে থাকে।
২. ইসলামী রাষ্ট্র চালানো আসলে তার আদর্শ ও মূলনীতিতে যারা বিশ্বাসী তাদের কাজ। এ রাষ্ট্র স্বীয় প্রশাসনে অমুসলিমদের সেবা গ্রহণ করতে পারে বটে, তবে নীতি নির্ধারক ও প্রশাসনের পদ তাদের পদ তাদের দিতে পারেনা।
২. জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় নীতি নির্ধারণ প্রশাসনের কাজে শুধু আপন জতির লোকদের ওপরই নির্ভর করে। অন্যান্য সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে এ ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য মনে করা হয়না। এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা না হলেও কার্যত এটাই হয়ে থাকে। সংখ্যালঘুদের কোনো ব্যক্তিকে যদি কখনো কোনো শীর্ষ স্থানীয় পদ দেয়াও হয়, তবে তা নিছক লোক দেখানো ব্যাপার হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তার কোনোই ভূমিকা থাকেনা।
৩. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতিই এমন যে, সে মুসলিম ও অমুসলিমদের সুস্পষ্টভাবে দু’ভাগে বিভক্ত করতে বাধ্য। অমুসলিমদের কি কি অধিকার দিতে পারবে আর কি কি অধিকার দিতে পাবেনা তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাড়ায়।
৩. জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ দ্বিমূখী আচরণ করা নিতান্তই সহজ কাজ যে , সে দেশের সকল অধিবাসীকে নীতিগতভবে সকল জাতি আখ্যায়িত করে কাগজে কলমে সকলকে সমান অধিকার দিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যত সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুর ভেদাভেদ পুরোপুরি বহাল রাখবে এবং সংখ্যালঘুদের বাস্তবিক পক্ষে কোনো অধিকারই দেবেনা।
৪. ইসলামী রাষ্ট্র স্বীয় প্রমাসনে অমুসলিমের উপস্থিতি জটিলতার সমাধান এভবে করে যে, তাদেরকে সুনির্দিষ্ট অঙ্গিকারের কার্যকর নিশ্চয়তা [Guaranteel] দিয়ে সন্তুষ্ট করে দেয়। নিজেদের নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থাপনায় তাদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করে এবং তাদের জন্য সব সময় এ ব্যাপারে দরজা খোলা রাকে যে, ইসলামী আদর্শ যদি তাদের ভালো লেগে যায় তাহলে তারা তা গ্রহণ করে শাসক দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।
৪. একটি জাতীয় রাষ্ট্র স্বীয় রাষ্ট্রকাঠামোতে বিজাতীয় লোকদের উপস্থিতিজনিত জটিলতার সমাধান তিন উপায় করে। প্রথমত, তাদরে স্বতন্ত্র জাতি সত্তাকে ক্রমান্বয়ে বিলুপ্ত করে নিজেদের জাতি সত্তাঃয় বিলীন করে নেয়। দ্বিতীয়তঃ তাদের জাতি সত্তাকে নির্মূল কারার জন্য হত্যা, লুটতরাজ ও দেশান্তরীকরণের নিপীড়ন মূলক কর্মপন্থা অবলম্বন করে। তৃতীয়তঃ তাদেরকে নিজেদের ভেতরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বানিয়ে রেখে দেয়। দুনিয়ার জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোতে এই তিনটে কর্মপন্থা ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছে এবং এখনও গৃহীত হয়ে চলেছে। আজকের ভারতে খোদ মুসলমানদেরকে এ সব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার তিক্ত অভিজ্ঞতার সন্মূখীন হতে হচ্ছে।
৫. ইসলামী রাষ্ট্র অমুসলিম সংখ্যালঘু নাগরিকদেরকে শরীয়ত প্রদত্ত অধিকারগুলো দিতে বাধ্য। এসব অধিকার কেড়ে নেয়া বা কমবেশী করার এখতিয়ার কারো নেই। এসব অধিকার ছাড়া অতিরিক্ত কিছু অধিকার যদি মুসলমানরা দিতে চায় তবে ইসলামের মূলনীতির পরিপন্থী না হলে তা দিতে পারে।
৫. জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদেরকে যে অধিকারই দেয়া হয় তা সংখ্যাগুরুর দেয়া অধিকার। সংখ্যাগুরুর ওসব অধিকার যেমন দিতে পারে তেমনি তাতে কমবেশী করা একেবারে ছিনিয়ে নেয়ারও অধিকার রাখে এ ধরনের রাস্ট্রে সংখ্যালঘুরা পূরোপূরিভাবে সংখ্যাগুরুর করুনার ওপর নির্ভন করে বেঁচে থাকে। তাদের জন্য মৌলিক মানবাধিকারের পর্যন্ত কোনো স্থায়ী নিশ্চয়তা থাকেনা।
উল্লিখিত মৌলিক পার্থক্যগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভবে বুঝা যায় যে, অমুসলিম সংখ্যালঘুদের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের আচরণ এবং সংখ্যালঘু জাতিসত্তার সাথে জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আচরণে কি আকাশ পাতাল ব্যবধান। এ ব্যবধানকে বিবেচনায় না আনলে মানুষ এই ভুল বুঝাবুঝি থেকে মুক্ত হবেনা যে, আধুনিক যুগের জাতীয় সংকীর্ণতার পরিচয় দেয়।
এই অত্যাবশ্যকীয় বিশ্লেষণের পর আমি মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যেতে চাই।
১. অমুসলিম নাগরিকরা কতো প্রকারের?
ইসলামী আইন স্বীয় অমুসলিম নাগরিকদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেঃ
এক. যারা কোনো সন্ধিপত্র বা চুক্তি বলে ইসলামী রাষ্ট্রের আওতাভুক্ত হয়েছে।
দুই. যারা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।
তিন. যারা যুদ্ধ কিংবা সন্ধি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
যদিও উক্ত তিন প্রকারের নাগরিকরাই সংখ্যালঘু অমুসলিমদের জন্য নির্ধারি ত সাধারণ অধিকারগুলোতে সমভাবে অংশীদার, কিন্তু প্রথমোক্ত দুই শ্রেণী সংক্রান্ত বিধিতে সামান্য কিছু পার্থাক্যও রয়েছে। তাই অমুসলিম সংখ্যালঘুদের অধিকার বিশদভাবে বর্ণনা করার আগে আমি এই বিশেষ দুটি শ্রেণীর আলাদা আলাদা বিধান বর্ণনা করবো।
চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিক
যারা যুদ্ধ ছাড়া অথবা যুদ্ধ চলাকালে বশ্যতা স্বীকার করতে সম্মত হয়ে যায় এবং ইসলামী সরকারের সাথে সুনির্দষ্ট শর্তবলী স্থির করে সন্ধিবদ্ধ হয় তাদের জন্য ইসলামরে বিধান এই যে, তাদের সাথে সকল আচরণ তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্তানুযায়ী করা হবে। আজকালকার সভ্য জাতিগুলো এরূপ রাজনৈতিক ধড়িবাজীতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে যে, শত্রু পক্ষকে বশ্যতা স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কিছু উদার শর্ত নির্ধারণ করে নেয়। তারপর যেই তারা পূরোপূরি আয়াত্তে এসে যায় অমনি শুরু হয়ে যায় ভিন্ন ধরনের আচরণ। কিন্তু ইসলাম এটাকে হারাম ও মহাপাপ গণ্য করে। কোনো জাতির সাথে যখন কিছু শর্ত স্থির করা হয়ে যায়। (চাই তা মনোপুত হোক বা না হোক) এখন তাতে চুল পরিমাণও হেরফের করা যাবেনা। চাই উভয় পক্ষের আপেক্ষিক অবস্থান, শক্তি ও ক্ষমতায় [Relative position] যতোই পরিবর্তন এসে থাকনা কেন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ
“যদি তোমরা কোনো জাতির সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হও, বিজয়ী হও এবং সেই জাতি নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের প্রাণ রক্ষার্থে তোমাদের মুক্তিপণ দিতে রাযী হয় (অপর বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের সাথে কোনো সন্ধিপত্র সন্পাদন করে) তাহলে পরবর্তী সময়ে ঐ নির্ধারিত মুক্তিপণের চেয়ে কণা পরিমাণও বেশী নিওনা। কেননা সেটা তোমাদের জন্য বৈধ হবেনা।” (আবুদাউদ, কিতাবুল জিহাদ)
অপর হাদীসে আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ
“সাবধান! যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ নাগরিকের ওপর যুলুম করবে কিংবা তার প্রাপ্য অধিকার থেকে তাকে কম দেবে, তার সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা তার ওপর চাপাবে, অথবা তার কাছ থেকে কোনো জিনিস তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে, এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই তার সম্মতি ছাড়া আদায় করবে , এমন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিন আমি নিজেই ফরিয়াদী হবো।” [আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ]
উক্ত উভয় হাদীসের ভাষা ব্যাপক অর্থবোধক। তাই ঐ হাদীস দুটি থেকে এই সাধারণ বিধি প্রণয়ন করা হয় যে, চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকদের সাথে সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত নির্ধারিত হবে, তাতে কোনো রকম কমবেশী করা কোনোক্রমেই জায়েয হবেনা। তাদের ওপর কর খাজনাও বাড়ানো যাবেনা। তাদের জমিজমাও দখল করা যাবেনা, তাদের ঘরবাড়ী দালান কোঠাও কেড়ে নেয়া যাবেনা। তাদের ওপর কড়া ফৌজদারী দন্ডবিধিও চালু করা যাবেনা, তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতায়ও হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। তাদের ইজ্জত সম্মানেরও ক্ষতি করা যাবেনা এবং তাদের সাথে এমন কোনো আচরণ করা যাবেনা, যা যুলুম, অধিকারহরণ, সামর্থের সাত্রারিক্ত বোঝা চাপানো অথবা সম্মতি ব্যতিরেকে সম্পতি হস্তগত করার পর্যায়ে পড়ে। এই নির্দেশাবলীর কারণেই ফকীহগণ সন্ধি বলে বিজিত জাতিগুলো সম্পর্কে কোনো আইন প্রনয়ন করেনি। বরং শুধুমাত্র একটি সাধারণ সনংক্ষিপ্ত বিধি প্রণয়ন করেই ক্ষান্ত থেকেছেন। সেটি এই যে, তাদের সাথে আমাদের আচরণ হুবহু সন্ধির শর্ত অনুসারে পরিচালিত হবে। ঈমাম আবু ইউসুফ লিখেছেনঃ
“তাদের সন্ধিপত্রে যা নেয়া স্থির হয়েছে, তাদের কাছে থেকে শুধু তাই নেয়া হবে। তাদের সাথে সম্পদিত সন্ধির শর্ত পুরণ হবে। কোনো কিছু বাড়ানো হবেনা।” [কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠাঃ ৩৫]
যুদ্ধে বিজিত অমুসলিম নাগরিক
দ্বিতীয় প্রকার অমুসলিম নাগরিক হচ্ছে যারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলমানদের সাথে লড়াই করেছে এবং ইসলামী বাহিনী যখন তাদের সকল প্রতিরোধ ভেংগে তাদের আবাসিক এলাকায় প্রবেশ করেছে, কেবল তখনই অস্ত্র সংবরণ করেছে। এ ধরনের বিজিতদেরকে যখন “সংরক্ষিত নাগরিকে” (যিম্মী) পরিণত করা হয় তখন তাদের কয়েকটি বিশেষ অধিকার দেয়া হয়। ফিকহ্ শাস্ত্রীয় প্রন্থাবলীতে এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিন্মে এই সকল বিধির একটি সংক্ষিপ্ত সার দেয়া হচ্ছে। এ থেকে এই শ্রেণীর অমুসলিম নাগরিকদের সাংবিধানিক মর্যাদা ও অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যাবেঃ
১. মুসলমানদের সরকার তাদরে কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই তাদের সাথে সংরক্ষণ চুক্তি সম্পাদিত হয়ে যাবে এবং তাদরে জান ও মালের হিফাযত করা মুসলমানদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কেননা জিযিয়া গ্রহণ করা মাত্রই প্রমাণিত হয় যে, জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়েছে। (বাদায়েউস্ সানায়ে, ৭ম খন্ড, ১১১ পৃষ্ঠা)
এরপর মুসলিম সরকারের বা মাধারণ মুসলমানদের এ অধিকার থাকেনা যে তাদের দম্পত্তি দখল করবে বা তাদেরকে দাসদাসী বানাবে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবু উবায়দাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছিলেনঃ
“যখন তুমি তাদের কাছ থেকে জিযিয়া গ্রহণ করবে, তখন তোমার আর তাদের ওপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার থাকবেনা।” (কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠা ৮২)
২.“সংরক্ষিত নাগরিক” (যিম্মি) পরিণত হয়ে পাওয়ার পর তাদের জমির মালিক তারাই হবে। সেই জমির মালিকানা উত্তরাধিাকার সূত্রে হস্তান্তরিত হবে এবং তারা নিজেদের সম্পত্তি বেচা, কেনা, দান করা ও বন্ধক রাখা ইত্যাদির নিরংকুশ অধিকারী হবে। ইসলামী সরকার তাদেরকে বেদখল করতে পারবেনা। (ফাতুহুল কাদীর ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠাঃ ৩৫৯)
৩. জিযিয়ার পরিমাণ তাদের আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে যারা মধ্যবিত্ত তাদের কাছ থেকে কম এবং যারা দারিদ্র তাদের কাছ থেকে অনেক কম নেয়া হবে। আর যার কোনো উপার্জনের ব্যবস্থা নেই, অথবা যে অন্যের দান দক্ষিণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে। জিযিয়ার জন্য যদিও কোনো বিশেষ পরিমাণ নিদিষ্ট নেই। তবে তা অবশ্যই এ ভাবে নির্ধারিত হওয়া চাই যাতে তা দেয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ধনীদের ওপর মাসিক এক টাকা, মধ্যবিত্তদের ওপর মাসিক ৫০ পয়সা এবং গরীব লোকদের ওপর মাসিক ২৫ পয়সা জিযিয়া আরোপ করেছিলেন। (কিতাবুল খারাজ পৃষ্ঠাঃ ৩৬)
৪. জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদের ওপর আরোপ করা হবে। যারা যুদ্ধ করতে সমর্থ নয়, যথা শিশু, নারী, পাগল, অন্ধ, পংগু উপাসনালয়ের সেবক, সন্যাসী, ভিক্ষু, খুনখুনে বৃদ্ধ। বছরের উল্লেখযোগ্য সময় রোগে কেটে যায় এমন রোগী, এবং দাস দাসী ইত্যাদিকে জিযিয়া দিতে হবেনা। (বাদায়ে ৭ম খন্ড পৃষ্ঠাঃ ১১১-১১৩)
৫.যুদ্ধের মাধ্যমে দখলীকৃত জনপদের উপাসনালয় দখল করার অধিকার মুসলমানদের রয়েছে। তবে সৌজন্য বশত এই অধিকার ভোগ করা থেকে বিরত থাকা এবং উপাসনালয়গুলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় বহাল রাখাপ উত্তম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে যতো দেশ বিজিত হয়েছে তার কোথাও কোনো উপাসনালয় ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি। ইমাম আর ইউসুফ লিখেছেনঃ
“সেগুলোকে যেমন ছিলো তেমনভাবেই রাখা হয়েছে। ভাঙ্গা হয়নি বা তাতে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করা হয়নি।” (কিতাবুল খারাজ, পৃষ্ঠাঃ ৮৩)
তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোকে ধ্বংস করা কোনো অবস্থায়ই বৈধ নয়। (বাদায়ে, ৭ম খন্ড পৃষ্ঠাঃ ১১৪)
২. অমুসলিম নাগরিকদের সাধারণ অধিকার
এবার আমি শ্রেণীর নাগরিকের সকলেই এ অধিকারগুলোতে অংশীদার।
প্রাণের নিরাপত্তা
অমুসলিম নাগরিকের রক্তের মূল্য মুসলমানদের রক্তের মূল্যের সমান। কোনো মুসলমান যদি অমুসলিম নাগরিককে হত্যা করে, তাহলে একজন মুসলমান নাগরিককে হত্যা করলে যেমন তাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হতো ঠিক তেমনি মৃত্যুদন্ড দেয়া হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমকে হত্যা করলে তিনি খুনীকে কৃত্যুদন্ড দেন। তিনি বলেনঃ
“যে নাগরিকের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেয়া হয়েছে, তার রক্তের বদলা নেয়ার দায়িত্ব আমারই।”{ইনায়া শরহে হিদায়া ৮ম খন্ড ২৫৬ পৃষ্ঠা।}
হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে বকর বিন ওয়ায়েল গোত্রের এক ব্যক্তি জনৈক হীরাবাসী অমুসলিম যিম্মীকে হত্যা করে। তিনি খুনীকে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের হতে সমর্পণের আদেশ দেন। অতঃপর তাকে উত্তরাধিকারীদের হতে সমর্পন করা হলে তারা তাকে হত্যা করে। (বারহান শরহে মাওয়াহিবুর রাহমানঃ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৮৭)
হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে হযরত ওমরের ছেলে উবায়দুল্লাহকে হত্যার পক্ষে ফতুয়া দেয়া হয়। কেননা তিনি হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর হত্যার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে হুরমুযান ও আবু লুলুর মেয়েকে হত্যা করেন।
হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমলে জনৈক মুসলমান জনৈক অমুসলিমের হত্যার দায়ে গ্রেফতার হয়। যথারীতি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর তিনি মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেন। এই সময় নিহত ব্যক্তির ভাই এসে বললো, “আমি মাফ করে দিয়েছি।” কিন্তু তিনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে বললেনঃ ওরা বোধ হয় তোমাকে ভয় দেখিয়েছে।” সে বললো! “না, আমি রক্তপণ পেয়েছি এবং আমি বুঝতে পারছি যে, ওকে হত্যা করলে আমার ভাই ফিরে আসবেনা।” তখন তিনি খুনীকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেনঃ
“আমাদের অধীনস্থ অমুসলিম নাগরিকদের রক্ত আমাদের রাক্তের মতোই এবং তাদের রাক্তপণ আমাদের রক্তপণের মতোই।”২{বুরহান ২য় খন্ড ২৮২ পৃষ্ঠা।}
অপর এক বর্ণনা মুতাবিক হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছিলেনঃ
“তারা আমাদের নাগরিক হতে রাযী হয়েছেই এই শর্তে যে, তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো এবং তাদের রক্ত আমাদের মতো মর্যাদাসম্পন্ন হবে।”
এ কারণেই ফকীহগণ এই বিধি প্রণয়ন করেছেন যে, কোনো অমুসলিম নাগরিক কোনো মুসলমানের নিহত হবার ক্ষেত্রে দিতে হয়। (দুর্রে মুখতার, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২০৩)
ফৌজদারী দন্ডবিধি
ফৌজদারী দন্ডবিধি মুসলিম অমুসলিম সকলের জন্য সমান। অপরাধের যে সাজা মুসলমানকে দেয়া হয়, অমুসলিম নাগরিককেও তাই দেয়া হবে। অমুসলিমের জিনিস যদি মুসলমান চুরি করে কিংবা মুসলমানের জিনিস যদি অমুসলিম চুরি করে, তাহলে উভয় ক্ষেত্রেই চোরের হাত কেটে ফেলা হবে। কারো ওপর ব্যভিচারের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে অপবাদ আরোপকারী মুসলমানই হোক আর অমুসলমানই হোক উভয়কে একই শাস্তি দেয়া হবে। অনুরূপভাবে ব্যভিচারের শাস্তিও মুসলিম ও অমুসলিমের জন্য একই রকম। তবে মদের বেলায় অমুসলিদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ১{কিতাবুল খারাজ পৃঃ ২০৮,২০৯, আল মাব্সূত, ৯ম খন্ড, পৃঃ ৫৭-৫৮, ইমাম মালেকের মতে অমুসলিমকে মদের ন্যায় ব্যভিচারের শাস্তি থেকেও অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ইমাম মালেকের অভিমতের উৎস হলো হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু ও হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই সিদ্ধান্ত যে, অমুসলিম নাগরিক ব্যভিচার করলে তার ব্যাপারটা তাদের সম্প্রদায়ের ওপর ছেড়ে দিতে হবে। অর্থাৎ তাদের ধর্মীয় বা পারিবারিক আইন অনুসারে কাজ করতে হবে।}
দেওয়ানী আইন
দেওয়ানী আইনেও মুসলমান ও অমুসলমান সমান। “তাদের সম্পত্তি আমাদের সম্পত্তির মতো” হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর এই উক্তির তাৎপর্য এই যে, মুসলমানের সম্পত্তি যেভাবে হিফাযত করা হয় অমুসলিমের সম্পত্তির হিফাযতও তদ্রূপ করা হবে এবং আমাদের ও তাদের দেওয়ানী অধিকার সমান ও অভিন্ন হবে। এই সাম্যের অনিবার্য দাবী অনুসারে দেওয়ানী আইনের আলোকে মুসলমানের ওপর যে সব দায় দায়িত্ব অর্পিত হয় অমুসলিমের ওপরও তাই অর্পিত হবে।
ব্যবসায়ের যেসব পন্থা আমাদের নিষিদ্ধ, তা তাদের জন্যও নিষিদ্ধ। তবে অমুসলিমরা শুধুমাত্র শুয়রের বেচাকেনা খাওয়া এবং মদ বানানো, পান ও কেনাবেচা করতে পারবে। (আল মাবসূত, ১৩শ খন্ড, পৃঃ৩৭-৩৮)
সম্মানের হিফাযত
কোনো মুসলমানকে জিহ্বা বা হাত পা দিয়ে কষ্ট দেয়া, গালি দেয়া, মারপিট করা, বা গীবত করা যেমন অবৈধ, তেমনি এসব কাজ অমুসলিমের বেলায়ও অবৈধ। দুর্রে মুখতারে আছেঃ
“তাকে কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব এবং তার গীবত করা মুসলমানের গীবত করার মতোই হারাম।”[৩য় খন্ড, পৃঃ ২৭৩-২৭৪]
অমুসলিমদের চিরস্থায়ী নিরাপত্তা
অমুসলিমদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চুক্তি মুসলমানদের জন্য চিরস্থায়ীভাবে বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ এই চুক্তি করার পর তারা তা ভাংতে পারেনা। অপরদিকে অমুসলিমদের এখতিয়ার আছে যে, তারা যতোদিন খুশি তা বহাল রাখতে পারে এবং যখন ইচ্ছা ভেংগে দিতে পারে। ‘বাদায়ে’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ
“অমুসলিমদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দানের চুক্তি আমাদের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলমানরা কোনো অবস্থাতেই তা ভাংতে পারেনা। পক্ষান্তরে অমুসলিমদের পক্ষে তা বাধ্যতামূলক নয়। [অর্থাৎ তারা যদি আমাদের নাগরিকত্ব ত্যাগ করতে চায় তবে তা করতে পারে।”] [দুর্রে মুখতার, ৭ম খন্ড, পৃষ্টা ১১২]
অমুসলিম নাগরিক যতো বড় অপরাধই করুক, তাদের রাষ্টীয় রক্ষাকবচ সম্বলিত নাগরিকত্ব বাতিল হয়না। এমনকি জিযিয়া বন্ধ করে দিলে, কোনো মুসলমানকে হত্যা করলে রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেয়াদবী করলে অথবা কোনো মুসলিম নারীকে ধর্ষণ করলেও তার নিরাপত্তার গ্যারান্টিযুক্ত নাগরিকত্ব বাতিল হয়না। এসব কাজের জন্য তাকে অপরাধী হিসেবে শাস্তি দেয়া হবে। কিন্তু বিদ্রোহী আখ্যয়িত করে নাগরিকত্বহীন করা হবেনা। তবে শুধু দুই অবস্থায় একজন অমুসলিম নাগরিকত্বহীন হয়ে যায়। এক. যদি সে মুসলমানদের দেশ ছেড়ে গিয়ে শত্রুদের সাথে মিলিত হয়। দুই. যদি সে ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খোলাখুলি বিদ্রোহে লিপ্ত হয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করে। [বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩, ফাতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৩৮১-৩৮২]
ঘরোয়া কর্মকান্ড
অমুসলিমদের ঘরোয়া কর্মকান্ড তাদের নিজস্ব পারিবারিক আইন (personal law) অনুসারে স্থির কারা হবে। তাদের ওপর ইসলামী কার্যকর করা হবেনা। আমাদের ঘরোয়া জীরনে যেসব জিনিস অবৈধ, তা যদি তাদের ধর্মীয় ও জাতীয় আইনে। বৈধ হয়, তাহলে ইসলামী আদালত তাদের আইন অনুসারেই ফয়সালা করবে। উদাহরণ স্বরূপ, সাক্ষী ছাড়া বিয়ে, মুহ্র ছাড়া বিয়ে, ইদ্দ্তের মধ্যে পুনরায় বিয়ে অথবা ইসলামে যাদের সাথে বিয়ে নিষিদ্ধ তাদের সাথে বিয়ে যদি তাদের আইনে বৈধ থেকে থাকে তাহলে তাদের জন্য এসব কাজ বৈধ বলে মেনে নেয়া হবে। খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তাদের পরবর্তী সকল যুগে ইসলামী সরকারগুলো এই নীতিই অনুসরণ করেছে। হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয এ ব্যাপারে হযরত হাসান বস্রীর কাছে নিম্নরূপ প্রশ্ন করেছিলেনঃ
“খোলাফায়ে রাশেদীন অমুসলিম নাগরিকদেরকে নিষিদ্ধ মেয়েদের সাথে বিয়ে, মদ ও শুয়রের ব্যাপারে স্বাধীন ছেড়ে দিলেন কিভাবে?
জাবাবে হযরত হাসান লিখলেনঃ
“তারা জিযিয়া দিতে তো এজন্যই সম্মত হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আকীদা বিশ্বাস অনুসারে জীবন যাপন করার স্বাধীনতা দিতে হবে। আপনার কর্তব্য পূর্ববর্তীদের পদ্ধতি অনুসরণ করা, নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা নয়।”
তবে কোনো ক্ষেত্রে যদি বিবদমান উভয় পক্ষ স্বয়ং ইসলামী আদালতে আবেদন জানায় যে, ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক তাদের বিবাদের ফয়সালা করা হোক, তবে আদালত তাদের ওপর শরীয়তের বিধান কার্যকর করবে। তাছাড়া পারিবারিক আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো বিবাদে যদি একপক্ষ মুসলমান হয়, তাহলে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক ফালসালা হবে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন খৃষ্টন মহিলা কোনো মুসলমানের স্ত্রী ছিলো এবং তার স্বামী মারা গেলো। এমতাবস্থায় এই মহিলাকে শরীয়ত মুতাবিক স্বামীর সে বিয়ে বাতিল হবে। [আল মাবসূত ৫ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৩৮-৪১]
ধর্মীয় অনুষ্ঠান
অমুসলিমদের ধর্মীয় ও জাতীয় অনুষ্ঠানদি প্রকাশ্যভাবে ঢাকঢোল পিটিয়ে উদযাপন করা সম্পর্কে ইসলামের বিধান এই যে, অমুসলিমরা নিজস্ব জনপদে এটা অবাধে করতে পারবে। তবে নির্ভেজাল ইসলামী জনপদগুলোতে ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার ইচ্ছা করলে তাদেরকে এ ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতাও দিতে পারবে। আবার কোনো ধরনের কড়াকড়ি আরোপ করতে চাইলে তাও করতে পারবে।১{নির্ভেজাল ইসলামী জনপদ শরীয়তের পরিভাষায় “আমসারুল মুসলিমীন” (বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ) আখ্যায়িত অঞ্চলকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সব অঞ্চলের ভূসম্পত্তি মুসলমানদের মালিকানাভুক্ত এবং যে সব অঞ্চলকে মুসলমানরা ইসলামী অনুষ্ঠানাদি ও উদযাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে।} বাদায়ে গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ
“যেসব জনপদ বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নয়, সেখানে অমুসলিমদেরকে মদ ও শুকর বিক্রি, ক্রুশ বহন করা ও শংখ ধ্বনি বাজানোতে বাধা দেয়া হবেনা। চাই সেখানে মুসলিম অধিবাসীদের সংখ্যা যতোই বেশী হোকনা কেনো। তবে বিধিবদ্ধ ইসলামী অঞ্চলে এ সব কাজ পছন্দনীয় নয়। অর্থাৎ যেসব জনপদকে জুম্য়া, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধি প্রচলনের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে।……তবে যে সমস্ত পাপ কাজকে তারাও নিষিদ্ধ মনে করে যেমন ব্যভিচার ও অন্যান্য অশ্লীল কাজ, যা তাদের ধর্মেও নিষিদ্ধ সেসব কাজ প্রকাশ্যে করতে তাদেরকে সর্বাবস্থায়িই বাঁধা দেয়া হবে। চাই সেটা মুসলমানদের জনপদে হোক কিংবা তাদের জনপদে হোক।”২{বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃঃ ১১৩}
কিন্তু বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদগুলোতেও তাদেরকে শুধুমাত্র ক্রুশ ও প্রতিমাবাহী শোভাযাত্রা বের করতে এবং প্রকাশ্যে ঢাকঢোল বাজাতে বাজাতে বাজারে বাজারে বের হতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে প্রাচীন উপাসনালয়গুলোর অভ্যন্তরে তারা সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করতে পারবে। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার তাতে হস্তক্ষেপ করবেনা [শর্হে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১]
উপাসনালয়
নির্ভেজাল মুসলিম জনপদগুলোতে অমুসলিমদের যেসব প্রাচীন উপাসনালয় থাকবে, তাতে হস্তক্ষেপ করা যাবেনা। উপাসনালয় যদি ভেংগে যায়, তবে তা একই জায়গায় পূর্ননির্মাণের অধিকারও তাদের আছে। তবে নতুন উপাসনালয় বানানোর অধিকার নেই।[বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৪, শর্হে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৫১]
তবে যেগুলো নির্ভেজাল মুসলিম জনপদ নয়, তাতে অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণের অবাধ অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে যেসব এলাকা এখন আর বিধিবদ্ধ ইসলামী জনপদ নেই, সরকার সেখানে জুম্য়া, ঈদ ও ফৌজদারী দন্ডবিধির প্রচলন বন্ধ করে দিয়েছে, সেখানেও অমুসলিমদের নতুন উপাসনালয় নির্মাণ নিজস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের অধিকার রয়েছে। (বাদায়ে, ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠাঃ ১১৪, শরহে সিয়ারুল কবীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ২৫৭]
ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ফতুয়া নিম্মরূপঃ
“যেসব জনপদকে মুসলমানরা বাসযোগ্য বানিয়েছে, সেখানে অমুসলিমদের নতুন মন্দির, গীর্জা ও উপাসনালয় বানানো, বাদ্য বাজানো এবং প্রকাশ্যে শুয়রের গোস্ত ও মদ বিক্রি করার অধিকার নেই। আর অনারবদের হাতে আবাদকৃত, পরে অমুসলিমদের অধিকার তাদের সাথে সম্পদিত চুক্তির শর্তঅনুসারে চিহ্নিত হবে। মুসলমানরা তা মেনে চলতে বাধ্য থাকবে।”
জিযিয়া ও কর আদায়ে সুবিধা দান
জিযিয়া ও কর আদয়ে অমুসলিম নাগরিকদের ওপর কঠোরতা প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ। তাদের সাথে নম্র ও কোমল ব্যবাহার করতে বলা হয়েছে। তারা বহন করতে পারেনা এমন বোঝা তাদের ওপর চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত ওমরের নির্দেশ ছিলো, “যে পরিমাণ সম্পদ রাষ্ট্রকে প্রদান করা তাদের সামর্থের বাইরে তা দিতে তাদেরকে বাধ্য করা চলাবেনা।” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮,৮২]
জিযিয়ার বদলায় তাদের ধনসম্পদ নীলামে চড়ানো যাবেনা। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তার জনৈক কর্মচারীকে নির্দেশ পাঠিয়েছিলেন যেঃ
“কর খাজনা বাবদে তাদের গরু, গাধা, কাপড় চোপড় বিক্রী করোনা।” [ফাতহুল বায়ন, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ ৯৩]
অপর এক ঘটনায় হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় কর্মচারীকে পাঠানোর সময় বলে দেনঃ “তাদের শীত গ্রীষ্মের কাপড়, খাবারের উপকরণ ও কৃষি কাজের পশু খাজনা আদায়ের জন্য বিক্রি করবেনা, প্রহার করবেনা, দাঁড়িয়ে রেখে শাস্তি দেবেনা এবং খাজনার বদলায় কোনো জিনিস নীলামে চড়াবেনা। কেননা। আমরা তাদের শসক হয়েছি বলে নরম ব্যবহারের মাধ্যমে আদায় করাই আমাদের কাজ। তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে আল্লাহ্ আমার পরিবর্তে তোমাকে পাকড়াও করবেনা। আর আমি যদি জানতে পরি যে, তুমি আমার আদেশের বিপরীত কাজ করছো, তাহলে আমি তোমাকে পদচ্যুত করবো। [কিতাবুল খারজ, পৃঃ ৯]
জিযিয়া আদায়ে যে কোনো ধরনের কঠোরতা প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু গভর্নর হযরত আবু উবায়াদাকে যে ফরমান পাঠিয়েছিলেন তাতে অন্যান্য নির্দেশের পাশাপাশি এ নির্দেশও ছিলোঃ
“মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের ওপর যুলুম করা, কষ্ট দেয়া এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পত্তি ভোগ দখল করা থেকে বিরতে রাখো।” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ৮২]
সিরিয়া সফরকালে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু দেখলেন, সরকারী কর্মচারীর জিযিয়া আদায় করার জন্য অমুসলিম নাগরিকদের শাস্তি দিচ্ছে। তিনি তাদের বললেন, “ওদের কষ্ট দিওনা। তোমরা যদি ওদের কষ্ট দাও তবে আল্লাহ্ কিয়ামতের দিন তোমাদের শাস্তি দেবেন।” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭১]
হিশাম ইবনে হাকাম দেখলেন জনৈক সরকারী কর্মচারী জিযিয়া আদায় করার জন্য জনৈক কিবতীকে রোদে দাঁড় করিয়ে রাখছে। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং বললেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ
“যারা দুনিয়ায় মানুষকে শাস্তি দিতো, আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দেবেন।” [আবু দাউদ]
মুসলিম ফিকহ্ শাস্ত্রকারগণ জিযিয়া দেয় অস্বীকারকারীদের রড়জোর বিনাশ্রম কারদন্ড দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, “তবে তাদের সাথে সদয় আচরণ করা হবে এবং প্রাপ্য জিযিয়া না দেয়া পর্যন্ত আটক করে রাখা হবে। [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ৭০]
যেসব অমুসলিম নাগরিক দারিদ্রের শিকার ও পরমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তাদের জিযিয়া তো মাফ করা হবেই, উপরন্তু ইসলামী কোষাগার থেকে তাদের জন্য নিয়মিত সাহায্যও বরাদ্দ করা হবে। হযরত খালিদ হীরাবাসীদের যে লিখিত নিরাপত্তা সনদ দিয়েছিলেন, তাতে এ কথাও লেখা ছিলো যেঃ
“আমি হীরাবাসী অমুসলিমদের জন্য এ অধিকারও সংরক্ষণ করলাম যে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বার্ধক্যের দরুণ কর্মক্ষমতা হারিয়ে বসেছে, যার ওপর কোনো দুর্যগ নেমে এসেছে, অথবা যে পূর্বে ধনী ছিলো, পরে দরিদ্র হয়ে গেছে, ফলে তার স্বধর্মের লোকেরাই তাকে দান দক্ষিণা দিতে শুরু করেছে, তার জিযিয়া মাফ করে দেয়া হবে এবং তাকে ও তার পরিবার পরিজন ও সন্তানদের বাইতুল মাল থেকে ভরণ পোষণ করা হবে।” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৮৫]
একবার হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জনৈক বৃদ্ধ লোককে ভিক্ষা করতে দেখে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বললো, “কী আর করবো বাপু, জিযিয়া দেয়ার জন্য ভিক্ষে করছি।” এ কথা শুনে তিনি তৎক্ষনাত তার জিযিয়া মাফ ও তার ভরণ পোষণের জন্য মাসিক বৃত্তি নির্ধারণ করে দিলেন। তিনি কোষাগারের কর্মকর্তাকে লিখলেন, “আল্লাহ্র কসম, এটা কখনো ইনসাফ নয় যে, আমরা যৌবনে তার দ্বারা উপকৃত হবো, আর বার্ধক্যে তাকে অপমান করবো।” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭২, ফাতহুল কাদীর, ২য় খন্ড, পৃঃ ৩৭৩]
দামেষ্ক সফরের সময়ও হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু অক্ষম অমুসলিম নাগরিকদের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারণ করার আদেশ জারী করেছিলেন। [বালাযুরীঃ ফতুহুল বুলদান, পৃঃ ১২৯]
কোনো অমুসলিম নাগরিক মারা গেলে তার কাছে প্রাপ্য বকেয়া জিযিয়া তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবেনা এবং তার উত্তরাধিকারীদের ওপরও এর দায়ভার চাপানো হবেনা। ইমাম আবু ইউসুফ বলেনঃ
“কোনো অমুসলিম নাগরিক তার কাছে প্রাপ্য জিযিয়া পূরো অথবা আংশিক দেয়ার আগেই মারা গেলে তা তার উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে বা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে আদায় করা হবেনা।” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭০, আল মাবসূত ১০ম খন্ড, পৃঃ ৮১]
বাণিজ্য কর
মুসলিম ব্যবসায়ীদের মতো অমুসলিম ব্যবসায়ীদেরও বাণিজ্য পণ্যের ওপর কর আরোপ করা হবে যদি তাদের মূলধন ২০০ দিরহাম পর্যন্ত পৌঁছে অথবা তারা ২০ মিসকাল স্বর্ণের মালিক হয়ে যায়। ১{কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ৭০, তবে আজও কর আরোপের জন্য অবিকল এই পরিমাণ নিসাব নির্ধারণ করা জরুরী নয়। এটা সেই সময়কার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত নির্ধারিত হয়েছিল।} এ কথা সত্য যে, ফিকহ্ শাস্ত্রকারগণ অমুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর বাণিজ্যের শতকরা ৫ ভাগ এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের ওপর আড়াই ভাগ আরোপ করেছিলেন। তবে এ কাজটা কুরআন বা হাদীসের কোনো সুস্পষ্ট বাণীর আলোকে করা হয়নি। এটা তাদের ইজতিহাদ বা হবেষণালদ্ধ সিদ্ধান্ত ছিলো। এটা সমকালীন পরিস্থিতির চাহিদা অনুসারে করা হয়েছিল। সে সময় মুসলমানগণের অধিকাংশেই দেশরক্ষার কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং সমস্ত ব্যবসায় বাণিজ্য অমুসলিমদের হতে চলে গিয়েছিল। এজন্য মুসলিম ব্যবসায়ীদের উৎসাহ বৃদ্ধি এবং তাদের ব্যবসায়ের সংরক্ষণের জন্য তাদের ওপর কর কমিয়ে দেয়া হয়েছে।
সামরিক চাকুরী থেকে অব্যাহতি
অমুসলিমগণ সামরিক দায়িত্বমুক্ত। শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা এককভাবে শুধু মুসলমানদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কারণ একটা আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্রের রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য কেবল তারাই উপযুক্ত বিবেচিত হতে পারে, যারা ঐ আদর্শকে সঠিক বলে মানে। তাছাড়া লড়াইতে নিজেদের আদর্শ ও মূলনীতি মেনে চলাও তাদের পক্ষেই সম্ভব। অন্যেরা দেশ রক্ষার জন্য লড়াই করলে ভাড়াটে সৈন্যের মতো লড়বে এবং ইসলামের নির্ধারিত নৈতিক সীমা রক্ষা করে চলতে পারবেনা। এজন্য ইসলাম অমুসলিমদের সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে এবং কেবলমাত্র দেশ রক্ষার কাজের ব্যয় নির্বাহে নিজেদের অংশ প্রদানকে তাদের কর্তব্য বলে চিহ্নিত করেছে। এটাই জিযিয়ার আসল তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। এটা শুধু যে আনুগত্যের প্রতীক তা নয় বরং সামারিক কর্মকান্ড থেকে অব্যাহতি লাভ ও দেশ রক্ষার বিনিমসয়ও বটে। এজন্য জিযিয়া শুধুমাত্র যুদ্ধ করতে সক্ষম পুরুষদের ওপরই আরোপ করা হয়। আর কখনো যদি মুসলমানরা অমুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অক্ষম হয়, তাহলে জিযিয়ার টাকা ফেরত দেয়া হয়। ১{এ বিষেয়ে বিস্তারিত অধ্যায়নের জন্য দেখুন আলমাবসূত, ১০ম খন্ড, পৃঃ৭৮-৭৯, হিদায়া, কিতাবুল সিয়ার, ফতহুল কাদীর, ৪র্থ খন্ড, পৃঃ৩২৭-৩২৮, এবং ৩৬৯-৩৭০, কোনো বহিশত্রুর আক্রমণের সময় দেশের অমুসলিম নাগরিকরা যদি দেশ রক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করার আগ্রহ প্রকাশ করে, তবে আমরা তাদেরকে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিতে পারি। তবে সে ক্ষেত্রে তাদের জিযিয়া রহিত করতে হবে। উল্লেখ্য যে, জিযিয়ার নাম শুনতেই অমুসলিমদের মনে যে আতংক জন্মে, সেটা শুধুমাত্র ইসলামের শত্রুদের দীর্ঘকাল ব্যাপী অপপ্রচারের ফল। অন্যথায় এই আতংকের কোনো ভিত্তি নেই। জিযিয়া মূলতঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমরা যে নিরাপদ ও সুরক্ষিত জীবন যাপনের সুযোগ পায় তারই বিনিময়। শুধুমাত্র সক্ষম ও প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের কাছ থেকে এটা নেয়া হয়। এটাকে যদি ইসলাম গ্রহণ না করার জরিমান বলা হয়, তাহলে যাকাতকে কি বলা হবে? যাকাত তো শুধু প্রত্যেক সক্ষম পুরুষই নয় বরং সক্ষম নারীর কাছ থেকেও আদায় করা হয়। ওটা কি তাহলে ইসলাম গ্রহণেল জরিমানা?} ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন রোমকরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিশাল সামাবেশ ঘটালো এবং মুসলমানরা সিরিয়ার সকল বিজিত এলাকা পরিত্যাগ করে একটি কেন্দ্রে নিজেদের মক্তি কেন্দ্রীভূত করতে বাধ্য হলো, তখন হযরত আবু উবাইদা নিজের অধীনস্থ সেনাপতিদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা যেসব জিযিয়া ও খাজনা অমুসলিমদের কাছ থেকে আদায় করেছেলে তা তাদের ফিরিয়ে দাও এবং বলো যে, “এখন আমার তোমাদের রক্ষা করতে অক্ষম, তাই যে অর্থ তোমাদের রক্ষা করার বিনিময়ে আদায় করেছিলাম তা ফেরত দিচ্ছি” [কিতাবুল খারাজ, পৃঃ ১১১]
এই নির্দেশ মুতাবিক সকল সেনাপতি আদায় করা অর্থ ফেরত দিয়েন। এ সময় অমুসলিম নাগরিকদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে ঐতিহাসিক বালাযুরী লিখেছেন, মুসলমান সেনাপতিগণ যখন সিরিয়ার হিম্স নগরীতে জিযিয়ার অর্থ ফেরত দেন, তখন সেখানকার অধিবাসীবৃন্দ সমস্বরে বলে ওঠে, “ইতিপূর্বে যে যুলুম অত্যাচারে আমরা নিষ্পেষিত হচ্ছিলাম, তার তুলনায় তোমাদের শসন ও ন্যায়বিচারকে আমরা বেশী পছন্দ করি। এখন আমার যুদ্ধ করে পরাজিত হওয়া ছাড়া কোনো মতেই হিরাক্লিয়াসের কর্মচারীদেরকে আমাদের শহরে ঢুকতে দেবোনা।” [ফতুহুল বুলদান, পৃঃ ১৩৭]
৩.মুসলিম ফকীহদের সমর্থন
হিজরী প্রথম শতাব্দীতে অমুসলিম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে যে আইন প্রণীত হয়েছিল, ওপরের আলোচনার তার কিছু বিশদ বিবরণ দেয়া হলো। পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে আমি এ কথাও উল্লেখ করতে চাই যে, খোলাফায়ে রাশেদীনের পরবর্তী রাজতন্ত্রের যুগে যখনই অমুসলিমদের সাথে অবিচার করা হয়েছে, তখন মুসলিম ফকীহগণই সর্বাগ্রে মযলুম অমুসলিমদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন। ইতিহাসের প্রসিদ্ধ ঘটনা যে, উমাইয়া শাসক ওলীদ বিন আব্দুল মালেক দামেষ্কের ইউহান্না গীর্জাকে জোরপূ্র্বক খৃষ্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। হযরত ওমর
বিন আব্দুল আযীয ক্ষমতায় এলে খৃষ্টানরা এ ব্যাপারে তার কাছে অভিযোগ দায়ের করলো। তিনি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে লিখে পাঠালেন, মসজিদের যে টুকুই অংশ গীর্জার জায়গার ওপর নির্মাণ করা হয়েছে তা ভেংগে খৃষ্টানদের হাতে সোপর্দ করে দাও।”
ওলীদ বিন এযীদ রোমক আক্রমণের ভয়ে সাইপ্রাসের অমুসলিম অধীবাসীদের দেশ থেকে বহিষ্কার করে সিরিয়ায় পুনর্বাসিত করেন। এতে মুসলিম ফকীহগণ ও সাধারণ মুসলমানরা ভীষণভাবে বিক্ষুব্ধ হয় এবং তারা একে একটা মস্তবড় গুনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর যখন ওলীদ বিন এযীদ পুনরায় তাদের সাইপ্রাসে নিয়ে পুর্নবাসিত করলেন, তখন তার প্রশংসা করা হয় এবং বলা হয়, এটাই ইনসাফের দাবী। ইসমাঈল বিন আইয়াশ বলেনঃ
“মুসলমানরা তার এ কাজে কঠোর অসন্তোষ প্রকাশ করে এবং ফকীহগণ একে গুনাহর কাজ মনে করেন। অতঃপর যখন এযীদ বিন ওলীদ খলীফা হলেন এবং তাদের আবার সাইপ্রাসে ফেরত পাঠালেন, তখন মুসলমানরা এ কাজ পছন্দ করেন এবং একে ন্যায়বিচার আখ্যায়িত করেন।” [ফতুহুল বুলদান, পৃঃ ১৫৬]
ঐতিহসিক বালাযুরী বর্ণনা করেন, িএকবার লেবাননের পার্বত্য এলাকার অধিবাসীদের মধ্য থেকে একটি গোষ্ঠী সরকারের বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সালেহ বিন আব্দুল্লাহ তাদের দমন করার জন্য একটি সেনাদল পাঠান। এই সেনাদল উক্ত বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সকল সশস্ত্র পুরুষদের হত্যা করে এবং বাদবাকীদের একদলকে দেশান্তরিত করে ও অপর দলকে যথাস্থানে বহাল রাখে। ইমাম আওযায়ী তখন জীবিত ছিলেন। তিনি সালেহকে এই যুলুমের জন্য তিরষ্কার করেন এবং একটা দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রটির অংশ বিশেষ নিম্নে দেয়া হলোঃ
“লেবানন পর্বতের অধিবাসীদের বহিষ্কারের ঘটনাটা তোমার অজানা নয়। তাদের ভেতরে এমনও অনেকে আছে, যারা বিদ্রেহীদের সাথে মোটেই অংশ গ্রহণ করেনি। তথাপি তুমি তাদের কতককে হত্যা করলে এবং কতককে তাদের বাসস্থানে ফেরত পাঠিয়ে দিলে। আমি বুঝিনা, কতিপয় বিশেষ অপরাধীর অপরাধমূলক কর্মকান্ডের শাস্তি সাধারণ মানুষকে কিভাবে দেয়া যায় এবং তাদের সহায় সম্পত্তি থেকে তাদের কিভাবে উৎখাত করা যায়? অথচ আল্লাহ্র সুস্পষ্ট নির্দেশ এই যে, একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবেনা।” এটা একটা অবশ্য করণীয় নির্দেশ। তোমার জন্য আমার সর্বোত্তম উপদেশ হলো, তুমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথাটা মনে রেখো যে, “যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম নাগরিকের ওপর যুলুম করবে এবং তাদের সামার্থের চেয়ে বেশী তার ওপর বোঝা চাপাবে, তার বিরুদ্ধে আমি নিজেই ফরীয়াদী হবো।” [ফুতুহুল বুলদান, পৃঃ১৬৯]
ইতিহাসে এ ধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ সব দৃষ্টান্ত থেকে বুঝা যায় যে, মুসলিম আলেম সমাজ নিরদিনই অমুসলিমদের অধিকার সংরক্ষণে সোচ্চার থেকেছেন। কখনো কোনো রাজা বা শাসক তাদের ওপর যুলুম ও বাড়াবাড়ি যদি করেও থাকে, তবে তৎকালে ইসলামী আইনের যেসব রক্ষক বেঁচে ছিলেন, তারা কখনো সেই যালিমকে তিরস্কার না করে ছাড়েননি।
৪. অমুসলিমদের যে সব বাড়তি অধিকার দেয়া যায়
উপরে আমরা অমুসলিমদের যে সব অধিকারের উল্লেখ করেছে, সেগুলো তাদের জন্য শরীয়তে সুনির্দিষ্ট এবং সেগুলো যে কোনো ইসলামী শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।
এক্ষনে আমি সংক্ষেপে বলবো যে, বর্তমান যুগে একটি ইসলামী রাষ্ট্র তার অমুসলিম নাগরিকদেরকে ইসলামী মূলনীতির আলোকে কী কী অতিরিক্ত অধিকার দিতে পারে।
রাষ্ট্র প্রধানের পদ
সর্ব প্রথম রাষ্ট্র প্রধানের প্রশ্নে আসা যাক। যেহেতু ইসলামী রাষ্ট্র একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র, তাই ধর্মহীন জাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলো সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার সম্পর্কে যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, ইসলামী রাষ্ট্র তার আশ্রয় নিতে পারেনা। ইসলামে রাষ্ট্র প্রধানের দায়িত্ব হলো ইসলামের মূলনীতি অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনা করা। সুতরাং যারা ইসলামের মূলনীতিকেই মানেনা, সে আর যাই হোক রাষ্ট্র প্রধানের পদে কোনোক্রমেই অভিষিক্ত হতে পারেনা।
মজলিশে শূরা বা আইন সভা
এরপর আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মজলিশে শূরা বা পার্লামেন্ট তথা আইন সভা। এই আইন সভাকে যদি শতকরা একশো ভাগ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলামী আদর্শ মুতাবিক গঠন করতে হয়, তাহলে এখানেও অমুসলিম প্রতিনিধিত্ব শুদ্ধ নয়। তবে বর্তমান যুগের পরিস্থিতির আলোকে এর অবকাশ এই শর্তে সৃষ্টি করা যেতে পারে যে, দেশের সংবিধানে এই মর্মে সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন নিশ্চয়তা দিতে হবে যেঃ
ক.আইন সভা কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবেনা এবং এই সীমা লংঘনকারী যে কোনো সিদ্ধান্ত আইনের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হবে।
খ.দেশের আইনের সর্ব প্রধান উৎস হবে কুরআন ও সুন্নাহ।
গ.আইনের চূড়ান্ত অনুমোদনের কাজটি যে ব্যক্তি করবেন তিনি মুসলমান হবেন। এরূপ একটি পদ্ধতিও অবলম্বনম করা যেতে পারে যে, অমুসলিমদের দেশের আইন সভার অন্তর্ভুক্ত করার পরিবর্তে তাদের জন্য একটা আলাদা প্রতিনিধি পরিষদ বা আইন সভা গঠন করে দেয়া হবে। এই পরিষদ দ্বারা তারা নিজেদের সামষ্টিক প্রয়োজনও মেটাতে পারবে এবং দেশের প্রশাসন সংক্রান্ত ব্যাপারেও নিজেদের দৃষ্টিভংগি তুলে ধরতে পারবে। এই পরিষদের সদস্যপদ এবং ভোটাধিকার শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য নির্দিষ্ট থাকবে এবং এখানে তাদের মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। এই পরিষদের মাধ্যমে তারা নিম্ন লিখিত কজগুলো সমাধা করতে পারবে।
১. তারা নিজেদের পারিবারিক ও ধর্মীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন ও আগে থেকে প্রচলিত সকল আইনের খসড়া রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদনক্রমে আইনে পরিণত হতে পারে।
২. তারা সরকারের প্রশাসনিক কর্মকান্ড ও মজলিশে শূরার সিদ্ধান্ত সমূহ সম্পর্কে নিজেদের অভিযোগ, পরামর্শ ও প্রস্তাব অবাধে পেশ করেতে পারবে এবং সরকার ইনসাফ সহকারে তার পর্যালোচনা করবে।
৩. তারা আপন সম্প্রদায়ের স্বার্থ দেশের অন্যান্য ব্যাপরে প্রশ্নও করতে পারবে। সরকারের একজন প্রতিনিধি তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যও উপস্থিত থাকবে।
উপরোক্ত তিনটি পন্থায় যে কোনো একটি পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুসারে গ্রহণ করা যেতে পারে।
পৌরসভা ও স্থানীয় সরকারের স্তরগুলোতে (Local bodies) অমুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব ও ভোট দানের পূর্ণ অধিকার দেয়া যেতে পারে।
বাক স্বাধীনতা, লেখার স্বাধীনতা ইত্যাদি
ইসলামী রাষ্ট্রে একজন মুসলমান যেমন বাক স্বাধীনতা, লোখার স্বাধীনতা, সমাবেশ ও সংগঠনের স্বধীনতা এবং মতামত ও বিবেকের স্বাধীনতা ভোগ করে, অমুসলিমরাও অবিকল সেরূপ স্বধীনতা ভোগ করবে। এ ব্যাপারে যেসব আইনগত বিধিনিষেধ মুসলমানদের ওপর থাকবে, তা তাদের ওপরও থাকবে।
আইন সংগতভাবে তারা সরকার, সরকারী আমলা এবং স্বয়ং সরকার প্রধানেরও সমালোচনা করতে পারবে।
ধর্মীয় আলোচনা ও গবেষণার যে স্বধীনতা মুসলমানদের রয়েছে, তা আইন সংগতভাবে তাদেরও থাকবে।
তারা নিজেদের ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করবে এবং একজন অমুসলিম যে কোনো ধর্ম গ্রহণ করলে তাতে সরকারের কোনো অপত্তি থাকবেনা। তবে কোনো মুসলমান ইসলরমী রাষ্ট্রের চৌগদ্দীতে থাকা অবস্থায় আপন ধর্ম পরিবর্তন করতে পারবেনা। তবে এরূপ ধর্মত্যাগী মুসলমানকে আপন ধর্মত্যাগের ব্যাপারে যে জবাবদিহীর সন্মুখীন হতে হবে, সেটা তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যে অমুসলিম ব্যক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সে ইসলাম ত্যাগ করেছে, তাকে এজন্য আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবেনা।
তাদেরকে তাদের বিবেকের দিরুদ্ধে কোনো চিন্তা ও কর্ম অবলম্বনে বাধ্য করা যাবেনা। দেশের প্রচলিত আইনের বিরোধী নয় এমন যে কোনো কাজ তারা আপন বিবেকের দাবী অনুসারে করতে পারবে।
শিক্ষা
ইসলামী রাষ্ট্র গোটা দেশের জন্য যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করবে, তাদেরকে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাই গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ইসলামের ধর্মীয় পুস্তকাদি পড়তে তাদেরকে বাধ্য করা যাবেনা। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্টানে অথবা নিজেদের বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্টানে আপন ধর্ম শিক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের থাকবে।
চাকুরী
কতিপয় সংরক্ষিত পদ ছাড়া সকল চাকুরীতে তাদের প্রবেশাধিকার থাকবে এবং এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোনো বৈষম্য করা চলবেনা। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের যোগ্যতার একই মাপকাঠি হবে এবং যোগ্য লোকদেরকে ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে নির্বাচন করা হবে।
সংরক্ষিত পদসমূহ বলতে ইসলামের আদর্শগত ব্যবস্থায় মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন নির্বাচন করা হবে।
সংরক্ষিত পদসমূহ বলতে ইসলামের আদর্শগত ব্যবস্থায় মৌলিক গুরুত্বসম্পন্ন পদ। একটা আদর্শবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এইসব পদ কেবল সংশ্লিষ্ট আদর্শে বিশ্বাসীদেরকেই দেয়া যেতে পারে। এই পদগুলো বাদ দেয়ার পর বাদবাকী সমগ্র প্রশাসনের বড় বড় পদেও যোগ্যতা সাপেক্ষে অমুসলিমদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরুপ, রাষ্টের মহা হিসাব রক্ষক, মহা প্রকৌশলী কিংবা। পোস্ট মাস্টার জেনারেলের ন্যায় পদে সুযোগ্য অমুসলিম ব্যুক্তিদের নিয়োগে কোনো বাঁধা নেই।
অনুরূপভাবে সেনাবাহিনীতেও শুধুমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ সংক্রান্ত দায়িত্ব সংরক্ষিত দায়িত্ব তলে গণ্য হবে। এ ছাড়া অন্যান্য সামরিক বিভাগ যার কোনো সম্পর্ক সরাসরি যুদ্ধের সাথে নেই, অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পেশা
শিল্প, কারিগরি, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্য সকল পেশার দুয়ার অমুসলিমদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে মুসলমানরা যে সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকে, তা অমুসলমানরাও ভোগ করবে এবং মুসলমানদের ওপর আরোপ করা হয়না এমন কোনো বিধিনিষেধ, অমুসলিমদের ওপরও আরোপ করা যাবেনা। মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের অর্থনৈতিক ময়দানে তৎপরতা চালানোর সমান অধিকার থাকবে।
অমুসলিমদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায়
একটি ইসলামী রাষ্ট্র আপন অমুসলিম নাগরিকদেরকে যে অধিকারই দেবে, তা পার্শ্ববর্তী কোন অমুসলিম রাষ্ট্র তার মুসলিম নাগরিকদেরকে কী কী অধিকার দিয়ে থাকে, বা আদৌ দেয়ানা, তার পারোয়া না করেই দেবে। আমারা একথা মানিনা যে, মুসলমানরা অমুসলিমদের দেখাদেখি আপন কর্মপন্থা নির্ণয় করবে। তারা ইনসাফ করলে এরাও ইনসাফ করবে আর তারা যুলুম করলে এরাও যুলুম করবে, এটা হতে পারেনা। আমরা মুসলমান হিসেবে একটা সুস্পস্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শের অনুসারী। আমাদের যাতোদুর সাধ্যে কুলায়, নিজস্ব নীতি ও আদর্শ অনুসারেই কাজ করতে হবে। আমরা যা দেবো তা আন্তরিকতা ও সদুদ্দেশ্য নিয়েই দেবো এবং তা শুধু কগজে কলমে নয় বরং বাস্তবেই দেবো। যে দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করবো তা পূর্ণ ইনসাফ ও সততার সাথে পালন করবো।
এরপর একথা আর বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে অমুসলিমদের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা এই রাষ্ট্রগুলোকে পরিপূর্ণ ও নির্ভেজাল ইসলামে রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা ছাড়া আর কোনোভাবে দেয়া সম্ভব নয়। দুর্ভাগ্য বশত গোটা এই উপমহাদেশ জুড়ে যুলুম ও নিপীড়নের যে পৈশাচিক বিভীষিকা চলছে, তাকে প্রশমিত করার এটাই একমাত্র অব্যর্থ উপায়। শুধুমাত্র এই পন্থা অবলম্বনেই পাকিস্তানও হতে পারে ইনসাফের আবাসভূমি আর ভারত এবং অন্যান্য দেশও ইনসাফের পথ খুঁজে পেতে পারে। পরিতাপের বিষয় হলো, অমুসলিমরা দীর্ঘকালব্যাপী ইসলামের কেবল অপব্যাখ্যাই শুনে ও দেখে আসছে। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী শাসনের কথা শুনলেই আতংকিত হয়। আর তাদের কেউ কেউ দাবী জানাতে থাকে যে, আমাদের এখানেও ভারতের ন্যায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কায়েম হওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র কি এমন কোনো আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, যার প্রত্যাশা করা যেতে পারে? তার পরিবর্তে এমন একটি ব্যবস্থার পরীক্ষা করা কি ভালো নয় যার ভিত্তি খোদাভীতি, সততা এবং শাশ্বত সুন্দর আদর্শের অনুসরণের ওপর প্রতিষ্টিত?
চতুর্দশ অধ্যায়
ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার
ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো সামাজিক সুবিচার ও জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং নিজের সীমার মধ্যে অবস্থান করে প্রতিটি মানুষের জন্যে সন্মানজনক জীবন যাপনের ব্যবস্থাকে সহজতর করা। মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ’লা মওদূদী হজ্জ উপলক্ষে মক্কায় অনুষ্ঠিত মু’তামারে আলমে ইসলামীর সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এখানে সে প্রবন্ধটি সংকলিত হলো। এতে ইসলামী রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক নীতিমালার উপর আলোকপাত করা হয়েছে। -সংকলক
ইসলাম ও সামাজিক সুবিচার
[১৩৮১ হিজরী মুতাবেক ১৯৬২ ঈসায়ীতে হজ্জ উপলক্ষ্যে মুতামারে আলমে ইসলামীর উদ্যোগে মক্কা মুয়াজ্জামায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এই প্রবন্ধ পাঠ করা হয়]
আধুনিক কালের কতিপয় প্রতারণা
আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে যে সর্বোত্তম কাঠামোর সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে রয়েছে একটি বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব। সে সুস্পষ্ট ফিতনা ফাসাদ ও প্রকাশ্য বিপর্যয় বিশৃংখলার দিকে খুব কমই ঝুঁকে পড়ে। এজন্য শয়তান তার নিজের ফিতনা ফাসাদকে কোনো না কোনো ভাবে সংস্কার সংশোধন ও কল্যাণের ছদ্মবরণে মানুষের সামনে তুলে ধরে। শয়তান যদি বেহেশতে আদম আলাইহিস সালামকে একথা বলতো, “আমি তোমাদের দ্বারা আল্লাহর নাফারমানী করাতে চাই এবং এর ফলে তোমাদের বেহেশত থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে” তাহলে সে কখনোও তাঁদেরকে ধোঁকা দিতে পারতোনা। বরং তাঁদের সে এই বলে ধোঁকা দিলোঃ
“তোমাকে সেই গাছটি দেখিয়ে দেবো কি যার মাধ্যমে চিরন্তন জীরন ও অক্ষয় রাজত্ব লাভ করা যায়?” (সূরা ত্বাহাঃ ১২০)
মানুষের প্রকৃতি আজ পর্যন্ত এ পথেরই অনুগামী হয়েছে। আজও শয়তান তাকে যতো প্রকার বিভ্রন্তি ও নির্বুদ্ধিতায় নিক্ষেপ করেছে তার সবই কোনো না কোনো বিভ্রান্তিকর শ্লোগান এবং মিথ্যার ছত্রছায়ায় জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে।
উল্লেখিত প্রতারণাসমূহের মধ্যে একটি মারাত্মক প্রতারণা হচ্ছে, সেই প্রতারণা যা বর্তমানে সামাজিক সুবিচারের (Socisl Justice) নামে মানবজাতির সাথে করা হচ্ছে। প্রথমে শয়তান একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দুনিয়াকে ব্যক্তি স্বাধীনতা (Individual liberty) এবং উদার নীতির (Liberalism) নামে ধোঁকা দিতে থাকে এবং এবই ভিত্তিতে সে অষ্টাদশ শতকে পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন (Secular) গণতন্ত্র কায়েম করায়। এক সময় এই ব্যবস্থার এতোই প্রভাব ছিলো যে, দুনিয়াতে মানবজাতির উন্নতির জন্য এটাকে চূড়ান্ত হাতিয়ার মনে করা হতো এবং প্রত্যেক ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রগতিবাদী এবং প্রগতিশীল বলে পরিচয় করাতে পছন্ত করতো সে স্বাধীনচেতা ও উদারপন্থী হওয়ার শ্লোগান দিতে বাধ্য ছিলো। লোকেরা মনে করতো, মানব জীরনের জন্য যদি কোনো ব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে কেবল এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং এই ধর্মহীন গণতন্ত্রই আছে যা পাশ্চাত্যে কায়েম হয়েছে। কিন্তু দেখতে দেখতে সেই সময় এসে গেলো যখন গোটা বিশ্ব অনুভব করতে লাগলো যে, এই শয়তানী ব্যবস্থা পৃথিবীকে যুলুম ও স্বৈরাচারে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। এরপর অভিশপ্ত ইকলীসের পক্ষে এই শ্লোগানের দ্বারা মানুষেকে আর অধিক সময় ধোঁকা দেয়া সম্ভর ছিলোনা।
অদপর খুর বেশী সময় অতিবাহিত হতে পারেনি, এর মধ্যেই শয়তান সামাজিক সুবিচার ও সমাজতন্ত্রের নামে আরেকটি প্রতারণার জন্ম দেয়। এখন সে এই মিথ্যার ছদ্মবরণে অন্য একটি ব্যবস্থ কয়েম করাচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থা বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এতো মারাত্মক যুলুম নির্যাতন ও স্বৈরাচারে প্লাবিত করে দিয়েছে যার দৃষ্টান্ত মানব জাতির ইতিহাসে কখনো পাওয়া যায়নি। কিন্তু এই প্রতারণাপূর্ণ মতবাদটি এতোই শক্তিশালী যে, আরো কিছু সংখ্যক দেশ এটাকে উন্নতির সর্বশেষ উপায় মনে করে তা গ্রহণ করার জন্য তৈরী হচ্ছে। এখন পর্যন্ত এই প্রতারণার মুখোশ পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়নি।[ ১. এটি ১৯৬২ সালের বক্তৃতা। ইতোমধ্যেই মুখোশ উন্মোচিত হয়ে এ প্রতারণা একেবারে নগ্ন হয়ে পড়েছে। -আ. শ. ন-]
মুসলমানদের অবস্থা এই যে, তাদের কাছে আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ বর্তমান রয়েছে। এর মধ্যে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন বিধান মওজুদ রয়েছে। তা তাদেরকে শয়তানের ধোঁকা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং জীরনের সার্বিক ব্যাপারে পথনির্দেশ দেয়ার ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এই ভিক্ষুকেরা নিজেদের দীন সম্পর্ক চরম অজ্ঞ এবং সাম্রাজ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অক্রমণে নিকৃষ্টরূপে পরাজিত। এজন্য দুনিয়ার জাতিগুলোর শিবির থেকে যে শ্লোহানই উত্থিত হয় তা এখান থেকেও ত্বরিত প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে। যে যুগে ফরাসী বিপ্লব থেকে উত্থিত চিন্তা দর্শনের জোর ছিলো, মুসলিম দেশসমূহের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে সেখানে এই চিন্তা দর্শনের প্রকাশ এবং তারই আলোকে নিজেকে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক মনে করতে। পশ্চাদপন্থী মনে করা হবে। এই যুগটা যখন শেষ হলো, আমাদের আধুনিক শিক্ষিত সমাজের কেবলাও পরিবর্তন হতে শুরু করলো। নতুন যুগের সূচনা হতেই আমাদের মাঝে সামাজিক সুবিচার এবং সমাজতন্ত্রের শ্লোগান উচ্চারণকারীদের আবির্ভাব হতে থাকলো। এ পর্যন্ত পৌঁছেও ধৈর্য ধারার মতো ছিলো। কিন্তু পরিতাপের ব্যাপার হলো, আমাদের মাঝে এমন একটি দল মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো যারা নিজেদের কেবলা পরিবর্তন করার সাথে সাথে চাইতো যে, ইসলামও তার কেবলা পরিবর্তন করুক। মনে হয় বেচারারা যেনো ইসলাম ছাড়া বাঁচতে পারছেনা। তাদের সাথে ইসলামেরও থাকা দরকার আছে। কিন্তু তাদের খাহেশ হচ্ছে, সেও সন্মানিত হবে এবং ‘সেকেলে ধর্ম’ হওয়ার অপবাদ থেকেও বেঁচে যাবে। এই কারণে প্রথমে ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার নৈতিকতা, পুঁজিবাদ ও ধর্মহীন গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগিকে অবিকল ইসলামী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হতো। আর আজ এরই ভিত্তিতে প্রমাণ হচ্ছে যে, ইসলামেও সমাজতান্ত্রিক দর্শনের সামাজিক সুবিচার বর্তমান রয়েছে। এটা সেই স্তর
যেখানে পৌছে আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিক গোলামী এবং তাদের চরম অজ্ঞতার প্লাবন অপমানের চরম পর্যায়ে পৌছে গেছে।
সামাজিক সুবিচারের তাৎপর্য
আমি এই সংক্ষিপ্ত প্রবেন্ধে বলতে চাই যে, আসলে সামাজিক সুবিচার বলতে বুঝায় এবং এর প্রতিষ্ঠার সঠিক পন্থাই বা কি? যদিও এটা খুব কমই আশা করা যায় যে, যেসব লোক সমাজতন্ত্রকে ‘সামাজিক সুবিচার’ প্রতিষ্ঠার একমাত্র পন্থা মনে করে তা বাস্তবায়িত করার জন্য লেগে আছে তারা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেবে এবং তা থেকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা মূর্খ যতক্ষণ মূর্খ থাকে ততোক্ষণ তার সংশোধনের কিছু সম্ভাবনা অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু যখন সে শাসন দন্ড হতে পায় তখন “মা আলিমতু লাকুম মিন ইলাহিন গাইরী- আমি তো নিজেকে ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো খোদাকে জানিনা” (সূরা কাসাসঃ ৩৮) এই অহমিকা তাকে কোনো বুদ্ধিমান মানুষের অবস্থা ভিন্নরকম। যুক্তিযুক্ত পন্থায় তাদেরকে কথা বুঝিয়ে দিতে পারলে তারা শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে সর্তক হতে পারে। এই সাধারণ লোকদের সরলতার সুযোগ নিয়ে তাদের ধোঁকা দিয়ে পথভ্রষ্ট লোকেরা নিজেদের ভ্রন্তির প্রসার ঘটায়। এজন্য সাধারণ লোকদের সামনে প্রকৃত সত্য তুলে ধরাই মূলত আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য।
কেবল ইসলামেই রয়েছে সামাজিক সুবিচার
এ প্রসংগে আমি আমার মুসলমান ভাইদের সর্বপ্রথম যে কথা বলতে চাই তা হলো, যেসব লোক “ইসলামেও সামাজিক সুবিচার মওজূদ রয়েছে”- এই শ্লোগানে মূখর, তারা সম্পূর্ণ একটি ভাল কথা বলে। বরং সঠিক কথা হলো, “কেবলমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার রয়েছে।” ইসলাম সেই সত্য জীবন ব্যবস্থা যা বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মানবজাতির পথ পদর্শনের জন্য নাযিল করেছেন। মানবজাতির মধ্যে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা এবং তাদের জন্য কোনটি ন্যায় ইনসাফ এবং কোনটি ন্যায় ইনসাফ নয় তা নির্ণয় করা মানবজাতির সৃষ্টিকর্তারই কাজ। অন্য কেউ ন্যায় ইনসাফ ও যুলুমের মানদন্ড নির্ধারণের অধিকার রাখেন এবং তাদের মধ্যে প্রকৃত অর্থে ইনসাফ কায়েম করার যোগ্যতাও নেই। মানুষ নিজেই নিজের মালিক এবং কর্তা নয় যে, সে নিজের জন্য নিজেই সুবিচারের মানদন্ড নির্ধারণের ক্ষমতা রাখে। বিশ্বে তার মর্যাদা হচ্ছে খোদার প্রজা বা অধীনস্থ হিসেবে। এজন্য সুবিচারের মানদন্ড নিরুপণ করা তার কাজ নয়, তার মালিক এবং শাসকের কাজ। তাছাড়া মানুষ যতো উন্নত মর্যাদা সম্পন্নই হোক না কেন, এক ব্যক্তির পরিবর্তে উচ্চ মর্যাদা ও যোগ্যতা সম্পন্ন অসংখ্য লোক একত্রিত হয়ে নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধি খরচ করুক না কেন মানবীয় জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, এর ক্রটি, অনিপুণত ও অপূর্ণাংগতা এবং মানবীয় জ্ঞানের উপর প্রবৃত্তি ও গোঁড়ামির প্রভাব এসব কিছু থেকে মুক্ত হওয়া কোনো অবস্থায়ই সম্ভব নয়। এজন্যই ন্যায় ইনসাফের উপর ভিত্তিশীল কোনো জীবন বিধান নিজেদের জন্য রচনা করা মানুষের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয়। মানুষের বিধান ব্যবস্থা আপাত প্রকাশ্যত যতোই ন্যায়ানুগ বলে দৃষ্টিগোচর হোক, কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা খুব দ্রুত প্রমাণ করে দেয় যে, মূলত এর মধ্যে কোনো ন্যায়ইনসাফ নেই। এজন্য মানব মস্তিষ্ক প্রসূত প্রতিটি ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পর তা অকেজো প্রমাণ হ্য় এবং মানুষ তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দ্বিতীয় একটি নির্বুদ্ধিতা প্রসূত পরীক্ষা নীরিক্ষার দিকে ধাবিত হয়। প্রকৃত সুবিচার কেবল সেই ব্যবস্থার মধ্যেই মহাপবিত্র এক মহান সত্তা তৈরী করেছেন।
সুবিচার প্রতিষ্ঠাই ইসলামের উদ্দেশ্য
দ্বিতীয় কথা যা প্রথমেই বুঝে নেয়া দরকার তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি “ইসলামে সুবিচার আছে” বলে, সে বাস্তব ঘটনা থেকে কম বলে। বাস্তব কথা এই যে, সুবিচার হচ্ছে ইসলামের লক্ষ্য। আর সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্যই ইসলামের আগমন। মহান আল্লাহ্ বলেন:
“আমি আমার রাসূলদের উজ্জ্বল নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মীযান (মানদন্ড) নাযিল করেছি- যেনো লোকেরা সুবিচারের উপর কায়েম হয়ে যায়। আর আমরা লৌহ নাযিল করেছি। এর মধ্যে রয়েছে অসীম শক্তি এবং মানুষের জন্য কল্যাণ। আল্লাহ্ জানতে চান কে না দেখেই আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলদের সহযোগী হয়্ নিশ্চিতই আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারি এবং পরাক্রমশালী।” (সূরা আল হাদীদঃ ২৫)
এই দুটি কথা সম্পর্কে যদি কোনো মুসলমান অমনোযোগী না হয় তাহলে সে সামাজিক সুবিচারের খোঁজে আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ছেড়ে অন্য কোনো উৎসের দিকে ধাবিত হওয়ার ভ্রান্তিতে লিপ্ত হতে পারেনা। যে মুহূর্তে তার সুবিচারের প্রয়োজনীতা অনুভূত হবে তৎক্ষণাতই সে জানতে পারবে যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কারো কাছে সুবিচার নেই এবং থাকতেও পারেনা। সে এও জানতে পারবে যে, আদল কয়েম করার জন্য এছাড়া আর কিছুই করার নেই যে, ইসলাম, পূরাপূরি ইসলাম, এবং যোগ বিয়োগ ছাড়াই ইসলাম কায়েম করতে হবে। সুবিচার ইসলাম থেকে স্বতন্ত্র কোনো জিনিসের নাম নয়, স্বয়ং ইসলামই সচ্ছে সুবিচার। ইসলাম কায়েম হওয়া এবং সুবিচার কায়েম হওয়া একই জিনিস।
সামাজিক সুবিচার কি?
এখন আমাদের দেখতে হবে মূলত কোন জিনিসটির নাম সামাজিক সুবিচার এবং তা কায়েম করার সঠিক পন্থাই বা কি?
ব্যক্তিত্বের বিকাশ
প্রতিটি মানব সমাজ হাজার হাজার লাখ লাখ এবং কোটি কোটি মানুষের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এই মিশ্র সমাজির প্রতিটি ব্যক্তি সজীব, বুদ্ধিমান এবং সচেতন হয়ে থাকে। প্রতিটি সদস্যই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব এবং স্বাধীন সত্তার অধিকারী। এর বিকাশ এবং ফলে ফুলে সুশোভিত হওয়ার জন্য সুযোগের প্রয়োজন রয়েছে। প্রতিটি সদস্যেরই একটি ব্যক্তিগত ঝোঁক প্রবণতা রয়েছে। তার নিজের কিছু আকর্ষণ ও কামনা বাসনা রয়েছে। তার দেহ ও সত্বার কিছু প্রয়োজন রয়েছে। সমাজের এই সদস্যদের অবস্থা কোনো প্রণতীন যন্ত্রের খুচরা অংশের মতো নয় যে, মূল জিনিস হচ্ছে মেশিন আর খুচরা অংশগুলো তারই প্রয়োজনে তৈরী করা হয়েছে এবং এই অংশগুলোর নিজস্ব কোনো ব্যক্তিত্ব নেই। বরং মানব সমাজ জীবন্ত এবং জাগ্রত মানুষের একটি সমষ্টি। এই ব্যক্তিগণ একত্র হয়ে এই সমষ্টি বা সংগঠন এজন্যই কায়েম করে যে, পরস্পরের সহায়তায় তারা নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস অর্জন এবং দেহ ও অত্মার দাবি পূর্ণ করার সুযোগ পাবে।
ব্যক্তিগত জবাবদিহি
তাছাড়া সমস্ত মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। প্রতিটি ব্যক্তিকে এই দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট সময় পরীক্ষার মধ্য দিয়ে (যা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত) অতিবাহিত করার পর আল্লাহর দরবারে জবাবদিহির জন্য হাযির হতে হবে। তাকে এই পৃথিবীতে যে শক্তি, যোগ্যতা ও উপায় উপকরণ দান করা হয়েছেল তা কাজে লাগিয়ে সে নিজের জন্য কি ধরনের ব্যক্তিত্ব গঠন করে নিয়ে এসেছে এজন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে। আল্লাহ্র দরবাবে মানবজাতির এই জবাবদিহি সম্মিলিতভাবে নয় বরং ব্যক্তিগতভাবে হবে। সেখানে বংশ, গোত্র, জাতি একত্রে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করবেনা বরং দুনিয়ার যাবতীয় সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে আল্লহ্ তায়ালা প্রতিটি ব্যক্তিকে পৃথক ভাবে নিজের আদালতে হাযির করবেন এবং প্রত্যেককে স্বতন্ত্রভাবে জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কি করে এসেছো এবং কি হয়ে এসেছো?
ব্যক্তি স্বাধীনতা
এই দুটি ব্যাপারে অর্থাৎ পৃথিবীতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ এবং আখিরাতে মানুষের জবাবদিহির দাবি হচ্ছে পৃথিবীতে সে স্বাধীনতার অধিকার লাভ করবে। কোনো সমাজে যদি ব্যক্তিকে তার পছন্দমতো নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না দেয়া হয় তাহলে তার মধ্যে মানবতা শবদেহের মতো নির্জীব হয়ে যায়, তার দম বন্ধ হয়ে যেতে থাকে, তার শক্তি সামর্থ ও যোগ্যতা চাপ পড়ে যায়। সে নিজেকে অবরুদ্ধ ও বন্দিদশায় দেখতে পেয়ে জড়তা ও অকর্মন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। আখিরাতে এ ধরনের অবরুদ্ধ ও পরাধীন ব্যক্তির দোষ ত্রুটি বেশীর ভাগ দায় দায়িত্ব এই ধরনের সমাজ ব্যবস্থা গঠনকারী ও পরিচালনাকারীদের ঘাড়ে চাপবে। তাদের কাছ থেকে কেবল তাদের ব্যক্তিগত কর্যকলাপের হিসাব নিকাশই নেয়া হবেনা; বরং তারা যে স্বৈরাচারী ব্যবস্থা কায়েম করে অসংখ্য মানুষকে নিজেদের মর্জির বিরুদ্ধে এবং তাদের মর্জিমত ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে বাধ্য করেছে এজন্যও তাদের জবাবদিহি করতে হবে। প্রকাশ থাকে যে, কোনো ঈমানদার ব্যক্তি এ ধরনের ভরি বোঝা নিজের কাঁধে চাপিয়ে আখিরাতে আল্লাহ্র দরবারে হাযির হওয়ার কল্পনাও করতে পারেনা। সে যদি আল্লাহ্ভীরু মানুষ হয়ে থাকে তাহলে সে অবশ্যেই আল্লাহ্র বান্দাদের অধিক পরিমাণে স্বাধীনতা প্রদানের দিকেই ঝুঁকে পড়বে যেনো প্রতিটি ব্যক্তি যা হবার নিজের দায়িত্বেই হতে পারে। সে যদি নিজেকে ত্রুপিপূর্ণ ও ভ্রান্তি ব্যক্তিত্ব হিসেবে গঠন করে তাহলে এ দায়িত্ব তখন আর সমাজের পরিচালকদের উপর চাপবেনা। সামাজিক সংস্থা এবং এর কতৃত্ব
এতো গেলো ব্যক্তি স্বধীনতার ব্যাপার। অপরদিকে সমাজকে দেখুন যা পরিবার, বংশ গেত্র, জাতি এবং গোটা মানবতার আকারে পর্যয়ক্রমিকভাবে কায়েম আছে। একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোক ও তাদের সন্তানদের নিয়ে এই সমাজের সূচনা হয়। এদের দ্বারা একটি পরিবার গঠিত হয়। পরিবারের সমন্বয়ে বংশ, গোত্র ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে। তাদের সমন্বয়ে একটি জাতি অস্তিত্ব লাভ করে এবং জাতি তার সামষ্টিক ইচ্ছা আকাংখার বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কয়েম করে। বিভিন্ন আকৃতিতে এই সামাজিক সংস্থাগুলো আসলে যে উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজন তা হচ্ছে এই সংস্থার তত্ত্বাবধানে ও এর সহায়তায় ব্যক্তি তার ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভ করবে, যা তার একার প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। কিন্তু এ মৌলিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে উল্লেখিত প্রতিটি সংস্থার হাতে ব্যক্তিদের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার থাকতে হবে, যাতে এই সংস্থাগুলো এমন ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিরোধ করতে পারে যা অন্যদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা পর্যায়ে পৌঁছে সামাজিক সুবিচারের প্রশ্ন দেখা দেয় এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির পরস্পর বিরোধী দাবিসমূহ একটি গ্রন্থির আকার ধানণ করে। একদিকে মানব কল্যাণের দাবি হচ্ছে হলো, সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকতে হবে যেনো সে নিজের যোগ্যতা ও পছন্দ মাফিক নিজের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করতে পারে। অনুরূপভাবে পরিবার, বংশ গোত্র, ভ্রতৃবন্ধন এবং অন্যান্য সংস্থা যেনো নিজেদের চেয়ে বৃহত্তর পরিধির মধ্যে স্বাধীরতা ভোগ করতে পারে যা তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমার মধ্যে তাদের অর্জিত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু অপর দিকে মানব কল্যাণেরই দবি হচ্ছে ব্যাক্তির উপর পরিবারের, পরিবারের উপর বংশের, ভ্রাতৃবন্ধনের এবং সমস্ত লোকের ও ছোট সংস্থার উপর বড় সংস্থার এবং বৃহৎ পরিসরে বাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থাকতে হবে, যেনো কেউ নিজের সীনা অতিক্রম করে অন্যদের উপর যুলুম নির্যাতন ও বাড়াবাড়ি করতে না পারে। আরো সামনে অগ্রসর হলে গোটা মানব জাতির ক্ষেত্রেও এই একই প্রশ্ন দেখা দেয়। একদিকে প্রতিটি জাতি এবং রাষ্ট্রের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় থাকার প্রয়াজন রয়েছে, অপরদিকে কোনো উচ্চতর ক্ষমতা সম্পন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার বর্তমান থাকারও প্রয়োজন রয়েছে যাতে কোনো জাতি বা রাষ্ট্র সীমা লংঘন করতে না পারে।
এখন সামাজিক সুবিচার যে জিনিসের নাম তা হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, বংশ, ভ্রাতৃসমাজ এবং জাতির মধ্যে প্রত্যেকের যুক্তিসংগত পরিমাণ স্বাধীনতাও থাকতে হবে এবং সাথে সাথে যুলুম শত্রুতা ও সীমা লংঘনকে প্রতিহত করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাসমূহের হাতে ব্যক্তিদের উপর এবং একে অপরের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকারও থাকতে হবে। যাতে করে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবাও আদায় করা যেতে পারে।
পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের ত্রুটি
এই সত্যকে যে ব্যক্তি ভালোভাবে হৃদয়ংগম করে নেবে সে প্রথম দৃষ্টিতেই জানতে পারবে যে, ফরাসী বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার নৈতিকতা, পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা যে ভাবে সামাজিক সুবিচারের পরিপন্থী ছিলো ঠিক তদ্রূপ বরং তার চেয়েও অধিক পরিমাণ সমাজতান্ত্রিক মতবাদ সামাজিক সুবিচারের সম্পূর্ণ বিরোধী, যা কার্লমার্কস এবং এঞ্জেলসের দর্শনের অনুসরণে গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে হলো, সে ব্যক্তিকে যুক্তিসংগত সীমার অধিক স্বাধীনতা দান করে পরিবার, বংশ, প্রতিবেশী, সমাজ এবং জাতির উপর বাড়াবাড়ি করার অবাধ সুযোগ দিয়ে দিলেছে এবং তার কাছ থেকে সামাজিক কল্যাণরে জন্য সেবা গ্রহণ করার জন্য সমাজের নিয়ন্ত্রক শক্তিকে খুবই ঢিলা করে দিয়েছে। আর দ্বিতীয় ব্যবস্থাটির ত্রুটি হচ্ছে এই যে, তা রাষ্ট্রকে সীমাতিরিক্ত শক্তিশালী করে ব্যক্তি, পরিবার, বংশ ও ভ্রাতৃবন্ধনের স্বাধীনতার প্রায় সবটুকুই হরণ করে নেয় এবং ব্যক্তির কাছ থেকে সমষ্টির জন্য সেবা আদায় করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে এতো অধিক ক্ষমতা দেয় যে, ব্যক্তি প্রাণবন্ত মানুষ হওয়ার পরিবর্তে একটি মেশিনের প্রাণহীন অংশে পরিণত হয়। কেউ যদি বলে এই মতবাদের মাধ্যমে সামাজিক সুবিচার কায়েম হতে পারে, সে ডাহা মিথ্যা কথা বলে।
সামাজিক নির্যাতনের নিকৃষ্টমত রূপ সমাজন্ত্র
এটা মূলত সামাজিক যুলুম ও নির্যাতনের সেই নিকৃষ্টতম রূপ যা কখনো কোনো নমরূদ, কোনো ফিরাউন এবং কোনো চেংগিজ খানের যুগেও ছিলোনা। শেষ পর্যন্ত এই জিনিসিটিকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি “সামাজিক সুবিচার” নামে ব্যাখ্যা করতে পারে যে, এক ব্যক্তি অথবা কয়েক ব্যক্তি বসে নিজেদের একটি সামাজিক দর্শন রচনা করে নেবে, অতপর রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে এই দর্শনকে জোরপূর্বক পূরা করবে, জমাজম দখল করে নেবে, শিল্প কারখানা জাতীয় মালিকানায় নিয়ে নেবে এবং গোটা দেশটাকে এমন একটি জেলখানায় পরিণত করবে যার মধ্যে সমালোচনা, ফরিয়াদ, অভিযোগ ও সাহায্য প্রার্থনা করার পথ রূদ্ধ হয়ে যাবে? দেশের মধ্যে কোনো দল থাকবেনা, কোনো সংগঠন থাকবেনা, কোনো প্লাটফরম থাকবেনা যেখানে লোকেরা মুখ খুলতে পারবে, কোনো প্রেস থাকবেনা যেখানে লোকেরা মত প্রকাশের সুযোগ পাবে এবং কোনো বিচারালয় থাকবেনা ইনসাফ পাবার আশায় যার দরজার কড়া নাড়া যাবে। গোয়েন্দাগিরির জাল ব্যপকভাবে বিস্তার করে দেয়া যাতে প্রতিটি ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে ভয় করবে যে, হয়তো এও গোয়েন্দা বিভাগের লোক। এমনকি নিজের ঘরের মধ্যেও মুখ খোলার সময় কোনো ব্যক্তি জবান তার কথা সরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছে দেয়ার জন্য নিকটে কোথাও লুকিয়ে নেই তো? তাছাড়া গণতন্ত্রের ধোঁকা দেয়ার জন্য নির্বাচন অনুষ্টান করানো হবে, কিন্তু সমগ্র প্রচেষ্টা নিয়োজিত হবে যাতে এই দর্শন রচনাকারীদের সাথে দ্বিমত পোষণকারী এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে না পারে এবং এমন কোনো ব্যক্তিও যেনো তাতে প্রবেশ করতে না পারে যার স্বতন্ত্র মত রয়েছে এবং যে নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিক্রি করতে প্রস্তুত নয়।
যদি ধরেও নেয়া যায় যে, এই পন্থায় আর্থিক সমবন্টন হতে পারে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে আজ পর্যন্ত কোনো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তা করতে সক্ষম হয়নি। তারপরও কি অর্থিক সমতার নামই কেবল সামাজিক সুবিচার? আমি এ প্রশ্ন তুলছে না যে, এই ব্যবস্থায় শাসক এবং শাসিতের মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্য আছে কি না? আমি এ প্রশ্নও তুলছি না যে, এই ব্যবস্থায় ডিকটেটর এবং তার অধীন একজন কৃষকের জীরন যাত্রার মধ্যে সমতা আছে কি না? আমি কেবল এই প্রশ্ন করছি যে, বা্স্তবিকই যদি তাদের মধ্যে পূর্ণ আর্থিক সমতা কায়েম হয়েও থাকে তাহলে এরই নাম কি সামাজিক সুবচার হবে? এটা কি ধরনের সামাজিক সুবিচার যে, এক ডিকটেটর ও তার সাংগপাংগরা যে দর্শন রচনা কনেছে তা পুলিশ বাহিনী, সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা ব্যবস্থার সহায়তায় জাতির, ঘাড়ে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবে এবং জাতির কোনো ব্যক্তির এই দর্শনের উপর, অথবা তা কর্যকর করার কোনো ক্ষুদ্রতর পদক্ষেপের বিরুদ্ধেও মুখ দিয়ে একটি বাক্যও বের করার স্বাধীনতা থাকবেনা? এটা কি ধরনের সামাজিক সুবিচার যে, এ ডিকটেটর ও তার মুষ্টিমেয় সাথী নিজেদের দর্শনের প্রজার ও প্রসারের জন্য গোটা দেশের উপায় উপকরণ ব্যবহার এবং যে কোনো ধরনের সংগঠন ও সংস্থা কায়েম করার অধিকার ভোগ করবে, কিন্তু তাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী দুই ব্যক্তিও একত্র হয়ে কোনো সংগঠন কায়েম করতে পারবেনা, কোনো জনসমাবেশে ভাষণ দিতে পারবেনা এবং কোনো প্রচার মাধ্যমে একটি শব্দও প্রচার করতে পারবেনা? এর নাম কি সামাজিক সুবিচার যে, গোটা দেশের জমির এবং কলকারখানার মালিকদের বেদখল করে দিয়ে একজন মাত্র জমিদার এবং একজন মাত্র শিল্পপতি থাকবে যার নাম হচ্ছে রাষ্ট্র? আর সেই রাষ্ট্র থাকবে হাতে গোনা কয়েক ব্যক্তির কজায় এবং এই লোকগুলো এমন সব কর্মপন্থা গ্রহণ করবে যার ফলে গোটা জাতি সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়বে এবং রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব তাদের দখল থেকে অন্যদের হাতে চলে যাওয়াটা সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে যাবে? শুধু পেটের নাম যদি মানুষ না হয়ে থাকে এবং মানবজীবন শুধু অর্থনীতি পর্যন্ত সীমিত না হয়ে থাকে তাহলে কেবল আর্থিক সমতাকে কি করে সুবিচার বলা যেতে পারে? জীবনের প্রতিটি বিভাগে যুলুম নির্যাতন কায়েম করে, মানবতার প্রতিটি গতিকে প্রতিহত করে শুধু অর্থিক সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে জনগণকে যদি এক সমান করেও দেয়া হয় এবং স্বয়ং ডিকটেটর এবং তার সাংগপাংগরাও নিজেদের জীবনযাত্রায় জনগণের সমপর্যায়ে নেমে আসে তবুও এই বিরাট যুলুমের মাধ্যমে এই সমতা প্রতিষ্ঠা করা সামাজিক সুবিচার বলে অখ্যায়িত হতে পারেনা। বরং এটা আমি পূর্বেও যেমন বলে এসেছি সেই নিকৃষ্টতম সামাজিক নির্যাতন যার সাথে মানবেতিহাস ইতিপূর্বে কখনো সাক্ষাত লাভ করেনি।
ইসলামে সামাজিক সুবিচারের ধারণা
এবার আমি আপনাদের বলবো, ‘ইসলাম’ যার অপর নাম ‘সুবিচার’ তা কি? কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী মানব জীবনের জন্য ন্যায় ইনসাফের কোনো দর্শন রচনা জনগণের উপর তা চাপিয়ে দেবে আর যে কোনো প্রতিবাদকারীর কন্ঠস্বরকে স্তব্ধ করে দেবে এরূপ করার কোনো অবকাশ ইসলামে নেই। আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা অনহু এবং উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তো দূরের কথা স্বয়ং সুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও এরুপ করার কোনো অধিকার ছিলোনা। কেবল আল্লাহ্ তায়ালারই এই অধিকার ও ক্ষমতা রয়েছে যে, মানুষ বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁর সামনে মস্তক অবনত করে দেবে। স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর হুকুমের অধীন ছিলেন। তাঁর (নবীর) নির্দেশের আনুগত্য করা কেবল এজন্য ফরয ছিলো যে, তিনি খোদার পক্ষ থেকেই নির্দেশ দিতেন, মাআযাল্লাহ নিজের পক্ষ থেকে দর্শন রচনা করে নিয়ে আসতেননা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং রসূলের খলীফাদের ব্যবস্থায় কেবল শরীয়তে ইলাহিয়াই সমালোচনার ঊর্ধ্বে ছিলো। এরপর প্রতিটি ব্যক্তিরই যে কোনো ব্যাপরে মুখ খোলার পূর্ণ অধিকার ছিলো।
ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা
আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই ইসলামে মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতার সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। একজন মুসলিক ব্যক্তির জন্য কোন কাজ হারাম যা থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে এবং কোন কোন জিনিস ফরয যা তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে, তা আল্লাহ্ তায়ালা নিজেই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অন্যদের উপর তার কি কি অধিকার রয়েছে এবং তার উপর অন্যদের কি কি অধিকার রয়েছে, কি উপায় উপকরণের মাধ্যমে কোন সম্পদের মালিকানা তার হস্তগত হওয়া জায়েয এবং এমন কি কি উপায় উপাদান রয়েছে যার মাধ্যমে কোনো সম্পদের মালিকানা হস্তগত হলে তা জায়েয হবেনা, ব্যক্তির কল্যাণের জন্য সমষ্টির এবং সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির কি দায়িত্ব রয়েছে, ব্যক্তির উন্নতির জন্য বংশ, পরিবার, গেত্র এবং গোটা জাতির উপর কি বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যায় এবং কি করা অত্যাবশ্যকীয় করে দেয়া যায়, এসব কিছুই কিতাব ও সুন্নাহর চিরস্থায়ী সংবিধানে বর্তমান রয়েছে যার উপর হস্তক্ষেপ করার এবং যাতি সংযোজন ও সংকোচন করার অধিকার কারো নেই। এই সংবিধানের আলোকে কোনো লোকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যে গন্ডি নির্দেশ করে দেয়া হয়েছে তা হরণ করে নেয়ার অধিকার কারো নেই। আয় উপার্জনের যেসব উপায় এবং তা ব্যয়ের যেসব পন্থা হরাম করা হয়েছে সে তার কাছেও ঘেঁষতে পারবেনা। যদি সে ঐ নিষিদ্ধ পথে পা বাড়ায় তাহলে ইসলামী আইন তাকে শাস্তির যোগ্য মনে করে। কিন্তু যেসব উপায় ও পন্থা বৈধ সাব্যস্ত করা হয়েছে তার মাধ্যমে অর্জিত মালিকানার উপর তার অধিকার সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ থাকবে এবং ব্যয়ের যেসব খাত বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে তা থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারবেনা। অনুরূপভাবে সমষ্টির কল্যাণের জন্য ব্যক্তির উপর যেসব দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে তা পালন করতে সে বাধ্য। কিন্তু এর অধিক বোঝা তার উপর চাপানো যাবেনা। তবে সে যদি স্বেচ্চায় অতিরিক্ত কছু করতে চায় তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। সমষ্টি এবং রাষ্ট্রের অবস্থাও তদ্রূপ। তার উপর ব্যক্তির যে অধিকার রয়েছে তা ব্যক্তিকে পৌছিয়ে দেয়া তার জন্য বাধ্যতামূলক, যেভাবে সমষ্টি এবং রাষ্ট্র নিজ নিজ অধিকার তার কাছ থেকে আদায় করে নেয়ার এখতিয়ার রাখে। এই চিরস্থায়ী সংবিধানকে যদি কর্যত বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে বাঞ্ছিত সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে, যার পর আর কোনো জিনিসের দাবি অবশিষ্ট থাকেনা। এই সংবিধান যতক্ষণ বর্তমান থাকবে, ততক্ষাণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি যতোই চেষ্টা করুক না কেন মুসলমানদের কখনো এই ধোঁকায় ফেলতে পারবেনা যে, সে কোথাও থেকে যে সমাজতন্ত্র ধার করে নিয়ে এসেছে সেটাই খাঁটি ইসলাম।
ইসলামের এই চিরস্থায়ী সংবিধান ব্যক্তি এবং সমষ্টির মধ্যে এমন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে সমষ্টির স্বার্থ ক্ষুন্ন করার কোনো অধিকার ব্যক্তিকে দেয়া হয়নি এবং সমষ্টিকেও এমন কোনো এখতিয়ার দোয়া হয়নি যার মাধ্যমে সে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গঠন ও এর পরিপোষণের জন্য তার প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা হরণ করতে পারে।
সম্পদ হস্তান্তরের শর্তসমূহ
ইসলাম কোনো ব্যক্তির হাতে সম্পদ আসার মাত্র তিনটি পথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। উত্তরাধিকার, দান এবং উপার্জন। কোনো সম্পদের বৈধ মালিকের কাছ থেকে ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক কোনো ওয়ারিস যে সম্পদ লাভ করে থাকে কেবল এই ধরনের উত্তরাধিকারই গ্রহণযোগ্য। কোনো সম্পদের বৈধ মালিক শরীয়তের সীমার মধ্যে যে দান বা উপটৌকন দিয়ে থাকে কেবল তাই বিবেচনাযোগ্য। এই দান যদি কোনো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে তাহলে এটা কেবল এমন অবস্থাই জায়েয হবে যখন তা কোনো বিশেষ খিদমতের জন্য অথবা সমষ্টির স্বার্থের জন্য রাষ্ট্রীয় মালিকানা থেকে ন্যায়ানুগ পন্থায় দেয়া হয়। অনন্তর এই ধরনের দান করার অধিকার কেবল এমন রাষ্ট্রেরই রয়েছে যা শরীয়ত ভিত্তিক সংবিধান অনুযায়ী সংসদীয় পন্থায় পরিচালিত হয় এবং যার কাছে কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে। এখন থাকলো উপার্জনের ব্যাপার, যে উপার্জন হারাম পন্থায় হয়নি ইসলাম কেবল তারই স্বীকৃতি দেয়। চুরি, আত্মসাত, ওজনে কম বেশী, আমানত আত্মসাত, ঘুষ, বেশ্যাবৃত্তি, মজুতদারী (নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা এবং নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বিস্তারকারী ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জন করা ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। এসব সীমারেখা বজায় রেখে কারো হাতে যে সম্পদ এসে যায় সে তার বৈধ মালিক, চাই তা বেশী হোক অথবা কম। এ ধরনের মালিকানার জন্য কোনো নিম্নতম সীমাও নির্ধারণ করা যেতে পারেনা, আর না উচ্চতম সীমা। পরিমাণ এই সীমার কম হওয়াতে অন্যের সম্পদ ছিনিয়ে এনে তা বৃদ্ধি করে দেয়াও জায়েয নয়, আর নির্দিষ্ট সীমার অধিক পরিমাণ হয়ে গেলে তা জোরপূর্বক ছিনিয়েও নেয়া যাবেনা। অবশ্য এই বৈধ সীমা অতিক্রম করে যে সম্পদ অর্জিত হয়েছে তার সম্পর্কে মুসলমানদের এই প্রশ্ন তোলার অধিকার রয়েছে, “মিন আইনা লাকা হাযা” এ সম্পদ তুমি কোথায় পেলে? এই ধরনের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রথমে আইনানুগ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। অতপর যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, তা বৈধ পন্থায় উপার্জিত হয়নি তাহলে এটা বাজেয়াপ্ত করার পুর্ণ অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে।
সম্পদ ব্যয়ের উপার নিয়ন্ত্রণ আরোপ
বৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও ব্যক্তিকে অবাধ সুযোগ দেয়া হয়নি। বরং এখানেও কিছু আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। যাতে কোনো ব্যক্তি এমন পথে তা ব্যয় করতে না পারে যা সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে, অথবা তার মাধ্যে স্বয়ং সম্পদের মালিকের দীনি এবং নৈতিক ক্ষতি বিদ্যমান রয়েছে। ইসলামে কোনো ব্যক্তি নিজের ধন সম্পদ পাপ কাজে ব্যায় করতে পারেনা। মদপান এবং জুয়া খেলার দরজা তার জন্য বন্ধ। যেনা ব্যভিচারের দরজাও তার জন্য রুদ্ধ। ইসলাম স্বাধীন মানুষকে ধরে নিয়ে গোলাম বাঁদীতে পরিণত করা এবং তার ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার কাউকে দেয়না এবং তাদের ক্রয় করে সম্পদশালী লোকদের ঘর বোঝাই করার অধীকারও দেয়না। অপচয় এবং সীমাতিরিক্ত ভোগ বিলাসের উপরও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। ব্যক্তির ভোগ বিলাসের উপরও ইসলাম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। নিজে ভোগ বিলাসে ডুবে থাকবে আর প্রতিবেশী অভুক্ত অবস্থায় রাত কাটাবে ইসলাম তা মোটেই জায়েয রাখেনি। ইসলাম ব্যক্তিকে কেবল শরীয়ত সম্মত এবং ন্যায়ানুগ পন্থায়ই সম্পদের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অধিকার দান করে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের মাধ্যমে যদি কেউ আরো অধিক সম্পদ আয় করার জন্য তা ব্যবহার করতে চায় তাহলে সে সম্পদ অর্জনের বৈধ পন্থাই অবলম্বন করতে বাধ্য। উপার্জনের শরীয়ত সম্মত পন্থার বাইরে সে যেতে পারেনা।
সামাজিক সেবা
যে ব্যক্তির কাছে নেসাবের অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে, সমাজ সেবার উদ্দেশ্যে ইসলাম তার উপর যাকাত ধার্য করে। অনন্তর সে ব্যবসায়িক পণ্য, জমির ফসল, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু এবং আরো অন্যান্য সম্পদের উপর নির্দিষ্ট হারে যাকাত ধার্য করে। আপনি দুনিয়ার কোনো একটি দেশ বেছে নিন এবং হিসেব করে দেখুন, সেখানে যদি শরীয়তের নীতি অনুযায়ী নিয়মিত যাকাত আদায় করা হয় এবং কুরআন নির্ধারিত খাতসমূহে তা বন্টন করা হয় তাহলে কয়েক বছর পরই সেখানে আর এমন কোনো ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যাবেনা যে জীবন ধারণের উপকরণ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছে।
এরপরও কোনো ব্যক্তির কাছে যে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকে তার মৃত্যুর সাথে সাথে ইসলাম তা তার ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টন করে দেয়। যাতে সম্পদের এই স্তুপ একটি স্থায়ী স্তুপে পরিণত হয়ে থাকতে না পারে।
যুলুমের মূলোৎপাটন
তাছাড়া ইসলাম যদিও এটাই পছন্দ করে যে, জমির মালিক এবং শ্রমিক অথবা কারখানার মালিক এবং শ্রমিকের মধ্যকার ব্যপারগুলো সন্তোষের ভিত্তিতে ন্যায়ানুগ পন্থায় সমাধান হোক এবং আইনের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন না হোক, কিন্তু যেখানেই এই ব্যাপারে যুলুম চলছে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করার পূর্ণ অধিকার রাখ এবং আইনের মাধ্যমে ইনসাফের সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারে।
জনস্বার্থের জন্য জাতীয় মালিকানার সীমা
রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা ইসলাম হারাম করেনি। যদি কোনো শিল্প অথবা ব্যবসা এমন হয় যে, তা জনস্বার্থের জন্য জরুরী বটে কিন্তু মালিকানায় তা পরিচালনা করতে কেউ প্রস্তুত নয় অথবা ব্যক্তি মালিকানায় তা পরিচালিত হওয়াটা সমষ্টিগত স্বার্থের পরিপন্থী, তাহলে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা যেতে পারে। তাছাড়া কোনো শিল্প অথবা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যদি কতিপয় ব্যক্তির মালিকানায় এমন পদ্ধতিতে পরিচালিত হয় যা সমষ্টিগত স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর, এক্ষেত্রে সরকার মালিকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে এবং অন্য কোনো পন্থায় তা পরিচালনার ব্যাপারে শরীয়তের কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু ইসলাম এটাকে একটি মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেনা যে, সম্পদ সৃষ্টির যারতীয় উপায় উপকরণ সরকারী মালিকানায় থাকবে এবং রাষ্ট্রই হবে একক শিল্পপতি, ব্যবসায়ী এবং একচ্ছত্র মালিক।
বাইতুলমাল ব্যয়ের শর্তাবলী
বইতুলমাল (ট্রেজারী) সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এই যে, তা আল্লাহ্ এবং মুসলিম জনগণের সম্পদ এবাং তা ব্যয় করার মালিকানা স্বাত্ত্ব কারো নেই। মুসলমানদের যাবতীয় বিষয়ের মতো বাইতুল মালের ব্যবস্থাপনাও জাতি অথবা তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পরামর্শ অনুযায়ী হতে হবে। যার তাছ থেকেই কিছু নেয়া হবে এবং যে খাতেই সম্পদ ব্যয় করা হবে তা অবশ্যই শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় হতে হবে এবং এ সম্পর্কে হিসেব চাওয়ার পূর্ণ অধিকার জনগণের থাকবে।
একটি প্রশ্ন
এই আলোচনার শেষ পর্যায়ে আমি প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির সামনে একটি প্রশ্ন রাখতে চাই। কেবল ‘অর্থনৈতিক সুবিচারের’ নামই যদি ‘সামাজিক সুবিচার’ হয়ে থাকে, তাহলে ইসলাম যে অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে তা কি আমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? এরপরও কি এমন কোনো প্রয়োজন অবশিষ্ঠ থাকে যার জন্য সমগ্র জাতির স্বাধীনতা হরণ করা, তাদের ধন সম্পদ হরণ করা এবং গোটা জাতিকে মুষ্টিমেয় কয়েক ব্যক্তির গোলামে পরিণত করাই অপরিহার্য হয়ে পড়বে? আমরা মুসলমানরা আমাদের দেশসমুহে ইসলামী সংবিধান অনুযায়ী শরীয়ত ভিত্তিখ খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করবো এবাং সেখানে কাটছাট ব্যতিরেকেই আল্লাহ্র দেয়া শরীয়তকে কোনো সংযোজন সংকোচন ছাড়াই কর্যকর করবো এ পথে আমাদের জন্য শেষ পর্যন্ত কি প্রতিবন্ধক থাকতে পারে? যেদিনই আমরা এটা করতে পারবো, সেদিন কেবল সমাজদন্ত্র থেকে ফয়েয গ্রহন করার প্রয়োজনীতাই শেষ হয়ে যাবেনা বরং সাথে সাথেসমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের জনগণ আমাদের জীরন ব্যবস্থা দেখে অনুভব করতে থাকবে, যে আলোর অভাবে তারা অন্ধকারে সাঁতার কাটছে তা তাদের চোখের সামনেই বর্তমান রয়েছে।
পঞ্চদশ অধ্যায়
ইমলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালা
(কুরআনের আলোকে)
১। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য
২। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি
৩। পরামর্শ বা শূরা
৪আদল ও ইহসান
৫। নেতৃত্ব নির্বাচনের মূলনীতি
৬। প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধ ও সন্ধির মূলনীতি
৭। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং শিক্ষানীতির সাধরণ মূলনীতি
৮। নাগরিকত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি
এ খন্ডের শেষ নিবন্ধটির শিরোনাম হলো “ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালা”। এ বিষয়টি সংকলিত হয়েছে মাওলানার বিখ্যাত তাফসীর তাফহীমুল কুরআনে প্রদত্ত বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যামূলক টীকার সমন্বয়ে। মাওলানার এ তাফসীর আধুনিককালের ইসলামী সাহিত্য সম্বরের শিরমনি। প্রথম খন্ডে আমরা এ তাফসীরের টীকা দিয়েই ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন, অংশটি উপস্থাপন করেছি। এখন সে তাফসীরের টীকা দিয়েই ইসলামী রাষ্ট্রের কার্যব্যবস্থা ও তার পলিসির প্রধান প্রধান নীতিমালা উপস্থাপন করছি। এখানে সংক্ষিপ্ত কিন্তু সর্বাংগিনতার সাথে সেই সব নীতিমালা উল্লেখ হয়েছে, যেগুলোর ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র আর্থ রাজনৈতিক এবং শিক্ষা ও সামাজিক পলিসি প্রণয়ন করবে। এখনে উল্লেখিত প্রতিটি মূলনীতিই স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিকারী। এগুলো কার্যকর করার মাধ্যমে সুন্দরতম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আর এটাই ইসলামের কাম্য। যাতে করে মানুষ পৃথিবীতে এমনভাবে জীবন-যাপন করতে সক্ষম হয় যে, এ পৃথিবীতেও থাকবে তারা শান্তিতে ও নিরাপদে আর পরকালের জীবনেও থাকবে অতীব সুখে। আয়াতগুলোর অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা স্বয়ং মাওলানার লিখিত। বক্তব্যের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখার জন্যেই কেবল সংকলক মাঝে মাঝে দু’একটি বাক্য সংযোজন করে দিয়েছেন। -সংকলক
১. রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য
কুরআনের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হলোদ, সততা, সুবিচারও আল্লাহ্র আইনের প্রতিষ্ঠাঃ
ক. “এরা হলো সেসব লোক, যাদেরকে আমরা পৃথিবীর কর্তৃত্ব দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত পরিশোধ করবে, সৎ কর্মের নির্দেশ দেবে এবং অসৎ কর্মে বাঁধা দেবে। সকল কাজের পরিণতি আল্লাহ্র ইখতিয়ারভুক্ত।” (সূরা আল হজ্জঃ ৪১)
অর্থাৎ আল্লাহ্র সাহায্যকারী এবং তাঁর সাহায্য ও সহায়তা লাভের অধিকারী লোকদের গুণাবলী ব্যক্তিগত জীবনে ফাসেকী, দুষ্কৃতি, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার শিকার হবার পরিবর্তে নামাজ কায়েম করবে। তাদের ধন সম্পদ বিলাসিতা ও প্রবৃত্তি পূজার পরিবর্তে যাকাত দানে ব্যায়িত হবে। তাদের রাষ্ট্রযন্ত্র সৎকাজকে দাবিয়ে দেবার পরিবর্তে তাকে বিকশিত ও সম্প্রসারিত করার দায়িত্ব পালন করবে। তাদের শক্তি অসৎকাজকে ছাড়াবার পরিবর্তে দমন করার কাজে ব্যবহৃত হবে। একটি বাক্যের মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য এবং তার কর্মী ও কর্মকর্তাদের বৈশিষ্টের নির্যাস বের করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি বুঝতে চায় ইসলামী রাষ্ট্র আসলে কোন জিনিসের নাম, তাহলে এ একটি বাক্য থেকেই তা বুঝে নিতে পারে।
এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষত্ব হলো এই যে, তাদেরকে গোটা মানবতার জন্য সত্য কল্যাণ ও ন্যায়ের আহবায়ক বানানো হয়েছে। তাকে ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে হবেঃ
খ. “আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি ‘মধ্যপন্থী’ উম্মতে পরিণত করেছে, যাতে তোমরা দুনিয়াবাসীদের ওপর সাক্ষী হতে পারো এবং রসূল হতে পারেন তোমাদের ওপর সাক্ষী। (সূরা আল বাকারাঃ ১৪৩)
এটি হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের নেতৃত্বের ঘোষণাবাণী। ‘এভাবেই’ শব্দটির সাহায্যে দুদিকে ইংগিত করা হয়েছে। একঃ আল্লাহ্র পথ প্রদর্শনের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। যার ফলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যাকারীর সত্য সরল পথের সন্ধার পেয়েছে এবং তারা উন্নতি করতে করতে এমন একটি মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে যেখানে তাদেরকে ‘মধ্যপন্থী’উম্মত গণ্য করা হয়েছে। দুইঃ এ সাথে কিবলাহ পরিবতর্নের দিকেও ইয়গিত করা হয়েছে।
অর্থাৎ নির্বোধরা একদিক থেকে আর এদিকে মুখ ফিরানো মান করছে। অথচ বাইতুল মাকদিস থেকে কাবার দিকে মুখ ফিরানোর অর্থ হচ্ছে, মহান আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলরকে বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব পদ থেকে যথা নিয়মে হটিয়ে উম্মতে মুহাম্মদীয়কে সে পদে বসিয়ে দিলেন।
‘মধ্যপন্থী উম্মত’ শদ্বটি অত্যন্ত গভীর ও ব্যপক তাৎপর্যর অধিকারী। এর অর্থ হচ্ছ, এমন একটি উৎকৃষ্ট ও উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন দল, যারা নিজেরা ইনসাফ, ন্যায় নিষ্ঠা ও ভারসাম্যের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, দুনিয়ার জাতিদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় আসন লাভের যোগ্যতা রাখে, সত্য ও সততার ভিত্তিতে সবার সাথে যাদের সম্পর্ক সমান এবং কারোর সাথে যাদের কোনো অবৈধ ও অন্যায় সম্পর্ক নেই।
বলা হয়েছে, তোমাদেরকে মধ্যপন্থী উম্মতে পরিণত করার কারণ হচ্ছে, “তোমরা লোকদের ওপর সাক্ষী হবে এবং রমূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের উপর সাক্ষী হবেন।” এ বক্তব্যের অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে আখিরাতে যখন সমগ্র জাতিকে একত্র করে তাদের হিসেব নেয়া হবে, তখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দায়িত্বশীল প্রতিনিধি হিসেবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ব্যাপারে এ মর্মে সাক্ষ্য দিবেন যে, সুস্থ ও সঠিক চিন্তা এবং সৎ কাজ ও সুবচারের যে শিক্ষা দিয়ে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল তা তিনি তোমাদের কাছে হুবহু এবং পূরোপূরি পৌঁছেযে দিয়েছেন আর বাস্তবে সেই অনুযায়ী নিজে কাজ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্থালাভিষিক্ত হিসেবে সাধারণ মানুষদের ব্যাপারে তোমাদের এই মর্মে সাক্ষ্য দিতে হবে যে, রসূল তোমাদের কাছে যা কিছু পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন তা তোমরা সাধারণ সনুষের কাছে পৌঁছেয়ে দিয়েছো। আর তিনি যা কিছু কার্যকর করে দেখিয়ে ছিলেন তা তাদের কাছে কার্যকর করে দেখাবার ব্যাপারে তোমরা মোটেই গড়িমসি করোনি।
এভাবে কোনো ব্যাক্তি বা দলের এ দুনিয়ায় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাক্ষ্য দানের দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়াটাই মূলত তাকে নেতৃত্বের মর্যাদার অভিষিতক্ত করার নামান্তর। এর মধ্যে যেমন একদিকে মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির প্রশ্ন রয়েছে তেমনি অন্যদিকে রয়েছে দায়িত্বের বিরাট বোঝা। এর সোজা অর্থ হচ্ছে, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে এ উম্মতের জন্য আল্লাহ্ ভীতি, সত্য সঠিক পথ অবলম্বন, সুবিচার, ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্য প্রীতির জীবন্ত সাক্ষী হয়েছেন, তেমনিভাবে এ উম্মতকেও বিশ্ববাসীর জন্য জীরন্ত সাক্ষীতে পরিণত হতে হবে। এমন কি তাদের কথা, কর্ম, আচরণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি বিষয় দেখে দুনিয়াবাসী আল্লাহ্ ভীতি, সততা, ন্যায় নিষ্ঠা ও সত্য প্রীতির শিক্ষা গ্রহণ করবে। এর আর একটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্র হিদায়াত আমাদের কাছে পৌছাবার ব্যাপারে যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব ছিলো বড়ই কঠিন, এমনকি এ ব্যাপারে সামান্য ত্রুটি বা গাফলতি হলে আল্লাহ্র দরবারে তিনি পকড়াও হতেন, অনুরূপভাবে এ হিদায়াতকে দুনিয়ার সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারেও আমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যদি আমরা আল্লাহ্র আদালতে পথার্থই এ সাক্ষ্য দিতে ব্যার্থ হই যে, “তোমার রসূলের মাধ্যমে তোমার যে হিদায়াত আমরা পেয়েছিলাম তা তোমার বান্দাদের কাছে পৌঁছাবার ব্যাপারে আমরা কোনো প্রকার ত্রুটি করিনি” তাহলে আমরা সেদিন মারাত্মকভাবে পকড়াও হয়ে যাবো। সেদিন এ নেতৃত্বের অহংকার সেখানে আমাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাড়াবে। আমাদের নেতৃত্বের যুগে আমাদের যথার্থ ত্রুটির কারণে মানুষের চিন্থায় ও কর্মে যে সমস্ত গলদ দেখা দেবে, তার ফলে দুনিয়ায় যেসব গোমরাহী ছড়িয়ে পেড়বে এবং যতো বিপর্যয় ও বিশৃংখলার রাজত্ব বিস্তৃত হবে, সেসবের জন্য অসৎ নেতৃবর্গ এবং মানুষ ও জিন শয়তানদের সাথে সাথে আমরাও পকড়াও হবো। আমাদের জিজ্ঞেস করা হবে পৃথিবীতে যখন যুলুম নির্যাতন, অন্যায়, অত্যাচার, পাপ ও ভ্রষ্টতার রাজত্ব বিস্তৃত হয়েছিল তখন তোমরা কেথায় ছিলে?
গ. “এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম দল তোমাদের কর্মক্ষেত্রে আনা হয়েছে মানুষের হিদায়াত ও সংস্কার সাধনের জন্য। তোমরা নেকীর হুকুম দিয়ে থাকো, দুষ্কৃতি থেকে বিরত রাখো এবং আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনো।” (সূরা আলে ইমরানঃ ১১০)
ইতোপূর্বে সূরা বাকারার ১৭ রুকুতে যে কথা বলা হয়েছেল এখনোও সেই একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের বলা হচ্ছে, নিজেদের অযোগ্যতার কারণে বনী ইসরাঈলকে দুনিয়ার নেতৃত্ব ও পথ প্রদর্শনের যে আমন থেকে বিচ্যুত করা হয়েছে সেখানে এখন তোমাদেরকে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। করণ নৈতিক চরিত্র ও কার্যকলাপের দিক দিয়ে এখন তোমরাই দুনিয়ায় সর্বোত্তম মানব গোষ্ঠী। সৎ ও ন্যায় নিষ্ঠা নেতৃত্বের জন্য যেসব গুণাবলীর প্রয়োজন সেগুলো তোমদের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে গেছে। অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে ন্যায় ও সৎবৃত্তির প্রতিষ্ঠা এবং অন্যায় ও অসৎবৃত্তির মূলোৎপাটন করার মনোভাব ও কর্ম স্পৃহা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর এই সংগে তোমরা এক ও লা শরীক আল্লাহ্কেও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে এবং কাজের দায়িত্ব এখন তোমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমরা নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করো এবং তোমাদের পূর্ববর্তীরা যেসব ভুল করে গেছে তা থেকে নিজেদের দূরে রাখো।
ঘ. “বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরির পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মরিয়মের পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। করণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল, তারা পরস্পরকে খারপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল, তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি ছিলো বড়ই জঘন্য।” (সূরা মায়েদাহঃ ৭৮-৭৯)
প্রত্যেক জাতির বিকৃতি শুরু হয় কয়েক ব্যক্তি থেকে। জাতির সামগ্রিক বিবেক জাগ্রত থাকলে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোকদের দমিয়ে রাখে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জাতি পদি ঐ ব্যক্তিগুলোর ব্যাপারে উপেক্ষা অবহেলা ও উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করে এবং দুষ্কৃতকারীদের তিরস্কার ও নিন্দা করার পরিবর্তে তাদেরকে সমাজে খারপ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়,তাহলে যে বিকৃতি প্রথমে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো তা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈল জাতির বিকৃতি এভাবেই হয়েছে।
ঙ. “এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে।”(সূরা মায়েদাহঃ ৩৫)
এখানে ‘জাহিদু’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। নিছক ‘প্রচেষ্টা ও সাধনা’ শব্দ দুটির মাধ্যম এর অর্থের সবটুকু প্রকাশ হয়না। আর ‘মুজাহাদা’ শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার অর্থ পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে, যেসব শক্তি আল্লাহ্র পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহ্র মর্জি তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহ্র বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয়না এবং নিজের বা আল্লাহ্র ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।
এভাবে এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্থমুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার নির্দেশ দেয়। একদিকে আছে অভিশাপ্ত ইবলীস এবং তার শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফ্স ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ্র বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূত্র বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্যক করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহ্র পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহ্র অনুগত হওয়া এবং ভিতর থেকে বাহির পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহ্র নির্ভেজাল বান্দায় পরিণত হয়ে যাওয়র ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া নির্ভর করে। কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রাম মূখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে আল্লাহ্র পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছানো তার পক্ষ্যে কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।
২. ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি
ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে একটি বিশিষ্ট স্বভাব প্রকৃতি। এ রাষ্ট্র একজন অহবায়ক ও সংস্কারকের ভূমিকা রাখে। এ রাষ্ট্র তার ক্ষমতার সীমার মধ্যে দীনকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচষ্টা চলায়, আর বাকী বিশ্বের সকল জাতির কাছে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দেয়। এ রাষ্ট্রের মর্যাদা হলো একজন প্রচারক, শিক্ষকও সয়স্কারকের মর্যাদা। এর সমস্ত কাজ ভালোবাসা, ভ্রতৃত্ব, পরামর্শদ,সহানুভূতি ও মমতার ভিত্তিতে আঞ্জাম দেয়া হয়, আর এটাই এ রাষ্ট্রের বিশিষ্ট স্বভাব প্রকৃতি।
ক. “যদি আল্লাহ্র ইচ্ছা হতো, তাহলে (তিনি নিজেই এমন ব্যবস্থা করতে পারতেন যাতে) এরা শির্ক করতোনা। তোমাকে এদের উপর পাহারাদার নিযুক্ত করিনি এবং তুমি এদের অভিভাবকও নও। আর (হে ঈমানদারগণ) এরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাকে দোমরা তাদর গালি দিয়োনা। কেননা,এরা শির্ক থেকে আরো খানিকটা অগ্রসর হয়ে অজ্ঞতবশত যেনো আল্লাহ্কে গালি দিয়ে না বসে”। (সূরা আনয়ামঃ ১০৭-১০৮)
এর অর্থ হচ্ছে, তোমাকে অহবায়ক ও প্রচারকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে কোতোয়ালের দায়িত্ব নয়। লোকদের সামনে এ আলোকবর্তিকাটি তুলে ধরা এবং সত্যের কাজ। এখন কেউ এ সত্যটি গ্রহণ না করতে চাইলে না করুক। লোকদেরকে সত্যপন্থী বানিয়েই ছাড়তে হবে, এ দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। তোমার মবূওয়তের প্রভাবধীন এলাকার মধ্যে মিথ্যার অনুসারী কোনো এক ব্যক্তিও থাকতে পারবেনা, একথাটিকে তোমার দায়িত্ব ও জবাবদিহির অন্তুর্ভুক্ত করা হয়নি। কাজেই অন্ধদেরকে কিভাবে চক্ষুমান করা যায় এবং যারা চোখ খুলে দেখতে চায়না তাদেরকে কিভাবে দেখানো যায়? –এ চিন্তায় তুমি খামখা নিজের মন মস্তিষ্ককে পেরেশান করোনা। দুনিয়ায় একজনও বাতিলপন্থী থাকতে না দেয়াটা যদি যথার্থই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হতো তাহলে এ কাজটি তোমাদের মাধ্যমে করাবার আল্লাহ্র কি প্রয়োজন ছিলো? তার একটি মাত্র প্রাকৃতিক ইংগিতই কি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে সত্যপন্থী করার জন্য যথেষ্ট ছিলোনা। কিন্তু সেখানে এটা আদতে উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্তই নয়। সেখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষের জন্য সত্য ও মিথ্যার মধ্য থেকে কোনো একটি বাছাই করে নেবার স্বাধীনতা বজায় রাখা, তারপর সত্যের আলো তার সামনে তুলে ধরে উভয়ের মধ্য থেকে কোনটিকে সে গ্রহণ করে তার পরীক্ষা করা। কাজেই যে আলো তোমাকে দেখানো হয়েছে তার উজ্জ্বল আভায় তুমি নিজে সত্য সরল পথে চলতে থাকো এবং অন্যদেরকে সে পথে চলার জন্য আহবান জানাও। এটিই হচ্ছে তোমার জন্য সঠিক সর্মপদ্ধতি। যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করে তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতোই নগন্য হোক না কেন তাদেরকে বুকে জড়িয়ি ধরো এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে তারা যতোই নগণ্য হোক না কেন তাদেরকে তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন করোনা। আর যারা এ দাওয়াত গ্রহণ করেনি তাদের পেছনে লেগে থেকোনা। তারা যে অশুভ পরিণামের দিকে নিজেরাই চলে যেতে চাল এবং যাবার জন্য অতি মাত্রায় উদগ্রীব, সেদিকে তাদেরকে যেতে দাও।
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদেরকে এ উপদেশ দেয়া হয়েছিল। তাদেরকে বলা হয়েছিল, নিজেদের ইসলাম প্রচারের আবেগে তারা যেনো এমনই লাগামহীন ও বেসামাল হয়ে না পড়ে যার ফলে তর্ক বিতর্ক ও বিরোধের ব্যপারে এগিয়ে যেতে যেতে তারা অমুসলিমদের আকীদা বিশ্বাসের কঠোর সমালোচনা করতে গিয়ে তাদের নেতৃবৃন্দ ও উপাস্যদেরকে গালিগালাজ করে না বসে। কারণ, এগুলো তাদেরকে সত্যের নিকটবর্তী করার পরিবর্তে তা থেকে আরো দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে।
খ. “(হে নবী) এটা আল্লাহ্র বড়ই অনুগ্রহ যে, তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়ই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চারপাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদের অন্তর্ভুক্ত করো। তারপর যখন কোনো মতের ভিত্তিতি তোমরা স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা করো। আল্লাহ্ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর উপর ভরসা করে কাজ করে।” (সূরা আলে ইমরানঃ ১৫৯)
গ. “আর উত্তম পদ্ধতিতে ছাড়া আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করোনা। তবে তাদের মধ্যে যারা যালিম।”(সূরা আনকাবূতঃ ৪৬)
অর্থাৎ বিতর্ক ও আলাপ আলোচনা উপযুক্ত যুক্তি প্রমাণ সহকারে, ভদ্র ও শালীন ভাষায় বুঝবার ও বুঝাবার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে করতে হবে। এর ফলে যার সাথে আলোচনা হয় তার চিন্তার সংশোধন হবে। প্রচারকের চিন্তা করা উচিত, তিনি শ্রোতার হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করে সত্য কথা তার মধ্যে বসিয়ে দেবেন এবং তাকে সঠিক পথে আনবেন। একজন পাহ্লোয়ানের মতো তার সাথে লড়াই করা উচিত নয়, যার উদ্দেশ্যই হয় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দেয়া। বরং একজন ডাক্তারের মতো তাকে সবসময় উদ্বিগ্ন থাকতে হবে, যিনি তার রোগীর চিকিৎসা করার সময় একথাকে গুরুত্ব দেন যে, তাঁর নিজের কোনো ভুলের দরুন রোগীর রোগ যেনো আরো বেশী বেড়ে না যায় এবং সর্বধিক কম কষ্ট সহ্য করে যাতে তাঁর রোগীর নিরাময় হওয়া সম্ভব হয় এজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক আলোচনা করার ব্যাপারে এ নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু এটা কেবলমাত্র বিশেষভাবে আহ্লি কিতাবদের জন্য নয় বরং দীনের প্রচারের ক্ষেত্রে এটি একটি সাধারণ নির্দেশ। কুরআন মজীদের বিভিন্ন এর উল্লেখ রয়েছে। যেমনঃ “আহবান করো নিজের রবের পথের দিকে প্রজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট উপদেশের মাধ্যমে এবং লোকদের সাথে উত্তম পদ্ধতিতে বিতর্ক আলোচনা করো।” (সূরা আননাহলঃ ১২৫)
“সুকৃতি ও দুষ্কৃতি সমান নয়। (বিরোধীদের আক্রমণ) প্রতিরোধ করো উৎকৃষ্ট পদ্ধতিতে। তুমি দেখবে এমন এক ব্যক্তি যার সাথে তোমার শত্রুতা ছিলো সে এমন হয়ে গেছে যেমন তোমার অন্তরংগ বন্ধু।” (সূরা হা-মীম আস্সাজদাহঃ ৩৪)
“তুমি উত্তম পদ্ধতিতে দুষ্কৃতি নির্মূল করো। আমি জানি (তোমার বিরুদ্ধে)তারা যেসব কিছু তৈরী করে।”(সূরা আল মু‘মিনূনঃ ৯৬)
“ক্ষমার পথ অবলম্বন করো, ভালো কাজ করার নির্দেশ দও এবং মূর্খদের এড়িয়ে চলো। আর যদি (মুখে মুখে জবাব দেবার জন্য) শয়তান তোমাকে উস্কানী দেয় তাহলে আল্লাহ্র আশ্রয় চাও।” সূরা আল আ’রাফঃ ১৯৯-২০০)
অর্থাৎ যারা যুলুমের নীতি অবলম্বন করে তাদের সাথে তাদের যুলুমের প্রকৃতি বিবেচনা করে ভিন্ন নীতিও অবলম্বন করা যেতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, সবসময় সব অবস্থায় সব ধরনের লোকদের মুকাবিলায় নরম ও সুমিষ্ট স্বভাবের হয়ে থাকলে চলবেনা। যেনো মানুষ সত্যের আহবানের ভদ্রতাকে দুর্বলতা ও অসহায়তা মনে না করে বসে। ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অবশ্যই ভদ্রতা, বিনয়, শালীনতা ও যুক্তিবাদীতার শিক্ষা দেয়, কিন্তু হীনতা ও দীনতার শিক্ষা দেয়না। তাদেরকে প্রত্যেক যালিমের যুলুমের সহজ শিকারে পরিণত হবার শিক্ষা দেয়না।
ঘ. “প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করে এবং তার অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়।” (সূরা কাসাসঃ ৪)
অর্থাৎ তার রাজ্য শাসনের নীতি অনুযায়ী আইনের চোখে দেশের সকল অধিবাসী সমান থাকেনি এবং সবাইকে সমান অধিকার দেয়াও হয়নি। বরং সে সভ্যতা সংস্কৃতি ও রাজনীতির এমন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যার মাধ্যমে রাজ্যের অধিবাসীদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয়া হয়। একদলকে সুযোগ সুবিধা ও বিশেষ অধিকার দিয়ে শাসক দলে পরিণত করা হয় এবং অন্যদলকে অধীনে করে পদানত, পর্যুদস্ত, নিষ্পেষিত ও ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা হয়।
এখনে কারো এ ধরনের সন্দেহ করার অবকাশ নেই যে, ইসলামী রাষ্ট্রেও তো মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে ফারাক করা হয় এবং তাদের অধিকার ও ক্ষমতাও সকল দিক দিয়ে সমান রাখা হয়নি। এ সন্দেহ এজন্য সঠিক নয় যে, ফেরাউনী বিধানে যেমন বংশ, বর্ণ, ভাষা বা শ্রেণীগত বিভেদের ওপর বৈষম্যের ভিত রাখা হয়েছে ইসলামী বিধানে ঠিক তেমনটি নয়। বরং ইসলামী বিধানে নীতি ও মতবাদের ওপর এর ভিত রাখা হয়েছ। ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অমুসলিম ও মুসলমানের মধ্যে আইনগত অধিকারের ক্ষেত্র মোটেই কোনো ফারাক নেই। সকল পার্থক্য একমাত্র রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে। আর এ পার্থক্যের কারণ এছাড়া আর কিছুই নয় যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্রে শাসকদল একমাত্র তারাই হতে পারে যারা হবে রাষ্ট্রের মূলনীতির সমর্থক। এদলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি শামিল হতে পারে যে এ মূলনীতি মেনে নেবেনা। এপার্থক্য ও ফেরাউনী ধরনের পার্থক্যের কোনো মিল নেই। কারণ, ফেরাউনী পার্থক্যের ভিত্তিতে পরাধীন প্রজন্মের কোনো ব্যক্তি কখনো শাসক দলে শামিল হতে পারেনা। যেখানে পরাধীন প্রজন্মের লোকেরা রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার তো দূরের কথা মৌলিক মানবিক অধিকারও লাভ করেনা। এমন কি জীবিত থাকার অধিকারও তাদের থেকে ছিনিয়ে নিয়া হয়। সেখানে কখনো পরাধীনদের জন্য কোনো অধিকারের জামানত দেয়া হয়না। সব ধরনের স্বার্থ, মুনাফা, সুযোগ সুবিধাও মর্যাদা একমাত্র শাসক সমাজের জন্য নির্দিষ্ট থাকে এবং এ বিশেষ অধিকার একমাত্র শাসক জাতির মধ্যে জন্মলাভকারী ব্যক্তিই লাভ করে।
ঙ. “হে মানব জাতি! তোমাদের রবকে ভয় করো। তিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। তারপর তাদের দু’জনার থেকে সারা দুনিয়ায় ছিড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী।”(সূরা নিসাঃ১)
যেহেতু সামনের দিকের আয়াতগুলোতে মানুষের পারস্পারিক অধিকারের কথা আলোচনা করা হবে, বিশেষ করে পারবারিক ব্যবস্থাপনাকে উন্নত সুগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন কানুন বর্ণনা করা হবে, তাই এভাবে ভুমিকা ফাঁদা হয়েছে, একদিকে আল্লাহ্কে ভয় করার ও তাঁর অসন্তোষ থেকে আত্মরক্ষার জন্য জোর তাকীদ করা হয়েছে এবং অন্যদিকে একথা মনের মধ্যে গেঁথে দেয়া হয়েছে যে, একজন মানুষ থেকে সমস্ত মানুষের উৎপত্তি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ।
“তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।” অর্থাৎ প্রথমে এক ব্যক্তি থেকে মানব জাতির সৃষ্টি করেন। অন্যত্র কুরআন নিজেই এর ব্যাখ্যা করে বলেছে যে, সেই প্রথম ব্যাক্ত ছিলেন হযরত আদম আলাইহিস সালাম। তাঁর থেকেই এ দুনিয়ায় মানব বংশ বিস্তার লাভ করে।
“সেই একই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া।” এ বিষয়টির বিস্তরিত জ্ঞান আমাদের কাছে নেই। সাধারণ ভাবে কুরআনের তাফসীরকারগণ যা বর্ণনা করেন এবং বাইবেলে যা বিবৃত হয়েছে তা হচ্ছে নিন্মরুপ, আদমের পাঁজর থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তালমুদে আর একটু বিস্তারিত ভাবে বলা হয়েছে, ডান দিকের ত্রয়োদশ হাড় থেকে সষ্টি হয়েছে। কিন্তু কুরআন মজীদ এ ব্যাপারে নীরব। আর এর সপক্ষে যে হাদীসটি পেশ করা হয় তার অর্থ লোকেরা যা মনে করে নিয়েছে তা নয়। কাজেই কথাটিকে আল্লাহ যেভাবে সংক্ষিপ্ত ও অস্পস্ট রেখেছেন তেমনি রেখে এর বিস্তারিত অবস্থা জানার জন্য সময় নষ্ট না করাই ভালো।
চ. “ দীনের ব্যাপারে কোনো জোর জবরদস্তি নেই।” (সূরা আল বাকারাঃ ২৫৬)
এখানে দীন বলতে পূর্ববর্তী আয়াত আয়াতুল কুরসীতে বর্ণিত আল্লাহ্ সম্পর্কিত আকীদা ও সেই আকীদার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠেত জীবন ব্যবস্থা বুঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, “ইসলাম” এর এই আকীদাগত এবং নৈতিক ও কর্মগত ব্যবস্থা কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া যেতে পারেনা। যেমন কাউকে ধরে তার মাথায় জোর করে একটা বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়, এটা তেমন নয়।
উপরে উল্লোখিত আয়াত ও সেগুলোর ব্যাখ্যা থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের বিশেষ ধরনের স্বভব প্রকৃতি পরিস্ফুট হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র এ প্রকৃতির অনন্য রাষ্ট্র, যে তার সর্বোচ্চ ক্ষমতাকেও দয়া, মমতা ও বন্ধুতার সাথে প্রয়োগ করে। বল প্রয়োগ এর প্রকৃতিতে নেই। কঠোরতার সাথে এর সম্পর্ক নেই। এটা হলো সেই রাষ্ট্র, যা মানবতার জন্য রহমত হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাসর্শের ভিত্তিতে কাজ করাও এর বিশিষ্ট প্রকৃতিরই এক অনিবার্য দাবি।
৩. পরামর্শ বা শূরা
আল্লাহ্ তায়ালার ঘোষণাঃ
“এবং তারা নিজেদের সব কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে চালায়।”(সূরা শূরাঃ৩৮)
এ বিষয়টিকে এখানে ঈমানদারদের সর্বোত্তম গুণাবলীর মধ্যে গণ্য করা হয়েছে এবং সূরা আল ইমরানে (আয়াত ১৫৯) এর জন্য আদেশ করা হয়েছে। এ কারণে পরামর্শ ইসলামী জীবন প্রণালীর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। পরামর্শ ছাড়া সামষ্টেক কাজ পরিচালনা করা শুধু জাহেলী পন্থাই নয়, আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধানের সুস্পষ্ট লংঘন। ইসলামে পরামর্শকে এই গুরুত্ব কেন দেয়া হয়েছে? এর কারণসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলে আমাদের সামনে তিনটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায়ঃ
এক. যে বিষয়টি দুই বা আরো বিশী লোকের স্বার্থের সাথে জড়িত সে ক্ষেত্রে কোনো এক ব্যক্তির নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিদের উপেক্ষা করা যুলুম। যৌথ ব্যাপারে কারো যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার নেই। ইনসাফের দাবী হচ্ছে,কোনো বিষয়ে যতো লোকের স্বার্থ জড়িত সে ব্যাপারে তাদের সবার মতামত গ্রহণ করতে হবে এবং তাতে যদি বিপুল সংখ্যক লোকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তাদের আস্থাভাজন প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শের মধ্যে শামিল করতে হবে।
দুই. যৌথ ব্যাপারে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করার চেষ্ট করে অন্যদের অধিকার নস্যাত করে নিজের ব্যক্তি স্বার্থ লাভ করার জন্য, অথবা এর কারণ হয় সে নিজেকে বড় একটা কিছু এবং অন্যদের নগণ্য মনে করে। নৈতিক বিচারে এই দুটি জিনিসই সমপর্যায়ের হীন। মু’মিনের মধ্যে এ দুটির কোনেটিই পাওয়া যেতে পারেনা। মু’মিন কখনো স্বার্থপর হয়না। তাই সে অন্যদের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করে নিজে অন্যায় ফায়দা চাইতে পারেনা এবং অহংকারী বা অত্মপ্রশংসিতও হতে পরেনা যে নিজেকেই শুধু মহাজ্ঞানী ও সবজান্তা মনে করবে।
তিন, যেসব বিষয় অন্যদের অধিকর ও স্বার্থের সাথে জড়িত সেসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি বড় দায়িত্ব। যে ব্যক্তি আল্লহ্কে ভয় করে এবং একথা জানে যে এর জন্য তাকে তার প্রভর কাছে কতো কঠিন জবাবদিহি করতে হবে সে কখনো একা এই শুরুভার নিজের কাঁধে উঠিয়ে নেবার দুঃসাহস করতে পারেনা। এ ধরনের দুঃসাহস কেবল তারাই করে যারা আল্লাহ্র ব্যাপারে নির্ভিক এবং আখিরাত সম্পর্কে চিন্তাহীন। খোদাভীরু ও আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতি সম্পন্ন লোক কোনো যৌথ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত কিংবা তাদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই শরীফ করার চেষ্টা করবে যাতে সর্বাধিক মাত্রায় সঠিক, নিরপেক্ষ এবং ইনসাফ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। এ ক্ষেত্রে যদি অজ্ঞাতসারে কোনো ত্রুটি হয়েও যায় তাহলে কোনো এক ব্যক্তির ঘাড়ে তার দায়দায়িত্ব এসে পড়বেনা।
এতিনটি কারণ এমন, যদি তা নিয়ে কেউ গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে তাহলে অতি সহজেই সে একথা উপলব্ধি করতে পারবে যে, ইসলাম যে নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয় পরামর্শ তার অনিবার্য দাবী এবং তা এড়িয়ে চলা একটি অতি বড় চরিত্রহীনতার কাজ। ইসলাম কখনো এ ধরনের কাজের অনুমতি দিতে পারেনা। ইসলামী জীরন পদ্ধতি সমাজের ছোট বড় প্রতিটি ব্যাপারেই পরামর্শের নীতি কার্যকরী হোক তা চায়। পারিবারিক ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রী পরামর্শ করে কাজ করবে এবং ছেলেমেয়ে বড় হলে তাদেরকেও পরামর্শে শরীফ করতে হবে। খান্দান বা গোষ্ঠীর ব্যাপার হলে সে ক্ষেত্রে গোষ্ঠীর সমস্ত বুদ্ধিমান ও বয়প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। যদি একটি গোত্র বা জাতিগেষ্ঠী কিংবা জনপদের বিষয়াদি হয় এবং তাতে সব মানুষের অংশগ্রহণ সম্ভব না হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত বা সভা পালন করবে যেখানে কোনো সর্বসম্মত পন্থা অনুসারে সংশিষ্ট আস্থাভাজন প্রতিনিধিরা শরীফ হবে। গোটা জাতির ব্যাপার হলে তা পরিচালনার জন্য সবার ইচ্ছানুসারে তাদের নেতা নিযুক্ত হবে জাতীয় বিষয়গুলোকে সে এমন সব ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ অনুসারে পরিচালনা করবে জাতি যাদেরকে নির্ভরযোগ্য মনে করে এবং সে ততক্ষণ পর্যন্ত নেতা থাকবে যতক্ষণ জাতি তাকে নেতা বানিয়ে রাখতে চাইবে। কোনো ঈমানদার ব্যক্তি জোরপূর্বক জতির নেতা হওয়ার বা হয়ে থাকার আকাংখ্যা কিংবা চেষ্টা করতে পারেনা। প্রথম জোরপূর্বক জাতির ঘাড়ে চেপে বসা এবং পরে জবরদস্তি করে মানুষের সম্মতি আদায় করা, এমন প্রতারণাও সে করতে পারেনা। তাকে পরামর্শ দানের জন্য মানুষ স্বাধীর ইচ্ছানুসারে নিজেদের মনোনীত প্রতিনিধি নয় বরং এমন প্রতিনিধিকে নির্বাচিত করবে। যে তার মর্জি মুতাবিক মতামত প্রকাশ করবে, এমন চক্রান্তও সে করতে পারেনা। এমন আকাংখা কেবল সে মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি হতে পারে যার মন অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা কলুষিত। এই আকাংখার সাথে এর বাহ্যিক কাঠামো নির্মাণ এবং তার বাস্তব প্রণসত্তাকে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচষ্টা শুধু সে ব্যক্তিই চালাতে পারে যে আল্লাহ্ এবং তাঁর সৃষ্টিকে ধোঁকা দিতে ভয় করেনা। অথচ না আল্লাহ্কে ধোকা দেয়া সম্ভব না আল্লাহ্র সৃষ্টি মানুষ এমন অন্ধ হতে পারে যে, প্রকাশ্য দিবালোকে কেউ ডাকাতি করছে আর মানুষ তা দেখে সরল মনে ভারতে থাকবে যে, সে ডাকাত নয়, মানুষের সেবা করছে।
এর নিয়মটি প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পাঁচটি জিনিস দাবী করেঃ
এক. যৌথ বিষয়সমুহ যাদের অধিকার ও স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত তাদের মত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধিনতা থাকতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে ব্যাপারহুলো কিভাবে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়ে তাদের অবহিত রাখতে হবে। তারা যদি তাদের ব্যাপারগুলো নেতৃত্বে কোনো ত্রুটি, অপবিপক্কতা বা দুর্বলতা দেখে তহলে তা তুলে ধরার ও তার প্রতিবাদ করার এবং সংশোধিত হতে না দেখলে পরিচালক ও ব্যবস্থাপকদের পরিবর্তন করার অধিকার থাকতে হবে। মানুষের মুখ বন্ধ করে, হাত পা বেঁধে এবং তাদেরকে অনবহিত রেখে তাদের সামষ্টিক ব্যাপারসমূহ পরিচালনা করা সুস্পষ্ট প্রবঞ্চনা। কেউই এ কাজকে নীতির অনুসরণ মানতে পারেনা।
দুই. যৌথ বিষয়সমুহ পরিচালনার দায়িত্ব যাকেই দেয়া হবে তাকে যেনো এ দায়িত্ব সবার স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে দান করা হয়। জবরদস্তি ও ভয়ভীতি দ্বারা অর্জিত কিংবা লোভ লালসা দিয়ে খরিদকৃত অথবা ধোঁকা প্রতারণা ও চক্রান্তের মাধ্যমে লুন্ঠিত সম্মতি প্রকৃতপক্ষে কোনো সম্মতি নয়। যে সম্ভাব্য সব রকম পন্থা কাজে লাগিয়ে কোনো জাতির নেতা হয় সে সত্যিকার নেতা নয়। সত্যিকার নেতা সেই যাকে মানুষ নিজেদের পছন্দানুসারে সনন্দ চিত্তে নেতা হিসেবে গ্রহণ করে।
তিন. নেতাকে পরামর্শ দানের জন্যও এমন সব লোক নিয়োগ করতে হবে যাদের প্রতি জতির আস্থা আছে। এটা সর্বজনতিদিত যে, যারা চাপ সৃষ্টি করে কিংবা অর্থ দ্বারা খরিদ করে অথবা মিথ্যা ও চক্রান্তর সাহায্যে বা মানুষকে বিভ্রান্ত করে প্রতিনিধিত্বের স্থানটি দখল করে তাদেরকে সঠিক অর্থে আস্থাভাজন বলা যায়না।
চার. পরামর্শদাতাগণ নিজেদের জ্ঞান, ঈমান ও বিবেক অনুসারে পরামর্শ দান করবে এবং এভাবে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তাদের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে। এ দিকগুলো যেখানে থাকবেনা, যেখানে পরামর্শদাতা কোনো প্রকার লোভ লালসা বা ভীতির কারণে অথবা কোনো দলাদলির মারপ্যাঁচের কারণে নিজের জ্ঞান ও বিবেকের বিরুদ্ধে মতামত পেশ করে সেখানে প্রকৃতপক্ষে হবে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা এর অনুসরণ নয়।
পাঁচ. পরাসর্শদাতাদের ‘ইজমা’র (সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত) ভিত্তিতে যে পরামর্শ দেয়া হবে, অথবা যে সিদ্ধান্ত তাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করবে তা মেনে নিতে হবে। কেননা সবার মতামত জানার পরও যদি এক ব্যাক্তি অথবা একটি ছোট্র গ্রুপকে স্বেচ্ছাচার চালানোর সুযোগ দেয়া হয় তাহলে পরামর্শ অর্থহীন হয়ে যায়। আল্লাহ্ একথা বলছেননা যে, “তাদরে ব্যাপার তাদের পরামর্শ গ্রহণ করা হয়” বরং বলছেন, “তাদের কাজকর্ম পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে চলে।” শুধু পরামর্শ করলেই এ নির্দেশ পালন করা হয়না। তাই পরামর্শের ক্ষেত্রে সর্বসম্মত অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজকর্ম পরিচালনা প্রয়োজন।
ইসলামের পরামর্শ ভিত্তিক কাজ পরিচালনা নীতির এই ব্যাখ্যার সাথে সাথে এই মৌলিক কথাটির প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মুসলমানদের পারস্পরিক বিষয়সমূহ পরিচালনায় এই শূরা স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নয়, বরং অবশ্যই সেই দীনের বিধি বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ আল্লাহ্ নিজেই যার জন্য বিধান রচনা করেছেন। সাথে সাথে তা সেই মূল নীতিরও আনুগত্য করতে বাধ্য, যাতে বলা হয়েছে “যে ব্যাপারেই তোমাদের মধ্যে মতভেদ হবে তার ফয়সালা করবেন আল্লাহ্।” এবং “তোমাদের মধ্যে যে বিরোধই বাঁধুক না কেনো সে জন্য আল্লাহ্ তাঁর রসূলের দিকে ফিরে যাও। “ এই সাধারণ সূত্র অনুসারে মুসলমানরা শর’য়ী বিষয়ে মূল গ্রন্থের কোন্ অংশের কি অর্থ এবং কিভাবে তা কার্যকর করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ করতে পারে যাতে তার মূল ইদ্দেশ্য পূরণ হয়। কিন্তু যে ব্যাপারে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সে ব্যাপারে তার নিজেরা স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এ উদ্দেশ্যে কোনো পরামর্শ করতে পারেনা।
৪. আদল ও ইহসান
“আল্লাহ্ আদল, ইহসান ও আত্মীয় স্বজনকে দান করার হুকুম দেন এবং অশ্লীলতা নির্লজ্জতা ও দুষ্কৃতি এবং অত্যাচার বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করেন।” (সূরা আননহলঃ ৯০)
এ ছোট্র বাক্যটিতে এমন তিনটি জিনিসের হুকুম দেয়া হয়েছে যেগুলোর ওপর সমগ্র মানব সমাজের সঠিক অবকাঠামোতে ও যথার্থ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকা নির্ভরশীল।
প্রথম জিনিসটি হচ্ছে আদল। দু’টি স্থায়ী সত্যের সমন্বয়ে এর ধারণাটি গঠিত। এক. লোকদের মধ্যে অধিকারের ক্ষেত্রে ভারসাম্য ও সষমতা থাকতে হবে। দুই. প্রত্যেককে নির্দ্বিধায় তার অধিকার দিতে হবে। আমাদের ভাষায় এ অর্থ প্রকাশ করার জন্য “ইনসাফ” শদ্ব ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু এ শদ্বটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এ থেকে অনর্থক এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, দু’ ব্যক্তির মধ্যে “নিস্ফ” “নিস্ফ” বা আধাআধির ভিত্তিতে অধিকার বন্টিত হতে হবে। তারপর এ থেকেই আদল ও ইনসাফের অর্থ মনে করা হয়েছে সাম্য ও সমান সমান ভিত্তিতে অধিকার বন্টন। এটি সম্পূর্ণ প্রকৃতি বিরোধী। আসলে “আদল” সমতা বা সাম্য নয়, বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় দাবী করে। কোনো কোনো দিক দিয়ে “আদল” অবশ্যই সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাম্য চায়। যেমন নাগরিক অধিকারের ক্ষেত্রে। কিন্তু আবার কোনো কোনো দিক দিয়ে সাম্য সম্পূর্ণ “আদল” বিরোধি। যেমন পিতা মাতা ও সন্তানদের মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সাম্য এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মজীবী ও নিন্ম পর্যায়েল কর্মজীবীদের মধ্যে বেতনের সাম্য। কজেই আল্লাহ্ যে জিনিসের হুকুম দিয়েছেন তা অধিকারের মধ্যে সাম্য নয় বরং ভারসাম্য ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা। এ হুকুমের দাবী হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে প্রদান করতে হবে।
দ্বিতীয় জিনিসটি হচ্ছে ইহ্সান। এর অর্থ হলো, পরোপকার তথা সদাচার, ঔদার্যপূর্ণ ব্যবহার, সহানুভূতিশীল আচরণ,সহিষ্ণুতা, ক্ষমাশীরতা, পারস্পরিক সুযোগ সাবিধা দান, একজন অপর জনের মর্যাদা রক্ষা করা, অন্যকে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশী দেয়া এবং নিজের অধিকার আদায়ের বেলায় কিছু কমে রাযী হয়ে যাওয়া। এহচ্ছে আদলের অতিরিক্ত এমন একটি জিনিস যার গুরুত্ব সামষ্টিক জীবনে আদলের চাইতেও বেশী। আদল যদি হয় সমাজের বুনিয়াদ তাহলে ইহ্সান হচ্ছে তার সৌন্দর্য ও পূর্ণতা। আদল যদি সমাজকে কটুতা ও তিক্ততা থেকে বাঁচায় তাহলে ইহ্সান তার মধ্যে সমাবেশ ঘটায় মিষ্ট মধুর স্বাদের। কোনো সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বক্ষণ তার অধিকার কড়ায় গন্ডায় মেপে মেপে আদায় করতে থাকবে এবং তারপর ঐ নির্দিষ্ট পরমাণ অধিকর আদায় করে নিয়েই তবে ক্ষান্ত হবে, আবার অন্যদিকে অন্যদের অধিকারের পরিমাণ কি তা জেনে নিয়ে কেবলমাত্র যতোটুকু প্রাপ্য ততোটুকুই আদায় করে দেবে, এরূপ কট্রর নীতির ভিত্তিতে আসলে কোনো সমাজ টিকে থাকতে পারেনা। এমনি ধরনের একটি শীতল ও কাঠখোট্টা সমাজে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত থাকবেনা ঠিকই কিন্তু ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা, ঔদার্য, ত্যাগ, আন্তরিকতা, মহানুভাবতা ও মঙ্গলাকাংখার মতো জীবনের উন্নত মূল্যবোধগুলোর সৌন্দর্য সুষমা থেকে সে বঞ্চিত থেকে যাবে। আর এগুলোই মূলত এমন সব মূল্যবোধ যা জীবনে সুন্দর আবহ ও মধুর আমেজ সৃষ্টি করে এবং সামষ্টিক মানবীয় গুণাবলীকে বিকশিত করে।
তৃতীয় যে জিনিসটির এ আয়াতে হুকুম দেয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে আত্মীয় স্বজনকে দান করা এবং তাদের সাথে সদাচার করা। এটি আত্মীয় স্বজনদের সাথে ইহ্সান করার একটি বিশেষ ধরন নির্ধারণ করে। এর অর্থ শুধু এই নয় যে, মানুষ নিজের আত্মীয়দের সাথে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হবে। বরং এও এর অর্থের অন্তরভুক্ত যে, প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের ধন সম্পদের ওপর শুধুমাত্র নিজের ও নিজের সন্তান সন্ততির অধিকার আছে বলে মনে করবেনা বরং একই সংগে নিজের আত্মীয় স্বজনদের অধিকারও স্বীকার করবে। আল্লাহ্র শরীয়ত প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবের্গের ওপর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছে যে, তাদের পরিবারের অভাবী লোকেরা যেনো অভুক্ত ও বস্ত্রহীন না থাকে। তার দৃষ্টিতে কোনো সমাজের এর চেয়ে বড় দুর্গতি আর হতেই পারেনা যে, তার মধ্যে বসবাসকারী এক ব্যক্তি প্রাচুর্যর মধ্যে অবস্থান করে বিলাসী জীবন যাপন করবে এবং তারই পরিবারের সদস্য তার নিজের জ্ঞাতি ভাইয়েরা ভাত কাপড়ের অভাবে মানবতার জীবন যাপন করতে থাকবে। ইসলাম পরিবারবে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান গণ্য করে এবং এ ক্ষেত্রে এ মূলনীতি পেশ করে যে, প্রত্যেক পরিবারের গরীব ব্যক্তিবর্গের প্রথম অধিকার বর্তায় তাদের পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর, তারপর অন্যদের ওপর তাদের অধিকার আরোপিত হয়। আর প্রত্যেক পরিবারের সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের ওপর অধিকার আরোপিত হয় তাদের গরীব আত্মীয় স্বজনদের, তারপর অন্যদের অধিকার তাদের ওপর আরোপিত হয়। এ কথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিভিন্ন বক্তব্যে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাই বিভিন্ন হাদীসে পরষ্কার বলে দেয়া হয়েছে, মানুষের ওপর সর্বপ্রথন অধিকার তার পিতামাতার, তারপর স্ত্রী সন্তানদের, তারপর ভাই বোনদের, তারপর যার তাদের পরে নিকটতর এবং তারপর যারা তাদের পরে নিকটতর। এ নীতির ভিত্তিতেই হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একটি ইয়াতীম শিশুর চাচাত ভাইদেরকে তার লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিলেন। তিনি অন্য একজন ইয়াতীমের পক্ষে ফয়সালা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, যদি এর কোনো দূরতম আত্মীয়ও থাকতো তাহলে আমি তার ওপর এর লালন পালনের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিতাম। অনুমান করা যেতে পারে, যে সমাজের প্রতিটি পরিবার ও ব্যক্তি (Unit) এ ভাবে নিজেদের ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব নিজেরাই নিয়ে নেয় সেখানে কতোখানি অর্থনৈতিক সচ্ছলতা, কেমন ধরনের সামাজিক মাধুর্য এবং কেমনতর নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্র, পরিচ্ছন্ন ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে।
ওপরে তিনটি সৎ কাজের মুকাবিলায় আল্লাহ্ তিনটি অসৎ কাজ করতে নিষেধ করেন। এ অসৎকাজগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সমাষ্টিক পর্যায়ে সমগ্র সমাজ পরিবেশকে খারাপ করে দেয়। প্রথম জিনিসটি হচ্ছে অশ্লীলতা নির্লজ্জতা। সব রকমের অশালীন, কদর্য ও নির্লজ্জ কাজ এর অন্তরভূক্ত। এমন প্রত্যেকটি খারাপ কাজ যা স্বভাবতই কুৎসিত, নোংরা, ঘৃণ্য ও লজ্জাকর। তাকেই বলা হয় অশ্লীলতা। যেমন কৃপণতা, ব্যাভিচার, উলংগতা, সমকামিতা, মাহরাম আত্মীয়কে বিয়ে করা, চুরি, শরাব পান, ভিক্ষাবৃত্তি, গালাগালি করা, কটু কথা বলা ইত্যাদি। এভাবে সর্ব সমক্ষে বেহায়পানা ও খারাপ কাজ করা এবং খারাপ কাজকে ছড়িয়ে দেয়াও অশ্লীলতা নির্লজ্জতার অন্তরভুক্ত। যেমন মিথ্যা প্রচারণা, মিথ্যা দোষারোপ, গোগন অগরাধ জনসমক্ষে বলে বেড়ানো, অসৎকাজের প্ররোচক গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্র, উলংগ চিত্র, মেয়েদের সাজগোজ করে জনসমক্ষে আসা, নারী পুরুষ প্রকাশ্যে মেলামেশা এবং মঞ্চে মেয়েদের নাচগান করা ও তাদর শারীরিক অংগভংগির প্রদর্শনী করা ইত্যাদি।
দ্বিতীয়টি হচ্ছে দুষ্কৃতি। এর অর্থ হচ্ছে এমন সব অসৎ কাজ যেগুলোকে মানুষ সাধারণভাবে খারাপ মনে করে থাকে, চিরকাল বলে আসছে এবং আল্লাহ্র সকল শরীয়ত যে কাজ করতে নিষেধ করেছে।
তৃতীয় জিনিসটি যুলুম বাড়াবাড়ি। এর মানে হচ্ছে, নিজের সীমা অতিক্রম করা এবং অন্যের অধিকার তা আল্লাহ্র হোক বা বান্দার লংঘন করা ও তার ওপর হস্তক্ষেপ করা।
৫. নেতৃত্ব নির্বাচনের মূলনীতি
ইমলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্ব নির্বাচনের নীতিও অন্যান্য রাষ্ট্রের চেয়ে ভিন্নতর। এখনে বিবেচ্য বিষয় হলো যোগ্যতা, বেশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, আল্লাহ্ভীতি ও উত্তম আচরণঃ
ক.“হে মুসলিমগণ! আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারদের হাতে ফেরত দেবার নির্দেশ দেচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় ‘আদল’ ও ন্যায়নীতি সহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ্ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যি আল্লাহ্ সবকিছু শোনেন ও দেখেন।”(সূরা আন-নিসাঃ ৫৮০)
অর্থাৎ বনী ইসরাঈলরা যেসব খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে গেছে তোমরা সেগুলো থেকে দূরে থেকো। বনী ইসরাঈলদের একটি মৌলিক দোষ ছিলো এই যে, তারা নিজেদের পতনের যুগে আমানতসমূহ অর্থাৎ দায়িত্বপূর্ণ পদ, ধর্মীয় নেতৃত্ব ও জাতীয় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ পদসমূহ (Posutions of trust) এমন সব লোকদের দেয়া শুরু করেছিল যারা ছিলো অযোগ্য, সংকীর্ণমনা, দুশ্চরিত্র, দুর্নীতিপরায়ণ, খিয়ানতকারী ও ব্যভিচারী। ফলে অসৎ লোকদের নেতৃত্বে সমগ্র জাতি অনাচারে লিপ্ত হয়ে গেছে। মুসলমানদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে, তোমরা এই বনী ইসরাঈলদের মতো আচরণ করোনা। বরং তোমরা যোগ্য লোকদেরকে আমানত সোপর্দ করো। অর্থাৎ আমানতের বোঝা বহন করার ক্ষমতা যাদের আছে কেবল তাদের হাতে আমানত তুলে দিয়ো। বনী ইসরাঈলদের দ্বিতীয় বড় দুর্বলতা এই ছিলো যে, তাদের মধ্যে সুবিচার ও ন্যায়নীতির প্রাণশক্তি বিলু্প্ত হয়ে গিয়েছিল। ব্যক্তিগত ও জাতীয় স্বার্থে তারা নির্দ্বিধায় ঈমান বিরোধী কাজ করে চলতো। সত্যকে জেনেও সুস্পষ্ট হঠধর্মীতায় লিপ্ত হতো। ইনসাফের গলায় ছুরি চালাতে কখনো একটুও কুষ্ঠাবোধ করতোনা। সে যুগের মুসলমানরা তাদের বেইনসাফীর তিক্ত অভিজ্ঞতা হতে কলমে লাভ করে চলছিল। একদিকে তাদের সামনে ছিলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর ওপর যারা ঈমান এনেছিল তাদের পুতপবিত্র জীবনধারা। অন্যদিকে ছিলো এমন এক জনগোষ্ঠীর জীবন যারা মূর্তিপূজা করে চলছিল। তারা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দিতো। বিমাতাদেরকেও বিয়ে করতো। উলংগ অবস্থায় কাবাঘরের চারদিকে তাওয়াফ করতো। এই তথাকথিত আহলি কতিাবরা এদের মধ্য থেকে প্রথম দলটির ওপর দ্বিতীয় দলটিকে প্রাধান্য দিতো। তারা একথা বলতে একটুও লজ্জা অনুভব করতোনা যে, প্রথম দলটির তুলনায় দ্বিতীয় দলটি অধিকতর সঠিক পথে চলছে। মহান আল্লাহ্ তাদের এই বেইনসাফির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করার পর এবার মুসলমানদের উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা ওদের মতো অবিচারক হয়োনা। কারো সাথে বন্ধুতা বা শত্রুতা যাই হোক না কেন সব অবস্থায় ইনসাফ ও ন্যায়নীতির কথা বলবে এবং ইনসাফ ও সুবিচার সহকারে ফয়সালা করবে।
খ.“যেসব লাগামহীন লোক পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে এবং কোনো সংস্কার সাধন করেনা তাদের আনুগত্য করোনা।” (সূরা শুয়ারাঃ ১৫১-১৫২)
অর্থৎ তোমাদের যেসব রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দ এবং শাসকদের নেতৃত্বে এ ভ্রান্ত বিকৃত জীরন ব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছে তাদের আনুগত্য পরিহার করো। এরা সব লাগাম ছাড়া। নৈতিকতার সমস্ত সীমা লংঘন করে এরা লাগামহীন পশুতে পরিণত হয়েছে। এদের দ্বারা সমাজ সভ্যতার কোনো সংস্কার হতে পারেনা। এরা যে ব্যবস্থা পরিচালনা করবে তার মধ্যে বিকৃতিই ছড়িয়ে পড়বে। তোমাদের জন্য কল্যাণের কোনো পথ যদি থাকে তাহলে তা কেবলমাত্র এই একটিই। অর্থাৎ তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি করো এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের আনুগত্য পরিহার করে আমার আনুগত্য করো। কারণ আমি আল্লাহ্র রসূল। আমার আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে তোমরা পূর্ব থেকেই অবগত আছো। আমি একজন নিস্বার্থ ব্যক্তি। নিজের কোনো ব্যক্তিগত লাভের জন্য আমি এ সংস্কারমূলক কাজে হাত দেইনি। এ ছিলো হযরত সালেহ আলাইহিস্ সালামের ঘোষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার। নিজের জাতির সামনে তিনি এটি পেশ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধু প্রচারণাই ছিলোনা বরং একই সংগে তামাদ্দুনিক ও নৈতিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক বিপ্লবের দাওয়াতেও ছিলো।
গ. “এমন কোনো লোকের আনুগত্য করোনা যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির কামনা বাসনার অনুসরণ করেছে এবং যার কর্মপদ্ধতি কখনো উগ্র, কখনো উদাসীন।” (সূরা আল কাহফঃ ২৮)
অর্থাৎ তার কথা মেনোনা, তার সমনে মাথা নতো করোনা, তার ইচ্ছা পূর্ণ করোনা এবং তার কথায় চলোনা। এখানে আনুগত্য শদ্বটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়েছে।
৬. প্রতিরক্ষা এবং যুদ্ধ ও সন্ধির মূলনীতি
ইসলামী রাষ্ট্রের একটি বুনিয়াদী পলিসি হলো, তা সর্বদিক থেকে হবে মজবূত, সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত সামরিক দিক থেকেও, অথনৈতিক দিক থেকেও। সে যে মহান দায়িত্ব পালন করবে তা প্রবল প্রতিরক্ষা শক্তির প্রস্তুতি ছাড়া কিছুতেই পালন করা সম্ভব নয়ঃ
ক. “আর তোমরা নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী সর্বাধিক পরিমাণ শক্তি ও সদাপ্রস্তুত ঘোড়া তাদের মুকাবিলার জন্য যোগড় করে রাখো। এর মাধ্যমে তোমরা ভীত সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহ্র শত্রুকে, নিজের শত্রুকে এবং অন্য এমন সব শত্রুকে যাদের তোমরা চিনোনা। কিন্তু আল্লাহ্ চিনেন।” (সূরা আনফালঃ ৬০)
এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যুদ্ধোপকরণ ও একটি স্থায়ী সেনাবাহিনী (Standing Army) সর্বক্ষণ তৈরী থাকতে হবে। তাহলে প্রয়োজনের সময় সংগে সংগেই সামরিক পদক্ষেপ নেয়া সম্ভবপর হবে। এমন যেনো না হয়, বিপদ মাথার ওপর এসে পরার পর হতবুদ্ধি হয়ে তাড়াতাড়ি স্বেচ্ছাসেবক, অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য রসদপত্র যোগাড় করার চেষ্টা হবে এবং এভাবে প্রস্তুতি পর্ব সম্পন্ন হতে হতেই শত্রু তার কাজ শেষ করে ফেলবে।
খ. “যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে লড়াই এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে। দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখিরাতে রয়েছে তদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি।” (সূরা মায়িদাঃ ৩৩)
পৃথিবী বলতে এখানে পৃথিবীর সেই অংশ ও অঞ্চল বুঝাচ্ছে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ্ ও রসূলের সাথে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী সরকার দেশে যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠা সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠা রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আল্লাহ্র ইচ্ছা এবং এ জন্য নিজের রসূল পাঠিয়েছেলেন। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, মানবতা তার প্রকৃতির কাংখিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীর সমুদয় উপায় উপকরণ এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার ফলে সেগুলো মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির নয় বরং তার উন্নতির সহায়ক হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা কোনো ভূখন্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো, বা ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লন্ঠন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদি পর্যায়ে চালানো হোক অথবা আরো বড় আকারে, এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই চালানো হোক না কেন, তা আসলে আল্লাহ্ ও তার রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটা ঠিক তেমনি যেমন ভারতিয় দন্ডবিধিতে কোনো ব্যক্তির ভারতে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে “সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ” (Waging war against the king) করার অপরাধে অভিযুক্ত গণ্য করা হয়েছে- সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো একজন মামূলী সিপাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করলেও এবং সম্রাট তার নাগালের বহু দূরে অবস্থান করলেও তার অপরাধের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়না।
বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা এখানে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কাযী বা সমকালীন ইসলামী শাসক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা প্রকাশ করা যে, ইসলামী হুকুমতের আওতায় বাস করে কোনো ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের কোনো ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ এবং এ জন্য তাকে উল্লেখিত চরম শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন্ শাস্তি দেয়া যেতে পারে।
গ. “আহলি কিতাবদের যারা আল্লাহ্ ও পরকালি ঈমান আনেনা, যা কিছু আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল হারাম গণ্য করেছেন তাকে হারাম করেনা এবং সত্য দীনকে নিজেদের দীনে পরিণত করেনা, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের হাতে জিযিয়া দেয় ও পদানত হয়ে থাকে।”(সূরা তওবাঃ ২৯)
আল্লাহ্ তাঁর রসূলের মাধ্যমে যে শরীয়ত নাযিল করেছেন তাকে যারা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেনা, এখানে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে।
তারা ঈমান আনবে ও আল্লাহ্র সত্য দীনের অনুসারী হয়ে যাবে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য লক্ষ্য তা নয়। বরং যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছেঃ তাদের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য খতম হয়ে যাবে। তারা পৃথিবীতে শসন কর্তৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবেনা। বরং পৃথিবীতে মানুষের জীবন ব্যবস্থার লাগাম এবং মানুষের ওপর কর্তৃত্ব করা ও তাদের নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সত্যের অনুসারীদের হাতে থাকবে এবং তারা এ সত্যের অনুসারীদের অধীনে অনুগত জীবন যাপন করবে।
যিম্মীদেরকে ইসলামী শাসনের অওতায় যে নিরাপত্তা ও সংরক্ষণ দান করা হবে তার বিনিময়কে জিযিয়া বলা হয়। তাছাড়া তারা যে হুকুম মেনে চলতে এবং ইসলামী শাসনের আওতাধীন বসবাস করতে রাযী হয়েছে, এটা তার একটা আলামত হিসেবেও চিহ্নিত হবে। “নিজের হাতে জিযিয়া দেয়” –এর অর্থ হচ্ছে, সহজ সরল আনুগত্যের ভংগিতে জিযিয়া আদায় করা। আর “পদানত হয়ে থাকে” এর অর্থ, পৃথিবীতে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের নয় বরং যে মুমিন ও মুসলিমরা আল্লাহ্র খিলাফত ও প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করেছে তাদের হাতে থাকবে।
প্রথম দিকে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কাছ থেকে জিযিয়া আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছেল। কিন্তু পরবর্তীকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মাসজীদের (অগ্নিউপাসক) থেকে জিযিয়া আদায় করে তাদেরকে যিম্মী করেন। এরপর সাহাবায়ে কিরাম সর্বসম্মতিক্রমে আরবের বাইরের সব জাতির ওপর সাধারণভাবে এ আদেশ প্রয়োগ করেন।
ঊনিশ শতকে মুসলিম মিল্লাতের পতন ও অবনতির যুগে এ ‘জিযিয়া’ সম্পর্কে মুসলমানদের পক্ষ থেকে বড় বড় সাফাই পেশ করা হতো। সে রকম কিছু লোক এখনো রয়েছে এবং তারা এখনো এ ব্যাপারে সাফাই গেয়ে চলেছে। কিন্তু আল্লাহ্র দীন এসবের অনেক উর্দ্ধে। আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহের ভূমিকায় অবতীর্ণ, ও সোজা কথায়, যারা আল্লাহ্র দীনকে গ্রহণ করেনা এবং নিজেদের বা অন্যের উদ্ভাবিত ভুল পথে চলে, তার বড় জোর এতোটুকু স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকার রাখে যে, নিজেরা ভুল পথে চলতে চাইলে চলতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র যমীনে কোনো একটি জায়গায়ও মানুষের ওপর শাসন চালাবার এবং নিজেদের ভ্রান্তনীতি অনুযায়ী মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত করার আদৌ কোনো অধিকার তাদের নেই। দুনিয়ার যেখানেই তারা এ জিনিসটি লাভ করবে সেখানেই বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তাদেরকে এ অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়ে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ জীবন বিধানের অনুগত করার জন্য প্রচষ্টা চালানোই হবে মুমিনদের কর্তব্য। এখন প্রশ্ন থেকে যায়, এ জিযিয়া কিসের বিনিময়ে দেয়? এর জবাব হচ্ছে, ইসলামী শামন কর্তৃত্বের আওতাধীনে নিজেদের গোমরাহীর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য অমুসলিমদের যে স্বাধীনতা দান করা হয় এটা তারই মূল্য। আর যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা তাদের এ স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার অনুমতি দেয় এবং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করে তার শাসন ও আইন শৃংখলা ব্যবস্থা পরিচালনায় এ অর্থ ব্যয়িত হওয়া উচিত। এর সবচেয়ে বড় ফায়দা হচ্ছে এই যে, জিযিয়া আদাল করার সময় প্রতি বছর যিম্মীদের সধ্যে একটি অনুভূতি জাগতে থাকবে। প্রতি বছর তারা মনে করতে থাকবে, তারা আল্লাহ্র পথে যাকাত দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত আর এর পরিবর্তে গোমরাহী ও ভ্রষ্টতার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য তাদের মূল্য দিতে হচ্ছে। এটা তাদের কত বড় দুর্ভাগ্য। এ দুর্ভাগ্যের কারাগারে তারা বন্দী।
ঘ. “তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।” (সূরা মায়িদাঃ ৩৪)
অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও তাকে ছিন্নভিন্ন করার অপচেষ্টা পরিহার করে এবং তাদের পরবর্তী কর্মনীতি একথা প্রমাণ করে যে, তারা শান্তিপ্রিয়, আইনের অনুগত ও সদাচারী হয়ে গেছে আর তারপর যদি তাদের আগের অপরাধের কথা জানা যায়, তাহলে ওপরে বর্ণিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোনো শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবেনা। তবে যদি তারা মানুষের অধিকারের ওপর কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত মুক্ত করা যাবেনা। যেমন তারা যদি কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে থাকে অথবা কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করে থাকে বা অন্য কোনো অপরাধ করে থাকে, তবে এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ অপরাধ সংক্রন্ত ফৌজদারী মামলা চালানো হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা বা আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কিত কোনো মামলা তাদের বিরুদ্ধে চালানো হবেনা।
৭. সমাজনীতি রাজনীতি ও শিক্ষানীতির সাধারণ মূলনীতি
“তোমার রব ফায়সালা করে দিয়েছেনঃ
১. তোমরা কারোর ইবাদত করোনা, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করো!
২. পিতামাতার সাথে ভাল ব্যবহার করো। যদি তোমাদের কাছে তাদের কোনো একজন বা উভয় বৃদ্ধ অবস্থায় থাকে, তাহলে তাদেরকে “উহ” পর্যন্তও বলোনা এবং তাদেরকে ধমকের সুরে জবাব দিয়োনা বরং তাদের সাথে মর্যাদা সহকারে বথা বলো। আর দয়া ও কোমলতা সহকারে তাদের সামনে বিনম্র থাকো এবং দোয়া করতে থাকো এই বলেঃ হে আমার প্রতিপপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা দয়া, মায়া, মমতাসহকারে শৈশবে আমাকে প্রতিপালন করেছিলেন। তোমাদের রব খুব ভালো করেই জানেন তোমাদের মনে কি আছে। যদি তোমরা সৎকর্মশীল হয়ে জীবন যাপন করো তাহলে তিনি এমন লোকদের প্রতি ক্ষমাশীল যারা নিজেদের ভুলের ব্যাপারে সতর্ক হয়ে বন্দেগীর নীতি অবলম্বন করার দিকে ফিরে আসে।
৩. আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও তাদের অধিকার দাও।
৪. বাজে খরচ করোনা। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই আর শয়তান তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ।
৫. যদি তাদের থেকে (অর্থাৎ অভাবী, আত্মীয় স্বজন মিসকীন ও মুসাফির থেকে) তোমাকে মুখ ফিরিয়ে নিতে হয় এ জন্য যে, এখনো তুমি আল্লাহ্র প্রত্যাশিত রহমতের সন্ধান করে ফিরছো, তাহলে তাদেরকে নরম জবাব দাও।
৬. নিজের হাত গলায় বেঁধে রেখোনা এবং তাকে একবারে খোলাও ছেড়ে দিয়োনা, তাহলে তুমি নিন্দিত ও অক্ষম হয়ে যাবে। তোমার রব যার জন্য চান রিযিক প্রশস্ত করে দেন আবার যার জন্য চান সংকীর্ণ করে দেন। তিনি নিজের বান্দাদের অবস্থা জানেন এবং তাদেরকে দেখছেন।
৭. দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করোনা। আমি তাদেরকেও রিযিক দেবো এবং তোমাদেরকেও। আসলে তাদেরকে হত্যা করা একটি মহাপাপ।
৮. যিনার কাছেও যেয়োনা, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং খুবই জঘন্য পথ।
৯. আল্লাহ্ যাকে হত্যা করা হারাম করে দিয়েছেন, সত্য ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করোনা। আর যে ব্যক্তি মযলুম অবস্থায় নিহত তার অভিভাবককে আমি কিসাস দাবী করার অধিকার দান করেছি। কাজেই হত্যার ব্যাপারে তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়, তাকে সাহায্য করা হবে।
১০. এতীমের সম্পত্তির ধারে কাছে যেয়োনা, তবে হ্যাঁ সদুপায়ে, যে পর্যন্ত না সে বয়োপ্রাপ্ত হয়ে যায়।
১১. প্রতিশ্রুতি পালন করো, অবশ্যই প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তোমাদের জবাবদিহি করতে হবে।
১২. মেপে দেবার সময় পরিমাপ পাত্র ভরে দাও এবং ওজন করে দেবার সময় সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো। এটিই ভালো পদ্ধতি এবং পরিণামের দিক দিয়েও এটিই উত্তম।
১৩. এমন কোনো জিনিসের পেছনে লেগে যেয়োনা যে সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। নিশ্চিতভাবেই চোখ. কান ও দিল সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।
১৪. যমীনে দম্ভভরে চলোনা। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌছে যেতে পারবে।
এ বিষয়গুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটির খারাপ দিক তোমার রবের কাছে অপছন্দনীয়। তোমার রব তোমাকে অহীর মাধ্যমে যে হিকমতের কথাগুলো বলেছেন এগুলো তার অন্তর্ভুক্ত। (সূরা বনী ইসরাঈলঃ ২৩-২৯)
এখানে এমন সব বড় বড় মূলনীতি ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে যেগুলোর ওপর ভিত্তি করে ইসলাম মানুষের সমগ্র জীবন ব্যবস্থার ইমারত গড়ে তুলতে চায়। একে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আন্দোলনের ঘোষণাপত্র বলা যায়। মক্কী যুগের শেষে এবং আসন্ন মাদানী যুগের প্রারন্ত লগ্নে এ ঘোষণাপত্র পেশ করা হয়। এভাবে এ নতুন ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রের বুনিয়াদ কোন্ ধরনের চিন্তামূলক, নৈতিক, তামাদ্দুনিক, অর্থনৈতিক ও আইনগত মূলনীতির ওপর রাখা হবে তা সারা দুনিয়ার মানুষ জানতে পারবে। এ প্রসংগে সূরা আন’য়ামের ১৯ রুকু’ এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট টীকার ওপরও একবার চোখ বুলিয়ে নিলে ভালো হয়।
ধারা ১: এর অর্থ কেবল এতটুকুই নয় যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো পূজা উপাসনা করোনা বরং এ সংগে এর অর্থ হচ্ছে, বন্দেগী, গোলামী ও দ্বিধাহীন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্রই করতে হবে। একমাত্র তাঁরই হুকুমকে হুকুম এবঙ তাঁরই আইনকে আইন বলে মেনে নাও এবং তাঁর ছাড়া আর কারো সার্বভৌম কর্তৃক স্বীকার করোনা। এটি কেবলমাত্র একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত কর্মধারার জন্য একটি পথনির্দেশনাই নয়। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদীনা তাইয়েবায় পৌছে কার্যত যে রাজনৈতিক, তামাদ্দুনিক ও নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন এটি হচ্ছে সেই সমগ্র ব্যাবস্থার ভিত্তি প্রস্তরও। এ ইমারতের দুনিয়াদ রাখা হয়েছিল মতাদর্শের ভিত্তিতে যে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্ই সমগ্র বিশ্বলোকের মালিক ও বাদশাহ এবং তাঁরই শরীয়ত এ রাজ্যের আইন।
ধারা ২: এ আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র পরে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হক ও অগ্রধিকার হচ্ছে পিতামাতার! সন্তানকে পিতামাতার অনুগত, সেবা পরায়ণ ও মর্যাদাবোধসম্পন্ন হতে হবে। সমাজের সামষ্টিক নৈতিক বৃত্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে, যার ফলে সন্তানরা বাপমায়ের মুখোপেক্ষাহীন হয়ে পড়বেনা। বরং তারা নিজেদেরকে বাপমায়ের অনুগৃহীত মনে করবে এবং বুড়ো বয়েসে তাদেকে ঠিক তেমনিভাবে বাপমায়ের খিদমত করা শেখবে যেমনিভাবে বাপমা শিশুকালে তাতে পরিচর্যা ও লালান পালন এবং মান অভিমান বরদাশ্ত করে এসেছে। এ আয়াতটিও নিছক একটি নৈতিক সুপারিশ নয় বরং এরি ভিত্তিতে পরবর্তী পর্যায়ে বাপমায়ের জন্য এমনসব শর’য়ী অধিকার ও ক্ষমতা নির্ধারণ করা হয়েছে যেগুলোর বিস্তারিত বিবরণ আমরা হাদীসে ও ফিকাহর কিতাবগুলোতে পাই। তাছাড়া ইসলামী সমাজের মানসিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণ এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক শিষ্টাচারের ক্ষেত্রে বাপমায়ের প্রতি আচরণ ও আনুগত্য এবং তাদের অধিকারে রক্ষণাবেক্ষণকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ জিনিসগুলো চিরকালের জন্য নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র নিজের আইন কানুন, ব্যবস্থাপনামূলক বিধান ও শিক্ষানীতির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালি ও সংরক্ষিত করার চেষ্টা করবে, দুর্বল করবেনা।
ধারা ৩-৫: তিনটি ধারার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ নিজের উপার্জন ও ধন দৌলত শুধুমাত্র নিজের জন্যই নির্ধারিত করে নেবেনা বরং ন্যায়সংগতভাবে ও ভারসাম্য সহকারে নিজের প্রয়োজন পূর্ণ করার পর নিজের আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশী ও অন্যান্য অভাবী লোকদের অধিকারও আদায় করবে। সমাজ জীবনে সাহায্য সহযোগিতা, সহানুভুতি এবং অন্যের অধিকার জানা ও তা আদায় করা প্রবণতা সক্রিয় ও সঞ্চারিত থাকবে। প্রত্যেক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের সাহায্যকারী এবং প্রত্যেক সমর্থ ব্যক্তি নিজের আশপাশের অভাবী মানুষেদের সাহায্যকারী হবে। একজন মুসফির যে জনপদেই যাবে নিজেকে অতিথি বৎসর লোকদের মধ্যেই দেখতে পাবে। সমাজে অধিকারে ধারণা এতো বেশী ব্যাপক হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি যাদের মাধ্যে অবস্থান করে নিজের ব্যক্তি সত্তা ও ধন সম্পদের ওপর তাদের সবার অধিকার অনুভব করবে। তাদের খিদমত করার সময় এ ধারণা নিয়েই খিদমত করবে যে সে তাদের অধিকার আদায় করছে, তাদেরকে অনুগ্রহ পাশে আবদ্ধ করছেনা। কারোর খিদমত করতে অক্ষম হলে তার কাছে ক্ষমা চাইবে এবং আল্লাহ্র বান্দাদের খিদমত করার যোগ্যতা লাভ করার জন্য আল্লাহ্র কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা করবে।
ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাগুলোও শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নৈতিকতার শিক্ষাই ছিলোনা বরং পরবর্তী সময়ে মদনিা তাইয়েবার সমাজে ও রাষ্ট্রে এগুলোর ভিত্তিতেই ওয়াজিব ও নফল সদকার বিধানসমূহ প্রদত্ত হয়, অসিয়ত, মীরাস ও ওয়াকফের পদ্ধতি নির্ধারিত হয়, এতিমের অধিকার সংরক্ষণেল ব্যাবস্থা করা হয়, প্রত্যেক জনবসতির ওপর মুসাফিরের কমপক্ষে তিনদেন পর্যন্ত মেহমানদারী করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হয় এবং সংগে সমাজের নৈতিক ব্যবস্থা কর্যত এমন পর্যায়ে উন্নীত করা হয় যার ফলে সমগ্র সামাজিক পরিবেশে দানশীলতা, সহানুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাব সঞ্চারিত হয়ে যায়। এমনকি লোকেরা স্বতস্ফুর্তভাবে আইনগত অধিকারসমূহ দেয়া ছাড়াও আইনের জোরে যেসব নৈতিক অধিকার চওয়া ও প্রদান করা যায়না সেগুলোও উপলব্ধি ও আদায় করতে থাকে।
ধারা ৬: “হাত বাঁধা” একটি রূপক কথা। কৃপণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর “হাত খোলা ছেড়ে দেয়ার মানে হেচ্ছে, বাজে খরচ করা। ৪র্থ ধারার সাথে ৬ষ্ঠ ধারাটির এ ব্যক্যোংশটি মিলিয়ে পড়লে এর পরিষ্কার অর্থ এই মানে হয় যে, লোকদের মধ্যে এতোটুকু ভারসাম্য হতে হবে যাতে তারা কৃপণ হয়ে অর্থের আবর্তন রুখে না দেয় এবং অপব্যয়ী হয়ে নিজের অর্থনৈতিক শক্তি ধ্বংস না করে ফেলে। এর বিপরীত পক্ষে তাদের মধ্যে ভারসাম্যের এমন সঠিক অনুভূতি থাকতে হবে যার ফলে তারা যথার্থ ব্যয় থেকে বিরত হবেনা আবার অযথা ব্যয়জনিত ক্ষতিরও শিকার হবেনা। অহংকার ও প্রদর্শনেচ্ছামূলক এবং লোক দেখানো খরচ, বিলাসিতা, ফাসেকী ও অশ্লীল কাজে ব্যয় এবং এমন যাবতীয় ব্যয় যা মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনেও কল্যাণমূলক কাজে লাগার পরিবর্তে ধন সম্পদ ভুল পথে নিয়োজিত করে, তা আসলে আল্লাহ্র নিয়ামত অস্বীকার ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা এভাবে নিজেদের ধন-দৌলত খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।
এ ধারাগুলোও নিছক নৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত হিদায়াত পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়। বরং এদিকে পরিষ্কার ইংগিত করছে যে, একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজকে নৈতিক অনুশীলন, সামষ্টিক চাপ প্রয়োগ ও আইনগত বাঁধা নিষেধ আরোপের মাধ্যমে অযথা অর্থ ব্যয় থেকে বিরত রাখা উচিত। এ কারণেই পরবর্তীকালে মদীনা রাষ্ট্রে বিভিন্ন কার্যকর পদ্ধতিতে এ উভয় ধারা নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা হয়। প্রথমত অপব্যয় ও বিলাসিতার বহু নীতি প্রথাকে আইনগতভাবে হারাম করা হয়। দ্বিতীয়দ পরোক্ষভাবে আইনগত কৌশল অবলম্বন করে অযথা অর্থব্যয়ের পথ বন্ধ করা হয়। তৃতীয়ত সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে এমন বহু রসম রেওয়াজের বিলোপ সাধন করা হয় যেগুলোতে অপব্যয় করা হতো। তারপর রাষ্ট্রেকে বিশেষ ক্ষমতা বলে এবং বিশেষ ব্যবস্থাপনা বিধান জারী করে সুস্পষ্ট অপব্যয়ের ক্ষেত্রে বাঁধা দেয়ার ইখতিয়ার দেয়া হয়। এভাবে যাকাত ও সদকার বিধানের মাধ্যমে কৃপণতার শক্তিকে গুড়িয়ে দেয়া হয় এবং লোকেরা সম্পদ পুঞ্জীভূত করে অর্থের আবর্তনের পথ বন্ধ করে দেবে এ সম্ভাবনাও নির্মূল করে দেয়া হয়। এসব কৌশল অবলম্বন করার সাথে সমাজে এমন একটি সাধারণ জনমত সৃষ্টি করা হয়, যা দানশীলতা ও অপব্যয়ের মধ্যকার পার্থক্য সঠিকভাবে জনতো এবং কৃপণতা ও ভারসাম্যপূর্ণ ব্যয়ের মধ্যে ভালোভাবেই ফারাক করতে পারতো। এ জনমত কৃপণদেরকে লাঞ্ছিত করে, ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষাকারীদেরকে মর্যাদাশীল করে, অপব্যয়কারীদের নিন্দা করে এবং দানশীলদেরকে সমগ্র সমাজের খেশবুদার ফুল হিসেবে কদর করে। সে সময়ের নৈতিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রভাব আজো মুসলিম সমাজ রয়েছে। আজো দুনিয়ার সব দেশেই মুসলমানরা কৃপণ ও সম্পদ পুঞ্জিীভূতকারীদেরকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখে এবং দানশীলরা আজো তাদের চোখে সন্মানার্হ ও মর্যাদা সম্পন্ন।
অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ নিজের বান্দাদের মধ্যে রিযিক কমবেশী করার ক্ষেত্রে যে পার্থাক্য রেখেছেন তার উপযোগিতা বুঝা মানুষের পক্ষে সম্বব নয়। কাজেই রিযিক বন্টনের যে প্রাকৃতিক ব্যবস্থা রয়েছে কৃত্রিম মানবিক কৌশলের মাধ্যমে তার মধ্যে হস্তক্ষেপ না করা উচিত। প্রাকৃতিক অসাম্যকে কৃত্রিম সাম্যে পরিবর্তিত করা অথবা এ অসাম্যক প্রাকৃতিক সীমার চৌহদ্দী পার করিয়ে বেইনসাফির সীমানায় পৌঁছিয়ে দেয়া উভয়টিই সমান ভুল। একটি সঠিক অর্থেনৈতিক ব্যবস্থার অবস্থান আল্লাহ্ নির্ধারিত রিযিক বন্টন পদ্ধতির নিকটতরই হয়ে থাকে।
এ বাক্য প্রাকৃতিক আইনের যে নিয়মটির দিকে পথনির্দেশ করা হয়েছেল তার কারণে মদীনা সংস্কার কর্মসূচীতে এ ধারণাটি আদতে কোনো ঠাঁই করে নিতে পারেনি যে রিযিক ও রিযিকের উপায় উপকরণগুলোর মধ্যে পার্থক্য ও শেষ্ঠত আসলে এমন কোনো অকল্যাণকর বিষয় নয়, যাকে বিলুপ্ত করা এবং একটি শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করা কোন পর্যায়ে কাংখিত হতে পারে। পক্ষান্তরে সৎকর্মশীলতা ও সদাচারের ভিত্তিতে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির বুনিয়াদ কায়েম করার জন্য মদীনা তাইয়েবায় এক বিশেষ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সে কর্মপদ্ধতি ছিলো এই যে, আল্লাহ্র দেয়া প্রকৃতি মানুষের মধ্যে যে পার্থক্য করে রেখেছে তাকে আসল প্রাকৃতিক অবস্থায় অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা অপরিবর্তিত রাখতে হবে এবং ওপরে প্রদত্ত পথনির্দেশনা অনুযায়ী সমাজের নৈতিকতা আচার আচরণ ও কর্মবিধানসমূহ এমনভাবে সংশোধন করে দিতে হবে, যার ফলে জীবিকার পার্থক্য ও ব্যবধান কোনো যুলুম ও বেইনসাফির বাহনে পরিণত হবার পরিবর্তে এমন অসংখ্য নৈতিক, আধ্যত্মিক ও তামাদ্দুনিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধির বাহনে পরিণত হবে, যে জন্য মূলত বিশ্বজাহানের স্রষ্টা তাঁর বান্দাদের মধ্যে এ পার্থক্য ও ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছেন।
ধারা ৭: যেসব অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রাচীনকাল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত যুগে যুগে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন আন্দোলন দানা বেঁধেছে, এ আয়াতটি তার ভিত পুরোপুরি ধ্বসিয়ে দিয়েছে। প্রাচীন যুগে দারিদ্রভীতি শিশু হত্যাও গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভপাতের কারণ হতো। আর আজ তা দুনিয়াবাসীকে তৃতীয় আর একটি কৌশল অর্থাৎ গর্ভনিরোধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের ঘোষণাপত্রের এ ধারাটি তাকে অন্নগ্রহণকারীদের সংখ্যা কমাবার ধ্বংসাত্মক প্র্রচেষ্টা ত্যাগ করে এমনসব গঠনমূলক কাজে নিজের শক্তি ও যোগ্যতা নিয়োগ করার নির্দেশ দিচ্ছে যেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ্র তৈরী প্রাকৃতিক বিধান অনুযায়ী রিযিক বৃদ্ধি থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এ ধারাটির দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণের স্বল্পতার আশংকায় মানুষের বারবার সন্তান উৎপাদনের সিলাসিলা বন্ধ করে দিতে উদ্যত হওয়া তার বৃহত্তও ভুলগুলোর অন্যতম হিসেবে চিহিৃত হয়েছে। এ ধারাটি মানুষকে এ বলে সাবধান করে দিচ্ছে যে, রিযিক পৌঁছাবার ব্যবস্থাপনা তোমার আয়ত্বাধীন নয় বরং এটি এমন এক আল্লাহ্র আয়ত্বাধীন যিনি তোমাকে এ যমীনে আবাদ করেছেন। পূর্বে আগমনকারীদেরকে তিনি যেভাবে রুযি দিয়ে এসেছেন বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা যতোই বৃদ্ধি হতে থেকেছে ঠিক সেই পরিমাণে বরং বহুসময় তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ বেড়ে হেয়েছে। কাজেই আল্লাহ্র সৃষ্টি ব্যবস্থাপনায় মানুষের অযথা হস্তক্ষেপ নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়।
এ শিক্ষার ফলেই কুরআন নযিলের যুগ থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত কোনো যুগ মুসলমানদের মধ্যে জন্ম শাসনের কোনো ব্যাপাক ভাবধারা জন্ম লাভ করতে পারেনি।
ধারা ৮: “যিনার কাছেও যেয়োনা” এ হুকুম ব্যক্তির জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র সমাজের জন্যও। ব্যক্তির জন্য এ হুকুমের দিক টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন কাজ থেকে দূরে থেকেই ক্ষান্ত হবেনা বরং এ পথের দিকে টেনে নিয়ে যায় যিনার এমন সব সূচনাকারী এবং প্রাথমিক উদ্যোগ ও আকর্ষণ সৃষ্টিকারী বিষয় থেকেও দূরে থাকবে। আর সমাজের ব্যাপারে বলা যায়, এ হুকুমের প্রেক্ষিতে সমাজ জীবনে যিনা, যিনার উদ্যেগ আকর্ষণ এবং তার কারণসমূহের পথ বন্ধ করে দেয়া সমাজের জন্য ফরয হয়ে যাবে। এ উদ্দেশ্যে সে আইন প্রণয়ন, শিক্ষা ও অনুশীলন দান, সামাজিক পরিবেশের সংস্কার সাধন, সমাজ জীবনের যথাযোগ্য বিন্যাস এবং অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যবস্থা অবলম্বন করবে।
এ ধারাটি শেষ পর্যন্ত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার একটি বৃহত্তম অধ্যায়ের বুনিয়াদে পরিণত হয়। এর অভিপ্রায় অনুযায়ী যিনা ও যিনার অপবাদেকে ফৌজদারী অপরাধ গন্য করা হয়। পর্দার বিধান জারী করা হয়। অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতার প্রচার কঠোরভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়। মদ্যপান, নাচ, গান ও ছবির (যা যিনার নিকটতম আত্মীয়) ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। আর এ সংগে এমন একটি দাম্পত্য আইন প্রণয়ন করা হয় যার ফলে বিবাহ সহজ হয়ে যায় এবং যিনার সামাজিক কারণসমূহের শিকড় কেটে যায়।
ধারা ৯: কাউকেও হত্যা করা মানে কেবলমাত্র অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করাই নয়, নিজেকে হত্যা করাও এর অন্তরভূক্ত। কারণ মানুষকে মহান আল্লাহ্র মর্যাদা সম্পন্ন করেছেন। অন্যের প্রাণের সাথে সাথে মানুষের নিজের প্রাণও এ সংজ্ঞার অন্তরভূক্ত। কাজেই মানুষ হত্যা যতো বড় গুনাহ ও অপরাধ, আত্মহত্যা করাও ঠিক ততো বড় অপরাধ ও গুনাহ। মানুষ নিজেকে নিজের প্রাণের মালিক এবং এ মালিকানাকে নিজ ক্ষমতায় খতম করে দেবার অধিকার রাখে বলে মনে করে, এটা তার একটা বিরাট ভুল ধারণা। অথচ তার এ প্রাণ আল্লাহ্র মালিকানাধীন এবং সে একে খতম করে দেয়া তো দূরের কথা একে কোনো অনুপযোগী কজে ব্যবহার করার অধিকারও রাখেনা। দুনিয়ার এ পরীক্ষাগৃহ আল্লাহ্ যেভাবেই আমাদের পরীক্ষা নেন না কেন, পরীক্ষার অবস্থা ভালো হোক বা মন্দ হোক, সেভাবেই শেষ সময় পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা দিতে থাকা উচিত। আল্লাহ্র দেয়া সময়কে ইচ্ছা করে খতম করে দিয়ে পরীক্ষাগৃহ থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা একটি ভ্রান্ত পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আবার এ পালিয়ে যাবার কাজটিও এমন এক অপরাধের মাধ্যমে সম্পন্ন করা যকে আল্লাহ্ সুস্পষ্ট ভাষায় হারাম গণ্য করেছেন, এটা তো কোনোক্রমেই গ্রহণীয় হতে পারেনা। অন্য কথায় বলা যায়, দুনিয়ার ছোট ছোট কষ্ট, লাঞ্ছনা ও অপমানের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মানুষ বৃহত্তর ও চিরন্তন কষ্ট ও লাঞ্ছনার দিক পালিয়ে যাচ্ছে।
পরবর্তীকালে ইসলামী আইন ‘সত্য সহকারে হত্যাকে শুধুমাত্র পাঁচটি ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এক. জেনে বুঝে হত্যাকারী থেকে কেসাস নেয়া। দুই. আল্লাহ্র সত্যদীনের পথে বাঁধাদানকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। তিন. ইসলামী রাষ্ট্রে শাসন ব্যাবস্থা উৎখাত করার প্রচেষ্টাকারীদের শাস্তি দেয়া। চার. বিবাহিত পুরুষ ও নারীকে ব্যভিচার লিপ্ত হওয়ার শাস্তি দেয়া। পাঁচ. মুরতাদেকে শাস্তি দেয়া। শুধুমাত্র এ পাঁচটি ক্ষেত্রে মানুষের প্রাণের মর্যাদা তিরোহিত হয় এবং তাকে হত্যা করা বৈধ গণ্য হয়।
মূল শদ্ব হচ্ছে, “তার অভিভাবককে আমি সুলতান দান করেছে।” এখানে সুলতান অর্থ হচ্ছে “প্রমাণ” যার ভিত্তিতে সে কিসাস দাবী করতে পারে। এ থেকে ইসলামী আইনের এ মূলনীতি বের হয় যে, হত্যা মুকদ্দামার আসল বাদী সরকার নয়। বরং নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণই এর মূল বাদীপক্ষ। তারা হত্যাকারীকে মাফ করে দিতে এবং কিসাসের পরিবর্তে রক্তপণ করতে সম্মত হতে পারে।
হত্যার ব্যাপারে বিভিন্নভাবে সীমা অতিক্রম করা যেতে পারে। এগুলো সবই দিষিদ্ধ। যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে উন্মত্তোর মতো অপরাধী ছাড়া অন্যদেরকেও হত্যা করা অথবা অপরাধীকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরে ফেলা। কিংবা মেরে ফেলার পর তার লাশের ওপর মনের ঝাল মেটানো। অথবা রক্তপণ নেবার পর আবার তাকে হত্যা করা ইত্যাদি।
যেহেতু সে সময় পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাই কে তাকে সাহায্য করবে, একথা স্পষ্ট করে বলা হয়েনি। পরে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন ফয়সালা করে দেয়া হয় যে, তাকে সাহায্য করা তার গোত্র বা সহযোগী বন্ধু দলের কাজ নয় বরং এটা হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র এবং তার বিচার ব্যবস্থার কাজ। কোনো ব্যক্তি বা দল নিজস্বভাবে হত্যার প্রতিশোধ নেবার অধিকার রাখেনা। বরং এটা ইসলামী সরকারে দায়িত্ব। ন্যায় বিচার লাভ করার জন্য তার কাছে সাহায্য চাওয়া হবে।
ধারা ১০: এটিও নিছক একটি নৈতিক নির্দেশনামা ছিলোনা। বরং পরবর্তীকালে যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এতিমদের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য প্রশাসনিক ও আইনগত উভয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ আমারা হাদীস ও ফিকহর কিতাবগুলোতে পাই। তার পর এখান থেকে এ ব্যাপক ভিত্তিক মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক নিজেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার কোনো অভিভাবক নেই আমিই তার অভিভাবক” এ হাদীসটি এদিকেই ইংগিত করে এবং এ ইসলামী আইনের একটি বিস্তৃত অধ্যায়ের ভূমিকা রচনা করে।
ধারা ১১: এটিও নিছক ব্যক্তিগত নৈতিকতারই একটি ধারা ছিলোনা বরং যখন ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখন একেই সমগ্র জাতির আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক রাজনীতির ভিত্তি গণ্য করা হয়।
ধারা ১২: এ নির্দেশটাও নিছক ব্যক্তিবর্গেন পারস্পরিক লেনদেন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয় বরং ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠির পর হাট, বাজার ও দোকানগুলোতে মাপজোক ও দাঁড়িপাল্লাগুলো তত্বাবধান করা এবং শক্তি প্রয়োগ করে ওজনে ও মাপে কম দেয়া বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। তারপর এখান থেকেই এ ব্যাপক মূলনীতি গৃহীত হয় যে, ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সব রকমের বেঈমানী ও অধিকার হরণের পথ রোধ করা সরকারের দায়িত্বের অন্তরভূক্ত।
ধারা ১৩: এ ধারাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে, লোকেরা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে ধারণা ও অনুমানের পরিবর্তে “জ্ঞানের” পেছনে চলাবে। ইসলামী সমাজ এ ধারাটির প্রয়োগ ব্যাপকভাবে নৈতিক ব্যবস্থায়, আইনে, রাজনীতিতে, দেশ শাসনে, জ্ঞান বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থায় তথা জীবনের সকল বিভাগে সুষ্ঠুভাবে করা হয়েছে। জ্ঞানের পরিবর্তে অনুমানের পেছনে চলার কারণে মানুষের জীবনে যে অসংখ্য দুষ্ট মতের সৃষ্টি হয় তা থেকে চিন্তা ও কর্মকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। নৈতিকতার ক্ষেত্রে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কুধারণা থেকে দূরে থাকো এবং কোনো ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার অনুসন্ধান ছাড়াই কোনো দোষারোপ করোনা। আইনের ক্ষেত্রে এ মর্মে একটি স্থায়ী মূলনীতি স্থির করে দেয়া হয়েছে যে, নিছক সন্দেহ নীতি নির্দেশ করা হয়েছে। অনুমানের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার, মারধর বা জেলে আটক করা সম্পূর্ণ অবৈধ। বিজাতিদের সাথে আচার আচারণের ক্ষেত্রে নীতি নিধারণ করা হয়েছে যে, অনুসন্ধান ছাড়া কারো বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবেনা এবং নিছক সন্দেহের ভিত্তিতে কোনো গুজব ছাড়ানোও যাবেনা। শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যেসব তথাকথিত জ্ঞান নিছক আন্দাজ অনুমান এবং দীর্ঘসূত্রীতাময় ধারণা ও কল্পনা নির্ভর, সেগুলোকেও অপছন্দ করা হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে এই যে, আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ধারণা কল্পনা ও কুসংস্কারের মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে এবং ঈমানদারদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ্ ও রসূল প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রমাণেত বিষয় মেনে নেবার শিক্ষা দিয়া হয়েছে।
ধারা ১৪: এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীদের মতো আচরণ করোনা। এ নির্দেশটি ও ব্যক্তিগত কর্মপদ্ধতি ও জাতীয় আচরণ উভয়ের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এ নির্দেশের বদৌলতেই এ ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে মদীনা তাইয়েবায় যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তার শাসকবৃন্ত, গভর্নর ও সিপাহসালারদের জীবন ক্ষমতাহর্ব ও অহংকারের ছিটোফোটাও ছিলোনা। এমনকি যুদ্ধরত অবস্থায়ও কখনো তাদের সুখ থেকে দ্বন্দ্ব ও অহংকারের কোনো কথাই বের হতোনা। তাদের ওঠা বসা, চল চলন, পোশাক পরিচ্ছদ, ঘর বাড়ী,সওয়ারী ও সাধারণ আচার আচরণে বেশে কোনো শহরে প্রবেশ করতেন তখনও দর্প ও অহংকার সহকারে নিজেদের ভীতি মানুষের মনে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতেননা।
খ. রাষ্ট্রের শিক্ষা নীতির ব্যাপারে কুরআনে এই নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে যেঃ
“ আর মুমিনদের সবার এক সাথে বের হয়ে পড়ার কোনো দরকার ছিলোনা। কিন্তু তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে এলে ভালো হতো। তারা দীন সন্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতো এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করতো, যাতে তারা (অমুসলমানী আচরণ থেকে) বিরত থাকতো, এমনটি হলোনা কেন?” (সূরা তওবাঃ১২২)
এ আয়াতের অর্থ অনুধাবন করার জন্য এ সূরার ৯৭ আয়াতটি সামনে রাখতে হবে। তাতে বলা হয়েছেঃ
“মরুচারী আরবরা কুফরী ও মুনাফিকীতে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং আল্লাহ্ তাঁর রসূলের প্রতি যে দীন নাযিল করেছেন তার সীমারেখা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ হওয়ার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত বেশী।”
সেখানে শুধু এতোটুকু বলেই শেষ করা হয়েছেল যে, দারুল ইসলামের গ্রামীণ এলাকার বেশীরভাগ জনবসতি মুনাফিকী রোগে আক্রন্ত। কারণ এসব লোক অজ্ঞতার মধ্যে ডুবে আছে। জ্ঞানের কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ না থাকা এবং জ্ঞানবানদের সাহচর্য না পওয়ার ফলে এরা আল্লাহ্র দীনের সীমারেখা জানেনা। আর এখানে বলা হচ্ছে, গ্রামীণ জনবসতিকে এ অবস্থায় থাকতে দেয়া যাবেনা। বরং তাদের অজ্ঞতা দূর এবং তাদের সধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি করার জন্য এখন যথাযথ ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এ জন্য গ্রামীণ এলাকার সমস্ত আরব অধিবাসীদের নিজেরদের ঘর বাড়ী ছেড়ৈ মদীনায় জমায়েত হবার এবং এখানে বসে জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন নেই। বরং এই জন্য প্রয়োজন হচ্ছে প্রত্যেক গ্রাম, পল্লী ও গোত্র থেকে কয়েকজন করে লোক বের হবে। তার জ্ঞানের কেন্দ্রগুলো যেমন মদীনা ও মক্কা এবং এ ধরনের অন্যান্য জায়গায় আসবে। এখানে এসে তারা দীনের জ্ঞান আহরণ করেবে। এখানে থেকে তারা নেজেদের জনবসতিতে ফিরে যাবে এবং সাধারণ সানুষের মধ্যে দীনী চেতনা ও জগরণ সৃষ্টিতে তৎপর হবে।
এটি ছিলো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ। ইসলামী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও মজবূত করার জন্য সঠিক সময়ে এ নির্দেশটি দেয়া হয়েছিলো। শুরুতে ইসলাম যখন আরবে ছিলো একেবারেই নতুন এবং একটি চরম প্রতিকূল পরিবেশে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিলো তখন এ ধরনের নির্দেশের প্রয়োজন ছিলোনা। কারণ তখন যে ব্যক্তি ইসলামকে পুরোপুরি বুঝে নিতো এবং সব দিক দিয়ে তাকে যাচাই করে নিশ্চিন্ত হতে পারতো একমাত্র সেই ইসলাম গ্রহণ করতো। কিন্তু যখন এ আন্দোলন সাফল্যের পর্যায়ে প্রবেশ করলো এবং পৃথিবীতে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো তখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগলো এবং এলাকার পর এলাকা ইসলামের সুশীলতা ছায়াতলে আশ্রয় নিতে থাকলো। এ সময় খুব কম লোকই ইসলামের যাবতীয় চাহিদা ও দাবী অনুধাবন করে ভালোভাবে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে চলে আসছিলো। নতুন মুসলিম জনবসতির এ দ্রুত বিস্তার ব্যহ্যত ইসলামের শক্তিমত্তার কারণ ছিলো। কেননা, ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিলো। কিন্তু বাস্তবে এ ধরনের জনবসতিতে ইসলামী চেতনা ছিলোনা এবং এ ব্যবস্থার নৈতিক দাবি পূরণ করতেও তারা প্রস্তুত ছিলোনা। বস্তুত তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির সময় এ ক্ষতি সুস্পষ্ট আকারে সামনে এসে গিয়েছিল। তাই সঠিক সময়ে মহান আল্লাহ্ নির্দেশ দিলেন, ইসলামী আন্দোলনের বিস্তৃতির কাজ যে গতিতে চলছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তাকে শক্তিশালী ও সজবূত করার ব্যবস্থা করতে হবে। আর সে ব্যবস্থাটি হচ্ছে, প্রত্যেক এলাকার লোকদের মধ্যে থেকে কিছু লোককে নিয়ে শিক্ষা ও অনুশীলন দান করতে হবে, তারপর তারা প্রত্যেক নিজেদের এলাকায় ফিরে গিয়ে সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও অনুশীলনের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে সমগ্র মুসলিম জনবসতিতে ইসলামের চেতনা ও আল্লাহ্র বিধানের সীমারেখা সম্পর্কিত জ্ঞান ছড়িয়ে পড়বে।
এ প্রসংগে এতোটুকু কথা অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে যে, এ আয়াতে যে সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা করার হুকুম দেয়া হয়েছে তার আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে নিছক সাক্ষারতা সম্পন্ন করা এবং তাদের মধ্যে বইপত্র পড়ার মতো যোগ্যতা সৃষ্টি করা ছিলোনা। বরং লোকদের মধ্যে দীনের বোধ ও জ্ঞান সৃষ্টি করা এবং তাদেরকে অমুসলিম সূলভ জীবনধারা থেকে রক্ষা করা, সতর্ক ও সজ্ঞান করে তোলা এর আসল উদ্দেশ্য হিসেবে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হয়েছেল। এটিই মুসলমানদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। মহান আল্লাহ্ নিজেই চিরকালের জন্য এ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে যাচাই করতে হবে। দেখতে হবে এ উদ্দেশ্য সে কতোটুকু পূরণ করতে সক্ষম। এর অর্থ এ নয়, ইসলাম লোকদেরকে লেখা পড়া শেখাতে বই পড়তে সক্ষম করে তুলতে ও পার্থিব জ্ঞান দান করতে চায়না। বরং পড়া অর্থ হচ্ছে, ইসলাম লোকদের নির্ধারিত আসল উদ্দেশ্যের দিকে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নয়তো প্রত্যেক ব্যক্তি যদি তার যুগের আইনষ্টাইন ও ফ্রয়েড হয়ে যায় কিন্তু দীনের জ্ঞানের ক্ষিত্রে তারা শূণ্যের কোঠায় অবস্থান করে এবং অমুসলিম সূলভ জীরনধারায় বিভ্রান্ত হতে থাকে তাহলে ইসলাম এ ধরনের শিক্ষার ওপর অভিশাপ বর্ষণ করে।
এ আয়াতে উল্লেখিত বাক্যাংশটির ফলে পরবর্তীকালে লোকদের মধ্যে আশ্চর্য ধরনের ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়ে গেছে। মুসলমানরদের ধর্মীয় শিক্ষা বরং তাদের ধর্মীয় জীরনধারার ওপরও এর বিষময় প্রভাব দীর্ঘকাল থেকে মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ্ “তাফাক্কুহ্ ফীদ্ দীন” কে শিক্ষার উদ্দেশ্যে পরিণত করেছিলেন। এর অর্থ হচ্ছে, দীন অনুধাবন করা বা বুঝা, দীনের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করা , তার প্রকৃতি ও প্রাণশক্তির সাথে পরিচিত হওয়া এবং এমন যোগ্যতার অধিকারী হওয়া যার ফলে চিন্তা ও কর্মের সকল দিকে ও জীবনের প্রত্যেকটি বিভাগে কোন্ চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি ইসলামের প্রাণশক্তির অনুসারী তা মানুষ জানতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে যে আইন সম্পর্কিত জ্ঞান পরিভাষিক অর্থে ফিক্হ নামে পরিচিত হয় এবং যা ধীরে ধীরে ইসলামী জীরনের নিছক বাহ্যিক কাঠামোর (প্রাণশক্তির মুকাবিলায়) বিস্তারিত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে, লোকেরা শাব্দিক অভিন্নতার কারণে সেটিই সম্পূর্ণ উদ্দে্যে ও লক্ষ্য নয়। বরং তা ছিলো উদ্দেশ্য লক্ষ্যের একটি অংশ মাত্র। এ বিরাট ভুল ধারণার ফলে দীন ও তার অনুসারীদের যে ক্ষতি হয়েছে তা বিশ্লেষণ ও পর্যলোচনা করতে হলে একটি বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন। কিন্তু এখানে আমার এ সম্পর্কে সতর্ক করে দেবার জন্য সংক্ষেপে শুধুমাত্র এতোটুকু ইংগিত করছি যে, মুসলমাদের ধর্মীয় শিক্ষাকে যে জিনিসটি দীনি প্রাণশক্তি বিহীন করে নিছক দীনি কাঠমো ও দীনি আকৃতির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মধ্যে করে দিয়েছে এবং অবশেষে যার বদৌলতে মুসলমানদের জীবনে একটি নিছক প্রাণহীন বাহ্যিকতা দীনদারীর শেষ মনযিলে পরিণত হয়েছে তা বহুলাংশে এ ভুল ধারণারই ফল।
৮.নাগরিকত্ব ও পররাষ্ট্রনীতি
ক. “যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং আল্লাহ্র পথে নিজের জানমালের ঝুঁকি নিয়ে জিহাদ করেছে আর যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে, আসল তারাই পরস্পরের বন্ধু ও অভিভবক। আর যারা ঈমান এনেছে ঠিকই কিন্তু হিজরত করে (দারুল ইসলামে) আসেনি তারা হিজরত করে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের বন্ধুত্বের ও অভিভাবকত্বের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে হাঁ, দীনের ব্যাপারে যদি তারা তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের জন্য ফরয। কিন্তু এমন কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ্ তা দেখেন।” (সূরা আনফালঃ৭২)
এ আয়াতটি ইসলামের সাংবিধানিক আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা। এখানে একটি মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছে। সেটি হচ্ছে, “অভিভাবকত্বের”সম্পর্ক এমন সব মুসলমানদের মধ্যে স্থাপিত হবে যার দারুল ইসলামের বাসিন্দা অথবা বাইরে থেকে হিজরত করে দারুল ইসলামে এসেছে। আর যেসব মুসলমান ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে বাস করে তাদের সাথে অবশ্যি ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে, কিন্তু “অভিাভাবকত্বের” সম্পর্ক থাকবেনা। অনুরূপভাবে যেসব মুসলমান হিজরত করে দারুল ইসলামে আসবেনা বরং দারুল কুফরের প্রজা হিসেবে দারুল ইসলামে আসবে তাদের সাথেও এ সম্পর্ক থাকবেনা। অভিভাবকত্ব শব্দটিকে এখানে মূলে “ওয়ালায়াত” শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে। আরবীতে “ওয়ালায়াত” বলতে সাহায্য, সহায়তা, সমর্থন, পৃষ্ঠপোষকতা, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, নিকট আত্মীয়তা, অভিাভাবকত্ব এবং এ সবের সাথে সামঞ্জস্যশীল অর্থ বুঝায়। এ আয়াতের পূর্বাপর আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে এ থেকে এমন ধরনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে, যা একটি রাষ্ট্রের তার নাগরিকদের সাথে, নাগরিকদের নিজেদের রাষ্ট্রের সাথে এবং নাগরিকদের নিজেদের মধ্যে বিরাজ করে। কাজেই এ আয়তটি “সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব” কে ইসলামী রাষ্ট্রের ভূখন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেয়। এ সীমানার বাইরের মুসলমানদেরকে এ বিশেষ সম্পর্কের বাইরে রাখে। এ অভিভাবকত্ব না থাকার আইনগত ফলাফল অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। উদাহরণ হিসেবে শুধুমাত্র এতোটুকু ইংগিত করাই যথেষ্ট হবে যে, এ অভিভাবকত্বহীনতার ভিত্বিতে দারুল কুফর ও দারুল ইসলামের মুসলমানরা পরস্পরের উত্তরাধিকারী হতে পারেনা এবং তারা একজন অন্যজনের আইনানুগ অভিভাবক(Guarduan) হতে পারেনা, পরস্পরের মধ্যে বিয়ে শাদী করতে পারেনা এবং দারুল কুফরের সাথে নাগরিকত্বের সম্পর্ক ছিন্ন করেনি এমন কোনো মুসলমানকে ইমলামী রাষ্ট্র নিজেদের কোনো দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করতে কোনো মুসলমানকে ইসলামী রাষ্ট্র নিজেদের কোনো দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠত করতে পারেনা। ১.তাছাড়া এ আয়াতটি ইসলামী রাষ্টের বিদেশ নীতির ওপরও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে। এর দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যেসব মুসলমান অবস্থান করে তাদের দায়িত্বই ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়। বাইরের মুসলমানদের কোনো দায়িত্ব ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর বর্তায়না। একথাটিই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিন্মোক্ত হাদীসে বলেছেনঃ[ ১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন লেখেকের “রাসায়েল ও মাসায়েল” ২য় খন্ডের “দারুল ইসলাম ও দারুল কুফরে মুসলমানদের মধ্যে উত্তরাধিকার ও বিয়ে-শাদীর সম্পর্ক নিবন্ধকটি।–অনুবাদক]
“আমার ওপর এমন কোনো মুসলমানের সাহায্য সমর্থন ও হিফাযতের দায়িত্ব নেই যে মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে।”
এভাবে সাধারণত যেসব বিবাদের কারণে আন্তর্জাতিক জটিলতা দেখা দেয়, ইসলামী আইন তার শিকড় কেটে দিয়েছে। কারণ যখনই কোনো সরকার নিজের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে অবস্থানকারী কিছু সংখ্যালঘুর দায়িত্ব নিজের মাথায় নিয়ে নেয় তখনই এর কারণে এমন সব জটিলতা দেখা দেয়, বার বার যুদ্ধের পরও যার কোনো মীমাংসা হয়না।
এ আয়াতে দারুল ইসলামের বাইরে অবস্থানকারী মুসলমানদের “রাজনৈতিক অভিভাবকত্বের” সম্পর্ক মুক্ত গণ্য করা হয়েছেল। এখন এ আয়তটি বলছে যে, তারা এ সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করা সত্ত্বেও “ইসলামী ভ্রাতৃত্বের” সম্পর্কের বাইরে অবস্থান করছেনা। যদি কোথাও তাদের ওপর যুলুম হতে থাকে এবং ইসলামী ভ্রাতৃ সমাজের সাথে সম্পর্কের কারণে তারা দারুল ইসলামের সরকারের ও তার অধিবাসীদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে নিজেদের এ মযলূম ভাইদের সাহায্য করা তাদের জন্য ফরয হয়ে যাবে। কিন্তু এরপর আরো বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে, চোখ বন্ধ করে এসব দীনি ভাইয়ের সাহায্য করা যাবেনা। বরং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আরোপিত দায়িত্ব ও নৈতিক সীমারেখার প্রতি নযর রেখেই এ দায়িত্ব পালন করা যাবে। যুলুমকারী জাতির সাথে যদি ইসলামী রাষ্ট্রের চুক্তমূলক সম্পর্ক থাকে তাহলে এ অবস্থায় এ চুক্তর নৈতিক দায়িত্ব ক্ষুন্ন করে মযলূম মুসলমানদের কোনো সাহায্য করা যাবেনা।
আয়াতে চুক্তির জন্য “মীসাক” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর মূল হচ্ছে “ওসূক”। এর মানে আস্থা ও নির্ভরতা। এমন প্রত্যেকটি জিনিসকে “মীসক” বলা হবে, যার ভিত্তিতে কোনো জাতির সাথে আমাদের সুস্পষ্ট ‘যুদ্ধ নয়’ চুক্তি না থাকলেও তারা প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের ও তাদের মধ্যে কোনো যুদ্ধ নেই এ ব্যাপারে যথার্থ আস্থাশীল হতে পারে।
তারপর আয়াতে বলা হয়েছেঃ “যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে।” এ থেকে পরিষ্কর জানা যাচ্ছে, ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার কোনো অমুসলীম সরকারের সাথে যে
চুক্তি স্থাপন করে তা শুধুমাত্র দু’টি সরকারের মধ্যকার সম্পর্ক নয় বরং দু’টি জাতির সম্পর্কও এবং মুসলমান সরকারের সাথে সাথে মুসলিম জাতি ও তার সদস্যরাও এর নৈতিক দায়িত্বির অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। মুসলিম সরকার অন্য দেশ বা জাতির সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে ইসলামী শরীয়ত তার নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুসলিম জাতি বা তার ব্যক্তিবর্গকে মুক্ত থাকাকে আদৌ বৈধ গণ্য করেনা। তবে দারুল ইসলাম সরকারের চুক্তিগুলো মেনে চলার দায়িত্ব একমাত্র তাদের ওপর বর্তাবে যারা এ রাষ্ট্রের কর্মসীমার মধ্যে অবস্থান করবে। এ সীমার বাইরে বসবাসকারী সারা দুনিয়ার মুলসমানরা কোনোক্রমেই এ দায়িত্ব শামিল হবেনা। এ কারণেই হুদাইবিয়ায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফিরদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন হযরত আবু বসীর ও আবু জান্দাল এবং অন্যান্য মুসলমানদের ওপর তার কোনো দায়িত্ব অর্পিত হয়নি, যারা মদীনার দারুল ইসলামের প্রজা ছিলেননা।
খ. “আর যদি কখনো কোনো জাতির পক্ষ থেকে তোমাদের খিয়ানতের আশংকা থাকে তাহলে তার চুক্তি প্রকাশ্যে তার সামনে ছুঁড়ে দাও।” (সূরা আনফালঃ ৫৮)
এ আয়াতের দৃষ্টিতে যদি কোনো ব্যক্তি, দল বা দেশের সাথে আমাদের চুক্তি থাকে এবং তার কর্মনীতি আমাদের মনে তার বিরুদ্ধে চুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে গড়িমসি করার অভিযোগ সৃষ্টি করে অথবা সুযোগ পেলেই সে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এ ধরনের আশংকা দেখা দেয়, তাহলে আমাদের পক্ষে একতরফাভাবে এমন সিদ্ধান্ত করা কোনোক্রমেই বৈধ নয় যে, আমাদের ও তার মধ্যে কোনো চুক্তি নেই। আর এই সংগে হঠাৎ তার সাথে আমাদের এমন ব্যবহার করা উচিত নয় যা একমাত্র চুক্তি না থাকা অবস্থায় করা যেতে পারে। বরং এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হলে কোনো বিরোধীতামূলক কর্যক্রম গ্রহণ করার আগে দ্বিতীয় পক্ষকে স্পষ্টভাষায় একথা জানিয়ে দেবার জন্য আমাদের তাগিদ দেয়া হয়েছে যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এখন আর কোনো চুক্তি নেই। এভাবে চুক্তি ভংগ করার জ্ঞান আমরা যতটুকু অর্জন করেছি তারও ততটুকু অর্জন করতে পারবে এব চুক্তি এখনো অপরিবর্তিত আছে, এ ধরনের ভুল ধারণা তারা পোষণ করবেনা। আল্লাহ্র এ ফরমান অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিন্মোক্ত স্থায়ী মুলনীতি ঘোষণা করেছিলেনঃ
“কোনো জাতির সাথে কারোর কোনো চুক্তি থাকলে মেয়াদ শেষ হবার আগে তার চুক্তি লংঘন করা উচিত নয়। এক পক্ষ চুক্তি ভংগ করলে উভয় পক্ষের সমতার ভিত্তিতে অপর পক্ষ চুক্তি বাতিল করার কথা জানাতে পারে।”
তারপর এ নিয়মকে তিনি আরো একটু ব্যাপকভিত্তিক করে সমস্ত ব্যাপারে এ সাধারণ নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন “যে ব্যক্তি তোমার সাথে খিয়ানত ও বিশ্বাসঘাতকতা করে তুমি তার সাথে খিয়ানত করোনা” এ নীতিটি শুধুমাত্র বক্তৃতা বিবৃতিতে বলার ও বইয়ের পাতার শোভা বর্ধনের জন্য ছিলোনা বরং বস্তব জীবনে একে পূরাপূরি মেনে চলা হতো। আমীর মু’য়াবীয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু একবার নিজের রাজত্বকালে রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তে সেনা সমাবেশ করতে শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার সাথে সাথেই অতর্কিতে রোমান এলাকায় আক্রমণ চালাবেন। তাঁর এ পদক্ষেপের বিরুদ্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আমর ইবনে আনবা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু কঠোর প্রতিবাদ জানান। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি শুনিয়ে চুক্তির মেয়াদের মধ্যেই এ ধরনের শত্রুতামূলক কর্যকলাপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন। অবশেষে আমীর মু’য়াবিয়াকে এই নীতির সামনে মাথা নোয়াতে হয় এবং তিনি সীমান্ত সৈন্য সমাবেশ বন্ধ করে দেন।
একতরফাভাবে চুক্তি ভংগ ও যুদ্ধ ঘোষণা করা ছাড়া আক্রমণ করার পদ্ধতি প্রচীন জাহিলী যুগেও ছিলো এবং বর্তমান যুগের সুসভ্য জাহিলিয়াতেও এর প্রচলন আছে। এর নতুনতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিগত দ্বিতিয় মহাযুদ্ধে রাশিয়ার ওপর জার্মানীর আক্রমণ এবং ইরানের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও বৃটেনের সামরিক কার্যক্রম। সাধারণত এ ধরনের কার্যক্রমের সপক্ষে ও ওযর পেশ করা হয় যে, আক্রমণের পূর্বে জনিয়ে দিলে প্রতিপক্ষ সতর্ক হয়ে যায়। এ অবস্থায় কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতার সন্মুখীন হতে হয় অথবা যদি আমরা অগ্রসর হয়ে হস্তক্ষেপ না করতাম তাহলে আমাদের শত্রুরা সুবিধা লাভ করতো। কিন্তু নৈতিক দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এ ধরনের বাহানাকে যদি যথিষ্ট মনে করা হয় তাহলে দুনিয়ায় আর এমন কোনো অপরাধ থাকেনা যা কোনো না কোনো বাহানায় করা যেতে পারেনা। প্রত্যেক চোর, ডাকাত, ব্যভিচারী, ঘাতক ও জালিয়াত নিজের অপরাধের জন্য এমনি ধরনের কোনো না কোনো কারণ দর্শাতে পারে। অথচ মজার ব্যাপার হচ্ছে, আন্তর্জাতিক পরিবেশে এরা একটি জাতির জন্য এমন অনেক কাজ বৈধ মনে করে যা জাতীয় পরিবেশে কোনো ব্যক্তি করলে তাদের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে গণ্য হয়।
এ প্রসংগে একথা জেনে নেয়ারও প্রয়োজন রয়েছে যে, ইসলামী আইন শুধুমাত্র একটি অবস্থায় পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই আক্রমণ করা বৈধ গণ্য করে। সে অবস্থাটি হচ্ছে, দ্বিতীয় পক্ষ যখন ঘোষণা দিয়েই চুক্তি ভংগ করে এবং আমাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রুতামূলক কাজ করে। এহেন অবস্থায় উল্লেখিত আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের পক্ষ থেকে তার কাছে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেবার প্রয়োজন হয়না। বরং আমরা অঘোষিতভাবে তার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার অধিকার লাভ করি। বনী খুযায়ার ব্যাপারে কুরাইশরা যখন হুদাইবিয়ার চুক্তি প্রকাশ্যে বংগ করে তখন নবী সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে চুক্তি ভংগ করার নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি এবং কোনো প্রকার ঘোষণা না দিয়েই মক্কা আক্রমণ করে বসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কার্যক্রম থেকেই মুসলিম ফকীহগণ এ ব্যতিক্রমধর্মী বিধি রচনা করেছেন। কিন্তু কোনো অবস্থয় যদি আমরা এ ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম থেকে ফায়দা উঠাতে চাই তাহলে অবশ্যি সেই সমস্ত অবস্থা আমাদের সামনে থাকতে হবে যে অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। এভাবে তাঁর সমগ্র কার্যক্রমের একটি সুবিধাজনক অংশ মাত্রের অনুসরণ না করে তার সবটুকু অনুসরণ করা হবে। হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো থেকে যা কিছু প্রমাণিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরুপঃ
এক. কুরইশদের চুক্তি ভংগের ব্যাপারটি এতো বেশী সুস্পষ্ট ছিলো যে, চুক্তি ভংগ করেছে এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করার কোনো সুযোগ ছিলোনা। কুরাইশরা এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্টি লোকেরা নিজেরাও চুক্তি যথার্থই ভেংগে গেছে বলে স্বীকার করতো। তারা নিজেরাই চুক্তি নবায়ণের জন্য আবু সুফিয়ানকে সদীনায় পাঠিয়েছিল। এর পরিষ্কার অর্থ ছিলো, তাদের দৃষ্টিতেও চুক্তি অক্ষুন্ন ছিলোনা। তবুও চুক্তি ভংগকারী জাতি নিজেই চুক্তি ভংগ করার স্বীকার করবে, এটা জরুরী নয়। তবে চুক্তি ভংগ করার ব্যাপারটি একেবারে সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীত হওয়া অবশ্যি জরুরী। দুই. কুরাইশদের পক্ষ থেকে চুক্তি ভংগ করার পরও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে বা ইশারা ইংগিত এমন কোনো কথা বলেননি যা থেকে এ ইশারা পাওয়া যায় যে, এ চুক্তি ভংগ করা সত্ত্বেও তিনি এখনো তাদেরকে একটি চুক্তিবদ্ধ জাতি মনে করেন এবং এখনো তাদের সাথে তাঁর চুক্তিমূলক সম্পর্ক বজায় রয়েছে বলে মনে করেন। সমস্ত বর্ণনা একযোগে একথা প্রমাণ করে যে, আবু সুফিয়ান যখন মদীনায় এসে চুক্তি নবায়ণের আবেদন করে তখন তিনি তা গ্রহণ করেননি।
তিন. তিনি নিজে কুরাইশদের বিরুদ্ধে সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করেন এবং প্রকাশ্যে গ্রহণ করেন। তাঁর কার্যক্রমে কোনো প্রকার প্রতারণার সামান্যতম গন্ধও পাওয়া যায়না। তিনি বাহ্যত সন্ধি এবং গোপনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেননি।
এটিই এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম আদর্শ। কাজেই ওপরে উল্লেখিত আয়াতের সাধারণ বিধান থেকে সরে গিয়ে যদি কোনো কার্যক্রম অবলম্বন করা যেতে পারে তাহলে তা এমনি বিশেষ অবস্থায়ই করা যেতে পারে এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের সরল সহজ ভদ্রজনোচিত পথে তা করেছিলেন তেমনি পথেই করা যেতে পারে।
তাছাড়া কোনো চুক্তিবদ্ধ জাতির সাথে কোনো বিষয়ে যদি আমাদের কোনো বিবাদ সৃষ্টি হয়ে যায় এবং আমরা দেখি পারস্পরিক আলাপ আলোচনা বা আন্তর্জাতিক শালিশের মাধ্যমে এ বিবাদের মীমাংসা হচ্ছেনা অথবা যদি আমরা দেখি, দ্বিতীয় পক্ষ বল প্রয়োগ করে এর মীমাংসা করতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে আমাদের জন্য বল প্রয়োগ করে মীমাংসায় পৌছানো সম্পুর্ণরূপে বৈধ হয়ে যাবে। কিন্তু উপরোক্ত আয়াতে আমাদের ওপর এ নৈতিক দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে যে, আমাদের এ বল প্রয়োগ পরিষ্কার ও দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর হতে হবে এবং তা হতে হবে প্রকাশ্যে। লুকিয়ে গোপণে এমন ধরনের সামরিক কার্যক্রম গ্রহণ করা যার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে আমরা প্রস্তুত নই, একটি অসদাচার ছাড় আর কিছুই নয়। ইসলাম এর শিক্ষা আমাদের দেয়নি।
গ. “কাজেই এ লোকদের যদি তোমরা যুদ্ধের মধ্যে পাও তাহলে তাদের এমনভাবে মার দেবে যেনো তাদের পরে অন্য যারা এমনি ধরনের আচরণ করতে চাইবে তারা দিশা হারিয়ে ফেলে। আশা করা যায়, চুক্তি ভংগকারীদের এ পরিণাম থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।” (সূরা আনফালঃ ৫৭)
এর অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো জাতির সাথে আমাদের চুক্তি হয়, তারপর তারা নিজেদের চুক্তির দায়িত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে আমরাও চুক্তির নৈতিক দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবো। এ ক্ষেত্রে আমরাও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ন্যায়সংগত অধিকার লাভ করবো। তাছাড়া যদি কোনো জাতির সাথে আমাদের যুদ্ধ চলতে থাকে এবং আমরা দেখি, শত্রুপক্ষের সাথে এমন এক সম্প্রদায়ের লোকেরাও যুদ্ধে শামিল হয়েছে যাদের সাথে আমাদের চুক্তি রয়েছে তাহলে আমরা তাদেরকে হত্যা করতে এবং তাদের সাথে শত্রুর মতো ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করবোনা। কারণ তারা ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের সম্প্রদায়ের চুক্তি ভংগ করে তাদের ধন প্রাণের নিরাপত্তার প্রশ্নে তাদের সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের যে চুক্তি রয়েছে তা লংঘন করেছে। ফলে নিজেদের নিরাপত্তার অধিকার তারা প্রমাণ করতে পারেনি।
ঘ. “আর হে নবী, শত্রু যদি সন্ধি ও শান্তির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তুমিও সেদিকে ঝুঁকে পড়ো এবং আল্লাহ্র প্রতি নির্ভর করো। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। যদি তারা তোমাকে প্রতারিত করতে চায় তাহলে তোমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট।” (সূরা আনফালঃ ৬১-৬২)
অর্থাৎ আন্তর্জাতিক বিষয়াদিতে তোমাদের কাপুরুষোচিত নীতি অবলম্বন করা উচিত নয়। বরং আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে নির্ভীক ও সাহসী নীতি অবলম্বন করা উচিত। শত্রু সন্ধির কথা আলোচনা করতে চাইলে নিসংকোচে তার সাথে আলোচনার টেবিলে বসে যাবার জন্য তৈরী থাকা প্রয়োজন। সে সদুদ্দেশ্যে সন্ধি করতে চায়না বরং বিশ্বাসঘাতকতা করতে চায়, এ অজুহাত দেখিয়ে তার সাথে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করোনা। কারোর নিয়ত নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভবপর নয়। সে যদি সত্যিই সন্ধি করার নিয়ত করে থাকে তাহলে অনর্থক তার নিয়তের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে রক্তপাতকে দীর্ঘায়িত করবে কেন? আর যদি বিশ্বাসঘাতকতা করার নিয়ত করে থাকে তাহলে তোমাদের আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে সাহসী হওয়া দরকার। সন্ধির জন্য যে হাত এগিয়ে এসেছে তার জবাবে হাত বাড়িয়ে দাও। এর ফলে তোমাদের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হবে। আর যুদ্ধ করার জন্য যে হাত উঠবে নিজের তেজস্বী বাহু দিয়ে তাকে ভেংগে গুঁড়ো করে দাও। এভাবে সমুচিত জবাব দিতে পারলে কোনো বিশ্বাসঘাতক জাতি আর তোমাদের ননীর পুতুল মনে করার দুঃসাহস দেখাবেনা।
উপরোক্ত পৃষ্ঠগুলোতে যেসব আয়াত এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে, তা কুরআনের রাজনৈতিক দর্শন ও ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান নীতিমালাকে পরিস্ফুট করে। কুরআন মানব জীবনের এই বিভাগ সম্পর্কে স্পষ্ট পথ নির্দেশনা দান করেছ। মুসলমানদের কর্তব্য হলো, নিজেদের যাবতীয় সামাজীক কার্যক্রম এগুলোর ভিত্তিতে পরিচালনা করা। কেবল এভাবেই তারা নিজেদের দীন ও ঈমানের দাবী পূরণে সক্ষম হবে।
পিডিএফ লোড হতে একটু সময় লাগতে পারে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে এখানে ক্লিক করুন।
দুঃখিত, এই বইটির কোন অডিও যুক্ত করা হয়নি