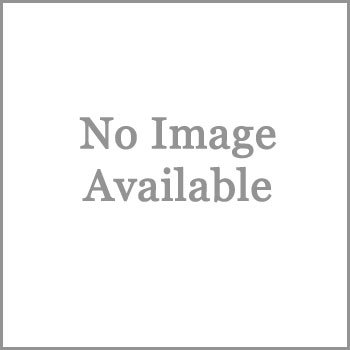১.
‘বঙ্গভঙ্গ’ (১৯০৫) এবং ‘বঙ্গভঙ্গ রদ’ (১৯১১) শব্দদ্বয় নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের অবকাশ আছে, যথেষ্ট পরিমাণে বিতর্কের সুযোগও রয়েছে। একইভাবে ‘বঙ্গভঙ্গ’ এবং ‘বঙ্গভঙ্গ রদ’ নামক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ভিন্ন ভিনণ পর্যালোচনা এবং উপসংহার প্রণীত হওয়াও খুবই স্বাভাবিক।
এটা ঠিক যে, তৎকালীন বঙ্গের রাজধানী কলকাতা থেকে বঙ্গকে বিভক্ত করে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ব বঙ্গ ও আসামকে নিয়ে আলাদা স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা তাদের জন্য ‘বঙ্গভঙ্গ’ বটে। যেজন্য তারা ১৯০৫ সালের এ বিভক্তিকে মেনে নিতে পারেন নি এবং কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের স্বার্থ হানি হয়েছে বিধায় হিন্দু ধর্মাশ্রিত তীব্র ধর্মান্ধ ও সাম্প্রদায়িক-সন্ত্রাসবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করাতে সমর্থ হন। তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল: বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে কলকাতা থেকে ঢাকায় রাজধানী করে নতুন প্রদেশ হতে না দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতা থেকে সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে বলা হয়েছে:
‘‘বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের স্মৃতি আজও বাঙালি (সমগ্র বাঙালি জাতিসত্তা নয়, হিন্দু বাঙালি পড়তে হবে) গর্ব ভরে মনের মধ্যে লালন করে। বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গরদ কেন্দ্রিক আন্দোলন শুধুমাত্র প্রতিবাদী ছিল না, এর সঙ্গে ছিল আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী আকাঙ্ক্ষা। এই অধ্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বাঙালি পরিচালিত ব্যাঙ্ক, স্বদেশী ভান্ডার, হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসুওরেন্স, বাঙালি পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র। সর্বোপরি বাঙালি পেয়েছিল জাতীয় চেতনা ও জাতীয় বিদ্যালয়। বাংলার শিল্প-সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রভাব অভূতপূর্ব। আবেগ ও মননের যৌথ সন্মিলনে, শিল্প-সাহিত্যের উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি তা আন্দোলনকে বেগবান করতেও সাহায্য করেছিল। সাহিত্যের প্রতিটি শাখা, গান, নাটক, চিত্রকলার অনন্য সৃষ্টিময়তা দীর্ঘ বিংশ শতাব্দীর সৃষ্টি সাধনকে প্রভাবিত করেছে, পুষ্ট করেছে।’’
অর্থাৎ প্রতিটি কাজই হয়েছে কলকাতাকে ও হিন্দু-বাঙালিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য এবং ঢাকাকে এবং পূর্ববঙ্গে মুসলিম-বাঙালি অধিকারের গলা টিপে ধরবার জন্য।
কিন্তু আজকের বাংলাদেশের দিক থেকে সমগ্র বিষয়টির ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে নতুন রাজধানী ও প্রদেশ প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে ‘বঙ্গভঙ্গ’ বলার যৌক্তিকতা খুব বেশি স্পষ্ট নয়। বরং মধ্যযুগের সুলতানি আমলের সোনারগাঁ এবং মুঘল আমলের ঢাকা থেকে ঔপনিবেশিক ইংরেজরা যে রাজধানীকে সরিয়ে নিয়ে নতুন রাজধানী কলকাতা তৈরি করেছিল, সেটা প্রায় দুই শ বছর পর আবার ঢাকাতেই ফিরে এসেছিল। ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত যে সময়কালকে বঙ্গভঙ্গ ও বঙ্গভঙ্গ রদের নামে কলকাতায় হিন্দু-বাঙালি জাতীয়তাবাদের জঙ্গি ও ধর্মান্ধ-সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ও আবেগে ঢেকে রেখেছে, সে সময়কালটিই ঢাকার জন্য রাজধানীর গৌরববহ এবং উন্নয়ন, অগ্রগতি ও সচেতনতা বৃদ্ধির স্মারকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। অতএব, ঢাকা বা পূর্ব বঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশের দিক থেকে ১৯০৫-১৯১১ সময়কালকে বঙ্গভঙ্গ বলা উচিত, নাকি স্বাধীন বিকাশের পর্যায় বলা ভালো, সেটাও বিবেচনা করে দেখা দরকার। কলকাতার জন্য যা বঙ্গভঙ্গ, ঢাকার জন্য সেটা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন, জনগণের ক্ষমতা মূল ভূখন্ডে ফিরে আসা, যা ছিল কলকাতার ইংরেজ ও তাদের স্থানীয় দোসর-জমিদারদের হাতে বন্দি। বঙ্গভঙ্গ যে আসলে একটি আবেগের ফানুস এবং কলকাতাওয়ালাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার আবেগি-রাজনৈতিক স্লোগান, সে প্রমাণও রয়েছে। যারা ১৯০৫ সালে বাংলা ভাগ হল বলে রক্ত ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিল, তারাই ১৯৪৭ সালে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার মাধ্যমে হিন্দুত্বের স্বার্থে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গেছে। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলে কোন কিছুকেই তারা স্বীকারও করলেন না: তারা নিজেদেরকে পরিচিত ও সনাক্ত করলেন প্রথমে হিন্দু এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় হিসাবে। শেষ পর্যন্ত বাংলার অস্তিত্বকে রক্ষা করতে ঢাকাকেই এগিয়ে আসতে হয়, যার ধারাবাহিকতার ফল আজকের বাংলাদেশ। ফলে কলকাতা বা ভারতীয় হিন্দু-বাঙালির কাছে ১৯০৫ সালের ঘটনাবলী তথাকথিত বঙ্গভঙ্গ হলেও বাংলাদেশের জন্য স্বদেশে, স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তনই। বস্তত, ঢাকায় রাজধানী স্থাপন করে বাংলাকে ভাগ করে (যার মধ্যে আসাম, উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশও যুক্ত ছিল) নতুন প্রদেশ স্থাপনের ঘটনা এবং এর বিরোধিতার মধ্য দিয়ে সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণেই সম্ভব হয়েছিল বাঙালি-মুসলিম জাতিসত্তার বিকাশ আর মানসিক-রাজনৈতিক ভিত্তি রচিত হয়েছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্র কাঠামোর। ফলে বাংলাদেশ ও এর অন্তর্গত জাতিসত্তার জন্য ১৯০৫ এবং ১৯১১-এর ঘটনাবলী খুবই শিক্ষণীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ।
প্রসঙ্গত, ‘বঙ্গভঙ্গ’ ও ‘বঙ্গভঙ্গ-রদ’-এর মতো একই ধরনের শব্দগত সমস্যা দেখা যায় ১৯৪৭ প্রসঙ্গেও। সাধারণভাবে এবং ব্যাপক ব্যবহারে বলা হয় ‘১৯৪৭-এর দেশভাগ’ শব্দটি। ‘দেশভাগ যথাযথ’ নাকি ১৯৪৭ সালে দুই’শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ‘উপমহাদেশ তথা পাকিস্তান ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ’ বলাটা যৌক্তিক? এখানেও দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গটি এসে যায় এবং পার্থক্যটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়।
তার মানে কি, যখন ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা পায়, তখন ‘বঙ্গভঙ্গ’ হয়ে যায়? আর যখন বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তিকে সরিয়ে উপমহাদেশের স্বাধীনতা লাভ হয়, তখন ‘দেশভাগ’ হয়ে যায়?
২.
১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে তথাকথিত বলে উল্লেখের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তথাকথিত এই জন্য যে, বাংলাকে ভাগ শুধু ১৯০৫ সালেই যে হয়েছে, তা নয়। ১৯০৫ সালের আগেও বাংলা ভেঙে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছে। তখন বাংলা বিভক্ত হয় নি? যখন ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন একটি প্রদেশ হল তখন বাংলা বিভক্ত হয়ে গেল? ইতিহাসের দিকে তাকালে এই ফাঁক ও ফাঁকিটুকু ধরা পড়বে।
১৮৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলা, বিহার ,উড়িষ্যা ও আসাম ‘বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি’র অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ বছরই আসামকে চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসাবে পৃথক করা হয়। এমন কি, বাংলা ভাষাভাষি সিলেট জিলাকেও আসামের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। তখন কিন্তু বাংলার অঙ্গচ্ছেদ ঘটছে মর্মে রাজধানী কলকাতা থেকে টু শব্দটিও উচ্চারিত হয় নি। একই রহস্যজনক নিশ্চুপ দেখতে পাওয়া যায় কলকাতা ও তার বিচক্ষণ অধিবাসীদেরকে ১৯৪৭ সালেও। বরং তখন তাদের কণ্ঠস্বর ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতাত্মক।
ইতিহাসে ১৮৭৪-এর মতো দেখি যে, ১৮৯৭ সালে ‘বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি’র অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চলও আসামের নিকট হস্তান্তর করা হয়। আশ্চর্যজনকভাবে কলকাতা তখনও নিশ্চুপ। এগুলো কোন ভাগ-বিভক্তি-অঙ্গহানি নয়? ভাগটা ঢাকা এবং পূর্ববঙ্গ, আরো স্পষ্ট ভাষায় মুসলমানদের পক্ষে হলেই যত বিপত্তি, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ আর হট্টগোল!
বস্ত্তত, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যাতায়াত সমস্যা এবং প্রদেশের অন্তর্গত প্রশাসনিক ব্যবস্থার উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব বাংলার বিস্তৃর্ণ এলাকা দীর্ঘ দিন যাবত অবহেলিত ছিল। পূর্ব বাংলা ও আসামের জনগণের সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য মূলত প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসাবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং মালদহ জিলাকে চিফ কমিশনার শাসিত আসামের সঙ্গে যুক্ত করে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ নামের একটি নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। আর তখনই শুরু হয় বাংলার রাজনীতিতে অর্থনৈতিকভাবে সুবিধাভোগী হিন্দু উচ্চশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক, ধর্মান্ধ ও সশস্ত্র-সন্ত্রাসবাদী প্রতিরোধ আন্দোলন।
৩.
মূলত বাংলার পূর্বাঞ্চলের পশ্চাৎমুখীতার সূচনা ঢাকা থেকে বৃহৎ বঙ্গের কেন্দ্রীয় রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমেই হয়েছিল। ১৭০০ থেকে ১৭২৭ পর্যন্ত বাংলার দেওয়ান এবং পরে দেওয়ান ও সুবাদার ছিলেন মুর্শিদ কুলি খান। তিনি ঢাকা থেকে নতুন স্থাপিত শহর মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ঢাকা থেকে রাজধানী স্থানান্তরের কারণ সমূহের মধ্যে একটি ছিল--‘‘প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য মুর্শিদাবাদের তুলনায় ঢাকা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ছিল না এবং মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের অত্যাচার কমে যাওয়ায় প্রশাসনিক ও সামরিক দিক থেকে ঢাকার গুরুত্ব অনেক কমে যায়।’’ এই বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয় এবং এটাই রাজধানী সরানোর প্রধান কারণ ছিল না। কারণ সুবেদার মুর্শিদ কুলি খান ক্রমশ নিজের ক্ষমতা দৃঢ় করছিলেন এবং দিল্লির দুর্বল কর্তৃত্বের কারণে নিজেকে স্বাধীন নৃপতিতে পরিণত করতে সচেষ্ট ছিলেন। যে কারণে তাঁর নিজস্ব পরিকল্পনায় একটি নতুন শক্তিকেন্দ্র ও রাজধানী প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। যারই বহিঃপ্রকাশে ঢাকা থেকে সরে আসা এবং মুর্শিদাবাদের জন্ম। এর প্রমাণ হলো এটাই যে:
‘‘মুর্শিদ কুলি খাঁন তাঁর সঙ্গে ঢাকার সমস্ত উচ্চ পদস্থ রাজস্ব কর্মচারী, সম্পদশালী ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্কারদেরকেও নিয়ে আসেন এবং তাঁরা স্থায়ীভাবে মুর্শিদাবাদে বসতি স্থাপন করেন। বহু সংখ্যক প্রশাসনিক কর্মচারী, অফিসার, কেরানী, পিয়ন ও অন্যান্য সহকারীসহ সেক্রেটারিয়েট স্থানান্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাজধানী (তথা ক্ষমতা কেন্দ্র) পরিবর্তন ভূম্যাধিকারী, ব্যবসায়ী ও রাজধানীর উপর নির্ভরশীল সব শ্রেণীকে এ অঞ্চল থেকে মুর্শিদাবাদমুখী করে তোলে। (পরবর্তীতে) ইংরেজ কোম্পানির অধীনে কলকাতায় রাজধানী স্থাপন ও পরবর্তীকালে কলকাতাকেন্দ্রিক অগ্রগতি হওয়ায় বাংলার পূর্বাঞ্চলীয় জিলাগুলো অধিকতর অবহেলিত হতে থাকে।’’
পরবর্তীতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি-শিল্প-অর্থনীতির শ্বাস নিঙড়ে, কোটি কোটি পূর্ববঙ্গবাসীর কঙ্কাল-করোটি দিয়ে পত্তন করল কৃত্রিম শহর কলকাতা। ইংরেজ বণিক জব চার্নক তৃতীয়বার সুতানুটীর ঘাটে অবতরণ করেন ১৬৯০ সালের ২৪ আগস্ট। এই জায়গাটি কৌশলগত কারণে আগেই তার খুব পছন্দ হয়েছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পৌত্র ঢাকার সুবাদার শাহজাদা মুহাম্মদ আজিমুদ্দিনের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা ১৬৯৮ সালের জুলাই মাসে স্থানীয় সাবর্ণ চৌধুরীর কাছ থেকে সুতানটী-কলকাতা-গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ১৩০০ টাকার বিনিময়ে ইজারা নেয়। ইজারা লাভের মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে ইংরেজরা কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গ গড়ে তোলে। এ সম্পর্কে নারায়ণ দত্ত লিখেছেন:
‘‘জন্মের সেই পরম লগ্নেই কলকাতার অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির মানুষ এক অসুস্থ খেলায় মেতেছিল। তাতে স্বার্থবুদ্ধিই একমাত্র বুদ্ধি, দুর্নীতিই একমাত্র নীতি, ষড়যন্ত্রের চাপা ফিসফিসানিই একমাত্র আলাপের ভাষা।’’
নতুন পরিস্থিতিতে ঢাকা যখন মৃত্যুর পথে আর মুর্শিদাবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজছে, তখন অতি সন্তর্পণে কলকাতায় বসে ইংরেজরা নিজেদের প্রস্ত্তত করতে থাকে এবং তাদের স্থানীয় দোসর হিন্দুদের নিয়ে পাকাপোক্ত শাসন-শোষণ পরিচালনা করতে শুরু করে। শোষক শ্রেণী বাংলার তাঁত ও বস্ত্র শিল্প ধ্বংস করে। গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙে দেয়। কলকাতার আশেপাশে কলকারখানা আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে পূর্ববঙ্গকে শোষণ করে। পরে এখানে ঘাঁটি তৈরি করে জমিদারগণ, যারা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে ইংরেজদের কাছ থেকে ক্ষমতার ভাগ পায়। পূর্ববঙ্গের ভূমি রাজস্ব সংগ্রহ করে কলকাতায় বিলাসে ভাসানো হয়। তৈরি হয় তাবেদার উকিল, কেরানিসহ হিন্দু মধবিত্ত ‘বাবু বাঙালি’ শ্রেণী। প্রতিষ্ঠা পায় স্কুল, কলেজ, পত্রিকা, সমিতি। কলকাতাকে তাবেদার ব্যক্তিবর্গ আর শোষনের উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা হয় বাংলাকে চুষে খাওয়ার জন্য এবং ঢাকাকেন্দ্রিক আদি ও অকৃত্রিম বাংলার মূল শক্তি, সামর্থ্য ও প্রতিবাদের ক্ষমতাকে ধ্বংস করার জন্য। এহেন কলকাতাকে ইংরেজ ও হিন্দুরা শোষনের ঘাঁটি হিসাবে তৈরি করে, যা পরবর্তীতে বাংলার অন্যান্য অংশের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। শুধু তাই নয়, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা পর্যায়েও এই শহর ও শহরবাসীর ভূমিকা অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক দেখতে পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কলকাতা সর্বশক্তি নিয়ে ইংরেজের পক্ষে দাঁড়ায়। পরবর্তীতেও এ চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশেষত ১৯০৫-১৯১১ এবং ১৯৪৭ সালের ভূমিকা অত্যন্ত কলঙ্কজনক। কলঙ্ক শুধু রাজনৈতিকই নয়--ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে কলকাতার মতো বিশ্বের অন্য কোন শহরে এত নির্মম রক্তপাত, দাঙ্গা ও হত্যাকান্ডসহ মানবতার অপমান হয়নি।
৪.
ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সামনে রেখে বলা যায় যে, সুলতানি ও মুঘল আমলের রাজধানী ও তাবৎ বঙ্গের শক্তিকেন্দ্র পূর্ববঙ্গ তথা ঢাকা ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসনামলে এসে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক দিয়ে হয়ে যায় দুর্বল, অদক্ষ এবং সুপরিকল্পিতভাবেই অকার্যকর ও অসক্রিয়তার দ্বারা সীমাবদ্ধ। একজন বিশিষ্ট গবেষক দেখতে পান যে:
‘‘জনকল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য যে অর্থ এ এলাকায় ব্যয় করা হতো তা ছিল বাস্তব প্রয়োজন অপেক্ষা নিতান্তই অপ্রতুল। এমনকি, এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান সমস্যাকেও উপেক্ষা করা হতো--শিক্ষা ছিল অবহেলিত, যোগাযোগ ও উৎপাদন ব্যবস্থা অনুন্নত। কৃষকরা সাধারণত কলকাতায় বসবাসকারী জমিদার এবং তাদের এজেন্ট ও কর্মচারীদের হাতে অত্যাচারিত হতো। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও এ অঞ্চল দারুনভাবে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম বন্দরের কোন উন্নতি না হওয়ার ফলে পূর্ব বাংলার বড় বড় নদীগুলোকে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের জন্য যথাযথ ব্যবহার করা হয়নি। অথচ গঙ্গা অববাহিকার সঙ্গে উত্তর ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য টিকিয়ে রাখার জন্য এবং কলকাতার সঙ্গে উত্তর-পশ্চিমের পশ্চাৎভূমির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।’’
পূর্ব বাংলা তথা ঢাকার পশ্চাৎপদতা আর অবহেলার মুখে অচিরেই কলকাতা ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রত্যাশা এবং কলকাতার নব্যশিক্ষিত-ইংরেজভক্ত-হিন্দু-বাঙালিদের যৌথ উদ্যোগে উপমহাদেশের ব্রিটিশ সংস্কৃতি, আর্থিক ও সামাজিক প্রভাব বিস্তারের জন্য একটি অগ্রভূমিতে পরিণত হয়। ইংরেজ প্রণীত নতুন প্রশাসন ব্যবস্থায় যারা সবচেয়ে বেশি লাভবান হন, তারা হল কলকাতাকেন্দ্রিক-নব্যশিক্ষিত-ইংরেজভক্ত-হিন্দু-বাঙালি, কলকাতার ব্যবসায়ী মহল এবং অধিকাংশই ইংরেজ কোম্পানির সমর্থনপুষ্ট। বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জণ শুরু থেকেই এরা নতুন শাসকদের নিঃশর্ত সমর্থন ও আনুগত্য করার মাধ্যমে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এবং যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে তাদেরকে একটি অধিক প্রভাবশালী গ্রুপ হিসাবে গণ্য করা হয়। এরা অর্থনীতি ছাড়াও কংগ্রেস রাজনীতিতে নেতৃত্ব দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু জাতীয়তাবাদকে সম্প্রসারিত করে।
ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের অবক্ষয়ের চিত্রটি হাল আমলের গবেষণাতেও ধরা পড়েছে। একজন বিদেশী গবেষক জানাচ্ছেন:
“Colonial Kolkata was more than Bengal’s prime administrative and cultural city. It also emerged as its commercial and economic hub. Valuable cash crops such as opium (for the Chinese market) and indigo and tea (for the European market) were transshipped in its ports, and jute from the field of eastern Bengal was processed in its many jute factories before being exported.’’
ঢাকার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও গুরুত্ব হারানোর সঙ্গে সঙ্গে এর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের চিত্রও গবেষকরা উপস্থাপন করেছেন:
“At the same time, however, many industrial centers in eastern Bengal declined or stagnated. the most dramatic example was Dhaka, which, till the early eighteenth century, had been the capital of Bengal and, till the British take-over, a major textile-exporting city. By 1800, however, British commercial policies and the rise of Kolkata had led to a sharp decline.”
বিদ্যমান শোষণ ও অবহেলায় ঢাকা কিভাবে মানবশূন্য হয়ে যায়, তার বিবরণ বড়ই মর্মান্তিক:
“Dhaka’s exports of fine textile had halved and would soon disappear; its population had shrunk to about 200,000 and would dwindle to about 50,000 in the 1840s, Dhaka’s lowest point.”
Willem Van Schendel, A History of Bangladesh গ্রন্থে আরো জানাচ্ছেন যে, ঢাকা ব্রিটিশ আমলে জনশূন্য বিরান শহর থেকে আবার জমজমাট হয় তথাকথিত বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে এবং এর ক্ষমতা পুরোপুরি ফিরে পায় ১৯৭০-এর দিকে:
“After the Dhaka began to recover gradually, mainly as a result of the jute trade and administrative expansion, but it did not recover the population level of 1800 till the 1930s and did not regain its industrial power till the 1970s.”
৫.
বাস্তবতা যদিও দাবি করছিল যে, একটি মুসলিম-বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সৃষ্টি করে পূর্ববঙ্গ ও ঢাকার ঐতিহাসিক অবস্থান ফিরিয়ে দেওয়ার এবং ক্রমবর্ধমান হিন্দু প্রভাব থেকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে ঢাকা-পূর্ববঙ্গ ও এ অঞ্চলের মানুষদের রক্ষা করার। কিন্তু এমন মহতী উদ্যোগ নেওয়া ঔপনিবেশিক শোষক ইংরেজদের চিন্তা ও কাজে স্থান পায়নি। তারা যা করেছে, তা তাদের প্রশাসন ও শোষণের প্রয়োজনে। কিন্তু এহেন প্রশাসনিক বিন্যাসে ঢাকা, পূর্ববঙ্গ এবং স্থানীয জনগণ কিছু কাঠামোগত ও শাসন ও তৎসংশ্লিষ্ট সুবিধার অধিকারী হওয়ায় সেটাও কলকাতা আর সেখানকার হিন্দু কায়েমী স্বার্থবাদীগণ মেনে নিতে পারেনি। বরং তীব্র রক্তাক্ত, ধর্মান্ধ, সহিংস আন্দোলন আর বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই-এর মাধ্যমে তারা সেটাকে বানচাল করে দেয়। অতএব এ পর্যায়ে আমাদের দেখা দরকার: ক) প্রশাসনিক পরিবর্তনের মাধ্যমে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের পটভূমি ও রূপরেখাটি কেমন ছিল; আর খ) ঢাকা ও পূর্ববঙ্গকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশ গঠনকে ‘বঙ্গভঙ্গ’ নাম দিয়ে কলকাতার হিন্দু বাঙালি শ্রেণীর আন্দোলন ও সন্ত্রাসের স্বরূপ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল।
(ক)
১৮৬৬-এর ঊড়িষ্যার দুর্ভিক্ষ মুকাবিলায় ব্যর্থতা থেকে সাধারণত এই রাজনৈতিক কাহিনীর সূত্রপাত ধরা হয়। বঙ্গদেশ ছাড়াও তখনকার বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম। দুর্ভিক্ষের মতো জরুরি অবস্থা সামলানো এত বড় একটা অঞ্চলের পক্ষে প্রায়-অসম্ভব ব্যাপার। এই যুক্তিতে স্যার স্টাফোর্ড নর্থকোট ১৮৬৮ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির বিশাল আয়তনের দিকে সরকারের দৃষ্ট আকর্ষণ করেন। ১৮৭৪ সালে আসামকে একটি চিফ কমিশনার শাসিত প্রদেশ হিসাবে তৈরি করা হয়, যার সঙ্গে বাংলাভাষী সিলেট অঞ্চলকেও জুড়ে দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা (কুমিল্লাসহ পার্বত্য ত্রিপুরা) নিয়ে গঠিত চট্টগ্রাম বিভাগকেও আসামের সঙ্গে দেয়ার প্রস্তাব নিয়েও নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে কথা হয় । ১৮৯৬ সালে আসামের চিফ কমিশনার স্যার উইলিয়াম ওয়ার্ড ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলাকেও আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা তোলেন। পরবর্তী চিফ কমিশনার স্যার হেনরি কটন পূর্ববর্তী প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং শুধু লুসাই পাহাড়কে আসামের অন্তর্গত করার পক্ষে মত দেন। ১৮৯৭ সালের ২৯ এপ্রিল ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত হয় যে, তখনকার মতো শুধুমাত্র দক্ষিণ লুসাই পার্বত্য অঞ্চল আসাম প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। বাংলার ভাগাভাগি নিয়ে কলকাতা কোন উদ্বেগ প্রকাশ করেনি এবং শান্তিপূর্ণভাবেই সবকিছু সম্পন্ন হয়।
এর পরের পর্যায়ের শুরু ১৯০১ সালে। এবারের প্রশ্ন সম্বলপুর নিয়ে। মধ্যপ্রদেশের চিফ কমিশনার স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার সম্বলপুর সমেত ঊড়িষ্যাকে বঙ্গ থেকে সরিয়ে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। ১৯০৩ সালের ২৮ মার্চ ফ্রেজার ঢাকা ও ময়মনসিংহ জিলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব বাংলার লাট লর্ড কার্জন গ্রহণ করেন এবং ১৯০৩ সালের ভাইসরয়ের মিনিটে (আলোচ্যসূচিতে) তা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ভিত্তিতে ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত সচিব এইচ.এইচ. রিজলে বাংলা সরকারের প্রধান সচিবকে এক চিঠিতে ঢাকা, ময়মনংংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেন। এই অবস্থায় প্রদত্ত প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব প্রসঙ্গে সরেজমিনে মতবিনিময়ের জন্য ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেন। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে, ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আর ২০ ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে নবতর প্রসাশনিক বিন্যাস সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেন এবং ব্যাপক মত বিনিময় করেন। তারপর তিনি ইংল্যান্ডে যান এবং বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ সরকারের উচ্চতর পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করেন। পুরো পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে কার্জন ১৯০৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ভারত সচিবকে প্রদেশের নতুন বিন্যাস সংক্রান্ত চূড়ান্ত প্রস্তাব পাঠান। ৯ জুন এক বার্তা মারফত ভারত সচিব এ ব্যাপারে সরকারের সম্মতির কথা জানান। ১৯ জুলাই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ ও আসাম নিয়ে ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ নামে নবতর প্রাদেশিক কাঠামোর কথা জানানো হয়। ঢাকা এই নতুন প্রদেশের রাজধানী হয় আর চট্টগ্রাম দ্বিতীয় সদর দফতর। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়, যার লোকসংখ্যা তিন কোটি দশ লক্ষ, তন্মধ্যে এক কোটি আশি লক্ষ মুসলমান আর এক কোটি কুড়ি লক্ষ হিন্দু। এখানে একটি আইন পরিষদ এবং একটি রাজস্ব বোর্ড থাকবে। এ পুনর্বিন্যাসে সমগ্র চা শিল্প এলাকা, পাট, ধানসহ কৃষি উৎপাদনের বিশাল অঞ্চল নতুন প্রদেশভুক্ত হয়।
(খ)
ঢাকা ও পূর্ববঙ্গ যখন একটি নতুন প্রাদেশিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে এবং বিকেন্দ্রিকৃত সুবিধার মধ্যে কাজ করার জন্য তৈরি, তখন কলকাতায় অঙ্গহানির আর্তনাদ শোনা যায়। এটা হল নতুন, প্রগতি আর আধুনিক ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার উজ্জ্বল নমুনা। কার্জন যখন বাংলাদেশ সফরকালে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রশাসনিক বিষয়ে মানুষের সঙ্গে মত-বিনিময় ও সভা-সমাবেশ করছেন, তখনই কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তীব্র বিরোধিতার সূচনা করেন হিন্দু-বাঙালি বুদ্ধিজীবীগণ, যাদের মধ্যে কেউ কেউ হিন্দু ও মুসলিম--উভয় বাঙালি মহলে সমাদৃত, যদিও তাদের তৎকালীন অবস্থান সমগ্রকে নয় নিজস্ব ধর্ম-সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেছিল ক্রমে ক্রমে আন্দোলন তীব্র সশস্ত্র পথে এবং হিন্দু ধর্মীয় উন্মাদনায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ‘পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ প্রদেশ প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে বাঙালি হিন্দু সমাজ স্মরণকালে সবচেয়ে ভয়াবহ আক্রমণমূলক ভূমিকায় অবর্তীণ হয় এবং বাংলা তথা ভারতে সন্ত্রাসবাদী রাজনীতির উদ্ভব ঘটায়। একজন ইতিহাসকার জানাচ্ছেন যে:
‘‘পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সমাজ কংগ্রেসের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ (বঙ্গভঙ্গের বদলে আসলে পাঠ করা উচিত ‘ঢাকায় নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠা’) রহিত করার এক সর্বাত্মক আন্দোলনে এগিয়ে আসে। বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত করতে গিয়ে স্বদেশী আন্দোলনের (হিন্দু জঙ্গিবাদ ) সূত্রপাত হয়। নবগঠিত পূর্ব বাংলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে, এ আশঙ্কায় কলকাতার হিন্দু সমাজ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। তারা বিশ্বাস করে যে, শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের তড়িৎ উন্নতিতে বাধা প্রদান করার জন্য সরকার পূর্ববঙ্গে মুসলিম ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সভার সভাপতি জমিদার মহারাজা মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বলেন, ‘নতুন প্রদেশে মুসলমানরা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর হিন্দুরা হবে সংখ্যালঘু। হিন্দুরা স্বদেশেই আগন্তুক হবে। এর সম্ভাবনা নিয়ে শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায় ভীত এবং স্বজাতীয়দের ভবিষ্যতের চিন্তায় মুহ্যমান।’ এ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যারিস্টার, উকিল, ব্যবসায়ী; আরো ছিলেন কেরানি, স্কুল শিক্ষক, বড় বাজারের মাড়োয়াড়ি, চাঁদনিচকের দোকানদার-সবাই হিন্দু।’’
কলকাতা থেকে কেন তারা (উপরের উদ্ধৃতিতে তারা কারা, সেই পরিচয় সুস্পষ্ট) একাট্টা হয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের বিরোধিতায় কোমর বেধে নেমে পড়ে, সেটার অনেক কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলো হলো:
• কলকাতার জমিদারদের স্বার্থে আঘাত, কারণ তারা এই শহরে বসে পূর্ববঙ্গে জমিদারির খাজনা আদায় ও নানাবিধ শোষণে মত্ত ছিল।
• কলকাতার ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার নষ্ট হওয়া। অর্থাৎ কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নতুন রাজধানী ঢাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজারের সম্প্রসারণ ও বিকাশের কারণে কলকাতার হিন্দু মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী মহলের ভীতি।
• নতুন প্রদেশে কোর্ট-কাচারি চলে যাবে, তাই কলকাতার হিন্দু আইনজীবী সম্প্রদায়ের বিরোধিতা।
• হিন্দু মালিক ও সাংবাদিকগণ পত্রিকার বাজার ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য হারাবে ঢাকার কাছে। ফলে তারাও বিরোধিতায় লিপ্ত।
• ঢাকা ও পূর্ববঙ্গের স্বতন্ত্র বিকাশ হলে কলকাতার বর্ণহিন্দুদের রাজনৈতিক কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কায় তাদের বিরোধিতা।
• নতুন প্রদেশে বঞ্চিত মুসলমান কৃষক-প্রজারা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, সেইজন্য বাধা প্রদান।
কলকাতার হিন্দু স্বার্থবাদী গোষ্ঠী প্রতিরোধের স্বরূপ ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে একজন গবেষক জানাচ্ছেন যে:
‘‘কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন এই আন্দোলনকে উৎসাহ যোগানোর জন্য এবং বাংলাভাষাভাষীদের একতাবদ্ধ করে বঙ্গভঙ্গ রহিত করার জন্য তাঁর বিখ্যাত গান ‘আমার সোনার বাংলা’ রচনা করেন। গানটি কোলকাতা টাউন হলের জনসভায় ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট প্রথমবারের মতো গাওয়া হয়।
রবি ঠাকুর এ সময় নতুন প্রদেশ ঠেকানোর জন্য আয়োজিত অন্তত দুটি জনসভায খোদ সভাপতিত্ব করেন। এসব সভায় ঢাকাকেন্দ্রিক ‘পূর্ববাংলা ও আসাম’ প্রদেশ কার্যকর করার দিন, অর্থাৎ ১৬ অক্টোবরকে ‘রাখিবন্ধন’ দিবসরূপে ঘোষণা করা হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর ‘মহালয়া’-এর দিনে কলকাতা শহরের কালিঘাটের বিখ্যাত কালিমন্দিরে হিন্দুরা বাংলাকে ভাগ করার কারণে (ঢাকায় নতুন প্রদেশ গড়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে) ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার ‘রক্ত শপথ’ নেয়। পুরো পরিস্থিতিটি বিশ্লেষণ করে একজন বিশিষ্ট গবেষক, যিনি নিজে ধর্মনিরপেক্ষ ও কমিউনিস্টও বটে, লিখছেন:
‘‘উচ্চবর্ণভুক্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর (কলকাতার বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়) নেতৃত্বে পরিচালিত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ‘স্বদেশী’ ধর্মীয় চরিত্র আন্দোলনের ঘটনাগুলোর মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দেমাতরম’ বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের রণহুঙ্কারে পরিণত হয়েছিল। ভদ্রলোক শ্রেণীর শক্তিপ্রতীক ব্যবহারের প্রতি অনুরাগ স্বদেশীকে হিংস্রতা অবলম্বনে সাহায্য করেছিল, সন্দেহ নেই।’’
হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও সন্ত্রাসবাদ কিরূপ চরম অবস্থান গ্রহণ করেছিল ঢাকাতে নতুন প্রদেশ স্থাপন করতে না-দেওয়ার কাজে, সে সম্পর্কে একটি বিশ্লেষণ প্রণিধানযোগ্য:
‘‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন অচিরেই চরমপহ্নীদের প্রাধান্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই সাম্প্রদায়িক আন্দোলন ১৮৯৭ সালে মারাঠা নেতা তিলক আয়োজিত ‘শিবাজি উৎসব’-এর মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ তথা কোলকাতায় ‘শিবাজি উৎসব’ শুরু করেন সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৯০৪ সালে। ১৯০৬ সালে কলকাতায় ‘শিবাজি উৎসব’-এর আয়োজন করেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। এই উৎসবে অন্যতম অঙ্গ ছিল ‘ভবানী পূজা’। ‘শিবাজি উৎসব’ ও ‘ভবানী পূজা’ উপলক্ষে মহারাষ্ট্র থেকে তিলক, খাপার্দে, মুঞ্জেকে কলকাতায় আনা হয়। লোকমান্য তিলক এই উৎসবের উদ্বোধন করেন। তিলক একদিন ত্রিশ হাজার লোক নিয়ে গঙ্গাস্নানে যান, সেই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে ছিল একখানি ভারতমাতার (বঙ্গমাতা বা বাংলা মায়ের নয়!) ছবি। বস্ত্তত এই আন্দোলনের নেতা তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধবদের জাতীয়তাবোধ পৌরানিক হিন্দুত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই পথ বঙ্কিম প্রদর্শিত ও অনুপ্রাণিত। অরবিন্দ ও তার দলের জাতীয়তার মূলে হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ভাবনাই প্রধান। তাই ‘বঙ্গভঙ্গ’ ও ‘স্বদেশী আন্দোলন’, ‘শিবাজি উৎসব’ বা ‘ভবানী পূজা’র রূপ পরিগ্রহ করেছিল। আর এ কারণেই বাংলার মুসলমান সমাজ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গ্রহণ করতে পারেনি।...প্রতিক্রিয়ার শেষ এখানেই হয়নি, ১৯০৭ সালেই বাংলাদেশে প্রথম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘঠিত হয়। পূর্ব বাংলার নানা স্থানে, যেমন জামালপুর, কুমিল্লা, পাবনায় দাঙ্গা হয়। ১৯০৭ সাল থেকেই সন্ত্রাসবাদীরা ‘অনুশীলন সমিতি’ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজনৈতিক হত্যা, লুণ্ঠন শুরু করে। আর এই সন্ত্রাসবাদীরা শুধু ইংরেজবিরোধী ছিল না, তারা মুসলিম বিরোধীও ছিল।’’
৬.
অথচ নতুন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করে। মুঘল রাজধানী ঢাকা নিজের লুপ্ত গৌরব ফিরে পায় এবং দ্রুত প্রসার লাভ করতে থাকে। প্রতি ক্ষেত্রেই উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেনেন্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সচেতন ছিলেন যে, মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং সরকারি চাকুরিতে তাদের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। অতএব নতুন প্রদেশের উন্নয়নের প্রতি তিনি বিশেষ যত্নবান হন। তাছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়ন ও অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও সড়ক পথের উন্নতি সাধনের জন্য এক বছরের মধ্যে বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্যের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে স্থানীয় বণিক ও বাণিজ্যিক পণ্যের নিরাপত্তা বিধানের জন্য নৌ-পুলিশের শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। গ্রামের সঙ্গে শহর এবং বাণিজ্য কেন্দ্রের সংযোগের জন্য পুরাতন রাস্তাসমূহের সংস্কার এবং নতুন নতুন রাস্তা নির্মাণের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।
নতুন প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ বিশেষভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং শিক্ষার সর্বক্ষেত্রেই সংস্কার সাধন করা হয়। মুসলমান ছাত্রদের জন্য সরকারে মঞ্জুরীকৃত বৃত্তির পরিমাণ বাড়ানো হয়--এতে অল্পকালের মধ্যেই স্কুল কলেজের ছাত্র সংখ্যা বেড়ে যা্য় এবং বিনা বেতনে পড়াশুনার সুযোগ সৃষ্টির জন্যও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থ বরাদ্ধ বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য অতিরিক্ত পদক্ষেপ হিসাবে বেশি সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়।
মাত্র ছয় বৎসর (১৯০৫-১১) অসম্ভব কিছু সাধন করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নয়। কিন্তু এ অল্প সময়েই যা কিছু করা সম্ভব হয়েছিল, সেটা মূল্যায়ন করে এবং যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, তাতেই নতুন প্রদেশ সৃষ্টির যৌক্তিকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়।
১৯০৫ থেকে ১৯১১ মাত্র ৫-৬ বছর সময়কালে রাজধানী ঢাকাকেন্দ্রিক নতুন প্রদেশের যে ব্যাপক এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় উন্নতি-অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল, তা রাজধানী-কলকাতার অধীনে ইংরেজ শাসনের ১৭৫৭ থেকে ১৯০৪ সাল এবং ১৯১২ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত কয়েক শ বছরের কাল-পর্যায়ে ভাবনাতীত ছিল। এর কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে:
• প্রোভিন্সিয়াল মোহামেডান এসোসিয়েশন: ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর প্রদেশের প্রথম দিনেই জনগণের রাজনৈতিক চিন্তাধারা বিকাশে নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে সংস্থাটি গঠিত হয় নথব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক সভার মাধ্যমে।
• সিমলা ডেপুটেশন ও সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেন্সি গঠনের খসড়া প্রস্তাব: ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর নবাব সলিমুল্লাহর অসুস্থতার কারণে তার প্রতিনিধিরূপে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও আবুল কাশেম ফজলুল হক আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে নবাব সলিমুল্লাহ প্রণীত সর্বভারতীয় মুসলিম কনফেডারেন্সি গঠনের খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন।
• সর্বভারতীয় মুসলিম নেতাদের ঢাকা সন্মেলন: নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম নেতারা অল ইন্ডিয়া মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স-এ যোগ দেন।
• উপমহাদেশের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ গঠন: ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক দল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার ২১ বছর পর ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব সলিমুল্লাহর উদ্যোগে ঢাকায় অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয় উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্দোলনের জন্য।
• ফজলুল হকের রাজনৈতিক জন্ম হয় নতুন প্রদেশের ঢাকাকেন্দ্রিক কার্যক্রমের মাধ্যমে।
• ঢাকায় সূচিত হয় নবনির্মাণের নতুন যুগ: নির্মিত হয় গভর্নর হাউস (বঙ্গভবন), রমনা এলাকায় সরকারি ভবনাদি, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, বর্ধমান হাউস (বাংলা একাডেমি), হুদা হাউস, কাকরাইল ও বেইলি রোড এলাকায় সার্কিট হাউসসহ বহু অফিস ও আবাসস্থল।
• রোমান্স অব ইস্টার্ন ক্যাপিটাল: ১৯০৫ থেকে ১৯১১ পর্যন্ত সময়কালে আবার সুলতানি ও মুঘল আমলের গৌরব ফিরে এসেছে মর্মে উল্লেখ করেন এফ. ব্রাডলি বার্ট তাঁর রোমান্স অব ইস্টার্ন ক্যাপিটাল গ্রন্থে।
• শিক্ষা ও চাকরি ক্ষেত্রে জাগরণের ঢেউ: ইংরেজ আমলে শিক্ষা, চাকরিসহ সর্বক্ষেত্রে মুসলমানরা সহনাগরিক হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় পিছিয়ে যায়। ১৯০১ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এ অঞ্চলে প্রতি দশ হাজার মুসলমানের (শতকরা বা হাজারে নয়, দশ হাজারে!) মধ্যে ইংরেজি জানতেন মাত্র ২২ জন!! হিন্দুদের মধ্যে এর সংখ্যা ছিল ১১৪ জন। সরকারি উঁচু পদে মাত্র ৪১ জন মুসলমান ছিলেন। তার বিপরীতে হিন্দুরা জনসংখ্যায় মুসলমানদের অর্ধেকের চেয়েও কম হওয়ার পরেও ১২৩৫টি পদ দখল করে রেখেছিল। ঢাকায় নতুন প্রদেশ শিক্ষা ও চাকরির দ্বার খুলে দেয় এবং স্থানীয় মুসলমান অধিবাসীগণ এক্ষেত্রে ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকেন।
• শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি: ১৯০৭-১৯১২ সময়কালে স্থবির পূর্ববঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় গড়ে ৩৭%ভাগে। এ সময়কালে, অর্থাৎ ঢাকায় রাজধানী ও প্রশাসনিক সুবিধা বিস্তারের কল্যাণে পূর্ব বাংলায় শিক্ষার্থী বৃদ্ধির পরিমাণ সর্বোচ্চ ৮২.৯% ভাগ পর্যন্ত উঠেছিল, যা সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের মধ্যে রেকর্ডস্বরূপ। ১৯০৬ সালে নবগঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশে কলেজিয়েট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১৬৯৮ জন এবং কলেজিয়েট শিক্ষার জন্য ব্যয় হতো ১,৫৪,৯৫৮ টাকা। ১৯১২ সালে ছাত্র সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫৬০ জনে এবং শিক্ষা ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩,৮৩,৬১৯ টাকায়, যা বঙ্গভঙ্গ রদের মাধ্যমে নতুন প্রদেশ বাতিলের সঙ্গে সঙ্গে আবার কমতে থাকে। একই চিত্র দেখা যায় সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রেও। ১৯০৫ সালে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৬,৯৯,০৫১ জন। তা ১৯১০-১১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৯,৩৬,৬৫৩ জনে। এ সময় প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা খাতের ব্যয় ১১,০৬,৫১০ টাকা থেকে ২২,০৫,৩৩৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় শিক্ষা ব্যয়ও ৪৭,৮১,৮৩৩ টাকা থেকে ৭৩,০৫,২৬০ টাকায় বৃদ্ধি পায়।
• শিক্ষার ব্যাপ্তি ও উন্নতি: শিক্ষার ব্যাপক বিস্তৃতি ও ব্যাপ্তি প্রমাণ সে সময়ে ভৌগোলিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গে নারী শিক্ষারও বিপুল অগ্রগতি হয়। ১৯০৮-০৯ সাল নাগাদ ৮১৯টি নতুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ২৫,৪৯৩ জনে। ঢাকার প্রাদেশিক সরকারের অধীনে এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে। ১৯১০-১১ সাল নাগাদ বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৫৫০টিতে। আর ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে গিয়ে হয় ১,৩১,১৩৯ জন। নতুন প্রদেশ গঠনের ফলে প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিক্ষারও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়। ১৯০৭-০৮ সালে পূর্ববঙ্গে মক্তব ছিল ১২৯৯টি। ১৯১১-১২ সালে তা ১৫৪৮টিতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সময় মক্তবগুলোতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০,১৮৮ থেকে ৫৪,৭০৩ জনে উন্নীত হয়। এ সময় বহু মাধ্যমিক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃত্তির সংখ্যাও বাড়ানো হয়। অনেকগুলো মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মিত হয় স্কুল ও কলেজকে কেন্দ্র করে। পূর্ববঙ্গে ১৯১১-১২ সালে ৮২টি মুসলিম ছাত্রাবাস ছিল।
• শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তা বৃদ্ধি: নতুন প্রদেশ গঠনের আগে স্কুল ও কলেজগুলোর প্রায়-সকল শিক্ষকই ছিলেন হিন্দু। লে. গভর্নর ফুলার এক আদেশে মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা কমপক্ষে ৩৩% বৃদ্ধির লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এর ফলে ১৯১২ সালে মুসলমান শিক্ষকের সংখ্যা ১৪,৬৫৬তে দাঁড়ায়। অন্যদিকে শিক্ষা বিভাগে মুসলমান অফিসারের সংখ্যা ছিল প্রায়-শূন্যের কোঠায়। এ সংখ্যা যুক্তিযুক্ত করার জন্য প্রাদেশিক সরকার প্রতিটি জিলায় মুসলিম জনসংখ্যানুপাতে উপ-পরিদর্শক নিয়োগের নির্দেশ দেয়। ১৯১২ সালে উপ-পরিদর্শকের সংখ্যা ১১৪ জনে উন্নীত হয়।
• নতুন জীবন ও সম্ভাবনার হাতছানি: নতুন প্রদেশ জনগণের সামনে নতুন ও সম্ভাবনাময় জীবনের দ্বার উন্মোচিত করে। নবাব সলিমুল্লাহর ভাষায় ‘‘বঙ্গভঙ্গ আমাদেরকে নিস্ক্রিয় জীবন থেকে জাগিয়ে তুলেছে এবং সক্রিয় জীবন ও সংগ্রামের পথে ধাবিত করেছে।’’ লর্ড কার্জন বলেন “The new province advanced in education, in good governance, in every mark of prosperity.” লর্ড হার্ডিঞ্জ অন্য ভাষায় নতুন প্রদেশ স্থাপনের ফলে অর্জিত উন্নতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।
• পেশাগত দিগন্তের উন্মোচন: নতুন প্রদেশ প্রতিষ্ঠার আগে পূর্ব বাংলার সরকারি চাকুরিতে বিভিন্ন দফতরে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ছয় ভাগের মধ্যে এক ভাগেরও কম। পুলিশ বিভাগে মুসলমানরা ছিল সবচেয়ে বঞ্চিত। মোট জনসংখ্যার ৬০% ভাগের বেশি হওয়া সত্ত্বেও ৫৪টি পুলিশ ইন্সপেক্টরের পদের মধ্যে বাঙালি মুসলমান ছিলেন মাত্র ৪ জন! ৪৮৪টি সাব-ইন্সপেক্টর পদের মধ্যে ছিলেন মাত্র ৬০ জন! আর ৪৫৯৪ জন কনস্টেবলের মধ্যে মুসলমান ছিলেন ১০২৭ জন। নতুন প্রদেশে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের চাকরিগত বৈষম্য অনেক কমে আসতে থাকে।
• সোনালি আঁশের সৌভাগ্য ও অর্থনৈতিক সুদিন: নতুন পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার কারণে বিশেষ ইতিবাচক প্রভাব জনগণের অর্থনৈতিক ভাগ্যের চাকা গতিশীল করে। এ সময় নতুন প্রদেশে নিজস্ব বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রধান অর্থকরী ফসল পূর্ব বাংলার সোনালি আঁশ পাটের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পায়। ১৯০৪ সালের চেয়ে ১৯০৬-১৯০৭ সালের পাটের দাম প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে যায়, যা পরবর্তী কয়েক বছর স্থায়ী হয়। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯৬-১৮৯৭ সালে প্রতি বেল পাটের মূল্য ছিল ৩০ টাকা। তা ১৯০৬-১৯০৭ সালে বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ৫৯ টাকায়। আন্তর্জাতিক বাজারের সুফলও বৃদ্ধি পায় এবং সেটা পূর্ব বাংলার কৃষকগণ সরাসরি লাভ করেন। কারণ, কলকাতার ফড়িয়া, ব্যবসায়ী সে সময় কমিশন ও বাড়তি লভ্যাংশ নিজেদের কব্জায় নেওয়ার মওকা পায় নি।
• শিল্প ও অন্যান্য: ঢাকাকেন্দ্রিক পূর্ব বাংলার শিল্প, কল-কারখানা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ক…ৃষ উৎপাদনসহ সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে এক ব্যাপক উন্নয়ন ও নবজাগরণের সূচনা ঘটে। সাহিত্য, চিত্রকলা, নন্দনতত্ত্ব, বিনোদন ও জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে আসে নতুন প্রাণাবেগ। ঢাকার সঙ্গে কেবল ভারতের প্রধান প্রধান শহরেরই নয়, বিশ্বের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও ব্যক্তিবর্গের যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের বীজ তখনই অঙ্কুরিত হয়।
একজন বিশিষ্ট গবেষক মূল্যায়ন করেছেন যে, ‘‘তাছাড়া এটা এ ইঙ্গিত বহন করে যে, একটা পশ্চাৎপদ অঞ্চলে সরকারি উদ্যোগে কতখানি উন্নয়ন সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে আরো অগ্রগতি সম্ভব হতো, যদি এ বিভাগ বিলুপ্তির জন্য তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা না হতো।’’
৭.
ব্যাপক রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও হিন্দু ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতায় জানমালের প্রভূত ক্ষতির মুখে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর নতুন প্রশাসনিক ব্যবস্থা তুলে নেওয়াকে বঙ্গভঙ্গ-রদ বলা হলেও আমরা এমনটি বলতে নারাজ। আমরা বলতে পারি যে, ঢাকার রাজধানীর মর্যাদা ও পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক মর্যাদা ছিনিয়ে নিয়ে আমাদেরকে আবার কলকাতার অধীনস্থ করা হলো। আম্বেদকরের মতো পন্ডিতও বলতে বাধ্য হলেন:
‘‘সারা বাংলা, উড়িষ্যা, আসাম এমন কি যুক্ত প্রদেশ পর্যন্ত ছিল বাংলার হিন্দুদের চারণভূমি। এ সবগুলো প্রদেশের সিভিল সার্ভিসই তারা দখল করে নিয়েছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল এ চারণভূমি হ্রাসকরণ। বাংলা বিভাগের বিরুদ্ধে হিন্দুদের এই বিরোধিতার মুখ্য কারণ হচ্ছে পূর্ব বাংলার বাঙালি-মুসলমানদেরকে তাদের ন্যায্য অংশ গ্রহণে বাধা দেয়া।’’
এর ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, সে সম্পর্কে একজন গবেষকের মূল্যায়ন প্রণিধানযোগ্য:
‘‘বাংলার মুসলমানগণ তাদের স্বার্থের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতার কথা ভুলতে পারেনি। তারা বুঝতে সক্ষম হন যে, একদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায় এবং অপরদিকে বিদেশী শাসকশ্রেণী--এ দুই শক্তির বিরুদ্ধে নিজেদের ন্যায়সঙ্গক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ কেবলমাত্র তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমেই সম্ভব।’’
আধিপত্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে চলমান এই সংগ্রাম কি শেষ হয়েছে?
রেফারেন্সঃ
. কারণ, ১৯০৫ সালে ‘বেঙ্গল ফোর্ট উইলিয়াম প্রেসিডেন্সি’ ভাগ করে যে এলাকা নিয়ে ‘পূর্ব বাংলা ও আসাম’ প্রদেশ গঠিত হয়েছিল, সে এলাকা একটি স্বতন্ত্র সত্তারূপে উপস্থাপিত হয় ১৯৪০ সালের ‘লাহোর প্রস্তাব’-এ। ১৯০৫ সালে ‘বঙ্গমাতার অখন্ডতা’ রক্ষার নামে প্রবল হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মাধ্যমে যারা ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ গঠনের বিরোধিতা করেছিল, তাদেরই প্রবল দাবির মুখে ১৯৪৭ সালে বাংলা দ্বি-খন্ডিত হয়ে ১৯০৫ সালের বাংলা বিভাগের সময়কালের আদলে ঔপনিবেশিক ইংরেজের কবল মুক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ নামে পূর্ণ রাষ্ট্রসত্তা অর্জন করে। ৪০০ বছর পরে ঢাকা আবার রাজধানীর মর্যাদা ফিরে পায়।
. দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ২০০৬.
. দেশভাগও যদি ধরি, তাহতে সেটাও তো ন্যায্যভাবে হয় নি। মুসলমান জনসংখ্যানুপাতে অবিভক্ত বঙ্গের প্রাপ্য অংশ আমরা পাই নি। মুসলিম প্রধান মুর্শিদাবাদ, মালদহ, আসামের কাছাড়, করিমগঞ্জ, গোয়ালাপাড়া, হাইলাকান্দি আমাদের পাওয়ার কথা ছিল। কথা ছিল, কলকাতা, যা পূর্ববঙ্গের রক্ত শোষণ করে গড়ে ওঠেছে, তারও অর্ধেক অংশ পাবে ঢাকা বা পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশ। কিন্তু দিল্লিতে র্যাডক্লিফ কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যোগসাজশ করে পূর্ববঙ্গকে বঞ্চিত করে।
বিস্তারিত জানতে দেখুন,
আবুল হাশেম, আমার জীবন ও বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি, কলকাতা: চিরায়ত, ১৯৮৮.
আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৫.
. মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি যখন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠল, তখন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করার প্রস্তাব করে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নেতৃত্বে সকল হিন্দু নেতা বাংলাকে ভাগ করার দাবির প্রথম উত্থাপক। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে এ বিভক্তির পক্ষে হিন্দু-বাঙালি নেতৃত্ব সক্রিয় হয়ে ওঠে। যে দাবিতে তারা অখন্ড ভারতের প্রস্তাব করে মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনে বাধা প্রদান করছিলেন, বাংলা ও পাঞ্চাব ভাগ করার দাবি ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত। সাম্প্রদায়িকতা ও দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতার নামেই তারা ভারত-বিভক্তি রোধ করতে চেয়েছিলেন; অথচ সেই সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিই তাদেরকে বাংলা ও পাঞ্জাব বিভক্তির মতো সঙ্কীর্ণ ও ধর্মান্ধ দাবির পথে টেনে নিয়ে গেল। ১৯৪৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে বাংলা ভাগের দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রচার করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য কৃপালিনীও আরেকটি বিবৃতিতে ‘বঙ্গভঙ্গ’-এর দাবি জানান।
বিস্তারিত দেখুন,
জয়া চ্যাটার্জি, বাংলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও পার্টিশান, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৯.
. S. Ahmad, Muslim Community in Bengal 1884-1912, S. Sarkar, The Swadeshi Movement in Bengal 1903-1908, K. K. Aziz, Britain and Muslim India, N. Ahmad, An Economic Geography of East Pakistan.
. বিস্তারিত জানতে, দেখুন,
অমর দত্ত, ঊনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৪.
মাহফুজ পারভেজ, ‘‘বাংলাদেশে রাজনৈতিক সন্ত্রাস: কতিপয় ঐতিহাসিক সূত্র’’, সেমিনার প্রবন্ধ, ঢাকা: বিআইসি, ২০০৯.
. A. Karim, Dacca the Mughal Capital.
. K.M. Mohsin, A Bengal District in Transition: Murshidabad 1765-93.
. নারায়ণ দত্ত, জন কোম্পানির বাঙালি কর্মচারি, কলকাতা।
. বিমলানন্দ শাসমল লিখেন, ‘‘ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য করতেই এসেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা দেশের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। এতে এক শ্রেণীর হিন্দুদের ও বিশেষত বাঙালি-হিন্দুদের উৎসাহ, প্ররোচনা এবং সক্রিয় সাহায্য ছিল সবচেয়ে বেশি। যে মুসলমান প্রভুত্ব হিন্দুরা নিজেদের আয়াসে ধ্বংস করতে পারেনি, ইংরেজের সাহায্যে এবং বুদ্ধিতে তারা সেই উদ্দেশ্যে সফল হলেন। ধীরে ধীরে মুসলমান প্রভুত্ব লোপ পেল। ইংরেজ হয়ে উঠল দেশের প্রভু।’’ বিস্তারিত দেখুন,
বিমলানন্দ শাসমল, ভারত কী করে ভাগ হলো, কলকাতা: হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯১, পৃ. ১৬-৭.
. বিস্তারিত জানতে, দেখুন,
মাহফুজ পারভেজ, ‘‘১৮৫৭: সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদবিরোধী স্বাধীনতার মহাসংগ্রাম’’, সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বিআইসি, ২০১০.
. পূর্ব বাংলার অবহেলা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ দেখুন, A. R. Mallick, “The Muslim and the Partition of Bengal”, in History of Freedom Movement, Part-3.
. এরা পলাশী বা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম তথা সিপাহী বিদ্রোহ কিংবা যে কোন ইরেজবিরোধী স্বাধীকার আন্দোলনের সময় প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা ও আনুগত্যের নির্লজ্জ্ব নমুনা প্রদর্শন করে। এদের কার্যক্রম জানতে, পড়ুন, মাহফুজ পারভেজের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭) সংক্রান্ত প্রবন্ধ, সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার।
. J. Long, Adam’s Report on Vernacular Education in Bengal, Behar (1835, 1836 and 1838).
. Willem Van Schendel, A History of Bangladesh, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.65.
. Iftikhar-ul-Awwal, “State of Indigenous Industries”, in Sirajul Islam (ed.), History of Bangladesh 1704-1971. Vol.II: Economic History, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.
. Ahmed, Dhaka: Recalling the Forgotten City, Dhaka: Bangla Academy, 1993.
. Willem Van Schendel, A History of Bangladesh, Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.66.
. বিভিন্ন সময়ের নানামুখী প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে দেখুন,
জয়া চ্যাটার্জি, বাংলা ভাগ হল: হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা ও পার্টিশান, ঢাকা: ইউপিএল, ১৯৯৯.
. ১৮৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর প্রশাসনিক যোগ্যতার প্রতীক লর্ড কার্জন ভারতের ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয়ের পদে সমাসীন হন।
. A.R. Mollick.
. এই প্রসঙ্গে কোন কোন সমালোচক খোদ রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করেন। এছাড়া যারা চরম সাম্প্রদায়িক অবস্থান গ্রহণ করে ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ স্থাপনের বিরোধিতায় লিপ্ত হন, তারা হলেন সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (তার ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকা এক্ষেত্রে তীব্র ভূমিকা পালন করে), মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী, নরেন্দ্রনাথ সেন, আনন্দমোহন বসু। যারা হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও ভারতের জাগৃতির জন্য স্বসমাজে নন্দিত। তাদের দর্শনে বাঙালিত্ব বলতে হিন্দুত্ব ও ভারতীয়ত্বের সংমিশ্রণ বুঝানো হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ সুরেন্দ্রনাথের নিজের লেখা A Nation in the Making এবং সমাদিত ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার রচনাসমূহ পাঠ করা যেতে পারে।
. বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রীক শতবর্ষের রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঢাকা: কথামেলা, ২০০৮.
. অমর দত্ত, ঊনিশ শতকের শেষার্ধে বাঙলাদেশে হিন্দু জাতীয়তাবাদ, কলকাতা: প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ১৯৯৪.
. S. Ahnad, p. 246.
. কাজী আনওয়ারুল হক, তিন পতাকার তলে, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮, পৃ. ৪৮.
. বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রীক শতবর্ষের রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঢাকা: কথামেলা, ২০০৮.
. বিদেশী পণ্য বর্জন এবং হিন্দুত্বের আদর্শে সংগ্রামের শপথ ছিল স্বদেশীদের মন্ত্র।
বিস্তারিত দেখুন, আবদুল মান্নান, বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ: ঢাকা-কলকাতাকেন্দ্রীক শতবর্ষের রাজনীতি এবং হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক, ঢাকা: কথামেলা, ২০০৮.
. আসহাবুর রহমান, ‘‘বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে ভদ্রলোক শ্রেণীর ভূমিকা’’. বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১.
. এইসব আন্দোলনের দর্শন বাঙালিত্ব ছিল না, ছিল হিন্দুত্ব। দার্শনিক নেতারাও বাঙালি ছিলেন না, ছিলেন বিশিষ্ট ভারতীয় হিন্দু। বঙ্গভঙ্গরদ করার জন্য বাঙালি হিন্দুদের হাতে বাঙালিত্বের কোন তত্ত্ব ছিল না; ছিল ভারতীয়ত্ব ও হিন্দুত্বের ধ্বজা।
. রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮১.
. Bradley Birt, Dacca: Romance of an Eastern Capital, p. 21.
. S. Ahmad, ibid. p. 399-410.
. ibid
. M. K. Molla, PhD thesis “New Province of Eastern Bengal and Assam”, (University of London), 1966.
. নবাব সলিমুল্লাহ উদীয়মান মুসলিম ব্যারিস্টার জিন্নাকে সন্মেলনে আনার জন্য একে ফজলুল হককে বোম্বে পাঠান। কিন্তু জিন্না কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকায় নীতিগতভাবে সন্মেলনে আসতে রাজি হননি।
. মুন্সি আবদুর রহমান আলী তায়েশ তার বিখ্যাত তাওয়ারিখে ঢাকা গ্রন্থে লিখেন: ‘‘ঢাকা এক সময় ছিল ইসলামি রাজধানী। ব্রিটিশ শাসন আমলে অনেক কাল পর তা আবার রাজধানীতে পরিণত হলো। এখন নবযুগের সুচনা হয়েছে। ঢাকাবাসীর সুপ্ত ভাগ্য প্রসন্ন হয়েছে। এখন উন্নতির ধারা বয়ে চলেছে। ঢাকাতে একটি সিভিল সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সময়ে যে সব স্থানে জাঁকালো সৌধ এবং শাহি প্রাসাদ দন্ডায়মান ছিল, আল্লাহর শুকুর, সে সব জায়গায় আবার নতুন করে নির্মাণ কাজ চলছে। এইসব উচ্ছন্ন স্থানে নতুন সৌধ নির্মিত হয়েছে। নবনির্মিত এলাকাকে বলা হয় ‘নিউ টাউন’।
. মুন্সিগঞ্জের এক জনসভায় তিনি এ উক্তি করেন।
. কেএম মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১, পৃ. ৯.
. B. R. Ambedker, Pakistan or Partition of India, p.11.
. ইংরেজ সরকারের এহেন সিদ্ধান্ত মুসলমানদের মনে এমন নিদারুণ আঘাত হানে যে, এটাকে তারা সত্যিকারার্থে একটি বিশ্বাসঘাতকতা বলে আখ্যায়িত করে। হিন্দু সম্প্রদায় ও কংগ্রেস দলের সম্মিলিত বিরোধিতামূলক আন্দোলনের জবাবে পূর্ব বাংলার মুসলমানরা প্রবল প্রতিরোধ ও বিক্ষোভ আয়োজনে সক্ষম ছিল এবং কলকাতা থেকে বেরিয়ে নতুন প্রদেশের মাধ্যমে তাদের উন্নতির ব্যাপারেও তারা সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের আশ্বাসের কারণে তারা আইনমান্যকারী সুশৃঙ্খল প্রজার ন্যায় আচরণ করে। কিন্তু ইংরেজ সরকার বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে প্রদত্ত ওয়াদার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করে, এমন কি, তাদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা ও মতামত গ্রহণ না-করেই এক তরফাভাবে নতুন প্রদেশটি উঠিয়ে নিয়ে ওয়াদা ভঙ্গ করে। আর হিন্দুরা প্রবল দাঙ্গা-হাঙ্গামার মাধ্যমে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলে সক্ষম হয়। এই অবস্থায় বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ ও বাঙালি হিন্দুদেরকে প্রতিপক্ষরূপে দেখতে পায়।
. কেএম মোহসীন, বঙ্গভঙ্গ, ঢাকা: সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ১৯৮১, পৃ.১২.
. বিস্তারিত জানতে, পড়ুন
মুহাম্মদ নূরুল আমিন, ‘‘ইন্ডিয়া ডকট্রিন’’, সেমিনার স্মারক ২০০৮, ঢাকা: বিআইসি।
আজিজুল হক বান্না, ‘‘বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এবং আমাদের অস্তিত্বের সংগ্রাম’’, সেমিনার স্মারক ২০০৮, ঢাকা: বিআইসি।
মাহফুজ পারভেজ, ‘‘বাংলাদেশের প্রতি ভারতের আচরণ’’, সেমিনার স্মারক ২০০৮, ঢাকা: বিআইসি।
আজিজুল হক বান্না, ‘‘ভারত-উৎসারিত বাংলাদেশবিরোধী বুদ্ধিবৃত্তিক ও মিডিয়া সন্ত্রাস’’, সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বিআইসি।
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, ‘‘বাংলাদেশ ও ভারত সম্পর্ক: অভিন্ন নদীগুলোর পানি বণ্টন’’, সেমিনার স্মারক ২০০৯, ঢাকা: বিআইসি।
সুপ্রকাশ রায়, ভারতের জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম, কলিকাতা: পত্রপুট, ১৯৮৩.
P. Hardy, The Muslims of India, Cambridge: The Cambridge University Press, 2002.